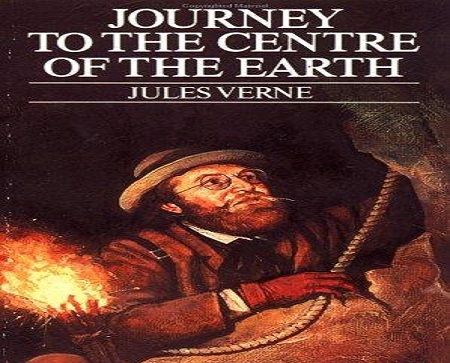০১. রুনিক হরফের ভোজবাজি
জার্মেনির হামবুর্গে কনিগ স্ট্রাস স্ট্রিট নামে যে রাস্তাটা আছে, সেইখানে পুরোনো একটা ছোটো বাড়িতে থাকতেন অধ্যাপক লিডেনক। লিডেনব্রক আমার কাকা।
কাকামণির কথা বলতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে চাইনে। রসায়ন, ভূতত্ত্ব আর ধাতুবিজ্ঞানে নিত্য-নতুন গবেষণা করে অধ্যাপক লিডেনকে যে কী পরিমাণ বিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন, আজকে তার আর কোনো বিশদ বিবরণ দেয়ার প্রয়োজন নেই। যখনকার কথা বলতে বসেছি, তখন কাকামণির বয়েস পঞ্চাশের মতো। কিন্তু এতো বয়েস হলে কী হবে, উৎসাহ-উদ্দীপনা তার বিন্দুমাত্র কম ছিলো না যুবকদের চেয়ে।
ভূতত্ত্ব পড়তে আমার ভালো লাগতো বলে কাকামণি নিজে আমাকে পড়ানোর ভার নিয়েছিলেন। তার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই অধ্যাপক লিডেনকের সহকারী বলে পণ্ডিতমহলে আমার নাম ছড়িয়ে পড়েছিলো।
আমি আর কাকামণি ছাড়া সেই পুরোনো বাড়িটায় থাকতো অনেক দিনের পুরোনো ঝি বুড়ি মাথা, আর কাকামণির ধর্মকন্যা গ্লোবেন। গ্লোবেন অবশ্য হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতো, কিন্তু সপ্তাহ-শেষে একবার করে তার বাড়ি আসাটা যেন নিয়ম হয়ে গিয়েছিলো।
সেদিন ছিলো সোমবার, পনেরোই মে। কড়া করে এক কাপ কফি তৈরি করে বসেছি, এমন সময় দেখতে পেলাম, কাকামণি হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন। হাতে একটা মোটা বই। কোনো দিকে দৃকপাত না করে কাকামণি সোজা পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। হাতের ছড়িটা এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, টুপিটা আছড়ে ফেলে দিলেন টেবিলের উপর। তারপর আমায় ডাকতে শুরু করে দিলেন : অ্যাকজেল! অ্যাকজেল!
কাকামণির হৈ-চৈ করার স্বভাব জানতুম বলে কফির কাপটা হাতে নিয়েই তাড়াতাড়ি পড়ার ঘরে এসে ঢুকলুম। পড়ার ঘর না বলে ওটাকে জাদুঘর বলাই উচিত। পৃথিবীর সমস্ত খনিজ পদার্থের নমুনা সে-ঘরে থাকে-থাকে সাজানে? কাকামণির সংগ্রহের বাতিক সারা জার্মেনিতে প্রসিদ্ধ ছিলো।
ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলাম, ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে কাকামণি সেই মোটা বইটা নাচাড়া করতে করতে তৃপ্তির স্বরে বলছেন : আহা, কী চমৎকার বই!
কাকামণির মাথায় যে খানিকটা ছিট ছিলো, এ-কথা অন্য কেউ না জানলেও আমি জানতুম। পণ্ডিতদের অমন হয়েই থাকে। কিন্তু তবু আমি অবাক হলুম একটু। কেউ যা পড়তেও পারেনি, তেমনি দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুঁথি ছাড়া কাকামণির কাছে অন্য কোনো বইয়ের কদর ছিলো না। কাকামণির হাতের বইটাও নিশ্চয়ই তেমনি কিছু হবে।
আমাকে দেখেই কাকামণি বলে উঠলেন : কথায় বলে, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলে পাইতে পারো অমূল্য রতন। সাংঘাতিক খাঁটি কথা! সেই ইহুদি বুড়োর দোকানটা তন্নতন্ন করে খুঁজে আজ এই রত্নটা উদ্ধার করেছি। আহা কী চমৎকার বই! আর দ্যাখ, বাঁধাই ও কী চমৎকার। কত পুরোনো হয়ে গেছে, কিন্তু তবু কী মজবুত আছে এখন। জানিস, কত পুরোনো বইটা? সাতশো বছরের। অথচ বইটার চেহারা,! একদম নতুনের মতো লাগছে না? এমন বাঁধানো বই দেখলে বড়ো-বড়ো দপ্তরিরা পর্যন্ত থ হয়ে যাবে।
জিজ্ঞেস করলাম : নাম কী বইটার?
নাম? তেমনি উত্তেজিত গলায় বললেন কাকামণি : বারো শতকে টার্লেশন নামে যে পণ্ডিত ছিলেন, বইটা তারই লেখা। নাম হিমস্ ক্রিলো!
জার্মান তর্জমা কে করেছে?
তর্জমা! তুই কি বলছিস অ্যাকজেল! এটা সেই আসল বই-খাঁটি আইসল্যাণ্ডের ভাষায় লেখা। আহা কী সুন্দর ভাষা, আর কী সাবলীল। ঠিক যেন জার্মান বই!
ছাপা কেমন? হরফগুলো দেখতে খুব সুন্দর বোধহয়?
ছাপা! কাকামণি যেন ভূত দেখলেন : ছাপা? বলিস কী রে তুই? এ হচ্ছে পাণ্ডুলিপিটা, হাতে লেখা পুঁথি–খাঁটি রুনিক হরফে লেখা।
রুনিক? অবাক হয়ে শুধোলাম : সে আবার কী?
ততোক্ষণে ভাষা সম্পর্কে কাকামণির বক্তৃতাটা শুরু হয়ে গেছে। অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতাটা সম্পূর্ণ শুনতে হলো। শেষটায় বললেন : সেকালে এই রুনিক হরফই আইসল্যাণ্ডে চলতি ছিলো। সেখানকার লোকদের মতে, দেব অডিন নাকি স্বয়ং এই বর্ণমালা তৈরি করেছিলেন। বইটা নাড়াচাড়া করতে-করতে কথাগুলো বললেন কাকামণি। হঠাৎ বইটার মধ্য থেকে ছোটো একটা বিবর্ণ, হলদে রঙের কাগজ মেঝেয় ছিটকে পড়লো। তক্ষুনি কাকামণি উদগ্রীব আগ্রহে সেটা তুলে নিলেন। খুব সাবধানে কাগজটার ভাজ খুলে মেলে রাখলেন টেবিলের উপর। কাগজটা লম্বায় পাঁচ ইঞ্চি, চওড়ায় ইঞ্চি-তিনেক হবে। কী-সব হিজিবিজি হরফে কি যেন লেখা কাগজটায়। কিন্তু কী যে লেখা, তার কোনো মাথামুণ্ডুই বুঝতে পারলাম না।
কাকামণি ততোক্ষণে মহা উৎসাহে কাগজটার পাঠোদ্ধারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমি নির্বিকার চোখে দেয়ালের ছবিগুলো দেখতে লাগলাম। কিন্তু একটু বাদেই শুনতে পেলাম কাকামণির গলা : রুনিক হরফেই তো চিরকুটটা লেখা। কিন্তু কী যে লেখা, তা তো বুঝতে পারছি নে?
দুনিয়ার সব ভাষা যার সমান দখলে, তার মুখে এমন কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু অবাক হওয়ার তখনও ঢের বাকি ছিলো। ক্রমশ তাঁর চোখে-মুখে উত্তেজনার এমন সব চিহ্ন জেগে উঠলো যা দেখে বোঝা গেলো চিরকুটটার কোনো মানেই উনি বার করতে পারছেন না। আর, মানে বার করতে না পারার দরুন, কাকামণি সেদিনই প্রথম খাবার ব্যাপারে অবহেলা দেখালেন। মার্থা যখন এসে খেতে যাওয়ার কথা বললে, তখন কাকামণি খাবারের নিকুচি করেছে বলে তাকে তাড়া লাগালেন। গতিক সুবিধের নয় দেখে আমি অবিশ্যি খাবারের ব্যাপারে অবহেলা করলাম না। গোগ্রাসে গিলে এলাম গিয়ে। বলা নিষ্প্রয়োজন, কাকামণির প্লেটটাও আমি একাই সাবাড় করলাম।
খাওয়া-দাওয়া সেরে পড়ার ঘরে গিয়ে দেখি, কাকামণি ভুরু কুঁচকে আপন মনেই বিড়বিড় করে বকছেন : হরফগুলো যে রুনিক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো মানে বুঝতে পারা যাচ্ছে না কেন? নিশ্চয়ই গোপন কোনো সঙ্কেতে চিরকুটটা লেখা। সেই সঙ্কেতটা কী বুঝতে পারলেই সব মানে স্পষ্ট হয়ে যাবে।
হঠাৎ চোখ তুলে আমাকে দেখতে পেলেন কাকামণি। তক্ষুনি একটা চেয়ার আমায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। বললেন, বোস। যা বলি, সব একটা কাগজে টুকে নে তো! রুনিক বর্ণলিপির যে হরফ আমাদের যে হরফের মানে বোঝায়, কাগজটা দেখে-দেখে তা আমি বলে যাচ্ছি। সাবধানে লিখিস। দেখিস যেন ভুল না হয়।
কাকামণি বলতে লাগলেন আর আমি লিখতে লাগলাম। লেখা শেষ হলে দেখি, অক্ষরগুলি এমনভাবে বসেছে, কোনো বাক্যই তৈরি হয় না, মানে বার করা তো দূরের কথা। লেখাগুলো এরকম :
rnlls esrevel seeclde sgtssmf
vnteief niedrke kt. samn atrate
saodren emtuoel uvaect rrilsa
Atsaar .nverc ieaabs ccdrmi
eevtVI frAurV dt,iac Oseibo
Kediil
লেখা শেষ হলে কাকামণি কাগজটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পড়বার চেষ্টা করলেন। নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন : কী মানে এর? মনে হচ্ছে এ কোনো সাঙ্কেতিক চিরকুট, ক্রিপটোগ্রাফ। অক্ষরগুলো যদি কোনোমতে ঠিক করে সাজানো যায়, তাহলেই কিস্তিমাত। কিন্তু…
কাকামণি বইটা আর কাগজটা মিলিয়ে দেখতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ধরে কী যেন লক্ষ্য করলেন উনি। তারপর বললেন : হুঁ, যা ভেবেছি তাই। চিরকুট আর পুঁথি যে দুই হাতের লেখা, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। চিরকুটটা। বইটার ঢের ঢের পরের লেখা। চিরকুটটার প্রথম হরফ হলো ইংরিজি জোড়া নাম-টার্লেশমের বইয়ে এমন কোনো হরফই নেই। এই হরফটা প্রথম ব্যবহার করা হয় চোদ্দ শতকে-তার মানে চিরকুটটা ঐ পুঁথিটার অন্তত দুশো বছর পরে লেখা হয়েছে। একটু থেমে আবার বললেন কাকামণি : আমার মনে হয়, যার কাছে এই পুঁথিটা ছিলো, এই রহস্যময় চিরকুটটা তারই লেখা। কিন্তু কে সেই ব্যক্তি? কার কাছে ছিলো পুঁথিটা? পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে কাকামণি জানালেন : না, তার নাম তো পাওয়া যাচ্ছে না!
বইটার প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত তন্ন-তন্ন করে দেখলেন কাকামণি, যদি কারও নাম পাওয়া যায়। কিন্তু কারও নাম পাওয়া গেলো না। এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার লোক ছিলেন না কাকামণি! আতস কাচ দিয়ে বইটার পাতাগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। প্রথম পাতায় এক কোণে অস্পষ্ট একটু কালির দাগ দেখা গেলো। অনেক পরীক্ষার পর বোঝা গেলো কালির দাগটা কতকগুলো আবছা-হয়ে-যাওয়া অক্ষরের সমষ্টি। ভালো করে সেই অক্ষরগুলো দেখতে-দেখতে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন কাকামণি : আরে, এ যে আর্ন্ সাক্ষ্যউজমের নাম! উনি তো আইসল্যাণ্ডের মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক! রসায়নে আজও তার জুড়ি পাওয়া যায়নি। শোনা যায়, উনি অ্যালকেমির গবেষণায় সাফল্য লাভ করেছিলেন। বোধ হয়, সাক্ন্যুউজম কোনো নতুন জিনিশ আবিষ্কার করে সঙ্কেতের সাহায্যে চিরকুটটায় লিখে গেছেন। কিন্তু কী তিনি লিখে গেছেন? কী?
কিন্তু কাকামণি, সাক্ন্যুউজম যদি নতুন কিছু আবিষ্কার করেই থাকেন, তবে এমন রহস্যময় সঙ্কেত ব্যবহার করেছেন কেন?
নিশ্চয়ই কোনো কারণ ছিল। কাকামণি জানালেন : গ্যালিলিয়ো যখন নতুন গ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন, তখন এমনিভাবেই সঙ্কেতলিপিতে সমস্ত তথ্য লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই সঙ্কেতের মানে আমাকে বের করতেই হবে। যতক্ষণ না এর অর্থ বার করতে পারছি, ততক্ষণ সব কাজ বন্ধ। বুঝলি অ্যাকজেল, এখন আমাদের একমাত্র কাজ হলো এই বিদঘুটে হরফগুলোর মধ্য থেকে মানে বের করা।
ভালো ছেলের মতো ঘাড় নেড়ে সায় দিতে দিতে ভাবলাম, কাকামণি যখন পুরোদস্তুর খেপে গেছেন, তখন আর রেহাই নেই, আহার নিদ্রা সব একেবারে বাতিল।
কাকামণি কিন্তু একটানা বলেই চলেছেন : কাজটা অবশ্যি মোটেই কঠিন নয়, একেবারে জলের মতো সোজা। চিরকুটটার মধ্যে একশো বত্রিশটা অক্ষর আছে, তার মধ্যে সাতাত্তরটা হলো ব্যঞ্জনবর্ণ, আর বাকিগুলি স্বরবর্ণ। সাউজম অনেক ভাষা জানতেন মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন তো। সুতরাং চিরকুটটা তিনি মাতৃভাষায় না লিখে লাতিনেই লিখেছেন বলে মনে হচ্ছে, কেমন। সেকালে লাতিই ছিলো পণ্ডিতদের ভাষা। কিন্তু গোলমেলে ব্যাপার হলো, হরফগুলো ওলট-পালট করে সাজানো হয়েছে। কী ভাবে সাজানো হয়েছে, তার ধরনটা বুঝতে না পারলেই সব মাটি। ঠিক কী করে যে সাজানো হয়েছে… ভুরু কুঁচতে গেলে কাকামণির। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, সাউজম লাইনগুলো সোজা না লিখে উপর থেকে নিচের দিকে লিখে
গেছেন। এই ধরনেও তো অনেকে সঙ্কেতলিপি লিখে থাকে।
সায় দিয়ে বললাম : তা লিখে থাকে বৈকি।
তাহলে এবার চটপট দেখা যাক সান্যউজম কী লিখেছেন। এই বলে গভীর মনোযোগর সঙ্গে চিরকুটটা পড়তে লাগলেন কাকামণি। অনেকক্ষণ ভাবনা-চিন্তার পর হরফগুলো এইভাবে সাজালেন : messvnka senrA ice fdok, seg nitt amvrtn.
না, কিছুই হলো না। উত্তেজিত স্বরে বললেন কাকামণি : এই ধরনে লিখলেও তো কোনো মানে হয় না। এই বলে চেঁচিয়ে উঠে একলাফে ঘর থেকে বেরিয়ে হুড়মুড় করে নিচে নেচে সোজা রাস্তায় গিয়ে হাজির হলেন কাকামণি, যেন বিদ্যুৎবেগে পাহাড়ের চুড়ো থেকে একটা বড়ো পাথর নিচে গড়িয়ে পড়লো। আর, তাই দেখে আমি তোত একেবারে হতভম্ব।
কাকামণিকে হঠাৎ এমনি উত্তেজিতভাবে বেরিয়ে যেতে দেখে মাথাও অবাক হয়ে আমায় এসে জিগেস করলে : উনি যে বেরিয়ে গেলেন বাওয়া-দাওয়া না করে?
খাওয়া-দাওয়া বোহ আজ আর কাকামণির বরাতে নেই।
মার্থাও আশ্চর্য হলো : তার মানে? রাত্তিরেও কি খাবেন না নাকি?
খাবেন বলে তো মনে হচ্ছে না। এই বলে আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আকাশ-পাতাল কত কি ভাবতে লাগলাম।
কাকামণির স্বভাব তত ভালো করেই জানা ছিলো। ঐ হেঁয়ালির কোনো সমাধান না হওয়া অবধি অন্য কোন দিকেই দৃকপাত করবেন না আর। তার মানে, ওর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও আহার-নিদ্রা সব সমাপ্ত।
হঠাৎ মনে হলো, চিরকুটটা একবার নেড়ে-চেড়ে দেখলে কেমন হয়? দৈবাৎ কোনো হাদশও তো মিলে যেতে পারে। কাগজটা টেবিল থেকে তুলে নিলাম। না, কোনো মানেই হয় না এর! মনে-মনে নানানভাবে সাজালাম অক্ষরগুলো। কিন্তু, বৃথাও হেঁয়ালির সমাধান করা মানুষের সাধ্য নয়। কাকামণি যেভাবে অক্ষরগুলো সাজিয়েছিলেন, তার এক জায়গায় পাওয়া গেল ইংরেজি icc, আরেক জায়গায় পাওয়া গেলো ইংরেজি Sir। এ ছাড়া কতকগুলো লাতিন শব্দও দেখা গেলো-rota, mutalsile, ira, nec, atra, luco। একটা হিব্রু শব্দও পাওয়া গেলো–talsiled। আরে,-তিন-চারটে ফরাসি কথাও তত রয়েছে দেখছি,–mer, are, mire!
মাথাটা আরো ঘুলিয়ে গেলো। ইংরেজি, লাতিন, হিব্রু, ফরাশি—চারচারটে ভাষা! বাব্বা! এর মানে বের করা আমার কর্ম না। বরফ, মশায়, রাগ, নিষ্ঠুর, পবিত্র, অরণ্য, পরিবর্তনশীল, মা, ধনুক, সমুদ্র—এসব শব্দের মানে হয় কোনো? বরফ আর সমুদ্র কথাটি অবশ্য আইসল্যান্ডের কোনো লোকের লেখায় বেশ মানানসই। কিন্তু বাকি কথাগুলোর মানে কী?
ভাবতে ভাবতে craterem, terrestre-এমনি আরো কয়েকটা লাতিন কথা চোখে পড়লো।… আরে, এখন তো বেশ মানে বোঝা যাচ্ছে। শেষ লাইনের শেষ হরফে শুরু করে ডান থেকে বাঁয়ে পড়তেই সব মানে স্পষ্ট বোঝা গেলো। আর, যেই বুঝতে পারলাম, অমনি উত্তেজনায় ভরে গেলো মন। কী সর্বনাশ! এ কী লেখা চিরকুটে! একথা জানলে কাকামণিকে আর কোনোমতেই ঘরে আটকে রাখা যাবে না। তক্ষুনি ছুটে বেরুবেন উনি! অসম্ভব। কিছুতেই একথা ওঁকে জানালে চলবে না।
তক্ষুনি মনে হলো, এই চিরকুটটা আমার নষ্ট করে ফেলা উচিত, নইলে একবার যদি কাকামণি বুঝতে পারেন কী লেখা আছে এতে, তাহলে আর রেহাই নেই।
চিরকুটটা তুলে নিয়ে চুল্লিতে ফেলতে যাচ্ছি, এমন সময়ে কাকামণি ঝড়ের মতো ঘরে এসে ঢুকলেন। তাকে দেখেই সাত-তাড়াতাড়ি কাগজটা টেবিলের উপর রেখে দিলাম। কাকামণির চেহারা দেখে বোঝা গেলো, বাইরে গিয়েও তিনি মুহূর্তের জন্য স্বস্তি পাননি–চিরকুটটা তাকে ভূতের মতো তাড়া করে ফিরেছে।
চেয়ারে বসে কাকামণি কাগজ-কলম নিয়ে কি সব লিখতে লাগলেন। একবার লেখেন, তার পরেই তা ঘ্যাচ করে কেটে ফেলেন। ওঁর রকম-সকম দেখে আমার বুক দুরুদুরু করতে লাগলো। এই বুঝি পাঠোদ্ধার করে ফেলেন লেখাটার।
কিন্তু না, সে আশা করাটা রীতিমতো বাতুলতা। চিরকুটের একশো বত্রিশটা অক্ষর অসংখ্যভাবে সাজানো যায়। কতভাবে আর সাজাবেন কাকামণি! আসল সঙ্কেতটা না বার করতে পারলে চিরকাল এই গোলোকধাঁধায় পথ হাতড়ে বেড়াতে হবে। কিন্তু তবু আমার ভয় করতে লাগলো। যদি চিরকুটটার অর্থ করতে পারেন উনি।
অনেকক্ষণ কেটে গেলো। সন্ধে হলো, রাত হলো, রাত গভীর হলো, পথঘাটের সোরগোল থেমে গেলো, কিন্তু তবু হুঁশ ফিরলো না কাকামণির। একমনে উনি অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে চলেছেন।
মার্থা একবার দরজা দিয়ে উকি দিয়ে বলেছিল, খাবার তৈরি। কিন্তু কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে সে আস্তে-আস্তে চলে গেল। আমি নিরুপায়ভাবে বসে রইলাম। তারপর কখন যে চেয়ারের উপরেই ঘুমিয়ে পড়লাম, তা জানি না।
ভোরবেলা যখন চোখে-মুখে এসে বোদ পড়লো, তখন ঘুম ভাঙলো আমার। বড়মড় করে উঠে বসলাম আমি। তাকিয়ে দেখি, তখন কাকামণি ঘাড় গুঁজে হরফের পর হরফ সাজিয়ে চলেছেন। চোখদুটো রাঙা টকটকে, মুখ শুকিয়ে গেছে, আলুথালু চুল এসে পড়েছে চোখে-মুখে, সারা শরীরে রাত-জাগার ক্লান্তি। রাতটা যে ওর এইভাবে কাটবে, তা আমি জানতাম। কিন্তু কী করতে পারি আমি? যদি ওকে সব খুলে বলি, তাহলে উনি তো সঙ্গে সঙ্গে রওনা হবেন মৃত্যুর পথে। অথচ এমন ভীষণ মানসিক শ্রমেও একটা কিছু বিপদ-আপদ ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। কী করবো ঠিক করতে না পেরে চুপচাপ বসে রইলাম।
শেষ পর্যন্ত কাকামণির রকম-সকম দেখে সব কিছু খুলে বলা উচিত বলেই ঠিক করলাম। আস্তে-আস্তে জিগেস করলাম, সাক্ষ্যউজমের চিরকুটটার কোনো। মানে বের করতে পেরেছে কাকামণি?
সচমকে আমার দিকে ফিরে তাকালেন উনি, আকুল হয়ে আমার হাত ধরলেন। দেখতে পেলাম ওঁর হাতদুটি থরথর করে কাঁপছে। এবার আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম, আমি কিন্তু এর মানে খুঁজে পেয়েছি। কাকামণি।
কাকামণি চেঁচিয়ে উঠলেন একবারে : পেরেছিস? মানে করতে পেরেছিল। তুই!
সঙ্কেতটা জানিয়ে দিলাম : যদি শেষ হরফ থেকে পড়তে থাকে, তাহলে তুমিও এর মানে বুঝতে পারবে কাকামণি।
আমার কথা শেষ হবার আগেই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন কাকামণি। মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল ওঁর চেহারা। চিরকুটটা হাতে তুলে নিয়ে এক নিশ্বাসে উনি পড়ে গেলেন :
In Sneffels joculis craterem quem delibat.
Umbra Scartaris julii intra calendas descende,
Audax viator, et terrestre centrum attinges
Quod feci, Arne Sakunussemm.
কথাগুলো লাতিন। তার মানে এই দাঁড়ায় :
হে নির্ভীক ভ্রামণিক। জুলাই মাসের গোড়ার দিকে যখন স্কাটারিস পর্বতচুড়োর ছায়া পড়বে স্নেফেল অগ্নিগিরির মুখের উপর, তখন সে-পথে অবতরণ করলে তুমি পৌঁছতে পারবে পৃথিবীর অন্তঃপুরে। আমি সে-পথে গিয়েছিলাম।–আর্ন্ সাক্ন্যুউজম।
ছোটো ছেলের মতো উল্লাসে কাকামণি রীতিমত নৃত্যকলায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তারপর হঠাৎ কী যেন মনে পড়তেই ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে নিস্তেজ গলায় শুধোলেন, কটা বাজলো?
দুটো।
তাই তো বলি, খিদেয় নাড়ি-ভুড়ি হজম হয়ে যেতে চাইছে কেন? ঈশ। কতো বেলা হয়ে গেছে দেখেছিস! চল, চল শিগগির খেতে চল। তারপর অনেক কাজ। মাল-পত্তর গুছোতে হবে তো।
সে কী? তার মানে?
শুধু আমার বাক্সই না, সেইসঙ্গে তোর বাক্সও গুছিয়ে নিতে হবে। এই বলে খাবার-ঘরের দিকে পা বাড়ালেন কাকামণি।
০২. বৈজ্ঞানিকের খেয়াল
বুকটা কেঁপে উঠলো। যে ভয় করছিলাম, শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো।
তখন অবশ্য মিছিমিছি বেশি মাথা ঘামালাম না। কাকামণি তো একেবারে পাগল নন। ভাল-মন্দ বুঝবার শক্তি নিশ্চয়ই তাঁর আছে। পৃথিবীর অন্তঃপুরে ঘুরে বেড়ানো কি আর সম্ভব? তাই তখনকার মতো সব ভাবনা-চিন্তা ঝেড়ে ফেলে খাবার ঘরে ঢুকলাম।
ঢুকে দেখি, কাকামণি পর্বতপ্রমাণ খাবার নিয়ে বসেছেন। কালকে সারাদিনে খাওয়া-দাওয়া হয়নি, তাই আজ তার শোধ তুলছেন।
খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে কাকামণি আমাকে আবার পড়ার-ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। চেয়ারে আয়েস করে গা এলিয়ে দিয়ে কাকামণি বললেন, অ্যাকজেল, তুই যে আমার কী উপকার করেছিল তা বলে বোঝাতে পারবো না। কিন্তু সাবধান, এ-কথা যেন কাক-পক্ষীও টের না পায়। একবার যদি কেউ এ কথা জানতে পারে, অমনি সেফেলে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো লেগে যাবে।
আমি বাধা দিয়ে বললাম, আচ্ছা কাকামণি, তুমি কি মনে করো লোকে এ-কথা বিশ্বাস করবে?
সকলের কথা বলতে পারিনে। কিন্তু কোনো বিজ্ঞানী এ-কথা জানতে পারলে তখুনি যে আইসল্যাণ্ডে ছুটবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই!
আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না। চিরকুটের কথাগুলো যে সত্যি, তার তো কোনো প্রমাণ নেই?
কাকামণি আমার কথা শুনে তো রেগেই অস্থির! তুই বলতে চাস স্যাক্ন্যুউজম মিথ্যে কথা লিখে গেছেন? তা, তোমার মতো গবেট এ-কথা বলবে না তো কে বলবে? সেদিন পিটার্মানের কাছ থেকে যে ম্যাপখানা পেয়েছি, নিয়ে আয় সেটা। তোকে সবকিছু দেখিয়ে দিচ্ছি।
ম্যাপটা টেবিলের উপর বিছিয়ে কাকামণি বলে চললেন, এটা হলো আইসল্যাণ্ডের সবচেয়ে ভালো ম্যাপ, সমস্ত খুঁটিনাটি দেয়া আছে। এই দ্যাখ, কতোগুলো আগ্নেয়গিরি এখানে। এদের অনেকগুলোই এখন মরে গেছে। এবার এদিকে দ্যাখ, আইসল্যাণ্ডের এটা পশ্চিম উপকূলে। এটা হলো আইসল্যাণ্ডের রাজধানী রিজ কিয়াভি। এই উপকূলে অগুন্তি পর্বতময় ঘাঁটি আছে। এইটে হলো পয়ষট্টি ডিগ্রি অক্ষাংশ। আর এটা হলো একটা ছোটো উপদ্বীপ। এবার এর বরাবর উপরে তাকিয়ে দ্যাখ। বল দিকিন এটা কী?
সমুদ্রের কোল থেকে একটা পাহাড় উঠেছে।
এই পাহাড়টাই হলো স্নেফেল। এই পাহাড়ের চুড়ে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু। এই চুড়োর উপরে যখন স্কার্টারিস পর্বতচুড়োর ছায়া পড়বে, তখন পাওয়া যাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরে যাবার পথ।
অসম্ভব! সে কী করে হবে? এই আগ্নেয়গিরির মধ্যে হয়তো এখন জ্বলন্ত আগুন, অঙ্গার, ছাই, ধাতু, লাভা-সবকিছুই আছে–
মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কাকামণি বললেন, পৃথিবীর বেশির ভাগ আগ্নেয়গিরিই তো এখন নিভে গেছে। এইটে যে যায়নি তা তুই কী করে জানলি? বাবোশো উনিশ সালে স্নেফেল শেষবার অগ্ন্যুদ্গার করেছিল। এরপর থেকে তো একদম চুপ করে আছে।
বলেই চললেন কাকামণি : সাকৃউজম যে কতত হুঁশিয়ায় হয়ে এ-কথা লিখে গেছেন, তা তুই বুঝতে পারিসনি এখনো। আমাদের যাতে কোনো ভুল না হয় সেজন্য তাঁর কতো সতর্কতা, সেটা তুই খেয়াল করেছিস? স্নেফেলের অনেকগুলো জালামুখ। যে-জ্বালামুখটা দিয়ে ঢুকলে একবারে পাতালে পৌঁছনো যায়, সেটা বোঝানোর জন্যেই জুলাই মাসের কথা উল্লেখ করেছেন উনি। জুলাই মাসের গোড়ার দিকে স্কার্টারিস পর্বতচুড়োর ছায়া ঠিক সেই নির্দিষ্ট মুখের উপর পড়ে। এটা উনি খুব ভালো করে লক্ষ্য করেছিলেন বলেই লিখে গেছেন। এর পরও কি ওঁকে অবিশ্বাস করা চলে?
কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে সাকউজম তার দেশের চলতি প্রবাদ শুনেই এ-কথা লিখে গেছেন? আইসল্যাণ্ডের লোকেদের হয়তো ধারণা ছিলো যে এই পাহাড়ের মুখ দিয়ে একেবারে পৃথিবীর মধ্যখানে গিয়ে পৌঁছনো যায়। এমন প্রবাদ তো কতো দেশেই শুনতে পাওয়া যায়। এইটেও হয়তো তেমনি একটা কিছু।
কাকামণি চটে উঠে বললেন, আর-কিছু বলবার আছে তোর?
আছে! বললাম আমি। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে যাওয়া অসম্ভব, বিজ্ঞান সে-কথা জোর গলায় বলে। বিজ্ঞান বলে যে, পৃথিবীর ভিতর অসহ্য উত্তাপ, যে-উত্তাপে কোনো প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। পৃথিবীর নিচে প্রতি সত্তর ফুট অন্তর এক ডিগ্রী করে উত্তাপ বাড়ে। সে হিশেবে পৃথিবীর ঠিক মধ্যখানের উত্তাপ দাঁড়ায় তিন লক্ষ হাজার বত্রিশ ডিগ্রির কাছাকাছি। সেখানটা গ্যাসে ভরা।
তাহলে তোর প্রধান আপত্তি হলো সাঙ্ঘাতিক উত্তাপ, তাই না?
জোর গলায় বললাম, নিশ্চয়ই! বিজ্ঞান এ-কথাও বলে যে, পৃথিবীর ত্রিশ মাইল নিচু পর্যন্ত মাটি, বালি বা কাদা। তারপরেই জ্বলন্ত তরল পদার্থ।
কাকামণি রাগ করে বলে উঠলেন, আমোক কি আর কথায় বলে–অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী! পৃথিবীর নিচে কী হচ্ছে-না-হচ্ছে সে-কথা কেউই নিশ্চয় করে বলতে পারে না, সবই আন্দাজের ব্যাপার। বিজ্ঞান তো এখনো রীতিমতো শিশু। সে আজ যে-কথা বলে, কালকেই তার উল্টো কথা বলে। তুই নিশ্চয়ই মস্ত বড়ো বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক পোজঁসের নাম শুনেছিস। উনি কি বলেন নি যে, যদি পৃথিবীর নিচে তিন লক্ষ ষাট হাজার বত্রিশ ডিগ্রি উত্তাপ থাকতো, তবে ঐ ভয়ঙ্কর উত্তাপ ভিতরে বন্ধ করে রাখার ক্ষমতা উপরের এই ত্রিশ মাইল মাটির মোটই থাকতো না-কবে ভেঙে-চুরে গুড়ো গুড়ো হয়ে যেত। আর শুধ পোঅঁস নন, আরো অনেকেই সে-কথায় সায় দিয়েছেন। পৃথিবীর ভিতরে যে গ্যাস বা আগুন নেই, এ তো সবাই জানে। হাজার-হাজার বছর আগে যে-সব আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুদ্গার করত, এখন তার বেশির ভাগই মরে গেছে। তার মানে কি এই নয় যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে! যাক-এ নিয়ে তোর সঙ্গে তর্ক করে কোনো লাভ নেই। চাক্ষুষ প্রমাণ নিলেই সতিমিথ্যে বোঝা যাবে। আঠারো শো পঁচিশ সালে স্যর হাফ্রি ডেভির সঙ্গে আমার তর্ক বেধেছিলো যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর এখনো তরল আছে কি না। শেষে মীমাংসা হলো যে তরল থাকতেই পারে না।
কোন যুক্তির উপর নির্ভর করে তোমরা সিদ্ধান্ত করেছিলে?
কাকামণি হেসে বললেন, এ তো খুব সহজ ব্যাপার। যা-কিছু তরল, তা-ই সমুদ্রজলের মতো চন্দ্রের আকর্ষণের পাল্লায় পড়ে। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ যদি তরল হতো তাহলে নিশ্চয়ই দিনে দুবার করে তা জোয়ারের মতো ফুলে-ফেঁপে উঠতো। তাতে নিয়মিত সময়ে দু-বার করে ভূমিকম্প হতো দিনে।
আমি আর কোনো যুক্তি খুঁজে না পেয়ে বললাম, কিন্তু পাতালে যাবে কী করে? যা অন্ধকার–
কেন? টর্চ নেই?
শুকনো গলায় বললাম, তাহলে পৃথিবীর অভ্যন্তরে গেলেও যাওয়া যেতে পারে?
উত্তেজিত হয়ে কাকামণি বললেন, তার মানে? নিশ্চয়ই যাওয়া যাবে। নইলে এতক্ষণ ধরে তোকে কী আর বোঝালাম?
আমি আর কোনো কথা না বলে নীরবে পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। কাকামণির কথা শুনে মাথাটা ঝিমঝিম করলো। একটু ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেড়িয়ে এলে ভালো লাগবে বলে মনে হলো। পথে বেরিয়ে লক্ষ্যহীনের মতো অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু মনে হলো যেন হ্যামবুর্গ শহরে একটুও হাওয়া নেই।
কাকামণির কথা শুনে বোঝা গেছে যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে না গিয়ে ছাড়বেন না কোনোমতেই। অথচ পাতালে যাওয়া যায় বলে আমার বিশ্বাস হতে চাইছিলো না। যতোই যুক্তি দেখান কাকামণি, পৃথিবীর অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই দিনরাত আগুন জ্বলছে। মানুষের পক্ষে কি আর সেখানে যাওয়া সম্ভব?
অনেকক্ষণ পর বাসায় ফিরে এসে দেখলাম, গ্লোবেন হোস্টেল থেকে ফিরে এসেছে কী উপলক্ষে দিন-দুয়েকের ছুটি পেয়েছে বলে। ওকে দেখতে পেয়ে সবকিছু খুলে বললাম। ও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, এ তো খুব গৌরবের কথা, অ্যাকজেল। ভয় কিসের? সম্ভব হলে আমিও তোমাদের সঙ্গে যেতাম। ইতিহাসে তোমাদের নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। ভাবতেও তো আমার রীতিমতো হিংসে হচ্ছে।
এ-কথার জবাবে আর কী বলতে পারি আমি? চুপচাপ নিজের ঘরে চলে এলাম। সারা রাতটা কাটলো পাগলের মতো নানান এলোমেলো চিন্তায়। ভোরের দিকে কখন ঘুম এসেছিলো জানি নে, ভাঙলো লোকজনের শোরগোলে। কাকামণি একলাই চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় করে তুলেছেন।
হঠাৎ ঝড়ের মতো আমার ঘরে ঢুকলেন কাকামণি। তখনো শুয়ে আছি দেখে রেগে উঠলেন একেবার। শিগগির, শিগগির ওঠ! চটপট জিনিশপত্র গুছিয়ে নে। আমার কাগজপত্রও সব নি কিন্তু।
ভ্যাবাচাকা খেয়ে চিঁ-চিঁ করে বললাম, সত্যিই তবে যাব আমরা?
সত্যি না তো কি মিথ্যে? কালই তো আমরা রওনা হবে। তাড়াতাড়ি ওঠ তুই-এই বলে আমাকে আরো হতভম্ব করে দিয়ে কাকামণি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।
খানিকক্ষণ বাদে সম্বিত ফিরলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সেখানে তখন ভীষণ ব্যাপার। বাক্স, পোর্টম্যান্টো, দড়ির মই, গিঠদেয় দড়ি, মশাল, বড়োবড়ো শিশি-বোতল, কুঠার, গাইতি-কতো কী ছড়ানো!
এমন সময় পিছন থেকে গ্রোবেন আমায় ডাক দিলে। বললে, অতো ভয় পাচ্ছে। কেন তুমি? বাবার সঙ্গে এইমাত্র আমার আলোচনা হলো। যা বললেন তাতে বুঝলাম, যে কাজে তোমরা নামছ, তা মোটেই অসম্ভব নয়। আমার মন বলছে, তোমরা সফল হবেই।
গ্রোবেনের দৃঢ় গলা শুনে একটু জোর পেলাম মনে। ওকে সঙ্গে নিয়ে কাকামণির ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। আচ্ছা কাকামণি, যেতেই যদি হয়, তবে এতে তাড়াহুড়ো করবার দরকার কী? এখনও তো ঢের সময় হাতে আছে। এখনও তো মে মাসই শেষ হয়নি–
আইসল্যাণ্ড তত আর দুদিনের পথ নয়-বললেন কাকামণি জুনের শেষের দিকে আমাদের স্নেফেলের উপর উঠতে হবে। তারপর জুলাই মাসের গোড়ার দিকে সে পয়লা জুলাইও হতে পারে, দোসরাও হতে পারে–আমাদের কেটারের মধ্য দিয়ে নিচে নামতে হবে। এ ছাড়া এক্ষুনি কোপেন–
হেগেনের জাহাজের আপিস থেকে আইসল্যাণ্ডের টিকিট কাটতে হবে। কারণ, মাসে শুধু একবার কোপেনহেগেন থেকে জাহাজ ছাড়ে আইসল্যাণ্ডের দিকে। এ মাসে সে তারিখটা হলো বাইশে মে। কাজেই দেখ-হাতে মোটেই সময় নেই আমাদের।
বললাম, কিন্তু বাইশে জুন জাহাজে চড়লেও তো চলে।
না, চলে না। কাকামণি যেন একটু রেগে উঠলেন : তাতে প্রচুর দেরি হয়ে যাবে। কারণ, কখন যে স্কার্টারিস পর্বতচুডোর ছায়া স্নেফেলের উপর পড়বে, তার কোনো ঠিক নেই। সেইজন্যে আমাদের সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। তাই কোপেনহেগেনে যতো শিগগির পৌঁছুনো যায় ততই ভালো।
সুতরাং সারাদিন জিনিশপত্র গোছগাছ করতেই কাটল। সন্ধেবেলা কাকামণি জানালেন যে, পরদিন ভোর ছটায় আমরা রওনা হবে।
রাত দশটার সময়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম কি আর সহজে আসে? রাত সতো গভীর হলো, ততোই ভয় করতে লাগলো। তার থে; কটা দুঃস্বপ্নও দেখলাম। মনে হলো, যেন পৃথিবীর অভ্যন্তরে নেমেছি। নিরেট অন্ধকার। চলতে-চলতে এক সময় এক গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলেছি। হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়েছি একটা বড়ো পাথরে, আর সঙ্গে-সঙ্গে সারা পৃথিবী ভেঙে পড়েছে আমার গায়ের উপর। সঙ্গে-সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেলো। ঘড়িতে তখন পঁচটা বাজে।
হাত-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় পরে নিচে নেমে দেখি কাকামণি প্রাতরাশে বসেছেন। আমাকেও তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ করে নিতে বললেন। এখুনি রওনা হতে হবে।
সাড়ে পাঁচটার সময় একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেলো ফটকের সামনে। মালপত্র তোল। হলো গাড়িতে। গ্রোবেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি আর কাকামণি গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসলাম। গাড়ি ছেড়ে দিলো। চলতে লাগলো স্টেশনের দিকে।
০৩. আইসল্যাণ্ডে
কোপেনহেগেন শহরটা দেখতে ভারি সুন্দর। রাজপ্রাসাদটা কী বড়ো! চারধারে তার পরিখা। পরিখার উপরে একটা সেতু। ষোলো শতকে তৈরি হয়েছিলো।
আমরা কোপেনহেগেনে এসে পৌঁছেছিলাম বেলা দশটার সময়। স্টেশন। থেকে সমস্ত মালপত্র ফিনিক্স হোটেলে পাঠিয়ে দিলেন কাকামণি। তারপর আমায় নিয়ে তখুনি চললেন মিউজিয়ামের দিকে।
সুন্দর শহরটা দেখতে-দেখতে চলেছি। এক্সচেঞ্জ আপিসের দালানের গম্বুজটা চমৎকার লাগছিলো। মনে হচ্ছিলো যেন চারটে সোনালি ড্রাগনের ল্যাজ জড়িয়ে-জড়িয়ে তৈরি। কাকামণির চোখ কিন্তু সেদিকে পড়লো না। কিছু দূরে যে আকাশ-ছোঁয়া গিঞ্জের চুড়ো দেখা গেলো, সেদিকে নিয়ে চললেন আমাকে।
গির্জের চুড়োটা এতো উঁচু যে, মনে হয় আকাশের মেঘ এসে ছুঁয়েছে ওর গা। গিঞ্জের গা বেয়ে একটা ঘোরানো সিঁড়ি সেই উঁচু চুড়োকে লক্ষ্য করে আকাশে উঠে গেছে।
কাকামণি যখন বললেন যে এই সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা যাক, তখন সত্যিসত্যিই আমি আঁৎকে উঠলাম। কিন্তু কাকামণি আমার কোন কথায় কান দিলেন না। বললেন, উঁচু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে আমাদের। উঁচুতে ওঠা অভ্যেস করতে হবে তো!
কোনো বারণ না শুনে কাকামণি আমায় নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন। যততক্ষণ পর্যন্ত সিঁড়িটা ভিতর দিয়ে ঘুরে-ঘুরে উপরে উঠেছিলো ততক্ষণ বেশ সহজেই ওঠা গেলো। কিন্তু প্রায় দেড়শোটা সিঁড়ি ভেঙে ওঠবার পর খোলা জায়গায় এসে হাজির হলাম। এখান থেকে গির্জের গা বেয়ে সিঁড়ি গম্বুজের চুড়ো অবধি উঠে গেছে।
কোনোরকমে রেলিং ধরে ধরে আস্তে-আস্তে উঠতে লাগলাম। এলোমেলো হাওয়া এসে ছুলো শরীর। তাতে আরো ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হতে লাগলো যেন হাওয়ায় গির্জেটা কাঁপছে, থর-থর করে দুলছে গির্জের চুড়ো। খানিকক্ষণ উঠেই মাথা ঘুরতে লাগলো। আর দাঁড়াতে পারলাম না, ধপ করে সিঁড়ির উপরে বসে পড়লাম।
তারপরে কী করে যে কাকামণির ধমক শুনতে-শুনতে চুড়োর মাথায় এলাম, তা আমি নিজেই জানি নে। কিন্তু চুড়োয় উঠেও নিস্তার নেই। কাকামণির নির্দেশ শোনা গেলো, এবারে বেশ সাহস করে নিচের দিকে তাকা দিকিন! না, না, ভয় পেলে চলবে কী করে? পাহাড়ের চূড়ো থেকে এমনি করেই পাতাল-ছোঁয়া গহ্বরের দিকে তাকাতে হবে। এখন থেকে তা অভ্যেস করে না। নিলে চলবে কেন?
ভয়ে-ভয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, ঘরবাড়ি সমস্তই যেন ধোয়ার চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। পুতুলের দেশের মতো ছোটো ছোটো ঘরবাড়ি, পিপড়ের মতো সারি-সারি চলমান জনস্রোত। এতো উঁচুতে উঠেছি বলে মনে হতে লাগলো আকাশের মেঘের ভেলাগুলি স্থির নিষ্কম্প, গিঞ্জের চুড়ো-সমেত আমিই বরং বে-বো করে ঘুরছি। দূরে দিগন্তে তমালতালীবনরাজিনীলা, অন্য দিকে ধারানিবদ্ধলবণাম্বুরাশির কলঙ্করেখা। সবই যেন বনৃবন্ করে লাটুর মতো ঘুরছে।
সারা শরীর শিরশির করে উঠলো। ঝিমঝিম করে উঠলো মাথা 1 কাঁপতে লাগলো পা-দুটি। কিন্তু তবু কাকামণির নির্দেশমতো পুরো একটি ঘণ্টা কাটাতে হলো ওখানে। যখন গিঞ্জের চুড়ো থেকে নেমে এলাম, তখন দেখি পা-দুটি ব্যথায় টনটন করছে।
জাহাজ-আপিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেলো, আমাদের জাহাজ ছাড়তে আরো পাঁচদিন বাকি। ভেবেছিলাম এই পাঁচ দিন বেশ জিরোনো যাবে। কিন্তু কাকামণি নাছোড়বান্দা। এই পাঁচ দিনই আমাকে দিয়ে স্টেজ রিহার্সাল দেওয়ালেন। পাঁচ দিনই আমাকে উঠতে হলো গির্জের চুড়োয়। সত্যি বলতে কি, এতে কাজও হয়েছিল প্রথম দিনের চেয়ে পঞ্চম দিনে যে অনেক বেশি সাহস ও জোর পেয়েছিলাম, তা নিঃসন্দেহ।
পাঁচদিন পর ভলকিরিয়া জাহাজে উঠে কাকামণি রীতিমতো একটা কাণ্ড করে ফেললেন; উল্লাসে অধীর হয়ে তিনি এতো জোরে জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করলেন যে ক্যাপ্টেনকে বেশ কয়েকদিন ধরে কজির ব্যথা অনুভব করতে হয়েছিলো। কাকামণির রকম-শকম দেখে ক্যাপ্টেন বেশ একটু আশ্চর্যও হয়েছিলেন। অবশ্য আমি এতে অবাক হইনি। আইসল্যাণ্ড যাওয়ার আনন্দে কাকামণি যে এমনি একটা কিছু করবেন, তা আমি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম।
দশ-এগারো দিনের মধ্যেই আইসল্যাণ্ডের রাজধানী রিজকিয়াভিকে পৌঁছুনো গেলো। জেটি থেকেই আঙুল দিয়ে কাকামণি আমাকে স্নেফেল দেখালেন। বরফে মোড়া পাহাড়টির চুড়ো যেন আকাশের মেঘ ভেদ করে কোন্ মহাশূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো।
আগেকার ব্যবস্থা-মতো রিজকিয়াভিকের বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফ্রিদিকসনের অতিথি হলাম আমরা। ফ্রিদিকসনের বাড়িতে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কাকামণি বেরোলেন লাইব্রেরির সন্ধানে, যদি দৈবাৎ সাকৃত্যুউজমের লেখা কোনো পুঁথি-টুথি পাওয়া যায়, তাই দেখতে। আর আমি বেরোলাম শহরটা ঘুরে বেড়াতে।
শহরটা ছোটো, মাত্র দুটি রাজপথ। ভালো লাগলো না শহরটা। যতদূর চোখ গেলো শুধু আগ্নেয়গিরির মেলা দেখা গেলো। হয়তো সেই কারণেই শহরটা আমার ভালো লাগলো না। কারণ, এখান থেকেই তো আমাদের রওনা হতে হবে পাতালের পথে।
অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। বাসায় এসে দেখি দুই বৈজ্ঞানিকের মধ্যে জোর কথা চলছে। বলা বাহুল্য, কাকামণি যথেষ্ট সতর্ক হয়ে আমাদের আইসল্যাণ্ডে আসার উদ্দেশ্য গোপন রাখতে চেষ্টা করছেন।
কথায় কথায় কাকামণি প্রশ্ন করলেন : আর সাফউমের কোনো বই কি আপনাদের লাইব্রেরিতে আছে?
গর্বের স্বরে ফ্রিদিকসন বললেন : যিনি যে-কোনো ধাতুকেই সোনা করতে পারতেন, ষোলো শতকের সেই অসাধারণ বিজ্ঞানীর কথা বলছেন তো? আইসল্যাণ্ডের গৌরব উনি। এদেশের বিজ্ঞান আর সাহিত্যের সম্রাট। পৃথিবীর সর্বত্রই পুজো ওর।
কাকামণি বললেন : হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি তারই বই দেখতে চাইছি।
ফ্রিদিকসন আফশোস করে বললেন : কিন্তু এখানে তো ওঁর কোনো বই পাবেন না। শুধু এখানে কেন, দুনিয়ার কোথাও পাবেন না। এটা কি কম দুঃখের কথা? ম্লেচ্ছ, ধর্মবিদ্বেষী বলে পনেরো শো তিয়াত্তর সালে ওঁর যে লাঞ্ছনা হয়েছিল, সে কথা ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আইসল্যাণ্ডের, তথা পৃথিবীর দুর্ভাগ্য যে সেই সময়েই ওঁর সব বই কোপেনহেগেনে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিলো।
আপন মনেই কাকামণি বললেন : হুঁ! এখন বুঝতে পারছি কেন উনি হেঁয়ালির মধ্য দিয়ে অতো বড়ো আবিষ্কারটার কথা লিখে গেছেন।
আর বুঝি কিছু গোপন থাকে না! এ-কথা শুনেই ফ্রিদিকসন অবাক গলায় শুধদলেন : হেঁয়ালি! আবিষ্কার!–তার মানে? আপনি কি ওঁর কোনো গুপ্তলিপি পেয়েছেন?
কাকামণি কথা ঘুরোবার চেষ্টায় আমতা আমতা করে বললেন : না, না। আমি পাব কোত্থেকে? ও একটা অনুমান মাত্র!
ও, অনুমান! তাই বলুন।
হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যেন কাকামণি। বললেন, আইসল্যাণ্ডে আসতে আমার বোধকরি দেরি হয়ে গেলো। অনেকেই বোধহয় আগে এখানে এসে সব-কিছু দেখে-শুনে গেছেন।
তাতে কী হলো? বললেন ফ্রিদিকসন : আইসল্যাণ্ড তো ভূতত্ত্বের দেশ। এখনো যে কতো কী দ্রষ্টব্য আছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এখানে যে কত পাহাড়-পর্বত, আগ্নেয়গিরি, হিমশৈল আছে কে তার খোঁজ রাখে? বেশি দূরে যাওয়ারই বা কী দরকার? ঐ যে স্নেফেল পর্বত, ও-রকম আশ্চর্য আগ্নেয়গিরি দ্বিতীয় আর নেই দুনিয়ায়। তবু তো পাঁচশো বছর হলো নিভে গেছে।
তাই নাকি? বিপুল আনন্দ চেপে কোনোরকমে কাকামণি বললেন : আমি তাহলে ঐ স্নেফেলেই যাবে। কিন্তু কী করে যাওয়া যায় বলুন তো?
স্থলপথে যেতে হবে আপনাকে। বললেন ফ্রিদিকসন, পথ অবশ্য খুব সোজা, —সমুদ্রতীর ধরে নাক-বরাবর চলে গেলেই হলো।
কিন্তু এখানকার পথ-ঘাট তো জানিনে। একজন গাইড না হলে চলবে কী করে?
গাইডের জন্যে আর ভাববার কী আছে? একটি লোকের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। ওকে বললে ও ঠিক নিয়ে যাবে। লোকটি খুব চালাক আর বিশ্বাসী।
ফ্রিদিকসনকে ধন্যবাদ জানালেন কাকামণি। তা, লোকটির সঙ্গে এক্ষুনি আলাপ করে নেয়া যাবে তো?
না, আজ আর ওকে পাওয়া যাবে না। কোথায় যেন কী-একটা কাজে গেছে। কাল ভোরে ফিরে আসবে। তখনই আলাপ করে নেবেনখন। বললেন ফ্রিদিকসন।
কাকামণি এইভাবে যে নিজের উদ্দেশ্যের কথা একটুও ফাস না করে সমস্ত ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন, তা আমি আগে কল্পনাও করতে পারিনি।
০৫. আইসল্যাণ্ডের সেই বৈজ্ঞানিক
তাড়াতাড়ি সামান্য কিছু গলাধঃকরণ করে সমুদ্র থেকে পাঁচ হাজার ফুট উপরে স্নেফেলের চুড়োয় পাথরের উপরে গা এলিয়ে দিলাম আমরা। সঙ্গে-সঙ্গেই চোখের পাতায় নেমে এলো একঝাঁক ঘুম। এমন গাঢ় ঘুম আমার অনেকদিন হয়নি। জেগে উঠে দেখি বেলা প্রায় দুপুর।
দিগন্তের অন্যান্য পাহাড়ের চুড়গুলিকে ছোটো-ছোটো প্রাচীরের মতো দেখালো। নদীগুলো যেন সরু সুতো। দক্ষিণ দিকের বরফ-ছাওয়া ভূমির উপরে রোদের রঙ ঝলমল করছে। পশ্চিম দিকে সমুদ্রের গাঢ় নীল রঙ। সবকিছুই দেখতে অপূর্ব লাগছিলো।
এমন সময়ে কাকামণি আর হান্স্ আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। ওরা দুজনে সেই লোকদুটিকে বিদায় দিতে গিয়েছিলো। কাকামণি এসে পশ্চিম দিকে কুয়াশার মতো কী যেন একটা আঙুল দিয়ে দেখালেন। বললেন : ঐ দ্যাখ, গ্রীনল্যাণ্ড!।
অবাক হয়ে বললাম : গ্রীনল্যাণ্ড!
গ্রীনল্যাণ্ড তো এখান থেকে খুব বেশি দূর নয়। শখানেক মাইল দূরে মাত্র। যাক সেকথা।…আমরা এখন স্নেফেলের উপরে। দুটি চুড়োও দেখতে পাচ্ছি। একটা তো এইটে—যেটার উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি, অন্যটা ঐ যে। কোনটার কী নাম, সেটা এখন জানা দরকার। হাসের দিকে তাকালেন কাকামণি : আচ্ছা হ্যাঁ, আমরা যে চুড়োটার উপর দাঁড়িয়ে আছি, এটার নাম কী?
হাস্ উত্তর করলে : স্কার্টারিস।
আনন্দে কাকামণি অধীর হয়ে উঠলেন। তবে আর দেরি কিসের? এক্ষুনিই তোত নামা যেতে পারে?
আমার বুক একবার ভয়ে কেঁপে উঠলো। কিন্তু এখন আর ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। হাসকে কিন্তু একটুও বিচলিত দেখালো না। সে সহজভাবেই আমাদের ক্রেটারের দিকে নিয়ে চললো। আমি মুখ অন্ধকার করে চুপচাপ ওদের পিছন পিছন চললাম।
স্নেফেলের প্রধান ক্রেটারের মুখটা মাইলখানেক চওড়া। গভীরতা কম করেও দুহাজার ফুটের বেশি। পাগল না হলে মানুষ কখনো এমন সাংঘাতিক চিমনির মধ্যে নামবার কল্পনা করতে পারে? মুখের কাছ থেকে একটা রাস্তা অনেকদূর পর্যন্ত নিচে নেমে গেছে। হাসকে অনুসরণ করে সেই রাস্তা ধরে আমাদের অবতরণ শুরু হলো। ঠিক দুপুরবেলায় আমরা একটা চাতালের মতো প্রশস্ত জায়গায় এসে হাজির হলাম। সেখান থেকে দেখা গেলো, আগ্নেয়গিরির তিনটি জ্বালামুখ সর্বনাশের আভাস নিয়ে অন্ধকার মুখকে বিস্ফারিত করে আছে। এক-একটি মুখের পরিধি প্রায় একশো ফুট করে। স্নেফেল যেন আমাদের গ্রাস করবার জন্যেই এই গহ্বর তিনটে তৈরি করেছে। আমার এতো ভয় করলো, যে গহ্বরগুলোর কাছে গিয়ে নিচের দিকে তাকাতে পর্যন্ত সাহস হলো না।
কাকামণি তখন পাগলের মতো ছুটে-ছুটে মুখগুলো দেখছেন, আর আপনমনে কত-কী বকে চলেছেন। তার রকম-সকম দেখে এই প্রথম হাসকে পর্যন্ত একটু অবাক দেখালো, সে আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো তার কাণ্ড।
হঠাৎ কাকামণি তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন। সেই তীব্র কণ্ঠস্বরে চারপাশ গমগম করে উঠলো। আমি তো হঠাৎ এমন চাচানো শুনে মনে করলাম, কাকামণি বুঝি-বা সেই তলহীন গহ্বরের মধ্যেই পড়ে গেছেন! তাকিয়ে দেখি, বড়ো একটা পাথরের সামনে গোল-গোল চোখে দাঁড়িয়ে আছেন উনি।
কাকামণির চোখে-মুখে এমন বিস্ময় দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলুম। তাড়াতাড়ি পাশে এসে দাঁড়াতেই কাকামণি আঙুল দিয়ে দেখালেন, সেই পাথরটার উপর কতকগুলি রুনিক হরফ খোদাই করা। কোনো-কোনো জায়গায় ক্ষয়ে গেলেও কোনোমতে পড়া গেলো। পাথরটার গায়ে লেখা : আর্ন্ সাক্ন্যুউজম্।
০৬. আর্ন্ সাক্ন্যুউজম্
আর্ন্ সাক্ন্যুউজম্! বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। রইলাম আমি।
এবারে আর কাকামণির সিদ্ধান্তকে অহেতুক বলে উড়িয়ে দেয়া চলবে না। তার এতো কাণ্ড, এতো আয়োজন, এতো সমারোহকে নিছক পাগলামি বলে আর উড়িয়ে দেবার জো নেই। অসমসাহসী আবু সান্যউজম-আইসল্যাণ্ডের সেই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-এখানকারই কোনো একটি গহ্বর দিয়েই যে পাতালে নেমেছিলেন, এই লেখা তারই প্রমাণ বহন করছে।
কাকামণি হেসে বললেন : কী রে? আরো প্রমাণ চাই নাকি তোর?
না, এমন অব্যর্থ ও অকাট্য প্রমাণের পরে আর কোনো কথাই বলা চলে। অসহায়ভাবে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।
আস্তে-আস্তে সন্ধে হয়ে এল। এই গহ্বর তিনটের পাশে, এই চত্বরের মধ্যেই রাত্রিবাস করতে হবে আমাদের। সারাদিনের পরিশ্রমে সারা শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। পা-দুটি ব্যথায় টনটন করছিলো। এইটুকু পথ নামতে তো আর কম কষ্ট করতে হয়নি!
হান্স্ খুঁজে-পেতে একটু সমতল জায়গা বের করে বিছানা পাতার বন্দোবস্ত করলে। জায়গাটা কঠিন লাভার প্রলেপ-মোড়া। লাভার সেই পুরু প্রলেপের উপর গরম চাদর পেতে আমি আর হান্স্ শুয়ে পড়লাম। কাকামণি কিন্তু আলো জ্বেলে চারদিক পরীক্ষা করতে লাগলেন, কখনো বা ইতস্তত ছুটোছুটি করতে লাগলেন আশে-পাশে। তারপর এক সময়ে আমাদের ঘুমিয়ে নিতে বলে আলো নিয়ে চারদিক টহল দিয়ে আসতে গেলেন।
একটু পরে হান্সের দিকে তাকিয়ে দেখি, নির্বিকারভাবে সে ঘুমিয়ে রয়েছে। আমার কিন্তু ঘুম আসছিলো না। শ্রান্তিতে শরীর এলিয়ে পড়ে রইলাম শুধু। আর দুর্ভাবনায় ভরে উঠলো মন।
কাকামণি কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, কে জানে? এখনো আলো নিয়ে ফিরে আসছেন না কেন? হা তো অঘোরে ঘুমোচ্ছ। আমি চোখ মেলে পড়ে আছি। হঠাৎ কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো। মনে হলো, অন্ধকারের মধ্যে যেন অসংখ্য অশরীরী আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেইসব আত্মার উৎপত্তি যেন পাতালের অন্ধকারে।
এমনি গাঢ় ভয়ের মধ্যে কখন যে ঘুমে দুচোখ জুড়িয়ে এসেছিলো জানিনে। ঘুম ভাঙলো একেবারে সকাল বেলায়। ঘুম ভাঙতেই দেখি কাকামণি মুখোনা অন্ধকার করে বসে আছেন। প্রথমটা তার রাগের কারণ বুঝতে পারলাম না, পরে অবশ্য বোঝা গেলো।
আকাশ মেঘলা হয়ে আছে বলেই কাকামণির এই অসহায় ভাব। সঙ্কেতলিপিতে ছিল, জুলাই মাসের গোড়ার দিকে স্কার্টারিসের ছায়া যে-জ্বালামুখের ওপরে পড়বে, সেই পথ দিয়েই নামতে হবে পাতালে। কিন্তু আকাশ মেঘলা বলে স্কার্টারিসের কোনো ছায়াই পড়লো না। আর কাকামণির রাগের কারণ হল তাই। যদি জুলাই মাসের গোড়ার দিকে সূর্যের সাক্ষাৎ না মেলে তবে আরো এক বছরের জন্য যাত্রা বন্ধ থাকবে।
সে কী রাগ কাকামণির! সুর্যকে কতোবার যে ধমক দিলেন, অভিশাপ দিলেন, তার কোনো ইত্তাই নেই। সারা দিনে একবারও সূর্যের দেখা পাওয়া গেল না। এক হিসেবে অবশ ভালোই হলো। একটানা পরিশ্রমের পর এই ছুটিটা বেশ উপভোগ করা গেলো আয়েশ করে শুয়ে-শুয়ে।
পর-পর তিন দিন আকাশ এত মেঘলা হয়ে রইলো যে, বোদের নামগও দেখা গেলো না। কাকামণির রাগের পরিমাণও ক্রমে বেড়েই চললো। কিন্তু চৌঠা জুলাই সানন্দে কাকামণি সুপ্রভাতকে স্বাগত জানালেন। সূর্যের সোনালি রোদে সকালবেলাতেই চারিদিক ঝলমল করে উঠলো। আস্তে-আস্তে দুপুর হলো। সঙ্গে সঙ্গে রোদের রঙও উজ্জ্বল হতে লাগলো আররা। তারপর এক সময়ে স্কার্টারিসের ছায়া ক্রমশ সরে এসে পড়লো একটি জ্বালামুখের উপর।
সঙ্গে সঙ্গে আনলে কাকামণি সেই বুড়ো বয়সেই দস্তুরমতো নৃত্য শুরু করে দিলেন। চাচামেচি করে আমাদের প্রস্তুত হতে বললেন। পৃথিবীর অন্দরমহলে রওনা হতে হবে এবার। সে কি খুব সহজ কথা?
হাস্ যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলো। উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়ালো সে বলল : চলুন।
তখন বেলা একটা বেজেছে। পাথরের খাঁজকাটা সিঁড়ি দিয়ে পাতালের দিকে আমাদের অবতরণ শুরু হলো।
০৭. পথের পাঁচালী
পাথরের খাঁজ-কাটা সিঁড়ি দিয়ে পাতালের দিকে নামতে লাগলাম আমরা। কেটারের পরিধি ক্রমশ বেড়ে গিয়েছে। শতিনেক ফুট হবে হয়তো খানিক নিচে। আর সেই নিচে আছে পাতাল-ছায়া অন্ধকার। গহরের যতটুকু দেখা গেল তাতেই মনে হলো, এর পাঁচিল সোজাসুজি নিচে নেমে গেছে। হয়তো অতি মণ রেখায়। অবশ্য পাঁচিলের গায়ে মাঝে-মাঝে এমনভাবে খাজের মত পাথর বেরিয়ে ছিলো যে তাতে আমাদের সিঁড়ির কাজ হয়ে গেলো। উপরে যদি কোথাও বড়ো একটা দড়ি বাধা যেত, তবে সহজেই সেই দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামা যেত। কিন্তু তার জন্যে বড়ো বড়ো দড়ির দরকার, ততো বড়ো দড়ি কি আছে আমাদের?
কাকামণি বললেন : এর জন্যে এতো ভাবনা তোর?
চারশো ফুট লম্বা একটা দড়ি নিয়ে তার ঠিক মাঝখানটা পাঁচিলের গায়ের একটা পাথরের সঙ্গে দু-তিন পাক জড়িয়ে দিলেন উনি। বুঝতে পারলাম যে, দুহাতে দড়ির দুই প্রান্ত ধরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে হবে। দুশো ফুট নেমে দড়ির এক প্রান্ত ধরে টানলেই দড়ি উপর থেকে খুলে আসবে। তখন ঐভাবেই দড়ির সাহায্যে সহজেই আরো নিচে নামা যাবে।
এই বন্দোবস্তই ভালো হলো, কী বলিস? বললেন কাকামণি। কিন্তু, সমস্যা হলো, মালপত্রের ব্যবস্থা কী করা যায়। যতটুকু সম্ভব আমাদের সঙ্গে করে নিতে হবে। বিশেষ করে যেসব জিনিশ একটুতেই ভেঙে যেতে পারে। হাস, তুমি নাও কিছু যন্ত্রপাতি আর খাবার-দাবার। অ্যাজেল, তোর কাছে গুলি-বারুদ আর কিছু খাবার থাক। বাকি খাবার আর যন্ত্রপাতিগুলো আমিই নিচ্ছি।
বললাম : তা না-হয় নেয়া গেলো, কিন্তু বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড় আর অন্য সব জিনিশের কী হবে?
কাকামণি জানালেন : সেজন্যে ঘাবড়াতে হবে না তোকে। তারা আপনি আমাদের সঙ্গে যাবে। এই বলে বাকি জিনিশপত্র একসঙ্গে খুব ভালো করে বেঁধে কাকামণি গহ্বরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেললেন। শো করে বাণ্ডিলটা নেমে গেলো। যতক্ষণ দেখা গেলো, কাকামণি সেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর নির্বিকার গলায় বললেন : চল, এবার নামা যাক।
আর দ্বিরুক্তি না করে মরিয়া হয়ে পাতালের দিকে নেমে চললাম। সবচেয়ে আগে হা. তারপর কাকামণি এবং সবশেষে আমি। একের পর এক তিনজনে দড়ি ধরেধরে নামতে লাগলাম। আলগা পারগুলি পায়ের আঘাতে ঝুরঝুর করে নিচে পড়তে লাগলো।
আধ ঘণ্টা নামবার পর দড়ির শেষ প্রান্তে পৌঁছে একটু প্রশস্ত চত্বরের মতো দেখা গেলো। সেখানেই থামলাম আমরা। টান দিয়ে উপর থেকে দড়িটা খুলে নিলেন কাকামণি। আবার দড়ি বাধা হলো তিন-চার পাক দিয়ে। আবার নিচের দিকে নেমে চললাম।
আমি তখন নিজেকে সামলাতে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে শিলাস্তরের বিন্যাসের দিকে নজর দেবার মতো অবসর ছিলো না। এমন পাগল ভূতত্ত্ববিদ কে আছে যে এই অবস্থায়ও চারদিককার শিলাস্তরের নানান লক্ষণ খেয়াল করতেকরতে নামতে পারে? কাকামণি কিন্তু শিলাস্তরের বিন্যাস করতে করতেই নামতে লাগলেন। তাঁর রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন কোনো মিউজিয়ামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।
হঠাৎ একবার কাকামণি আমায় বললেন : যতোই নামছি নিচের দিকে, ততোই নিঃসন্দেহ হচ্ছি। এই অগ্নিগিরির শিলান্তরের বিখ্যাস দেখে মনে হচ্ছে যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে খুব বেশি উত্তাপ নেই। দেখছিস নে, এখন আমরা যে শিলান্তরের মধ্য দিয়ে চলেছি, তা-ই হলো পাথরের আদিম অবস্থা। ধাতব পদার্থের গায়ে জল হাওয়া লেগে তখন যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেছিলো, এখনো তার চিহ্ন পাথরের গায়ে বর্তমান। তুই ভালো করে নজর রাখলেই বুঝতে পারবি সব।
আমি কোনো কথা বললাম না। দড়ি ধরে কোনোমতে টাল সামলিয়ে নামতে লাগলাম শুধু। ইতিমধ্যে গহর ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছিলো, গাঢ় হচ্ছিল অন্ধকার! আলগা পাথরের টুকরোগুলি ক্রমশ আরো জোরে নিচে পড়তে লাগলো, আর তাদের নিচে পড়ার শব্দ ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠতে লাগলো।
প্রায় দুহাজার আটশো ফুট নামবার পর কাকামণি যখন জানালেন যে আমাদের পথ আপাতত এখানেই শেষ হয়ে গেছে, তখন রাত দুপুর হয়ে গেছে। নিচে যাওয়ার নতুন পথ আবিষ্কার করা এই রাত্তিরে মোটেই সহজ ব্যাপার নয় বলে আমরা রাত কাটাবার উদ্যোগে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সহজেই একটি প্রশস্ত সমতল ভূমি পাওয়া গেলো। আমাদের শোওয়া বসার কোনো অসুবিধে হলো না। কিছু খেয়ে নিয়ে কোনো রকমে শুয়ে পড়লাম আমরা।
চারদিক নিস্তব্ধ। সুচীতে অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে আকাশ-পাতাল কতো-কি যে ভাবতে লাগলাম, তার ইয়ত্তা নেই। ঘুম যখন ভাঙলো, তখন বেলা আটটা। মৃদু সূর্যরশ্মির সরু একটি রেখা এসে পড়ছিলো আমাদের পাশে।
আমার ঘুম ভেঙেছে দেখে কাকামণি হেসে বললেন : কী রে, কেমন লাগছে তোর? কাল রাত্তিরের মতো এমন শান্তিতে ঘুমিয়েছি আর কখনন? গাড়ি বোড়ার গোলমাল নেই, লোকনের সোরগোল নেই–কী রকম নিস্তব্ধ চারদিক দেখছিস?
এতে নিস্তব্ধ বলেই তো ভয় করছে বেশি।
কাকামণি হেসে উঠলেন : এখনই ভয় করছে তোর? এরই মধ্যে? এখনো তো প্রচুর পথ বাকি! সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা তো এখনো পৃথিবীর অন্তঃপুরে প্রবেশই করিনি—ঠিক সমুদ্রের সমতলে আছি।
অবাক হয়ে বললাম : সে কী করে হয়?
আবার কাকামণির হাসির শব্দ শোনা গেলো : এই ব্যারোমিটার দ্যাখ,–ভূপৃষ্ঠের মতো এখানেও চাপ সমান। যখন ব্যারোমিটারে বাতাসের চাপ মাপা যাবে না, ম্যানোমিটারে মাপতে হবে, তখনই বোঝা যাবে যে আমরা সত্যি-সত্যি পৃথিবীর অন্দরমহলে প্রবেশ করেছি।
হঠাৎ একটা গুরুতর প্রশ্ন জেগে উঠলে মনে : কিন্তু কাকামণি, পৃথিবীতে যে-পরিমাণ বাতাসের চাপ সহ্য করা আমাদের অভ্যেস, এখানে তার চেয়ে বেশি চাপ হলে সহ করা যাবে না তো।
নিশ্চিন্ত গলায় কাকামণি বললেন : আমরা তো খুব আস্তে-আন্তে নামছি। যন হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে-নিতে ক্রমশ আমাদের অভ্যেস হয়ে যাবে। আমরা তো জানি, বেলুনে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের উপরে বাতাসের চাপ কতো কম। কিন্তু তা তত তারা সহ করে থাকে।
তার মানে, তুমি বলতে চাইছে আস্তে-আস্তে অভ্যেস হয়ে যাবে?
হ্যাঁ। বললেন কাকামণি। আর অভ্যেস হলেই সহ হয়ে যাবে। কাল যে বাণ্ডিলটা ফেলে দিয়েছিলুম, এবারে তার খোঁজ নেয়া যাক।
খানিকক্ষণের মধ্যেই হান্স্ বাণ্ডিলটা খুঁজে বার করলে। আহার সেরে নিয়ে হান্স্ আর কাকামণি তাদের টর্চ জ্বালিয়ে নিলেন। তারপর সেই আলোয় পথ দেখে পাতালের অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চললাম সবাই।
বারোশো ঊনত্রিশ খ্রীস্টাব্দে মেফেলের শেষ অগ্নদগীরণ ঘটেছিল। এখনো তার চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেলো। সেই আগ্নেয় উদগার জমাট বেঁধে কঠিন হয়ে গিয়েছিল। টর্চের আলোয় তা অজ্বল করতে লাগলো। পথ এতো গড়াননা যে, আমাদের খুব সাবধানে এগোতে হচ্ছিল। মাথার উপরে অসংখ্য কাৰ্তজোপলের স্বচ্ছ ফানুশ ঝড়ের মতো ঝুলছিলো, তাদের গায়ে যেন পরিচ্ছন্ন কাচ বসাননা। টর্চের আলোয় ফানুশগুলো ঝলমল করতে লাগলো। ভারি সুন্দর লাগলো দেখতে। লাল, নীল, সবুজ-নানান রঙের সব ফানুশ। তাদের উপর আলো পড়ে তৈরি হয়েছে পাতালের রামধনু।
অনেক দূর পর্যন্ত এগোলাম সেদিন। উত্তাপ কিন্তু সেই অনুপাতে বেড়েছে বলে মনে হলো না।
রাত্রে খেতে বসে আবিষ্কার করলাম, জল কমে এসেছে। আগেও জলের কথা কাকামণিকে অনেকবার জানিয়েছি। কিন্তু ওঁর মুখে সেই এক কথা : ঝরনার জল পাওয়া যাবে পথে। কাজেই ভয় কিসের? কিন্তু এখন যখন দেখতে পেলাম অর্ধেকেরও বেশি জল ফুরিয়ে গেছে, তখন আবার জানালাম ওঁকে। শুনে কাকামণি বললেন : এতো ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? ঝরনার জল পাওয়া যাবে পথে। যখনই এই অগ্ন্যুদ্গারের দেয়াল ভেদ করবো, ঠিক তখুনি জলের দেখা মিলবে।
এ দেয়াল কতদুর গেছে, তা কী করে বুঝতে পারবে? আমরা যে নিচের দিকে খুব বেশি নামতে পেরেছি, তা কিন্তু মনে হচ্ছে না আমার। সমতল ক্ষেত্র দিয়েই বোধহয় চলেছি আমরা। কারণ যতো নিচে নামবে তততই তো উত্তাপ বাড়বার কথা। কিন্তু তাপ একটুও বাড়েনি। খুব বেশি হলে আমরা এগারোবারোশো ফুট নামতে পেরেছি।
হো-হো করে হেসে উঠলেন কাকামণি। তার ধারণা ভুল। এখন আমরা সমুদ্র-তলের চেয়েও দশ হাজার ফুট নিচে।
দুচোথ বিস্ফারিত করে বললাম : আঁ? বলো কী কাকামণি?
কাকামণি অঙ্ক কষে তার সিদ্ধান্তের প্রমাণ দিলেন।
পরদিন ভোরবেলাতেই আবার আমাদের চলা শুরু হলো। দুপুর বেলায় আমরা দুটি সুড়ঙ্গ পথের মোহানার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। দুটি পথই সঙ্কীর্ণ, অন্ধকার এবং অপ্রশস্ত। সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গের সামনে দাঁড়িয়ে যদি অনন্তকাল ভাবতাম কোন পথ দিয়ে যাবে, তাহলেও পথের সন্ধান পাওয়া যেতো না। কাকামণি কিন্তু চট করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। বললেন : পূর্বদিকের সুড়ঙ্গ দিয়েই যাওয়া যাক, কী বলিস?
এগোতে-এগোতে দেখতে পেলাম ঐ সুড়ঙ্গের অবসর্প বেশ কম, আর সামনের দিকে তোরণের পর তোরণ যেন আমাদেরই জন্য উন্মুক্ত হয়ে আছে। মাইলখানেক যেতে-না-যেতেই তোরণগুলি ক্রমশ ছোটো হয়ে আসতে লাগলো। সেই কারণে কোথাও আমাদের মাথা নুইয়ে চলতে হলো, কোথাও বা এগোতে হলো বুকে হেঁটে অতি সন্তর্পণে।
উত্তাপ এখনো সহনীয়। তবে, এক-একবার যখন মনে হচ্ছিল যে এই পথ দিয়ে একদা প্রচণ্ড আবেগে তরল আগুনের স্রোত বয়ে গিয়েছিলো, তখুনি ভয়ে শিউরে উঠছিলো শরীর। এমনও তো হতে পারে যে এখন কোথাও আবার শুরু হয়েছে দ্রবীভূত আগুনের অসহ্য তাণ্ডব! আর তার মানেই হলো নিশ্চিত মৃত্যু।
কাকামণি কিন্তু নির্বিকারভাবে এতো কষ্ট সহ্য করেও এগিয়ে চললেন। হাসেরও ঠিক তেমনি বিরামহীন গতি। শুধু আমারই ভারি কষ্ট হচ্ছিল এগোতে।
সন্ধের সময় যখন আমরা জিরোবার জন্যে থামলাম, তখন হিশেব করে দেখা গেলো যে আমরা মোটে ছমাইল পথ অতিক্রম করেছি সারাদিনে, আর নিচের দিকে নেমেছি মাত্র আধমাইল।
পরদিন ভোরবেলায় আবার যাত্রা শুরু হলো। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা গেলো সুড়ঙ্গ-পথ নিচের দিকে না গিয়ে সমতল ক্ষেত্রেই চলেছে। আমার তো মনে হলো আমরা ক্রমশ উপরের দিকে উঠছি। চলতে তখন ভারি ক্লান্তি লাগছিলো। আস্তে-আস্তে চলছি দেখে কাকামণি অধৈর্য গলায় আমাকে তাড়াতাড়ি হাঁটতে বললেন।
অবসন্ন গলায় বললাম : আর যে পারছি নে কাকামণি!
পারছিস নে! অবাক হলেন যেন কাকামণি। এমন সুন্দর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে তোর কষ্ট হচ্ছে। মোটে তোত তিন ঘণ্টা হলো রওনা হয়েছি।
আমার পা যে ভেঙে আসছে, কাকামণি! উপরে ওঠা তো সহজ ব্যাপার নয়।
কী সর্বনাশ! তুই পাগল হয়ে গেলি নাকি? কোনটা উঁচু, কোনটা নিচু তাও জানিস নে? চল, চল! কাকামণি তর্জনীসঙ্কেতে সামনের পথ দেখিয়ে দিলেন। আর কোনো দ্বিরুক্তি না করে মরিয়া হয়ে এগোতে লাগলাম।
দুপুরবেলায় দেখি শহরের প্রাচীর অন্যরকম রূপ নিয়েছে। আমাদের হাতের আলোয় আর তেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে না। লক্ষ্য করে দেখি, এবার আর অগ্ন্যুদগারে গঠিত নয়, পাষাণময়। খানিকক্ষণ বাদেই দেখি, চারিদিক চূর্ণোপলে আর প্লেট-পাথরে ছাওয়া। গ্রন্থি-প্রান্তরের প্রাচীর পেছনে পড়ে রয়েছে।
আমাকে বিস্ময়ে অর্ধস্ফূট চিৎকার করতে দেখে কাকামণি শুধোলেন : ব্যাপার কী?
বললাম : দ্যাখো কাকামণি, আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি। যে-যুগে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিলো, প্রথম উদ্ভিদ দেখা দিয়েছিলো, আমরা এখন সৃষ্টির সেই পরিবেশে এসে উপস্থিত হয়েছি। প্রাচীরের গায়ে আলো ফেলে দেবালাম ওঁকে। কাকামণি কিন্তু একটুও অবাক হলেন না। নীরবে এগিয়ে চললেন।
তবে কি আমারই ভুল হলো? হয়তো। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হরে থাকে, তবে প্রাচীন যুগের উদ্ভিদ-জগতের কিছু-না-কিছু চিহ্ন নিশ্চয় পাওয়া যাবে। আমি তারই অপেক্ষায় রইলাম।
অল্পক্ষণের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম, আমরা বালির উপর দিয়ে চলেছি। এখানে নদী নেই, সমুদ্রও নেই,–তবে বালি এলো কোত্থেকে? এ তাহলে উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া অন্য কিছু না। আর একটু পরেই প্রাচীরের গায়েও উদ্ভিদ জগতের অভ্রান্ত চিহ্ন দেখা গেলো।
কাকামণি কিন্তু তবুও এগিয়ে চললেন। দেখে আর সত্যু হলো না। একটা ঝিনুক কুড়িয়ে কাকামণির হাতে দিয়ে বললাম : এই দ্যাখো কাকামণি, ট্রিলোবাইট জাতের ঝিনুক। এ দেখেও কি মনে হয় না–
–যে আমরা পথ হারিয়েছি? অকম্পিত স্বরে আমার কথাটা শেষ করলেন কাকামণি, তারপর বললেন : পথ তো অনেকক্ষণ হলো হারিয়েছি। গ্রন্থিপ্রকার আর অগ্ন্যুদ্গারের প্রাচীর ছাড়িয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝতে পেরেছি, আমরা ঠিক পথে আসছি নে। কিন্তু এই পথটাও যে পাতালে যায়নি, তারই বা প্রমাণ কী? এর শেষ না দেখে কি ফিরতে পারি?
অবাক গলায় বললাম : তুমি তবে পথের শেষ না দেখে ফিরবে না? ওদিকে যে আমাদের জল ফুরিয়ে এলো!
তাতে কী হয়েছে? নির্বিকার স্বরে কাকামণি বললেন : অল্প-অল্প করে খেতে হবে আর-কি!
০৮. পথের শেষ কোথায়, পথের শেষ?
কাকামণির কথায় প্রতিবাদ করবার মতো অবস্থা তখন আমার না,–না দেহের, না মনের। শুধু একবার কতটুকু জল এখনো হাতে আছে দেখে নিলাম। তখন তিনদিনের উপযোগী জল ছিলো। কিন্তু কদিন যে লাগবে এই পথের শেষ দেখতে, তা কে জানে? সে-কথা আর ভাববার চেষ্টাও করলাম না। ভেবে কোনোই লাভ নেই। কাকামণি তো আর আমার কথা শুনবেন না। কাজেই শ্রান্ত পায়ে এগিয়ে চলতে লাগলাম শুধু।
এবার দেখতে পেলাম, মারবেল পাথরের রাজ্যে এসে পৌঁছেছি। শাদা, লাল, নীল, হলুদ নানান বর্ণের পাথর। কোনো-কোনো জায়গায় আবার দেখলাম, নানান জাতের মাছ ও সরীসৃপের কঙ্কাল ইতস্তত ছড়ানো। বুঝতে পারলাম, আমরা ক্রমশ সৃষ্টির আদি যুগের দিকে চলেছি। তবে কি আমরা একেবারে পৃথিবীর অন্দরমহলের কাছাকাছি এসে পৌঁছলাম?
ক্রমশ আবার সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গে এসে নামলে আর-একটি রাত্রি। লণ্ঠনের অল্প আলোয় কোনোরকমে আমরা আহার সেরে নিলাম। জল ফুরিয়ে যাবে এই ভয়ে বেশি জল খাওয়ার সাহস পর্যন্ত হলো না। তারপর অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়েই আশ্রয় নিলাম প্রস্তর-শয্যায়।
পরদিন একটানা দশ ঘণ্টা চলবার পর দেখলাম, প্রাচীরের গায়ে টর্চের আলো আর তেমন যেন ফুটতে চাইছে না। পরীক্ষা করে দেখতে পেলাম, মারবেল পাথর, চুন পাথর, শ্বেত পাথর নেই, স্নেট পাথরের স্তরও অন্তর্হিত। সামনে আছে শুধু ঘন কালো রঙের আস্তরণ-ঢাকা সুড়ঙ্গ-প্রাচীর। প্রাচীরের গা থেকে হাত সরিয়ে নিতেই চোখে পড়লো, হাত কালো হয়ে গেছে।
বিস্ময়ে অস্ফুট কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলাম : কয়লার খনি! কয়লার খনি!
কাকামণি হেসে বললেন : এই কয়লার খনিতে এর আগে মানুষের আবির্ভাব ঘটেনি। আমরাই এই দেশের প্রথম আগন্তুক। তারপর হাসের দিকে ফিরে তাকালেন উনি। বললেন : আজ এখানেই থামা যাক, হান্স্। অনেকক্ষণ এগোেনো গেছে। একদিনের পক্ষে এই যথেষ্ট।
রাত্রির আহার সেরে নিতে বসলাম সবাই মিলে। খেতে আমার কোনোই আগ্রহ ছিলো না। আমার ভাগে যে অল্প-একটু জল পড়লে প্রাণভরে তাই শুধু পান করলাম।
খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই সবাই শুয়ে পড়লাম। কাকামণি আর হান্স্ সহজেই ঘুমিয়ে পড়লো, কিন্তু আমার চোখে ঘুম নামলো না। জলের চিন্তায় আমার ঘুম আসতে চাইলো না। অনেকক্ষণ জেগে থাকবার পর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, টের পাইনি। সকালবেলায় যখন কাকামণি আর হান্স্ যাত্রার অঙ্গে প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন আমার ঘুম ভাঙলো। প্রাতরাশ সেরে নিয়ে আবার নিয়মিতভাবে চলা শুরু হলো।
কিছুদূর এগোনোর পর সামনে একটা বিপুল আকারের গহবর পড়লো। অন্ধকার হাঁ মেলে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই অন্ধকারে রয়েছে সর্বনাশের সম্ভাবনা। প্রকৃতি ছাড়া এমনতরো দ্বিতীয় একটি গহ্বর সৃষ্টি করবার ক্ষমতা আর কারো নেই। গহ্বরটার পাশ কাটিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম।
সেদিনও সারা দিন হেঁটে পথের শেষ দেখা গেলো না। আমাদের যেমন চলার বিরতি নেই, তেমনি সুড়ঙ্গটারও কোনো শেষ হবার লক্ষণ নেই। যতই এগোই না কেন, সুড়ঙ্গ যেন আর ফুরোবে না। কাকামণি পর্যন্ত আস্তে-আস্তে অধৈর্য হয়ে উঠতে লাগলেন।
রাত না দিন বোঝবার জো নেই এমনিতে। শুধু আকারহীন ঘন অন্ধকার। আমাদের হাতের আলো যেন সেই অন্ধকারকে আরো বাড়িয়ে তুলছিলো। ঘড়ি দেখেই নিয়ম-মতো সময়ে আমরা জিরোই, আহার করি, ঘুমোই, তারপর আবার চলতে থাকি।
অবশেষে ঘড়িতে একসময়ে সন্ধে ছটা বাজলো। আর ঠিক সেই সময়েই দেখতে পেলাম, আমাদের সামনে একটা নিরেট প্রাচীর মাথা তুলে পড়িয়ে আছে। এই পথের তাহলে এখানেই শেষ।
কাকামণি কিন্তু নির্বিকার। শুধু বললেন : ভালো। এতক্ষণে তবু একটা পথের শেষ দেখা গেলো। সাউজ তবে এই পথে আসেননি। এবার তাহলে ফেরার উদ্যোগ করা যাক। আফশোষ করে আর লাভ কী খামোকা? আমরা পথ ভুল করেছিলুম-এবার ফিরে গিয়ে আসল পথ ধরে এগোবে।
এই হতাশার মধ্যেও কেন জানি না হাসি পেলে আমার। ম্লান স্বরে বললাম : ফিরবে তত নিশ্চয়ই, কিন্তু শক্তি কই?
নেই মানে? এতোটা পথ আসতে পারলাম, আর কেরবার বেলা পারবো না?
আশঙ্কাটা প্রকাশ করে বললাম : কিন্তু কাকামণি, কালকেই যে সব অল ফুরিয়ে যাবে!
নিকুচি করেছে তোর জলের! অধৈর্য হয়ে উঠলেন কাকামণি। অল ফুরিয়ে যাবে বলে কি আমাদের ধৈর্য, সাহস, সঙ্কল্প সবকিছুই ফুরিয়ে যাবে নাকি?
এই কথার জবাব দেবার সাধ্য আমার ছিলো না। আমি শুধু ভাবতে লাগলাম, এতটা পথ আসতে লেগেছে পাঁচ দিন, ফিরে যেতেও তো আবার সেই পাঁচ দিনের ধাক্কা। ততোদিন কি জল না খেয়ে বাঁচবো?
কিন্তু এখানে হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকলেও তো বাচবার সম্ভাবনা নেই। গেলেও মৃত্যু, থাকলেও তথৈবচ। সুতরাং বৃথা দেরি না করে তখুনি প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করলাম আমরা।
০৯. অন্য পথ
সে যে কী কষ্ট, কী অসহ্য যন্ত্রণা, তা লিখে বোঝাতে পারি এমন ভাষা নেই আমার। কাকামণির কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতার কোনো তুলনা নেই। সঁতে দাঁত চেপে এগোতে লাগলেন তিনি। আর হাস? হাসের যে কোনো কষ্ট হচ্ছে এমন কোনো লক্ষণই চোখে পড়লো না। নীরবে চলতে লাগলো সে। শুধু পারলাম না আমি।
প্রথম দিনেই অল গেলো ফুরিয়ে। তখন জলের বদলে জিন পান করলাম আমরা। সেই তরল আগুনে পুড়ে যেতে চাইলে কণ্ঠনালী। বুক জুড়ে আকণ্ঠ পিপাসা, কিন্তু তবু ঐ জিনের বোতলের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করলো না আমার। বরং ক্রমেই আমার মনে হতে লাগলো চারদিকে যেন অসহ্য উত্তাপ, যেন আগুনের চুল্লির ভিতর দিয়ে চলেছি আমরা, মরুভূমিও বোধহয় এর চেয়ে ভীষণ নয়।
সত্যিসত্যিই শেষটায় আর পারলাম না। এক পাও চলবার মতো ক্ষমতা রইলো না আমার। কততবার যে চেতনা হারালাম তার কোনো হিশেব নেই। কাকামণি আর হান্স্ অনেক করে আমার চেতনা সঞ্চার করতে লাগলেন। ওদের মুখ দেখে বুঝতে পারছিলাম, অসহ্য পিপাসা ও নিদারুণ শ্রমে ওরাও ক্রমশ অবসন্ন হয়ে পড়ছেন।
কী করে যে পাঁচ দিন কাটলো, জানি নে। বহু কষ্টে শ্রান্ত তৃষ্ণাদীর্ণ দেহ টেনে-টেনে কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো বুকে হেঁটে আমরা সেই সুড়ঙ্গের মোহানার কাছে এসে পৌঁছলাম। বেলা তখন দশটা। সেখানে পৌঁছে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। জ্ঞান হারিয়ে পাথরের উপর পড়ে গেলাম।
যখন জ্ঞান ফিরলো, তখন দেখি কাকামণি আমাকে বুকে নিয়ে রুদ্ধ স্বরে বলছেন : হায়রে বাছা আমার! কেন তোকে সঙ্গে টেনে আনলাম!
কাকামণির এমন গাঢ় কথা শুনে আমার গলার কাছটা বেদনায় টন-টন করে উঠলো। আমার দু-হাতে ওঁর হাত তুলে নিয়ে একটু চাপ দিলাম। কাকামণির চোখ দিয়ে অঝোর ধারে অশ্রু ঝরতে লাগলো। নিজের বোতলটা আমার মুখের কাছে ধরে কাকামণি বললেন : এইখানে অল্প একটু জল আছে–
হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। স্বপ্ন, না সত্যি? পাগল না তো কাকামণি? বোতলে কি আর এক ফোঁটাও জল আছে?
কাকামণি বোতলটা আমার মুখে উপুড় করে ধরলেন। জল! সত্যিকার অল।
আমার আতপ্ত জিহ্বার উপরে যেন অমৃত ঝরে পড়লো। তৃপ্তিতে দুচোখ গাঢ় হয়ে এলো।
কাকামণি বললেন : অ্যাকজেল, এইটুকুই আমার শেষ সম্বল ছিলো, শেষ মুহুর্তের জন্য তুলে রেখেছিলাম। আর এক বিন্দুও জল নেই। আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এই পর্যন্ত আসতেই একেবারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়বি। তাই জলটুকু তোর জন্যে রেখে দিয়েছিলাম। কততবার তৃষ্ণায় আকুল হয়ে ঐ বোতলের দিকে তাকিয়েছি, হাতও বাড়িয়েছি, মনে করেছি একফোঁটা জল খাই। কিন্তু খাইনি—তোর জন্যেই রেখে দিয়েছি। কজেল, অ্যাকজেল, আর আমাদের এক ফোঁটাও জল নেই।
কাকামণি খালি বোতলটা উপুড় করে ধরলেন। এবারে আমি কেঁদে ফেললাম। কাকামণি কি মানুষ, না অন্য কিছু?
ঐ একফোঁটা জলে আমার তৃষ্ণার জালা সামান্যই কমলো বটে, কিন্তু তাতেই শরীর বেশ সুস্থ হলো। গলা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিলো, এখন আবার খানিকটা ভিজলো, কথা বলবার ক্ষমতা ফিরে পেলাম। কাতর কণ্ঠে বললাম : কাকামণি, আর না। জল যখন ফুরিয়ে গেছে, তখন পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নেই। চলো, এখুনি আমরা ফিরে যাই।
কাকামণি নত মুখে চুপ করে আমার কথা শুনলেন। কোনো জবাব দিলেন না।
আমি আবার বললাম : ফিরতে আমাদের হবেই কাকামণি, ফিরতে আমাদের হবেই। তবে শেষ পর্যন্ত স্নেফেলের চুড়ো অবধি ওঠবার শক্তি থাকবে কি না কে জানে।
অক্ষুট কণ্ঠে কাকামণি বললেন : এততদুরে এসে শেষটায় ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবো?
ফিরতে আমাদের হবেই। আরো জোর দিয়ে বললাম এবার। ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। আর এক মুহূর্তও দেরি করা ঠিক হবে না।
অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন কাকামণি। বিবর্ণ মুখে হতাশার রঙ লাগলো। মুখ দেখে বোঝা গেলো, কী করবেন তা ঠিক করে উঠতে পারছেন না। কিন্তু অবশেষে আবার প্রতিজ্ঞার দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ওঁর চোখমূখ। অনতিক্ষুট কণ্ঠে বললেন : তুই যে আশা হারিয়ে ফেলেছিল, তা আমি জানি, অ্যাকজেল। কিন্তু আমার শেষ সম্বলটুকু দিয়ে গলা ভিজিয়েও কি তোর। হারানো সাহস ফিরে এলো না? এখনও তুই হতাশ হয়ে ফিরে যেতে বলছিস? তোর মনে কি আর কখনো আশার আলো জেগে উঠবে না, অ্যাকজেল?
এমন কথা আমি মোটেই আশা করিনি। এইরকম সঙ্কটময় মুহূর্তে কোনো মানুষ যে এরকম কথা বলতে পারে, আমার তা ধারণারও বাইরে ছিলো। অস্ফূট স্বরে বললাম : তবে কি তুমি ফিরতে চাও না কাকামণি?
কাকামণি বললেন : যখন পরিবেশ আমার অনুকূলে তখন কি আর ফিরতে পারি? তা কখনও হতে পারে না।
বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। পরিবেশ তোমার অনুকূলে? তুমি কী বলছে কাকামণি?
কাকামণি বললেন : ঠিকই বলছি। জলের অভাবই তো এখন আমাদের সবচেয়ে বড়ো বাধা? তুই তো সেই কারণেই ফিরে যেতে চাস? কিন্তু ভেবে দ্যাখ, এবার আমরা ঠিক পথ ধরেই এগোবো। আর সাউজও এই পথ বরে গিয়েছিলেন। এই পথে যদি জল না থাকতো, তবে তিনি যেতে পেরেছিলেন কী করে? এই পথে গেলে আমরা জল পাবো।
শুধোলাম : কী করে তুমি অতোটা নিঃসন্দেহ হলে?
এই সুড়ঙ্গের ভিতরে খানিক দূর আমি গিয়েছিলাম। প্রস্তরের স্তরবিন্যাস দেখেই বুঝতে পেরেছি, এই পথে জল আছে।
কিন্তু যদি জল না পাওয়া যায়?
বাধা দিয়ে কাকামণি বললেন : কলম্বাসের আবিষ্কারের কাহিনী জানিস তো? যখন কলম্বাস ঠাণ্ডায় খিদেয় আর উপর্যুপরি বিপদের আবাতে ভেঙে পড়েছিলেন, যখন তার নাবিকেরা ঠিক করেছিলো আর অগ্রসর হবে না, তিনি তখন তাদের কাছ থেকে মাত্র তিনদিন সময় চেয়েছিলেন; বলেছিলেন-তিন দিনের মধ্যে যদি কোনো নতুন দেশের মাটি চোখে পড়ে, ভালো-নইলে নিশ্চয়ই দেশে ফিরে যাবেন। নাবিকেরা সহজেই তাকে সেই সময়টুকু দিয়েছিলো, আর তাই তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন আমেরিকা। আমি কিন্তু তোর কাছে তিন দিনও সময় চাইনে, অ্যাকজেল-শুধু আজকের দিনটা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর। যদি জল না পাওয়া যায়, তবে, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোর সরে কালকেই ফিরে যাবো।
এই কথায় রাজি না হয়ে উপায় ছিলো না বলে সম্মতি জানালাম। কাকামণি বললেন, বেশ। তবে এক সেকেণ্ডও দেরি না আর। শিগগির চল পশ্চিমের সুড়ঙ্গে।
অন্য পথে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কেন যেন মনে হলো এই গহ্বর থেকে জীবনে আর ফিরতে পারবে না। কে জানে, এই সুড়ঙ্গ ঘুরে-ফিরে কোথায় কোন অন্ধকারে গিয়ে শেষ হয়েছে। এবারে কখনো গাঢ়, কখনো ফিকে-নীল রঙের স্লেট-পাথরের প্রাচীর; প্রাচীরের গায়ে কোথাও সোনা, কোনোখানে বা প্ল্যাটিনামের আর সোনার সুতো বিনুনির মতো প্রাচীরের গায়ে।
স্লেট-পাথরের পর স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো ধাতব পদার্থের গ্রন্থিপ্রস্তর। রাশিরাশি অভ্র আমাদের টর্চের আলোয় হিরের মতো জ্বলতে লাগলো। সন্ধের কিছুক্ষণ আগে এই হিরের আলোর ঝলমলানি অন্ধকারের অতলে মিলিয়ে গেলো। আবার আমরা আভাহীন গ্রন্থি-প্রস্তরের প্রাচীরের পাশ দিয়ে চলতে লাগলাম।
আরো দু-ঘণ্টা কাটলো, কিন্তু জলের কোনো চিহ্ন দেখা গেলো না কোথাও। ক্রমশ আবার যন্ত্রণা বেড়ে চললো আমার। বুঝতে পারছিলাম কাকামণিদের আমাদের চেয়েও বেশি কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তবু থামলেন না কাকামণি। একটানা এগিয়ে চললেন।
ক্রমশ আমার আর হাঁটবার শক্তি রইলো না। পা যেন আর চলতে চাইছে না। তবু কোনোমতে ধুকতে ধুকতে এগিয়ে চললাম। তারপর একসময় অস্ফুট আর্ত কণ্ঠে চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে পাথরের উপর পড়ে গেলাম।
জ্ঞান ফিরতেই তাকিয়ে দেখি কাকামণি আর হান্স্ আমার পাশেই পাথরের উপরে শুয়ে ঘুমোচ্ছন। মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর তখন আমার অবস্থা। অতন্দ্র চোখে তাকিয়ে রইলাম অন্ধকারের দিকে। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ দেখতে পেলাম, হান্স্ ঘুম থেকে উঠে একটা টর্চ হাতে নিয়ে আস্তে-আস্তে কোথায় যেন চলেছে। তবে কি আমাদের মৃত মনে করে পালিয়ে যাচ্ছে ও? প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু শুকনো গলা থেকে কোনো শব্দই বেরুলো না। ইচ্ছে হলে ছুটে গিয়ে ধরি ওকে। কোনোমতেই শরীরটাকে টেনে তুলতে পারলাম না। ওদিকে হাসের টর্চের আলো অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো, পায়ের শব্দ ঢাকা পড়ে গেলো অসহ নীরবতায়। আর যন্ত্রণায়, দুর্ভাবনায় আমি কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। তারপর হঠাৎ মনে হলো, হান্স্ তো ক্রমশ নিচে নেমে গেলো, উপরে তত উঠল না। নিচে তো পাতালের অন্ধকার! হান্স্ তবে গেলো কোথায়? পালিয়ে যাবার উদ্দেশ্য থাকলে তো উপরে উঠতো, নিচে নামলো কেন তবে?
কোনো কিছু বুঝবার ক্ষমতা আমার তখন ছিলো না। তাই আমি সেই অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলে পড়ে রইলাম শুধু। ঘণ্টাখানেক বাদে হাসের পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া গেলো।
হান্স্ ফিরে এসে কাকামণির ঘুম ভাঙালো ধাক্কা দিয়ে। বিড়বিড় করে কী যেন বললে তাঁকে।
জ্যা-মুক্ত তীরের মতো উঠে দাঁড়ালেন কাকামণি : জল। কোথায় জল? কোনখানে?
প্রথমটা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম, তারপর কোনোরকমে টেনে-হিচড়ে খাড়া করলাম শরীর। শুনতে পেলাম হান্স্ বলছে : ঐ যে দূরে-নিচের দিকে জল আছে। উল্লাসে অধীর হয়ে সজোরে ওর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলাম আমি। হাসের মুখ কিন্তু চীনেদের মতো নির্বিকার।
জলের আশা শরীরে নতুন শক্তি আনলো। তখনি জলের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। কোনোরকমে শ্রান্ত শরীর টেনে-টেনে হাজার-দুই ফুট নিচে নামলাম। এমন সময়ে কাকামণি হঠাৎ আমায় বললেন : কান পেতে শোন দিকিন, কিছু শুনতে পাচ্ছিস কি না?
রুদ্ধশ্বাসে কান পেতে শুনতে পেলাম, গ্রন্থি-পাথরের কঠিন দেয়াল ভেদ করে দূরাগত বজ্রনির্ঘোষের মতো কি যেন এক উদাত্ত আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ঐ শব্দ নিঃসন্দেহে কালের কল্লোলের।
যতো নিচে নামতে লাগলাম, ততই স্পষ্ট হতে লাগলো জলের কলতোল। মনে হলো, দেয়ালের ওপাশ দিয়ে একটি সঞ্জীবনী ঝরনা-ধারা বয়ে চলেছে। কিন্তু জল কই-জল তো চোখে পড়ছে না! হয়তো এরই নাম মৃগতৃষ্ণিকা।
আরো আধ ঘণ্টা কাটলো। আরো প্রায় মাইলখানেক নিচে নামলাম। এবার ক্রমশ জলের রাগিণী মিলিয়ে যেতে লাগলো। তখন আমরা ফিরে দাঁড়ালাম। দেয়ালের গায়ে যেখানে শব্দ সবচেয়ে স্পষ্ট ছিলো, হান্স্ সেখানে দাঁড়ালো। আমার আর দাঁড়াবার শক্তি ছিলো না। পাথরের উপরে বসে পড়লাম।
এই দেয়াল ভাঙবার পরে জল পাওয়া যাবে? সে তো অসম্ভব! এ দেয়াল ভাঙবার ক্ষমতা কার আছে? তাহলে মৃত্যু।–আমি মরবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম।
হান্স্ আমার দিকে তাকিয়ে বিবর্ণভাবে ইসলো। তারপর আবার কান পাতলে দেয়ালের গায়ে। শুনবার চেষ্টা করলো অদেখা ঝরনার কলয়োল। তারপর ও ওর বিরাট গাঁইতিটা হাতে তুলে নিলে। কোনোদিকে না তাকিয়ে একমনে আস্তে-আস্তে পাথরে আঘাত করতে লাগলো। প্রায় এক ঘণ্টা কাটলো। হান্স্ তখনও পাথরে আঘাত করে চলেছে। শেষটায় কাকামণিও গিয়ে গাইতি ধরলেন।
আরো খানিকক্ষণ কাটলো। তারপর হঠাৎ একটা তীব্র শোঁ-শোঁ শষ শোনা গেলো। বিদ্যুৎবেগে একটা জলধারা বেরিয়ে এসে আছড়ে পড়লো অন্য পাশের দেয়ালে। জলের আঘাতে হান্স্ আর্তনাদ করে উঠলো।
জল ছুঁয়ে দেখি আগুনের মতো গরম, যেন টগবগ করে ফুটছে। উষ্ণ বালে সারা সুড়ঙ্গ ভরে গেলো। বন্ধনহীন উত্তপ্ত জলতর পাতালের দিকে তীব্রবেগে ছুটে চললো।
সেই জল অনেকক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা করে আমরা পান করলাম। অমৃতের মতো লাগলো সেই সঞ্জীবনী ধারা। তারপর যখন আনন্দের প্রথম উদাস কালো, কাকামণি বললেন : এর নাম আজ থেকে হলো হাল নদী।
সানন্দে কাকামণির কথায় সায় দিয়ে উঠলাম আমি। হান্স্ কিন্তু তখনো এমন নির্বিকার, যেন কিছুই ঘটেনি। একপাশে বসে সে তখন জলের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ছিলো।
কাকামণিকে বললাম : এমন করে জল নষ্ট করা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না আমাদের। জলের বোতলগুলি ভরে নিয়ে দেয়ালের রন্ধ্রটা বন্ধ করে দিই।
হেসে কাকামণি বললেন : ভয় নেই। এই উৎসধারা অফুরন্ত। দরকার নেই ঐ রন্ধ্র বন্ধ করে। জল যেমন যাচ্ছে, যাক,-নিচের দিকেই তো যাচ্ছে। আমরাও নিচেই যাচ্ছি। জলস্রোতের অনুসরণ করে চললে পথ হারানোরও ভয় থাকবে না, জলেরও অভাব ঘটবে না কখনো।
যদি উৎস ফুরিয়ে যায়?
ঘাড় নেড়ে কাকামণি বললেন : না, তা যাবে না। জলের এতো স্রোত দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এর উৎস অনেক উপরে–এ উৎস ফুরোবে না।
উৎফুল্ল মনে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। অনেক দিনের পর আজ খেয়ে-দেয়ে ভালো করে ঘুমোনো যাবে!
অন্তহীন অন্ধকার ভেদ করে পাতালের দিকে জলধারা এগিয়ে চললো। ঠিক যেন আমাদের বিনি-মাইনের পথ-প্রদর্শক।
১০. অজানার উজানে
পরদিন ঘুম থেকে উঠেই আবার আমরা নিচে নামতে লাগলাম। এবার পথ সাপের মতো একেবেঁকে এগিয়ে গেছে। পায়ের তলায় কুলকুল শব্দ করে বয়ে চলেছে জলের স্রোত।
হঠাৎ সামনে পড়লো প্রকাণ্ড বড়ো একটা গহ্বর। যেন পাতালের অন্ধকারে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। গহ্বরের মধ্য দিয়ে রাস্তা একরকম সোজা নিচে নেমে গেছে দেখে কাকামণি আনলে চেঁচিয়ে উঠলেন।
হান্স্ দড়ি বের করে আমাদের কোমরে বাংলো, যাতে কেউ যদি পড়েও যায়, তবে অন্য দুজনের সাহায্যে আত্মরক্ষা করতে পারবে। উনিশে জুলাই থেকে সাতাশে জুলাই পর্যন্ত একটানা নিচে চললাম আমরা। কিন্তু সেই প্রকাণ্ড গহ্বরের যেন আর শেষ নেই; অতল, নিতল যেন সে।
কাকামণি বললেন, এখন আমরা কোথায় আছি জানিস? অতলান্তিক মহাসাগরের নিচে।
অবাক হয়ে বললাম, কী বলছে কাকামণি? এখন আমাদের মাথার উপরে প্রখর ভয়ঙ্কর অতলান্তিক? অসম্ভব।
কে বললে অসম্ভব? সত্যিই আমরা এখন অতলান্তিকের নিচে। অবশ্য এতো নিচে, যে আমাদের কাছে এখন সবই সমান।
উনত্রিশে জুলাই সন্ধের সময় আমরা একটা বিশাল গুহার মধ্যে প্রবেশ করলাম। সেখানেই সে-রাতটা কাটানো গেলো। পরদিন ভোরে আবার যাত্রার প্রস্তুতি চললো। গ্রানাইট পাথরের মেঝের উপর দিয়ে তখনো সেই জলস্রোত বয়ে চলেছে।
কাকামণি হিশেব করতে করতে বললেন : আজ পর্যন্ত আমরা মোটে একশো পঞ্চান্ন মাইল পথ চলেছি। মাথার উপরে এখন অতলান্তিক গর্জাচ্ছে। হয়তো এখন সমুদ্রের উপরে চলছে ঝড়, ঝঙ্কা বজ্রপাত–উন্মাদ হয়ে নাচছে ঢেউ–হয়তো কোনো জাহাজ ড়ুবতে ড়ুবতে চলেছে–হয়তো–
কাকামণির হয়তো আর ফুরোবে না দেখে বাধা দিয়ে শুধোলাম, আচ্ছা কাকামণি, সবশুদ্ধ আমরা কতো নিচে এখন?
হিশেব করে কাকামণি বললেন, আটচল্লিশ মাইল। এতে নিচে নেমেছি, অথচ দ্যাখ, কোনো রকম কষ্ট হচ্ছে না আমাদের, শুধু কানের মধ্যে সামান্য যা। তাও ক্রমশ সহ্য হয়ে যাবে।
ক্রমশই আমরা নিচে নেমে চলেছি। পথ কোথাও ঢালু, কোথাও একেবারে সোজা নেমে গেছে পাতালের দিকে অন্য পৃথিবীর সন্ধানে। একত্রিশে জুলাই অবধি ক্রমাগত নেমেই চললাম, কিন্তু পথের আর শেষ নেই যেন। শুধু অজ্ঞাত পথে এগিয়ে চলা।
এ কদিন আমাদের কোনো বিপদ ঘটেনি। শুধু সাতই আগস্ট আমি ভয়ানক এক বিপদে পড়লাম। আমি চলছিলাম সকলের আগে। পিছনে কাকামণি আর হানস। কাকামণির হাতে একটা আলো, আমার হাতেও একটা। পথের দুপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি, হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরতেই দেখি, আমি একলা। কাকামণি আর হাসকে চারপাশে কত খুঁজলাম, কিন্তু কোনো সাড়াশব্দও পাওয়া গেল না। অগত্যা যে-পথ ধরে এসেছিলাম সে-পথে ফিরে চললাম। অনেকক্ষণ ঘুরেও কাকামণি বা হাসের সাক্ষাৎ পেলাম না। ওদের সাক্ষাৎ না পাওয়ার মানে সহজেই বুঝতে পারলাম। ভয়ে ছমছম করে উঠলো শরীর। বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর সম্বিত ফিরতেই খুব জোরে চেঁচিয়ে কাকামণিকে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু কর্কশ প্রতিধ্বনির অট্টহাসি ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলাম না।
এই পাতালে তো একটিই পথ-তবে আমি পথ হারালাম কী করে? হঠাৎ মনে পড়লো সেই জলধারার কথা। সেই জলরেখা ধরে হাঁটলেই তো আবার সেই গুহার কাছে পৌঁছনো যাবে।
হেঁট হয়ে জলে হাত-মুখ ধুতে যাচ্ছি, তখনই সমস্ত আশাভরসার শোচনীয় বিনাশ ঘটলো। কী সাংঘাতিক! পথের উপর জলের চিহ্নমাত্র নেই-শুকনো গ্রানাইট পাথর শুকনো পাত বের করে আমাকে যেন ব্যঙ্গ করতে লাগলো।
মাথায় যেন সারা পৃথিবী ভেঙে পড়লো। ভাববার শক্তি পর্যন্ত রইলো না। একেই হয়তো পুথি-পত্রে জীবন্ত সমাধি বলে! রহীন নীরবতা যেন শব্দহীন অট্টহাসিতে আমাকে টিটকিরি করতে লাগলো! ঝিমঝিম করতে লাগলো সমস্ত চৈতন্য।
কখন যে অন্যমনস্কভাবে চলতে-চলতে ভুল পথে এসে পড়েছি, তা বুঝতেও পারিনি। এখন কী করে কাকামণির সন্ধান পাওয়া যায়? তবে কি পাতালের এই অন্ধকার পথে জীবন্ত সমাধি হবে আমার মনে পড়লো পৃথিবীর আলো হাওয়ার কথা, শ্যামল স্নিগ্ধতার কথা, গ্রোবেনের কথা। বেদনায় গলার কাছটা টন-টন করে উঠলো।
সমস্ত ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম। আমার সঙ্গে দিন-তিনেক কাটানোর উপযোগী খাবার আছে, আর আছে এক বোতল জল। সেই ভরসায় ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠলাম-যদি আবার জলস্রোতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়–অন্ততপক্ষে যদি কোনো রকমে স্নেফেলের উপরেও উঠতে পারি।
আধ ঘণ্টা ধরে এগিয়ে চললাম। পথের চেহারা, দেয়ালের রঙ, পার্থরের কুচি দেখে পথ চেনবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। তবু দ্রুতপায়েই এগোলাম। চলা-চলতে হঠাৎ এক জায়গায় কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা লাগলো, হাত বাড়িয়ে দেখতে পেলাম আমার সামনে নিরেট পাথরের দেয়াল। বোধহয় আমাকে এই অবস্থাতে ব্যঙ্গ করার অঙ্কই তার সৃষ্টি!
সর্বনাশ! এগোবা কী করে তবে? এবার আর কোনো আশা নেই, ভরসা নেই, শুধু অসহায়ভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষ্ণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও নেই। দুঃসহ নিরাশায় পাগলের মতো মেঝেয় মুখ ঘষতে লাগলাম। চেঁচিয়ে শেষবারের মতো কাকামণিকে ডাকবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোলো না।
এদিকে আস্তে-আস্তে নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগলো আলো। আর সামান্য কিছুক্ষণ তার আয়ু। শূন্য চোখে ক্রমক্ষীয়মান আলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম, আলো ক্রমেই নিভে আসছে। চারপাশে কারা যেন ছায়ার মতো নাচছে। অন্ধকারের চাপ ঘন হচ্ছে ক্রমশ। যেন পিষে মারবে আমাকে। তারপর এক সময়ে দপ করে নিভে গেলো। এবার অন্ধকার।
অন্ধকার, অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। চারদিকে গভীর, সুতীক্ষ্ণ, অন্তহীন অন্ধকার–সে অন্ধকার যেন স্পর্শ করা যায়, জড়ানো যায় হাতে। ভয়ে শিরশির করে উঠলে গা। মরি যদি, আলোয় মরি যেন। আলো, আলো, একটু আলো–
তারপর আমার জ্ঞান হারিয়ে গেলো।
কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলাম, সঠিক বলতে পারি না। জ্ঞান ফিরতেই উঠে দাঁড়ালাম-তারপর পাগলের মতো সেই অন্ধকারেই ছুটতে লাগলাম। কতোবার আছাড় খেয়ে পড়লাম, কতবার যে মাথা ঠুকে গেলো দেয়ালে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। রক্তে ভরে গেলো চোখ-মুখ। তবু ছুটতে লাগলাম উন্মাদের মতো। তারপর হঠাৎ সজোরে দেয়ালে মাথা ঠুকে গেলো। আবার আমার জ্ঞান হারিয়ে গেলো।
জ্ঞান ফিরতেই শুনতে পেলাম, দূরে-বহুদূরে, বজ্রগর্জনের মতো একটা শব্দ। কিসের শব্দ বুঝতে পারলাম না। উৎকর্ণ হয়ে সেই শব্দ শুনবার চেষ্টা করলাম। মিনিট-কয়েক পরে সেই আশ্চর্য শব্দ থেমে গেলো। বুঝতে পারলাম, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, তাই ঐ শব্দের সৃষ্টি হয়েছিলো আমার মগজের স্নায়ু উপশিরায়।
না ঐ তো আবার আবারো শব্দ শোনা যাচ্ছে। এবারে অন্যরকম শব্দ। কারা যেন কথা বলছে। কারা? কারা কথা বলছে দেয়ালের ওপাশে? মরিয়া হয়ে প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচিয়ে উঠলাম : বাঁচাও, বাঁচাও।
প্রথমটা কোনো উত্তর পেলাম না। অনেকক্ষণ পরে আবার যেন কাদের কথা কানে ভেসে এলো। তার পরমুহূর্তেই একটা ভীষণ শব্দে চারদিক ছেয়ে গেলো। যতোবারই কথা শুনছি, তার পরক্ষণেই বজ্রের মতো শব্দ উঠছে আমার চারপাশে।
কে যেন আমার নাম ধরে ডাকলো, অ্যাকজেল! অ্যাকজেল।
এবারে বুঝতে পারলাম। তারের মধ্য দিয়ে যেমন করে বিদ্যুতের প্রবাহ বয়, তেমনই এই দেয়ালের ভিতর দিয়ে শব্দ আসছে। আমার কথা ওদের শোনাতে হলে এই দেয়ালে মুখ লাগিয়ে বলতে হবে। দেয়ালে মুখ রেখে ডাকলাম, কাকামণি।
উৎকর্ণ হয়ে রইলাম উত্তরের জন্য। এক-এক পলক যেন এক-একটি যুগ। অবশেষে আমার কানে এলো কাকামণির গলা : আকজেল, এ কি তোর গলার শব্দ? তুই এখন কোথায়?
হ্যাঁ কাকামণি, আমি অ্যাকজেল। পথ হারিয়ে ফেলেছি। আলোটাও নিভে গেছে।
সেই জলের রেখাটাই বা কী হলো?
জলস্রোতটাও হারিয়ে ফেলেছি।
হুঁ। কাকামণির কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। যাক, কোনো ভয় নেই। গ্যালারির রাস্তা ধরে তোকে কতো খুঁজেছি, তোর নাম ধরে কতো ডেকেছি, বন্দুকের শব্দ পর্যন্ত করেছি।-অ্যাকজেল, আরেকটু সাহস করে থাক। পরস্পরের গলা শোনা যাচ্ছে, অথচ কেউ কারো কাছে যেতে পারছি নে; কী করা যায়, ভেবে নি,–একটু অপেক্ষা করে থাক।
কাকামণি, আমাদের মধ্যে দূরত্ব কততটা বলতে পারো?
তোর কাছে ফসফরাস-দেয়া নোমিটারটা আছে তো? কাকামণি বললেন; এক কাজ কর। তুই বড়ি ধরে আমার নাম উচ্চারণ কর, আমিও খড়ি ধরে শুনছি, তারপর খেয়াল রাখ ঠিক কতো সময়ে আমার কথা শুনতে পাস। হ্যাঁ এবার ডাকতে পারিস।
আমি দেয়ালে মুখ রেখে কাকামণিকে ডাকলাম। একটু পরেই শুনতে পেলাম আমার নাম।
কাকাশি শুধোলেন, কতো সময় লাগলো?
চল্লিশ সেকেণ্ড।
তাহলে শব্দ আসতে ঠিক বিশ সেকেণ্ড লেগেছে। বললেন কাকামণি। শব্দ সেকেণ্ডে এগারোশো বিশ ফুট চলে। তার মানে, বিশ সেকেণ্ডে বাইশ হাজার চারশো ফুট। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে ব্যবধান হলো প্রায় শোয়া চার মাইল।
অবাক হয়ে বললাম, শোয়া চার মাইল।
হ্যাঁ। তুই এক কাজ কর। নিচের দিকে নেমে আয়, তাহলে শিগগিরই দেখতে পাবি আমাদের। তাড়াতাড়ি কর।
সঙ্গে-সঙ্গে রওনা হয়ে পড়লাম। পা চলতে চাইছিলো না, শ্রান্তিতে নুয়ে পড়তে চাইছিলো শরীর, তবু সেই ঢালু পথ ধরে এগিয়ে চললাম। পথ এমনভাবে গড়ানো যে কোনো-কোনো জায়গায় আমাকে হাঁটতে হলো না-কে যেন আমাকে ঠেলে নামতে লাগলো। মনে হলো যেন একটা কুয়োর মধ্যে দিয়ে নামছি। গতি ক্রমশ তীব্র হতে লাগলো। চেষ্টা করেও তাকে একটু ধীর করতে পারলাম না। তারপর অনেক নিচে একটা পাথরের উপর আছাড় খেয়ে পড়লাম। চোখের সামনে নেমে এলো একঝাক ঘন অন্ধকার, তারপরে কী হলো, তা আমার মনে নেই।
জ্ঞান ফিরতেই দেখলাম একটা কম্বলের উপরে শুয়ে আছি-কাকামণি আমার উপরে ঝুকে পড়ে হাতের নাড়ি দেখছেন। আমাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে শিশুর মত উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন উনি। ক্ষীণভাবে হাসবার চেষ্টা করে শুধোলাম, আমরা এখন কোথায় আছি?
এখন আর একটাও কথা না, কথা কাল হবে। এখন ঘুমো।
সত্যি বলতে কি, আমি তখন ভীষণ দুর্বল। তাই পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বুজোলাম দ্বিরুক্তি না-করে।
ভোরবেলায় আমার ঘুম ভাঙল। চারদিক খচ্ছ আলোয় উল। দূরে, অনেক দূরে, কিসের যেন শব্দ হচ্ছিল–ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট, মৃদু অথচ উদাত্ত সেই শব্দ যেন দূরে বেলাভূমির উপরে সমুদ্রতরঙ্গ এসে আছড়ে পড়ছে। প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেলাম। স্বপ্ন, না সত্যি?–
না, স্বপ্ন তো নয়—স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তরঙ্গের শষ। তবে কি—
কাকামণি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছিস এখন?
ভালো। কিন্তু ও কীসের শব্দ? আর এতো উজ্জ্বল আলোই বা কিসের?
আস্তে-আস্তে সব বুঝতে পারবি, শুধু আজকের দিনটা ধৈর্য ধরে থাক। এখন খোলা হাওয়া লাগলে তোর অসুখ করতে পারে।
চমকে উঠলাম। খোলা হাওয়া? কী বলছ তুমি?
ঠিকই বলছি। হাওয়া এখন প্রবল, এমন অবস্থায় তোর চলাফেরা করা ঠিক হবে না। আজকের দিনটা জিরিয়ে নে। নইলে কাল সমুদ্রযাত্রায় আবার তোর অসুখ করবে।
আমি আরো হতভম্ব হয়ে পড়লাম। সম্বিত ফিরতেই উঠে দাঁড়ালাম। গায়ে রাগ্টা জড়িয়ে এগোলাম কাকামণির সঙ্গে।
অল্পক্ষণ পরেই চোখ-ধাঁধাঁনো দিগন্ত-বিসারী উজ্জ্বল আলো পিছলে পড়লো আমার উপরে। সহ্য হলো না সেই আলো, অনভ্যস্ত চোখ সহজেই বুজে এলো। একটু পরে চোখ খুলে যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ে অস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে উঠতে হলো, সমুদ্র।
হ্যাঁ, সমুদ্র। বললেন কাকামণি! এই সমুদ্রের নাম আমার নামেই দিয়েছি, লিডেনব্রক সাগর।
নীলাঞ্জিত সমুদ্রের ঢেউ উচ্ছ্বসিত হয়ে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমির সোনালি বালিতে, আর সেই সোনালি বালিতে চিকচিক করছে ঢেউ-এর রুপোলি ফেনী। দেখতে একেবারে সমুদ্রের মতো। কিন্তু এ অন্য পৃথিবীর সমুদ্র, পাতালের। তাই যেন একটু নিষ্প্রাণ। চারদিকে যে উজ্জ্বল আলো, তা সূর্যালোক বা চন্দ্রালোক কিছুই নয়, অরোরা বোরিয়ালিসের মতো এও এক ধরনের বৈদ্যুতিক আলো।
নিঃসীম শূন্যে তখন অসম্ভব মেঘ করেছে। যে-কোনো মুহূর্তে মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে পারে। বিস্ফারিত চোখে এই অলৌকিক দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। মনে হলো পৃথিবী ছেড়ে যেন অন্য কোনো গ্রহে এসে পড়েছি। পাথরের অন্ধকার গহ্বরে সাতচল্লিশ দিন কাটানোর পর এমন উন্মুক্ত বাতাস আর নীলাঞ্জিত সমুদ্র আমাকে আশ্বাস দিলো, শক্তি দিলো, স্বাস্থ্য দিলো।
উপকূল ধরে হাঁটতে লাগলাম কাকামণির সঙ্গে। উপকূল অসম্ভব আঁকাবাকা। শুধু পাথর, আর পাথর। কোনোখানে-বা পাহাড়ের ফাটলের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে ঝর্নাধারা, কোথাও বা উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে উঠছে গরম তাপ।
একটু দূরে গভীর জঙ্গল দেখা গেলো। সেই জঙ্গলের ভিতর ঢুকতেই কেমন যেন শীত করতে লাগলো, পায়ের তলার মাটি ভিজে। আধ ঘণ্টা পর সেই জঙ্গল পেরিয়ে আবার সমুদ্র-কূলে এসে পৌঁছলাম। সামনে দেখতে পেলাম আর-একটি জঙ্গল। এই জঙ্গলের গাছপালা খুব বড়ো-বড়ো, প্রত্যেকটি একশো থেকে দেড়শো ফুট উঁচু। মাটিতে নানা জন্তুর শ্বেতবর্ণ কঙ্কাল। অনেকক্ষণ পর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলাম। কাকামণি আমাকে তাঁবুর দিকে নিয়ে চললেন। এইটুকু হাঁটতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাই তাঁবুতে পৌঁছেই শুয়ে পড়লাম আমি।
পরদিন সকালবেলায় ঠিক করলাম, অনেক দিন স্নান করিনি, আজ এমন সুন্দর সমুদ্রে স্নান করতেই হবে। স্ফটিক-স্বচ্ছ উজ্জল জলে স্নান করে উঠবার পর সারা শরীরে স্বাস্থ্যের আবির্ভাব অনুভব করলাম। খিদেও লাগলো বেশ। তাড়াতাড়ি আহার সেরে নিলাম।
অল্পক্ষণ পরে কাকামণি জানালেন, এবারে সমুদ্রে জোয়ার আসবে।
পাতালের সমুদ্রেও জোয়ার-ভাটা হয়? আশ্চর্য!
আশ্চর্য কিছুই না, স্বাভাবিক। পৃথিবীর সব কিছুই তো অভিকর্ষের অধীন।
আচ্ছা কাকামণি, এখন আমরা কোন্ জায়গায় আছি?
আইসল্যাণ্ড থেকে প্রায় সাড়ে চারশো মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। আর পৃথিবীর উপর থেকে কতোটা নিচে নেমেছি জানিস? প্রায় একশো দশ মাইল। এখন আমাদের মাথার উপরে হয় স্কটল্যাণ্ড, নয়তো ইংল্যাণ্ড।-হ্যাঁ, এবারে এই সমুদ্র পেরোবার ব্যবস্থা করতে হবে।
সমুদ্র পার হবে? অবাক হলাম আমি। কী করে? জাহাজ কই?
জাহাজ বা নৌকা করে পেরোবার কথা তো বলিনি। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে ভেলা বানিয়ে নেবো।
আবার এখন গাছ কাটতে হবে?
কাটা অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। চল, দেখে আসবি।
কাকামণির সঙ্গে মাইলখানেক দূরে গিয়ে দেখি, হান্স্ কাঠের টুকরো ও গুঁড়ি দিয়ে বেশ মজবুত করে একটা ভেলা তৈরি করছে।
পরদিন সন্ধের সময় ভেলা তৈরি হলো। লম্বায় দশ ফুট, চওড়ায় পাঁচ। তিনজনে ঠেলে ভেলাটিকে জলে নামালাম। জলের উপর বেশ সুন্দর দেখালো আমাদের জল-পোতকে। তখন অন্ধকার গাঢ় হয়েছে বলে ভেলাটিকে দড়ি দিয়ে একটা পাথরের সঙ্গে বেঁধে রাখা হলো। কাল ভোরে এই ভেলায় চড়েই আমরা পাড়ি দেবো অথই সমুদ্রে।
১১. অন্য পৃথিবীর সমুদ্র পাড়ি
তেইশে অগস্ট সকালবেলায় আমাদের ভেলা অজানা সমুদ্রে রওনা হলো। হান্স্ পাল তুলে দিয়ে হালের কাছে গিয়ে বসলো। অনুকূল হাওয়া আর
স্রোতের টানে তরতর করে ভেলা এগিয়ে চললো।
কাকামণি বললেন, যেখান থেকে আমাদের ভেলা ছাড়লো, সেই বন্দরটার একটা নাম দেয়া উচিত। কী নাম দেওয়া যায় বল তো?
কেন? বন্দরটার নাম পোর্ট গ্রোবেন দিলেই তো হয়।
স্মিতমুখে আমার দিকে তাকিয়ে কাকামণি বললেন, পোর্ট গ্রোবেন? বেশ, তাই হোক।
এই লক্ষ্যহীন নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরোবার পর থেকে সত্যিই গ্রোবেনকে খুব বেশি করে মনে পড়ছিলো।
চব্বিশে অগস্ট শুক্রবার বাতাসকে বেশ শান্ত আর সুস্থির মনে হলো। ভেলা তেমনি তরতর করে এগিয়ে চলেছে। সামনে, দু-পাশে, পিছনে–চারদিকে শুধু এল আর জল।
দুপুরবেলার দিকে হান্স্ একটি ছিপ নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে বসলো। বঁড়শিতে মাংসের টোপ গেঁথে ছিপ ফেলে বসে রইলো সে। ঘণ্টা-য়েক পরে একসময়ে কিন্তু সত্যি সত্যি ছিপে টান পড়লো। হান্স্ তক্ষুনি ছিপ টানলে। দেখতে পেলাম জলে একটা মাছ ছটফট করে নড়ছে।
মাছটা একটু অদ্ভুত ধরনের। মাথাটা আশ্চর্য রকম চ্যাপ্টা, মুখটা গোল, গারে বনরুইয়ের মতো শক্ত আঁশ। মুখে দাত নেই, পিছনে লেজও নেই। কাকামণি বললেন, এটা এ-যুগের মাছ নয়। এ হচ্ছে কোটি-কোটি বছর। আগেকার যুগের মাছ। পৃথিবী থেকে এ-মাছ লোপ পেয়ে গেছে। ঐ দ্যাখ, মাছটার কোনো চোখ নেই। পণ্ডিতেরা এ-মাছের তিনটে নাম দিয়েছেন–গ্যানোখাড, ফোলাসপিডে আর প্টেরিকথিস।
আমি অবাক চোখে এই দাতভাঙা ত্ৰিনামধারী অদ্ভুত মাছটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। হান্স্ আবার ছিপ ফেললে। দেখতে-দেখতে হান্স্ সেই আতের ও অন্যান্য ধরনের প্রায় কুড়িটা মাছ ধরলে। কাকামণি সযত্নে সেগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করলেন।
সমুদ্রে এতো মাছ, কিন্তু আশ্চর্য, শূন্তে কোনো পাখি নেই।
ছাব্বিশে অগস্ট, রবিবার। কাল সারাদিনে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি, শুধু আকাশটা একটু মেঘলা ছিলো। আজ আকাশ আবার পরিচ্ছন্ন।
সমুদ্রের কোনো কিনারা চোখে পড়লো না। কাকামণিকে খুব উত্তেজিত দেখালো। সমুদ্রের শেষ নেই বলে তার রাগের সীমা ছিলো না। আরেকটা প্রশ্নও আমাদের সামনে ছিলো। সাক্ন্যুউজম্ কী সত্যিই সমুদ্রপথে এসেছিলেন?
আটাশে অগস্ট, মলবার। কাল বিকেল থেকে সমুদ্রের জলে ভীষণ আলোড়ন চলছে। তবু হান্স্ সতর্ক হাতে ভেলাটিকে সামলে রেখেছে। আজো সারাদিনে কোথাও সমুদ্রের শেষ দেখা গেলো না। সন্ধেবেলার দিকে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।
হঠাৎ এক ভীষণ ধাক্কায় আমার দুঃস্বপ্নভরা ঘুম ভেঙে গেলো। ভেলার যে কোণে আমি শুয়েছিলাম, সেই প্রচণ্ড ধাক্কায় সে-কোণ থেকে ছিটকে এসে লোর অন্য কোণে পড়লাম আমি। ঘুমের ঘোর কাটবার আগেই একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা গেল যে, কোনো মারাত্মক কারণেই সমুদ্র এমন আলুথালু হয়ে উঠেছে।
তারপরেই সন্ধেবেলার অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পেলাম ছ-শো গজ দূরে প্রকাণ্ড একটা রাত্রির মতো কালো জিনিশ। সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে-সঙ্গে সেও লাফালাফি করছে। অবাক হয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, এ যে একটা অতিকায় শুশুক!
কাকামণি পর্যন্ত অক্ষুট বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, ঐ যে একটা ভয়ঙ্কর কুমির! কী বিরাট দেহ! মুখের হাঁ আর চোয়ালের বহরটা দেখেছিস?
ঐ দ্যাখো কাকামণি, একটা সামুদ্রিক গিরগিটি–অনায়াসে আমাদের মতো জনাপঞ্চাশকে গিলে ফেলতে পারে!
ঐদিকে দ্যাখ তিমিমাছটা কীভাবে জলের মধ্যে আলোড়ন তুলেছে!
এতগুলো মারাত্মক রকমের অতিকায় জলজন্তু একসঙ্গে দেখে বিস্ময় হতবাক হয়ে গেলাম। দেখতে-দেখতে চারদিকে আরো অনেকগুলো লিজ ভেসে উঠলো। তাদের সে কী বিরাট চেহারা। শরীরে কী অসম্ভব জোর! তাদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে ছোটো, সেও বোধহয় তার লেজের এক ঝাপটায় আমাদের এই ডেলাটি একেবারে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিতে পারে।
এইসব ভয়ানক জলজন্তুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য হান্স্ তাড়াতাড়ি ভেলার মুখ খুলে দিলে, যাতে কোনোমতে কোনো নিরাপদ এলাকায় গিয়ে পৌঁছননা যায়। কিন্তু যেদিকেই সে তেলা চালায়, সেদিকেই পথ বন্ধ। কোথাও পঞ্চাশ ফুট লম্বা একটি কচ্ছপ পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বা তারও বড়ো একটি সাপ ফণা তুলে লেজের ঝাপটা মেয়ে কি করে তুলেছে জল। কোনোদিকে যাওয়ার উপায় নেই।
ভয়ে কাঠ হয়ে বসে রইলাম। এ-কথা বুঝতে আমাদের বাকি ছিলো না যে এদের গুলি করেও কোনো লাভ নেই। এমন সময়ে দুটি জন্তু একেবারে ভেলায় দুপাশে এসে পড়লো–একদিকে সেই মারাত্মক কুমির, আর অন্যদিকে একটি সাংঘাতিক সাপ। ভয়ে আমি চোখ বুজোলাম-এবারে আর রেহাই নেই! জলজন্তু-দুটি কিন্তু ভেলা আক্রমণ না করে পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভেলা থেকে প্রায় তিনশে গজ দূরে তাদের লড়াই চলতে লাগলো। সেই ভয়ংকর ও অলৌকিক লড়াই-এর বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তাদের লেজের ঝাপটা আর দেহের পেষণে সমুদ্র ফুলে, ফেঁপে, ফুশে উঠলো রাগে। সাপের চোখদুটি টকটকে লাল মাথাটা আকারে মানুষের মাথার মতো। লম্বায় একশো ফুট সাপটা। কুমিরের শরীরে লোহার মতো কঠিন কালো রঙের আঁশ। তাদের প্রচণ্ড সংগ্রামে মথিত-উন্মথিত হতে লাগলো সমুদ্র। আর সেই উথালপাখাল সমুদ্রে কতবার যে ওল্টাতে-ওটাতে বেঁচে গেলো আমাদের ভেলা, তার কোনো লেখাজোখা নেই।
কততক্ষণ যে ওদের লড়াই চললো, সে-কথা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব। শুধু এই কথাই বলতে পারি, অনেকক্ষণ পর অকস্মাৎ দুটিতেই জলের ভিতরে ড়ুব দিয়ে সমুদ্রের নিচে লড়াই শুরু করে দিলে, আর আরো অনেকক্ষণ পর হঠাৎ জলের উপরে জেগে উঠল একটি ভয়ংকর মাথা। সেটি সাপের। কুমিরের মরণকামড়ে মুহূর্ষু সাপটা যন্ত্রণায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে, আর তার মৃত্যু-যন্ত্রণার আলোড়নে সমুদ্র আলুথালু হতে থাকলো। কিছুক্ষণ পরে আর সেই সাপটার চিহ্নমাত্র দেখা গেলো না। কুমিরটা কোথায় অদৃশ্য হয়েছে কে জানে। সমুদ্রজলের উপর নেমে এলো একরাশ শব্দহীন সমারোহ।
বরাত? হ্যাঁ, বরাত ভালো না থাকলে এমনি অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। আর একটুও দেরি না করে প্রাণপণে ভেলাটিকে অন্যদিকে নিয়ে চললাম আমরা।
উনত্রিশে অগস্ট, বুধবার। আকাশে ঘন মেঘ। বিদ্যুতের চাবুক বারে বারে সেই মেঘকে ছিন্ন-ভিন্ন করছে। বিকেল চারটের সময় হান্স্ মাস্তুলের উপরে উঠে চারদিক লক্ষ করতে লাগলো—কোথাও তীরের সন্ধান পাওয়া যায় কি না। সমুদ্রের একদিকে সে অনেকক্ষণ ধরে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ দূরে কিসের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো, অবাক গলায় বললো, ঐ যে! ঐ দেখুন।
তক্ষুনি দূরবীন নিয়ে নির্দেশিত দিকে তাকালেন কাকামণি। তারপর উনিও চেঁচিয়ে উঠলেন, হুঁ! তাই তো দেখছি!
বিস্মিত হয়ে শুধোলা, কী কাকামণি? আবার নতুন কোনো জানোয়ার নাকি? তবে আর দেরি করা ঠিক হবে না। শিগগিরই অন্যদিকে জেলা নিয়ে যেতে হবে।
হ্যাঁ বললেন কাকামণি, আর দেরি করা ঠিক হবে না।
ভেলা থেকে সেই অপার্থিব অতিকায় বস্তুটি মাইলকয়েক দূরে হবে। তিমিমাছের মতন শূন্যে জলের ফোয়ারা ছুড়ছিলো সে।
হান্স্ যখন সেই অতিকায় জলজন্তুটির দিকেই ভেলা চালাতে লাগলো, তখন রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সহস্রবার বারণ করা সত্ত্বেও সে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করলো না আমার কথায়। আস্তে-আস্তে সেই প্রচণ্ড ফোয়ারা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো, আর স্পষ্ট হয়ে উঠলো সেই অতিকায় জন্তুটির কুচকুচে কালো শরীর। আর ঠিক সেই সময়ে হান্স্ আইসল্যাণ্ডের ভাষায় কী যেন বলে উঠলো ঐ জন্তুটিকে নির্দেশ করে।
হান্সের কথা শুনে কাকামণি অবাক হয়ে গেলেন। দ্বীপ? বলো কী হান্স্?
আমার তো বিস্ময়ে বাকরোধ হয়ে গেলে একেবারে। হান্স্ কি পাগল হয়ে গেলে নাকি? কিন্তু পরক্ষণে শুনলাম কাকামণি বলছেন, না, হান্স্ ঠিকই বলেছে। দ্বীপই। ঐ জলের ফোয়ারাটা হলো উষ্ণ প্রস্রবণ।
একটু পরেই বোঝা গেলো যে কাকামণির ধারণা মোটেই মিথ্যে নয়। স্পষ্ট হতে থাকার সঙ্গে-সঙ্গে উষ্ণ প্রস্রবণটিকে সুন্দর দেখাতে লাগলো। দ্বীপের গড়নটুকুও ভারি অদ্ভুত। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটা অতিকায় জলজন্তু জলের উপরে ভাসছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সেই ফোয়ারার চারদিকে বারেবারে নীল রঙের বিদ্যুৎ ঝিলিক মেরে উঠছিলো।
প্রস্রবণটি যেদিকে ছিলো, তার বিপরীত দিকে ভেলাটিকে বাধা হলো। দ্বীপটি গ্রানাইট পাথরের। দ্বীগকে দেখলাম থরথর করে কাঁপছে টিম-ইঞ্জিনের বয়লারের মতো; দেখা গেলো দ্বীপটা ফাপা, ভিতরটা কেবল গরম বাষ্পে ভরা।
খানিকটা এদিক-ওদিক ঘুরে ডেলায় ফিরে দেখি, হান্স্ ইতিমধ্যে ভেলার হালটা মেরামত করে নিয়েছে। সেদিন একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল কিনা জলের ঝাপটায়! ভেলায় উঠে আবার সেই প্রস্রবণটির দিকে তাকালাম, একটা অদ্ভুত ব্যাপার নজরে পড়লো। ফোয়ারার জল একবার খুব জোরে উঠছে, আর পরের বারে উঠছে খুব আস্তে-আস্তে–ঠিক যেন ইঞ্জিনের ভাল্ভ থেকে ভলকে ভলকে বাষ্প বেরোচ্ছে,
এইসব লক্ষণ দেখে বুঝতে বাকি রইলো না যে এটা একটা ভয়াবহ আগ্নেয় দ্বীপ।
সারারাত্রি ভেলায় করে অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলাম আমরা, তাই পরদিন ভোরবেলায় সেই উষ্ণ প্রস্রবণটি আর চোখে পড়লো না।
জোরালো হাওয়ার মুখে পড়ে বেশ দ্রুতবেগেই ভেলা চলছিলো। আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিলো ঘন-ঘন। মেঘের নিবিড় রঙ দেখে বোঝ গেলো, শিগগিরই একটা ভয়ংকর ঝড় উঠবে। এ-ঝড় তো আর আমাদের পরিচিত পৃথিবীর ঝড় নয় যে, খানিকক্ষণ ধুলোবালি উড়িয়ে গাছ-পালা ভেঙে চারদিক লণ্ডভণ্ড করে থেমে যাবে এ হলো শুধু বিদ্যুতের তাণ্ডবলীলা।
ধারণাটি যে মোটই মিথ্যে নয় তা বুঝতে পারলাম, যখন হঠাৎ আমার দম বন্ধ হয়ে যেতে চাইলো। সারা শরীরের মধ্যে কিসের যেন উন্মাদ নৃত্য চলতে লাগলো। স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠলো রক্ত। মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠলো, কাটা দিয়ে উঠলো গায়ে। আমার খালি মনে হতে লাগলো, এখন যদি কেউ আমাকে ছোঁয়, তবে তখুনি সে ভীষণ শক্ খাবে। এমন প্রবল বিদ্যুতের তোত আমার শরীরের মধ্য দিয়ে বয়ে যেতে লাগলো, অথচ এমনি স্থানকালের মাহাত্ম্য, যে আমার মৃত্যু হলো না।
বাতাসের বেগও বেড়ে চললো দ্রুতগতিতে। মনে হতে লাগলো, দিগন্তবিসারী মেঘ ফেটে এখনি বুঝি ভলকে ভলকে আগুন বেরোবে।
কাকামণি আর হান্সের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম যে তাদের অবস্থাও আমারই মতো।
ঠিক এমন সময়ে আকাশ ফেটে মুষলধারে নামল বৃষ্টি। ভীষণ বেগে ঝড় এলো। ঝড়ের পাল্লায় পড়ে নৌকোর মুখ ঘুরে গেলো, পাগল হয়ে গেলো যেন সে। কাকামণি আর আমি ভেলার উপর কাত হয়ে পড়ে গেলাম। শুধু হান্স্ কোনমতে হালটিকে শক্ত করে ঘরে বসে রইলো। হাওয়ায় তার চুল উড়তে লাগলো, আর চুলের ডগায় জ্বলতে লাগলো বিদ্যুৎ। ভেলা বিদ্যুতের মতো অজানার উজানে ছুটে চলল।
দোসরা সেপ্টেম্বর, রোববার। আজও তেমনি ভয়ংকর হয়ে আছে ঝড়ের প্রতাপ। ভেলা ঠিক আগের মতোই তীব্রগতিতে ধেয়ে চলেছে। আমরা তিনজনেই নিঃঝুম হয়ে পড়ে আছি ভেলার উপরে। শুধু সকালের দিকে একবার। যেন সম্বিত ফিরে এসেছিলো, বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার নাক আর কান দিয়ে দরদর করে রক্তধারা ছুটছে। তারপর যেন বোধশক্তি পর্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেলো।
তেসরা সেপ্টেম্বর, সোমবার। আজ ঝড় যেন আরো ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। উন্মাদ সমুদ্রের উপর দিয়ে আমাদের ডেলা হু-হু করে ছুটে চলেছে। আমরা তিনজনে কোনোমতে পড়ে আছি ভেলার উপরে। ভেলাটি যে এখনো কেন চুরমার হয়ে যাচ্ছে না, তা বুঝবার ক্ষমতা পর্যন্ত আমাদের নেই। তিনদিন ধরে আহার, নিদ্রা, কথা বলা–সমস্ত বন্ধ। যেন আমরা সবাই মৃত।
এমন সময়ে ঘটলো একটি অপার্থিব ব্যাপার। তার বর্ণনা দিই, এমন শক্তি আমার নেই। দূর থেকে নক্ষত্রবেগে একটা গোল আগুনের গোলা এসে পড়লো আমাদের ভেলার উপর। তারপর যে কী হতে লাগলো, তা যেন ঠিক বুঝতেই পারলাম না। তবে মনে হলো সেই আগুনের বলটার রঙ উজ্জল শাদা, আর তাতে নীল রঙের ঈষৎ আভাস। ভেলার উপরে বলটা তীব্রবেগে ছুটোছুটি করতে লাগলো। মাস্তুল, পাল, ছই–সব উড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে আমরা মৃত্যুর জন্যে তৈরি হয়ে নিলাম। সেই গোল অগ্নিপিণ্ড একবার কাকামণির দিকে এগোয়, আবার কখনো-বা আমার দিকে ছুটে আসে, হঠাৎ আবার হাসের দিকে যায়। সেই ভয়াবহ নীলাভ উজ্জ্বল উত্তপ্ত বলটির দিকে তাকালেও চোখ ঝলসে যায়। আর আশ্চর্য, কী-এক অদৃশ্য অলৌকিক ক্ষমতায় তখন ভেলার উপরকার সমস্ত লোহার জিনিশপত্র পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলো। তারপর হঠাৎ সেই অগ্নিপিণ্ড ভয়ংকর শব্দে ফেটে গেলো। চারদিকে ছুটতে লাগলো আগুনের ফুলকি। উগ্র নাইট্রোজেন গ্যাসে ভরে গেলো চারদিক। দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইলে আমাদের।
একটু সম্বিত ফিরলে পর তাকিয়ে দেখি, সেই অগ্নিপিণ্ড অদৃশ্য হয়েছে। কাকামণি ভেলার উপরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। হান্স্ হিস্টিরিয়া রোগীর মতো মৃত চোখে তাকিয়ে আছে দিগন্তের দিকে।
চৌঠা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। সকাল হতেই দেখা গেলো আকাশে তখন নিবিড় মেঘের অন্ধকার লীলা, তখনো ঝড়ের তেমনি তাণ্ডব। এরই মধ্যে কাকামণি হিশেব করে এক সময়ে চি-চি করে নিস্তেজ গলায় জানালেন যে, আমরা ঠিক জার্মেনির নিচে আছি। একথা শুনে হামবুর্গের কথা মনে পড়লো আমার, মনে পড়লো, আমাদের ছোটো বাড়িটার কথা, মাথার কথা, গ্রোবেনের কথা। আর, ঠিক এমন সময়ে একটা ভয়ংকর শব্দ কানে এলো।
কী হলো বুঝে ওঠার আগেই প্রবলবেগে ভেলা থেকে ছিটকে পড়লাম সমুদ্রের জলে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই হান্স্ জলে লাফিয়ে পড়ে তার সবল বাহুতে আমাকে জড়িয়ে ধরে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে আমাকে ফিরিয়ে আনলো হাসের সেই সুঠাম, সবল চেহারা আমি কখনো ভুলবো না। কিন্তু তারপরে কী ঘটেছিলো, তা আমার মনে নেই। জ্ঞান ফিরে এলে দেখি আমি ডাঙায় শুয়ে আছি। আমার চারিদিকে সকালবেলার অনাবিল আলো।
আমাকে চোখ খুলতে দেখে কাকামণি বললেন, যাক, শেষ অবধি এই নচ্ছার সমুদ্রযাত্রা শেষ হলো। শেষ হলো, তো যেন বাঁচা গেলো। এবার ডাঙার উপর দিয়ে চলব, আর তাও সোজা নিচের দিকে।
বললাম, আচ্ছা কাকামণি, দিনের পর দিন তো এগিয়েই চলেছি; কিন্তু ফিরবো কী করে? আর কবে?
কাকামণি হেসে বললেন, আগে তোত পৌঁছুই, তারপরে কবে ফিরবে। সে-কথা ভাবা যাবে। চল, ভেলার হাল-চাল কীরকম দেখে আসি।
ভেলার কাছে গিয়ে দেখি, অনেক খাবার ভেসে গেছে, বন্দুকগুলো অকেজো হয়ে গেছে, আর ভেলার যা হাল, তাতে মেরামত না করলে জলে ভাসানো চলবে না। খাবার যা আছে তাতে অনায়াসে মাসচারেক চলে যাবে। যন্ত্রপাতির মধ্যে কাকামণি দিকবীক্ষণ যন্ত্রটা (কম্পাস) তুলে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখমুখের ভাব বদলে গেলো। অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতেই নীরবে তিনি কম্পাসটি আমার হাতে তুলে দিলেন। লক্ষ করে দেখি, কী আশ্চর্য, যে দিক দক্ষিণ বলে ভেবেছিলাম, যন্ত্রের কাটা সে দিককে উত্তর বলে নির্দেশ করছে!
বিমূঢ়ভাবে কাকামণি খানিকক্ষণ ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর নিষ্ফল আক্রোশে কাঁপতে লাগলেন শুধু। সামনে না গিয়ে এতদিন তবে আমরা শুধু পিছিয়েই চলেছি! ভাগ্যের এ কী পরিহাস!!
ইতিমধ্যে কাকামণি নিজেকে সামলে নিয়েছেন। নিশ্চিত কণ্ঠে তিনি বললেন, আবার তবে নতুন করে রওনা হবো আমরা।
আমি থ হয়ে গেলাম। কাকামণি তবে কোনোমতেই হাল ছাড়বেন না।
কাকামণি কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে হাসকে নির্দেশ দিলেন ভেলাটি খুব শিগগির মেরামত করে ফেলবার জন্য, তারপর আমায় বললেন, আয় একবার দ্বীপটা ঘুরে আসা যাক।
প্রতিবাদ করবার কোনো চেষ্টা করলাম না আমি। জানতাম নিষ্ফল হবে। নীরবে কাকামণির সঙ্গে দ্বীপ-ভ্রমণে বেরোলাম। সামনেই একটা ছোটো টিলা পড়লো। টিলাট ছাড়িয়ে একটা ঢালু জায়গা। সেখানে রাশি রাশি সামুদ্রিক জন্তুর কঙ্কাল। যতোই এগোতে লাগলাম, ততোই এই কঙ্কালের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। এদের বিবর্ণ ধূলি-ধুসর অবস্থা দেখে বোঝা গেলো, বহু সহস্র বছর ধরে এরা পড়ে আছে। কাকামণি এক পা চলেন, তারপর থামেন, হেঁট হয়ে সেইসব কঙ্কাল পরীক্ষা করেন, আর বিস্ময়ে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার চোখ মুখ। মাঝে-মাঝে এই কারণে তিনি আমার পিছনে পড়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার বিহ্বল চিৎকার শুনে কাছে ছুটে গিয়ে দেখি, দুহাতের চেটোর উপর একটা মানুষের মাথার খুলি নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।
এ যে মানুষের মাথার খুলি।
অনেকক্ষণ আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না।
বৈজ্ঞানিকদের মত যাই হোক না কেন, স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম যে, কোটিকোটি বছর আগে হাতি গণ্ডার বা অন্য কোনো ভূচর প্রাণীর সৃষ্টির আগেই মানুষ জন্ম নিয়েছিলো। খানিকক্ষণ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে আবার কাকামণি এগোতে লাগলেন। আমিও নীরবে তাকে অনুসরণ করলাম। এইমাত্র নিজের চোখে যা দেখলাম, তা যেন আমার নিজেরই বিশ্বাস হতে চাইছিলো না। এরপর পথে অসংখ্য নরকঙ্কাল দেখতে পেলাম। পণ্ড কঙ্কালও। চারদিকেই যেন। মৃত্যু সদাজাগ্রত প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে—এমনি দেখাতে লাগলো সেই কঙ্কালময় শ্মশানভূমিকে।
দুমাইল চলবার পর এক বিশাল ধন-সন্নদ্ধ অরণ্যের কাছে এসে দাঁড়ালাম। গাছপালা যে এতো বড়ো, এতে সতেজ হতে পারে, সে ধারণা ছিলো না। পাইন, বার্চ, সাইপ্রেস, ফার, ওক প্রভৃতি আকাশ-ছোঁয়া নানান জাতের গাছের সমারোহ। তবে একটা জিনিশ দেখলাম যে, গাছগুলি সমস্তই বিবর্ণ। বুঝতে পারলাম, সূর্যালোকের অভাবই এর প্রচ্ছন্ন কারণ।
কাকামণি নির্ভয়ে অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। বাধ্য হয়ে আমিও তাকে পায়ে-পায়ে অনুসরণ করলাম। আর খানিকক্ষণ চলার পর যা চোখে পড়লো, তা দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম আমি। তাড়াতাড়ি থমকে দাঁড়িয়ে গতিরোধ করলাম কাকামণির। উজ্জল বিদ্যুতালোকে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো।
দেখা যাচ্ছিলো যে, অরণ্যের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অতিকায় সব মূর্তি ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই অতিকায় জন্তুগুলো আর কিছুই নয়,-হাতি আঠারোশো এক সালে ওডিও শহরে ভূগর্ত থেকে যে জাতের হাতির বিরাট একটি কঙ্কাল সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো, এই হাতিগুলোও সেই অধুনালুপ্ত আদিম পৃথিবীর হাতির দলের।
আমার জন্যে কিন্তু আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিলো। স্তম্ভিত বিস্ময়ে নিষ্পলক চোখে হাতিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময়ে কাকামণি অরণ্যের এক-প্রান্তের দিকে তর্জনী নির্দেশ করলেন। নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না। কোনো সুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তি এ-কথা কল্পনায় আনতে পারে না। দেখতে পেলাম, একটি আকাশ-ছোঁয়া ওক গাছের নিচে একটি জীবন্ত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে দানবের মতে, লম্বায়চওড়ায় আমাদের চারগুণ হবে, হাতে তার রীতিমতো বড়োসড়ো একটি গাছ। বুঝতে পারলাম, সে হাতিগুলোর রাখাল। মাথায় তার এলোমেলো বড়ো-বড়ো চুল, মাথাটি দেখতে অনেকটা মহিষের মতো, মুখের ভাব যেন কোনো বনমানুষের।
ভয়ে বিস্ময়ে আমার গলা শুকিয়ে গেলো। ছবির মতো পঁড়িয়ে রইলাম আমি হতবাক হয়ে। আর, ঠিক এমন সময়ে কাকামণি আমার হাতে চাপ দিয়ে ফিসফিশিয়ে বললেন : শিগগির, এখুনি আমাদের পালাতে হবে।
তারপর সে কী ছোটা! এক নিশ্বাসেই যেন ভেলার কাছে এসে পৌঁছলাম আমরা। হা–যে হানস কখনও অবাক হয় না-সে পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। তখনো আমাদের কথা বলবার শক্তি ফিরে আসেনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাফাচ্ছিলাম আমরা। এইমাত্র যা দেখে এলাম, তা কি সত্যি, না আমাদের বিকৃত কল্পনা? সত্যিই কি পৃথিবীর অনেক নিচে যে আরেক পৃথিবী, সেখানে এখনো আদিম যুগের মানুষদের বাস?
অনেকক্ষণ পর যখন একটু সুস্থ হলাম, তখন কাকামণি হিশেব করে জানালেন যে, পোর্ট গ্লোবেন থেকে আমরা বেশি দূরে নেই। কেননা ঝড়ের জন্যে আমরা দিক ভুল করে আবার সেই আগের দ্বীপেই ফিরে এসেছি।
এবার তাই হাসকে নিয়ে আমরা অন্য দিকে হেঁটে চললাম। যে করেই হোক, পোর্ট গ্লোবেন খুঁজে বার করতে হবে।
অল্পক্ষণ চলবার পর বেলাভূমির উপরে কী একটা চকচকে জিনিশ দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নিলাম। দেখি, একটি ছোরা, তার কোনো-কোনো স্থানে মরচে পড়ে গেছে। কাকামণিকে দেখাতে তিনি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে বললেন : কোত্থেকে এলো এটা? আমরা তো এদিকে আগে আসিনি। এরকম ছোরাও তো আমাদের নেই। ছোরাটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন কাকামণি। শেষে বললেন : না, এ আমাদের ছোরা নয়। এর গড়ন দেখে বোঝা যাচ্ছে এ অনেক দিন আগেকার ছোরা। আর যতদিন আগেকারই হোক না কেন, এ তো আর নিজে থেকে এখানে আসেনি, একজন কেউ নিয়ে
এসেছিল নিশ্চয়ই।
কিন্তু কে সেই ব্যক্তি? শুধোলাম আমি।
ছোরার ডগাটা কী রকম অসমানভাবে ক্ষয়ে গেছে, দেখেছিস? ঠিক মনে হয়। কেউ এটা দিয়ে পাথরের উপরে নিজের নাম খোদাই করে গেছে। এখন সেইটেই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।
কাকামণির কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে চারদিকের পাথরের গা পরীক্ষা করতে করতে চললাম। ঘণ্টাখানেক পরে সমুদ্র-সৈকতে একটা পাথরের উপরে দেখলাম দুটি অদ্ভুত ধরনের হরফ খোদাই করা রয়েছে। সেই অক্ষর-দুটো দেখে কাকামণি চেঁচিয়ে উঠলেন, এ, এস! তার মানে, আর সাউজ!
বলা বাহুল্য, খোদিত হরফ-দুটো রুনিক। আর যে পাথরটার উপরে তা খোদাই করা, তার পাশেই রয়েছে একটা সুড়ঙ্গপথ।
১২. জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে
আমাদের এই অবিস্মরণীয় ভ্রমণ যেদিন থেকে শুরু হয়েছে সেদিন থেকে অবাক হওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। কারণ, পাতালে প্রবেশ করবার পর থেকে এভোব আশ্চর্য ব্যাপার দেখে আসছি যে, ভেবেছিলাম আমাকে স্তম্ভিত করতে পারে এমন বোধহয় আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিন্তু যখন দেখলাম এই গভীর পাতালে, এই অন্য পৃথিবীতেও আর সাক্ন্যুউজম বিরাজ করছেন, তখন একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম। যে-ছোরাটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ মাথা ঘামাচ্ছিলাম, সেটি যে তারই তা স্পষ্টই বোঝা গেলো, কেননা পাথর কেটে নাম লেখবার দরুন এর ফলা স্থানে-স্থানে ভেঙে গিয়েছিলো।
সঙ্গে-সঙ্গে ভেলায় ফিরে গেলাম আমরা। ভেলাটা তাড়াতাড়ি মেরামত করে ঘণ্টাখানেক পরে সেখানটায় আবার ফিরে এলাম। বাতাস অনুকূল না থাকলে হয়তো আরো দেরি হতো। তেলাটা ঐ সুড়ঙ্গের কাছে নিয়ে আসবার কারণ হলো, একবার ঐ সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকে কী কী জিনিশ সুড়ঙ্গ-অভিযানে দরকার হতে পারে তা সঙ্গে নিয়ে বাকি সবকিছু ভেলায় রেখে যাওয়া যেতে পারে।
তখনি টর্চ জ্বেলে সেই অজানা সুড়ঙ্গের অন্ধকারে পদার্পণ করলাম। কাকামণি আর হান্স্, এবার আমার পিছনে পড়লেন, স্যামউজমের নাম আমার মনে এবার সত্যি সত্যি উদ্দীপার মশাল জ্বেলে দিয়েছিলো। কাকামণির হিশেবমতো তখনো পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছুতে সাড়ে চার হাজার মাইল বাকি ছিলো। সেটুকুই বা আর বাকি থাকে কেন? একেবারে শেষ দেখে যাওয়াই ভালো। এবং সেই শেষের পথ যে এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়েই এগিয়েছে, তা সুড়ঙ্গের বাইরে ঐ নাম খোদাই দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম।
সুড়ঙ্গের পথ চওড়ায় হাত-চারেক হবে,-দুধারে সুদৃঢ় পাথরের দেয়াল। একটু এগোতে-না-এগোতেই আমার মাথায় যেন বাজ পড়ল। দেখতে পেলাম, সুড়ঙ্গ-পথের মুখ বন্ধ করে একটি বিরাট পাথর সামনে পড়ে আছে। সে পাথর সরানো মানুষের পক্ষে অসম্ভব।
হতাশ হয়ে আমরা সেই সুড়ঙ্গের মেঝেয় বসে পড়লাম।
সাক্ন্যুউজম্ নিশ্চয়ই এখান থেকে ফিরে যাননি। পাতালে তিনি শেষাবধি নিশ্চয়ই পৌঁছেছিলেন, আর পৌঁছেছিলেন এই সুড়ঙ্গপথ ধরে এগিয়েই। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পরে বোধহয় কোনো ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাতে পাথর পড়ে এই পথ বন্ধ হয়ে গেছে।
অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ আমার চোখে আশার আলো বিকিয়ে উঠলো। বললাম : কাকামণি, বারুদ দিয়ে এই পাথরটা উড়িয়ে দিলে হয় না?
সঙ্গে-সঙ্গে উল্লসিত হয়ে উঠলেন কাকামণি : ঠিক বলেছিস!
তখনি বারুদ ঢালবার জন্য গর্ত খুঁড়তে শুরু করে দিলাম। পঁচিশ সের বারুদে আগুন দেবার ব্যবস্থা করতে অনেক সময় লাগলো। নাইট্রিক অ্যাসিড আর সালফিউরিক অ্যাসিডে তুলো ভিজিয়ে বারুদ তৈরি করেছিলাম আমরা। সাধারণ বারুদের চেয়ে এই বারুদের শক্তি অনেক বেশি। হান্স্ গর্ত করতে লাগলো। আমি আর কাকামণি বারুদে আগুন দেবার জন্যে লম্বা শলতে তৈরি করতে লাগলাম। ক্রমে রাত্রি হয়ে এলো। তারপর যখন সকল আয়োজন শেষ করে বারুদ দিয়ে গর্ত ভরাট করে শলতের এক প্রান্ত বারুদের মধ্যে রেখে অন্য প্রান্ত সুড়ঙ্গের বাইরে আনলাম, তখন কাকামণি বললেন : আজ আর কাজ নেই, কাল দিনের আলোয় শলতে আগুন দেয়া যাবে।
পরদিন সকালবেলা ছটার সময় আমরা তৈরি হয়ে সুড়ঙ্গের মুখে এসে দাঁড়ালাম, কাকামণিকে বলেকয়ে শলতেয় আগুন দেবার ভারটা আমিই নিলাম। কাকামণি আমাকে বারবার সতর্ক করে দিলেন : সাবধান, এক সেকেণ্ডও যেন দেরি না হয়, আগুন দিয়েই প্রাণপণে দৌড়ে এসে ভেলায় উঠবি! তুই ভেলায় এলেই আমরা সমুদ্রের মধ্যে ভেলা ঠেলে দেবে। পাহাড় যে কততখানি ধ্বসে যাবে, কে জানে! শলতের আগুন বারুদের কাছে যেতে লাগবে প্রায় দশ মিনিট। এর মধ্যেই আমাদের নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে হবে।
আমাকে এইভাবে বারবার বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হাসকে নিয়ে কাকামণি ভেলায় গিয়ে উঠলেন। ভেলাকে সমুদ্রপথে ঠেলে দেবার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়ালেন ওঁরা। একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে আমি শলতের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর একহাতে লণ্ঠন ধরে অন্য হাতে শলতের আগা ধরলাম। একবার হাত কাঁপলো। কাকামণি হাঁকলেন : হুঁশিয়ার! দাও আগুন!
তক্ষুনি শলতেয় আগুন দিলাম। দপ করে জ্বলে উঠলো শলতোট, তীব্রবেগে অগ্নিশিখা অগ্রসর হল সুড়ঙ্গের দিকে। আমিও বিদ্বেগে ভেলায় এসে উঠলাম। সঙ্গে-সঙ্গে কাকামণি আর হস, কোনোরকমে ভেলাটিকে তীর থেকে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে সরিয়ে নিলেন। আর, ঠিক তখনি–
ঠিক তখনি আকাশ-পাতাল কেঁপে উঠলো। বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম কি না মনে নেই, শুধু এইটুকুই মনে আছে যে, যেখানে পাথর ছিলো, পলকের মধ্যেই সেখানে একটি অতল গহ্বর দেখা দিল। সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে ফুশে উঠলো। যে সাংঘাতিক ধাক্কায় আমরা তিনজনেই ভেলার উপরে ছিটকে পড়লাম, আর নিবিড় অন্ধকার এসে আমাকে ঢেকে ফেলবার আগে শুধু এটুকুই বুঝতে পারলাম যে, আমরা নিচের দিকে নামছি।
সম্বিত যখন ফিরলো, তখন বুঝতে পারলাম যে ঐ বিপুল পাথরটার ওপাশে ছিলো একটি অতল গহ্বর। বিস্ফোরণের ফলে পাথরটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলে বিপুল একটি আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং সেই কারণেই সমুদ্রের জল প্রবল একটি জলপ্রপাতের মতো সেই গহ্বরটির ভিতর প্রবেশ করতে থাকে। স্রোতের সেই প্রবল আকর্ষণ আমাদের ভেলাটিকেও রেহাই দেয়নি। জলস্রোতের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের ভেলাও গহ্বরের ভিতর দিয়ে নামতে শুরু করে দিয়েছে। এবার যে আর বাঁচোয়া নেই, সে-কথা বুঝতে পেরে ভয়ে চোখ বুজে রইলাম। দুপাশের পাথরের গায়ে ঘা লাগলে ভেলার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও নিঃসন্দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবো।
প্রচণ্ড বেগে পাতালে নামতে লাগলাম। আশ্চর্য যে, একবারো পাথরের দেয়ালের সঙ্গে ভেলার সংঘর্ষ বাংলো না। বুঝলাম যে, গহ্বরের বিস্তার বিরাট বলেই এমন কোনো সংঘর্ষ ঘটলো না। স্যামুউজমের পাতালের পথে আমাদের দুবুদ্ধি একটি তীব্র জলস্রোতকে আমাদের অদৃষ্টের সঙ্গে গেঁথে নিয়ে এলো! যেরকম প্রবল বেগে হাওয়া আমাদের ঝাপটা মারছিলো, তাতে বুঝতে পারছিলাম যে দ্রুততম যানের চেয়েও অনেক বেশি দ্রুতগতিতে আমরা পাতালের দিকে নামছি। টর্চটা ভেঙে গিয়েছিলো বলে গহ্বরটা পরীক্ষা করতে পারছিলাম না অন্ধকারে।
কতোক্ষণ ধরে যে নেমেছিলাম, আজকে তা আমি সঠিক বলতে পারবো না, তবে এ-কথা মনে আছে যে, অনেক-অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেয়ে ভেলাটা থেমে গেলো, তারপর একটা জলধারা তীব্রবেগে আমাদের উপর পড়তে লাগলো। বোধহয় মিনিটখানেক পড়েছিলো সেই জলধারা, তারপরেই আবার ভেলাটা চলতে শুরু করে দিলে। এবার কিন্তু জলের গর্জন আর শোনা গেলো না।
এমন সময় কাকামণি আমাকে ডেকে বললেন : অ্যাকজেল, আমরা কিন্তু নামছি না, উপরে উঠছি।
বিস্মিত হয়ে শুধোলাম : উপরে উঠছি। কোথায়? কী করে?
কী করে জানি নে, কিন্তু সত্যিই উপরে উঠছি। বললেন কাকামণি। কোনোমতে যদি একটা আলো জ্বালা যায়, তবেই ভালো করে বোঝা যাবে,
একটামাত্র টর্চলাইটই তখন সম্বল ছিলো ভেলায়। হান্স্ অনেক চেষ্টা করে হাতড়ে হাতড়ে সেটা বার করে জ্বাললে। একটুখানি আলো অনেকখানি আশা আনলে মনে।
কাকামণি বললেন : যা ভেবেছিলাম! জলে গহ্বরের তলা ভরে যাওয়ায় জল এবারে অন্য পথ দিয়ে উপরে উঠছে, আমরাও সেই জলের সঙ্গে-সঙ্গে উপরে উঠছি। কিন্তু হুঁশিয়ার, প্রতি মুহুর্তেই একটা-না-একটা বিপদ আসতে পারে। এখন বোধহয় আমরা ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে উঠছি। যদি এইভাবে উঠতে থাকি–
আর যদি এই সুড়ঙ্গের একটা বহির্মুখ থাকে–
তাহলে ভালোই হয়। কিন্তু না থাকলে পাথরে ঘা লেগে চূর্ণ হয়ে যাবো, বললেন কাকামণি। কিন্তু সে তো আরো খানিকক্ষণ পরের ব্যাপার। এখন তো খেয়ে নিই কিছু!
এতোক্ষণ খবরটা চেপে রেখেছিলাম, কিন্তু এবার খুলে বলতে হলো। আগেই আমি লক্ষ্য করে দেখেছিলাম, ভেলায় কোনো বাবার নেই, সব জ্বলে ছিটকে পড়ে গেছে। খুঁজে পেতে দু-এক টুকরো শুকনো মাংস পাওয়া যেতে পারে হয়তো।
এই কথা শুনে শূন্য চোখে আমার নিকে তাকালেন কাকামণি।
যেমন বেগে উঠছিলাম, তেমনি উঠতে লাগলাম। ক্রমশ যেন উত্তাপ বাড়ছে বলে মনে হলো। হঠাৎ এমনটা কেন হলো বুঝতে পারছিলাম না। এতোদিন তো পাতালে কেটেছে, তবু কখনো এতে উত্তাপ দেখিনি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে উত্তাপ ভয়ানক বেড়ে গেলো। আমি শুধু কাকামণিকে একবার বললাম : নেহাৎ যদি ড়ুবে না মরি, পাথরের সঙ্গেও যদি ঘা না খাই, খিদের হাত থেকেও যদি রেহাই পেয়ে যাই,—তবু বাঁচবো বলে তো আশা হচ্ছে না। হয়তোবা পুড়েই মরতে হবে আমাদের।
কাকামণির চোখে-মুখে এই প্রথমবার ভয়ের চিহ্ন দেখলাম। কোনো কথা বললেন না তিনি, শুধু তার ঠোঁটদুটো একবার কাঁপলো।
আরো এক ঘণ্টা কাটলো। উত্তাপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তারপর হঠাৎ হু-হু করে আরো বেড়ে গেলো অনেকখানি। সঙ্গে সঙ্গে ভেলার গতিও যেন অনেকখানি বেড়ে গেল। ভেলার চারপাশে টগবগ করে জল ফুটতে লাগলো। উত্তাপ ক্রমশ সহাতীত হয়ে উঠলো। দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইলে আমার। গন্ধকের উগ্র গন্ধে ভরে উঠলো চারপাশ। আগুনের চেয়েও গরম যেন গহ্বরটি! কাকামণির দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার ভুরু কুঁচকে গেছে, কপালে পড়েছে চিন্তার রেখা। বুঝলাম, সাংঘাতিক একটি অনর্থ আসন্ন।
আর তার প্রমাণও পেলাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। মশালের ক্ষীণ, চঞ্চল আলোয় দেখলাম, দেয়াল ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, আর সেই ফাটল থেকে বেরুচ্ছে গ্যাস। আর তখন শুনতে পেলাম একটা গুরু-গুরু গর্জন।
ঠিক সেই মুহূর্তে বিবর্ণ, নিরুত্তাপ একটি হাসি ফুটলে কাকামণির ঠোটে। বললেন : সুড়ঙ্গপথে অগ্ন্যুদ্গার শুরু হয়েছে, অ্যাকজেল, এ-সব তারই অগ্রদূত। আগ্নেয়গিরির উদগার আমাদের ঠেলে উপরের দিকে তুলছে।
সর্বনাশ! ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। তাহলে কি আমরা অগ্নিময় তরল ধাতুস্রোতের মধ্যে এসে পড়েছি?
আবার কাকামণির ঠোঁটে সেই প্রাণহীন হাসিটা দেখলাম।
ভয়ংকর তীব্রবেগে উঠছে আমাদের ভেলা। একটি জ্বলন্ত ধাতুস্রোত তাকে ঠেলে তুলছে উপরে। পাথরের দেয়াল তখন একবার ফাটছে, আবার পরমুহূর্তেই জোড়া লাগছে। সবকিছু ছাপিয়ে উঠছে একটা প্রলয়-গর্জনের শব্দ।
এত দ্রুতবেগে আমাদের ভেলা উপরের দিকে উঠছিল যে, আমরা আগুনে ঝলসে যাইনি। ক্রমশ যেন ভেলার গতিবেগ প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর হচ্ছিলো।
তারপর যে কী হয়েছিলো, মনে নেই। জ্ঞান হারিয়ে ফেলার আগের মুহূর্তে শুধু এইটুকুই দেখেছিলাম যে, হানুসের সুগঠিত গ্রীক স্ট্যাচুর মতো দেহ আগুনের লালে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমার মস্তিষ্কের মধ্যে একাকার হয়ে গেলো জীবন আর মৃত্যু, আর তার পরক্ষণেই কে যেন আমাকে কামানের মুখে বেঁধে কামান দাগলো। অমনি আমি মহাশূন্যে উড়ে গেলাম।
১৩. সেই পুরাতন পৃথিবী
জ্ঞান যখন ফিরলো তখন দেখতে পেলাম, হাস, এক হাতে আমাকে, অন্য হাতে কাকামণিকে ধরে রেখেছে, আর আমাদের সামনে পাহাড়টি সোজা নেমে গেছে নিচের দিকে। হা ধরে না রাখলে সেই উঁচু পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে নিশ্চিতই মৃত্যু ঘটতো আমাদের।
অবসন্ন গলায় হান্স্ কে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কোথায়? আইসল্যাণ্ডে? হান্স্ ঘাড় নেড়ে বললে, না।
তবে কোথায়?
হান্স্ কোনো উত্তর দিলে না।
নিজের দেহের পানে তাকিয়ে দেখি, অর্ধনগ্ন দেহ, ধুলো-বালি-কালিতে ভূতের মতো দেখাচ্ছে। একটু দূরে পাঁচশো ফুট উঁচু একটি পর্বতশিখর থেকে পনেরো মিনিট অন্তর প্রচুর ধোঁয়া আর ছাই উঠছিলো তখন। আমাদের পাহাড়টি আর চারপাশের জমিও কাঁপছিলো বেশ।
ভালো করে চারদিকে তাকিয়ে দেখি, নিলীম নীল আকাশে পাজা-পাজা তুলোর মতো শাদা মেঘ, চারদিকে সূর্যের সোনালি। আকাশে, বাতাসে, মাটিতে অপর্যাপ্ত অজস্র আলো। সূর্যের প্রসন্ন আশীর্বাদকে যেন হৃদয়ের গহন প্রদেশে টেনে নিলাম আমি নিশ্বাসের সঙ্গে। কতদিন যে আকাশ দেখিনি!
বুঝতে পারলাম, আবার ফিরে এসেছি পৃথিবীতে। ফিরে এসেছি সেই পুরাতন পৃথিবীর কোনো এক দ্বীপে, যেখানে প্রাণ আছে, আলো আছে, প্রকৃতির সবুজ স্নেহ আছে। কিন্তু জায়গাটির নাম কী হতে পারে তা বুঝতে পারলাম না।
কাকামণি বললেন, কম্পাসের নির্দেশ অনুযায়ী জায়গাটা উত্তরমেরু হওয়া উচিত। কিন্তু তা যে নয়, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু জায়গাটার নাম যাই হোক, এখানে আর থাকা ঠিক হবে না, নিচে নামতে হবে আমাদের, এক্ষুনি।
ঘণ্টা-দুএক বাদে খুব আস্তে-আস্তে হেঁটে আমরা পাহাড়ের নিচে এসে দাঁড়ালাম। পাহাড়ের নিচে অজস্র ফল-মূলের গাছ। বোধহয় কারো বাগান। মালিকের অনুমতি নেবারও তর সইলো না। সেই ফল-মূল পেড়ে প্রাণ ভরে খেলাম আমরা। সামনেই একটা ঝরনা বন-হরিণীর মতো নৃত্যচপল ভঙ্গিতে ছুটে চলছিলো। আকণ্ঠ পান করলাম তার ঠাণ্ডা জল।
জল খেতে-খেতে লক্ষ্য করলাম, অদূরে একটি গাছের আড়াল থেকে একটি কিশোর ছেলে কৌতূহলী চোখে আমাদের দেখছে। ছেলেটি আমাদের দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। ভয় পাওয়ারই কথা। আমাদের তখন যা চেহারা, তাতে ভয় না পাওয়াটাই ছিলো তার পক্ষে অস্বাভাবিক। ছেলেটি প্রাণের ভয়ে দৌড় দেবার উপক্রম করতেই হানস তাকে পাকড়াও করলো।
কাকামণি ছেলেটিকে অনেক আদর করে প্রথমে জার্মান ভাষায় শুধোলন, এ জায়গাটার নাম কী থোক?
কোনো জবাব নেই।
বোঝা গেলো এটা জার্মানির কোনো এলাকা নয়। এবারে কাকামণি ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, জায়গাটার নাম কী বলো তো? ছেলেটি তবুও কোনো উত্তর দিলে না দেখে ইতালীয় ভাষায় কাকামণি একই প্রশ্ন উচ্চারণ করলেন। তবুও সে চুপ করে রইলো।
এবারে কাকামণি চটে-মটে ধমক দিয়ে উঠলেন।
অমনি ছেলেটি রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলো, স্ট্রম্বলি, স্ট্রম্বলি। আর তারপরেই সে কোনোমতে নিজেকে মুক্ত করে পড়ি কি-মরি করে দৌড় দিলো।
আমরা তিনজনেই সমস্বরে বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, স্ট্রম্বলি।
কোথায় আইসল্যাণ্ডের স্নেফেল পর্বত, আর কোথায় সিসিলির এটুনা আগ্নেয়গিরি। একশো কি দু-শো নয়, তিন হাজার মাইলের ব্যবধান! স্তম্ভিত হয়ে এটনার দিকে তাকালাম আমি।
কাকামণি বলে উঠলেন, কম্পাসটা ফেলে দে তো-ওটা আগাগোড়া আমাদের ভুল পথ দেখিয়েছে!
…
মাস-ছয়েক পরে জার্মেনির হামবুর্গের কনিগস্টাসের সেই ছোট্টো বাড়িটায়। অধ্যাপক হের লিডেনব্রকের পড়বার ঘরটা ঝেড়েমুছে সাজাচ্ছিলাম। এমন সময়ে হঠাৎ আমার চোখ পড়লো সেই পুরোনো কম্পাসটার উপর। পাতাল-ভ্রমণের সঙ্গী ছিল বলে ওটাকে আর ফেলে দিইনি। দেখতে পেলাম, কম্পাসের কাটা যাকে দক্ষিণ দিক বলে নির্দেশ করছে, তা আসলে উত্তর দিক।
অবাক হলাম আমি। কাকামণিকে খবর দিতেই তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, সত্যিই কম্পাসের কাটাটা দিক বদল করেছে। যেদিন আমরা এটনার মুখ দিয়ে বেরোই, সেদিনেও কাটাটা আসলে দক্ষিণ মুখেই ছিলো।
কিন্তু কী করে এমনটা হলো? বিস্মিত কণ্ঠে শুধোলাম আমি।
কাকামণি বললেন, পাতালের সমুদ্র পাড়ি দেবার সময় একটা বৈদ্যুতিক বল আমাদের ভেলায় ফেটেছিলো, তোর মনে আছে সে-কথা? সেদিন ভেলার সকল লোহাই চুম্বক হয়ে গিয়েছিলো। কম্পাসের কাটাটাও বাদ যায়নি। সেই থেকেই সব ওলোট-পালোট হয়ে গিয়েছিল। এই বলে হো-হহা করে হেসে উঠলেন তিনি।
আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, অন্তহীন পাতালসমুদ্রে খড়কুটোর মতো ভাসছে আমাদের ছোট্টো ভেলাটি, আর তার উপর ছুটোছুটি করছে শাদানীল একটি গোল অগ্নিচক্র; ঝড়ে সমুদ্র ফুশছে, উদ্দাম হাতে করতালি দিচ্ছে ঝড়।
…
আমি আর কাকামণি বারুদে আগুন দেবার জন্যে লম্বা শলতে তৈরি করতে লাগলাম। ক্রমে রাত্রি হয়ে এলো। তারপর যখন সকল আয়োজন শেষ করে বারুদ দিয়ে গর্ত ভরাট করে শলতের এক প্রান্ত বারুদের মধ্যে রেখে অন্য প্রান্ত সুড়ঙ্গের বাইরে আনলাম, তখন কাকামণি বললেন : আজ আর কাজ নেই, কাল দিনের আলোয় শলতেয় আগুন দেয়া যাবে।
পরদিন সকালবেলা ছটার সময় আমরা তৈরি হয়ে সুড়ঙ্গের মুখে এসে ঈাড়ালাম, কাকামণিকে বলে-কয়ে শলতেয় আগুন দেবার ভারটা আমিই নিলাম। কাকামণি আমাকে বারবার সতর্ক করে দিলেন : সাবধান, এক সেকেণ্ডও যেন দেরি না হয়, আগুন দিয়েই প্রাণপণে দৌড়ে এসে ভেলায় উঠবি! তুই ভেলায় এলেই আমরা সমুদ্রের মধ্যে ভেলা ঠেলে দেবো। পাহাড় যে কতোখানি ধ্বসে যাবে, কে জানে। শলতের আগুন বারুদের কাছে যেতে লাগবে প্রায় দশ মিনিট। এর মধ্যেই আমাদের নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে হবে।
আমাকে এইভাবে বারবার বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হাসকে নিয়ে কাকামণি ভেলায় গিয়ে উঠলেন। ভেলাকে সমুদ্রপথে ঠেলে দেবার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়ালেন ওঁরা। একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে আমি শলতের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর একহাতে লণ্ঠন ধরে অন্য হাতে শলতের আগা ধরলাম। একবার হাত কাঁপলো। কাকামণি হাঁকলেন : হুঁশিয়ার! দাও আগুন!
তক্ষুনি শলতেয় আগুন দিলাম। দপ করে জ্বলে উঠলো শলতেটি, তীব্রবেগে অগ্নিশিখা অগ্রসর হলো সুড়ঙ্গের দিকে। আমিও বিদ্যুদ্বেগে ভেলায় এসে উঠলাম। সঙ্গে-সঙ্গে কাকামণি আর হান্স্, কোনোরকমে ভেলাটিকে তীর থেকে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে সরিয়ে নিলেন। আর, ঠিক তখনি–
ঠিক তখনি আকাশ-পাতাল কেঁপে উঠলো। বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম কি না মনে নেই, শুধু এইটুকুই মনে আছে যে, যেখানে পাথর ছিলো, পলকের মধ্যেই সেখানে একটি অতল গহ্বর দেখা দিল। সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে ফুঁশে উঠলো। যে সাংঘাতিক ধাক্কায় আমরা তিনজনেই ভেলার উপরে ছিটকে পড়লাম, আর নিবিড় অন্ধকার এসে আমাকে ঢেকে ফেলবার আগে শুধু এটুকুই বুঝতে পারলাম যে, আমরা নিচের দিকে নামছি।
সম্বিত যখন ফিরলো, তখন বুঝতে পারলাম যে ঐ বিপুল পাথরটার ওপাশে ছিলো একটি অতল গহ্বর। বিস্ফোরণের ফলে পাথরটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলে বিপুল একটি আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং সেই কারণেই সমুদ্রের জল প্রবল একটি জলপ্রপাতের মতো সেই গহ্বরটির ভিতর প্রবেশ করতে থাকে। স্রোতের সেই প্রবল আকর্ষণ আমাদের ভেলাটিকেও রেহাই দেয়নি। জলস্রোতের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের ভেলাও গহ্বরের ভিতর দিয়ে নামতে শুরু করে দিয়েছে। এবার যে আর বাঁচোয়া নেই, সে-কথা বুঝতে পেরে ভয়ে চোখ বুজে রইলাম। দুপাশের পাথরের গায়ে ঘা লাগলে ভেলার সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও নিঃসন্দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবো।
প্রচণ্ড বেগে পাতালে নামতে লাগলাম। আশ্চর্য যে, একবারো পাথরের দেয়ালের সঙ্গে ভেলার সংঘর্ষ বাধলো না। বুঝলাম যে, গহ্বরের বিস্তার বিরাট বলেই এমন কোনো সংঘর্ষ ঘটলো না। স্যাকৃত্যুউজমের পাতালের পথে আমাদের দুবুদ্ধি একটি তীব্র জলস্রোতকে আমাদের অদৃষ্টের সঙ্গে গেঁথে নিয়ে এলো। যেরকম প্রবল বেগে হাওয়া আমাদের ঝাপটা মারছিলো, তাতে বুঝতে পারছিলাম যে দ্রুততম যানের চেয়েও অনেক বেশি দ্রুতগতিতে আমরা পাতালের দিকে নামছি। টর্চটা ভেঙে গিয়েছিলো বলে গহ্বরটা পরীক্ষা করতে পারছিলাম না অন্ধকারে।
কততক্ষণ ধরে যে নেমেছিলাম, আজকে তা আমি সঠিক বলতে পারবো না, তবে এ-কথা মনে আছে যে, অনেক অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেয়ে ভেলাটা থেমে গেলো, তারপর একটা জলধারা তীব্রবেগে আমাদের উপর পড়তে লাগলো। বোধহয় মিনিটখানেক পড়েছিলো সেই জলধারা,–তারপরেই আবার ভেলাটা চলতে শুরু করে দিলে। এবার কিন্তু জলের গর্জন আর শোনা গেলো না।
এমন সময় কাকামণি আমাকে ডেকে বললেন : অ্যাকজেল, আমরা কিন্তু নামছি না, উপরে উঠছি।
বিস্মিত হয়ে শুধোলাম : উপরে উঠছি। কোথায়? কী করে?
কী করে জানি নে, কিন্তু সত্যিই উপরে উঠছি। বললেন কাকামণি। কোনোমতে যদি একটা আলো জ্বালা যায়, তবেই ভালো করে বোঝা যাবে।
একটামাত্র টর্চলাইটই তখন সম্বল ছিলে ভেলায়! হান্স্ অনেক চেষ্টা করে হাতড়ে হাতড়ে সেটা বার করে জ্বাললে। একটুখানি আলো অনেকখানি আশা আনলে মনে।
কাকামণি বললেন : যা ভেবেছিলাম! জলে গহ্বরের তলা ভরে যাওয়ায় জল এবারে অন্য পথ দিয়ে উপরে উঠছে, আমরাও সেই জলের সঙ্গে-সঙ্গে উপরে উঠে এলাম।