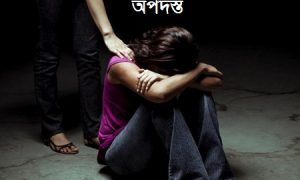এখন যেমন কথায় কথায় ফ্রিজের বরফ, কথায় কথায় বোতলে ভরা সফট ড্রিংক– বছর চল্লিশেক আগেও মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে সেটা ছিল শুধুই কল্পনা। তবে সফট ড্রিংক যে বাজারে ছিল না তা নয়। কিন্তু তার উপস্থিতি ছিল বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানকে ঘিরে। তখন গরমকালে গরম পড়ত খুবই জেঁকে আর বাড়িগুলোয় ডিসি লাইন থাকায় সারাদিন খেপে খেপে লোডশেডিং হত। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত বিভিন্ন সময় নানান অনুষঙ্গে আমাদের বাড়িতে নানারকম পানা বা শরবত খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। সেগুলো বেশিরভাগই বানাতেন আমার চার জ্যাঠাইমা এবং আমার মা। তবে কখনো কখনো নতুনজ্যাঠা বা ছোড়দাকেও শরবত বানাতে দেখতাম।
সকালে বাজার থেকে তেতেপুড়ে ফিরে বিরাট হাঁড়িওয়ালা ঊষা বা ক্রম্পটন গ্রিভস কোম্পানির সিলিং পাখার মিঠে হাওয়ার নিচে বসতেন জ্যাঠারা। পাঞ্জাবি খুলে হাফ-হাতা গেঞ্জি গায়ে যখন ঘাম শুকোতে বসতেন, তখন তাঁদের হাতে যে বিশেষ শরবতটি তুলে দেওয়া হত তা পাতিলেবুর সঙ্গে হয় বড়দানার চিনি আর তা নইলে গুড়ের বাতাসা ঘুঁটে বানানো। নামমাত্র বিটনুন মিশিয়ে দেওয়া হত তাতে । আর বরফ জলের বদলে দেওয়া হত রান্নাঘরের বিরাট দুটি মাটির লাল জালার স্নিগ্ধ ঠান্ডা জল। গরমকালে দেখতাম, তাদের গায়ে পরিষ্কার ভিজে গামছা জড়ানো থাকত। এই শরবতটি সবচেয়ে সুন্দর বানাতেন আমার সেজজ্যাঠাইমা। উনি বানালে কাচ বা পাথরের লম্বাটে গ্লাসের নিচে কোনো চিনি বা বাতাসার টুকরো পড়ে থাকত না এবং পানার ওপরের জলতলেও ভেসে থাকত না কোনো অবাঞ্ছিত পাতিলেবুর দানা। পাতিলেবুর জায়গায় গন্ধলেবুর রস পড়লে এর রোম্যান্টিকতা যেন আরও একটু বেড়ে যেত।
পানা শব্দটার মানে আসলে টক-মিষ্টি পানীয় বা এককথায় শরবত। তবু ঘরোয়া কথায় বাতাসার পানা আর নুন-চিনির শরবত শুনতেই আমরা বেশি অভ্যস্ত। যাইহোক, রোদ্দুর থেকে এলে তেষ্টা যে খুবই পাবে এত জানা কথা। কিন্তু তাই বলে আমি জ্যাঠাদের কোনোদিনও হাঁ হাঁ করে সব শরবতটুকু এক নিঃশ্বাসে গিলে ফেলতে দেখিনি। ওঁরা ওটা খেতেন ছোটো ছোটো চুমুকে। খেতে খেতে সবার সঙ্গে বাজারের হাল-হাকিকত নিয়ে টুকটাক আলোচনা করতেন। সেদিন যে মাছ বা সবজিটি ভালো পেয়েছেন, তা কেন ভালো– তাও বলতেন হাসিমুখে। এমন সময় যদি কখনো লোডশেডিং হত, তবে যিনি শরবতটি পৌঁছে দিতে এসেছেন, গ্লাসটি ধরিয়ে দেওয়ার পর, দেখতাম তালপাতার হাতপাখা দিয়ে তাঁকে হাওয়া করছেন। কিন্তু লোডশেডিং বলে তাঁদের মুখে কোনো বিরক্তি দেখেছি– এমনটা আমার স্মৃতিতে নেই। যেকোনো পরিবেশেই তাঁরা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারতেন। আর সেইজন্যেই এই পৃথিবীর বুকে তাঁদের বেঁচে থাকাটা যথেষ্ট সুখের ছিল।
মা-জ্যাঠাইমাদের কোনো পালা-পার্বণ থাকলে তাঁরা তো সারাদিন ফল-মিষ্টি খেয়েই কাটাতেন আর সঙ্গে থাকত সাবুভিজে বা ডালভিজে। সাবুভিজের সঙ্গে চিনি আর সোনামুগডাল ভিজের সঙ্গে সামান্য নুন মিশিয়ে খেতে দেখতাম। বলা বাহুল্য আমার কাছে এই দুটি পদ ছিল পরমলোভনীয়। এগুলো খাওয়ার আগে তাঁরা সদ্য পুজো সেরে উঠে একটি শরবত খেতেন। এই শরবতটি কখনো ছিল টক দইয়ের ঘোল, কখনো মৌরি, মিছরি, লেবু আবার কখনো ছিল যবের ছাতু, আখের গুড়, পাতিলেবু এবং এক চিমটে বিটনুন দিয়ে বানানো সামান্য ঘন একটি শরবত, যা খেলে পেট অনেকটাই ভরে যেত। এই শেষের শরবতটি আমার ন’জ্যাঠাইমা ভারি সুন্দর বানাতেন। এই শরবতগুলো সবই পরিবেশন করা হত বেনারস থেকে আনা দুধের মতো সাদা পাথরের গেলাসে।
গরমকালে দুপুরবেলায় ভাতটাত খেয়ে হয় লুডো, আর তা নইলে দাবা। কারোর কাছ থেকে বিশেষ পাত্তা না পেলে তখন গল্পের বই। এই সময় মন যে শরবতগুলির জন্যে অধীর অপেক্ষা করে থাকত তার প্রথমেই মনে পড়ে তরমুজের শরবতের কথা। আমাদের যৌথ পরিবারের সবার জন্যে তরমুজের শরবত করার জন্যে বিরাট বিরাট দু’খানা সাগুরে তরমুজ কাটতে হত। এখন বাজারে যেমন লম্বাটে তরমুজের ছড়াছড়ি, আমাদের ছোটোবেলায় কিন্তু তা ছিল না। তরমুজ মানে আমরা জানতাম গোলালো। আর সেটার পেট কাটলেই টুকটুকে লাল। তরমুজের শাঁস ভালো করে ছাড়িয়ে, তাকে নিংড়ে রস বার করে, ছেঁকে, তার সঙ্গে সামান্য বিটনুন মিশিয়ে অসামান্য একটি শরবত তৈরি করা হত, যা খুবই ভালো বানাতেন আমার
বড় জ্যাঠাইমা। এই শরবতটির শোভা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পেত যদি তা কাচের স্বচ্ছ গেলাসে করে পরিবেশন করা হত। এই শরবতটি বানানোর ক্ষেত্রেও প্রাথমিক শর্ত ছিল শরবতের ওপর তরমুজের দানা ভেসে না থাকা। ছোটোদের পত্রিকা ‘শুকতারা’য় ছবিতে গল্প বাঁটুল-দি-গ্রেট পড়তে গিয়ে জেনেছিলাম, লেবুর তৈরি শরবতের ভালোনাম যেমন লেমোনেড, তেমনি তরমুজের শরবতের নাম নাকি ‘তরমুনেড’। বলা বাহুল্য, এমন আশ্চর্য নামকরণ কেবল নারায়ণ দেবনাথের পক্ষেই বোধহয় সম্ভব ছিল। ছোটো বলে স্টিলের গ্লাসে করে দেওয়া সেই ‘তরমুনেড’ এর মধ্যে, স্কুলের ওয়াটার বটল থেকে খুলে নেওয়া একটি হার্ড প্লাস্টিকের স্ট্র ডুবিয়ে আস্তে আস্তে টান দেওয়ার সময় নিজেকে মনে মনে যেন হুবহু বাঁটুল দি গ্রেট বলেই মনে হত।
দুপুরবেলায় খাওয়া তেঁতুলজল, আখেরগুড় আর জিরে ভাজার গুঁড়ো দিয়ে বানানো একটি অসামান্য শরবত আজও আমার মুখে লেগে আছে, যা বেশিরভাগ বানাতেন আমার মা। এই শরবতটির রং ছিল ফিকে নস্যি। বাজার থেকে গোটা জিরে কিনে এনে তাকে শুকনো চাটুতে অনেকক্ষণ ধরে নেড়েচেড়ে মচমচে করে নেওয়া হত। ওপরের জলতলে জিরেভাজার গুঁড়োগুলো একজোট হয়ে ভেসে থাকত। চুমুকের পর জিভে করে চাপ দিলে মুড়মুড় গোছের একটা মৃদু শব্দ অন্তর থেকে অনুভবও করা যেত। একফোঁটা তেল ব্যবহার না করলেও সেঁকার এই প্রণালীটিকে কেন জিরে ‘ভাজা’ বলে, ছেলেবেলায় এটাও আমার একটা প্রশ্ন ছিল। এতে উত্তর পেয়েছিলাম, সেঁকা বেশি মাত্রায় হওয়ার ফলে সেঁকা জিনিসটি যেমন ভাজা-ভাজা হয়ে যায়, এটা সেইরকম ভাজা। রোদে বেশিক্ষণ থাকলে গায়ের চামড়াটাও তো ভাজাভাজা হয়ে যায়, তাতে কি তেল লাগে!
তেঁতুলজল না দিয়ে শুধু জিরেভাজার গুঁড়ো আর বিটনুন দিয়েও একটা শরবত হত, যা বাঙালি জীবনে জলজিরার শরবত নামে বিশেষ পরিচিতি। আর একটি শরবত তৈরি করা হত টাটকা পুদিনাপাতা বেটে তার রসের সঙ্গে চিনি, বিটনুন এবং লেবুররস মিশিয়ে। পুদিনাপাতার নিজস্ব একটা সুন্দর গন্ধ আছে, যার জন্যে এর সামান্য থেঁতো করা একটি-দুটি পাতাকে, লেবুচিনির শরবতের ওপরে লেবুপাতা ভাসানোর মতোই কখনো-সখনো ভাসিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু শান্তিনেকেতনে শ্রদ্ধেয়া কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে যে লেবুর শরবতটি আমি গ্রহণ করেছিলাম, তার ওপরে কিন্তু লেবুপাতাই ভাসানো ছিল– পুদিনাপাতা নয়।
আগে বিয়েবাড়িতে অতিথি আপ্যায়নের জন্যে আমপোড়ার শরবত ছিল একচেটিয়া। আমার জারতুতো দিদির বিয়ের সন্ধেটি আমার তাই এখনও পরিষ্কার মনে আছে। বাড়িতে বানানোর সময় সাবেক রান্নাঘরের মাটির তৈরি ডবল উনুনে, দুপুরের রান্না শেষ হলে সেই ঢিমি আঁচে, উনুনের সামনের দরজা দিয়ে গোটাকতক কাঁচাআম পুরে দেওয়া হত। এরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে পুড়ে কালচে হয়ে এলে, সাবধানে বাইরে বের করে এনে খোসা ছাড়িয়ে, চটকে, সামান্য নুন, চিনি আর জিরেভাজার গুঁড়োর সঙ্গে বরফকুচি মিশিয়ে পরিবেশন করা হত। এই কাজটা খুব উৎসাহ নিয়ে করত আমার ছোড়দা।
সেই ফ্রিজবিহীন যুগে বরফের জন্যে ভরসা করা হত বাজারের বরফের দোকানগুলোর ওপর। তখন যদুবাজারের পিছনে মোহিনীমোহন রোডে আর কালীঘাট বাজারের মধ্যে দুটি বরফের সাবেক দোকান ছিল। বড় স্ল্যাব থেকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে, সেই কাঠের গুঁড়োয় মাখামাখি বরফ ওজন করে তুলে দেওয়া হত বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া বাজারের ব্যাগে। মনে আছে, নতুনজ্যাঠার সঙ্গে এমনই একবার বরফ কিনে যদুবাজারের পিছন থেকে ফিরছি, আর উনি একহাতে ব্যাগ আর অন্যহাতে আমার বাঁ-হাতের কব্জি ধরে হাঁটতে হাঁটতে মাঝেমাঝেই হাসিহাসি মুখে পালকি বেহারাদের ছন্দে, ‘পা চালিয়ে গলে যাবে!/ পা চালিয়ে গলে যাবে!’ বলছিলেন। ইদানীং বাজারে বোতলবন্দী যে কাঁটা আমের শরবত পাওয়া যায়, তার গায়ে ইংরিজিতে লেখা থাকে ‘আম পান্না’। আসলে আমাদের আমের পানাটাই অবাঙালি উচ্চারণে আম পান্না হয়ে গিয়েছে।
এই কাঁচা আমের শরবতটির জন্যে যে দোকানটি আমার স্মৃতিতে স্মরণীয় হয়ে আছে তার নাম ‘কপিলা আশ্রম’। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে, নামকরণের সঙ্গে গঙ্গাসাগরের কপিলমুনির কোথাও একটা সূক্ষ্ম যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু তিনি নিজে শরবত পছন্দ করতেন কিনা তা আমার জানা নেই। উত্তর কলকাতার বিবেকানন্দ রোড ধরে কিছুটা এগোলেই শ্রীমানী মার্কেট। তার ঠিক গায়েই একটি বহুদিনের পুরনো ইটবেরনো বাড়ির একতলায় একশো বছর পেরিয়ে আসা এই শরবতের দোকান। এর সামনের দোহাট করা টিয়ারঙের কাঠের পাল্লাদুটির ঠিক মাঝখানে একটি সাদা সানমাইকা মারা লম্বাটে উঁচু টেবিল।
যার পিছনের ছোট ঘরটিতে উঁচু তক্তাপোশের ওপর বসে একজন মানুষ একটি পাথরের পাত্রের ভেতর কাঠের ঘুরনি দিয়ে দু’হাতে পাক দিয়ে চলেছেন। তার ভেতরে রয়েছে কাঁচা আমের শাঁস, পুদিনাপাতার রস, গোলমরিচ, হিং, জিরেভাজা গুঁড়ো মেশানো ‘কাঁচাআম-পুদিনার মশলা শরবত’। আর দোকানের সামনে একটি আঁকাবাঁকা লম্বা লাইন। সত্যি, শরবতের জন্যে মানুষের এই আকুলতা দেখে চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল। এই দোকানটির বর্তমান মালিক হলেন প্রতিষ্ঠাতা হৃষিকেশ শ্রীমানীর নাতি দিব্যেন্দুবাবু। আর আগের বছর গরমকালেও দোকান সামলাতে দেখেছি মহেন্দ্র দাঁ নামের একজন খটখটে বুড়োমানুষকে, যাঁর বাড়ি দোকানটির খুবই কাছে। এখনও দিব্যেন্দুবাবুরা নিজেরাই দই পাতেন, বরফ জমান। এখনও অন্য রাজ্য থেকে কেশরের মতো শরবতের সেরা মশলাগুলি নিয়ে আসেন। তাই এঁদের তৈরি ‘কেশর মালাই’ বা ‘আবার খাই’ এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।
গেরস্ত বাড়িতে জামাই খাতিরের জন্যে যে শরবতটি বাঙালি মধ্যবিত্ত বাড়িতে খুব হিট ছিল, তা হল বেলের শরবত। বেলের শরবত মানে যে বেলের পানা নয় এটা আমার একান্ত নিজস্ব একটা উপলব্ধি। ব্যাপারটা তাহলে আপনাদের কাছে একটু পরিষ্কার করেই বলি। আমি দেখেছি, বেলের পানায় শুধুমাত্র পাকা বেলের শাঁস থাকে। আর থাকে আখের গুড় এবং নুন। কদাচ দু’চার ফোঁটা পাতিলেবুর রসও তাতে যোগ করা হয়। এই ঘন থকথকে পানাটি কিন্তু জামাই খাতিরের উপযুক্ত নয়। জামাইকে দেওয়ার জন্যে বেলের শাঁসের সঙ্গে নুন-চিনি এবং টক দই মিশিয়ে সামান্য কেওড়ার জল যোগ করে পাতলা একটি দ্রবণ তৈরি করা হয়। তখন এর নাম হয় বেলের শরবত। আর বেলের পানা যেকোনো সাধারণ পাত্রে খাওয়া গেলেও বেলের শরবত খেতে হয় সামান্য মুখ-বড় ফিনফিনে কাচের গেলাসে।
এবার কেওড়ার জলের স্মৃতি নিয়ে সামান্য কিছু বলি। কেওড়া হল কেতকী বা কেয়া গাছের ডাক নাম। তবে সুন্দরবনের নোনামাটিতে কেওড়া নামের একটি ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছ জন্মায়, যার পেলব চকচকে সবুজ ফলটিকে ওখানে টক বানিয়ে খাওয়ারও চল আছে। আমি কিন্তু সেই গাছটির কথা এখন বলছি না। পুরুষ কেতকী গাছের ফুলের রং লেমন ইয়ালো। এই ফুলটি দেখতে অনেকটা ভুট্টার মতো এবং না-ফোটা অবস্থায় এর চারপাশের পাপড়িগুলি ভুট্টার মতোই মাথার দিকে জুড়ে থাকে। আমাদের মিত্রস্কুলের প্রাইমারি সেকশনের ভূগোল দিদিমণি তপতীদির কাছে গল্প শুনেছি, বালিকাবেলায় ওই ফুলটিকে তুলে এনে হাতে ঝাড়লে, তার ভেতর থেকে অবিকল ফেস পাউডারের রঙে সুগন্ধি রেনু বেরিয়ে আসত, যা তাঁরা প্রসাধন হিসেবে গালে মাখতেন। যদুবাজারের মাছপট্টির পিছন দিকের একটি উঁচু জায়গায় খালি-গায়ে লুঙ্গি পরে বসে থাকতেন একজন শাকপাতা বিক্রেতা, যাঁর কাছে ঢেঁকি শাক, নিশিন্দাপাতা বা হাড়ভাঙাপাতা কিনতে পাওয়া যেত। তাঁর কাছে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে শুকনো কেয়াফুল কিনে আনতেন নতুনজ্যাঠা। সেটাকে
তাঁর ডাক্তারি ল্যাবরেটরিতে কুচিকুচি করে কাটতেন। তারপর একটা কাচের ফানেলে ফিল্টার পেপার আটকে, তাতে একটুখানি রেক্টিফায়েড স্পিরিটের ঢেলে, তার মধ্যে সেই টুকরোটা দিয়ে দিন দুই-তিন ধরে ফিল্টার করে, তার সুগন্ধটুকু নিংড়ে নিতেন। তারপর সেই তরল নির্যাস একটি পরিষ্কার ছোট্ট কাচের বোতলে ভরে রাখতেন। সেইটার দু-এক ফোঁটা, শরবত তৈরির জলে মেশালেই জলটি আশ্চর্য রকম সুরভিত হয়ে উঠত। বিজয়া দশমীর দিন উনি যে সিদ্ধির শরবত বানাতেন, তাতেও ওই নির্যাস একটুখানি দিয়ে দিতে দেখেছি।
জামাই খাতিরের জন্যে দ্বিতীয় যে শরবতটি তুমুল জনপ্রিয় ছিল তা হল ডাবের কচি শাঁস, ডাবের জল, চিনি এবং পাতিলেবুর রস দিয়ে বানানো ডাব-শরবত। এই ডাব শরবতটি আমাদের বাড়িতে মাত্র কয়েকবার খেলেও জামাইষষ্ঠীর দিন বাবা, আমার মামারবাড়িতে গেলে এটা মোটামুটি বাঁধাধরা ছিল। ডাব-শরবতের কথা উঠলে অবধারিত ভাবে চলে আসে কলেজ স্কোয়ারের উল্টোদিকে ‘মহাবোধি সোসাইটি’র একই লাইনে শরবতের পীঠস্থান ‘প্যারামাউন্ট’ এর কথা। অনেক আগে সেখানে গিয়েই জানতে পেরেছিলাম, এই ডাব-শরবতটি নাকি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ব্রেনচাইল্ড। এর জন্যে এঁরা স্পেশাল ডাব নিয়ে আসেন বসিরহাট থেকে।
নেতাজী, কাজী নজরুল ইসলাম, বাঘাযতীন, মেঘনাদ সাহা বা উত্তম-সুচিত্রার মতো বিখ্যাত যত মানুষ এই দোকানটিতে এসেছেন, একটি লম্বাটে বোর্ডে তাঁদের সবার নাম লিখে বাঁধিয়ে রাখা আছে। এই নামের তালিকাটিতে মাঝে মাঝেই নতুন নাম যোগ হয়– আর যেটা খুবই স্বাভাবিক। যেদিনের কথা বলছি তখন তাতে জ্বলজ্বল করছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নবনীতা দেব সেনের মতো পাঁচ এর দশকের উজ্জ্বল নক্ষত্ররা। কিন্তু ছিল না সেই মানুষটির নাম, যিনি আমায় কম-সে-কম দু’বার ওখানে নিয়ে গিয়ে ডাব-শরবত খাইয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘আগে ডাব শরবত খেয়ে তারপর কোকো মালাই খাবি। আগে কোকো মালাই খেলে, জিভের দানাগুলো আর ডাব শরবতের সূক্ষ্ম ব্যাপারটা ধরতে পারবে না! বুঝতে পেরেছিস ?’ আমি ঘাড় কাৎ করে হ্যাঁ বলেছিলাম।
তো, সেদিন শরবত খেয়ে, টাকা দেওয়ার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা, এখানকার কর্তা মৃগেন্দ্র মজুমদারকে সেই কথা বলতেই অবাক হয়ে বলেছিলেন, ‘আপনি কার কথা বলছেন বলুন তো?’ আমি বলেছিলাম, ‘খুবই সুপুরুষ ছিলেন। ধুতি-পাঞ্জাবিতে চমৎকার মানাত। যা লিখেছেন– তার বেশিটাই ছিল ওঁর জীবন থেকে উঠে আসা!’ মৃগেনবাবু মৃদু হেসে বলেছিলেন, ‘সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু ভদ্রলোকের নামটা একটু বলবেন কি, তাহলে আমরা ওই নামটা এতে তুলে দিতে পারব!’ আমি সামনের স্টিলের বাটি থেকে একটুখানি মৌরি মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে খুব ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেছিলাম, ‘শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়।’