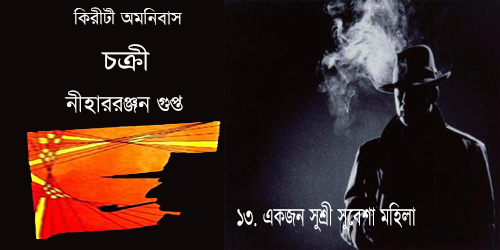টেলিফোন বাজছে।
“মা?”
“হ্যাঁ। ভাল আছিস তো তোরা?” কিছুক্ষণ চুপচাপ দু’ই দিক। ফোনের ভিতর দিয়ে শুধু নিঃশ্বাসের শব্দ তারপর পাশে নামিয়ে রাখা উলের সোয়েটারটা আবার বোনা শুরু করবার মত সোজা, উল্টা কথা শুরু।
“ভাবছিলাম তোমার ফোন আসবে। আমিও ভাবছিলাম করব। (মনে মনে বলে চলে আনন্দ, ‘আজ বাবার মৃত্যুদিন।’)”
“(মনে মনে উত্তর দেয় মা, ‘হ্যাঁ’…)
তোদের রাতের খাওয়া হয়ে গেছে? কী রেঁধেছিলি আজ?”
“নাহ্, খুব কিছু না। মুসুরির ডাল, ভাত, বড়ি দিয়ে পালং শাক, সরষে দিয়ে শিম–আলুর চচ্চড়ি আর পুঁটিমাছ ভাজা। মচমচে করে ভাজলে বাচ্চারা কাঁটা না বেছে চিবিয়েই মাছভাজা খেয়ে ফেলতে পারে।” “তাই নাকি? বাহ্, বাহ্।” এভাবেই গত ঊনচল্লিশ বছর ধরে কথা চলছে। এখন বাচ্চাদের নিয়ে, তখন সর্দি কাশির। জীবনের ডাল, ভাত, চচ্চড়ির গল্প সবসময়ই মনের সব গল্প ঢেকে দেয়। আর মানুষ ভাব দেখায় যেন তার চোখে বালু পড়েছে। অন্য কোনও কারণ নেই। শুধু সে জন্য চোখে জল।
সারা আঙিনা জুড়ে কি বিচ্ছিরি ঝরা পাতার স্তূপ। ১৯৭২ সাল। দেশটা স্বাধীন হয়ে গেছে। তবু কত মানুষ যে এখনও ফিরে আসে নি। আর কত মানুষ যে ফিরে এসেছে – একটা রক্তে ভেজা লুঙ্গি, চশমা কিংবা ঘড়ি হ’য়ে। অগোছালো জীবনে সবসময়ই দমবন্ধ হয়ে আসে। তাই খুব জোরে, জোরে কূয়াতলাটা ঝাঁট দিচ্ছিল আনন্দর মা। অথচ পাতাগুলোও যেমন। আরে ঝরাপাতা তো আর কাপাসতুলো নয়। কাপাসতুলোর এদিক, ওদিক উড়ে বেড়ানোর একটা তবু অর্থ আছে। যদি হঠাৎ উড়ে গিয়ে কোনওরকমে আবার মাটিতে পড়তে পারে, হয়ত স্বপ্ন গজিয়ে উঠবে। কিন্তু ঝরাপাতার তো তেমন কোনও ভবিষ্যত নেই। কথাটা মনে হ’তেই আরও জোরে, জোরে ঝাঁট দিতে থাকে মা।
সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আকাশের হলুদ রঙ বৌচি খেলবার মত প্রায় মাটি ছুঁয়ে ফেলেছে। হলুদের উপর লাল । নতুন বউ–এর ঘোমটার মত। আসলে ঠিক এই সন্ধ্যার সময়ই আকাশের বুকের রঙ দেখা যায়। হঠাৎ খবর ভেসে আসে। ৩০শে জানুয়ারি। জহির রায়হানের নিখোঁজ সংবাদ পুরানো রেডিওটার বিচ্ছিরি অডিও সিস্টেমের জন্য আরও বেশী হাহাকারের মত শোনায়। হোঁচট খেয়ে পড়ে মা। দেখে পায়ের কাছে একটা ছোট তুলসীর চারা। খুব ধার্মিক বাড়ি নয় আনন্দদের। হিন্দু বাড়ি হ’লেও কোনও তুলসীতলা নেই, তুলসীর মাথায় জল ঢালাও নেই। অন্যমনস্ক হয়ে জহির রায়হানের কথা ভাবতে, ভাবতে আনন্দর মা তবু তুলসীর চারাটাকে যত্ন করে একটা ছোট টবে পুঁতে জল দিতে থাকে। যদি গাছটা বাঁচে।
মানুষগুলো তো সব মরে গেছে চারদিকে। বধ্যভূমিতে মাথার খুলি আর হাড়ের ঠোকাঠুকি। মাঠের উপর সবুজ রঙের মিলিটারী জিপগুলো পড়ে আছে। তার উপর আনন্দ আর ওর বন্ধুরা লুকোচুরি খেলেছে আজ সারাদিন। এই লুকোচুরি খেলাটা খুব ভালো। ছেলেবেলা থেকে এই খেলা খেলতে, খেলতে বড় হ’লে জীবনের অর্ধেক কষ্টই গা সওয়া হয়ে যায়। মরুভূমির ভিতর একা হারিয়ে গেলেও কেমন যেন দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে নিশ্চয়ই পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। পথ তো চিরদিনই থাকে – পথের শেষে। ‘তুলসী আছে, বাড়িতে তুলসী আছে?’ ট্রাক থেকে একটা লাশ নামিয়ে রাখা হয়েছে আঙিনায়। অথচ ছোট টবে দিব্যি বেঁচে আছে তুলসীর চারা। আনন্দর মা তাড়াতাড়ি চারাটা এগিয়ে দেয়। কখন যে মানুষের জীবনে কোন কাজে লেগে যায়, কেও বলতে পারে না।
এর পর আনন্দদের দাদু, দিদা, মামা, মাসি ভরা জীবনটায় আর খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটে না। শুধু বাবাটা বসবার ঘরের দেয়ালে একটা শাদা কালো ছবি হয়ে ঝুলে পড়ে, এই। অবশ্য তাতে খুব একটা ক্ষতি হয় না। প্রত্যেক পরীক্ষার আগে আর কিছু না হোক, সেই ছবিতে প্রণাম তো করা যায়। মুড়ি মুড়কির মত আকাশ থেকে আশীর্বাদও ঝরে পড়ে। আর কানের কাছে হিতোপদেশের মত বিড়বিড় করে বলে চলতে থাকে দিদা, ‘কখনও মিথ্যা কথা বলো না, জীবনে কোন খারাপ কাজ করো না। বাবা কিন্তু সব উপর থেকে দেখছে।’ হ্যাঁ, আকাশে উঠে বাবার চোখে তো এখন সার্চ লাইট গজিয়েছে।
ফলে রাজশাহীর বড় বড় ফজলি আম পাকিয়ে দেয়া ভ্যাঁপসা গরমে বাড়ি শুদ্ধ লোক যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমাত; তখনও বড়ই–এর আচার চুরি করে খেতে আনন্দর কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকত। কোনওদিন পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের ফাঁকে কালো ডাঁই পিঁপড়ে কামড়ে ধরলে চুল আঁচড়ানো থামিয়ে মাথার চিরুনি দিয়ে তাকে দুই ভাগ করে দেওয়া কিংবা স্পঞ্জের স্যান্ডাল দিয়ে চটাস করে চ্যাপ্টা করে মেরে ফেলবার মত প্রতি দিনের সামান্য নিষ্ঠুরতাটুকু করতেও কখনও হাত সরত না ওর। তবু মাঝে মাঝে মনে হ’ত কোনও একটা ভয়ানক পাপ কাজই না হয় করে ফেলা যাক। বলা তো যায় না, সেই পাপের বিচার করতে বাবা হয়ত নালিশ দিতে বাড়িতে সবার কাছে একবার হলেও আসতে পারে! তার পর কি জানি কী হয়। কেন যেন মনে হয় সেই সব মহা, মহা পাপ কাজ ভালো কাজ করবার থেকেও আসলে অনেক বেশি কঠিন।
সুতরাং কি আর করা? মাথায় জব জব করে তেল দিয়ে মাথার দুই পাশে দু’টো বেনী বেঁধে পৃথিবীর সব চেয়ে লক্ষ্মী একটা মেয়ে হয়েই বড় হয়ে যেতে থাকে আনন্দ। দরজার হিঞ্জের ফাঁকে ওর আঙ্গুল চেপে ধরলেও ও ঠোঁট কামড়ে সব সহ্য করে নিতে পারে। কোনও কষ্ট দিয়েই ওকে ঠিক দমিয়ে রাখা যায় না। তবে একটা কথা সত্যি, অন্য বন্ধুরা যখন তাদের বাবাদের কোলে বসে ললিপপ খেত– আনন্দর যে এক্কেবারে লোভ হত না, তা নয়। কিন্তু দাঁতের স্বাস্থ্য বড়ই জরুরী, প্রাণের স্বাস্থ্যর চেয়েও। তাই যত লোভ বাড়তে থাকত, তত জোরে জোরে দাঁত মাজতে থাকত আনন্দ। কোন কোনওদিন দিনে ছয় বার। বাইরে কোথাও যেতে হ’লেই তার আগে দাদুর ঘরে ঝোলানো ছোট আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে তিনবার করে হাসি প্র্যাকটিস করে নিত। বন্ধুরা সবাই ওর হাসি ঝিলিক দেয়া বড়, বড় চোখ দেখত আর সারাদিন ধরে ওকে ভালোবাসত। কি জানি হবে হয়ত, ছেলেবেলায় বাবা, মা মরে যাওয়া বাচ্চাদের চোখগুলো হয়ত একটু বেশী রকম বেচারা হয়। ওদের বুকে জড়িয়ে না ধরে ঠিক যেন বাঁচা যায় না।
অন্যদের সঙ্গে কত ঝগড়া, কত চুল টানাটানি – কিন্তু আনন্দর সাথে কক্ষনওই কিছু না। স্কুলের সামনে ওই ‘হজমি দানা হজম করে, পেটের মামলা ডিসমিস করে, তেলাপোকা মারা, ছারপোকা মারা হজমি দানা’ বলে সারাদিন আকুল চিৎকার করা হজমিওয়ালার কাছ থেকে তেলাপোকা রঙের হজমিদানা কিংবা স্বচ্ছ প্লাষ্টিকে মোড়া একটাই তেঁতুলের আচারের প্যাকেট সবাই মিলে একইসাথে চেটে, চেটে প্রায় প্লাষ্টিকসহ চিবিয়ে খেয়ে ফেলবার মত সম্পর্ক ওর সব বন্ধুদের সঙ্গে।
আসলে সত্যি কথা বলতে কি মন খারাপ না করে জীবনে যখন যা পাওয়া যায়, তাই তো হাত পেতে নিতে হয়। এমন তো হ’তেই পারে যে বাড়িতে আগুন লেগে বাবার সবে ধন নীলমণি ওই ছবিটাও একদিন পুড়ে ছাই হয়ে গেল! তখন? ছবির তো নেগেটিভও নেই। mআর হাতের উপর বসে থাকা জোনাক পোকাটাই যে শেষ পর্যন্ত উড়ে গিয়ে আকাশের তারা হয়ে যায়, সে কথাটাও তো আর এক্কেবারে মিথ্যে নয়!
আনন্দর চার বছর বয়সেই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ সহনীয় হ’য়ে উঠল কারণ বাবার জন্য মাকে কোনওদিন চুপিচুপিও কাঁদতে দেখা গেল না। আসলে আনন্দর মা কান্নাকাটি করতে কেমন যেন ভয় পেত। কান্না বড় ছোঁয়াচে রোগ। বাড়িতে দিদা আছে, দাদু আছে, মামা আছে, মাসি আছে। মা যদি এখন পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে, বাড়িশুদ্ধ লোক কি তখন নিজেদের চোখ উপড়ে নিয়ে হাতে করে ঘুরবে? চোখ ছাড়া হোঁচট খেয়ে পড়বে তো গুষ্টিসুদ্ধ লোক! তাছাড়া দেশ মাত্র স্বাধীন হয়েছে। চোখের জল রাখবার জন্য অত বালতি, গামলা–ও বাজারে নেই। স্বাধীন বাংলাদেশের সব ঘরেই তো কেউ না কেউ মরে গেছে। ’৭৪–এর দুর্ভিক্ষ–ও এই এল বলে। দু’মুঠো চালের জন্য যে রেশনে লাইন দিতে হবে, সে খেয়াল আছে? ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে শুকিয়ে যাওয়া জলহীন পদ্মা নদীর মত এক খান লম্বা! পাওয়া যাবে বিটকেলে সবুজ আর হাওয়াই মিঠাই রঙের মচমচে প্লাষ্টিকের মত সিন্থেটিক টাফেটা শাড়ি। তাতেই ফুল তুলে এবার থেকে সব ক’টা বিয়েবাড়িতে যেতে হবে!
অবশ্য শেষ পর্যন্ত কি আর যায় আসে চোখের জল কয়েক ফোঁটা কম দেখলে? পৃথিবীতে চারদিক তো এমনিই ভেসে যাচ্ছে – রক্তে, জলে, প্রেমে। হাঁটু পর্যন্ত গামবুট পরেও খুব একটা সুবিধা হচ্ছে না। খুব বেশি চিন্তা ভাবনা না করে তাই সক্কালবেলা হ’তেই চার বছরের আনন্দ আর এক বছরের অশ্রুকে নিয়ে, আনন্দর মা একটা কালো কয়লার ধোঁয়া ছাড়া ট্রেনে চেপে বসল। সাতাশ বছর বয়সে, সাদা শাড়ি পড়ে – সারা জীবনের সব পোটলা পুঁটলি নিয়ে ভুলেও একবার মনে হ’ল না যে এই রেললাইনের শেষে আসলে কোনও স্টেশন নেই। কত জীবনেই তো থাকে না।
কী যে ভীষণ দুরবস্থা মায়ের, সত্যি। চোখ বন্ধ করলে স্বপ্ন দেখতে থাকে, চোখ খুলে ফেললেই দুঃস্বপ্ন। কোনটা যে সত্যি, কোনটা যে মিথ্যা, কোনটা যে ঘটেছে, কোনটা যে কোনওদিন ঘটবে না – কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। কেউ বলেও দেয় না যে একদিন একলা রাতের চোখের জলগুলো মোমের আলোর মত কাঁপতে, কাঁপতে গাল বেয়ে বুকের কাছাকাছি পৌঁছাবে। তখন সব জলরঙ ধুয়ে, ছবি মুছে কাফনের মত একটা সাদা কাগজ ঝড়ে উড়ে যাবে। তার নাম বাকিটা জীবন। পূর্বজন্মের গল্পগুলো এখনকার দিনগুলোকে জাপটে ধরে। একটা তেলচিটে বালিশে কে কবে শুয়েছিল। তার মাথার সুগন্ধি তেলের গন্ধ এখনও এই ঘরের ভিতর ঘোরাফেরা করে। অথচ জানালাগুলো বন্ধ করে কবেকার সেই কথা বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে রাখবার মধ্যে তো কোনওদিনই কোনও কৃতিত্ব নেই। কমলা, সবুজ ডোরাকাটা বালিশের কোণাটা ছিঁড়ে শিমুল তুলার কয়েকটা কালো বিচি এখন বিছানাটার উপর পড়ে আছে।
মনে হয় একশ’ বছরের পুরনো, পরিত্যক্ত এক বাড়ির সামনেই বুঝি দাঁড়িয়ে আছে মা। বাড়িটার গায়ের ইঁটগুলো লাল মাংস হ’য়ে খাবলা, খাবলা বেরিয়ে গেছে। কে জানে চিতা বাঘেই খাবল মেরেছে কিনা। ইঁটের ফাঁক দিয়ে অশ্বত্থ, পাকুড়ের চারা উঁকি দিচ্ছে। ভেঙ্গে পড়া ছাদ থেকে বটের একটা মোটা ঝুরি মাটি পর্যন্ত নেমেছে। অজগরের শরীরের মত। ছাদের উপর গলায় ময়ূরকন্ঠী মালা আঁকা, ছাই রঙা কবুতরের বাসা। কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই ঝাঁকে, ঝাঁকে তারা পায়ের কাছে নেমে আসে। আকাশের সব নীল, কাচের গ্লাসের মত চুরমার করে ভেঙ্গে এক্কেবারে মাটিতে – জলজ্যান্ত স্বপ্নের মত। একদিন এই বাড়িটায় অনেক লোক ছিল। মার্বেল পাথরের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ছোট, ছোট বাচ্চারা উপর তলা, নীচ তলায় কি ভীষণ হুল্লোড় করে দৌড়ে বেড়াত। এখন বাড়িটার চারপাশ ঘিরে কি কি সব কাঁটা ঝোপ গজিয়েছে। আগাছার মত বেড়ে ওঠা হাসনুহানা আর জুঁইফুলের গন্ধে বাস্তুসাপের বাসা। কবেকার সোনার সূতায় কাজ করা বেনারসি শাড়িগুলো অন্য কারও ট্রাঙ্কে বন্দী হয়ে শুয়ে আছে, ভোরবেলায় ঘুমিয়ে পড়া পতিতাদের মত। নীচতলার ঘরে কোনও ঝাড়বাতি জ্বলে না। আকাশে চাঁদ নেই।
মা স্পষ্ট বুঝতে পারে কোথাও একটা পথের মাঝখানে রেল লাইনটা ব্রীজের উপর ভেঙ্গে দু’ টুকরো হয়ে নদীতে পড়ে গেছে। তবু কিছুতেই ট্রেনটা থেকে নেমে যেতে পারে না তো। যে দুঃস্বপ্নগুলো মাঝরাতে পানা পুকুরের শেকড় বাকড়ের মত পা পেঁচিয়ে ধরে, এই ট্রেনটাও ঠিক সে রকম। ইচ্ছে করলেই চোখে মুখে জল ছিটিয়ে এক লাফ দিয়ে সব ফেলে, দুঃস্বপ্নগুলো ছেড়ে উঠে পড়া যায় না। আসলে কিছু বাবা যেমন পারে না এক দিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ঠিক ঘরের মাঝখানে হাত–পা ছড়িয়ে বসে থাকা, নিজে নিজে জামা কাপড় পরতে না পারা তার প্রতিবন্ধী মেয়েটাকে একা ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে; কিছু কিছু মা ও পারে না নিজের ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে এতিমখানায় ছেড়ে দিয়ে অন্য কারও হাত ধরে অন্য কোথাও চলে যেতে।
এই সব মানুষগুলো পুরো জীবন ট্রেনের ভিতর বসে, বসে বরং শুধু দেখতে থাকে ট্রেনের ভিতরও কত্ত রকম রঙ। গোলাপি রঙের চুল বাঁধবার ফিতা বিক্রি হচ্ছে…ঝাল–মুড়ি…সেফটি পিন…হাড়ের চিরুনি…গেরুয়া পোশাকে কেউ হয়ত খঞ্জনি বাজিয়ে গান ধরেছে, ‘হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হ’ল, পার কর আমারে একা, একা ঘুরপাক খাওয়ার জন্য তো মানুষের জন্ম না। মানুষের হাতের গড়নও তেমন নয়। মানুষের হাতের তালু ঝিনুকের একটা দিকের খোলসের মত। উপর দিকটা কালো, শক্ত। ভিতরটা নরম, শাদা। আর এক জন মানুষের হাত ধরলে তবে সে না সেই দুই হাতের ভিতরের অন্ধকারে মুক্তা গজিয়ে ওঠে।
কখনও ভুল করেও ট্রেনের জানালা দিয়ে ওরা কেউ ঘাড় কাত করে, উঁকি মেরে দেখে না আর কত দূর জল, কত দূর নদী…জলের কাছে আকাশের রঙ একদম আলাদা রঙের হয়। সবকিছু শেষ হয়ে গেলে যে রঙ বাকি থাকে, আকাশের রঙ সেখানে ঠিক সেই রকম নীল। বছরগুলো কেটে যায়। রাস্তায় জমে থাকা বৃষ্টির জলে চলে যাওয়া গাড়ির পেট্রল পড়ে পড়ে রঙধনু তৈরী হয়। অথচ নীল অপরাজিতাকে চমকে দিয়ে উড়ে যাওয়া জলফড়িং–এর পাখায় আলো আর জল মিলেমিশে আর কোনওদিনই কোনও সাত রঙ দেখা যায় না তারপর একসময় হঠাৎ করেই আবার চাঁদ ওঠে। গরাদ দেওয়া জানালা ফুঁড়ে সেই চাঁদের আলো এসে সাদা বিছানার চাদরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আনন্দ–র ঘুম ভেঙ্গে যায় কে জানে হবে হয়ত, আঠারো বছর বয়সে চাঁদের আলো বোরখা পড়ে চলাফেরা করলেও শরীরের সব লোমই কেমন যেন খাড়া হয়ে ওঠে।
রাতের ফোঁস, ফোঁস শব্দ শোনা যায়। পা টিপে টিপে পাশের ঘরে গিয়ে আনন্দ দেখে ঘরের দরজা হাট করে খুলে মা ঘুমাচ্ছে। চাঁদের আলো এসে পড়েছে দিদার বিয়ের বর্মা টিকের খাট–টায়। আনন্দদের বাড়ি আগেকার দিনের ফার্নিচার খুব কিছু নেই। শুধু এই রাজকীয় খাট। মাঝে মাঝে আনন্দর মনে হয় সোনা গলিয়ে যেমন আবার নতুন গয়না হয়, এই প্রাচীন কালো কাঠ গলিয়েও কি আজকের দিনের নতুন কিছু হবে না? আর মা–কে গলিয়ে নতুন এক মা? বাকি রাত ঘুম আসে না আনন্দর। এ কথা মনে হয়, সে কথা মনে হয়, বাবার কোনও কথাই যে প্রায় মনে নেই সেই কথাটাও মনে হয়।
জানালার গরাদের বাইরে চাঁদটা বিচ্ছিরিভাবে আকাশের আরও উঁচুতে উঠে যায়। ডাস্টবিন উপচে পড়া মুরগির বুকের হাড়, মাছের কাঁটা, পচা বাঁধাকপির পাতা, ফেন্সিডিলের ভাঙ্গা বোতল, পরচুলা, কবেকার বাসি ডাল, অপূর্ণ প্রেমের ছেঁড়াখোড়া সব চিঠি, হিন্দি সিনেমার নায়িকাদের কুঁচকে যাওয়া ব্লো আপ পোষ্টার, মরা বিড়াল; বস্তির ন্যাংটো বাচ্চা, আকাশ ফাটানো খিস্তি; রেল লাইনের পাশে তাঁবুর মত করে খাটানো নীল রঙের প্লাস্টিকের নীচে শুয়ে থাকা বর–বউ – এই সবে ভরা ঢাকা শহরের জেলখানায় বন্দী যে চাঁদ।
পরদিন মা–কে বলেই বসে আনন্দ, ‘জানো তো মা, তোমার আবার বিয়ে করা উচিত। এমন একা, একা থাকা কোনও মানুষের উচিত না!’ মা–র ঠোঁটটা অল্প কাঁপে। মামা, মাসি, দিদা সবাই যে যার চেয়ারে বসে থাকে। কে জানে কোন আদালত অবমাননা করে ফেলল এবার আনন্দ! তবে বেশীক্ষণ কলে আটকা পড়া ইঁদুরের মত ছটফট করতে হয়না ওকে। ছাদ কাঁপিয়ে সবাই হো, হো করে হেসে ওঠে। এমন কি মা–ও। আনন্দর তো সব সময়ই এমন পাগলের মত কথা! এর পর অনেক ‘আষাঢ়স্য প্রথম দিবস’ আসে, অনেক ‘পহেলা ফাগুন’…আনন্দর আর মায়ের বিয়ের ঘটকালি করা হয় না। বিধবা বিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নানা কীর্তিকান্ডর উপর ধুলা জমে যায়। আর মার কথা মনে হলেই আনন্দর কেবল মনে হয় জানালার পাশে কেউ যেন চুপ করে একটা চেয়ারে বসে আছে। তার কোলের উপর আলগোছে হাত দু’টো মুঠো করে রাখা। বাইরের আকাশে অনেক কালো মেঘ করেছে। বৃষ্টি নামবে।
অনেকদিন আগে একবার সমুদ্রে বেড়াতে গিয়েছিলো আনন্দ। কত যে দুই জন হাতে হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। শুধু একজন বয়স্ক মানুষ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল – একা। সূর্য ডুবছিল। সাগরের বিষন্নতায় আনন্দর সারা শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে সেদিন সারা রাত বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদেছিল আনন্দ। একা, একা ঘুরপাক খাওয়ার জন্য তো মানুষের জন্ম না। মানুষের হাতের গড়নও তেমন নয়। মানুষের হাতের তালু ঝিনুকের একটা দিকের খোলসের মত। উপর দিকটা কালো, শক্ত। ভিতরটা নরম, শাদা। আর এক জন মানুষের হাত ধরলে তবে না সেই দুই হাতের ভিতরের অন্ধকারে মুক্তা গজিয়ে ওঠে। আজ চারদিক কমলা আলোতে ভেসে যাচ্ছে। প্রেইরীতে হেমন্ত এসেছে। পিঙ্ক কোন–ফ্লাওয়ারের ভিতর কালো রঙের ছোট মৌচাকের মত বিচি। কোন–ফ্লাওয়ারের পিছনের সারিতে বেগুনি পালকের মত রাশিয়ান সেজ ক্যানাডিয়ান গীজগুলো প্রেইরীর বরফ ছেড়ে দক্ষিণে যাওয়ার জন্য আকাশ জুড়ে অনেক দুই কোনা ধনুক আঁকছে। আনন্দর হাতের উপর হেমন্তের রোদ আর শিরশিরে হাওয়া ভীষণভাবে কাঁপছে। এক ছুটে দূরে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করছে ওর। যেখানে কোন মানুষ একা নয়। আর সব বাচ্চারা সারাদিন হাত ধরে ধরে ঘুরে ঘুরে খেলে। তাদের পা বাতাসে দুলে শূন্যে উঠে যায়। মাথার বেনী মুখের পাশ ঘিরে খিলখিল করে হাসে। ‘এলেনা বেলেনা এক্কা দোক্কা ঝুম, সালাইকা, মালাইকা সালাই মালাইকুম।’
আকাশের হাঁসগুলো যত দূরে চলে যেতে থাকে, তত ছেলেবেলার আর একটা খেলার কথা খুব মনে হয় আনন্দর। রাজশাহীর দুপুরগুলোয় যত পলাশফুলগুলো লাল খই–এর মত আকাশের চ্যাপ্টা তাওয়া জুড়ে ফুটতে থাকত, বড়রা চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে নিয়ে আসা দড়ির খাটিয়া বারান্দায় টেনে এনে তত ঘুমাতে থাকত। কুন্ডলী পাকিয়ে রাস্তার ওইসব এতিম কুকুরগুলোর মত। গায়ে অবশ্য কাঁথা থাকত। শুধু ছোটদের তখন খুব বেশি কিছু করবার থাকত না। দু’টো চেয়ার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তার উপরটা মা’র শাড়ি দিয়ে ঢেকে ছাদ করে ঘর বানাতো ওরা। তারপর সেই ঘরের সামনে হাত ধরে গোল করে দাঁড়াত সবাই। তারপরই কম্পিটিশন শুরু। ‘কে সব চেয়ে বেশি দুঃখী’। বড়দের সামনে এইসব মন খারাপের যত্তসব গোপন খেলা তো খেলা যেত না কখনও! ওদের সামনে শুধু দাঁত খিলখিল হাসি!
আসলে আনন্দর প্রিয় বন্ধুদের অনেকেরই ছোটবেলায় বাবা মরে গিয়েছিল। নতুন কোনও ঘটনা নয়। একটা দেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন এমন হয়েই থাকে। তবে জীবনের এইসব রাজকীয় দুঃখ নিয়ে খুব বেশি হাহাকার করবার মত তখনও কিছু হয় নি। সব ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের বসবার ঘরের কাচের শো–কেসে সাজিয়ে রাখা সাদা শাড়ি কালো পাড় পরা বন্ধুদের মা’দের ধুলোটুলো ঝেড়ে প্রতি বছরই টেনেটুনে নামানো হ’ত। ৮ই ফাল্গুন না ২১শে ফেব্রুয়ারি বলা উচিত হবে তা নিয়ে নানা সভা করবার প্রচন্ড সরগরম ব্যস্ততার ফাঁকেও প্রভাতফেরির সামনের সারিতে ওঁদের রাখা হ’ত।
আর তাঁদেরও সামনে চার বছর, পাঁচ বছর, ছয় বছরের শহীদ বুদ্ধিজীবিদের সব কুচোকাচা সন্তান…সকলের খালি পা…সারা বছর কি অধীর অপেক্ষা করে থাকত ওরা এই দিনটার জন্য…কেমন যেন মনে হ’ত শহীদ মিনারের পা ঘেঁষে যে ফুলগুলো আজ দিচ্ছে তা হয়ত কোনও এক অলৌকিকভাবে হারিয়ে ফেলা বাবাদেরই একদম রক্ত মাংসের পা–এর চামড়াটাই ছুঁয়ে ফেলবে। রাত বারোটায় শহীদ মিনারের বুক হুঁ, হুঁ করা হাওয়া, পরের দিনই যে ফুটবল খেলা থাকলে এই একই রকম ব্যস্ততা নিয়ে সবাই সেদিকে দৌড় দেবে – সে কথাটা ভুলিয়ে দিয়ে এক অতি অদ্ভুত সবকিছু থমথম করে দেওয়া, হাত পা ঠান্ডা করা এক অন্য পৃথিবীতে নিয়ে যেত। আজ চারদিক কমলা আলোতে ভেসে যাচ্ছে। প্রেইরীতে হেমন্ত এসেছে। পিঙ্ক কোন–ফ্লাওয়ারের ভিতর কালো রঙের ছোট মৌচাকের মত বিচি। কোন–ফ্লাওয়ারের পিছনের সারিতে বেগুনি পালকের মত রাশিয়ান সেজ ক্যানাডিয়ান গীজগুলো প্রেইরীর বরফ ছেড়ে দক্ষিণে যাওয়ার জন্য আকাশ জুড়ে অনেক দুই কোনা ধনুক আঁকছে।
চার, পাঁচ, ছয় বছুরের সেই দলে টলমল করতে, করতে দুই বছরের পাপনও থাকত। আসলে আনন্দদের সবচেয়ে দুঃখীর সেই খেলাটায় পাপন সব সময়ই ফার্স্ট প্রাইজ পেত। ওর জন্ম পাকিস্তানীরা ওর বাবাকে মেরে ফেলবার দুই মাস পর কিনা, তাই। হিংসা করবার কিচ্ছু নেই। পাপনের দিদি পাপিয়া আর আনন্দ–ও অনেক ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে সেই কবিতাটা পড়ে, পড়ে – গলার ওঠানামা আর কান্নায় বুজে আসা স্বর দিয়ে…লোকজনকে একদম এক হাপুস চোখের জলে ভাসিয়ে। ‘এ–চোখে ঘুম আসে না। সারারাত আমার ঘুম আসে না মুন্ডুহীন বালিকার কুকুরে খাওয়া বীভৎস শরীর ভেসে ওঠে চোখের ভেতরে–আমি ঘুমুতে পারি না আমি ঘুমুতে পারি না কবিতাও কখনও কখনও সত্যিকারের জীবনের থেকে কম কাঁদায় না! মানুষকে।
কারো কারো বাবার নাম দেশের শহীদ তালিকায় ছিল, বুদ্ধিজীবিদের তালিকায় ছিল। কারো নাম শুধু বাড়ির লোক আর বন্ধুরাই জানত। একজন তো রেডিও খুলে কানটা একদম রেডিও–তে লাগিয়ে দিনের পর দিন অপেক্ষা করেই বসে থাকত। হয়ত ওর বাবার নাম কোথাও বলবে। হয়ত বাবার লাশ পাওয়া গেছে, সে খবরটা জানা যাবে। ‘বলুক না, ওরা একবার শুধু বলুক না, মরে গিয়ে ওর বাবা বিখ্যাত হ’য়ে গেছে বাংলাদেশটা স্বাধীন করবার জন্য ওর বাবা প্রাণ দিয়েছে’ প্রাণের বন্ধুটার সেই চাওয়াটা আজ আর নেই।
ছেলেবেলার চাওয়াগুলোর কথা মনে হ’লে আজকাল ভীষণ হাসিই পায় আনন্দরও। কোন দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ সেই দেশের মানুষের জীবনের জন্য। দিকে, দিকে কেবল কিছু মরণ ফলক বানানোর জন্য তো নয়! ‘এলেনা বেলেনা এক্কা দোক্কা ঝুম, সালাইকা, মালাইকা সালাই মালাইকুম…’ অস্থির হয়ে হাঁটতে হাঁটতে লাবণ্যকে ফোন করে আনন্দ। ওর দুই চোখ বেয়ে ততক্ষণে জল গড়িয়ে পড়ছে। আত্মহত্যা করা তো পাপ নয়। তবু কেন? কীসের কষ্ট ছিল? কী হয়েছিল? নিশ্চয়ই আত্মহত্যার মত ভয়ানক কিছুই হয়েছিল। নয়তো কেউ কেন কোনওদিন বাবার কথা বলে না? শুধু প্রশ্ন গুনে, গুনে আর তার মন গড়া উত্তর বুনে, বুনে জীবনটা কাটানো খুব সহজ কাজ নয়।
একা একা ঠান্ডা বেসমেন্টে বসে লাবণ্য তখন চা–তে টোস্ট বিস্কুট চুবিয়ে খাচ্ছিল। প্রাণের বন্ধু ও। নীচু স্বরে বলতে থাকে লাবণ্য, ‘কেন সবকিছু নিয়ে এত কষ্ট পাচ্ছিস, আনন্দ? কথা বল মা’র সঙ্গে। জানিস তো, যে মেয়েরা মা’র সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারে, খোলাখুলি কথা বলতে পারে, তারা সুখী হয় জীবনে। ঊনচল্লিশ বছর ধরে কেন ভেবে চলেছিস তোর বাবা আত্মহত্যা করে মরে গেছে। তোর বাবা একদম অন্যরকম মানুষ ছিল। হাসলে রাস্তার মোড় থেকে সে হাসি শোনা যেত। আর সে সময়টাও আসলে আলাদা রকম ছিল। একদম নাজি ক্যাম্প একটা। নাজি ক্যাম্পে বসে কেউ আত্মহত্যা করে না রে, আনন্দ। তোর বাবাকে মেরে গলায় গামছা দিয়ে লাশটা ঝুলিয়ে রেখেছিল ওরা। পা মাটিতে লেগে ছিল।’ বিকেলে মা’র ফোন আসে। আনন্দ কোনওভাবে শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে ফোনটার কাছে নিয়ে যায়। ‘কেন এত বছর ধরে বাবার কোন কথাই বল নি তোমরা?’ মনে, মনে বাকি কথা বলে চলে আনন্দ। ‘কোনওদিন বাড়িতে কোনও মৃত্যুদিন পালন হ’ল না। কিছুই তো হ’ল না এতগুলো বছর এদিকে কান পেতে এই কথা একটু শুনি, ওই কথা একটু শুনি। কত কিছুই যে ভেবেছি। কত কিছু…সেই চার বছর বয়স থেকে।’
মা’র গলা ফোনের ভিতর দিয়েও কান্নায় বুজে আসে। আনন্দর সামনেই। এত দিন পর এই প্রথম। ‘বাংলাদেশের কত মানুষ প্রাণ দিয়েছে যুদ্ধে। কয়টা নাম আর শহীদ তালিকায় আছে, বল্। আর তোরা সব এত ছোট ছিলি। কী বলব কিছুই ভেবে পাই নি। কোন কিছু না বলে বলে, না বলাটাই এক সময় অভ্যাস হ’য়ে গেল। বাবা চুপ করে গেল আমি কষ্ট পাব ভেবে, আমি চুপ করে থাকলাম মা কষ্ট পাবে ভেবে। বাড়িসুদ্ধ ভাই বোন সবাই কেমন একদম চুপ করে গেলাম। কেউ কাউকে কষ্ট দিতে চাই নি তো। দম বন্ধ করা সব কথা কি খোলাখুলি বলা যায়? কী বীভৎস একটা মৃত্যু! তোদের বড় করতেই সবাই কেমন দাঁত কামড়ে পড়ে থাকলাম। আর পুরোটা জীবন তো কেটেই গেল – এভাবেই। কিছুদিন আগে গ্রামের বাড়িতে একটা স্মৃতিফলক করতে চেয়েছিল।
আমার মন চায় নি। আজ আওয়ামীলীগ সভা করবে, কাল বিএনপি।’ যে গল্প হাহাকারের মত বাতাস কেটে যায় না, সে গল্প কোনও গল্প নয়। তবু মানুষের জীবনের সত্য গল্প তো লেখা যায় না। কাগজ ছিঁড়ে যায়। সেই সব গল্প জীবনভর পাতার শরীরের মত থরথর করে কাঁপে ঠিকই; কিন্তু যখন শেষ হয়ে যায়, তা ঝরা পাতার মত ঘুরে ঘুরে শব্দহীন তো মাটিতে পড়ে না। বঁড়শিতে গাঁথা খুব বড় একটা বোয়াল মাছ যেমন হাওয়ার ভিতর মোচড়াতে, মোচড়াতে আর একটু বাঁচবার চেষ্টা করে নৌকার গলুই–এ শেষমেষ আছড়ে পড়বার আগে; মানুষের জীবনের গল্পগুলোও ঠিক তেমন। বোয়াল মাছের মুখ দিয়ে কখনও খুব অল্প রক্ত গড়িয়ে পড়ে, কখনও কিছুই না বাইরে থেকে সব রঙ তো সব সময় দেখা যায় না। সে মৃত্যুরই হোক কিংবা জীবনের।