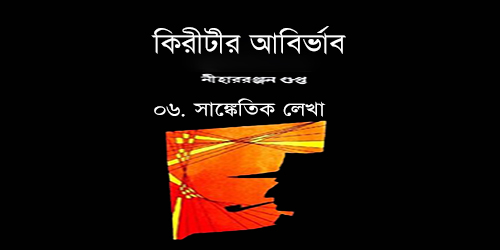চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে সারিবদ্ধ মানুষ দাঁড়িয়ে। তাদের প্রত্যেকের হাতে প্ল্যাকার্ড। প্ল্যাকার্ডে নানা কথা লেখা –
‘একাত্তরের রাজাকার
এখন যে দেশদরদি,
ওদের হাতে মরেছিল
বাবা এবং বড়দি।’
‘আর কিছু নয় চাইছি বিচার
দেশজনতা বাদী
ফাঁসির মঞ্চে ঝুলে থাকুক
যুদ্ধাপরাধী।’
মাথার ওপর ভাদ্রের কড়া রোদ। দরদর করে ঘামছে মানুষগুলো। বয়সীরা পকেট থেকে রুমাল বের করে মাঝে মাঝে কপালের ঘাম মুছে নিচ্ছে। নবীনরা রোদ, ঘাম – এসবকে উপেক্ষা করে মুষ্ঠিবদ্ধ হাত তালে তালে ওপরে উঠিয়ে আওয়াজ তুলছে – ‘রাজাকারের বিচার চাই, যুদ্ধাপরাধীর বিচার চাই।’
একটু দূরে আইল্যান্ডের ওপর দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ। নির্বিকার। এরকম হাজার স্লোগান তাদের শোনা। কত জঙ্গি মিছিলকে তাদের ধাওয়া দিতে হয়! সেই মিছিলে কত কিসিমের মানুষ! লুঙ্গিপরা থেকে প্যান্টপরা, রিকশাওয়ালা-ঠেলাওয়ালা থেকে রিটায়ার্ড সরকারি কর্মকর্তা, টোকাই থেকে ভবঘুরে ভিক্ষুক। মুখে সবার দাবি এক হলেও কারো কারো উদ্দেশ্য ভিন্ন। ধান্ধাবাজরা মিছিলে ঢুকে পড়ে। কেউ পকেট মারে, কেউ তক্কে তক্কে থাকে কখন লুটপাট শুরু হয়। শান্তিপূর্ণ মিছিলের নির্দেশ থাকলেও মিছিলের ভেতর থেকে হঠাৎ করে এসব উদ্দেশ্যবাদী জঙ্গি হয়ে ওঠে। মিছিলের মধ্য থেকে একজন কড়াহাতে পুলিশের মাথা লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়ে। রণংদেহী বলে পুলিশ এগিয়ে যায় মিছিলের দিকে। লাঠিপেটা, পাথর ছোড়া, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, জলকামান। সবশেষে রক্তারক্তি।
সে-তুলনায় আজকের এ-মানুষগুলো নিরীহ। কেমন জানি ম্যাড়ম্যাড়ে ওদের গলার আওয়াজ। অনেকে আবার দাবি ছেড়ে কথায় মশগুল। তাই পুলিশ নির্বিকার। বটগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে কেউ কেউ চোখ বুজে আছে, শীতসকালে মাছধরার জন্য হাঁটুপানিতে একপা তুলে যেমন করে বকরা ঝিম মেরে থাকে।
হঠাৎ তীক্ষè তীব্র একটা আওয়াজে পুলিশদের ঘুমে চটকা লাগল। হেলান ছেড়ে ধড়ফড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল তন্দ্রামগ্নরা। দেখল – চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একজন তরুণী লাগামছাড়া কণ্ঠে বলছে – মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা চাই, দিতে হবে।
শুধু পুলিশেরা নয়, সারিবদ্ধ মানুষও তার দিকে তাকাল, পাশের জনেরা ঘাড় ফিরিয়ে আর দূরের মানুষরা শরীর বেঁকিয়ে।
আজকের মানববন্ধনের উদ্দেশ্য ছিল – যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি। রাজাকাররাও যুদ্ধাপরাধী। তাই বড় বড় যুদ্ধাপরাধীর বিচারের দাবির সঙ্গে রাজাকারদের বিচারও চাওয়া হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধার কথা এখানে আসার কথা নয়। কিন্তু হঠাৎ করে ফারহানা আওয়াজ দিলো – মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা চাই। সবাই হকচকিয়ে গেল। স্লোগান ভুলে প্রশ্নবোধক চোখে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। একটুক্ষণ পরে ফারহানাও বুঝতে পারল নিজের অসংলগ্নতার ব্যাপারটি। ওইসময় পাশে দাঁড়ানো সৈকত জিজ্ঞেস করল, ‘কী ব্যাপার ফারহানা, হঠাৎ করে সিরিয়াস গলায় এরকম স্লোগান দিলি যে।’
ফারহানা কিছু বলল না। অসহায় ভঙ্গিতে সৈকতের দিকে তাকিয়ে থাকল। এইসময় সারি থেকে রাশেদ চিৎকার করে উঠল – যুদ্ধাপরাধীর বিচার চাই। সমস্বরে সবাই বলল – করতে হবে।
মানববন্ধন শেষ হয়েছে। প্রেসক্লাবের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রাশেদ বক্তৃতা দিচ্ছে। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে অন্যরা। বেশি বক্তৃতার সুযোগ নেই। রাশেদ বলছে – দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে কবে। এখনো ইউরোপ-আমেরিকায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হচ্ছে। অপরাধীদের বয়স যতই হোক, বিচারের হাত থেকে কেউ রেহাই পাচ্ছে না। আর আমাদের দেশে যুদ্ধাপরাধীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে; এমনকি মন্ত্রী-উপমন্ত্রী হয়ে গাড়িতে স্বাধীন দেশের পতাকা লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা কি মানুষ? যদি মানুষ হই, তাহলে এই অরাজকতা, দেশের এত বড় অপমান সহ্য করছি কী করে?
রাশেদের বক্তৃতা চলতে থাকে। এক সময় ফারহানা জটলা থেকে বেরিয়ে আসে। কী যেন ভাবছে সে, গভীরভাবেই ভাবছে। মাথা নিচু করে চেরাগি পাহাড়ের দিকে হাঁটতে থাকে ফারহানা।
‘কোথায় যাবি এখন?’ একটু পেছন থেকে সৈকত জিজ্ঞেস করে। সৈকত যে তার পেছন পেছন আসছে টের পায়নি ফারহানা।
সৈকতের প্রশ্ন শুনে চমকে ফিরে তাকায় ফারহানা। একটুক্ষণ দাঁড়ায়। সৈকত এগিয়ে এলে দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করে।
‘বললি না তো কোথায় যাবি?’ সৈকত আবার জানতে চায়।
‘এই যাচ্ছি – ।’ ফারহানা দায়সারা উত্তর দেয়।
‘এই যাচ্ছি বলে আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছিস?’
‘না। এড়াতে চাইছি না। আসলে কোথায় যাব তেমন করে ঠিক করিনি। তবে – ।’ ফারহানা নরম সুরে বলে।
‘তবে – ?’ বলে সৈকত ফারহানার মুখের দিকে তাকায়।
‘বাতিঘরে যেতে পারি। সেখানে একটা বই এসেছে, মুনতাসীর মামুনের শান্তিকমিটি : ১৯৭১। ৪৫০ টাকা দাম। কেনার ক্ষমতা নেই। গত কদিন ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছি। ৮৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়েছি। দেখি আজও কিছু পৃষ্ঠা পড়া যায় কিনা।’ আস্তে আস্তে কথাগুলো বলে যায় ফারহানা।
‘তুই তো ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী। শান্তি কমিটি : ১৯৭১ পড়ে তুই কী করবি?’ সৈকত বলে।
‘যে-কারণে আজকে মানববন্ধনে এসেছি, যে-কারণে পাগলের মতো হঠাৎ বেসুরো আওয়াজ তুলেছি – মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা চাই, সে-কারণে।’
‘তোর সব কথা বুঝতে পারি না ফারহানা। তবে এইটুকু বুঝি তোর ভেতরে কষ্টের বড় একটা ঢেলা আছে।’
‘তুই ঠিকই ধরেছিস, ওই ঢেলা যখন আমার ভেতরে ওলট-পালট খায়, তখন আমি বেদিশে হয়ে পড়ি। বর্তমানকে ভুলে যাই।’ বিষণ গলায় ফারহানা বলে।
ওরা দুজন বাতিঘরে ঢোকে। ফারহানা সংকুচিতভাবে তাক থেকে মুনতাসীর মামুনের বইটি টেনে নেয়।
সৈকত কাউন্টারের দিকে সরে আসে। চাপা গলায় বলে, ‘মুনতাসীর মামুনের শান্তি কমিটি : ১৯৭১ বইটি প্যাকেট করে দেন।’ সৈকত তাকিয়ে দেখে – গভীর মনোযোগ দিয়ে ফারহানা বইটির পৃষ্ঠা উল্টিয়ে যাচ্ছে। একটা সময়ে ফারহানা পড়া থামায়। অসহায় ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক তাকায়। বইটি যথাস্থানে রেখে সৈকতের উদ্দেশে বলে, ‘যাইরে সৈকত।’
‘দাঁড়া, আমিও যাব।’
চমকে সৈকতের মুখের দিকে তাকায় ফারহানা। মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করে, ‘তুই কোথায় যাবি?’
‘এই হাঁটব, তোর সঙ্গে একটু। আপত্তি নেই তো তোর?’ থতমত কণ্ঠে বলে সৈকত।
এবার হেসে উঠল ফারহানা।
‘হাসছিস কেন?’ জিজ্ঞেস করে সৈকত।
হাসতে হাসতে ফারহানা বলে, ‘তোর ভঙ্গি দেখে মনে হলো – রাজাগজা যেন আমি। আমার সঙ্গে হাঁটতে পারমিশন লাগবে!’
এবার সৈকতও ফিক করে হেসে দেয়, ‘রাজাগজা না রানিটানি। তুই আবার রাজা হবি কী করে? হলে রানি হবি।’ কৌতুকের ঝিলিক সৈকতের চোখে-মুখে।
ফারহানার মুখমণ্ডল থেকে হাসি বিলীন হয়ে যায়। বেদনার গভীর একটা ছায়া পড়ে সেখানে। ছোট্ট একটা শ্বাস টেনে ফারহানা বলে, ‘চল, হাঁটি।’
বাতিঘর থেকে বেরিয়ে ডিসি হিলের উত্তর পাশ ধরে লাভলেনের দিকে হাঁটতে থাকে দুজনে।
ফুটপাথের ধার ঘেঁষেই ফুলের দোকানগুলো। ফুলগুলো রাখা হয়েছে ফুটপাতজুড়ে। ফুটপাতচারীরা কখনো স্তূপাকৃতি ফুলের ওপর দিয়ে ছোট্ট একটি লাফ মেরে, কখনো ফুটপাথ থেকে নেমে, কখনো বা শরীরের নানা অংশ বেঁকিয়ে পথ ফুরাচ্ছে। ফুলের দোকান ছাড়িয়ে একটু এগোলেই ‘চট্টগ্রাম মঞ্চে’র বিলবোর্ড। ওখানকার ফুটপাত ফাঁকা। ওখানে পৌঁছেই সৈকত ভূমিকা ছাড়া বইয়ের প্যাকেটটি ফারহানার দিকে এগিয়ে ধরে, ‘নে এটা।’
‘কী এটা?’ অবাক চোখে জিজ্ঞেস করে ফারহানা।
‘বই। তোর জন্য।’
‘আমার জন্য! কী বই?’
‘শান্তি কমিটি : ১৯৭১।’
থমকে দাঁড়ায় ফারহানা। কী যেন ভাবে একটুক্ষণ। তারপর ম্লানমুখে বলে, ‘আমি এ-বই নেব নারে সৈকত।’
‘কেন নিবি না? তোর প্রিয় বই তো।’ সৈকত বলে।
‘তারপরও নেব না। তুই কেন এত দামি বই আমাকে উপহার দিবি?’
শান্ত গলায় সৈকত বলে, ‘আমি কোনো ধনী ঘরের সন্তান নইরে ফারহানা। বাপ গোয়ালা। গ্রামে দুধ বেচে। গৃহস্থদের কাছ থেকে দুধ কিনে গঞ্জে নিয়ে বেচে। ওই দিয়ে আমাদের সংসার চলে। এস.এস.সি. পাস করে শহরে আসি। রেজাল্ট খারাপ ছিল না। সিটি কলেজে ভর্তির সুযোগ পাই। এইচ এস সি পাস করে অনার্স, তারপর এম এসসি পড়ছি বোটানিতে। মেসে থাকি। টিউশনির টাকা দিয়ে চলি। কাল সন্ধেয় বেতন পেয়েছি। ওই টাকায় কিনেছি বইটি। বইটি নিলে খুশি হব।’ আগ্রহী চোখে ফারহানার দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করে সৈকত।
ফারহানা কিছু বলে না। সৈকতের দিকে কৃতজ্ঞ চোখে একটুক্ষণ তাকায় ফারহানা। বইটি হাত বাড়িয়ে নেয়। তারপর চুপচাপ দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে।
মোমিনরোড লাভলেনে মেশার আগে ঝাউতলা। চট্টগ্রামে ঝাউতলা দুটো। বোঝার সুবিধার জন্য মানুষ এই ঝাউতলাকে মেথরপট্টি ঝাউতলা বলে। এখানে একটি মেথরপট্টি আছে, সে অনেককাল আগে থেকে। মেথরপট্টির আশপাশে খোলা নিচু জলো জায়গা ছিল। ওই নিচু জায়গার একাংশে গড়ে উঠল বস্তি। হুলস্থূল করে মানুষ বেড়ে গেল চট্টগ্রাম শহরে। মেথরপট্টি ঘৃণার হলেও এর আশপাশে দুমদাম করে বড় বড় বিল্ডিং গজিয়ে উঠল। ধনীরা থাকতে শুরু করল ওইসব বিল্ডিংয়ে। ওরা রিকশাওয়ালা, ট্যাক্সি ড্রাইভারকে গন্তব্যের ঠিকানা বলতে শুরু করল ডিসি হিল ঝাউতলা।
ভূমিলোভীরা অনেক চেষ্টা করল বস্তি আর পট্টিকে উচ্ছেদ করতে। কিন্তু সম্ভব হলো না। নিম্ন আয়ের মানুষ বস্তিতে থাকে। পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করে। কিন্তু অস্তিত্বে টান পড়ল যখন, সবাই একজোট হলো। ভূমিদস্যুরা পিছিয়ে গেল। মেথরপট্টি আর বস্তি থেকে গেল। ওই বস্তিরই দু’কামরার একটা ঘরে ফারহানারা থাকে। ফারহানারা মানে ফারহানা, তার বাপ শামসু আর মা নীলু বেগম।
সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার বারহাল ইউনিয়নে শামসুর বাড়ি ছিল। বারহাল ইউনিয়নের মধ্যদিয়ে দুর্বাসা নদী বয়ে গেছে। বাংলাদেশের অসংখ্য নদীর মধ্যে দুর্বাসা একটি। মানচিত্রে নির্দেশিত না হলেও স্থানীয়দের মনোচিত্রে খোদাই করা আছে এই নদী। প্রচণ্ড ক্রোধপরায়ণ মুনি ছিলেন দুর্বাসা। রেগেমেগে একে তাকে অভিশাপ দিতেন শুধু। নামের সঙ্গে মিলের কারণে বোধহয় নদী দুর্বাসাও ক্ষেপা ধরনের। শুধু কূল ভাঙে। আজ এ-পাড় তো কাল ও-পাড়। বারহাল ইউনিয়নের চরখানপুর গাঁয়ের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া দুর্বাসার দক্ষিণ পাড়ে শামসুর বাড়ি ছিল। শামসুর বাপ ছিল চাষি। চার-পাঁচ কানি জমি ছিল তার। উঁচু ভিটে ছিল। ভিটের ওপর মাটির ঘর ছিল। শামসুর বাপ নিজের জমির সঙ্গে আরো দু’চার-পাঁচ কানি বর্গা জমি মিশিয়ে চাষ করত। ধানে আর রবিশস্যে বছর চলে যেত। অভাব ছিল না ঘরে। শামসুর বয়স কুড়ি পেরোতে না পেরোতেই নীলু বেগমকে পুতের বউ করে আনল শামসুর বাপ।
শামসুর আবেগ ছিল খুব। ভালো গান গাইতে পারত। লেখাপড়া তেমন জানত না। কোনোরকমে নাম সই করতে পারত। যুদ্ধ শুরু হলে এক সন্ধেয় শামসু বাপকে বলল, ‘বাবা, আমি যুদ্ধেত যাইতাম। মুক্তি যুদ্ধেত।’
বাপ বলে, ‘কিথা কছ, ঘরের মাঝে নয়া বউরে থুইয়া তুই যুদ্ধেত যাইতে কিথারলাগি?’
‘বাবা তুমি ত ঘরো আছও। মাও আছইন ঘরো। নীলুরে আমি বুঝাইয়া কইমু।’
চরখানপুর ছাড়িয়ে গোটা বারহাল ইউনিয়ন, বারহাল ইউনিয়ন ছাড়িয়ে জকিগঞ্জ উপজেলায় এ-সংবাদ চাউর হয়ে গেল – শামসু বুলেবা মুক্তিযোদ্ধা ওইছে। রাজাকার আর পাঞ্জাবিদের মারবার লাইগা হাতত্ অস্ত্র নিছে।
চরখানপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বশিরউদ্দিন। তারই সভাপতিত্বে চরখানপুরে শান্তিকমিটি গঠিত হলো। বশিরউদ্দিনের নেতৃত্বে একটা রাজাকার দলও গঠিত হলো। বশির জকিগঞ্জ উপজেলায় গিয়ে চরখানপুর গ্রামটা ঘুরে যাবার জন্য মেজর ফয়সল খানকে অনুরোধ করে এলো। মেজর ফয়সল খান চরখানপুরে এলে বশিরউদ্দিন শামসুর বাড়ি দেখিয়ে বলল, ‘স্যার, ইটা মুক্তিযুদ্ধার বাড়ি। ই বাড়ির পোলা শামসু হারামজাদা যুদ্ধেত গেছে।’ থেমে বড় করে একটা শ্বাস টানল। তারপর দুই হাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, ‘আহারে! আল্লায় জানে ওই হারামখোর এর মাঝে কজন পাঞ্জাবি খুন করছে!’ মেজর ফয়সল খান দাঁত কড়মড় করে বলল, ‘আগ লাগাও শালা বেহেনচোদ হারামি কো মোকাম মে।’
রাজাকাররা আগ লাগাতে গিয়ে শামসুর বাপকে ধরল। মা বউ নীলু বেগমকে নিয়ে পাটক্ষেতে আত্মগোপন করল। ফয়সল নিজ হাতে গুলি করল শামসুর বাপের কপাল বরাবর। তার সামনেই আগুন দেওয়া হলো শামসুর বাড়িতে।
রান্নাঘর পুড়ল, বসতবাড়ি পুড়ল। গরু-ছাগলগুলো রাজাকাররা নিয়ে গেল। এর কিছু গেল মিলিটারি ক্যাম্পে, বেশিরভাগ গেল বশিরউদ্দিনের গোয়ালে। সব পুড়লেও শামসুদের গোয়ালঘরটি পুড়ল না। মিলিটারি রাজাকাররা চলে গেলে নীলু আর শামসুর মা পাটক্ষেত থেকে বেরিয়ে এলো। উ™£ান্ত চোখে দুজনেই দেখল উঠানে শামসুর বাপ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কপালের গুলি মাথার পেছনটা উপড়ে বেরিয়ে গেছে। মাথার চারপাশে জমাট বাঁধা কালচে রক্ত।
প্রতিবেশী জলিল মাস্টারের সহায়তায় শামসুর বাপকে কোনোরকমে কবরে নামিয়ে দিয়ে শামসুর বউটাকে বুকে বেঁধে গ্রাম ছাড়ল শামসুর মা। পাঁচ গ্রাম পর শামসুর মায়ের বাপের বাড়ি। সেখানেই ঠাঁই নিল বউ-শাশুড়ি।
তারপর অপেক্ষার পালা। মাস ফুরায় – মে-জুন-জুলাই-আগস্ট। দিন যায়, নদী কাছে আসে। দুর্বাসা দক্ষিণপাড় ভাঙতে ভাঙতে শামসুর বাড়ির একেবারে কাছ ঘেঁষে ভাঙন থামায়। গ্রামবাসী বলে – একটু জিরিয়ে নিচ্ছে করালগ্রাসী দুর্বাসা। বাড়িঘর, ধানিজমি, গাছপালা, পুকুর-ডোবা, আলপথ-মেঠোপথ খেতে খেতে উদরপূর্ণ হয়ে গেছে দুর্বাসার। একটু বসে ঢেঁকুর তুলছে সে। উদরস্থ খাওয়া হজম হয়ে গেলে আবার ভাঙন শুরু করবে।
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর পেরিয়ে ডিসেম্বর এলো। ১৬ ডিসেম্বর সূর্য উঠল, বিজয়ের। শামসুর মা বউকে নিয়ে ওইদিনই চরখানপুরে ফিরল। যদি শামসু ফিরে আসে! গোয়ালঘরের কাঠামোটা আছে; ভাঙাচোরা বেড়া, চালের স্থানে স্থানে ফুটো হয়ে গেছে। কত ফলন্ত গাছ ছিল ভিটেয়; সব লুটপাট হয়ে গেছে। বাড়ির উত্তর কোনার তালগাছটি শুধু দাঁড়িয়ে আছে। বড় একটা বটগাছ ছিল। ডালপালা কেটে নিয়ে গেছে কারা। কাণ্ডটা নিয়ে কবন্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে বটগাছটি।
বশিরউদ্দিন গা ঢাকা দিয়েছে। লোকমুখে শোনা যায় – সুনামগঞ্জের বিল এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে সে। দাড়িগোঁফ কেটে, বাবরিচুল ছেঁটে লেবাস বদলে ফেলেছে সে। যুদ্ধের সময় চরখানপুরে বশিরউদ্দিন অত্যাচার চালিয়েছে ভীষণ। গরু-ছাগল নিয়ে গেছে যখন ইচ্ছে যার গোয়াল থেকে। সালামত আলীর চৌদ্দ বছরের মেয়েকে মেজর ফয়সল খানের ক্যাম্পে চালান দিয়েছে। একটেরে ছিল নাপিতপাড়া। নির্জীব, নির্বীর্য কিসিমের মানুষ তারা। বশিরউদ্দিনের উস্কানিতে রাজাকারদের অত্যাচার বেড়ে গেলে অধিকাংশ নরসুন্দর সপরিবারে গ্রাম ত্যাগ করেছে। দু-একটি পরিবার মাটি কামড়ে থেকে গেছে। কোথায় যাবে, কী খাবে এই অনিশ্চয়তায় তারা গাঁ ছেড়ে যায়নি। তাদের মধ্যে বিমল শীলের পরিবার একটি। টিনের বাক্স নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘোরে বিমল, দু-চারজনের চুল ছেঁটে যা পায় তা দিয়ে সংসার চালায়। পথে একদিন বশিরউদ্দিনের সঙ্গে বিমলের দেখা। মাথা নিচু করে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলে বশির হুঙ্কার দিয়ে উঠল, ‘কিথারে মালাউনের পুত, চোখে দেখছ না? আদাব-সালাম না দিয়া পাশ কাটাইয়া যাইতাছছ? তুই জানছ না আমি ক্যাটা?’
‘জি হুজুর জানি। আদাব হুজুর।’ কোঁতা হয়ে বিমল বলল।
‘তোর আদাবের মাইরে চোদি। চোদানির পোলা, তুই বেশি বাইড় বাইড়া গেছত? বাঁশঝাড়ের ওই বাঁশটা দেখছত? আইখ্যাওয়ালা মোটা বাঁশটা দেখতাছত না – ইটা তোর পোন্দে দিয়া যাইতা হারাইয়া দিমু পুঙ্গির পুত। খাড়ো মালাউনের বাইচ্চা, তোরে দেখাইতাছি।’ চোখ পাকিয়ে মেজাজ গরম করে কথাগুলো বলল বশিরউদ্দিন।
চুল কাটার সরঞ্জামভর্তি টিনের বাক্সটা পাশে নামিয়ে রেখে বিমল শীল দুই হাত কচলাতে কচলাতে বলল, ‘ভুল অইছে হুজুর, মাফ কইরা দেইন।’
বিমল শীলের কাঁচুমাচু ভঙ্গি দেখে তখন আর কিছু না করলেও শুক্রবারের দুপুরে রাজাকারের দল নিয়ে নাপিতপাড়ায় বিমলের উঠানে হাজির হলো বশিরউদ্দিন। বিমল, তার বউ, দুই সন্তান, বিমলের বুড়া বাপ – সবাইকে নিয়ে মসজিদে গেল। সেদিন জুমার নামাজের পর গোটা পরিবারকে মুসলমান করা হলো। বিমলের ছোট দুই ছেলের ছুন্নত করানো হলো। বিমলের মুসলমানি নাম রাখা হলো ইজ্জত আলী। ইজ্জত আলী মাথায় টুপি পরে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরল।
বশিরউদ্দিনের এইসব কর্মকাণ্ড গ্রামবাসী ভোলেনি। ভোলেনি বলেই ১৬ ডিসেম্বর তার সন্ধান করা হয়েছে। কিন্তু বশির ধুরন্ধর। ১৬ ডিসেম্বরের দুদিন আগে রাতের আঁধারে সে চরখানপুর ছেড়েছে।
শামসু যথাসময়ে ফিরে এলো না। যারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা ফিরল। যারা প্রত্যন্ত গ্রামে মিলিটারি-রাজাকারের ভয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা ফিরল। কিন্তু ফিরল না মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া শামসু। শামসু মরে গেছে না বেঁচে আছে ভিনগাঁয়ের মুক্তিরাও বলতে পারল না। শামসুর মা ভেঙে পড়ল – ‘ও আমার পোলারে, তুই আমরারে ছাইড়া কোয়াই গেলে রে পুত। ইবায় আমরা কিলা বাঁচমু। কিথা খাইমুরে বাবা।’
নীলু বেগমের প্রাণ শক্ত। সে ভেঙে পড়ে না। শামসুর না ফেরার বেদনা নীলুর আশাকে দুমড়ে দিতে পারে না। দিন যায় মাস যায়, নীলু আশায় পথ চেয়ে থাকে। মাস তিনেক পরে নীলু বেগমের পথ চাওয়া শেষ হয়। ক্র্যাচে ভর দিয়ে শামসু বাড়ি ফিরে। তার ডান পা হাঁটুর নিচ থেকে কাটা। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে এক অপারেশনে খানসেনার হাতে ধরা পড়ে শামসু। ডান পায়ে গুলি করে তারা। মৃত ভেবে চলে যায় খানরা। পরে মুক্তিযোদ্ধারা মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে সীমান্তের ওপারে নিয়ে যান। সেখানকার হাসপাতালে গত চার মাস চিকিৎসা নেয় শামসু। সুস্থ হয়ে ক্র্যাচে ভর দিয়ে বাড়ি ফিরে।
দিন যায়; সপ্তাহ, মাস, বছরও যায়। শামসু তার ঘরবাড়ি আগের মতো করে আর বানাতে পারে না। বাপ বুড়ো হয়ে গেলেও গায়ে শক্তি ছিল, মাথায় বুদ্ধি ছিল। ক্ষেত-খামারে শামসুর সঙ্গে হাত লাগাত। বুদ্ধির গুণে এক টাকাকে দুই টাকা করতে পারত। বাপ এবং মা চলে যাওয়ায় শামসু ভীষণ অসহায় হয়ে গেল। ক্র্যাচে ভর দিয়ে চাষাবাদ তো আর করা যায় না! শামসুর পরিবার-ঘরবাড়ি হতশ্রী হতে লাগল। এর-ওর কাছ থেকে চেয়েচিন্তে খাওয়ার মতো অবস্থা দাঁড়াল শামসুর। জমি বেচা শুরু করল সে। একদিন শেষ খণ্ড জমি বেচে একটি গাভিন গাই কিনে আনল। যদি দুধ বেচে সংসার চলে!
স্বাধীনতার বছর পাঁচেক পরে বশিরউদ্দিন ফিরে এলো। সাড়ম্বরেই ফিরল সে। তখন বাতাস অনুকূলে। যুদ্ধাপরাধীরা সমাজে সম্মান পেতে শুরু করেছে। বশিরউদ্দিন ফিরেই বাজারের চাতালটা পাকা করে দিলো। জামে মসজিদের ছাদ ঢালাইয়ে একশ বস্তা সিমেন্ট দিলো। তার বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া মেটে রাস্তাটায় ইট বসাল। চারদিকে বশিরের জয়জয়কার। দান-খয়রাতের বহর দেখে চরখানপুরের মানুষ যুদ্ধের সময় তার কৃতকর্মের কথা বেমালুম ভুলে গেল। সবাই ভুললেও ভুলল না শুধু শামসু আর ইজ্জত আলী। বশিরের সঙ্গে দেখা হলে এ দুজনের গলায় কফ আসে। সেই কফ ওরা থু বলে বশিরের সামনে ফেলে।
ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন হলো। আলহাজ মোহাম্মদ আমিন হেরে গেল বশিরউদ্দিনের কাছে। বশির চরখানপুরের মানুষকে বোঝাতে সমর্থ হলো যে, আলহাজ মোহাম্মদ আমিন ভারতের দালাল। যুদ্ধের সময় আমিন সপরিবারে ভারতে চলে গিয়েছিল।
বশিরউদ্দিন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান থেকে পুনরায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হয়ে গেল।
শামসুর গ্রামে টিকে থাকা মুশকিল হয়ে গেল। বশিরই তার জীবনকে অস্থির করে তুলল। রাতে শামসুর ঘরের চালে ঢিল পড়তে লাগল। মাঠ থেকে কে বাছুরটা চুরি করে নিয়ে গেল। রাস্তা ভরাটের নামে শামসুর বসতবাড়ির সীমানা-ঘেঁষা খাসজমি থেকে গভীর খাদ করে মাটি কাটাল। বর্ষায় ভিটের একাংশ ভেঙে পড়ল ওই খাদে। অসহায় শামসু এর-ওর কাছে গেল সুরাহার জন্য। কিন্তু কেউ বশিরের বিরুদ্ধে এগিয়ে এলো না। শামসুর অপরাধ – ক্র্যাচে ভর দিয়ে মোহাম্মদ আমিনের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘুরে আমিনের জন্য ভোট চেয়েছিল।
দুর্বাসা আবার জেগে উঠল। শামসুর বাড়ির উত্তর সীমানায় ঢুকে পড়ল দুর্বাসা। ঝড়জলের এক রাতে দুর্বাসা এক গ্রাসে শামসুর বাড়িটা গিলে ফেলল। শামসু মেয়ে আর বউকে নিয়ে সেই আঁধার রাতে ঘর থেকে বের হয়ে আসতে পারল। মা নদীর পেটে গেল। দুদিন পর দুবছরের ফারহানা আর বউকে নিয়ে সর্বস্বান্ত শামসু রেলস্টেশনে উপস্থিত হলো। শামসুর গাভিটা বশিরের গোয়ালে ঠাঁই পেল। সে-রাতে দড়ি ছিঁড়ে নদীর গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিল গাভিটি।
এক সন্ধেবেলা চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে নামল শামসু। তার বগিটা ছিল শেষের দিকে। নেমে দেখল – লোহার ওভারব্রিজ। কন্যা আর বউকে নিয়ে আঁধারে সামনের দিকে পা বাড়াতে সাহস করল না শামসু। ব্রিজের নিচে ঘুপচি জায়গাটিতে গুটিসুটি মেরে রাতটা কাটিয়ে দিলো শামসুর পরিবার।
পরদিন সকালে লাঠির গুঁতায় ঘুম ভাঙল শামসুদের। ‘হালার পুত, বাইর হ’ – গালি শুনতে শুনতে শামসু ঘুপচি জায়গাটি থেকে বেরিয়ে এলো। তার পেছনে নীলু বেগম। নজমুল গলায় বিষ মিশিয়ে বলল, ‘আরে লেইঙ্গাইয়া, হারা রাইত মাইয়াপোয়া বুগত্ লই কাডাইয়ছ। ক’টিঁয়া দিয়ছ মাগিরে।’
শামসু নজমুলের কথার মানে বুঝল না। শুধু বুঝল মাগি শব্দটি। আর রাগী চোখমুখ দেখে বুঝল, লোকটি খারাপ কিছু বলছে। তারপরও শান্ত স্বরে শামসু বলল, ‘কিথা কওরে বাই?’
‘তোর কিথা কওরের মারে চুদি। বাইর হ।’ নজমুল চোখ লাল করে গর্জন করে উঠল।
শামসু মারে চুদি শব্দ দুটোর মানে বুঝল। মুখে কোনো কথা বলল না। শুধু ক্র্যাচটা দিয়ে মজনুর পেটে জোরসে একটা গুঁতা দিল।
‘ওরে মারে’ বলে ধপাস করে বসে পড়ল দারোয়ান নজমুল।
মজনুর আর্তচিৎকার শুনে আশপাশ থেকে দু-চারজন কুলি ও যাত্রী এগিয়ে এলো। এলো সিগন্যালম্যান বদরুল।
বদরুল জিজ্ঞেস করল, ‘কী হইছে নজমুল?’
‘আমি কইরাম’ বলে ক্র্যাচে ভর দিয়ে এগিয়ে এলো শামসু। তারপর সংক্ষেপে জকিগঞ্জ থেকে রেলস্টেশনে নামা, ঘুপচি জায়গায় সপরিবারে রাত কাটানো আর নজমুলের অশালীন ব্যবহার – এসব খুলে বলল।
তারপর গলা উঁচিয়ে বলল, ‘মুক্তিযোদ্ধা আমি। একাত্তরে যুদ্ধেত গেছলাম।’ এরপর নজমুলের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, ‘এই ক্র্যাচ দিয়া যেমন আমি পথ চলি, পথও পরিষ্কার করি এই ক্র্যাচ দিয়া।’
জড়ো হওয়া মানুষগুলো ধীরে ধীরে সরে পড়ল। বদরুল বলল, ‘নজমুল, এরা অসহায় মানুষ। বিপদে পড়ে রাতটা কাটাইছে পুলের নিচে। এদের ওপর অত্যাচার করা তোমার উচিত হয় নাই। তুমি যাও এখান থেকে।’ বদরুল নজমুলের উপরস্থ কর্মচারী। নজমুল কটমট করে শামসুর দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরপায়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।
সেদিন থেকে বদরুলের সঙ্গে শামসুর ভাব হয়ে গেল। বদরুলের বোনকে পাঞ্জাবিরা তুলে নিয়ে গিয়েছিল। পাঞ্জাবিদের যারা শায়েস্তা করেছে শামসু তাদের একজন। বদরুল শামসুকে বলল, ‘তুমি আর এক দুই রাত থাকতে পারবে এখানে। আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি। কিন্তু তার বেশি না। বড়সাহেব জানতে পারলে অসুবিধা হবে। এর মধ্যে তুমি অন্য কোথাও ব্যবস্থা করে নাও।’
সজল চোখে শামসু বলল, ‘ঠিক আছে বাই।’
সেই থেকে শামসু থেকে গেল বটতলি রেলস্টেশনে। টাইগারপাস ওভারব্রিজের নিচে একটা ঝুপড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলো বদরুল। পাশের ঝুপড়ির সেহেলির মায়ের সহযোগিতায় সিটি কলেজের এক অধ্যাপকের বাসায় ঝিয়ের চাকরি নিল নীলু বেগম।
ডানপা-হীন শামসু একদিন মেয়ের হাত ধরে রেলস্টেশনের প্লাটফরমে এলো। ওভারব্রিজের নিচে জড়সড় হয়ে বসে পড়ল। মাথা নিচু করে ডান হাত সামনে প্রসারিত করে সর্বস্বান্ত কপর্দকহীন শামসু বলল, ‘একটা টেকা দিয়া যাওকা বাই, বাত খাইতাম।’ তার পাশে বসে পড়ে বাপকে নকল করে ফারহানা আধো কণ্ঠে বলল, ‘একটা টেকা দিয়া …।’
একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা শামসু ভিক্ষুক হয়ে গেল। যে শামসুর মুখ দিয়ে একসময় বেরোত – জয় বাংলা, সে শামসু এখন বলছে – ‘একটা টেকা দিয়া যাওকা বাই।’ শামসু নিরুপায়। কী করবে সে? কী করারই বা আছে তার? তার একটা পা নেই। সে সামর্থ্য হারিয়েছে। দুর্বাসা তার ভিটে কেড়ে নিয়েছে। বশির তার বাপকে খুন করিয়েছে, পাঞ্জাবি লেলিয়ে তাকে সর্বস্বান্ত করেছে। রাজাকার লিডার বশিরউদ্দিন গাঁয়ে নতুন করে ক্ষমতার আসনে বসেছে। জান এবং মান বাঁচাবার জন্য শামসু গাঁ ছেড়েছে। এখানে এসে জান বাঁচল, মান গেল।
দিন যায়, ফারহানা বড় হয়। চার থেকে পাঁচ, পাঁচ থেকে ছয়। কখনো পাশে বসে বাপের সঙ্গে কণ্ঠ মিলায় – একটা টেকা দিয়া যাওকা, কখনো প্লাস্টিকের বোতলে করে চা আনে। যেদিন দুটো টাকা বেশি জোটে, শামসু শিঙাড়া আনায়। মেয়ের হাতে দিয়ে বলে, ‘খা বেটি খা।’
কোনো কোনো দিন আমড়া খাওয়ার আবদার করে ফারহানা। শামসু একটা টাকা ফারহানার হাতে দিয়ে বলে, ‘যারে মা, একটা আমড়া কিনিয়া আন।’ একদিন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে ফারহানা। তার ডান গালে যেন কিসের দাগ। মোচড়ানো বুকে শামসু জিজ্ঞেস করে, ‘কীথা অইছেরে বেটি? কান্দে কিয়ল্লাগি?’
ফারহানা সজল চোখে বলে, ‘ও বেটা আমার গালে কামড় দিছে।’
‘ক্যাটায় রে? কোন পুঙ্গির পুত কামড় দিছে?’ বসা থেকে উঠতে গিয়ে ডানদিকে ঢলে পড়ল শামসু। ফারহানা ক্র্যাচ এগিয়ে ধরল।
দাঁড়িয়ে শামসু চাপা স্বরে আবার জিজ্ঞেস করল, ‘ক্যাটা? কেমনে এই কাম করল?’
‘চা আনতাম গেছলাম তারেইক্যার দোকানো। ওই যে দাড়িওয়ালা বেটা – আমারে ভিতরে ডাকি নিয়া ডান গালো কামড় দিল। আমিও ওই বেটার নাকো জুরে একখান কামড় বোয়াই দিছি।’ চোখের পানি মুছতে মুছতে ফারহানা বলল।
শামসু হঠাৎ করে শান্ত হয়ে গেল। মাথা নিচু করে কী যেন ভাবল। তারপর নাক দিয়ে বাহির থেকে জোরে বাতাস টেনে নিল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে বলল, ‘তুই ই কিথা কছগো মাই? আমার লগে আয় তো, দূর থেইক্যা আমারে ওই হারামজাদারে দেখাই দিবে।’
মেয়ের হাত ধরে তারেকের দোকানের দিকে গেল শামসু। কালামকে দেখিয়ে ফারহানা বলল, ‘বাবা, ওই বেটা…।’ মেয়ের মুখে হাত চাপা দিলো শামসু। নোংরা কথা মেয়ের মুখ থেকে আর শুনতে চায় না সে। মেয়েকে বলল, তুই একটু আউগ্যা। একটা রিকশারে খাড়া করা। আমি আইয়ার।’ বলে তারেকের চা দোকানের দিকে হন-হন করে এগিয়ে গেল শামসু।
শামসু কালামের মাথা বরাবর একটা জোর বাড়ি দিলো ক্র্যাচ দিয়ে। ‘আল্লা রে’ বলে মাটিতে পড়ে গেল কালাম। কী হয়েছে, কী হয়েছে বলে সবাই ভেতরের ঘরে এগিয়ে গেল। এই ফাঁকে শামসু সটকে পড়ল সেখান থেকে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে মেয়ের ঠিক করা রিকশায় উঠে পড়ল শামসু। রিকশাওয়ালাকে বলল, ‘একটু চালাইয়া যাওবা, আমরার কাম আছে।’
রিকশায় যেতে যেতে শামসু চাপা গলায় মেয়েকে বলল, ‘এরে, হুনগো মাই, আজকোর কথা তোর মাইরে কইছ না। তোর মাই হুনলে দুখ পাইবো।’
পরদিন শামসু আর বটতলি স্টেশনে গেল না। দুদিন ঝিম ধরে ঝুপড়িতে বসে থাকল।
নীলু বেগম জিজ্ঞেস করল, ‘কই তোমারতান এখন কিথা অইলো। ভিক্ষা করতে যাও না ক্যানে?’
স্ত্রীর প্রশ্ন শুনেও কোনো জবাব দিল না শামসু। কাজে যাওয়ার তাড়া থাকায় নীলু তার প্রশ্নটি আর দ্বিতীয়বার করল না। তৃতীয় দিন সকালে শামসু মেয়ে নিয়ে বেরোল। চট্টগ্রামে মেডিকেল কলেজ গেইটের সামনে শামসুর ভিক্ষুকজীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হলো।
এক রাতে নীলু বেগম বলল, ‘স্যারে আমারে কইছইন তোমার পুরিরে পড়াও না কিথার লাগি?’
অন্যমনস্ক শামসু বলল, ‘কোন স্যারে কইছইন?’
‘ওউ আমরার জসিম স্যার আর কী। আমি যে-ঘরও কাম করিয়ার।’
‘কিথা কইছইন কইলায়?’ শামসু নীলুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল এবার।
‘তুমি কিথা চিন্তা করো? আমি কিথা কই তুমি বুঝলায় নানি?’ নীলু বেগম জিজ্ঞেস করে।
শামসু বলল, ‘আমি তো পুরির কথা চিন্তা করিয়ার। পুরি তো সিয়ান হইরো। ই বস্তিত আমরা কিলা থাকমু?’ তারপর দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলল শামসু। নীলু বেগম দেখল – কী যেন একটা লুকাচ্ছে শামসু। তার চোখমুখ, তার গোটা চেহারা কী এক গভীর বেদনায় বিষণœ।
‘তোমার কিথা অইয়ে আমারে ঠিক কইরা কও তো। কুনু ভেজালো পড়ছনি তুমি?’ আচমকা জিজ্ঞেস করে নীলু।
‘না না, কুনতা অইছে না।’ মুখে কিছুই হয়নি বললেও শামসুর অভিব্যক্তি কিন্তু তার কথাকে সমর্থন করে না। তারপরও শামসু নিরুপায়। মেয়ের অপমানের কথা কী করে বাপ হয়ে স্ত্রীকে বলবে সে? কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে সে এ-কথা বলবে যে, ফুলের মতো নিষ্পাপ মেয়েটির ডানগালে কালাম শুয়োরের বাচ্চা লালসার কামড় বসিয়েছে! বাবা হয়ে সে এ-অপমান সহ্য করেছে, ক্র্যাচের বাড়ি দিয়ে কালামকে জানিয়েও দিয়েছে তার প্রতিবাদের ভাষা। কিন্তু নীলু বেগম তো মা! মেয়ের এ-অপমানের কথা জানলে সে মর্মঘাতী হবে। তাকে তা জানানো যাবে না। কিন্তু যখনই সেদিনের কথা মনে পড়ে, বুকটা আনচান করে ওঠে শামসুর। যে-দেশের মাটির পবিত্রতার জন্য সে জান কবুল করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যে-দেশের স্বাধীনতার জন্য তার ডান পা চিরতরে হারিয়েছে, সেই পবিত্র মাটিতে তার মেয়েটি লাঞ্ছিত হলো! এর চেয়ে বড় অপমান তার জন্য আর কী হতে পারে! মাথার রগ টনটন করে উঠল। অনেক কষ্টে শামসু নিজেকে দমন করে রাখল। হাসি হাসি মুখ করে বলল, ‘আমরা তো গরিব মানুষ। পুরিরে কিলা পড়াইমু? পড়ালেখা করাইতে টেকা লাগে নানি?’
‘জসিম স্যার কইছইন – তাইন সব ঠিক কইরা দিবা। তোমার কুনতা চিন্তা করন লাগত না।’ ব্যগ্র হয়ে নীলু বেগম বলল।
শামসু কিছু বলল না। উদাসীন চোখে চেরাগের টিমটিমে আলোয় নীলুর দিকে তাকিয়ে থাকল।
সে-বছর জানুয়ারিতে জসিম স্যার ফারহানাকে ভর্তি করিয়ে দিলো স্কুলে, রেলওয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।
সেই-ই শুরু। ফারহানা আর থামেনি।
বুদ্ধি হবার পর থেকেই ফারহানা বাবার মুখে একটু একটু করে শুনেছে মুক্তিযুদ্ধের কথা, যুদ্ধে বাবার বীরত্বের কথা। সে যখন আরো বড় হলো, তখন শুনল – বশিরউদ্দিনের অত্যাচারের কথা, তার দাদার হত্যার কথা। পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে বশিরদের ক্ষমতা দখলের কথা শামসু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে গেছে ফারহানার কাছে। এই বশিরউদ্দিনের চক্রান্তে শামসু সর্বহারা হয়েছে, গ্রাম ত্যাগ করে পথের ভিখিরি হতে বাধ্য হয়েছে – এসব কথা শামসুর কাছে শুনেছে ফারহানা। শুনে শুনে তার ভেতরে প্রচণ্ড ঘৃণা কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছে। পিতার কষ্ট এবং পরিবারের অপমানের দৃশ্যগুলো সে নিজের মধ্যে তৈরি করে নিয়েছে। সেই কল্পিত দৃশ্যগুলো যখন তার চোখের সামনে দিয়ে একের পর এক ভেসে যায়, সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অদেখা বশিরউদ্দিনের একটা ছবি সে নিজের মধ্যে কল্পনা করে নেয়। মনে মনে সেই ছবিতে থুতু ছিটায়, যখন-তখন।
একটা সময়ে ওভারব্রিজের বস্তিতে টেকা মুশকিল হয়ে উঠল শামসুদের। আশপাশের ঝুপড়ির মাথা তোলা ছাওয়ালরা চুরি-চামারি করে, রেলস্টেশনের ঘুপসি-ঘাপসি এলাকায় ছোটখাটো ছিনতাই-জোচ্চুরিও করে। কেউ কেউ ছুটকো-ছাটকা কুলিগিরি করে। মেয়েরা পিঠে বস্তা ঝুলিয়ে প্লাস্টিকের বোতল, ছেঁড়া জুতা, কাগজের টুকরো – এসব কুড়িয়ে যায় সারাদিন। কেউ কেউ মায়েদের সঙ্গে বাসাবাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতে যায়। শামসুর বউ নীলু বেগম বাসাবাড়িতে কাজ করতে গেলেও তার মেয়ে ফারহানা যায় স্কুলে। এ নিয়ে টিটকারি-উপহাসের শেষ নেই। আশপাশের মানুষের মধ্যে ঈর্ষাও কাজ করে প্রবলভাবে। নানা কটুকাটব্য শুনতে শুনতে শামসুরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ঠিক এই সময়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ফারহানা তখন ক্লাস এইটে পড়ে। দুপুরে ছুটিতে ভাত খেতে এসেছে ঘরে। সকালেই রান্না করে যায় নীলু বেগম। দুপুরে বাপ ভিক্ষায়, মা ঝিগিরিতে। মাথা নিচু করে ডালের সঙ্গে ভাত মাখছে ফারহানা। ওই সময় পাশের ঝুপড়ির সিরাজের বাপ ঘরে ঢোকে। জাপটে ধরে ফারহানাকে। মাটিতে চেপে ধরার আগে পানিভর্তি গ্লাস দিয়ে সিরাজের বাপের কপালে আঘাত করে ফারহানা। ‘অ-মারে’ বলে দ্রুত ঝুপড়ি থেকে বের হয়ে যায় সিরাজের বাপ। কপাল ফাটে না, কিন্তু আস্ত একটা সুপারি জেগে ওঠে তার কপালে।
অনেকক্ষণ ঝিম ধরে বসে থাকে ফারহানা। হঠাৎ করে ছোটবেলার চা-দোকানের দাড়িওয়ালা লোকটির কথা মনে পড়ে যায় ফারহানার। ওই সময় লোকটির কামড়ের অর্থ তেমন করে বোঝেনি সে। কিন্তু আজ পুরুষচরিত্রের সবকিছু সে বুঝে গেল। একবার মনে হলো¬ – বাপ-মা ফিরে এলে আদ্যোপান্ত খুলে বলবে। কিন্তু তার চোখের সামনে বাবার সেই দিনের মর্মাহত চেহারা ভেসে উঠল। বাপের ওই বেদনাময় অসহায় চোখ তাকে দীর্ঘদিন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। না, মা-বাপকে বলা যাবে না আজকের লাঞ্ছনার কথা। সে ঠিক করল – আজকের ঘটনার বিন্দুবিসর্গও মা-বাবাকে জানাবে না। জানালে শুধু দুঃখ বাড়বে মা-বাবার। হয়তো সিরাজের বাপের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়বে তারা। চার-পাঁচটা পোলা সিরাজের বাপের। যদি মারামারি লাগে, তাহলে পঙ্গু বাপ তার পড়ে পড়ে মার খাবে। তার চেয়ে কিল খেয়ে কিল হজম করে যাওয়া ভালো।
সে-রাতে ঘুম আসেনি ফারহানার। মা-বাবার পাশে শুয়ে চোখের দু’পাতা একত্র করতে পারেনি সে। চক্রাকারে বারবার এক পলকের দেখা সিরাজের বাপের লোভী চোখ তাকে গিলে খেতে চাইছিল। মনের মধ্যে গভীর একটা ব্যথা চনমনিয়ে উঠল। বলল, ‘বাবা তুমি হজাগ আছনি?’
শামসু বলে, ‘অয়গো মাই। তুই কুনথা কইবিনি আমারে?’
‘বাবা, আমি ইখানো আর থাকতাম পারতাম না। আইয়ো আমরা আর কুনুখানো যাইগি।’ বিষণœ গলায় ফারহানা বলে।
নীলু বেগম বলে, ‘ক্যানে গো মাই? কিথা অইছে তোর? আমারে ক’তো তুই।’
মায়ের প্রশ্নের কোনো জবাব দেয় না ফারহানা। অন্ধকারে বাপের দিকে তাকিয়ে থাকে শুধু।
দীর্ঘক্ষণ শামসু কথা বলে না। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে – কোনো একটা কিছু হয়েছে। এমন একটা কিছু ঘটেছে, যা মেয়ে তাকে বলতে চাইছে না। অথচ অসহনীয় যন্ত্রণায় ভেতরে ভেতরে কাতরাচ্ছে সে।
অনেকক্ষণ পরে শান্ত কণ্ঠে শামসু বলে ওঠে, ‘আমরা ইখান থাইক্যা এমনি যাইমু গিয়াগো মাই। জলদি যাইমু গো মাই।’
ঝাউতলার বস্তিতে বাসা ভাড়া নিল শামসু। বস্তিওয়ালারা জানে না শামসু কী কাজ করে; শুধু জানে – শামসুর বউ নীলু বেগম কোনো এক কলেজের প্রফেসরের বাসায় কাজ করে।
এভাবে চলে গেছে অনেক দিন, অনেকটা বছর। এস. এস. সি, এইচ. এস. সি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে ফারহানা। টিউশনি শুরু করার পর বাবার ভিক্ষা করা বন্ধ করিয়েছে। বলেছে, ‘বাবা, আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। মুক্তিযোদ্ধা ভিক্ষা করে জীবন কাটাল। আর না বাবা। আমি আয় করছি। মা আর আমার আয় দিয়ে কোনোভাবে আমাদের চলে যাবে।’
শামসুর এখন কোনো কাজ নেই। প্রতিদিনের বাঁধাধরা ভিক্ষাবৃত্তি থেকে সে এখন মুক্ত। সকালে ভেতরটা খলবলিয়ে ওঠে। মুখ দিয়ে নিজের অজান্তে বেরিয়ে আছে, ‘একটা টেকা দিয়া যাওকা বাই।’ নিজেকে সংযত করে। মেয়ে যায় ইউনিভার্সিটিতে, বউ যায় বাসার কাজে। শামসু বসে বসে যুদ্ধের কথা ভাবে, পা হারানোর কথা ভাবে, বশিরউদ্দিনের কথা ভাবে। যেদিন লালদীঘির ময়দানে বা শহীদ মিনারের চত্বরে জনসভা হয়, ক্র্যাচে ভর দিয়ে সেদিন ওই সব সভায় যায় শামসু। দূরে দাঁড়িয়ে নেতাদের ভাষণ শোনে। প্রলাপ বকে নেতারা। মিথ্যের আবরণ দিয়ে সত্যকে লুকানোর চেষ্টা দেখে, অহেতুক আস্ফালন দেখে ঘৃণায় গা রিরি করে শামসুর। একদলা থুতু মাটিতে ফেলে সে। তারপর হাঁটতে থাকে সামনের দিকে।
আজ এম.এ-র রেজাল্ট বের হয়েছে। ফারহানা পাস করেছে। সৈকত বলল, ‘চল, তোকে আমি পরোটা-মাংস খাওয়াবো। দারুল কাবাবে চল।’
‘কেন তুই আমাকে মাংস-পরোটা খাওয়াবি?’
‘তুই পাস করেছিস, তাই?’
‘তুই পাস করিসনি।’
‘হ্যাঁ, করেছি।’ আমতা আমতা করে বলল সৈকত।
‘তাহলে আমি খাওয়াবো না কেন তোকে?’ সৈকতের চোখে চোখ রেখে বলল ফারহানা।
‘না, বলছিলাম কী – আমি, আমি টিউশনির টাকা পেয়েছি।’
‘আমিও তো পেয়েছি। চল তো সৈকত, আমি আজকে তোকে খাওয়াবো। না করিস না তুই।’ ব্যগ্র গলায় ফারহানা বলল।
দারুল কাবাবের সামনের চত্বরে দুজনে মুখোমুখি বসল। খাবারের অর্ডার দিয়ে দুজনেই চুপচাপ বসে থাকল।
হঠাৎ সৈকত জিজ্ঞেস করল, ‘আচ্ছা ফারহানা, মুনতাসীর মামুনের শান্তি কমিটি : ১৯৭১ বইটা বিষয়ে এত আগ্রহ কেন তোর?’
ফারহানা কোনো জবাব দেয় না। উদাস চোখে দূরের সেগুনগাছের দিকে তাকিয়ে থাকে। সৈকত অপেক্ষা করতে থাকে ফারহানার জবাবের জন্য।
‘তুই আমার প্রকৃত পরিচয় জানিস না। জানাতে চাইওনি আমি কোনোদিন। পরিচয় দেওয়ার মতো আমার তেমন কিছু নেই।’ বলে হঠাৎ করে চুপ মেরে যায় ফারহানা।
যেমন হঠাৎ কথা বলা বন্ধ করেছিল, তেমনি হঠাৎ আবার কথা বলা শুরু করল ফারহানা, ‘আমার বাসায় তুই কখনো যেতে চাসনি; অবশ্য যেতে চাইলেও তোকে কোনোদিন আমার বাসায় নিতাম না।’
‘কেন?’ আলতো করে জিজ্ঞেস করে সৈকত।
‘কারণ আমার বাবা ভিক্ষুক আর মা কাজের বেটি।’ দূরের বাতাসে ভর করে সৈকতের কানে কথাগুলো ভেসে এলো।
চমকে ফারহানার দিকে তাকাল সৈকত। ফারহানা বলে যেতে লাগল, ‘আমাদের একটা ছোট্ট গ্রাম ছিল, একটা নদী ছিল, চড়–ই ডাকা দুপুর ছিল, পুকুর ছিল, গোয়াল ছিল। সবকিছু বাবাকে হারাতে হয়েছে।’ তারপর গলায় উন্মাদনা ঢেলে ফারহানা বলল, আমার বাপ মুক্তিযোদ্ধা ছিল। বাবা যুদ্ধে যাবার অপরাধে পাঞ্জাবিরা দাদাকে হত্যা করেছে। ঘরে আগুন দিয়েছে বশিরউদ্দিন।’
‘বশিরউদ্দিন কে?’ উদ্গ্রীব কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে সৈকত।
‘তার জন্যই তো আমার শান্তি কমিটি : ১৯৭১ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া। বশিরউদ্দিন চরখানপুরের শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। ও বিমলকে ইজ্জত আলী বানিয়েছে। পাঞ্জাবিদের নিয়ে এসেছে গ্রামে। আমাদের উঠানেই আমার দাদাকে গুলি করিয়েছে। তার জন্যই আমার বাবা পা হারিয়েছে।’
সৈকত ত্বরিত জিজ্ঞেস করল, ‘পা হারিয়েছে মানে?’
আমার বাবার ডান পা নেই। যুদ্ধে পাঞ্জাবিরা গুলি করে আমার বাবার পা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। বশিরউদ্দিনদের মতো মীরজাফররা যদি পাঞ্জাবিদের দোসর না হতো, আমার বাপকে যুদ্ধে যেতে হতো না। ঢাকা থেকেই ফিরে যেতে বাধ্য হতো ওই হায়েনার দল। যুদ্ধে না গেলে আজকে আমাকে ভিক্ষার টাকা দিয়ে বড় হতে হতো না।’ তারপর একটু দম নিল ফারহানা। ধীরে ধীরে বলল, মামুন স্যার দেশের নানা জেলার শান্তিকমিটির চেয়ারম্যানের নামের তালিকা দিয়েছেন তাঁর বইয়ে। ‘মামুন স্যারের ওই বইতে বশিরউদ্দিনের নাম আছে কিনা দেখেছি। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে গেছি, কিন্তু বশিরউদ্দিনের নাম খুঁজে পাইনি। তুই আমাকে বইটা দেওয়ার পর আরো ভালোভাবে দেখার সুযোগ পেরেছি আমি। বশিরউদ্দিনের নাম নেই ওই বইতে।’
খাবার টেবিলে এলে মৃদু কণ্ঠে সৈকত বলে, ‘খা’।
খাবারের দিকে নজর না দিয়ে ফারহানা বলে, ‘আমি ছাড়ব না। আমি মুনতাসীর মামুন স্যারের সঙ্গে আমার বাবাকে নিয়ে দেখা করব। বাবার মুখ দিয়ে দাবি জানাব – ওনার বইটিতে যাতে বশিরউদ্দিনের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন।’
‘তাতে তোর লাভ’! সৈকত খাবার মুখে তুলে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করে।
ফারহানা সৈকতের কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলে, ‘ওই দিন যে আমি মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা চাই, দিতে হবে বলে চিৎকার দিয়ে উঠেছিলাম, এখন তার কারণ তুই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিস।’ তারপর কঠোর কণ্ঠে বলল, ‘বশিরউদ্দিনের নাম বইটিতে অন্তর্ভুক্ত করাতে পারলে আমার ব্যক্তিগত কোনো লাভ হবে না সত্যি, কিন্তু এইটুকু লাভ তো হবে – দেশের একজন আসল শত্র“র নাম দেশবাসী জানতে পারবে। বশিরউদ্দিন নামের কোলাবরেটরের নামে একদলা থুতু ছিটাবে।’
তারপর মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে ফারহানা বলে, ‘এ দেশে বড় বড় যুদ্ধাপরাধীর বিচার হচ্ছে। আমি, আমার বাবা, আমার মা অপেক্ষা করে আছি – একদিন না একদিন কুখ্যাত শান্তিকমিটির চেয়ারম্যানদের বিচার হবে। তখন ওইসব চেয়ারম্যানের তালিকা দরকার হবে। মুনতাসীর স্যারের বইটির দরকার হবে তখন! ওই বইতে বশিরউদ্দিনের নাম থাকলে তারও বিচার হবে। ফাঁসি হবে তার।’ বলতে বলতে কেঁদে ফেলল ফারহানা।
সৈকত তার বাঁ-হাতটি দিয়ে ফারহানার ডান হাতটি স্পর্শ করল।