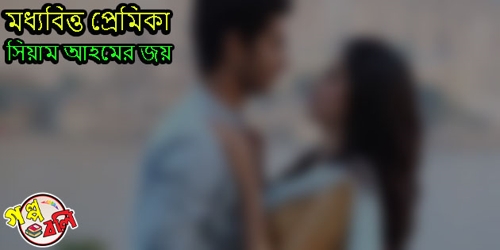খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে হঠাৎই চোখ তুলে তাকিয়েছি, দেখি ফ্ল্যাটের দরজায় একটি শিশু দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েশিশু। রোগা, ফর্সা, মাথায় লালচে ধরনের পাতলা চুল। শরীরের তুলনায় মাথাটা যেন একটু বড়। মুখটা মিষ্টি, চোখদুটো ডাগর।
নটার মতো বাজে। আমার সামনে কাচের সেন্টার টেবিল। তার ওপর একগাদা দৈনিক পত্রিকা। নামকরা কাগজগুলো ধরে-ধরে আমি চেক করছি। কোন কাগজ কী লিড করলো, কোন জরুরি নিউজ আমাদের কাগজ মিস করলো ইত্যাদি দেখছি। পায়ের কাছে এক লিটারের পানির বোতল। আটটার দিকে কাগজ নিয়ে বসেছি এই এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ধীরে-ধীরে পানিটাও খেয়েছি। বোতল প্রায় শেষ। এখন অর্ধেকটা এমারিল খাবো। দশ মিনিট পর খাবো একটা গ্যালভাস। তার দশ মিনিট পর নাশতা। টেবিলে জাহাঙ্গীর সব রেডি করে রেখেছে।
বাচ্চাটা কে?
দেখে বোঝা যায় ফ্ল্যাট-বাসিন্দাদের কারো বাচ্চা না। চেহারা-পোশাকে দারিদ্রে্যর ছাপ। কোনো ফ্ল্যাটের বুয়াদের বাচ্চা হবে।
আমার ধারণাই ঠিক।
পাশের ফ্ল্যাটের গেট খুলে একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। মলিন সালোয়ার-কামিজ পরা। ফর্সা মুখ ঘামে ভেজা, রোগা এবং বিষণ্ণ। কাজের মেয়ে বোঝা যায়। আমার দরজায় শিশুটিকে দেখে তার হাত ধরলো। মুখে বিরক্তির চিহ্ন। বেরিয়েছিস কেন? আমি কি কাজ করবো না তোকে আগলাবো? আর যদি দরজা খুলে বেরিয়েছিস!
বিব্রত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালো। আমি পাশের ফ্ল্যাটে কাজ করি সাহেব। আমার মেয়ে কোন ফাঁকে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে। আপনি কিছু মনে করবেন না।
না, না মনে করার কী আছে? বাচ্চার নাম কী?
মেয়েটি তার বাচ্চার দিকে তাকালো। নাম বলো।
পাখির মতো মিষ্টি গলায় শিশুটি বললো, জয়া।
বাহ! খুব সুন্দর নাম। দাঁড়াও-দাঁড়াও।
ফ্রিজে কিছু ক্যান্ডি আমি সবসময়ই রাখি। ফ্লিকার মার্স, সাফারির ওয়েফার।
সন্ধ্যার দিকে মাঝে-মাঝে সুগার কমে যায়। তখন খাই। সুগার না কমলেও কখনো-কখনো খাই। ডায়াবেটিসদের যা হয় আর কি! মিষ্টিজাতীয় জিনিস দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে।
একটা ফ্লিকার এনে জয়ার হাতে দিলাম।
এই ফ্লিকার দেওয়া থেকেই শুরু হলো ঘটনা।
এখন বলি, দিনটা শুরু করি কীভাবে?
ঘুম ভাঙে ভোর পাঁচটায়। উঠেই ওয়াশরুমে গিয়ে মুখটা ভালো করে ধুই। তারপর চলে যাই লেখার রুমে। একটানা তিন ঘণ্টা লিখি। সাতটার দিকে উঠে জাহাঙ্গীর লেগে যায় তার কাজে। অর্থাৎ আমার নাশতা তৈরি করা। এক বাটি সবজি, দুখানা মাঝারি সাইজের আটার রুটি, বড় লেবুর এক টুকরা লেবু, দুখানা ফুল বয়েলড ডিম, দশ-বারো টুকরা পাকা থাই পেঁপে, এই আমার নাশতা। ডিমদুটোর শুধু সাদা অংশ প্রতিদিনই খাই। সপ্তাহে তিনদিন খাই একটা করে কুসুমসহ ডিম। ডাইনিং টেবিলের পাশে ওষুধের ব্যাগ। নাশতার বিশ মিনিট আগে হাফ এমারিল, দশ মিনিট আগে একটা গ্যালভাস। দেশের তৈরি গ্যালভাস খাই না। আমারটা সুইজারল্যান্ডের তৈরি। দুটোই ডায়াবেটিসের ওষুধ।
নাশতার সর্বশেষ আইটেম পাকা পেঁপে। তার আগে একটা ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট আর একটা এ টু জেড ভিটামিন ট্যাবলেট। নাশতার মিনিট দশেক পর প্রেশারের ওষুধ এমডোকল একটা আর কার্ডিওকর একটা। বছর পাঁচেক ধরে এই নিয়মে চলছি।
আমার দেখভালের দায়িত্ব জাহাঙ্গীরের। বছর পঁয়ত্রিশের যুবক। প্রথম স্ত্রী সানজি নামের বছর চারেক বয়সের একটি মেয়ে রেখে জাহাঙ্গীরকে ছেড়ে চলে যায়। জাহাঙ্গীর তারপর আবার বিয়ে করে। সৎমা এসে সানজির সঙ্গে সৎমায়ের মতোই আচরণ শুরু করে। সানজিকে ঠিকঠাকমতো খেতে দেয় না। মারধর করে। এই দেখে মেয়েটিকে বুকে তুলে নেয় জাহাঙ্গীরের বড় বোন নূরজাহান।
নূরজাহান বহু বছর ধরে কাজ করে আমার মগবাজারের ফ্ল্যাটে। আমার স্ত্রীর দিক থেকে পরিচিত। ওদের বাড়ির কাছেই, লুপ্ত হয়ে-যাওয়া ধোলাইখালের পশ্চিম পাশে বহুকালের পুরনো একটা মন্দির। মন্দির-আঙিনায় ঘর তুলে থাকে কয়েকটি পরিবার। নূরজাহানরা থাকতো ওখানে।
জায়গাটা গেন্ডারিয়াতে। মন্দিরের জায়গাটা পড়েছে কলুটোলায়। ওদের পরিবারের অনেকেই আমার শ্বশুরবাড়িতে কাজ করতো। পরে নূরজাহান চলে আসে আমার সংসারে। দীর্ঘদিনের কাজের লোকদের সঙ্গে একধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। মালিকদের কাছে কাজের লোকদের অধিকারবোধ জন্মায়। নূরজাহানের তেমন এক অধিকারবোধ জন্মেছে আমাদের ওপর।
সানজিকে নিয়ে একদিন সে আমাদের ফ্ল্যাটে এলো। আমার স্ত্রীকে খুলে বললো সব ঘটনা। সানজিকে সে তার সঙ্গে আমাদের ফ্ল্যাটেই রাখতে চায়। মেয়েটির মায়াবী মুখ দেখে নূরজাহানের কথা আমরা ফেলতে পারিনি। সানজি আমাদের সংসারে থেকে গেল।
নূরজাহানের স্বামী একসময় কোনো এক ফ্যাক্টরিতে সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করত। তিনটি ছেলেমেয়ে তাদের। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে বরিশালে। তার অবস্থা ভালোই। মেজোটা ছেলে। সে বাংলাবাজার এলাকায় ব্লক তৈরির কাজ করে। ছোট মেয়েটার নাম বর্ষা। সে ফাইভে না সিক্সে যেন পড়ে।
স্বামীর সঙ্গে নূরজাহানের বয়সের ব্যবধান অনেক। লোকটা এখন আর কিছু করে না। বউ ছেলের রোজগারে বসে-বসে খায়। বড় মেয়েও সাহায্য করে। সপ্তাহ দশদিন পর এক বেলার জন্য নূরজাহান স্বামী-ছেলেমেয়ে দেখতে যায়। তবে মোবাইলে খবর নেয় রোজই একবার-দুবার।
নূরজাহানের রান্নার হাত অসাধারণ। তার হাতের ছোঁয়ায় অতিসামান্য খাবারও অসামান্য হয়ে যায়। নূরজাহানের রান্নায় আমরা তো বটেই আমাদের চারপাশের আত্মীয়স্বজনরা পর্যন্ত মুগ্ধ।
আমার স্ত্রী সানজিকে একসময় স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। ভালো খাওয়া-দাওয়া আর জামা-কাপড়ে মেয়েটির রূপ খুলতে লাগল। সানজির রূপে আমাদের ফ্ল্যাট আলোকিত হয়ে উঠল। মাঝে-মাঝে সে নূরজাহানের সঙ্গে গেন্ডারিয়ায় গিয়ে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে দেখা করে আসে। বাবার জন্য ব্যাপক টান।
এই মেয়েটি অদ্ভুত এক দুর্ঘটনায় মারা গেল।
সকালবেলা স্কুল থেকে ফিরছে, সঙ্গে আমাদের আরেকজন বুয়া। রাস্তার ধারের এক বাড়ির লোহার গেট ভেঙে পড়ল সানজির ওপর। বুয়া আর সে একসঙ্গেই হাঁটছিল। বুয়ার কিছুই হলো না, চাপা পড়লো সানজি। লোকজন কোলে করে তাকে আদ-দ্বীন হাসপাতালে নিয়ে গেল। বুয়া কাঁদতে-কাঁদতে এসে আমাদেরকে খবর দিলো। আমি সেদিন বাসায়। ছুটে গেলাম হাসপাতালে। ডাক্তাররা বললেন বঙ্গবন্ধু মেডিক্যালে নিয়ে যেতে। নিয়ে গেলাম। ঘণ্টা দুয়েক পর সানজি মারা গেল।
সানজিকে নিয়ে আমি একটা গল্প লিখেছিলাম। ‘সানজির গল্প’। সেই গল্প পড়ে ফোনে ধ্রুব এষ হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। খুবই আবেগপ্রবণ, নরম হূদয়ের মানুষ। ও যে-মাপের রংতুলির শিল্পী, ছোটদের লেখায় একেবারেই ভিন্ন মাত্রার এক লেখক, ওর তো এমনই হওয়ার কথা। দেখতেও সাধুসমেত্মর মতো। ধ্রম্নবকে আমি খুবই ভালোবাসি।
সানজির মৃত্যু আমাদের পরিবারে গভীর ছায়া ফেলেছিল।
এই ঘটনার তিন-চার বছর পর জাহাঙ্গীরের আবির্ভাব। সে একসময় চায়ের দোকানদার ছিল। বাংলাবাজার এলাকার ফুটপাতে বসে চা বিক্রি করতো। সানজির মা খুব সুন্দরী ছিল। সে চলে যাওয়ার পর, সানজির মৃত্যুর পর ধস নেমে গেল জাহাঙ্গীরের জীবনে। চা বিক্রির টাকায় সংসার চলে না। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে একটি মেয়ে জন্মেছে। তাদের নিয়ে দুর্বিষহ কষ্টের দিন।
এ সময় আমার জীবন বাঁক নিয়েছে অন্য দিকে। দেশের বৃহত্তম শিল্প গোষ্ঠী ‘বসুন্ধরা গ্রুপের’ কালের কণ্ঠ পত্রিকায় আমি জয়েন করেছিলাম জয়েন্ট এডিটর হিসেবে। তেমন কোনো কাজ নেই। যখন ইচ্ছা অফিসে আসি, যখন ইচ্ছা চলে যাই। অফিস থেকে গাড়ি দেওয়া হয়েছে। ওই নিয়ে ঘুরে বেড়াই। মাঝে-মাঝে ঢাকার বাইরে যাই পত্রিকার কাজে। পত্রিকা-সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে বেড়াই সারা দেশে। আমাকে নেওয়াও হয়েছিল এসব কাজের জন্যই।
বছর দেড়েকের মাথায় সম্পাদক চাকরি ছেড়ে চলে গেলেন। গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং এমডি আমাকে ডেকে নিয়ে সম্পাদকের চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। এত বড় দায়িত্ব পড়লো মাথায়, আমি খুবই দিশেহারা। অফিস বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায়। প্রথমেই মনে হলো মগবাজার থেকে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় কালের কণ্ঠ অফিসে আসতে-যেতে দুঘণ্টা-দুঘণ্টা চার ঘণ্টা সময় চলে যাবে। তাহলে? সম্পাদকের কাজ তো চবিবশ ঘণ্টার! ম্যানেজ করবো কী করে?
চেয়ারম্যান সাহেবকে বললাম, এমডি সাহেবকে বললাম। শুনে তাঁরা আমাকে তিন হাজার স্কয়ার ফিটের একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে দিতে চাইলেন অফিসের কাছে। ভাড়া ষাট হাজার টাকা, অফিস দেবে। ফ্ল্যাট সাজাতে যা-যা লাগে তাও দেবে। শুনে আমার স্ত্রী বললেন, আমরা মগবাজারেই থাকি, তুমি গিয়ে ওই ফ্ল্যাটে থাকো। প্রতি শুক্রবারে এসে আমাদের সঙ্গে থেকে যেও।
ঠাট্টা করে বললেন, তোমার এখন পঞ্চান্ন বছর বয়স, আমিও পঞ্চাশের কাছাকাছি। এই বয়সে দুজন দুদিকে থাকলে অসুবিধা কী?
কদিন পর বড়মেয়ের বিয়ে দেব। দু-তিন বছর পর দেব ছোটটার। ছেলে এখনো ছোট। তুমি তোমার মতো থাকো, আমি থাকি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার মতো। মাঝে-মাঝে দেখা হবে, এই যথেষ্ট।
আইডিয়া মন্দ লাগলো না। মনে পড়লো আমার বাবার কথা।
বাবাকে আমরা ডাকতাম আববা। ষাটের দশকের গোড়ার দিককার কথা। আমার বয়স পাঁচ-ছ বছর। বিক্রমপুরের মেদেনীম-ল গ্রামে নানাবাড়িতে থাকি। আববা চাকরি করেন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে। স্ত্রী-সন্তানসন্ততি রেখেছেন শ্বশুরবাড়িতে। তখনকার দিনে শনিবারে হাফ অফিস, রোববারে ছুটি। শনিবার অফিসে হাজিরা দিয়েই সদরঘাটে গিয়ে লঞ্চে চড়তেন আববা। মিউনিসিপ্যালিটি অফিসটা ছিল লক্ষ্মীবাজারে। সেখান থেকে সদরঘাট কয়েক মিনিটের হাঁটা রাস্তা।
শেষ বিকেল কিংবা গোধূলি বেলায় আববা গিয়ে হাজির হতেন আমার নানাবাড়িতে। কাঁধে একটা রেক্সিনের ব্যাগ, দুহাতে দুটা চটের ব্যাগ। আয়-রোজগারের সাধ্যানুযায়ী আমাদের জন্য পাউরুটি বিস্কুট সাগরকলা ইত্যাদি-ইত্যাদি নিয়ে যেতেন। শনিবার আর রোববার রাত আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে সোমবার ফজরের লঞ্চে ঢাকায় রওনা দিতেন।
আমিও কি আববার সেই পথ ধরবো? ঢাকায় থেকেও ঢাকা-বিক্রমপুরের জীবন! ষাটের দশকের মতো।
ধরলাম পথটা। ঠিক আছে, সপ্তাহে ছদিন থাকি বসুন্ধরায়। শুক্রবার ডে-অফ। বৃহস্পতিবার রাতে মগবাজারে এসে শনিবার সকালে ফিরে গেলেই হলো।
কিন্তু তিন হাজার স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাট দিয়ে কী করবো? এতবড় ফ্ল্যাটে একা একজন লোক থাকে কী করে?
আমার ছোটমেয়েটি ঠাট্টাপ্রিয়। সে বলল, বাবা, তুমি একটা বিয়ে করে নাও!
আমি হাসিমুখে স্ত্রীর দিকে তাকালাম। তুমি কী বলো?
আমার কোনো আপত্তি নেই। এই বয়সে তোমার মতো পচা চেহারার লোককে কেউ বিয়ে করবে না। আমি নিশ্চিত।
কিন্তু তিন হাজার স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাট!
আমার কিঞ্চিৎ ভূতের ভয় আছে। একা ঘরে থাকতে পারি না। বিদেশে গেলে হোটেলের রুমে সারারাত লাইট জ্বালিয়ে রাখি। ঢাকার বাইরে গেলেও একই অবস্থা। একা ঘরে মনে হয় চোখ মেললেই দেখবো আজদাহা কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে সামনে। পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে কেউ। বুকের ওপর চেপে বসেছে অশরীরী আত্মা।
না, এতবড় ফ্ল্যাটের দরকার নেই। কোম্পানির টাকা নষ্ট হবে, আমারও সেভাবে থাকা হবে না। চেয়ারম্যান সাহেবকে খুলে বললাম সব। শুনে তিনি আমাকে ট্যানামেন্ট হাউসের দশটা বিল্ডিংয়ের একটাতে এগারো-বারোশো স্কয়ার ফিটের একটা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দিলেন। ছোট পরিবার থাকার জন্য চমৎকার ফ্ল্যাট। কোম্পানির নিজস্ব ফ্ল্যাট। ভাড়ার বালাই নেই। মাঝারি সাইজের তিনটা বেডরুম। মোটামুটি প্রশস্ত ড্রয়িং-ডাইনিং। সোফা ফ্রিজ ডাইনিং টেবিল, তিন-চারটা বুক শেলফ, বেডরুমে যা-যা লাগে সব। একটা লেখার রুম, আরেকটা রুম ফাঁকা। ওই রুমে আমার দেখাশোনার লোক থাকবে।
দেখাশোনার লোক হিসেবে জাহাঙ্গীরের আগমন।
বসুন্ধরায় ফ্ল্যাট রেডি হয়েছে শুনে স্ত্রী চিন্তিত হলেন। আমার দেখভালের জন্য কাকে দেবেন ওই ফ্ল্যাটে। ছোট্ট একটা পরিবার হলে ভালো হয়। ফাঁকা রুমটায় থাকবে। চলার মতো বেতন দেওয়া হবে। শুনে নূরজাহান বলল জাহাঙ্গীরের কথা। বেকার, সংসার চালাতে পারে না। তিন বছরের একটা মাত্র মেয়ে। সেই মেয়েও চুপচাপ ধরনের। আমার কোনো ডিস্টার্ব হবে না। জাহাঙ্গীর খুবই কর্মঠ যুবক। হাজার বারো টাকা বেতন দিলেই হবে।
জাহাঙ্গীর এসে যুক্ত হলো আমার সঙ্গে।
সবই ঠিক ছিল। জাহাঙ্গীরের বউর পেটে যে আরেকটি বাচ্চা এই কথাটা নূরজাহান এবং জাহাঙ্গীর দুজনেই আমাদের কাছে চেপে গিয়েছিল। মাস দুয়েকের মধ্যে যখন জানলাম তখন আর কী করা! জাহাঙ্গীর অনেকখানি মানিয়ে নিয়েছে আমার সঙ্গে।
যথাসময়ে তাদের একটা পুত্রসন্তান হলো। হাসপাতাল ইত্যাদির খরচ আমিই দিলাম। সমস্যা দেখা দিলো নবজাতকটিকে নিয়ে। সারাদিন তার কোনো আওয়াজ নেই। আমি রাতে বাসায় ফেরার পরেই সে ত্রাহি ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকে। রাত বারোটার দিকে শুরু করে ভোর চারটা পর্যন্ত একটানা কাঁদে। আমার খুবই ডিস্টার্ব হয়।
এক্ষেত্রেও সহায়ক হলেন স্ত্রী। জাহাঙ্গীরকে বললেন তিন-চার হাজারের মধ্যে কাছাকাছি কোথাও একটা রুম ভাড়া করে বউ-বাচ্চা রাখতে। দিনেরবেলা সে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে আসবে রাতেরবেলা আমার সঙ্গে এসে ফ্ল্যাটে থাকবে। রুম ভাড়ার টাকাটা আমরা দিয়ে দেবো।
জাহাঙ্গীর সত্যিই করিৎকর্মা। দিন পনেরোর মধ্যেই সেভাবে সব গুছিয়ে ফেলল। টেনাম্যান্ট হাউসের ফ্ল্যাটে শুরু হলো দুই বিবাহিত ব্যাচেলরের জীবন। সপ্তাহে ছয়দিন আর পাঁচ রাত্রির জীবন।
দিনে-দিনে এই জীবনে আমরা দুজনই অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। আমি আর জাহাঙ্গীর।
সাড়ে নটার দিকে আমি নাশতা করতে বসি। জাহাঙ্গীর এক মগ চা আর তিনখানা রুটি নিয়ে চলে যায় তার রুমে। চায়ে ভিজিয়ে-ভিজিয়ে রুটি খায়। এই তার নাশতা।
ওষুধ খাওয়া শেষ করে খানিক পায়চারি করি আমি। ফোনে স্ত্রী-কন্যাদের সঙ্গে কথা বলি। ইতোমধ্যে বড়মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এক বছর আমেরিকায় কাটিয়ে মেয়ে মেয়ের জামাই দুজনেই দেশে ফিরেছে। জামাই একটা ইউনিভার্সিটির লেকচারার। মেয়ে ব্যাংকে চাকরি করে। শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে মোহাম্মদপুরে থাকে। ভালোই আছে। ছোটমেয়ে নর্থ সাউথে বিবিএ পড়ছে। আমার অফিসের কাছেই তার ক্যাম্পাস। ইউনিভার্সিটিতে আসতে-যেতে দুঘণ্টা করে চার ঘণ্টা সময় যাচ্ছে তাতে, তার কিছুই যেন আসছে যাচ্ছে না। দু-একবার বলেছি, আমার বসুন্ধরার ফ্ল্যাটে থাক। তাতে কষ্ট কম হবে। সে থাকবে না। মগবাজারের ফ্ল্যাটে নিজের রুম ছাড়া নাকি ঘুম হবে না।
আর আমার হয়েছে উলটো। মগবাজারের ফ্ল্যাটেই আমার ঘুম আসতে চায় না। বসুন্ধরার নিরিবিলি ফ্ল্যাটে চুপচাপ জীবনটা আমি ভালোবেসে ফেলেছি।
সকাল দশটার মধ্যে গোসল-টোসল সেরে আমি একদম ফ্রি। অফিসে যাই সাড়ে এগারোটায়। হাতে দেড় ঘণ্টা সময়। এই সময়টায় গান শুনি কিংবা বই পড়ি। কোনো-কোনো দিন জরুরি মিটিং থাকে। অফিসের বাইরে নানারকম কাজ থাকে। ওসবেও ছুটতে হয়। ওই ধরনের কাজ না থাকলে সাড়ে এগারোটায় অফিসে গিয়ে একটানা সাড়ে ছটা পর্যন্ত থাকি।
আগে মগবাজারের বাসা থেকে ড্রাইভারের সঙ্গে খাবার পাঠিয়ে দিতেন স্ত্রী। ড্রাইভারের নাম মতিন। ছোটমেয়েকে ইউনিভার্সিটিতে নামিয়ে দিয়ে সে চলে আসতো অফিসে। দুপুরের খাওয়া শেষ হলে হটপট তুলে রাখতো গাড়িতে। পরদিন আবার নিয়ে আসতো দুপুরের খাবার। রাতে খাই রুটি-সবজি। ওসব জাহাঙ্গীরই করতে পারে।
স্ত্রীকে বললাম, শুক্রবার শুক্রবার জাহাঙ্গীরকে মগবাজারে ডাকো। মাছ-মাংস ভালো রান্না করতে শেখাও। দুপুরের খাবার নিয়ে তাহলে আর কোনো ঝামেলা থাকে না।
দু-তিন শুক্রবারের ট্রেনিংয়ে জাহাঙ্গীর পাকা রাঁধুনি হয়ে গেল। তার মানে আমি একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মগবাজারের ওপর আর নির্ভরই করতে হয় না।
সাড়ে ছয়টার দিকে ফ্ল্যাটে ফিরে আধঘণ্টা খানিক রেস্ট নিয়ে পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট এক্সারসাইজ করি। হালকা গরম পানিতে গোসল করে ডিনার সেরে নটার দিকে আবার অফিস। ফার্স্ট এডিশন শেষ করে ফ্ল্যাটে ফিরতে-ফিরতে পৌনে এগারোটা-এগারোটা।
কোনো-কোনো সন্ধ্যায়ও থাকে নানা ধরনের অনুষ্ঠান। ডিনারে যেতে হয় দামি-দামি জায়গায়। সব মিলিয়ে এই হচ্ছে আমার এখনকার জীবন।
শুক্রবার দিনটা পরিবারের জন্য। ভাইবোন-বন্ধুবান্ধব, বিয়েশাদি ইত্যাদি। কোনো-কোনো প্রকাশক আসেন শুক্রবার সকালের দিকে। বইপত্রের খবরাখবর, রয়্যালিটির হিসাব, আগামী ফেব্রম্নয়ারিতে কী কী বই লিখবো সেসব পরিকল্পনা। যদিও এসবই সামলায় শাহীন। তারপরও নিজে মাঝে-মাঝে প্রকাশকদের সঙ্গে বসি।
শাহীন শুধু বইপত্র আর প্রকাশকই সামলায় না, আমার পুরো সংসারই সামলায়। আমার হাতের লেখা সে ছাড়া কেউ পড়তে পারে না। নিচতলার ফ্ল্যাটের একটা রুমে তার অফিস করে দিয়েছি। প্রতিদিন যতটা লিখি ড্রাইভারের সঙ্গে পাঠিয়ে দিই তাকে। সে কম্পোজ করে। আমি কম্পিউটার কম্পোজ পারি না। সাবেকি আমলের হাতের লেখাই চালিয়ে যাচ্ছি।
শাহীন গত কুড়ি বছর ধরে আমার সঙ্গে। দিনে-দিনে আমার পরিবারের অংশ হয়ে উঠেছে। সংসারে হেন কাজ নেই, যা সে না করে। আমরা প্রত্যেকেই তার ওপর খুব নির্ভরশীল। শাহীনের মতো সৎ-নির্লোভ মানুষ আজকালকার দিনে পাওয়া যাবে না। মাটির মানুষ বলতে যা বোঝায় শাহীন হচ্ছে তাই। ফাঁকিঝুঁকি-মিথ্যাচার কাকে বলে শাহীন জানে না।
সব মিলিয়ে এই হচ্ছে আমার এখনকার জীবন। এই জীবনে এসে ঢুকলো ওই তিন বছরের মেয়েটি। জয়া। সঙ্গে ওর মা যমুনা।
জয়াকে প্রথমদিন আমি ক্যান্ডি দেওয়ার ফলে শিশুটির ভালোরকম একটা লোভ জন্মালো। মায়ের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই নটার সময় সে আসে। যমুনা তার কাজের ফ্ল্যাটের ডোরবেল বাজায়। আর জয়া এসে দাঁড়ায় আমার ফ্ল্যাটের খোলা দরজায়। বুঝতে পারি শিশুটি কেন দাঁড়িয়েছে। আর এমন মিষ্টি করে হাসে, মুখের দিকে তাকালেই মায়া লাগে।
প্রতিদিনই আমি তাকে কিছু না কিছু দিতে লাগলাম। কোনোদিন একটা ক্যান্ডি, কোনোদিন একটা কমলা বা আপেল, কোনোদিন একটা কলা। এক প্যাকেট বিস্কুট ছিল টেবিলের ওপর। খাওয়াই হচ্ছিল না। পুরো প্যাকেটটা একদিন দিয়ে দিলাম জয়াকে। একদিন দুটো মিষ্টি দিলাম। একদিন দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না, একশটা টাকা দিলাম। যা ইচ্ছে হয়, কিনে খাও গিয়ে।
জয়া যে কী খুশি! কী আনন্দিত। তার এই আনন্দিত মুখ দেখার জন্যই নটা বেজে গেলেও ফ্ল্যাটের দরজা আমি বন্ধ করি না। মায়ের হাত ধরে মেয়েটির আসতে দেরি হলে, নাশতা করতে বসেও দরজার দিকে তাকাই। জাহাঙ্গীরকে জিজ্ঞেস করে খোঁজখবর নেই।
জয়ার জন্য আমার যে একটা বিশেষ মমতা তৈরি হয়েছে এটা যমুনা তো টের পেয়েছেই, জাহাঙ্গীরও খুব ভালোভাবেই বুঝেছে। ওদের খবরাখবর জাহাঙ্গীর রাখে। এর মধ্যে দিন সাতেক জয়াকে দেখি না। যমুনাও আসে না। কাজ ছেড়ে দিলো নাকি?
পাকিস্তানি পরিবারটির সঙ্গে আমি কথা বলি না। তাদের ছোট-ছোট দুটি মেয়ে নিজেদের মতো চলাফেরা করে। খোলা দরজা কিংবা জানালা দিয়ে কখনো-কখনো আমার ফ্ল্যাটে উঁকি দেয়। এটুকুই। আমি দুয়েকদিন ডেকেছি। কি রকম লজ্জা পেয়ে পালিয়ে যায়। হাজব্যান্ড-ওয়াইফ আর দুই বাচ্চা নিয়ে তাদের সংসার। ভদ্রলোক কোনো একটা টেক্সটাইল মিলে কাজ করেন। একটু মোটা ধাঁচের নিরীহ চেহারা। খুবই অর্ডিনারি প্যান্ট-শার্ট আর জুতো পরে কাজে যান। মাথায় অ্যাশ কালারের একটা গোল টুপি। আমার খোলা দরজার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় গোলাপপানি টাইপের একটা পারফিউমের গন্ধ আসে। কখনো মুখোমুখি দেখা হলে সে আমাকে সালাম দেয়। সালাম বিনিময় ছাড়া কোনো কথা হয় না।
ভদ্রমহিলাকেও দু-চারবার দেখেছি। ঘর থেকে তেমন বের হয় না। অথবা আমি যখন ফ্ল্যাটে থাকি না তখন বোধহয় বের হয়। ফ্ল্যাটের দরজা-জানালা দিয়ে আড়চোখে আমার দিকে তাকায়। ধবধবে ফর্সা, ভালোই মোটা। সিনথেটিকের সালোয়ার-কামিজ পরে থাকে, মাথায় ওড়নার ঘোমটা।
জাহাঙ্গীর একটু-একটু উর্দু জানে। আলাপি টাইপের মানুষ। তার সঙ্গে বোধহয় পাকিস্তানি পরিবারটির কথাবার্তা হয়।
জাহাঙ্গীরকে জিজ্ঞেস করলাম, যমুনা আর জয়ার খবর কী বলো তো? বেশ কয়েকদিন দেখি না!
জাহাঙ্গীর বলল, সেও কয়েকদিন ধরে দেখে না।
খবর নিয়ে দেখো তো। কাজ ছেড়ে দিয়ে গেল কি না?
জাহাঙ্গীর খবর নেওয়ার আগেই, পরদিন নটার দিকে দেখি জয়ার হাত ধরে যমুনা কাজে এসেছে। মেয়ের মাথা ন্যাড়া, মায়ের মুখে-হাতে শুকিয়ে আসা গোটাগাটি।
যমুনা, কী হয়েছে তোমার?
জলবসন্ত হয়েছিল স্যার।
জয়াকে একটা আপেল দিলাম। কিছুক্ষণ পর সেই আপেল হাতে ফিরে এলো মেয়েটি। আপেল পচা।
খুবই লজ্জা পেলাম। দেওয়ার সময় খেয়াল করিনি। পচা আপেল ফেলে দিয়ে দুটো তাজা আপেল ধরিয়ে দিলাম।
কদিন পর পাশের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যমুনা আমার ফ্ল্যাটের দরজায় এসে দাঁড়াল। সঙ্গে জয়া আছে। আজ তাকে একটা ক্যান্ডি দিলাম। তখন সাড়ে দশটার মতো বাজে। সোফায় বসে আমি চা খাচ্ছি। নটার দিকে একটা কমলা দিয়েছিলাম জয়াকে। তারপর আবার এলো কেন?
যমুনা বলল, স্যার, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলবো।
বলো।
আমার হাজব্যান্ড একটা এনজিওতে কাজ করতো। বেতন পেতো পনেরো হাজার টাকা। বাচ্চাটাকে নিয়ে আমরা ভালোই
চলতাম। মাস দুয়েক হলো চাকরি নেই। খুবই কষ্টে আছি স্যার। আমার হাজব্যান্ড বিএ পাস। আপনি যদি তাকে একটা চাকরি দেন, তাহলে আমার স্যার বুয়ার কাজটা করতে হয় না। আমি লেখাপড়া জানা মেয়ে। এসএসসি পাস করেছিলাম। অভাবের সংসার, বাবা কলেজে পড়াতে পারেননি। বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। আপনি যদি স্যার দয়া করে…
আমি অবাক। তাইতো বলি, এতো সুন্দর ভাষায় কথা বলা মেয়ে, উচ্চারণ-টুচ্চারণ সুন্দর, তার তো কাজের বুয়া হওয়ার কথা না!
তোমাদের বাড়ি কোথায়?
বাগেরহাটে। আমার বাবা স্যার একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমরা তিন বোন। বাংলাদেশের তিনটা নদীর নামে আমাদের নাম রেখেছিলেন বাবা। মুক্তিযুদ্ধের সময় একটা স্লোগান ছিল ‘তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা’ এই জন্য বাবা তার তিন মেয়ের নাম রেখেছিলেন পদ্মা মেঘনা যমুনা। বড় দুবোনের বিয়ে হয়েছে মোটামুটি ভালো ঘরে। টাকাপয়সা নেই কিন্তু ভদ্র পরিবার। আমার শ্বশুরবাড়িরও একই অবস্থা। ও ঢাকায় চাকরি নিয়ে এলো। একটা পরিবারের সঙ্গে তিন হাজার টাকায় সাবলেট থাকি। ভালোই চলছিলাম। হঠাৎ চাকরিটা স্যার চলে গেল।
এ সময় পাকিস্তানি পরিবারের ছোট মেয়েটি এসে আমার ফ্ল্যাটে একটু উঁকি দিয়েই চলে গেল।
যমুনা বলল, আমাকে দেখে গেল স্যার। বুয়ার কাজটাও যায় কিনা।
কেন? তুমি কী অন্যায় করেছো?
এরা চায় না তাদের বাড়ির কাজের বুয়া কারো সঙ্গে কথা বলুক। জয়াকে আপনি খাবার-টাবার দেন এটাও পছন্দ করে না।
আমি গম্ভীর গলায় বললাম, বেতন কত দেয় তোমাকে?
দুহাজার টাকা।
যদি কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেয়, মাসের শুরুর দিকে এসে আমার কাছ থেকে দুহাজার টাকা নিয়ে যাবে।
যমুনার চোখদুটো ছলছল করে উঠল। আমি যে বুয়ার কাজ করি এটা আমাদের বাড়ির কেউ জানে না। কাজ করা খারাপ না। পেটের দায়ে মানুষ তো কাজ করবেই। কিন্তু স্যার, আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধা ভাতায় আমাদের সংসার চলে। বাবার শরীরটা ভালো না। প্রায়ই বিছানায় পড়ে থাকেন। আমি বুয়ার কাজ করছি এটা শুনে তিনি কতটা রাগ করবেন আমি জানি না। তবে যদি শোনেন আমি একটা পাকিস্তানি পরিবারের কাজের বুয়া তাহলে প্রচন্ড রাগ করবেন। বলবেন, যাদের কারণে একাত্তর সালে ত্রিশ লাখ বাঙালি মারা গেছে, দু-তিন লাখ মা-বোন ইজ্জত হারিয়েছেন, সেই পাকিস্তানিদের বাড়ির কাজের বুয়া হয়েছে একজন মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে? এ-কথা শোনার আগে আমার মরে যাওয়া উচিত ছিল। এই মুহূর্তে তুই ওই কাজ ছেড়ে দে। দরকার হলে না খেয়ে মরে যাবি, তাও পাকিস্তানিদের বাড়িতে কাজ করতে পারবি না।
যমুনার কথা শুনতে-শুনতে আমার ভেতরটা একেবারেই অন্যরকম হয়ে গেছে। যমুনার বাবার জায়গায় নিজেকে যেন দেখতে পাই আমি। মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে বুয়ার কাজ করছে পাকিস্তানিদের ফ্ল্যাটে!
গম্ভীর গলায় বললাম, যমুনা, এই মুহূর্তে কাজটা তুমি ছেড়ে দেবে। তোমার হাজব্যান্ডকে নিয়ে কাল সকালে আমার এখানে আসো। একটা সিভি নিয়ে আসতে বলবে।
যমুনার চোখে পানি এসে গেছে। চোখ মুছতে-মুছতে চলে গেল।
আমার খুব বড় ভরসার জায়গা ফরিদুর রেজা সাগর। ‘ইমপ্রেস’ গ্রুপের মালিকদের একজন। চ্যানেল আইয়ের এমডি। ফোন করে বললাম সাগরকে, বলল কালই পাঠিয়ে দাও।
যমুনার হাজব্যান্ডের নাম ফখরুল। ছোটখাটো দেহের অত্যন্ত নম্র-বিনয়ী ছেলে। সাগর তাকে আঠারো হাজার টাকা বেতনের একটা চাকরি দিলো। চাকরি পেয়ে জয়াকে নিয়ে ওরা দুজন এসে খুবই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেল আমাকে।
যমুনাকে বললাম, কুড়িলের ওইদিকে আমার এক বন্ধু একটা স্কুল করেছে। আমি বলে দিচ্ছি। ওই স্কুলে তোমার একটা আয়ার চাকরি হবে। জয়াকেও ওই স্কুলে ভর্তি করে দিও। বেতন লাগবে না।
সাত মাস পরের কথা।
শনিবারের এক সকালে স্বামী-সন্তান নিয়ে যমুনা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। এই সাত মাসে একেবারেই বদলে গেছে তার চেহারা। ফখরুল এবং তাদের দুজনেরই শরীর স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে। পোশাকআশাক সুন্দর। জয়ার পরনে সুন্দর জামা। মাথার চুল বেশ বড় হয়েছে। দেখতে খুবই ভালো লাগছে বাচ্চাটিকে।
যমুনা বলল, আমরা খুব ভালো আছি স্যার। দুজনে মিলে পঁচিশ-ছাবিবশ হাজার টাকা পাই। ছয় হাজার টাকা দিয়ে ছোট্ট একটা বাসা নিয়েছি। জয়া আমার সঙ্গে স্কুলে যায়, আমার সঙ্গেই ফিরে আসে। আমরা খুব ভালো আছি।
শুনে ভালো লাগল। ফ্রিজ থেকে একটা ক্যান্ডি বের করে জয়ার হাতে দিলাম।
জয়া বলল, আমি একটা গান শিখেছি। শুনবে? মাত্র একটা লাইন পারি।
মজা লাগল, বললাম, শোনাও।
জয়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পাখির মতো মিষ্টি কণ্ঠে গাইলো ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’।
আমি মুগ্ধ হয়ে শিশুটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।