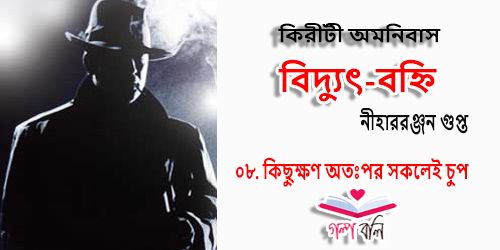আমার নাম যুগল বিন্দু। নামের শেষাংশ দেখে আপনারা নিশ্চয়ই কিছু একটা ভাবছেন। ইসমাত আরা শাওন, সুরভি বিশ্বাস নদী; ভাবছেন এই শাওন বা নদীর মতো বিন্দুও বুঝি নামের লেজুড়। না না, বিন্দু আমার নামের লেজ নয় কোনো। বিন্দু আমার সম্প্রদায়গত পদবি। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? না হওয়ারই কথা! কত কত পদবির নাম শুনেছেন আপনারা – দত্ত, সেন, চৌধুরী, মজুমদার, চক্রবর্তী, ব্যানার্জি, চ্যাটার্জি, দে, ঘোষ, মিশ্র, মিত্র, রায় – আরো কত কী! কিন্তু বিন্দু টাইটেল তো শোনেননি কখনো! কিন্তু বিশ্বাস করুন, বিন্দু পদবিধারী মানুষও বাংলাদেশে আছে।
কারা তারা? কী করে? জানতে চাইছেন?
মৎস্যজীবী, জেলে তারা। পদ্মানদীতে মাছ ধরে। এক-দুই পুরুষ ধরে নয়, শত শত বছর পুরুষানুক্রমে পদ্মায় মাছ মেরে জীবন চালাচ্ছে বিন্দুরা।
দেখতে ইচ্ছে করছে আমাদের? ফরিদপুরে চলে আসুন। ফরিদপুর শহর থেকে রিকশাপথে টেপাখোলা গ্রাম। ওই গ্রামেরই একটেরে বিন্দুপাড়া। পদ্মানদীর উত্তর পাড়ে, পদ্মাপাড় থেকে আধা মাইল দূরে ওই বিন্দুপাড়াটি। জেলেপাড়াগুলো যেমন হয়, ভদ্রপাড়া থেকে দূরে, আমাদের বিন্দুপাড়াও ঠিক সেরকম। টেপাখোলায় কত শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাস! ওরা সযত্নে আমাদের এড়িয়ে চলে। আমাদের এড়িয়ে চললে কী হবে, ওরা তো জানে না – ওদের গায়ে গায়ে লেগে আছি আমরা। ভদ্রলোকেরা থাকে কোথায়? কেন টেপাখোলায়? ওই টেপাখোলার সঙ্গে যে মাছ, মাছের গন্ধ জড়িয়ে আছে!
আমাদের এদিকে পুঁটি, মলা এরকম ছোট ছোট মাছ মাটির কলসি বা মটকায় ভরে মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়। ওগুলো ওখানে পচে-শুকিয়ে শুঁটকি হয়ে যায়। এ-ধরনের শুঁটকিকে টেপা বলা হয়। আর খোলার অর্থ তো জায়গাও হয়। তাহলে ভাবুন, টেপাখোলার মানেটা কী! শুঁটকির আবাসস্থলেই সজ্জন ব্যক্তিদের বসবাস।
আমার বর্তমান নাম যুগল বালা দাসী। আমার শাগরেদ সুবোধ পরামর্শ দিয়েছে, ‘গুরুমা, নামের মাঝখান থেইকা বালা বাদ দেন। দাসী থাউক। আপনে তো তানের চরণের দাসী।’ বলে দু-হাত একত্র করে কপালে ঠেকায় সুবোধ। এই প্রণাম যে আমার গুরুদেব ভোলানাথের উদ্দেশে, বুঝতে অসুবিধা হয় না আমার।
আমি কী করি জানতে চাইছেন?
আমি ভাঙা জিনিসকে জোড়া লাগাই, আবার অখ-কে কাঁচের টুকরার মতো ভেঙে খানখান করি। বুঝলেন না তো কিছু? না বোঝারই কথা! এত হেঁয়ালি করে বললে কি বোঝা যায়?
আমি মানুষ নিয়ে খেলা করি। মানুষ মানে মানুষের বিশ্বাস। আমি মানুষের মনকে তছনছ করি, আবার এক মনের সঙ্গে অন্য মনকে মিলিয়েও দিই। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে মিলন ঘটানো আর বিচ্ছেদ ঘটানো আমার কাজ। এরপরেও আপনার বুঝতে বোধহয় একটু অসুবিধা হচ্ছে। খুলেই বলি তাহলে। আমি একজন গুনিন। মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক নিয়েই আমার কাজ-কারবার।
একজন জেলের মেয়ে হয়ে সংসার, স্বামী, রাঁধন-বাড়ন, মাছ-নৌকা – এসবের দিকে না গিয়ে ওই তুকতাকের দিকে গেলাম কেন, তারও একটা কারণ আছে। বিয়ে যে আমার হয়নি, সে-কথাও ঠিক নয়।
তার আগে আমার নিজের সম্পর্কে আরো দু-চারটি কথা বলা দরকার।
আমাদের পাড়াটা পূর্ব-পশ্চিম লম্বালম্বী। চিকন গলি। দুজন পাশাপাশি হাঁটতে পারে না। একজনকে পথ ছেড়ে দিতে হয়। এই পথের ওপর থেকেই ঘরগুলো। ঘর মানে খোপ। কুঠুরিগুলো গায়ে গায়ে লাগানো। এক একটা কুঠুরিতে এক একটা পরিবার। প্রায় দেড়শো পরিবার মাথা গুঁজে আছে এই বিন্দুপাড়ায়। আমার বাপের বাড়িটা গলি ছাড়িয়ে একটু ভেতর দিকে, খালপাড়ে। খালপাড়ে বলে একটু খোলামেলা। বাপের ভিটেটা খোলামেলা হওয়ার কথা নয়। লোকচক্ষুর আড়ালে খালপাড়ের খাস জায়গায় একটু একটু করে মাটি ফেলে ভিটের পরিধিটা বাড়িয়ে নিয়েছিল বাপ সুধন্য। বাবা সামান্য লেখাপড়া জানত। পদ্মায় মাছ ধরত আর অবসরে পুঁথি পড়ত। সুধন্যর ঘরে আমিই একমাত্র সন্তান। আমার জন্মের পর মা বেঁকে বসেছিল, ‘এ আমার ছেমড়ি না। এই শ্মশানের কাঠ আমার কইন্যা হইতে পারে না।’
অসুরকুলে যেমন প্রহ্লাদ, কৈবর্তকুলে মা তেমনি উর্বশী ছিল। জেলে নারীরা তো কালো, সেই কালো নারীদের মধ্যে মা ছিল ফরসা আর সুন্দরী। মা আশা করে ছিল – তার কন্যাটিও দেখতে তার মতো রূপসী হবে। কিন্তু জন্মালাম আমি মা-কালীর গায়ের রং নিয়ে। তাই তো মায়ের দূর দূর, ছেই ছেই।
বাবা কিন্তু আমাকে কোলে তুলে নিয়েছিল। মায়ের তুচ্ছতাচ্ছিল্য বাবার আদরে-সোহাগে ভুলে যেতাম আমি।
মাথা তোলা হলে বাবা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলো আমায়; টেপাখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখানে আমি পেয়ে গেলাম আলতাফ স্যারকে। ওই স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন তিনি। ছুটির দিনে বা স্কুল ছুটির পর বিকেলের দিকে শুধু মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতেন তিনি। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর অনুরোধ করতেন। আমাদের বিন্দুপাড়ায় বেশি আসতেন তিনি। কিন্তু বিন্দুরা তাঁকে কোনো পাত্তা দিত না। কোনো কোনো নারী খেঁকিয়ে উঠত, ‘চাইয়া আছি ছাওয়ালডা কখন বড় হইব, বাপের লগে পদ্মাতে ইলিশ ধরতে যাইব! আর বেডা করে ঘ্যানর ঘ্যানর – ইস্কুলে পাডান, আপনাগো পোলা-মাইয়ারে ইস্কুলে পাডান! কাম নাই আর কী, ছাওয়ালরে ইস্কুলে পাডাইয়া ভাতঘর বন্ধ করি! আরে, তখন ভাতের বদলে ছাই খাইতে হইবে আমাগো!’
আলতাফ স্যার আর কী বলবেন! তাঁর কাছে যে কোনো জবাব নাই! ভাত বড়, না স্কুল বড় – বুঝে উঠতে পারেন না তিনি। ওখান থেকে মাথা নিচু করে সরে আসেন।
বাবা সুধন্যর কাছে এসে বড় সুখ আর স্বস্তি পেতেন আলতাফ স্যার। বাবাকে বলতেন, ‘তোমার মেয়ে বড় হলে স্কুলে পাঠাবে সুধন্য। পাঠাবে তো? কথা দিচ্ছো তো?’ জেলেসন্তানরা পড়ালেখা করুক, এটা একান্তভাবে চাইতেন আলতাফ স্যার।
রোদ-ঝলসানো মুখে একমুঠো হাসি ছড়িয়ে বাবা বলত, ‘মেয়েডা আরেকটু মাথাতোলা হউক ছার, তারপর আপনার ইস্কুলে পাডাইমু।’
বাবা কথা রেখেছিল। আলতাফ স্যারের স্কুলে নাম লিখিয়ে দিয়েছিল আমার। নিচুর দিকে ক্লাস নিতেন না আলতাফ স্যার। ক্লাস ফাইভে উঠে তাঁকে পেয়ে গেলাম। আমাদের পাড়ার সুধারানিও আমার সঙ্গে পড়ত। স্যার আমাদের বাংলা পড়াতেন। পড়াতে পড়াতে কোথায় হারিয়ে যেতেন তিনি। স্যার তাকিয়ে থাকতেন জানালার ওপারের খোলা মাঠটির দিকে, আর ক্লাসভর্তি আমরা চেয়ে থাকতাম স্যারের মুখের দিকে। গোলমাল করার সাহস ছিল না কারো। গোলগাল মুখ স্যারের। নাকের নিচে ইয়াবড় একটা গোঁফ। গোঁফের তলা দিয়ে টুপটাপ করে স্নেহের ধারা ঝরে পড়ছে। মাথার মাঝখানে মস্তবড় টাক। দু-কান আর পেছনটা ঘিরে একসারি চুলের গোছা।
একদিন আলতাফ স্যার একটা বই হাতে নিয়ে ক্লাসে ঢুকলেন। বইটা উঁচিয়ে ধরে বললেন, ‘এটা একটা উপন্যাস। উপন্যাস মানে তোমরা বুঝবে না। তবে বুঝে নাও – এই বইতে একটা কাহিনি আছে। জানো কাদের নিয়ে এই কাহিনি?’
সবাই সমস্বরে বলল, ‘জানি না স্যার।’
‘বইটার নাম – পদ্মানদীর মাঝি। লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পদ্মাপাড়ের জেলেদের নিয়ে কাহিনিটা লিখেছেন তিনি।’ আমার দিকে তাকালেন স্যার। বললেন, ‘তোমাদের পাড়াটা তো পদ্মা থেকে খুব বেশি দূরে নয়? তোমার বাপ-দাদারাও তো পদ্মায় ইলিশ ধরেছে, ধরে?’
স্যার বললেন, ‘এই উপন্যাসে কুবেরের কথা আছে, গণেশ-রাসুর কথা বলা হয়েছে। মালার কথা আছে, আছে কপিলার কথা। ওদের কেউ না কেউ হয়তো তোমাদের পাড়ারই লোক ছিল। এই চরিত্রগুলির পদবি ব্যবহার করেননি মানিক। যদি করতেন, তাহলে অবশ্যই লিখতেন কুবের বিন্দু, রাসু বিন্দু, কপিলা বিন্দু। পদ্মানদীর পাড়ের জেলেদের নিয়েই তো উপন্যাসটি লিখেছেন তিনি!’
স্যারের কথা আমরা কিছু বুঝলাম, বেশির ভাগ বুঝতে পারলাম না। সেদিকে স্যারের কোনো খেয়াল নেই। আপনমনে নিচু গলায় বললেন, ‘তোরা ছোটজাত নস রে যুগল! তোরা মানিকের উপন্যাসের চরিত্র রে!’
ফাইভ পাশের পর বাবার দোনামোনাকে উপেক্ষা করে আমাকে হাই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন আলতাফ স্যার। এইট পর্যন্ত পড়েছিলাম আমি ইয়াসিন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে।
তারপর বাপ সুধন্য আমাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দিলো।
মা মারা যাওয়ার পর বাপ খুব অসহায় হয়ে পড়েছিল। বাবা নদীতে মাছ ধরতে যায়, আমি একা একা ঘরে থাকি। কার মনে কী আছে তো বলা যায় না! যদি মেয়েটার অকল্যাণ হয়ে যায়!
বাবা বোধহয় অনেক আগে থেকে ছেলে খুঁজছিল। শেষ পর্যন্ত পেয়েও গেল। সে মদনমোহন। মদনমোহন ভাদাইম্যা টাইপের ছেলে। মা-বাপহারা, টো-টো করে বেড়ায় যারা তাদের আমাদের দিকে ভাদাইম্যা বলে। এই ভাদাইম্যা মদনমোহনের সঙ্গে যুগল দাসীকে বিয়ে দেবে বলে ঠিক করে ফেলল বাবা। শর্ত একটা – মদনমোহনকে ঘরজামাই হয়ে থাকতে হবে। মদনমোহন তো হাতে চাঁদ পেল। থাকতে পারার বাড়ি, সঙ্গে বউ! মদনমোহনের তো পোয়াবারো! বউ কালো, তাতে কী, সে তো বহুদিন পরে একটা বাপও পেয়ে গেল!
মদনমোহন দেখতে-শুনতে বেশ। বয়স খুব বেশি নয়, আমার চেয়ে বছর দু-তিনেকের বড় হবে। বিয়ের পর ওকে বড় ভালোবাসতে ইচ্ছে করল আমার। ভালোবাসলামও। সে কোনো কাজকাম করে না, শ্বশুরবাড়িতে বসে বসে খায়। তারপরও ভালো লাগল তাকে। সে সময়ে-অসময়ে আমার শরীর ঘাঁটে, তারপরও ভালোবাসলাম মদনমোহনকে।
এই করে করে ছেলে হলো একটা। তারপরও মদনমোহনের টনক নড়ে না। আমার বাপের সঙ্গে নদীতে যায় না বা এটা-ওটা করে দু-পয়সা আয়ও করে না। বাবার রোদপোড়া মুখ আর ছাল-ওঠা দেহটির দিকে তাকিয়ে আমার ভেতরটা দুমড়ে যায়। মদনমোহনকে আয়-রোজগারের কথা বললে তেড়ে ওঠে, ‘কালা বেটি গছাইছে আমারে। তোর রূপ আছে, না যৌবন আছে? ইস্তিরির মইয্যদা দিছি, এর বাড়া কী হইতে পারে রে বেটি?’
বাবা সব শুনেও চুপ থাকে। মদনমোহনকে তো সে-ই ঘরজামাই করে এনেছিল! এর মাঝে আবার গর্ভবতী হই আমি। মেয়ে হয়। ছেলেটা বাপের রং পেলেও জবা আমার রং পায়। মদনমোহনের তুচ্ছতাচ্ছিল্য বেড়ে যায়। দাওয়ায় বসে মা-মেয়ের উদ্দেশে গালাগাল করতে থাকে। এর মধ্যে বাবা একদিন স্বগ্গে যায়।
মদনমোহন আরো স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। কীভাবে ঘরে চাল আসে, কীভাবে রান্না হয়, কিছুরই খবর রাখে না মদনমোহন। দু-বেলা হাত ধুয়ে পাতে বসতে লজ্জা করে না তার।
বহুদিন আমার বিছানায় আসে না সে। দু-দুটো বাচ্চা নিয়ে নাকানি-চুবানি খেতে থাকি আমি। কী করব, দিশা পাই না। নদীতে ঝাঁপ দেব, গাছের ডালে আঁচল বাঁধব? তাহলে ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখবে কে? ওদের বাপ যে থেকেও নেই। পাড়ার মন্দিরে মা-চণ্ডিকার মূর্তির সামনে গিয়ে মাথা ঠুকি, ‘মা, আমাকে বাঁচাও। পথ দেখাও মা আমাকে।’
এক দুপুরে উত্তরপাড়ার শ্যামলের মায়ের কাছে সেরদুয়েক চাল ধার চাইতে গেছি, ফিরে দেখি ঘর থেকে ফুড়ুত করে রামচন্দরের বিধবা বোনটি বেরিয়ে গেল। দ্রুত ঘরে ঢুকে দেখি মদনমোহনের পরনের কাপড় আলুথালু।
আমি চিৎকার দিয়ে উঠি, ‘ভগবানরে! এও দেখতে হলো আমাকে!’
ভাতার আমার গলা উঁচিয়ে বলল, ‘বেশ কইরব, আমার ঘরে আমি যাকে খুশি এনে তুইলব।’
আমি ‘বাবারে’ বলে ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেলাম। ছেলেটি আমার মাথার পাশে বসে চোখেমুখে হাত বুলাতে লাগল। মেয়েটিকে কোলে নিয়ে আমি মা-চণ্ডিকার থানে গেলাম। ছেলেটিও পিছু পিছু এলো। আমি মূর্তির সামনে বসে পড়লাম।
আমি করুণ চোখে মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আমার বুকের ভেতরটা তখন ফেটে যাচ্ছে। দু-চোখে আঁধার আঁধার ঠেকছে। মাথা ঝিমঝিম করছে, মাথার দু-পাশের রগদুটো বুঝি এখনই ছিঁড়ে যাবে!
হঠাৎ আমার দেহটা থরথর করে কেঁপে উঠল। মাথা দুলতে শুরু করল। আমার হাত-পা-মাথা-শরীর আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। আমি মূর্তির সামনে তালে তালে মাথা ঠুকতে শুরু করলাম।
আমার কাণ্ডের কথা গোটা পাড়ায় দ্রুত চাউর হয়ে গেল। দলে দলে পাড়ার মানুষেরা চণ্ডিকার থানে জমা হলো। ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলে উঠল, ‘যুগলবালার উপর মা-চণ্ডিকা ভর কইরেছে। যুগল এখন মা চণ্ডিকা হইয়ে গেছে।’ বলতে-না-বলতে পাড়ার নারীরা আমাকে ঘিরে বসল।
কেউ বলল, ‘মা, আমার দুঃখের জবাব দেও, স্বামীরে আমার করে দেও।’
আরেকজন বলল, ‘আমার শ্যামলীর বিয়ে হচ্ছে না মা, তার বরের সন্ধান দেও।’
কেউ এক গ্লাস পানি আমার মুখের কাছে এগিয়ে ধরে বলল, ‘মা, এই জলে তুমি একটু ফুঁ দিয়ে দেও। ছাওয়ালডার পেট ব্যথা সারে না অনেকদিন। তোমার পানি পড়ায় সেরে উঠবে।’
আমি কী বলেছিলাম বা কী করেছিলাম জানি না, পরে শুনেছি আমার কথায় আর ফুঁ-এ কাজ হয়েছে। সোয়ামি কাছে এসেছে, শ্যামলীর জন্য ঘর এসেছে, ছাওয়ালডার পেট ব্যথা কমেছে। সবই কাকতালীয় ব্যাপার, ঝড়ে কাক মরার মতো। এতে আমার যে কোনো হাত নেই তা স্পষ্ট জানি।
কিন্তু পাড়ার মানুষেরা আমাকে অতিমানব করে তুলল। এ-গ্রাম ও-গ্রাম থেকে নানা সমস্যা নিয়ে লোকেরা আসতে শুরু করল। ফলে আমার ঘনঘন বান উঠতে লাগল। বান মানে ওই বেঘোর অবস্থা, উন্মাতাল দেহভঙ্গি। ওই অবস্থায় যাকে যেরকম মন চায় বলে যেতে লাগলাম। মানুষদের উপকারের নাকি সীমা থাকল না। কেউ শ্বশুর-শাশুড়ির যন্ত্রণার ব্যথা নিয়ে আসে, কেউ পরনারী আসক্ত স্বামীর সমস্যা নিয়ে আসে, কেউ পক্ষাঘাত নিয়ে আসে, কেউ প্রেমিকাকে বিয়ে করার উদগ্র বাসনা নিয়ে আসে। আমি কাউকেই ফিরাই না। কাউকে জড়িবুটি দিয়ে, কাউকে ঝাড়ফুঁক করে, কারো ঘাড়ে-মাথায় ঝাড়ুর বাড়ি মেরে, কারো বাহুতে-কোমরে তাবিজ বেঁধে চিকিৎসা করতে থাকি। এরা খালি হাতে আসে না। কাজশেষে আমার সামনের থালায় টাকা-পয়সা দিয়ে যায়। গড় হয়ে প্রণাম করে আমাকে। আমার কপালে তখন মস্তবড় সিঁদুরের ফোঁটা, আমার গায়ে তখন ঘনঘোর রক্তাম্বর।
সবার কাছে এখন আমি যুগলবালা দাসী নই, গুনিন মা যুগল দাসী। আমার খাবারের অভাব মিটে যায়। আমার ভিটেয় দোতলা ওঠে। মদনমোহনকে আমি তোয়াক্কা করি না। সে এখন ভেড়ুয়া মদনমোহন। আমার পায়ে পায়ে ঘোরে।
একসময় এই মদনমোহনের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমি কাঙালের মতো তার দিকে চেয়ে থেকেছি, এখন আমার সামান্য কৃপাদৃষ্টির জন্য তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করে থাকে মদনমোহন।
মদনমোহনের অবহেলা আমাকে প্রবঞ্চক বানিয়েছে। মানুষকে ঠকিয়ে, তাদের সঙ্গে মিথ্যে বোলচাল মেরে আজ আমি টেপাখোলার বিখ্যাত গুণিন।
বিশ্বাস করুন আমি শঠতার আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে চাইনি, চেয়েছিলাম স্বামী-সন্তান নিয়ে অন্য দশজন বিন্দুনারীর মতো সুখে-দুঃখে বেঁচে থাকতে। কিন্তু মদনমোহন আমাকে সেভাবে বাঁচতে দেয়নি।