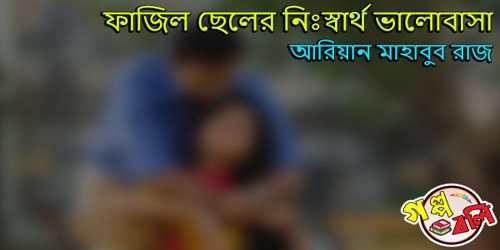থমথমে বাড়িটাতে কান পাতলে সামান্য বিরতিতে ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ। উঠোনের শেষপ্রান্তে বেড়ার পাঁচিলটা বাইরের দিকে নুয়ে পড়েছে। হয়তো কঞ্চিগুলোর দুর্বলতা নয়তো বাঁধনের তারে জং ধরে পড়েছে ছিঁড়ে। পাঁচিলটা উঠিয়ে ঠিক করার তাগিদ নেই কারো – মোল্লাবাড়ির কারো তো নয়ই, ভাঙা পাঁচিলের পাশে উঠোনের এককোণে যে-খোদেজা বেগম তার তিনটা ছাগলসমেত আশ্রয় নিয়েছে, তারও নয়। পাঁচিলের ওপারে থাকার মধ্যে আছে এক সুপারিবাগান। তাছাড়া, আজ না-হোক কাল যে-পাঁচিলের অস্তিত্ব থাকবে না তা নিয়ে কে মাথা ঘামাবে! কুড়িয়ে আনা বেড়ার টুকরো আর মরচেপড়া টিন দিয়ে পাঁচিলের ধারঘেঁষে কোনোরকমে একটা ছাপরা করে নিয়েছে খোদেজা বেগম। মোল্লা বাড়ির কেউ তাকে আপদ মনে করেনি, আপত্তিও তোলেনি। কদিন আগেও সাদাটে এঁটেল মাটিতে লেপা উঠোনটা রাতে জোছনার আলোয় ঝকমক করত। অন্ধকারে দেখলে মনে হতো পায়ের সামনে টইটম্বুর নিখুঁত পুকুর। দৌলতদিয়ার মোল্লাবাড়ির শুচিবায়ুগ্রস্ত বউ এখন আর দাঁড়িয়ে থেকে সাদা মাটিতে উঠোন লেপিয়ে নেন না। উঠোনে কোনোরকমে ঝাড়ু চলে। তারই এক-তৃতীয়াংশে জায়গা হয়েছে খোদেজা বেগমের। লেপালেপির সময়কার অর্ধবৃত্তাকার যেসব দাগ এখনো কোথাও কোথাও আছে তা নিতান্তই সুখের দিনের ফেলে যাওয়া চিহ্ন। এখন লেপে ঝকঝকে করে রাখা তো দূরের কথা, খোদেজা বেগম হঠাৎ উদয় হয়ে উঠোন দখল করলেও কারো কিছু যায়-আসে না।
সব হারানোর কালে উদারতা দেখানো ছাড়া কিছু করারও থাকে না। হাতের মুঠোয় যা থাকবে না তা কারো জন্যে ছেড়ে দিতে যা দরকার পড়ে তা ঠিক উদারতাও নয়, তা হলো সামান্য ভাবীদৃষ্টি। মোল্লাবাড়ির বউ, আকলিমা খাতুনের তা আছে। মুহুর্মুহু ঢেউয়ের গর্জনের মাঝখানে কখনো রংজ্বলা পেটিকোট আর ফেটে যাওয়া ব্লাউজ গায়ে খোদেজা বেগম এক হাতে বড়ো একটা পোঁটলা আরেক হাতে তিনটা ছাগলের গলা থেকে ধেয়ে আসা দড়ি ধরে উঠোনের ভেঙেপড়া পাঁচিলের ফোকর দিয়ে মোল্লাবাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিল। পড়ে থাকা পাঁচিল থেকে ছুরির ফলার মতো বেরোনো কঞ্চিতে পিঠে গুঁতো খেয়ে একটা ছাগল জোরেশোরে ব্যাঁ-ব্যাঁ করে উঠেছিল তখন। ওজর-আপত্তিতে খোদেজা বেগম পেছনে ফিরে তাকায়নি। সোজা উঠোনের মাঝখান অবধি গিয়ে কাকুতি-মিনতি করতে লেগে গিয়েছিল। দোতলা বাড়ির উঁচু বারান্দায় তখন দাঁড়িয়েছিলেন মোল্লাবাড়ির বউ, আকলিমা খাতুন। খোদেজাকে হুড়মুড় করে আসতে দেখে বিস্ময় বা বিরক্তি ভুলে তাকিয়ে ছিলেন। নদীর ঢেউ যেমন দিনকে দিন বাড়ির পাঁচিলের দিকে ধেয়ে এসেছে আর তিনি নির্বিকার থেকেছেন, খোদেজার দিকেও ঠিক তেমনি নির্লিপ্ত চোখে তাকিয়ে ছিলেন।
আকলিমার সঙ্গে বিড়ালের মতো অনুসরণ করা সহচর, রিনা পানের বাটা হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। চমকে সে ‘আরে কী হইল, এইহানে এগুলা নিয়া হান্দাও ক্যা?’ বলে চিৎকার করে ওঠাতে আকলিমা একটা হাত তুলে রিনাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর করুণ চোখে তাকিয়েছিলেন খোদেজার দিকে। খোদেজা অভয় পেয়ে বলেছিল, ‘আম্মা, কী করব তাইলে এহন?’
‘আইজ কি চইলা গেল?’ প্রয়োজনের চেয়ে অনেক আস্তে শোনাচ্ছিল আকলিমা খাতুনের গলা। আরেকটু হলে ঢেউয়ের গর্জনে প্রশ্নটা শোনাই যেত না। খোদেজার শোনার উপযুক্ত করতে তাই রিনাকে প্রশ্নটা আরেকবার বলে দিতে হয়।
‘গেল তো, আম্মা। ওইদিকের সবাই কইছিল আরো দিন-সাতেক সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু কীয়ের সাতদিন? আইজ রাইতেই যা হওনের হইয়া গেল। রাইতে মরণের ঘুম ঘুমাইছিলাম, পানি যে বেড়ার তলে চইলা আসছে, কসম খোদার, কইতে পারি না।’
‘তারপর?’
‘হের পরে আর কী, পানির দাক্কায় বেড়ার তলের মাটি সুড়সুড় কইরা সইরা গেছে গো আম্মা। গর ভাইঙ্গা আমারে যে ভাসায়ে নেয় নাই হেইডাই কপাল। এই বুইড়া শইলে কি সাঁতরাইয়া ফিরতে পারতাম?’
‘হায় হায়, শ্যাষে ট্যার পাইলা ক্যামনে?’
‘ট্যার পাই নাই তো কুনো! মনু-টুনু-তিনু একলগে চেঁচাইয়া উডছে, তাগো পায়ের তলায় পানি। হেইডা শুইনা ধড়ফড়াইয়া উডলাম। তখন ঘরের জিনিস আর কী নিব, মানে, আছেই কী যে নিব, তাও যা আছিল আন্দারের মইদ্দে পরনের শাড়িটা খুইলা বাইন্দা নিলাম।’
কথা বলতে বলতে খোদেজা তার হাতের পোঁটলার দিকে ইঙ্গিত করে। তিনটা ছাগল তখন জোড়ে-বেজোড়ে ভাগ হয়ে দুদিকে যেতে চাইলে খোদেজা টাল খেয়ে কোনোরকমে দাঁড়ায়। হাতের পোঁটলা উঠোনের মাটিতে ঝুপ করে পড়ে। পুরনো শাড়ি ভাঁজ করে চারদিকের কোণ একখানে এনে গিঁট দেওয়া হয়েছে। ভেতরে তার চেয়েও পুরনো কিছু কাপড়ের ছেঁড়াফাঁড়া অংশ দেখা যাচ্ছে। একটা ট্যাপ খাওয়া অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ির কিছু অংশ, কাচের বয়ামে সামান্য গুড় আর পলিথিনের স্বচ্ছ প্যাকেটে কিছু চিড়া। পোঁটলার বাঁধনের ফাঁক দিয়ে একটা ছোটমতো কাঁসার গ্লাস বেরিয়ে উঠোনের মসৃণ শরীরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে কিছুদূর গিয়ে পথভুলে থেমে যায়। চোখেমুখে ভয় ভয় অনিশ্চয়তা নিয়ে খোদেজা এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে আকলিমার দিকে। কাঁসার গ্লাসের গতিপথ অনুসরণ করে না। নিচু হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া পোঁটলা গোটানোর চেষ্টাও করে না। থতমত খেয়ে বলে, ‘শ্যাষে মনু-টুনু-তিনুরে দড়ি খুইলা নিয়া দৌড় দিয়া বাইর হইলাম। দৌড় না দিলে দরজা ভাইঙ্গা পানিই আমারে বাইর করত।’
‘হায় রে! কেউ ডাকেও নাই তোমারে?’
‘হেরা তো কয় ডাকছে মেলা। কিন্তু আপনেই কন, আম্মা, ডাকলে কি আমি হুনতাম না?’
দুর্দশার মধ্যেও আকলিমার হাসি পায়। পাড়াসুদ্ধ লোকও যদি বলে বুড়ি কানে কম শোনে, তবু খোদেজা কিছুতেই তা মানে না। সে জানে না যে তার সঙ্গে কথা বলতে হয় প্রায় চিৎকার করে। তারপরেও, অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলে সে কথার আগামাথা কিছুই ধরতে পারে না। ভালোমতো বুঝতে হলে তাকে সামনের মানুষটার ঠোঁটের দিকে ভালোমতো তাকিয়ে থাকতে হয়। ঠোঁট নাড়ানো দেখে মোটামুটি আন্দাজ করে নিতে পারলেই হলো। হুট করে কথা বিষয়ান্তরে চলে গেলে অবশ্য সে খেই হারিয়ে হা করে তাকিয়ে থাকে। এমনিতে মোটামুটি কাজ চলে। তবে মানুষ এ নিয়ে হাসাহাসিও করে, বুড়ির কান খারাপ হইলে কী, আন্দাজ ভালো। তবে দরজা ধাক্কানো বা ডাকাডাকি যে খোদেজার কানে কেন পৌঁছেনি তা বুঝতে আকলিমার একটুও অসুবিধা হয় না। শেষে তিন ছাগলের তারস্বরের চেঁচামেচিতে তার টনক নড়েছে সেটা বুঝে নিয়ে আকলিমা বলেন, ‘তাইলে কী করবা এখন?’
খোদেজা বলে, ‘কী আর করুম, কইলে এইহানে আপনের উডানেই এট্টু ব্যবস্তা কইরা নিতাম।’
কথা শুনে আকলিমার পেছন থেকে রিনা উত্তেজিত হয়ে পানের বাটাসহ এক পা এগোয়। আকলিমা তাকে আবারো হাত উঠিয়ে ইশারায় নিষেধ করেন। আকলিমা বলেন, ‘তাই তো করবা, খোদেজা। এইখানেই থাকো আপাতত। তারপর আমি যেইখানে যাব, তুমিও সেইখানেই যাবা।’
উঁচু বারান্দা থেকে খোদেজার মাথার ওপর দিয়ে, পাঁচিলের ওপর দিয়ে, মাঠ-ঝোপঝাড়ের ওপর দিয়ে আকলিমা দূরে তাকান। ওদিকে তিনশো গজ পরে খোদেজার কুঁড়েঘরটা ছিল। পাশাপাশি ছিল আরো কয়েকটা একইরকমের ঘর। জমিতে কাজ করার লোকেরা থাকত। পানি ছাড়া সেদিকে এখন আর কিছুই দেখা যায় না। তবে এত দূর থেকেও পানির ফুলেফেঁপে ওঠা দেখা যায়। যেন রেগেমেগে ফেনা হতে চায় সব। তারপর তীরে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে রাগ কমায়, ফেনা থেকে তরল হয়ে ফিরে যায়। ফিরে যেতে যেতে মাটিকে চাক চাক করে নিজের দিকে টেনে নিয়ে যায়। সেদিক থেকে চোখ নামিয়ে খোদেজার দিকে তাকান আকলিমা। খোদেজা নিচু হয়ে কাঁসার গ্লাসটা কুড়িয়ে নেয়। এই বয়সে নিচু হতে বেশ কষ্টই হয় তার। হাত কখনো কাঁপে। বয়স তো কম হলো না। আকলিমার তেত্রিশ বছরের সংসার আর সংসারে এসে পায়ে পায়ে ঘোরার জন্য প্রথম যাকে পেয়েছিলেন সে ছিল খোদেজা। খোদেজা তখনই অন্তত পঁয়ত্রিশ পেরিয়েছে। একা মানুষ ছিল, আগেপিছে কেউ ছিল না তার। স্বামী-সন্তান হারিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়। দিনভর আকলিমার কাছে আগের জন্মের স্মৃতি আওড়ে যাওয়ার মতো করে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গল্প বলত খোদেজা। যুদ্ধের পর থেকে আকলিমার শাশুড়ির কাছে থাকত। শাশুড়ির মৃত্যুর পরেও এই বাড়িতে ছিল। শেষে বয়সের ভারে আর কাজ করতে না পারলে আকলিমা ঠিক করেছিলেন তাকে বাড়ি থেকে সামান্য দূরে নিজেদের জমিতে একটা ঘর বানিয়ে দিলেই হয়। অতিরিক্ত চিৎকার করে তার সঙ্গে কথা বলাটাও ছিল এক ঝক্কি। সে সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমাত আর ঘুম ভাঙলেই শুরু করতে হতো চেঁচামেচি। আকলিমা ভাবলেন, ঘুমাবেই যখন তাহলে ওই জমির শেষ মাথায় গিয়ে নিজের ঘরে ঘুমাক। প্রথমে বাছুরসহ একটা দুধেল গাই দিয়েছিলেন তাকে আকলিমা। সেটা দিয়ে বুড়ির ভালোই চলত। গাইটা মরে গেলে দিলেন একটা গাভীন ছাগল। মাঝেমধ্যে কিছু টাকা ধরিয়ে দিতেন। রাতে কখনো তরকারি বেঁচে গেলে তা-ও খোদেজার ভাগ্যেই লেখা থাকত।
তেত্রিশ বছর আগে এই বাড়িতে নতুন বউ হয়ে আসার পরে যত কৌতূহল আর দ্বিধা ছিল, সব মিটিয়েছিল ওই খোদেজা। ভাবতে ভাবতে তার দিকে তাকালে আকলিমা দেখেন পোঁটলার শাড়িটা ততক্ষণে খোদেজা গায়ে জড়িয়েছে। আগের দিনের হাজারটা ছবি কোনোরকমে শাড়ি প্যাঁচানো খোদেজার দিকে তাকালে আকলিমার চোখের সামনে দিয়ে দ্রুত সরে যায়। শাশুড়ির কাছে ভালো বউ হওয়ার জন্য তাকে গোপনে গোপনে বিরামহীন সাহায্য করে গেছে সে। কত দিনের কত স্মৃতি! আকলিমা চমকে উঠে চোখের কোণ মোছে। পুরনো দিন হারিয়ে ফেলার বেদনা নাকি চোখের সামনে খোদেজার দুর্দশা তাকে কাঁদায় ভেবে পায় না। পাশে তাকিয়ে বর্তমান সহচর রিনাকে বলে, ‘খাড়াইয়া থাকনের কাম নাই। দেখ, চাইরদিকে টিন-টুন নাইলে বেড়া যা পাও আইনা বুড়িরে একখানে ছাপড়া বানাইয়া দাও দেখি। তোমাগো লগে রাখলে ওরে তোমরা খুব জ্বালাইবা। ছাগল নিয়া ও একলাই থাক। কয়টা তো দিন, এই উডানটাই-বা টিকব কতক্ষণ আর!’
বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে আকলিমার বুক থেকে। মনে মনে ভাবে, এই দুর্যোগে বুড়ি ভাঙা ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েক কদম হেঁটে আরো দূরের অন্য কোনো বাড়িতে যেতে পারল না? এ-বাড়িতে আসার মানেইবা কী যেটা কয়েকদিনেই নদীতে চলে যাবে? এটা-সেটা দিয়ে ঘর বানানো, পলিথিন বা টিন বিছিয়ে ছাদ বানানো, দুচার দিনের জন্য এই ঝামেলার কী দরকার। কথাটা হয়তো বলতেও ইচ্ছা করে আকলিমার কিন্তু কেন যেন মুখে আসে না। খোদেজা যদি ভাবে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে? হাজার হলেও তার ওপরে খোদেজার একরকমের অধিকার আছে তা সে অস্বীকার করতে পারে না।
অনিচ্ছায় হলেও রিনা হাত থেকে পানের বাটা নামিয়ে রাখে। হেলেদুলে বেড়ার নুয়ে থাকা পাঁচিলের বাইরে যায়। টুকরো বেড়া আর ভাঙা টিনের টুকরো এখানে-ওখানে পড়েই থাকে। মানুষ বাড়ি আর দেয়াল খুলে নিয়ে যাওয়ার সময়ে অনেক কিছু পরিত্যক্ত হয়। সেসব থেকে খুঁজে কয়েকটা জিনিস হাতে করে ভাঙা পাঁচিল ফোকরে ফিরে আসতে তার বেশি সময় লাগে না। রান্নাঘর থেকে আনে দড়ি আর পাঁচিলের গা থেকে টান মেরে খুলে আনে কয়েকটা কঞ্চি। তারপর বাড়ির বাইরে গরু দেখাশোনা করার লোকটাকে ডাকতে যায়। বুড়ি যে সাহায্যে আসবে না সে তো জানা কথা, একা একা বানানোও কঠিন।
খোদেজা ততক্ষণে ধাতস্থ হয়। পাঁচিলের বাঁশে ছাগলগুলোকে বেঁধে উঠোনের একদিকে পা ছড়িয়ে বসে। আশ্রয়ের আশংকা মিটে গিয়ে তার কণ্ঠস্বরে তখন কেবল ব্যথা আর ব্যথা, ‘ভোরের আলো চউখের সামনে ফুটল গো, আম্মা। দ্যাখলাম ছুরি দিয়া টুকরা করণের মতো আমগো ভিটা কাইটা কাইটা নিয়া যাইতেছে। আমি সেইখান থেইকা সরতে পারলাম না, তাকাইয়া থাকলাম। এক টুকরা ভিটা দিছিলেন আপনি আমারে, আমার জীবনের সঞ্চয় … আমি তো সর্বস্বান্ত হইয়া গেলাম গো, আম্মা … সর্বস্বান্ত হইয়া গেলাম …।’
এতক্ষণে তীব্র কান্নায় ভেঙে পড়ে খোদেজা। সব হারানোর আর্তনাদ আকলিমা আকাশে-বাতাসে চারদিকে প্রতিধ্বনিত হতে দেখেন। চিৎকার আর কান্না বাড়ে। টিনে ঝোপেঝাড়ে বাড়ি খেয়ে সে-কান্না আকলিমার গায়ে এসে আছড়ে পড়ে। যেন বলে দিয়ে যায়, তার আর খোদেজার অবস্থানের মধ্যে এই মুহূর্তে কোনো পার্থক্য নেই। মোল্লাবাড়ির দুশো বিঘা আবাদি জমি নদীতে চলে গেছে আগেই। এরপর এদিকে পনেরো বিঘার ওপরে এই বসতভিটা, সবজির ক্ষেত আর গরুর গোয়াল যাই যাই করছে। বিয়ের পর থেকে তেত্রিশ বছরে অভাব কাকে বলে তা জানা হয়নি আকলিমা খাতুনের, বাড়িতে আদর-সম্মানও কম পায়নি। কিন্তু আজ এতদিন পরে সুখের সংসার তছনছ হয়ে যাওয়া ঢেউয়ের দিকে তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকেন। তাকিয়ে ভাবেন, তার আর খোদেজার ভাগ্য মাত্র কয়েকশো গজ আগে-পরে। এই একই কান্না কাঁদার সারিতে তিনিও প্রতীক্ষিত। আজ না-হয় কাল তারা একসঙ্গে কাঁদবে।
বাড়ির লোকেরা আরো চল্লিশ কিলোমিটার দূরে কাঠের বাড়ি বানানোতে ব্যস্ত। দিনের বেলা তাদের পাওয়া যায় না। বাড়িতে পুরুষ বলতে তখন থাকে গরু দেখাশোনা করার লোকটা, যার নাম জহিরুল। তার কাজ বাঁধাধরা। গরুর জন্য চারিভর্তি ভুসি, ঘাস, শাক-পাতা জোগাড় করে কুচি কুচি কেটে পানি মিশিয়ে পরিবেশন করা, গরুকে গোসল করানো আর দুধ দুইয়ে বাড়িতে আনা। তবে বলা নেই কওয়া নেই প্রায়ই সে বাইরে থেকে ছুটে আসে, উঠোনের মাঝবরাবর দাঁড়িয়ে হাউমাউ করে আকলিমাকে ডাকে, ‘আম্মা, শোনেন আম্মা, আইজ কী হইছে,’ কাল দুপুরেও তেমনই ছুটে এসে বলছিল।
‘কী হইল?’ আকলিমা বেশিরভাগ সময়ে তার ডাকে বারান্দায় এসে দাঁড়ান।
‘আইজ তো খালপাড়ের মসজিদটা ভাইঙ্গা পড়ছে, আম্মা।’
‘পইড়া গেল?’
‘হ, একদিকে তো কাইত হইয়া আছিল দুই সপ্তা ধইরা। ছাদের গম্বুজটা ছুইটা পিছলাইয়া নদীতে গিয়া পড়ছিল তখন। সঙ্গে মাইকটা অবশ্য যায় নাই। মসজিদের পাশের কাঁঠাল গাছে তারতুরসুদ্ধা ঝুইলা আছিল। মাইনষে তখন কইল, মসজিদ ভাইঙ্গা পড়বে না। নদীতে আর যাই নিক, আল্লাহ থাকতে তার মসজিদ ভাইঙ্গা নদীরে নিতে দিবে না। ইমাম সাহেব কইলেন, মানুষরে আজান শুনানির দরকারটা বোঝো তোমরা, মিয়া? দেখ, সেইজন্যি গম্বুজটা গেছে গেছে, মাইকটা কিন্তু ঠিকই আটকাইয়া থাকল। আজান শুইনা মন দিয়া এইখানে বইসা আল্লারে ডাকলে গম্বুজের কী দরকার?’
‘ভাইঙ্গা পড়ার পরেও কাইত হইয়া থাকা ওই মসজিদে তোমরা নামাজ পড়তেছিলা কোন হিসাবে? এমন কী দরকার পড়ছিল ওইখানে নামাজের?’ আকলিমা বলে ফেলেন হঠাৎ। এমনিতে গ্রামের কারো সাহস হবে না মসজিদে নামাজ পড়া নিয়ে রাস্তাঘাটে এমন প্রশ্ন তোলার। মুখ ফসকে বলার পরে আকলিমা আঁচল দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরেন। তবে সামনে উৎকণ্ঠিত জহিরুলের তা নজরে আসে না। সে বলে, ‘আসলে … হইছে কী, আম্মা, ইমাম সাহেব কইলেন পৃথিবীতে নাকি খুব নামডাকওয়ালা একখান বিল্ডিং আছে, যুগের পর যুগ এইরাম বাঁকা হইয়াই খাড়াইয়া আছে কিন্তু ভাইঙ্গা পড়ে নাই। এইরাম হেইলা আছে দেইখাই সেইটা বিখ্যাত আর কী। তাই আমরার মসজিদও ধরেন গিয়া সেইরাম হইতে পারে। এখন দ্যাখেন, কতা হইল কে ভাবছিল যে আল্লার ঘরও পানিতে ভাসাইয়া নিয়া যায়!’
আকলিমা সেই যে মুখে আঁচল চাপা দিয়েছেন, তারপর আর কথা বলেননি। কে জানে সরল আর বোকাসোকা জহিরুল আবার রাস্তায় গিয়ে তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কাকে কী বলে বসে।
এই বাড়িতে ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে থাকার মধ্যে ছিল আকলিমা আর তার মেয়ে পাপিয়া। থমথমে দুপুর আর আলো-পড়ে-যাওয়া বিকেলগুলোতে উঁচু বারান্দার দুদিকের দুটো বেঞ্চে বসে পাঁচিলের ওপর দিয়ে তারা নির্বাক সেদিকে তাকিয়ে থাকে। তবে প্রলয়ের ঢাকঢোল দুজন দুরকমভাবে শোনে, দেখে দুই ভিন্ন উপলব্ধি থেকে। আকলিমা তাকিয়ে থাকেন স্বামীর সংসারের গর্বের ধন আবাদি জমিগুলো ডুবে যাওয়া জায়গাটার দিকে, যেখানে এখন উথাল-পাতাল ঢেউ। আর আঠারো বছর বয়সী পাপিয়া তাকিয়ে থাকে বাড়ির ঠিক পেছনের সুপারিবাগানের দিকে। গোটা তিরিশেক সরু আর আকাশের দিকে ধাবমান সুপারিগাছ সেখানে একবার এদিক আরেকবার ওদিকে হেলে শুয়ে পড়তে চায়। বাতাসের ঘনঘন গতি পরিবর্তনের সঙ্গে একমত হতে গিয়ে লকলকে গাছগুলোর কোনোদিকেই শুয়ে পড়া হয় না। নদী থেকে আসা ভেজা ভেজা বাতাসে ডোবা আর ছায়ায় ঘেরা সেখানকার স্যাঁতসেঁতে মাটির দিকে পাপিয়া তাকিয়ে থাকে। সুপারিবাগানের মাটির ওপরে এখন আর কোনো চিহ্ন নেই যে সেখানে রাতের অন্ধকারে একটা কবর খোঁড়া হয়েছিল। লম্বায়-চওড়ায় ছোট্ট কবর, এমনকি গভীরও সাড়ে তিন হাত নয় মোটেই। মাঝরাতের অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে মাত্র হাত দুয়েক গভীর গর্ত করাও কঠিন ছিল। কিন্তু গরুর রাখাল, জহিরুল তা করেছিল। আকলিমার গোপন আদেশ পেয়ে গরুর গোবর ওঠানোর কোদাল হাতে নিয়ে সুপারিবাগানে গিয়ে হাজির হয়েছিল। সেখানে তখন হু-হু করে শিস দেওয়া বাতাস। স্রোতের ধাক্কায় বড় বড় মাটির চাক কিছু বিরতিতে পানির গর্ভে ঝুপঝাপ করে পড়ার বিষণ্ন শব্দ। অবশ্য তখনো এতটা ভাঙেনি, তাই সে-শব্দ ছিল দূর থেকে ভেসে আসা। ফাঁকে ফাঁকে আরো দূরের শিয়াল-কুকুরের ডাকও শোনা গেছিল। টর্চের টিমটিমে আলোয় যত দ্রুত পারা যায় নরম আর ভেজাভেজা মাটি সরিয়ে জহিরুল গর্তটা খুঁড়েছিল। তারপর কোদাল হাতে ফিরে এসে আকলিমাকে খবর দিয়েছিল। তাকে ফিরতে দেখে পাপিয়ার ঘর থেকে তিন-তিনটা চাদরে প্যাঁচানো মাংসের দলার মতো মৃত একটা বাচ্চা পেঁচিয়ে পোঁটলা করে আকলিমা চালান করেছিলেন জহিরুলের হাতে। শরীরের পাশ থেকে পড়ে থাকা আধাআধি তৈরি হওয়া বাচ্চাটাকে উঠিয়ে আনাতে পাপিয়া নিষেধ উপেক্ষা করে কেঁদে উঠতে গিয়েছিল। আকলিমা ইশারায় ওটা পুঁতে দেওয়ার কথা জহিরুলকে বলেই ছুটে গিয়ে পাপিয়ার মুখ চেপে ধরেছিলেন। মায়ের দশ আঙুলের চাপে পাপিয়ার তখন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়।
তারপর থেকে পাপিয়া আর শব্দ করে কাঁদেনি। তার আগে অনেক কেঁদেছিল যখন ভালোবাসার মানুষকে বাপ-চাচারা মিলে গ্রামছাড়া করেছিল। রাতারাতি পিটিয়ে পরিবারসহ তাদের গ্রামের সীমানা পার করে দিয়েছিল মোল্লাবাড়ির বিশ্বস্ত লোকজন। হুকুম পালনই ছিল তাদের ধর্ম যাদের মোল্লাবাড়ির জমিতে কাজ করে আয় করতে হতো, তাদের অনুগ্রহে বেঁচে থাকতে হতো। তারা জানত মোল্লাবাড়ির মুখের কথাই ওই গ্রামে আইন। তাদের সম্মান রক্ষাই তাই বিশ্বস্তদের দায়িত্ব হয়ে থাকত। চাষাভুষার ছেলে হয়ে পাপিয়ার সঙ্গে জীবন কাটাবে এরকমটা যে স্বপ্নেও ভেবেছে গ্রামছাড়া করে তার স্বপ্নভঙ্গ করানোটা জরুরি হয়ে পড়েছিল। সেই ঘটনার পর থেকে পাপিয়ার আশ্রয় হয়েছিল নিচতলার শেষ মাথার একটা ছোট্ট ঘরে। আগে যেখানে বাড়তি চালের বস্তাগুলো ফেলে রাখা হতো, যখন অনুমানের চেয়ে বেশি ফসল ঘরে উঠত, যখন গোলায় জায়গা ধরত না। বস্তা ফেলে রাখার উপযুক্ত একটা পরিবেশও ছিল সেই ঘরে, অনেক উঁচুতে বাতাস চলাচলের জন্য কয়েকটা ফোকর কিন্তু নিচের দিকে শুধুই দেয়াল। আকলিমা নিজে হাতে ঘুপচির মতো ঘরটার দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তালার চাবি সাত মাস ধরে আকলিমার আঁচলেই বাঁধা থাকত।
বদ্ধ ঘরটায় কখনো দুঃখে কখনো নিশ্বাসের উপযুক্ত বাতাস না পেয়ে হাউমাউ করে কাঁদত পাপিয়া। তার কান্নার শব্দে দরজা খুলত না। শেষে একদিন খাবার দিতে এলে মায়ের কাছে সে বলেই ফেলেছিল তিন-চার মাস ধরে পেটে বাচ্চা আসার কথাটা। ভেবেছিল ওটা বললে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে ওই ঘুপচি থেকে বের করে আনবে তারা। ভেবেছিল তাড়িয়ে দেওয়া ছেলেটিকে পরিবারসহ খুঁজে আনা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না তাদের। তারা ছেলেটির কিছু খোঁজখবর তখন করেছিল ঠিকই; কিন্তু নদীর ভাঙনে দূরগ্রাম থেকে এসে ওখানে কয়েক মাসের জন্য আস্তানা গাড়া পরিবারটি মোল্লাবাড়ির পালিত লাঠিয়ালদের ভয়ে কত দূরে, পৃথিবীর কোন কোণে গিয়ে আত্মগোপন করেছে তা আর খুঁজে বের করা যায়নি।
হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকের চিহ্নস্বরূপ পেটের সন্তানটিকে বড় মায়া লাগত পাপিয়ার। কিন্তু তাকে তো আর লোকচক্ষুর আড়ালে ওই ঘুপচিঘরে মানুষ করা চলে না। তাছাড়া, ওই খোদেজাকে দিয়ে আকলিমা কবিরাজের কাছ থেকে কী যেন এনে খাইয়ে দিয়েছিলেন তাকে। সাত মাসের মাথায় মরা সন্তান বেরিয়ে এসেছিল। তারও মাস তিনেক পরে কাঁদতে কাঁদতে থমকে যাওয়া পাপিয়া যখন বদ্ধ ঘর থেকে মুক্ত হয়েছিল তখন ছুটে গেছিল সুপারিবাগানে। মায়ের মুখে শোনা কথা অনুযায়ী সেখানে কোথাও কবরের মতো মাটি উঁচু করা ছিল না। তাকে উদ্ভ্রান্তের মতো দৌড়াতে দেখে শেষে গরু গোসল করিয়ে ফিরে আসতে থাকা রাখাল, জহিরুল সেখানে ঢুঁ মেরেছিল। ইশারায় দেখিয়ে দিয়েছিল তিনটা সুপারিগাছের জোড়া লাগা গোড়ার সামনের জায়গাটা। বলেছিল যে ইচ্ছে করেই চিহ্ন রাখা হয়নি। কেউ যেন জানতে না পারে।
সেই থেকে পাপিয়া তাকিয়ে থাকে তার সন্তানের কবরের দিকে আর আকলিমা তার সম্পদ – ভেসে যেতে থাকা জমির দিকে। দুজনের হারানোর বেদনা দুরকম। নদীর উত্তাল ঢেউ দুজনের স্মৃতি আর অনুভূতিতে দুভাবে আঘাত করে। পাপিয়া ভাবে, এই তো আর পাঁচ-ছয় বিঘা জমি চলে গেলেই তার অচেনা সন্তানের কবরটা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যে-সন্তান কোথাও ছিল না, কোনোদিন তার কোলে খেলেনি, যার অস্তিত্ব কেবল তার স্বপ্নে, তার গভীর উপলব্ধিতে, এরপর এই পৃথিবীর মাটিতেও তার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। সে হয়ে যাবে পুরোপুরি নিরাকার। ভাবতে ভাবতে তার চোখ থেকে পানি গড়ায়, স্বচ্ছ পানি নদীরই মতো এঁকেবেঁকে গাল বেয়ে গলায় নামে।
আর আকলিমার কাছে ওই জমির অস্তিত্ব তার জীবন ধারণের নিশ্চয়তা। দূরে বাড়ি করা হয়ে গেছে প্রায়, সে জানে। কিন্তু দুশো বিঘা জমি? সবটুকু ভেসে যাওয়ার পরে এখন কোথা থেকে আসবে ফসল, কোথা থেকে এই এত মানুষ চালানোর তাকত পাবে তারা? আসতে-যেতে এই যে সালাম, মাথাটা নুয়ে থাকা, মুখের কথায় মেরে পিটিয়ে উচ্ছেদ করানো আর দিনভর ক্ষমতার ছড়ি ঘোরানো, কী হবে তার? বাকি জীবনটা ঝকঝকে নতুন একটা বাড়ির মধ্যে চুনোপুঁটির মতো বাঁচতে হবে তাকে? সোনার খাঁচায় বন্দি পাখির মতো? অর্থবিত্তে ছোট, বুদ্ধিতে গাড়ল আর অধিকারের প্রশ্নে ছাড় দেওয়া গ্রামের হাবা ধরনের মানুষগুলোর ওপর হুকুম তামিলের সুযোগ থাকবে না? এ কী করে মানা যায়! শেষ জীবনে তার কপালে কত কষ্টই না লেখা ছিল। ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে তাই সে মনে মনে বলে, বাইরে বাইরে চাকচিক্য আর ভেতরে ভেতরে ওরকম অসহায় আর নিরুপায় জীবন থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো।
এই কথাটা তার স্বামীকেও আকলিমা মুখ ফুটে বলেছেন। তিনি অল্প সময়ের জন্য বাড়িতে আসেন। তার বহুদিকে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। এমনকি নদীভাঙন ঠেকানোর মতো অসম্ভব কাজও তিনি করতে চান। তবু সকালে নাস্তা খাওয়ানোর সময়ে আকলিমা ইনিয়ে-বিনিয়ে সেদিন তাকে প্রশ্ন করেন, ‘চাইর বছর হইয়া গেল ভাঙ্গন চলতেছে। কিছুই কি করণের নাই আর?’
‘আরে, দেখো না কত্ত দৌড়াদেড়ি করি এই নিয়া? জমি যা গেছে গেছে কিন্তু যা আছে সেইটাও যদি বাঁচাইতে পারতাম। পানি উন্নয়ন বোর্ডে কত্তবার গিয়া অফিসারদের সঙ্গে দেখা করলাম। বর্ষার মৌসুমে ভাঙার সময়ে গেলে বলে শুকনা মৌসুম আসুক তখন দেখা যাবে। আর শুকনা মৌসুমে আকাশ থেইকা পইড়া বলে, নদী কি ভাঙতেছে নাকি এখন? গেরামের মানুষগো গেরামছাড়া করতেই এই খেলা চলতেছে। আরে, কত অফিসার, কত নেতা আইল-গেল, আইসা আইসা আমাদের সর্বনাশ স্বচক্ষে দেইখা গেল, কিন্তু বছরতিনেক পর্যন্ত তো একটা বালুর বস্তাও কেউ ফালাইল না নদীর মইদ্দে!’
‘হুম, কী আর করবেন। আমি তো দেখছি আপনে অনেক চেষ্টা করছেন।’
‘তা করছি। কিন্তু কী হইছে তাতে, তিন বছর চেষ্টা করার পরে গত বছর তারা আইসা হাতেগোনা কয়টা বালুর বস্তা ফালায়া দিয়া গেল আমাগো তীরে। কিন্তু তাতে কী লাভ হইল, বলো? এইদিকে আছিল পুকুর, বস্তার বাঁধের নিচ দিয়া নরম মাটি সইরা পানি ঢুইকা গেল। এত্ত যে চেষ্টা করলাম, জমি তো বাঁচাইতে পারলাম না। এই বছর দৌলতদিয়া আর দেবগ্রামের একশ বাড়ি উইঠা গেছে। তারা কেউ কেউ সময়মতো উডতেও পারে নাই, জিনিস নিছে তো বাড়ি নিতে পারে নাই, গরু নিছে তো রান্নাঘর নেয় নাই। এই হইল অবস্থা।’
‘আপনে কি আর যাবেন না অফিসারদের কাছে?’
‘আর গিয়া তো লাভ নাই। শুনছি তারা আমাদের জমি বাঁচানির লাইগা একটা প্রজেক্ট নিছে, মানে, পরিকল্পনা। কিন্তু কথা হইল এইদিকে নদী ভাইঙ্গা উজাড় হইতেছে এখন আর ওই পরিকল্পনা নাকি পাশ হইয়া বাঁধ বানাইতেই সময় লাগবে দুই বছর। ততদিনে এই গ্রামের পরের দুইডা গ্রামও ভাইসা যাবে। তখন আবার নতুন পরিকল্পনা লাগবে, বুঝতে পারতেছ?’
‘হ, আমাগো আর উইডা যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। শ্যাষ বয়সে কপালে এত দুঃখ আছিল!’
‘দুঃখ পাইও না। এইহান থেইকা চল্লিশ কিলোমিটার দূরে আমি বাড়ি বানাইতেছি। গেরামের পর গেরাম ভাইসা গেলেও বাঁইচা থাকতে তোমার কষ্ট হবে না।’
‘কষ্ট হইব না কইলেই হইল? ওনারা বিরিজ বানাইতেছেন, ভালো কতা। শিমুলিয়াত ডকইয়ার্ড না কী জানি একটা বানাইয়া রাখছেন তাই ওইদিকে পড়ল চর। এহন উলডা দিকে যে নদী ভাঙব সেইটা তারা আগে দ্যাখবেন না? কিয়ের বিরিজ এত্তগুলা মানুষরে উডাইয়া দিয়া, জমিজমা কাইড়া নিয়া?’
বলতে বলতে আকলিমা কান্না শুরু করেন। স্বামী তার কান্নার দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ‘কত মানুষ সর্বস্বান্ত হইল, চউখের সামনে থানার পাশের দুই-তিন তলাগুলাও নদীর তলে গিয়া ঠেকল, কী আর করার আছে আমাগো। তুমি আর কাইন্দ না।’
স্বামীর কথা অমান্য করে সেখানে বসে কাঁদা অন্যায় হয় বলে আকলিমা উঠোনের দিকের বারান্দায় গিয়ে বসেন। ঢেউয়ের তীব্র গর্জন শুনলে মনে হয় তারা আকলিমাকে বলছে, খাইয়া ফালামু, ভাইগা যাও, চইলা যাও … আকলিমা ঢেউয়ের ভাষা বুঝতে পেরে ডুকরে কেঁদে ওঠেন। রাতের অন্ধকারে হু-হু বাতাসে শরীরে ভেজা ভেজা অনুভূতি হয়। উঠোনের বামদিকের ছাপড়া ঘরের ভেতরে খোদেজা বেগমের ছাগলেরা কখনো নড়াচড়া করে। কখনো ছোট্ট একটা ব্যাঁ শোনা যায়। উত্তর দেওয়ার মতো উঠোনের আরেক দিকের গোয়ালঘর থেকে একটা গরু হাম্বা করে ডেকে ওঠে। খোদেজা বেগমের কোনো সাড়া নেই। সে ঘুমে অচেতন থাকে প্রায়। আজকাল পেট পুরে বাড়ির খাওয়া পেয়ে বুড়ির ঘুম মনে হয় আগের চেয়েও গাঢ় হয়েছে। নিচু ছাপরা ঘরে দাঁড়ানোর উপায় নেই, প্রায় কুঁজো বুড়ির সুবিধা হয়েছে, দিনেও তাই পড়ে পড়ে ঘুমায়। তবে দিনে যতটুকু সময়ে জেগে থাকে ততক্ষণে নানান ধরনের কাজকর্ম চলে তার। পুরনো আর জং ধরে ফুটো হয়ে যাওয়া বড় একটা কড়াই রান্নাঘরের পেছনে পড়ে থাকতে দেখে খোদেজা কাদা গুলিয়ে নেয় একদিন। তারপর যত্ন করে তার ওপরে তিনটা গম্বুজ বানিয়ে চুলার আকৃতি এলে আকলিমাকে বলে, ‘বাড়ি ছাইড়া কুথাও দৌড়াইতে হইলে সবথেইকা আগে যা লাগে, তা হইল গিয়া চুলা।’ কড়াইয়ের দুদিকের আঙটা ধরে ভারী চুলাটা ওঠানোর চেষ্টা করেও না পেরে হাঁপায় সে। চুলাটা একচুল নাড়াতে না পারলেও আকলিমার দিকে তাকিয়ে গর্বের হাসি হাসে। অথচ উদ্বাস্তু চুলা দেখে আকলিমার চোখে পানি এসে যায়।
বিকেলের দিকে অবশ্য খোদেজা ভাঙা পাঁচিলের ফোকর দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় পাপিয়ার হাত ধরে। নদীই নাকি তার সব, নদী না দেখলে নাকি তার পেটের ভাত হজম হয় না।
পাপিয়াও আজকাল বুড়ির সঙ্গে ভালোই আছে। আকলিমার দিকে তাকায় না বেশি, তার সঙ্গে সারা বিকেল বারান্দায় বসেও থাকে না। মায়ের প্রতি তার হয়তো অনেক রাগ। নানান সহচর আর পানের সান্নিধ্যে বারান্দায় বসে বিকেলে আকলিমা দেখে পাপিয়া বুড়ির হাত ধরে সুপারিবাগানের ওদিকটায় যায়, কী কথা হয় তাদের সে জানে না, শুধু দূর থেকে দেখে কখনো পিঠ বেঁকে ঝুঁকে পড়া বুড়ি কষ্ট করে উঁচু হয়ে তার মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।
সত্যি সত্যিই প্রবল ঘৃণায় মায়ের কাছেধারে থাকতে ইচ্ছা করে না পাপিয়ার। তার চেয়ে খোদেজা বেগমের সঙ্গে এবড়োখেবড়ো জমির ওপর দিয়ে হেঁটে নদীর গর্জন শোনা ভালো। এই যে নদী তাদের সব কেড়ে নেয় অথচ নদীর প্রতি মায়া তো কাটে না! তার কাছে যেতেই হয়। হাঁটতে হাঁটতে দেখে টুপি মাথায় তিনজন মানুষ আলের ওপর দিয়ে সারি বেঁধে যায়। তাদের মধ্যে একজন চোখ মোছে। তাদের চেনে পাপিয়া, গ্রামের আরেক দিকের একই পরিবারের মানুষ তারা, তিন ভাই। খোদেজা বলে, ‘আহ্হা রে, শ্যাষবারের মতো কবর জিয়ারত কইরা গেল মুনে হয়।’
‘কার কবর?’ চমকে বলে পাপিয়া।
‘উনাদের বাপের। আল্লায় চাইলে আইজ রাইতেই মুনে হয় ভাইঙ্গা পড়ব। কাইল বিয়ানে আইলে আর বাপের কবর খুঁইজা পাইব না পোলারা।’
‘আইচ্ছা, বাড়ির মতো কবর উডাইয়া নিয়া যাওয়া যায় না, বুড়ি?’ হুট করে অক‚লে খড়কুটো পাওয়ার মতো করে বলে পাপিয়া।
‘ধুর, কী যে কয় মাইয়া। কবর উডাইব ক্যামনে? তাগো বাপ মরছে কত্ত বছর আগে, খুঁড়লে দ্যাখবে খালি দুই টুকরা হাড্ডি। ধরতে গেলে সেইডাও ঝুরা হইয়া পড়ব। কী করব হেইডা দিয়া?’
‘হুম’, বলে পাপিয়া সুপারিবাগানের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সুপারিগাছগুলো শনশন করে হেলেদুলে পাপিয়ার ভাবনায় অংশ নেয়। সে চোখ সরাতে পারে না। খোদেজা বলে, ‘এই জায়গা থেইকা সইরা গেলে ভুইলা যাবা। জোয়ান মাইয়া, বিয়া হইব, সব ঠিক হইয়া যাইব। তোমার জন্য এই নদী ভাঙ্গনই ভালা।’
পাপিয়া কেঁদে উঠে বলে, ‘তুমিও জানো, বুড়ি!’
‘মাইয়া কী কয়, জানব না? তর মায়ের সব জানতে হয় আমারে’, পাপিয়ার মুখ কান্নায় বিকৃত হয়ে গেলেও খোদেজা ঠিকই তার মুখের কথাটা ধরে জবাব দেয়।
শুনে পাপিয়া খোদেজাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ভাসায়। বুড়ি বলে, ‘শোনো, আমারো একটা মাইয়া আছিল, বুচ্ছ? আমার নিজের মাইয়া’, এক হাতে লাঠি ধরে কেঁপে উঠে নিজের পেটের ওপরে খোদেজা আরেকটা হাত রাখে। তারপর দূরে কোনোদিকে অর্থহীন দৃষ্টি রেখে বলে, ‘হেইডা হইল সেই যুদ্ধের বছর। ঠিক তোমার মতো বয়স আছিল আমার। আমাগো তখন খাওন নাই, লুকানির জায়গা নাই, খালি পলাইতে হইব, খালি দৌড়, দিনরাইত দৌড়। একদিন আর্মি আইসা গেরামের পোলাগো গুলি কইরা মারল। গুলির শব্দ শুইনা রান্নাঘর থেইকা বাইর হইয়া দেহি আমার স্বামী রক্ত মাইখা উডানে পইড়া আছে। দিশা না পাইয়া মাইয়াডারে কোলে নিয়া নদীর ঘাটের দিকে দৌড় দিলাম। সেইখানে অনেক মানুষ হুড়াহুড়ি কইরা নৌকায় উঠতেছে। আমিও উঠতে নিলাম। পিছন থেইকা গুলি আসতেছিল একটু পরপর। হঠাৎ মনে হইল আমি একটা ধাক্কা খাইলাম। ধাক্কা কেউ দিলো না; কিন্তু আমি একটু আগায়া গেলাম ধাক্কার টানে। তারপর সোজা হইয়া নৌকায় উইডা বসলাম।’
‘তারপর?’ পাপিয়া কান্না ভুলে চোখ গোল গোল করে তাকায়।
‘আমি বসতেই নৌকা জোরে টান দিলো। আরো গুলি আসল পিছনে কিন্তু আমাদের কারো গায়ে লাগল না। আমরা পলাইতে পারলাম। মাঝনদীতে যাওনের পরে মনে হইল আমার শরীর ক্যান জানি ভিজা। কোলের মধ্যে মাইয়ার মুখে হাতড়াইয়া দেখি তার মাথার খুলি নাই। ওই যে যখন ধাক্কা খাইছিলাম, তখনই গুলি আইসা তার মাথাডা উড়াইয়া নিছে। মনে হইল, এইডা কী করলাম আমি, মাইয়ার মাথার খুলিডা নদীর তীরে ফালাইয়া আসলাম! আফসোসে কাইন্দা ফেললাম। দুই পাশ থেইকা দুইজন আমার মুখ চাইপা ধরল। নৌকায় আলো আছিল না। কিন্তু শব্দ হইলে আর্মিরা আমাগো ধইরা ফেলতে পারে। মাঝনদীতে অনেকক্ষণ মূর্তির মতো বইসা থাকলাম আমরা। বুকের কাছে মাইয়ার লাশডারে চাইপা ধইরা থাকলাম যেন আর গুলি না লাগে। সবাই কইল লাশডা নদীত ফালায়ে দিতে, নাইলে পরে আমি দৌড়াব কেমনে? আমি ফেলতে চাই নাই। কিন্তু শ্যাষে সবার জোরাজুরিতে …’
খোদেজা বলতে বলতে থেমে যায়। পাপিয়া ওইটুকু শুনেই হু-হু করে কাঁদতে থাকে। খোদেজা কষ্ট করে একটু সোজা হয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, ‘পাগলি মাইয়া, কতজনের কত কী নদীতে যায় তার কি হিসাব আছে! একদিন এই নদীর মইদ্দে সব ফালাইয়া দিয়া তুমিও বাঁইচা থাকবা।’
খোদেজার হয়তো আর কান্না পায় না। দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে শুধু। দূর থেকে মাটির চাঙড় ভেঙে পড়ার শব্দ আসে। সামনে নদীর ঢেউ, গায়ে বাতাসের ঢেউ, পাশে সুপারিগাছগুলো শনশন করে কী যেন বলে যায়। দুর্বোধ্য সে-কথা পাপিয়া ছাড়া আর কেউ বোঝে না।