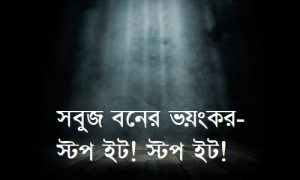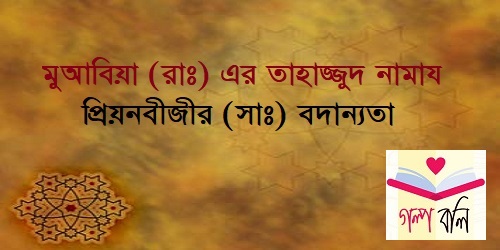জোছনাবৃষ্টি শুরু হলেই মা আমাকে ডাকে…।
দেশের আর কোথাও, কোনো গাঁ-ঘরে জোছনাবৃষ্টি হয় কিনা জানি না। কিন্তু আমাদের গাঁয়ে জোছনাবৃষ্টি হয়। প্রত্যেক পূর্ণিমায় জোছনাবৃষ্টির বান ডাকে গাঁয়ে। ঘরের চালে, খড়ের পালায় নৃত্য করে জোছনাবালিকার দল। সে এক দৃশ্য বটে! যাদের ওই নৃত্য দেখার চোখ আছে, সবার নেই; তারাই শুধু তা দেখে। ঘটনা আরো আছে। পূর্ণিমার চাঁদ তো উঠে – বলতে গেলে দিন থাকতেই। সূর্য গাঁয়ের পশ্চিমে চিতাখোলার ওপার, গোরস্তানের ওপার ডোবে কি ডোবেনি, পূর্ণিমার চাঁদ তখনই আকাশে তার মায়াবী মুখ বের করে। চাঁদ যেই না মুখ বের করে, যেই না জোছনা-ছড়ানো শুরু করে – চিতাখোলা আর গোরস্তানের আত্মাদেরও ঘুম ভেঙে যায়। কেউ উঠে বসে। আড়মোড়া ভাঙে। কেউ কেউ পায়চারি শুরু করে। চিতাখোলা কিংবা গোরস্তানের বাসিন্দারা কেউ তাদের স্বজনদের সেদিন ডাকে কিনা জানি না, আমার মা আমাকে ডাকে…।
আমাদের গাঁয়ের নাম সুনন্দপুর। গ্রামটি পুবে-পশ্চিমে লম্বা; অজগর সাপের মতো শুয়ে আছে। গাঁয়ের দক্ষিণ পাশে ঘোড়ার গাড়ি চলার মতো কাঁচা রাস্তা; রাস্তার সব বাড়ির সামনে সারিসারি সুপারি গাছ; বাড়িতে আম-কাঁঠাল, জাম-জামরুল, ডইয়া-ডেফল, আতা-কামরাঙা, চালতা গাছ। গাছে গাছে শালিক-ঘুঘু-দোয়েলের বাসা। সব বাড়ির পেছনে বাঁশঝাড়, বেতঝোপ, বেতঝোপে সন্ধ্যাতারার মতো ঝলমল করে কাইয়া-কাঁঠাল। গাঁয়ের উত্তর-গা-ঘেঁষে নদী। নদীর নাম সুনন্দা। পৃথিবীতে এতো সুন্দর নামের গ্রাম-নদী আর কোথাও নেই, তা আমি হলফ করে বলতে পারি। সব বাড়ির বাঁশঝাড়ের ছায়া নুয়ে পড়ে নদীতে। গাঁয়ের পশ্চিম মাথায়, এই সুনন্দার ধার ঘেঁষে, বসতবাড়ি থেকে একটু দূরে পাশাপাশি চিতাখোলা আর গোরস্তান। নদীর ঢালুতে চিতাখোলা, মাঝখানে রাস্তা, রাস্তার পাশে গোরস্তান। গাঁয়ের হিন্দু-মুসলমানদের ওপারবাড়ি। বাবা-মা শুয়ে আছে এই গোরস্তানে। বাবা আমাকে কোনোদিন ডাকে না। মায়ের পনেরো বছর আগে, গাবাক্ষেতে বিআর-২৯ ধানের চারা রোপণ করতে করতে; মাকে কিছু না-বলে, আমাদের ভাইবোন কাউকে কিছু না-বলে বাবা দুম করে ওপারবাড়ি চলে গেছে। বাবা ছিল আমার দাদার রাখালপুত্র। চকজুড়ে জমি-জিরেত ছিল দাদার। তখন আমি শিশু। তারপরও মনে পড়ে, দেখতাম – বাবা চাষবাস নিয়ে এতোটাই ব্যস্ত থাকত সারাদিন, আমাকে কখনো কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর ফুরসত মিলত না তার। এখনো হয়তো ওপারবাড়ির ক্ষেত-খলা, গরু-বাছুর নিয়ে দিনমান ব্যস্ত থাকে, এপারবাড়িতে যেমন ভোরবেলা বাড়ি থেকে বেরোত, কোনোদিন দুপুরে ভাত খেতে বাড়ি ফিরত, কোনোদিন ফিরত না, ফিরতে ফিরতে সেই সন্ধ্যা; ওপারবাড়িতেও হয়তো তাই। আমি ছিলাম বাবার পড়ন্তবেলার সন্তান। খুব বেশিদিন আমাকে দেখেইনি। হয়তো আমাকে তার মনেই নেই; ডাকবে কী? এই, এতোদিনে, ভুল করেও বাবা কোনোদিন আমাকে ডাকেনি। কিন্তু মা আমাকে ডাকে। গাঁয়ে জোছনাবৃষ্টি শুরু হলেই আমি মায়ের ডাক শুনি। অমোঘ ডাক। ব্যাকুল ডাক। আগুন দেখে অবোধ পতঙ্গ যেভাবে ছুটে যায়, আমিও সেভাবে মায়ের কাছে ছুটে যাই। মাকে জড়িয়ে ধরে বকুলতলায় বসি…।
মায়ের ওপারবাড়িতে বকুলগাছটি আমিই লাগিয়েছি। আমাদের বাড়িতে বিশাল বড় একটি বকুলগাছ ছিল। ছোটবেলায় দেখেছি – খাঁজকাটা বরফখ–র মতো অজস্র সাদা ফুল ধরত গাছে। ভোরবেলা গাছতলায় পড়ে থাকা ফুল কুড়িয়ে কুশিবুজি মালা গাঁথত। আমাকেও দিত মালা। সেই গাছটি, আমি সে-বছর এইটে পড়ি, ঝড়ে ভেঙে পড়ে। এতো সোজাসাপ্টা একটা গাছ ঝড়ে ভেঙে পড়তে পারে – এটা আমার কল্পনার মধ্যেও ছিল না। দাদা তখনো বেঁচে ছিল, এর কয় মাস পরে ১৫ জুলাই দাদা মারা যায়। সে যাই হোক, ঝড়ে-ভাঙা গাছটি কেটে দাদা কী কাজ যেন করেছিল। তখন নতুন করে আর বকুলের চারা লাগানো হয়নি। কে জানে, কেন, কিছুদিন ধরে মা বারবার বাড়িতে আবার একটা বকুলচারা লাগানোর কথা বলছিল। আমিও চারা খুঁজছিলাম। বকুলফুল আমারও খুব প্রিয়। কিন্তু কোথাও চারা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। দেশে এখন বকুলগাছ, বকুলচারার আকাল পড়েছে। ছোটবেলায় দেখেছি, গাঁয়ের প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে বকুলগাছ, ছোট কি বড়, পাতলা মাথার কি ঝোপালো; বকুলগাছ আছেই। আমাদের বাড়ির গাছটাই ছিল সবচেয়ে প্রকা- গাছ; সব বাড়িতেই বকুলগাছ দেখে – আমার কখনো কখনো মনে হয়েছে, আমাদের গ্রামের নাম সুনন্দপুর না-হয়ে বকুলপুরও হতে পারত। তাহলেও মন্দ হতো না। কোনো গ্রামের নাম বকুলপুর শুনলেই মনটা জুড়িয়ে যায়। এখন, আমাদের সুনন্দপুরে, কারো বাড়িতে বকুলগাছ নেই। মনিকেও বকুলচারা খোঁজার দায়িত্ব দিয়েছিলাম। মনি আমাদের প্রতিবেশী। সা’দত কলেজের ছাত্র। হিসাববিজ্ঞান পড়ে। আমার গল্প-কবিতার মুগ্ধ পাঠক। মনিকে বকুলচারা খোঁজার প্রস্তাব দিতেই সানন্দে রাজি হয়েছে। বলেছে – দুটি চারা পেলে একটি নিজেদের বাড়িতে লাগাবে। কার কাছে যেন শুনেছে – পাহাড়িয়া এলাকার নার্সারিতে বকুলের চারা পাওয়া যেতে পারে। সন্ধানপুর, শালিয়াবহ, সাগরদিঘি – আরো কোথায় কোথায় যেন চারা খুঁজেছে মনি। কোথাও পায়নি। যেদিন সখীপুরে বকুলচারা খুঁজে পেল মনি, দুপুরের পর চারা নিয়ে আমাদের বাড়িতে এলো, মা তখন ওপারবাড়ির পথে যাত্রা শুরু করেছে…।
সেদিন ছিল আশুরা – মহররম মাসের দশম দিবস; আমাদের যাপিত দিনপঞ্জিতে নভেম্বরের ২৫। ইতিহাস সাক্ষী – হিজরি ৬১ সালের এই দিনে ফোরাত নদীর তীরে কারবালা প্রান্তরে শহিদ হন ইমাম হোসেন। এজিদ-সৈনিক সিমার খঞ্জর চালিয়ে গলা কাটে মুহাম্মদ-দৌহিত্র হোসেনের। সেদিন হোসেন-বংশ প্রায় নির্বংশ হয়েছিল। ফোরাত নদীতে বইছিল শোণিত স্রোত। হোসেন-বংশের রক্তের বিনিময়ে পবিত্র হয়েছে দিনটি। তাই এই দিনে কেউ ওপারবাড়ি গেলে লোকটি স্বর্গবাসী হন বিনাবিচারে…।
মা ওপারবাড়ি যাচ্ছে। আমি বাড়িতে এসে দেখলাম – সমবেত গ্রামবাসী, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন অনেকেই কান্নাকাটির ফাঁকে ফাঁকে কিংবা মায়ের ফেলে-যাওয়া মরদেহের সৎকারের প্রস্ত্ততি নিতে নিতে সৃষ্টিকর্তার শুকরিয়া আদায় করছে। আহা রে, কী ভাগ্যবতী ছিল সুমিতের মা! আশুরার দিন গেল। জান্নাতবাসী হবে…।
ওপারবাড়ির ডাক এসেছে, যে-কোনোদিন মা আমাদের ছেড়ে চলে যাবে; এটা আমি অনেকদিন আগেই বুঝে ফেলেছিলাম। কীভাবে বুঝলাম? বলি তবে। আমি যতক্ষণ বাড়িতে থেকেছি, দেখতাম – মা বড়ঘরের বারান্দায় পিঁড়ি পেতে একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে থাকত। হাতে কুকুর-বিড়াল তাড়ানো লাঠি। কোনো কুকুর-বিড়াল তার কাছাকাছি আসুক কি না-আসুক, মা কিছুক্ষণ পরপর ‘এই বিলাই, এই কুত্তা, ঘরে ঢুকিস না’ বলে কুকুর-বিড়াল তাড়াত। কখনো কখনো মায়ের সঙ্গী থাকত তার ছোট পুতি – মিতু। বেশিরভাগ সময় একাকী বসে থাকত। আর একা থাকলেই মা কথা বলত। বিড়বিড় করে। কী কথা বলত কেউ বুঝত না। তার এই একাকী বিড়বিড় করে কথা বলা নিয়ে বাড়ির কেউ কথা ওঠালে মা স্বীকারই করত না যে, সে একা একা কথা বলে। পরে এ-নিয়ে কেউ আর কথা তুলত না। বুড়ো মানুষ, যা খুশি করুক; যা খুশি বলুক। কিন্তু একদিন মা আমার কাছে ধরা পড়ে স্বীকার করল – বাবার সঙ্গে কথা বলে…।
সেদিন আমি অবেলায় বাড়ি ফিরেছি। পৌনে একটার মতো বাজে। আমি সাধারণত দুটোর পরে বাড়িতে আসি। মা যথারীতি খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বারান্দায় বসে আছে। একাকী। ধারেকাছে কোথাও মিম-মিতু কেউ নেই। মিম মিতুর বড় বোন। মিম-মিতুর মাকেও দেখছি না। মায়ের এই দুই শিশু পুতি বাড়িতে থাকলে বাড়ি বাজারের মতো গমগম করে। দুই বোনের চিৎকার-চেঁচামেচিতে তিষ্টানো দায় হয়ে ওঠে। তখন নিঝুম বাড়ি। মা যেন কার সঙ্গে কথা বলছে, আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি…।
হঠাৎ আমাকে দেখে মা একটু চমকে উঠল। বলল – সুমিত তুই…!
– হ্যাঁ। অফিসে কাজ কম ছিল। বাড়িতে লেখালেখির কাজ আছে। তাই চলে এলাম। তুমি কার সাথে কথা বলছিলে মা? কাউকে তো এখানে দেখছি না…।
মায়ের চোখেমুখে কুসুমফুলের মতো হাসি ফুটে উঠল। লজ্জাও যেন একটু পেল। লজ্জার সঙ্গে হাসি মিশিয়ে মা বলল – তর বাবার সঙ্গে…।
– বাবার সঙ্গে! বলো কী? বাবাকে পেলে কোথায়…?
– তর বাবা একা একা হাঁপাইয়া উঠছে। এতোদিনেও বাড়িঘর গোছাইয়া উঠবার পারে নাই। মাঝেমধ্যেই আমারে নিবার আহে…।
বাবা মাকে নিতে আসে, এ যে ওপারবাড়ির ডাক; যে-কোনোদিন মা চলে যাবে – এই প্রতীতি নিয়ে আমি মনে মনে মায়ের চলে যাওয়ার মুহূর্তটি দেখার প্রস্ত্ততি নিচ্ছিলাম। মানুষ যখন ওপারবাড়ি চলে যায় তখন তার চোখ-মুখ কী বলে, কী পরিবর্তন ঘটে মানুষের চেহারায় – এটা দেখার ইচ্ছা আমার বহুদিনের। বাবা গাবাক্ষেতে ধানের চারা লাগাতে লাগাতে চলে গেল, খবর পেয়ে ক্ষেতে গিয়ে দেখি সে ওপারবাড়ি চলে গেছে, তার চলে যাওয়া দেখতে পারিনি। মায়ের চলে যাওয়াও দেখতে পেলাম না…।
যে-কোনোদিন মা চলে যাবে, জানতাম; কিন্তু কবে যাবে তা জানতাম না। কেউই কোনো মানুষের ওপারবাড়ি চলে যাওয়ার দিনক্ষণ, এমনকি যে যাবে, সেও জানে না। মায়ের চলে যাওয়ার দিনক্ষণ জানা থাকলে আমি সেদিন, অফিসে যত কাজই থাকুক, আমি বাড়িতে থাকতাম। মায়ের মৃত্যুশয্যায় তার মাথার কাছে বসে থাকতাম। তার চলে যাওয়ার মুহূর্তটি গেঁথে রাখতাম আমার করোটিতে…।
মা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি মা-বাবার কনিষ্ঠ সন্তান। তখন বয়স পঁয়তাল্লিশ, কিন্তু মায়ের কাছে আমি অবোধ ছেলে! আমি বাড়ি ফিরলে, শেষবারের মতো আমাকে একনজর দেখে তবেই মা বিদায় নেবে। কিন্তু আগের রাতে আমি বাড়িতে ফিরিনি। মাঝেমধ্যে এরকমটা করি। বাড়ির কাউকে কিছু না-বলে, জানি আমার চিন্তায় মায়ের চোখের ঘুম নষ্ট হবে, দু-তিনদিন বাড়িতে ফিরি না। মাঝেমধ্যে এরকম নিখোঁজ থাকতে আমার ভালো লাগে। যাই হোক, বাড়িতে ফিরেছি পরদিন দুপুরে। মায়ের হাতে আর একদম সময় ছিল না; ওপারবাড়ির যাত্রা শুরু করেছে। আমি ফিরে দেখি মা পুলসেরাতের পুলের গোড়ায় পা রেখেছে, এখনই পুলে উঠবে…।
ওপারবাড়ি চলে যাচ্ছে মা, আমার ভাইবোনরা একটু দূরে সজল-চোখে দাঁড়িয়ে আছে। এতোক্ষণ বুঝি ওরা সবাই বুক চাপড়ে কাঁদছিল। তখন কাঁদছে নিঃশব্দে। কারো বিদায়বেলায় নাকি চিৎকার করে কাঁদতে নেই। কিন্তু আমাকে দেখে কুশিবুজি হাউমাউ করে কান্না শুরু করল। আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে-কাঁদতেই বলল – তুই মানুষ, নাকি জানোয়ার! রাতে বাড়ি ফিরলি না। সকালেও তো আসতে পারতি। মা কত বলল তোর কথা…।
মা পুলে উঠল। আমরা মেঘভাঙা-চোখে তাকে বিদায় দিলাম। পুলের নিচে আগুন-উত্তাল নদী। এই নদীতে সবসময় মানুষসমান ঢেউ থাকে; কিন্তু সেদিন নিস্তরঙ্গ। ঢেউ নেই…।
বাড়িতে পা দিতেই কানে এসেছিল, কে যেন বলল – কী ভাগ্যবতী ছিল সুমিতের মা। আশুরার দিন গেল। জান্নাতবাসী হবে। মা পুণ্যবতী, জান্নাতবাসী হবে – হয়তো এজন্যই সেদিন আগুননদীতে ঢেউ ছিল না…।
মা হেঁটে যাচ্ছে। আমরা মায়ের চলে-যাওয়া দেখছি। হঠাৎ আমার কানে এলো, মা বলছে – ‘তোমরা সবাই বাড়িতে চইলা যাও। আর কান্দাকাটি কইরো না। আমি যাই। ওই পারে তোমার বাবা আমার জন্য অপেক্ষা করতাছে। বাগুনটালে ঠিকমতো পানি দিও। হাঁস-মুরগিগুলা দেইখা রাইখো – হিয়ালের প্যাটে না যায়। বাড়িতে ফকির-মিসকিন আইলে তারে খাইলা হাতে ফিরাইয়া দিও না…।’
পুলসেরাতের পুল নাকি এক কোটি কিলোমিটার দীর্ঘ, ওয়াজ মাহফিলে কোনো কোনো হুজুর বয়ান করেন। এতো বড় একটা পুল – দেখলাম, মা পার হয়ে গেল, সিকি সেকেন্ড সময়ও লাগল না…।
আমি প্রত্যেক জোছনারাতে মায়ের ডাক পেয়ে ওপারবাড়ি বকুলতলায় গিয়ে বসি। মা আমার কাছে আসে। আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমার শৈশবে যেভাবে কপালে-কপালে চুমু খেত, সেভাবেই চুমু খায়। যেন আমি এখনো তার সেই ছোট্ট সুমিত। আদর শেষে প্রত্যেকবারই মা উষ্মা প্রকাশের মধ্য দিয়ে কথা শুরু করে – ‘সুমিত, তুই কি এহনো দুপুররাইতে বাড়িতে ফিরস? মদ খাস? তর চিন্তায় স্বর্গেও আমার শাস্তি নাই…।’
আমি জানি, মা এটা বলবেই। প্রত্যেকবারই বলে। আমি কোনো কথা বলি না। সুবোধ বালকের মতো মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। মা তখন গল্প শুরু করে। ওপারবাড়ির গল্প, যেন রূপকথা; যা ছোটবেলা মা-দাদির মুখে শুনেছি…।
মা যখন আমাদের বাড়িতে ছিল, সুনন্দপুরে; আমার শৈশব-কৈশোর কিংবা যৌবনে, কোনোদিন তাকে শাস্তি-স্বস্তি দিইনি। মা যা বলত, আমি সবসময়ই তার উলটোটা করতাম। আমাকে নিয়ে মায়ের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। সকাল নেই, দুপুর নেই, সেই শৈশব-কৈশোরে, গাঁয়ের হারু সেনের পোড়োবাড়িতে গাবগাছে উঠে গাব পারতাম, চালতাগাছে উঠে চালতা পারতাম। কবে যে আমি গাছ থেকে পড়ে মারা যাব – এই চিন্তায় মা অস্থির থাকত, উদ্বিগ্ন থাকত…।
একদিন চালতাগাছ থেকে পড়ে মরতে মরতে বেঁচে গেছিলাম…।
নদী-ঘেঁষেই হারু সেনের পোড়োবাড়ি। আমার জন্মের দুবছর আগে, সেটা ছিল ১৯৬৫ সাল; পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ লেগেছিল, হারু সেন নাকি তখন একরাতে বাড়িঘর ফেলে পরিবার-পরিজন নিয়ে কলকাতা চলে যায়; আর কোনোদিন ফিরে আসেনি। বাড়িটি এখন ভূত-প্রেত, সাপ-বেজি, শেয়াল-খেঁকশিয়ালের আড্ডাখানা। ওই পোড়োবাড়িতে, নদী-ঘেঁষে বিশাল বড় বড় তিনটি চালতাগাছ। সব গাছেই বর্ষাকালে প্রচুর চালতা ধরে। একদিন আমি, আবিদ, কাদের, শহীদ; আমরা তখন সিক্সে পড়ি; চালতা পাড়তে গেছি। আমিই গাছে উঠেছি। ওরা নদীতে নেমেছে। আমি চালতা পেড়ে পানিতে ছেড়ে দিই, ওরা সাঁতার কেটে চালতা ধরে। চালতা কিন্তু আমি ডাঙায়ও ফেলতে পারতাম। তা না-করে পানিতে ফেলছি। ওরা সাঁতার কেটে স্রোতের টানে ছুটন্ত চালতা ধরছে। এটাও আমাদের একটা খেলা। যাহোক, গোটাবারো, প্রত্যেকের জন্য তিনটি করে চালতা পেড়ে আমি গাছ থেকে নদীতে লাফ দিই। লাফ দিছি তো দিছি, পানির নিচে তলিয়ে গেছি; আবিদরা ভেবেছে – আমি একটু ভাটিতে গিয়ে শুশুকের মতো ভুস করে ভেসে উঠব। কিন্তু আমার ভেসে ওঠার নাম নেই। উঠছি না যে উঠছিই না। আমার বন্ধুরা তখন হাহাকার করে ওঠে। সুমিতের কী হলো? ও কোথায় গেল? ভেসে উঠছে না কেন…?
শহীদ দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়েছিল। বাবা বাড়িতে ছিল না। দাদা চিতাবাঘের মতো দ্রুত ছুটে আসে। মা-দাদি সবাই আসে। বুক চাপড়ে কাঁদে মা। দাদি কাঁদতে কাঁদতে খোয়াজখিজিরের দরবারে শিন্নি মানত করে। প্রতিবেশীরাও অনেকে ছুটে আসে। নদীর ভাটিতে দুই পারে ঝাঁকিজাল ফেলে কেউ কেউ। যদি জালে উঠে আসে ম-লবাড়ির ছোট নাতি! অবাক কা-! গাছ থেকে নদীতে লাফিয়ে পড়ে কোথায় হারিয়ে গেল ছেলেটা…!
নদীর দুই পারে, হারু সেনের পোড়োবাড়ির উজানে-ভাটিতে তখন কান্নার রোল; মণ্ডলের নাতিটা নদীতে লাফিয়ে পড়ে, গাঁয়ের কত ছেলে-ছোকরাই তো গাছ থেকে, নৌকা থেকে, সাঁকো থেকে নদীতে লাফিয়ে পড়ে; মুহূর্তের মধ্যেই গায়েব হয়ে গেল, কারো জালেই উঠল না ছেলেটার লাশ; পানির পির খোয়াজখিজির কেন এতোটা রুষ্ট হলো এই কিশোর-বালকের ওপর; ম-ল নিজে, নাকি সুমিতের মা-বাবা কোনোভাবে না-বুঝে পানির পিরের সঙ্গে বেয়াদবি করেছে, তার খেসারত হিসেবে দিতে হচ্ছে অবুঝ শিশুর প্রাণ; এসব কলরব যখন নদীর ঘাটে ঘাটে, আমি তখন মৃত মাছের মতো, পোড়োবাড়ির বেশ কিছুটা ভাটিতে ভেসে উঠলাম। দাদার চোখেই প্রথম পড়ি। দাদা লাফিয়ে নদীতে নেমে আমাকে ডাঙায় তোলে…।
আমি বর্ষাকালে মাঝেমধ্যেই, কখনো একা, কখনো বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়ির ঘাটে সাঁকো থেকে কিংবা হারু সেনের চালতাগাছ থেকে নদীতে লাফিয়ে পড়তাম। নদীর তলদেশের মাটি ছুঁয়ে কিংবা একমুঠো মাটি হাতে ভেসে উঠতাম পানির ওপর। কিন্তু সেদিন উঠতে পারছিলাম না। আমি পানির ওপর ভেসে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা করি; কিন্তু উঠতে পারি না। কে যেন আমার পা টেনে ধরে। নদীতে চুলপেঁচানি থাকে, শুনেছিলাম দাদির মুখে। তারা নাকি পছন্দের শিশুদের ধরে ধরে খায়। আমি এসব বিশ্বাস করতাম না। মনে করতাম – আমি সকাল নেই, দুপুর নেই – নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ি, দাদি আমাকে ভয় দেখানোর জন্য চুলপেঁচানির কথা বলত। কিন্তু সেদিন, সেই চুলপেঁচানিই আমার পা টেনে ধরেছিল কিনা জানি না…।
মায়ের বড় প্রত্যাশা ছিল – আমি লেখাপড়া শিখে বিদ্বান হই, যেন বাবার মতো চাষা না হই; কিন্তু আমি মায়ের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারিনি। চাষাই হয়েছি। বাবা খেতখলায় ধান-পাট চাষ করত। আমি গল্প-কবিতার চাষ করি। সেই কৈশোরেই আমি গল্প-কবিতার চাষবাস শুরু করেছি। তখনই আমার মাথায় চেপে বসেছিলেন মীর মশাররফ হোসেন। আমি বিষাদসিন্ধু লিখব। আমার পাগলামি দেখে মায়ের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। ছেলে তার বখে গেল। কিন্তু আমাকে কিছু বলেও তো লাভ নেই। মা যা বলে আমি করি তার উলটোটা…।
পরে বুঝেছি বিষাদসিন্ধু আর কারো হাতে নতুন করে সৃজিত হবে না। এটি মীর মশাররফ হোসেনের নিজস্ব সৃষ্টি – তাঁরই ঔরসজাত সন্তান। আমাকে লিখতে হবে – আগুনঘেরা নদী, অন্ধকারে বৃষ্টির গান, জাদুর আয়না, তৌরাতের সাপ, গণিকাপ্রণাম। আমি সেইমতো খেতখলায় আমার ঔরসের বীজ বপন শুরু করি…।
১৯৮৮। আমি তখন একুশের সুমিত। দৈনিক মফস্বলে কাজ শুরু করেছি। পত্র-পত্রিকায় আমার গল্প-কবিতা ছাপা হয়। পানবাড়ির বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। ‘মদ্যপান না-করলে কারো করোটির ভেতর কবিতা সৃজিত হয় না’ – বলেন কবি রফিক আজাদ। তাঁকে গুরু মেনে বানুটি খেয়ে মধ্যরাতে বাড়িতে ফিরি। মা কিছু বলে না। রাগে, না অভিমানে, জানি না। জানার চেষ্টাও করি না। আমি একটা কুলাঙ্গার…!
একদিন মধ্যরাতে বাড়িতে ফিরেছি। পূর্ণিমা রাত। বরফসাদা জোছনা গলে গলে পড়ছে ঘরের চালে, গাছের ডালে, কুমুরের জাংলায়। বাড়িতে ঢোকার মুখেই সজনেগাছ। সজনেফুলের ওপর জোছনা লাফালাফি করছে ঘুঙুর-পায়ে বালিকার মতো। আমি মুগ্ধচোখে দেখছিলাম। আমার করোটির ভেতর সৃজিত হচ্ছিল কবিতার পঙ্ক্তি – ‘জোছনা পান করে যুবতী হয়ে উঠছে সজনেফুল…।’ হঠাৎ চোখে পড়ল – বারান্দার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে মা। জোছনাপস্নাবিত বাড়ি। দূর থেকেই দেখলাম – মায়ের চোখে পানি। মা কাঁদছে…।
– মা তুমি এতো রাত পর্যন্ত বারান্দায় বসে আছ? কাঁদছ যে…?
মহাভারতের সত্যবতীর মতো ধ্যানমগ্ন ছিল মা। আমার কথা শুনে ধ্যান ভাঙল। কাপড়ের আঁচলে তড়িঘড়ি চোখ মুছে মা বলল – ‘কই কানতাছি। চোখে কি একটা কুটা পড়ছিল। তাই পানি আইছে…।’
– কিন্তু ঘুমাওনি কেন…?
– বাবা রে, তুই বাড়িতে না আইলে যে আমার ঘুম ধরে না…।
মায়ের কথা শুনে আমার চোখ ফেটে পানি আসে। আমি মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকি। মা আমার চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বলল – ‘সুমিত, আমি তর সবকিছু মাইনা নিছি বাবা। তুই কবিতা ল্যাখ, গল্প-উপন্যাস ল্যাখ, মদ খা – আমার কোনো কথা নাই। তুই শুধু আমার একটা কথা রাখ…।’
– কী কথা মা…?
– তুই আমার ঘরে একটা টুকটুকে বউ আইনা দে…।
– বউ…!
– খালি বাড়িতে একা একা আমার দম বন্ধ অইয়া আহে…।
আমি মা-বাবার কুলাঙ্গার ছেলে। মায়ের কোনো স্বপ্ন-সাধ পূরণ করতে পারিনি – তারপরও আমি বাড়ি না-ফেরা পর্যন্ত মা আমার অপেক্ষায় বসে থাকত। বাড়ি, বাড়ির সব গাছপালা, ঝিঁঝি পোকারা – সবাই ঘুমিয়ে পড়ত, মা আমার ঘুমুতে যেত না। মা যেদিন ওপারবাড়ি চলে গেল, তার আগের রাতেও আমার পথ চেয়ে বসে ছিল মা…।
ওপারবাড়ির রূপকথা শুনতে আমার খুবই ভালো লাগে। বকুলতলায় বসে মায়ের মুখে রূপকথা শোনার সময় আমি যেন ছোট্ট শিশুটি হয়ে যাই। অবাক-চোখে মাকে প্রশ্ন করি – হুর কী পুরুষ, না নারী? দেখতে কেমন? বইয়ের ছবিতে দেখা পরীর মতো কি…?
অনেকদিন ধরে মায়ের ডাক পাচ্ছি না। আকাশে চাঁদ ওঠে, পূর্ণিমা আসে, পূর্ণিমা চলে যায়। গাঁয়ে জোছনার বানও ডাকে; কিন্তু মায়ের ডাক আসে না। কী হলো মায়ের? কোনো অসুখ-বিসুখ! যদ্দূর জানি, স্বর্গে কারো অসুখ-বিসুখ করে না। তা হলে? অনেকদিন মাকে না-দেখে মায়ের মুখে গল্প শুনতে না-পেরে আমি অস্থির হয়ে উঠি। নিজেকে কেমন পাগল-পাগল ঠেকে। কোনো কোনোদিন দিনের বেলা গোরস্তানে যাই। মায়ের কবরের শিয়রে, বকুলতলায় দাঁড়াই। নিঃশব্দে, সজল-চোখে দাঁড়িয়ে থাকি। বকুলপাতা ঝরে পড়ে আমার মাথার ওপর। মায়ের ডাক শুনি না। ওপারবাড়ির কোনো বাসিন্দা যে এরকম দিনের বেলা কাউকে ডাকে না কিংবা কারো ডাকে সাড়াও দেয় না তা জেনেও আমি বকুলতলায় দাঁড়িয়ে থাকি, হঠাৎ যদি মায়ের ডাক শুনতে পাই…!
কোনো জোছনাগ্রস্ত রাতে মায়ের ডাক আর পাইনি। একদিন মায়ের চিঠি পেলাম। বিশুদ্ধ চলতি ভাষায় লেখা। কবিতার মতো মেদহীন চিঠি। মা লিখেছে – ‘সুমিত বাবা, একা একা পৃথিবীতে কেমন আছিস তুই? এখনো কি মদ খেয়ে মধ্যরাতে বাড়িতে ফিরিস? সাপ-খোপের ভয় নেই তোর – ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করিস না, কী যে মানুষ তুই…!
কত করে বললাম – বে-থা করে সংসার কর। আমার কথা শুনলি না। তোকে একা রেখে এসে স্বর্গেও সুখ নেই আমার…।
তুই তো বইয়ের পোকা; বইপুস্তক নিয়েই থাকিস সারাদিন। নিজের লেখা বইগুলোকেই পুত্র-কন্যাজ্ঞান করিস। এবার বইমেলায় তোর কী বই বেরোবে? গল্প না কবিতার বই? বেঁচে থাক বাবা, তোর মতো করেই বেঁচে থাক…।
সুমিত, তুই কি আমাদের খেতখলা চিনিস? এখন একটু ওদিকে মন দে। মাটিকে মায়ের মতোই ভালোবাসতে হয়…।
তোর বাবা আমাকে পেয়ে খুব খুশি হয়েছে। দুজনে মিলে সংসার গুছিয়ে ফেলেছি। গাবাক্ষেতে ধানের চারা বুনতে বুনতে যেরকমটা চলে এসেছিল, এখনো ঠিক তেমনটাই আছে। স্বর্গে মানুষের বয়স বাড়ে না…।
সুমিত, শসা খেতে তুই খুব ভালোবাসিস। ভালোবাসিস সবজি-খিচুড়ি আর মদ। স্বর্গে প্রচুর শসার চাষ হয়; আর এখানকার মদ খুবই উৎকৃষ্টমানের। আমার খুব ইচ্ছা করে – তোর জন্য স্বর্গের শসা আর মদ পাঠাই; কিন্তু সে-সুযোগ নেই যে বাবা। সীমান্তে কড়া পাহারা…।’
মা যেদিন ওপারবাড়ি চলে গেল তার মরদেহটা রেখে, সেই মড়া দেখে আমি কাঁদিনি। কাঁদতে পারিনি। চোখে পানি ছিল না। মায়ের চিঠি পড়ে সদ্য-মাতৃহারা বালকের মতো হাউমাউ করে কাঁদলাম। মা, মাগো…!
কাঁদতে কাঁদতেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে কবরের মতো ঘন অন্ধকার…।