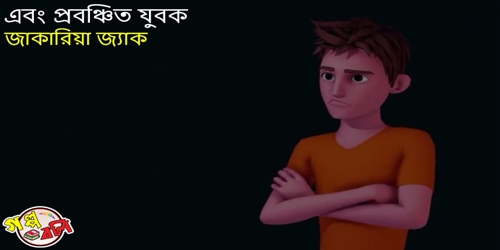এক জীবনে একটা মানুষ বুকের ভেতর কয়টা কবর ধরে? এই কথা আজকাল সারাদিনই একা-একা ভাবেন রইসউদ্দী। এই পঁচাশি কি ছিয়াশি কি নব্বই বছরের জীবনে এই পর্যন্ত ১৭ জন নিকট মানুষকে নিজের হাতে গোর দিয়েছেন তিনি। কবর জমতে জমতে বুকের ভেতর তার এখন একটা আস্ত গোরস্তান। পারিবারিক বিরাট কবরস্থ্থানে আছে পরিবার-পরিজনের ২৮টা কবর। আর রইসউদ্দীর বুকের ভেতরেও তো কবরের সংখ্যা কম না। নিকট ১৭ জনের বিদায়ের সাথে আছে সম্পর্কের ভাঙন। গভীর ভাঙনও তো মৃত্যুই। কবরই। সব মিলিয়ে তার ‘না হইলেও তো নব্বই বচ্ছর বয়স-এর এই জীবনে বুকের ভেতর গড়ে ওঠা কবরস্থানের ভার আর বইতে পারছেন না তিনি।
আর কোনো কবর ধারণের জায়গা তার বুকের মধ্যে নেই। এখন তার সকাল-বিকাল প্রার্থনা- নিজের মৃত্যু। পরশু রাতে তিনি সালাতুল হাজতের নামাজ পরে আল্লাহর কাছে কেঁদেকেটে নিজের মৃত্যু চেয়েছেন। বলেছেন, ‘হে খোদা! তুমি আমারে নেও। গোরে নামাও।’
রইসউদ্দীর মনটা আজ কয়েক দিন হলো খুব ভার। খুবই। ছোটো নাতির ঘরের পুতিটা হঠাৎ জ্বরে পড়ল। আর কিছু না। কিচ্ছু না। শুধু জ্বর। তিন দিনের জ্বর। কোনো অসুখ না, বিসুখ না। খালি জ্বর। জ্বরেই মেয়েটা মারা গেল। এই মেয়েটাই গত সাড়ে চারটা বছর ধরে ছিল রইসুদ্দীর প্রাণভোমরা।
একটু একটু করে যখন মেয়েটা ডাক শিখে, তখন সে অস্পষ্ট উচ্চারণে ডাকত- ‘বয়ো বাবা’। ‘বয়ো বাবা, বয়ো বাবা’ ডাকতে ডাকতে সে টলমল টলমল করে হাঁটত। তারপর দৌড় শিখল, ছড়া শিখল। কথার উচ্চারণও স্পষ্ট হলো- ‘বড় বাবা! বড় বাবা!’ বলে এসে বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। ছড়া শোনাত-
‘আতা গাচে তোতা পাকি, দালিম গাচে মউ,/ এতো দাকি তবু কতা কউ না কেন বউ।’
গত বছর দু’য়েক ধরে রইসুদ্দী নামাজের জন্য দুপুরে বা বিকেলে মসজিদে যাওয়ার সময় পিছু পছু সেও আসত। আঙুলে ধরে হাঁটতে হাঁটতে হাজার রকমের কথা বলতে বলতে মেয়েটা হাসত। খিলখিল হাসির শব্দে রইসুদ্দীর মনে হতো, দুপরের রোদের রঙ খুব উজ্জ্বল। বিকেলটা খুব মায়াবী। মনে হতো, বেঁচে থাকা সুন্দর। গল্প করতে করতে হেঁটে এসে রইসুদ্দী মসজিদে ঢুকে নামাজ পড়তেন। আর মেয়েটা মসজিদের পুকুরপাড়, পুকুরঘাটে খেলত, হাঁটত। মাঝে মাঝে মসজিদের ভেতরে ঢুকে সেও সিজদা দিতে দিতে ‘একা একাই বলত, বড় বাবা, আমিও নামাজ পড়ি।’
বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন রইসউদ্দী। কোমর বেঁকে গেছে। কুঁঁজো হয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটেন। কিন্তু এখনও ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন নিজের সীমানার শেষ মাথায় বছর পঁয়ত্রিশেক আগে বানানো মসজিদে গিয়ে। এখনও শরীরে কোনো বিশেষ রোগ-বালাই নেই। এখনও ঘাটে নেমে গোসল করেন। নিজের কাপড় নিচে কাচেন। এখনও চাষ-বাসের সময় মাঝে মাঝে বাড়ির সামনের ক্ষেতে গিয়ে কামলা-মুনিষদের নির্দেশনা দেন। এখনও হঠাৎ হঠাৎ লাঠিতে ভর করে দুই একবার পথে একটু বিশ্রাম নিয়ে আস্তে আস্তে চলে যান বন্দে। বন্দের মাঝখানে বড় ক্ষেতের ফসলটা কেমন হলো, সব ঠিকঠাক আছে কি-না, তা নিজেই দেখে আসেন।
বন্দের শেষ মাথার কিছুটা পর নদীর পাড়ে গিয়ে দুই-তিন মাস আগে বসে ছিলেন ঘণ্টাখানেক। এই নদী দিয়েই তার বিয়ের নৌকা গিয়েছিল। নৌকায় নওশা বেশে ছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিল ভাই-বেরাদর, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনসহ কত মানুষ! এই নদীর ঘাটেই ১০ বছর বয়সী নতুন বউ নিয়ে নেমেছিলেন জোয়ান রইসউদ্দী। ষাট কি পঁয়ষট্টি কি সত্তর বছর আগের সেই কথা। নদীও তখন রইসুদ্দীর মতো জোয়ান। কী পানি! কী সুন্দর! কী টলমল! এখন তো আর নদীই নেই।
এই নদীর দিকে তাকালেও নিজের বুকের ভেতর একটা কবর দেখতে পান রইসউদ্দী। কবরের নাম দুধলাইরচর নদী। খালি মানুষের মৃত্যু না, খুব প্রাণের কোনো বস্তুর ক্ষয়-লয়ও মৃত্যুই। সেই মৃত্যুও মানুষের মৃত্যুর মতোই কঠিন, যাতনাময়। এই নদীর মরণটাও তার বুকের ভেতর ভার হয়ে আছে। নদীর দুই পাশ শুকাতে শুকাতে, ভরাট হতে হতে, দখল করতে করতে নদী এখন কোনো কোনো জায়গায় ১০ কি ১৫ হাত আছে। সেসব জায়গায় বর্ষাতে একটু পানি জমলে নদীর মরণটা আরও স্পষ্ট বোঝা যায়। আর অন্য সময় তো শুকনা। চর। নানান ফসলের ক্ষেত। নদীর পাড়ে জায়গায় জায়গায় বসতি। বাজার-ঘাট, বাণিজ্য, ব্যস্ততা। এখন ‘নদীটা কানি আঙ্গুলের মতন চিক্কন হইয়া গেছে।’ ফিতার মতো খালি একটা চিকন রেখা ছাড়া নদীটার আর কিছু নেই। রেখাটার কোথাও কোথাও ডোবার মতো, জলার মতো খাবলা খাবলা একটুখানি পানি। এই নদীর পাড়ে এলেই রইসউদ্দীর বুকটা হু-হু করে ওঠে। ডুকরে ওঠে। বহু বছর ধরে কবরের পাশে যেতে যেতে একটা সময় যেমন কবরের পাশে গেলে আর চোখে পানি আসে না, কিন্তু বুকের ভেতর কেমন যেন একনাগাড়ে খালি ডাকতে থাকে ঘুঘু পাখি; তেমনি এখন লাগে রইসউদ্দীর এই নদীর পাড়ে এলে। নদীর পাড়ে ঘুঘু ডাকে বুকের ভেতর।
১৭ জন প্রিয় মানুষের কবরের সাথে, ভেঙে যাওয়া সম্পর্কগুলোর কবরের সাথে এই নদীর মৃত্যুটাও একটা মৃত্যু। একটা কবর। একটা ভার। ঘুঘুর ডাক। এই সব ভার আর তিনি বইতে চান না। এই সব ডাক তিনি আর শুনতে চান না। তাই, গত পরশু সালাতুল হাজতের নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করেছেন।
জীবনের প্রথম কবর তার বুকের ভেতর জমেছিল ৭ বছর বয়সী ছোটো ভাইটার মরণ দিয়ে। একটা কালসাপের কামড়ে সারা অঙ্গ তার নীল হয়ে গিয়েছিল। কবিরাজ-বৈদ্য কারও কাছে যাওয়ারই কোনো সুযোগ দেয়নি সেই ভাই। খেলার সময় জঙ্গলে ফুল তুলতে গিয়ে সেই যে সাপের কামড় খেয়ে মরল ভাই; সেই দিয়ে বুকের ভেতর ‘কব্বর’ জমা শুরু। তারপর একে একে দাদা, দাদী, মায়ের চেয়েও আপন বড় খালা, মা, চাচা, বাজান, শ্বশুর, শাশুড়ি, বড় চাচা, মেজো চাচা, বড় বোন, দুলাভাই, ছোটোবেলার দোস্ত আব্বাস- আরও কত কবর জমেছে!
তবে, আব্বাসের মরণটা এখনও তার চোখের সামনে ভাসে। হাটবারে হাট থেকে ফেরার সময় রেললাইন বরাবর তারা হেঁটে আসছিল। সেই সময় ‘আৎকা নামলো শাওইন্যা বৃষ্টি’। ঝুম বৃষ্টি। বৃষ্টির সাথে মুহুর্মুহু ‘ঠাডা’। বৃষ্টির মধ্যে রইসুদ্দীর খুব ‘পেশাব’ চাপল। সে পেশাব করতে বসল রেললাইনের একটু নিচে রাস্তার ঢালে। আর রেললাইনের উপরে দাঁড়িয়ে ভিজতে ভিজতে আব্বাস বলছিল, ‘রইসুদ্দী, লও কাইল মাছ মারতে যাই। নয়া পানির মাছ।’
রইসউদ্দী তখনও কোনো উত্তর না দিয়ে সে ‘পেশাব’ করে ওঠে প্রায়। এমন সময় পড়ল আরেকটা ‘ঠাডা’, বিকট শব্দে, একেবারে আব্বাসের মাথায়। জায়গায় দাঁড়িয়ে আব্বাস মুর্হূতে মূর্তির মতো হয়ে গেল। মুখটাও তার ছিল হাঁ করা। চোখের পাতাটাও ছিল খোলা।
আব্বাস কবে মরল! ‘কম তো নাহ। ষাইট কি সত্তর বছর তো অইবই। দেশ ভাগ হওনের কয়েক বছর পরেই তো ঘটল ঘটনা।’
তার পর সময় গেল। একে একে রইসউদ্দীর দুই মেয়ে গেল, তিন ছেলের মধ্যে এক ছেলে গেল, এক নাতি গেল। আরও কত নিকটজন, বন্ধুরা গেল! তাদের সকলকেই নিজের হাতে রইসউদ্দী দিয়েছেন বিদায়।
মানুষের মৃত্যুর বাইরে, দুধলাইরচর নদীর মৃত্যুর বাইরে যে কয়টা ঘটনা রইসউদ্দীর বুকের মধ্যে কবর হিসেবে জমেছে, সেগুলোর মধ্যে একটা হলো প্রিয় এক বন্ধুর সাথে তার ছাড়াছাড়ি। সেই ছাড়াছাড়ির কারণ সে মনেও আনতে চায় না। মুখে তো না-ই। তবে, মানুষ যে চোখ উল্টাতে পারে; সেই বন্ধুর ঘটনায় রইসুদ্দী তা প্রথম অনুধাবন করেন। মানুষ যে এমন চতুরতা করতে পারে, সেটা তখনই তিনি প্রথম টের পান। চতুরতা টের পেয়ে নিজেই ধীরে ধীরে সেই সম্পর্কের ইতি টানেন। কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে আবেগ যখন টইটম্বুর, অভিমানের যখন কোনো সীমা-পরিসীমা নেই, সেই ঘটনায় এমন ব্যথা তিনি পেয়েছিলেন যে, আজও বুকের মধ্যে ছিন্ন সম্পর্কের একটা কবর তিনি দেখেন।
আরও একটা ‘কব্বর’ তার আছে, খুব গোপন। সেই কবরের নাম গীতা। পাশের বাড়ির গীতাকে যখনই তিনি দেখতেন সেই কৈশোর শেষ হয়-হয় বয়সে, রইসউদ্দীর বুকের ভেতর কেমন যে করত! সেই ১৫ কি ১৬ বছর বয়সে তখন ক্ষণে মনে হতো, মনের ভেতর থেকে একশ’টা প্রজাপতি এক সাথে উড়ে গেল আসমানে। ক্ষণে মনে হতো, পেটের ভেতর একটা পাক দিয়ে সব কেমন খালি হয়ে গেছে! ক্ষণে মনে হতো, হাঁটুতে শক্তি নেই কোনো। আবার ক্ষণে মনে হতো, বুকের মধ্যে কীর্তনের ঢোলের মতো বাজছে। যেন তার শব্দে এখনই বন্ধ হবে নিঃশ্বাস। গীতাকে কোনোদিন কিছু বলা তো দূরের কথা, সামনা-সামনি হলে চোখ তুলে দেখতেও লজ্জা লাগত। কিন্তু সেই গীতারা ৪৭-এর দেশভাগের সময় ‘গেলো গা ইন্ডিয়ায়’। পাড়া-প্রতিবেশী কাউকে কিছু না জানিয়ে, এক রাতে গীতাদের পুরো পরিবার- বাবা, কাকা, দাদা, মেসো সবাই এক সাথে চলে গেল। তাদের গোয়ালভরা গরু গোয়ালে রইল। বাড়ির সামনে পুকুরে শান-বাঁধানো ঘাট রইল পড়ে। এমনকি গীতাদের বড় ঘরের বারান্দায় গীতার পোষা পাখির যে পিঞ্জিরাটা ছিল, সেটাও সেখানে ঝুলছিল। শুধু তার দরজাটা ছিল খোলা। যাওয়ার সময়, ময়নাটাকে নিশ্চয় সাথে নিয়ে যেতে পারেনি গীতা। ময়নাটা নিলে তো পিঞ্জিরাটাও নিত। নিশ্চয় ময়নাটাকে ছেড়ে দিয়েছিল গীতা বা তার মা।
গীতাদের এই হঠাৎ ‘নাই’ হয়ে যাওয়ার সংবদাটা পেয়ে তাদের বাড়িতে গিয়ে ভেঙে পড়ল সাত গাঁওয়ের মানুষ। সেই খবরে রইসুদ্দীও যান। গিয়ে দেখেন, সব ঘরের দুয়ার খোলা- হাট করে। খোলা দুয়ার দিয়ে যার ইচ্ছা যাচ্ছে, যার ইচ্ছা আসছে। কেউ বলার নেই, কেউ দেখার নেই। সকাল থেকে লোকেরা যারা আসছিল, তাদেরই মধ্য থেকে উৎসাহী কেউ কেউ হয়তো দরজার তালাগুলো ভেঙেছে। তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখেছে কী আছে, কী নেই। কিন্তু ময়নার খাঁচাটা ওইখানেই ছিল। ঝোলানো। কেউ ধরেনি, কেউ নেয়নি। পিঞ্জিরার খোলা দুয়ারটাও কেউ আটকে দেয়নি।
আর ‘গ গোল’-এর বছরটার কথা তো রইসউদ্দী মনেই করতে চান না। কী আজাবের দিন তখন গেছে! তিনি যুদ্ধে যাননি। কিন্তু মুক্তিদের জন্য কী তিনি করেননি! লুকিয়ে-চুরিয়ে খাওয়ানো, টাকা দেওয়া, আশ্রয় দেওয়া, খবর দেওয়া- কী তিনি করেননি! আর ‘মইত্যা রাজাকার তখন কী উৎপাতটাই না করল! দুই দিন পরে পরে সোলজার নিয়া আসার ডর দেখাইয়া সে সবাইরে লুঠছে! পাকবাহিনী নিয়া পুবপাড়ার হিন্দু পাড়াটাতে আগুন দিয়া তামা তামা কইরা দিল মইত্যা।’
রইসউদ্দীরা প্রাণ নিয়ে এই ক্ষেতে সেই ক্ষেতে, মাটির গর্তের ভেতর লুকিয়ে-চুরিয়ে থেকে দেখেছেন ২০ কি ২২ বছর বয়সী সেনাদের নিয়ে-নিয়ে সে হিন্দু বাড়ি-বাড়ি গেছে। মুক্তিদের বাড়ি-বাড়ি গেছে। হিন্দু বউ-ঝিদের টেনে-টেনে গাড়িতে তুলেছে। ‘কানাই কাকার মেয়েটারে যেদিন তুইল্যা নিলো, সেদিন তার কান্দনে একবার রামদা নিয়া ঝাঁপাইয়া পড়তে ইচ্ছা হইছিল’ রইসউদ্দীর।
রইসউদ্দীকেও তো কম শাসায়নি মইত্যা। ‘মুক্তিদের সাহায্য করলে ছাড়া নাই’ বলে কী দাবড়ানিটাই না সে মানুষকে দিল! পরে অবশ্য যুদ্ধের শেষে তাকে পাড়ার বড় শিমুল গাছের সাথে ‘বাইন্ধা খুঁচাইয়া খুঁচাইয়া মারছে মুক্তিরা’। এই মাত্র একটা মরণ, যা দেখে রইসউদ্দীর কষ্ট হয়নি, বরং শান্তি লেগেছে। তবু, একাত্তরের কথা মনে হলেই রইসউদ্দীর মনের মধ্যে খালি কবরই ভাসে। নদীর দক্ষিণের ঘাটে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে ‘নারায়ণ কাকা, নরেন কাকা, কানু, পরিমলসহ আরো কতজনকে মারলো!’ তারা কবরও পায়নি, চিতাও পায়নি। তারা ঘাটেই পচে-গলে স্বর্গে গেছে। কিন্তু একটু দূরের শ্মশানঘাটে তাদের লাশ কেউ নেওয়ার সাহস পায়নি।
এই ঘটনার পর গ্রামের মানুষ নদীর মাছ খায়নি দুই বছর। তাই একাত্তরের পুরো সময়টাই রইসউদ্দীর কাছে একটা কবর। একটা কবরে অনেক মানুষ, অনেক প্রিয়জন।
আরেকটা কবর, যা বুকের মধ্যে অষ্টক্ষণ ব্যথার মতো লাগে, তা হলো রইসউদ্দীর গিন্নির কবর। সেই কবে, ১০ বছর বয়সে পুতুলের মতো দেখতে সুন্দর আর ফড়িঙের মতো চটপটে একটা মেয়েকে বিয়ে করে বাড়িতে এনেছিল রইসুদ্দী! তখনও সে ঋতুবতীই হয়নি। তখনও সে সংসার বোঝে না। তখনও সে সুযোগ পেলে কাপড় কাছা দিয়ে উঠে যায় শ্বশুরবাড়ির বরই গাছে কি আমগাছে কি তেঁতুল গাছে।
সেই তারামুন্নেছা পরে কী শান্ত হলো! কী সংসারী হলো! সংসারে বিপুল জমাজমি, ঘর সামলে তো সে-ই রেখেছিল বুদ্ধি করে। সে না থাকলে রইসুদ্দীর কি এত কিছু হতো! হলেও থাকত না। সেই তারামুন্নেছা ৪৩ বছর সংসার করার পর একদিন চলে গেল। যাওয়ার আগে কিছু বলেও গেল না। প্রতিদিনের মতো সব কাজ শেষ করে সবকিছুর দেখভাল করে মেজো নাতিকে সাথে নিয়ে পালঙ্কে উঠল। মেজো নাতি রোজকার মতো থাকল মাঝখানে। তার দুই পাশে শুইল তারামুন্নেছা আর রইসউদ্দী। রোজ রাতের মতো গীত গাইল তারামুন্নেছা। নাতির অনুরোধে দুইবার করে গাইল নাতির প্রিয় ‘গাঙ্গে দিয়া ভাইস্যা যায় গো, নানান ফুলের কলি গো’ গীতটা। তার পর সকালে তারামুন্নেছা আর উঠল না। উঠলই না।
এই হাতে তারামুন্নেক রইসউদ্দী ‘কব্বরে শুয়াইছে’। এই হাতে তারামুন্নেছাকে তিনি রেখেছেন মাটির নিচে। আজ প্রায় ২০-২৫ বছর।
এত এত কবর তো আর সব খালি পারিবারিক গোরস্তানেই না। কবর জমে বুকের ভেতরেও। কিন্তু এক জীবনে একটা মানুষ বুকের ভেতর কয়টা কবর ধরতে পারে? সাড়ে চার বছরের মেয়েটা মারা যাবার পর থেকে কেবল এই কথাটাই ভাবছেন রইসউদ্দী।
একটা সময়ে প্রায় প্রতিদিনই তিনি কবরস্থানে যেতেন। ছোটো ভাই, বাবা-মা, বড় খালার কবর দেখতেন। কিন্তু তারামুন্নেছার মৃত্যুর পর থেকে কবরস্থানে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন রইসুদ্দী। বুকের ভেতর কবর জমতে জমতে তিনি নিজেই যখন একটা কবরস্থান, তখন কার কাছে আর তিনি যাবেন! রইসউদ্দী ভাবেন, ‘কব্বরস্থানে যায় জীবিত মানুষ। কব্বরের মাটি ছুঁইয়া জীবিতরা নিতে চায় প্রিয়জনের পরশ। কিন্তু একটা কব্বরস্থান আরেকটা কব্বরস্থানে গিয়া কী করবো!’
রইসুদ্দীর এখন নিজেকে মনে হয়, তার ভেতরটা একটা কবরস্থান। সেখানে সারি সারি শুয়ে আছে অনেক কবর। আর তার দেহটা কবরস্থানের সীমানা। সেই সীমানায় ‘পাক্কা ওয়াল তুলে দিয়ে দেওয়া আছে একটা লোহার গেইট। সেই গেইট খুইল্যা কেউ ভিতরে ঢুকলে দেখবো সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাটি।’ সেই মাটির নিচে প্রিয় সব মুখ। সেই মাটির নিচে দুধলাইরচর নদী। মাটির নিচে তারামুন্নেছা। মাটির নিচেই আছে সাড়ে চার বছরের বৈশাখী।
এক জীবনে একটা মানুষ বুকের মধ্যে কয়টা কবর ধরে- এ প্রশ্নের উত্তর রইসউদ্দীর কাছে নেই। কিন্তু বৈশাখীর মৃত্যুর পর থেকে এই দীর্ঘ আয়ুটাকে তার কাছে মনে হচ্ছে অভিশাপ। মনে হচ্ছে, বন্দি-জীবন। মনে হচ্ছে, শাস্তি। রইসউদ্দীর মনে হয়, আর কোনো কবর বুকের মধ্যে জায়গা দেওয়ার সামর্থ্য তার নেই। তাই, এইবার তিনি মুক্তি চান এই বন্দি জীবন থেকে। কিন্তু মুক্তির কোনো সহজ উপায় তো নেই। তিনি ভাবেন, ‘জেল ভাইঙ্গা বন্দি পলাইতে পারলেও, জীবন ভাইঙ্গা তো পলাইয়া যাওনের পথ নাই!’ তিনি ভাবেন, ‘জীবন ভাইঙ্গা গেলে তো পরপারেও আর কোনোদিন তারামুন্নেছার সাক্ষাৎ মিলবো না।’ তার বাবা-মা, ভাই-বোন, আব্বাসের দেখা মিলবে না। মিলবে না বৈশাখীর সাক্ষাৎও। কিন্তু আর তিনি বইতে পারছেন না এই দীর্ঘ-জীবনের ভার। বৈশাখীর মৃত্যুর পর তো না-ই। তাই নিজের মুক্তির জন্য সালাতুল হাজতের নামাজ পড়ে খোদার কাছে তিনি খুব কেঁদেছেন পরশু দিন। উপুড় হয়ে কাঁদতে কাঁদতে কখন যে নামাজের বিছানায়ই চোখ লেগে গিয়েছিল তার! সেই হাল্ক্কা ঘুম ভাঙল অদ্ভুত এক খোয়াব দেখে। খোয়াবে রইসুদ্দী দেখেন, নওশা বেশে তিনি বিয়ে করতে যাচ্ছেন। সাজানো-গোছানো নৌকা প্রস্তুত দুধলাইরচর নদীর ঘাটে। নদীটাও আগের মতো বড়; পানিতে টইটম্বুর। আর বিয়ের কনে সেজে সেই নৌকায় তার জন্য বসে আছেন ১০ বছর বয়সী তারামুন্নেছা।