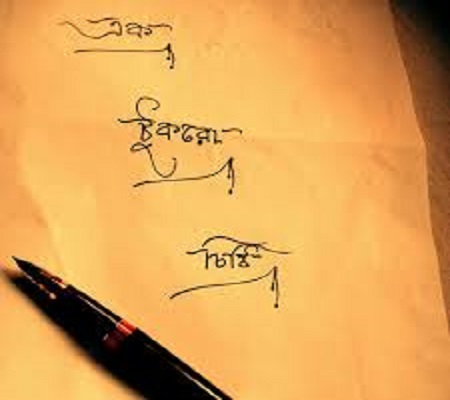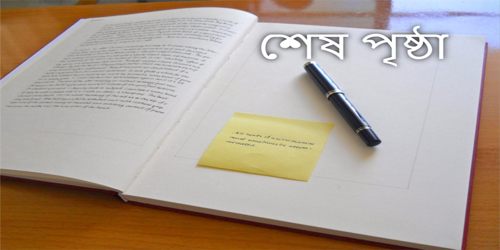আজ কণিকা আসবে। তার কথা জানার পর থেকেই একাত্তরে ডুবে আছি। ৪৬ বছর পর কণিকার সঙ্গে দেখা হবে। সময়টা যত লম্বাই হোক, একাত্তরে এক হয়ে ওঠা মানুষেরা কিছুতেই কেউ কাউকে ভুলতে পারে না। ভুলতে পারে না সে সময়ের সামান্য কোনো দিনের কথাও। সুপ্ত স্মৃতির পুকুরে ঢিল ছুড়ে দেখলাম একের ভেতর থেকে আরেক বৃত্ত তৈরি হচ্ছে। কণিকার বাংলাদেশে আসার খবর শোনার পর থেকে ক্রমশ সৃষ্টিশীল সেই বৃত্তগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি।
একাত্তরের দীর্ঘ বর্ষা শুরু হতেই যুদ্ধে যাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা মাথাচাড়া দিয়ে না উঠলে কণিকার সঙ্গে হয়তো আমার দেখা হতো না। যুদ্ধে আসলে আমাদের যেতে হয়নি, যুদ্ধে আমরা জড়িয়ে পড়েছিলাম। আমরা লড়ছিলাম, কারণ লড়া ছাড়া আমাদের সামনে অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। দেখলাম এদিক-ওদিকের বাড়ি থেকে ছেলেরা যুদ্ধে যাচ্ছে, যেন কোনো ইশারায় তাদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। যেন কোনো বাণী কোথাও বাজছে আর প্রত্যেকে তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছে; সবার দৃঢ়তা এক সুতোয় গিয়ে মিলছে। বঙ্গবন্ধু নারী-পুরুষনির্বিশেষে সবাইকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। অথচ আমার চোখের সামনে তখন যোদ্ধা মানেই কঠোর সংকল্পবদ্ধ পুরুষের মুখের সারি। ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে বলেছিলেন। তাঁর এই নির্দেশ যে একাত্তরের নারীরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল, তা আমার চেয়ে বেশি কে জানে! পাকিস্তানি আর্মির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের লুকিয়ে রাখতাম। নিজেরা না খেয়ে তাদের খাবারের জোগান দিতাম। তাদের অস্ত্র আর খবরাখবর গোপনে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চালান করতাম। আমাদের প্রায় প্রত্যেকের ঘর তখন সত্যিই একেকটা দুর্গ। অথচ তারই মধ্যে আমার কানে কেবল প্রীতিলতার কথা বাজত, ‘যদি আমাদের ভাইয়েরা মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে, আমরা ভগিনীরা কেন উহা পারিব না?’ অনেকে অনেক ভয় দেখাত, নিরুৎসাহিত করত। কিন্তু কী এক উন্মাদনা কিংবা গভীর আত্মত্যাগের আকুতি আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে ইতিহাসের কোনো একসময়ে আমরা, একাত্তরের মেয়েরা, হঠাৎ আবিষ্কৃত হইনি বা ব্যতিক্রমী কিছুও করিনি। কণিকা আমার সেই আকুতির সময়ের সাথি। তবে আমি নিশ্চিত, আজ সে কেবল আমাকে দেখার জন্য আসছে না। কণিকা আগেভাগে ইকবালের সঙ্গে যোগাযোগ করে তবে কলকাতা ছেড়েছে। আমি ঠিক জানি না এত দিন পরে সে ইকবালকে দেখতে চায় কেন।
যা হোক, একাত্তরের উত্তাল সময়ে বসে শুধু মেয়ে বলে যুদ্ধে যাব না, এটা মেনে নেওয়া আমার জন্য কঠিন ছিল। বাড়ির লোকেরা অবশ্য এটা দেখতেই অভ্যস্ত ছিল যে ছাত্র-জনতা দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমে আসবে, আর ওদিকে ঘর সামলাবে মেয়েরা। মনে মনে ঝালাই করে নিতাম, এই যে কদিন আগে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে এত বড় মিছিল হলো, তাতে কি অন্তত পাঁচ শ ছাত্রী ছিল না? তার দুই দিন বাদে ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে যে হরতাল ডাকা হলো, তাতে কি পুলিশ-বেষ্টনী ভেঙে দুটো মেয়ে কালো পতাকা হাতে এগিয়ে যায়নি? তারা বেষ্টনী ভেঙেছিল বলেই না সাধারণ মানুষ তাদের অনুসরণ করল। আর এই তো কদিন আগে, পয়লা মার্চ যখন ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেছিলেন, তখন আর সব পুরুষের মতো নারীর হৃদয়েও ‘স্বাধীনতা’ বান ডেকে দিয়েছিল, যা কি না তার আগ পর্যন্ত বুকের মধ্যে কেবল এক ফিসফিসানো শব্দের মতো বাজত, যেন বিরতিহীন ঝিঁঝির ডাক! আর সে কারণেই তো সাতই মার্চের ভাষণের ময়দানে অসংখ্য মেয়ে লাঠি হাতে উপস্থিত হলো। কারও হাতে ছিল তির-ধনুক। আমিও গিয়েছিলাম। মাথার ওপর বৃত্তাকারে ওড়া হেলিকপ্টারগুলোর দিকে লাঠি আর তির উঁচিয়ে কখনো চিৎকার করছিলাম আমরা। তখন কে না জানত, সেই যে ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে আমরা পরাজিত হয়েছিলাম, তারপর মাত্র তার আগের দিনটিতে নিজেদের শাসনে চলার সুযোগ পেয়েছি। আমাদের সামনে তাই তখন মৃত্যু যেন মৃত্যু নয়, সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত পরিণতি। জীবন-মৃত্যু-ভবিষ্যৎ সব ভুলিয়ে দিয়ে তার কদিন পরে বাড়ির ছাদে আমরা বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছিলাম। সবুজের মাঝখানে লাল বৃত্ত আর সেই বৃত্তে সোনালি বাংলাদেশ। ওড়ানোর আগে বাড়িতে থাকা আফসানের গুঁড়ো পুরু করে লাগিয়েছিলাম সেই সোনালি মানচিত্রে। পতাকার ঢেউয়ে বাতাসে আফসানের কণা ভাসছিল। উড়ে আসা আফসানের বিজলির মাঝখানে মুগ্ধ বিস্ময়ে আমি উড়ন্ত পতাকার দিকে তাকিয়ে ছিলাম।
কণিকা তখন আমার থেকে অনেক দূরে। যুদ্ধে যাওয়ার তাড়নায় নানান ফন্দি-ফিকির করে আমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম; সীমান্তের কাছে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাময়ের ছোট এক কেন্দ্র। অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার নেশা একসময় হার মেনেছিল আমার ভবিষ্যৎ পেশার কাছে। আমি তখন চিকিৎসক হওয়ার পথে। ভাবলাম যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসার চেয়ে শ্রেয়তর কাজ আর কী হতে পারে! কণিকা ছিল সেখানকার সবচেয়ে ত্বরিতকর্মা নার্স। সে এসেছিল কলকাতা থেকে। দেশের ভেতর থেকে আসা আরও ১৬ জন মেয়ে ছিল। কেউ পরিবার হারিয়ে, কেউ বাড়িঘর-আশ্রয় হারিয়ে বাতাসের দোলে পলকা শুকনো পাতার মতো ভাসতে ভাসতে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। প্রত্যেকের মুখের ওপর কোনো এক প্রতিজ্ঞা থমকে থাকত; সকাল-বিকেল সেই এক দৃপ্ত চাহনি। কিছু একটা ছিনিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়। কী করবে জানত না কিন্তু কিছু একটা করার নেশায় তারা উন্মত্ত হয়ে থাকত। সামান্য অস্ত্রচালনা শেখা হয়ে গেলে আমি তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দিতাম। চারদিকে উপযুক্ত রাস্তা নেই, কেবল চড়াই-উতরাই আর বর্ষার কাদা। বলতে গেলে কমই আহত মুক্তিযোদ্ধা সেখানে আসত। এলে আমরা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। তবে এটা জানতাম যে আমাদের কর্মক্ষমতা আরও অনেক বেশি। যদিও আমাদের হাতে আয়োজন ছিল সামান্য। প্রাথমিক চিকিৎসার বাইরে বড় কোনো চিকিৎসা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত বলতে গেলে কিছুই ছিল না। তাই মানসিক অস্থিরতা আর বিভ্রান্তির মধ্যে মাসখানেক কাটল। তারপর এক রাতে হঠাৎ আমাদের ধীরস্থির সময়ে অদ্ভুত এক ছোটাছুটি লেগে গেল। ২৫-৩০ জন মুক্তিযোদ্ধার দলের একটা ট্রাক অপারেশনে যাওয়ার পথে মধ্যরাতে আমাদের কেন্দ্রের কাছে এসে উল্টে আগুনে পুড়তে থাকল। একচোট গোলাগুলির শব্দের পর অন্ধকারে জঙ্গল থেকে আর্তনাদ ভেসে এল। নিজেদের হাতের গ্রেনেড, টোটাভর্তি বন্দুক, মর্টার—এসব ফুটে গিয়ে তারা কেউ কেউ ভয়ানক আহত হয়েছিল। আমরা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চিৎকার অনুসরণ করে ছুটতে লাগলাম। কাকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি, নিজেরাই মারা পড়ব কি না, এই জাতীয় কোনো চিন্তা আমাদের মাথায় আসেনি। বুকের ভেতর থেকে কেউ যেন বলে দিয়েছিল, আমাদের যেতে হবে। তাই ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে আমাদের অন্তত ৪০ জোড়া পা ধুপধাপ শব্দে ছুটে চলছিল। ছোট ছোট আগুনের উৎস চোখে পড়ল একসময়। আমরা পৌঁছতে পৌঁছতে ঝিরঝিরি বৃষ্টিতে নিভেও গেল। পড়ে থাকল মাটিতে গলা কাটা পাঁঠার মতো কাতরানো কিছু মানুষ, ছুঁতেই কারও কারও শরীরে বুলেটের মালার স্পর্শ লাগল। চ্যাংদোলা করে একের পর একজনকে কেন্দ্রে আনা হলো। কারও আঙুল, কারও হাত, কারও পা উড়ে গেছে। সামান্য চামড়ার যোগাযোগে হাতের কবজি ঝুলছে কারও। তাদের মধ্যে ছয়জনের অবস্থা মারাত্মক। আমাদের কাছে এত মানুষকে সারিয়ে তোলার মতো যথেষ্ট রক্ত আর সরঞ্জাম ছিল না। একটাই অ্যাম্বুলেন্স ছিল যার ছাদে বড়জোর দুটো স্যালাইন ঝোলানো যায়। তাই আহত ব্যক্তিদের যে সীমান্ত পেরিয়ে বড় হাসপাতালে নিয়ে যাব, সে সাহস করাও রীতিমতো হঠকারিতা। কিন্তু মানুষগুলো চোখের সামনে কাতরাতে কাতরাতে মরে যাবে, এটাই বা কী করে মানা যায়? আমাদের চোখের সামনে নার্স কণিকা যেন তখন অতিমানব হয়ে উঠল। তার শরীরে অসুরের শক্তি ভর করল। অনেকে সাহায্য করলেও বলতে গেলে একাই সে একে একে ছয়জনকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলল। ব্যান্ডেজ বাঁধা হলেও তাঁদের কারও রক্ত পড়া পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। পৃথক শরীর থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়া রক্তের ধারা গাড়ির মেঝেতে চুইয়ে এক হয়ে থমকে থাকল। রক্তের মাঝখানে কণিকা সটান দাঁড়িয়ে দুদিকে হাত বিস্তৃত করল। তার গলা, ঘাড় আর হাতে ঝোলানো হলো ছয়টি স্যালাইনের প্যাকেট। সিটে বসা মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে ততক্ষণে আহাজারির বদলে শত বছরের স্তব্ধতা আসন গেড়েছে। একজনের চোখ গলে গিয়েছিল। সে হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে বলল, ‘আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?’
‘হাসপাতালে’, কণিকা জবাব দিল।
‘কিন্তু আমরা যে একটা মিশনে যাচ্ছিলাম!’ মুক্তিযোদ্ধা হাহাকার করে উঠল।
‘আগে চোখটা তো ঠিক করে নিন’, কণিকা গম্ভীর স্বরে বলল।
‘আমার চোখ লাগবে না। আমাকে দয়া করে ফ্রন্টে পৌঁছে দিন, আমি ঠিকই যুদ্ধ করতে পারব’, যোদ্ধা ছেলেটি মিনতি করতে লাগল। যার হাত কি আঙুল নেই, যে এমনকি পা হারিয়েছে, কেউবা ঝলসে যাওয়া মুখের গভীর থেকে একই সুরে আওয়াজ তুলল, ‘আমাদের ফ্রন্টে পৌঁছে দিন। দয়া করে পৌঁছে দিন।’ কণিকা না শোনার ভান করে নিষ্প্রাণ খুঁটির মতো অ্যাম্বুলেন্সের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকল। কী কারণে জানি না, তার চোখ স্থির হয়ে ছিল হাঁটুর নিচ থেকে পা হারানো একজন মুক্তিযোদ্ধার দিকে। আর মুক্তিযোদ্ধার চোখও কণিকার দিকে। তাদের মধ্যে শব্দবিহীন, অভিব্যক্তিহীন অদ্ভুত এক যোগাযোগ হচ্ছিল। যেন একে অন্যের ভেতরে প্রবেশের সদর দরজা হয়ে উঠেছিল ওই দুই জোড়া চোখ। প্রায় রাস্তা ছাড়াই এবড়োখেবড়ো ভূমির ওপর প্রবল বেগে অ্যাম্বুলেন্স ছুটে চলছিল। জানি না, ওই ঝাঁকির মধ্যে কোন শক্তি কণিকাকে ছয়টি স্যালাইনের প্যাকেট সোজা করে ঝুলিয়ে রাখার ক্ষমতা দিয়েছিল। কখনো সে অস্থির হয়ে গাড়িটা আরও দ্রুত চালাতে অনুরোধ করছিল; বলছিল, ‘এদের শরীরে রক্ত লাগবে, সময় নেই!’
কিছুদিন পর আমি ফিরে এসেছিলাম। আমাদের কেন্দ্রটা তত দিনে বলতে গেলে শরণার্থী শিবির হয়ে গেছে। আহত মানুষের দেখাশোনা যেমন জরুরি, ঠিকানাবিহীন সর্বস্ব খোয়ানো মানুষের মানসিক ক্ষত সারিয়ে তোলাও তো কম ঝক্কি নয়। সেখানে তখন কত ভাসমান মানুষ! কেউ পালিয়ে এসেছে বাঁচতে, কেউ পাল্টা হত্যার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। গ্রাম আর জঙ্গলের ভেতর তিন থেকে পাঁচ দিন অভুক্ত আর ক্রমাগত হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছেছে তারা। তাই ফিরতেই তাদের প্রয়োজনের সঙ্গে মিশে গেলাম। কণিকা ফিরল না। ফিরে এল বেশ কিছুদিন পরে, ইকবালকে সঙ্গে নিয়ে। হাঁটুর নিচ থেকে একটা পা নেই তার। ক্রাচের খটখট শব্দ তুলে কণিকার সঙ্গে ইকবাল আসতেই তাকে চিনতে পারলাম। অ্যাম্বুলেন্সে আধশোয়া রক্তাক্ত শরীরে সে কণিকার সঙ্গে কেবল দৃষ্টি মিলিয়ে যোগাযোগ করছিল, মুহূর্তে সেই কথা মনে পড়ল। কণিকা এগিয়ে এসে বলল, ‘দেরি হয়ে গেল, দিদি। একে ছেড়ে আসতে পারলাম না।’ আমি মুচকি হাসতেই বলল, ‘তবে কী জানেন, ওদিকে এই ফাঁকে অনেক আহত মুক্তিযোদ্ধাকে সারিয়ে তুললাম। তা ছাড়া দেখলাম এদিক থেকে প্রতিদিন বহু মানুষ যাচ্ছে। তাদের ট্রেনিং হচ্ছে। তারা লড়তে আসবে। কত মেয়ে গেছে, না দেখলে বিশ্বাস করবে না। কেউ এমনিতেই যাবে, কেউ আবার নাকি পুরুষ সেজে ফ্রন্টে যাবে! সে এক বিরাট যজ্ঞ, দিদি, মানুষ আর মানুষ নেই, একেকটা গরম বুলেট হয়ে গিয়েছে।’
একেকটা গরম বুলেট হয়ে গেছে, একেকটা গরম বুলেট…মাথার ভেতর অনুরণিত হতে হতে কলবেলের আওয়াজটা ঘোর ভাঙিয়ে দেয়। দরজা খুলে চমকে উঠি, ‘কণিকা, না?’
‘পা ছুঁয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায় সে। মাথায় হাতটা বুলিয়ে নিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে, ‘আমি কিন্তু তোমাকে ঠিক চিনেছি, দিদি। একগাদা লোকের মাঝখানে ছেড়ে দিলেও চিনতাম। তোমার এই চেহারা কি ভোলার?’
‘তোমাকেও ভোলার নয়, কণিকা। একই রকম শক্ত-সামর্থ্য আছ দেখছি।’
‘সাদা চুল আর কুঁচকে যাওয়া চামড়ার দিকে চোখ পড়ল না বুঝি?’
‘আরে, সেটুকু যদি চিনতে না দিত তবে তো আমাকেও চিনতে পারতে না তুমি।’
‘ইকবাল কই, এল না তো? আর তাকে তুমি পেলেই বা কোথায়?’
‘আসবে। তার সঙ্গে বরাবর যোগাযোগ ছিল আমার। শুধু ভাবিনি কখনো দেখতে চলে আসব। হঠাৎ মনে হলো মরেই হয়তো যাব কদিন বাদে, তার আগে একবার যদি তোমাকে আর ইকবালকে…’
‘ভালো করেছ। নইলে মরার আগে আমিই বা দেখতাম কী করে তোমাদের? তা, উঠেছ কোথায়?’
‘সেসব পরে বলছি। অনেক কথা বলার আছে। তার আগে বলো তুমি কেমন আছ?’
‘আমি তো বেশ আছি, ভাই। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে, তাদের নিজেদের সংসারও হয়েছে। তা, তোমার সংসার হয়েছে? ইকবালের?’
‘শুধু ওটাই আর হয়ে উঠল না, দিদি। আমি তো বেলুর মঠের নার্সিং হোমে জীবনটা কাটিয়ে দিলাম আর সে এখানে, তার বাড়িতে। আহত হয়ে যুদ্ধের পুরো সময় লড়তে না পারার অনুশোচনা তাকে কখনো ছাড়েনি। পঙ্গুত্বের বাস্তবতার সঙ্গে নিজেকে ব্যর্থ ভাবতে ভাবতে জীবনটা খরচ করে ফেলল। আমি ঢাকায় এসেছি শুনে জানতে চাইল, তুমি আবার কেন কষ্ট করে এত দূরে…?’
কণিকার গলা ধরে আসে। আমিও চুপ করে থাকি। আমাদের স্তব্ধতার সুযোগে শহুরে কোকিল একটানা ডেকে যায়। মুষলধারার বৃষ্টির পরে কখনো সেই জঙ্গলের নিরাময়কেন্দ্রের পাশে এমনই কোকিল ডাকত। ডাকের বিরতিতে মেয়েরা একই সুরে কোকিলকে ভ্যাঙাত। কোকিলের ডাকের টান বাড়তে বাড়তে ধমকের মতো শোনাত তখন।
‘কী ভাবছেন, দিদি? আমাদের সেই সময়ের কথা, না?’
‘সেই তো, কণিকা, তোমাকে দেখতেই মনে হলো সেই সময়ে চলে গেছি।’
‘আমার খুব আফসোস হয়, কেন আরও অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলাম না। যুদ্ধ শেষ হলো, কে কোথায় ছড়িয়ে পড়ল কেউ জানল না। যেন প্রয়োজন শেষ তাই আর কখনো কেউ কাউকে খুঁজিনি। কত মেয়ে এসেছিল, কতজন প্রাণের সখী হয়ে উঠল! তা ছাড়া কে জানে, যারা তখনই মরতে চেয়েছিল তারা কি বাঁচল শেষে নাকি মরে গিয়ে বাঁচল?’
কণিকার কথায় আমার আত্মা কেঁপে ওঠে। হ্যাঁ, কতজনই না এসেছিল! একজন এসেছিল মিলিটারি ক্যাম্প থেকে পালিয়ে। হাড্ডি-চামড়া ছাড়া তার শরীরে আর কিছু ছিল না। না, ঠিক তা না, আরও ছিল শরীরভর্তি গভীর-অগভীর কামড় আর খামচির দাগ। কেউ যেন দিনের পর দিন তার চামড়ার ওপরে কাটাকুটি খেলেছে। কেউ কেউ এসেছিল জরায়ুতে সন্তান নিয়ে। সুযোগ পেলেই আমার পা জড়িয়ে ধরে বাচ্চাটাকে বের করে ফেলে দেওয়ার জন্য কাকুতিমিনতি করত। দেরি হয়ে গেছে বললে মরতে চাইত। কখনো চাইত সীমান্ত পেরিয়ে যেদিকে চোখ যায় চলে যেতে। নিজের দেশ ছেড়ে ওদিকে গেলে কপালে কী আছে কে জানে মনে করিয়ে দিলে ঠোঁট উল্টে বলত, ‘তাতে কী, ওখানে কেউ আমাকে চিনবে না। ওতেই চলবে।’
‘ওদের কথা ভাবছ, দিদি?’
‘সেই ভাবনা যে ছাড়ে না, কণিকা। কী কষ্ট একেকজনের! ভাবতে গেলে বুকটা টনটন করে।’
‘মিনু নামের সেই মেয়েটার কথা মনে আছে? তুমি করে দিতে চাওনি বলে নিজেই নিজের শরীরে চামচ ঢুকিয়ে গর্ভটা বের করে এনেছিল, মনে পড়ে? তারপর রক্ত পড়তে পড়তে মরে গেল বেচারি।’
‘মনে আছে। মিনু খুব দুর্বল ছিল তাই আমি রাজি হইনি। জানতাম রক্ত পড়তে শুরু করলে…যা হোক, কিছুই পেল না তারা।’
‘অথচ দেখো, ইকবাল কিংবা তার মতো যারা, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঠিকই সমাজে সম্মানের আসন পেল, সরকারের আনুকূল্যও পেল অনেকে। কেউ কেউ তো শুনেছি সরকারি টাকায় বিদেশ থেকে নকল হাত-পাও লাগিয়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু যে নারী নিজের ছেলেকে যুদ্ধে পাঠাল, যোদ্ধা স্বামীর অবর্তমানে সংসার আগলে রাখল কিংবা যে নারী ধর্ষিত হলো তাদের ভূমিকা হয়ে দাঁড়াল পরোক্ষ। ছেলে, ভাই আর স্বামী যুদ্ধ শেষে ফিরে আসাতে কিংবা শহীদ হওয়াতে গৌরব বোধ করা ছাড়া যেন তার আর কিছুই করার নেই। যুদ্ধ কি কেবল একাত্তরের পুরুষেরাই করেছে, দিদি?’
‘এই কথাটা তোমার মতো করে আমি হাজারবার ভেবেছি, কণিকা। কোনো সুরাহা পাইনি। সশস্ত্র সংগ্রামের যোদ্ধা হিসেবে মেয়েদের কী করে অস্বীকার করা হলো? মানলাম যে যুদ্ধবিধ্বস্ত মেয়েদের গ্রহণ করার জন্য সমাজ তখন তৈরি ছিল না কিন্তু তাই বলে শুধু ধর্ষিতা পরিচয়ের আড়ালে তার আসল অবদান এভাবে ধুলোয় মিশে যাবে? যাক, তবু আশার কথা যে যুদ্ধের ২৩-২৪ বছর পর হলেও, ধারণা পাল্টানোর চেষ্টা করা হয়েছে। খুঁজে খুঁজে বের কথা হয়েছে ভয়ানকভাবে অসুস্থ তারামন বিবিকে। পরপর আরও বেশ কয়েকজনকে…’
আমাদের কথার মাঝখানে সামনের করিডরে খটখট শব্দ শোনা যায়। একবার খট, পরমুহূর্তে শব্দহীন বিরতি, আবার খট। আমাদের কথা বন্ধ হয়ে যায়। কণিকা আসার পর আমি হয়তো দরজা লাগাইনি। শব্দটা দরজা পেরিয়ে ভেতরের দিকে আসে। কণিকা হঠাৎ ঘামতে থাকে, বলে, ‘এতকাল পরে দেখব, আমার যেন কেমন লাগছে, দিদি…তবে সে তুমি যাই বলো, আমি একজন নার্স, আমার কাছে ইকবাল কিংবা ওই মেয়েরা আলাদা নয়। প্রত্যেকের যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সম্মান পাওয়ার কথা। তাদের কেউ হারিয়েছে পা, কেউ জরায়ু। অঙ্গের তফাত কেবল।’
ধবধবে চুলের সৌম্য চেহারার ইকবাল ক্রাচ ঠুকে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমরা তিনজন নিস্তব্ধ হয়ে থাকি। তারপর কণিকা আর ইকবালের চোখের দৃষ্টিকে অনুসরণ করি আমি। সেই প্রথম দেখার দিনের মতো। চোখের দরজা দিয়ে তারা একে অন্যকে জানতে চায়। তারপর বহুক্ষণ আমাদের কারও চোখের পলক পড়ে না।
সূত্র: প্রথম আলো