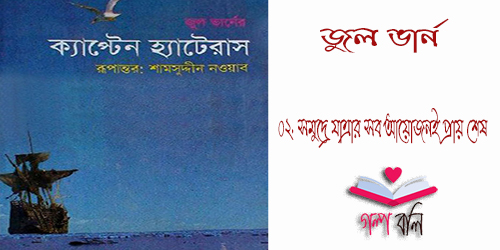লন্ডন এখন আগুনমুখো রঙিন পাতায় ছেয়ে আছে। রোদের আলোর মৃদু তাপে যখন ওম লাগাই শরীরে, তখন পাতারা ঝরে পড়ছে। যেদিন বৃষ্টি পড়ে একনাগাড়ে, ঘরদোরে বিছানা বালিশে ক্লান্ত মন শুয়ে থাকে, অথচ জীবন ব্যস্ত অফিস পাড়ায়, তখনও পাতা ঝরছে। আর মাত্র ক’দিন পরই শূন্য হবে গাছের ডালপালা। আমরা কয়েক পরতে গায়ে জড়াব শীতের কাপড়। পথের বাঁকেই হারাবে মানুষেরা, পাখির কোলাহল। নাকি এই শুকনো মচমচে পাতার পথ পেরিয়ে এক অজানা মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে তারা কুয়াশায়? মাঝে মাঝে মনে হয়, মানুষ আদ্যোপান্তই অগোছালো স্মৃতির টুকরো। জন্মাবধি তার শুধু যাওয়া আসা। এই আসা যাওয়ার সন্ধিতে আমরা মাঝে মাঝে কী কেবল বিরতি?
এই শহরে প্রথম যেবার এলাম, তখন শীত পড়তে শুরু করেছে। আমার থাকবার জায়গা হয়েছিল বাঙালি অধ্যুষিত ব্রিক্লেইনে। রাস্তার নামগুলো বাংলা অক্ষরে লেখা দেখে বেশ লাগছিল। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত নটিংহিল কার্নিভালের পর সবচেয়ে বেশি লোকারণ্য বাঙালির বৈশাখী মেলাতে। সেই মেলায় উপস্থাপক হিসেবে মঞ্চে ওঠার পর চোখের সামনে লক্ষ মানুষ, উৎসবে শামিল ভিনদেশিরাও। কত দূরের শহর বা দেশ থেকে যে এরা আসেন এখানে! কেন আসেন? কিসের টানে? এলোমেলো ভাবনার মাঝে এদিক-ওদিক দেখছি, চোখে পড়ছিল খাবারের দোকান। চটপটির, বিরিয়ানির। তারই মাঝে হুট করে বাংলাদেশি পোশাকের। মান বিচারের বিপরীতে, বেচা বিক্রি সেখানে নেহায়েত মন্দ হয় না। লন্ডন সেদিন মেঘলা, আমার লাল শাড়ি ঠাণ্ডা বাতাসে ফুলে উঠছিল বারবার। কাজের ফাঁকে গ্রিনরুমে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, মঞ্চে তখন কুমার শানু গাইছিলেন, ‘চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারই।’ এভাবে দিন ফুরাল। বাড়ি ফিরে যাচ্ছে সবাই। আমার ছুটির এক মাস সাঙ্গ হলে আমিও পেল্গনে উঠলাম এই শহরের অভিজ্ঞতা নিয়ে, আমার শহরে- প্রাণের ঢাকায়।
ভাবছিলাম, বৈশাখ নতুনের আবাহন নিয়ে বারবার আসে যায়। ষড়ঋতুর বাহারি উদযাপন তো বাঙালির জীবনে অনুপ্রেরণা। জায়গাভেদে তাতে হেরফের খুব একটা হয় না। তখন আমি জন্মশহর ঢাকা ছেড়ে গাজীপুরে থাকতে শুরু করেছিলাম। নতুন স্কুল, নতুন বন্ধু, নতুন শিক্ষক। তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সংস্কৃতি চর্চার নতুন বলয়। একবার খুব সকালে বের হবো বৈশাখের অনুষ্ঠানের জন্য। কিন্তু আকাশ দাপিয়ে শুরু হলো বৈশাখী ঝড়, থামার কোনো লক্ষণই নেই! কিন্তু আমরা যারা অনুষ্ঠানে অংশ নেব, তাদের রুখবে সেই সাধ্য তো বৈশাখী ঝড়ের নেই! রাস্তার কালো পিচ বর্ষণে ভিজে আছে, আমগাছের মুকুল ঝরে পড়েছে পথে। সোঁদা মাটির গন্ধে লেপ্টে আছে ভেজা ঘাস। ভেবেছিলাম, কালবোশেখী মানুষকে ঘরের বাইরে আসতে দেবে না, কিন্তু অনুষ্ঠান শুরু হতেই শত মানুষে মাঠ ভরে গেল। দুপুর নাগাদ কড়া রোদ উঠল। আমার আবৃত্তির শিক্ষক, যাকে আমি আজীবনের গুরু হিসেবে মান্য করি, তিনি তখন বলেছিলেন, ‘গোটা দুনিয়া একদিকে, তোমার বৃদ্ধি একদিকে। ঝড় তো তাকে রুখতে পারবে না।’ তার সেই উচ্চারণের দৃঢ়তা আমাকে এখনও স্পর্শ করে। ঢাকা ছেড়ে, প্রথম স্কুল, প্রথম হওয়া বন্ধুত্ব ফেলে, চিঠি লেখার দিনগুলোয় অচেনা শহর গাজীপুরে পা ফেলেছিলাম। ঢাকার স্কুলে প্রথম বন্ধু সোমা, সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি আর সবুজ হাফপ্যান্ট পরা মেয়েটার শ্যামলা কপালে ফ্রিঞ্জকাট, পেছনে কোমর ছুঁয়ে চুল, স্কুলে ওর আমার বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে থেকে গল্প পেছনে রয়ে গেল। ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার পর আজ অব্দি সোমাকে পাইনি খুঁজে। জানি না সেও আমার খোঁজ করে কি-না। এত বছর পেরিয়ে গেছে, আমরা দু’জন পাশাপাশি হেঁটে গেলেও চিনব না দু’জনকে আর। ফয়সল নামে একটা ছেলে আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকত। আমরা একসঙ্গে খেলতাম পাড়ার ছেলেমেয়েরা। একদিন সকালে ফয়সল আমার জন্য কোত্থেকে কুড়িয়ে পাওয়া রুপার ঝুমকো নিয়ে এসে একেবারে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে দিল! মাত্র তখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি। ওইটুকু বয়সে বিয়ের মতো সিরিয়াস কিছু নিয়ে ভাববার কোনোই কারণ নেই। তবে মা-খালামণির সঙ্গে আমিও খুব হেসেছিলাম। আমাদের খেলার বিশাল এক মাঠ ছিল। আজও মনে হয়, সেই মাঠ যেন অক্ষত মাটির আবরণে গেঁথে রেখেছে আমাদের শৈশব। ছোটবেলায় কুড়িয়ে পাওয়া ছোট্ট নুড়ি অথবা কোনো অনাত্মীয়ের স্নেহ বা ভর্ৎসনাও মনে গেঁথে যায় আজীবনের জন্য। শৈশব-কৈশোরের সন্ধিক্ষণে বড় হয়ে ওঠার সে সময়টায় ঢাকার ফ্ল্যাটবন্দি জীবনের গল্পগুলো এখনও মোলায়েম। সকাল বা দুপুরে মুড়ির মোয়া ধামায় ভরে বিক্রি করত, বিক্রেতার উচ্চৈঃস্বরে হাঁক ‘আই মোয়া’র প্রতিধ্বনি, ঝুট কাপড়ের টুকরো এনে দেওয়া গার্মেন্টের সেই টুম্পা নামের মেয়েটাকে কখনও ওই পথগুলোয় যদি খুঁজে পেতাম! শিল্পকলা আর চারুকলায় হরদম আসা যাওয়ার সময় হাতে হাওয়াই মিঠাই নয়তো টিয়ে অথবা কমলারঙা পাইপ আইসক্রিম থাকত। চাইলেও সেই দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে পারব না।
গাজীপুর আমার কাছে ছিল দেবদারুর ছায়ায় ঘেরা স্বপ্নপুরীর মতো। ওখানে স্কুলে ক্লাস পার্টিতে আমাকে স্বাগত জানানো হলো এক অদ্ু্ভত উপায়ে! আমার সমস্ত মুখে সহপাঠীরা চুমকি মেখে দিল, সেখান থেকেই কিছুটা চোখের ভেতরে ঢুকে যাওয়ায় কিছু দেখতে পারছিলাম না। হঠাৎ করে ওরকম পরিস্থিতিতে পড়ে আমার মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল, ক্লাস টিচারকে জানানোর পর সবাইকে একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে তিনি বেতের যে বাড়িগুলো দিয়েছিলেন ওদের, এখন ভাবলে আমার খারাপ লাগে। ওরা আমাকে ‘ঢঙ্গী’ খেতাব দিলো তবে সবাই মিশেও গেলাম তাড়াতাড়ি। এরপর শুরু হলো নতুন উপদ্রব। ক্লাসরুমে এবং রাস্তায় আসা যাওয়ার পথে দেখি আমার নামের সঙ্গে যোগচিহ্ন দিয়ে অন্য কারও নাম! কানাঘুষাতে বুঝতে পারলাম, এটা খুব ভালো কিছু না। দিনে দিনে আমার নামটা ঠিক থাকে, তবে পাশে যোগ হয় নিত্যনতুন নাম। তখনই প্রথম বুঝতে পারি ইভটিজিং কতটা মানসিক ভোগান্তির কারণ হয়ে ওঠে। সে সময়ে যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওরকম যন্ত্রণা করত, এখন হয়তো তারাও জীবন নিয়ে এগিয়েছে অনেকটা। ওরা সেই সময়টাকে কীভাবে মূল্যায়ন করে, জানতে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে। আমি তো শহরটাকে ছেড়েছি বহু বছর, ওদের কেউ কেউ আসা যাওয়ার পথে সেসব হুলুস্থূল কাণ্ড ভেবে কি লজ্জিত হয়? স্কুল থেকে বাসায় আসা যাওয়ার পথে তখন রিকশাভাড়া ছিল দুই টাকা। তখনই প্রথম বন্ধুদের মাধ্যমে টাকার ইচ্ছেমাফিক ব্যবহার শিখেছিলাম। টিফিনের খরচ আর রিকশাভাড়ার টাকা একসঙ্গে মিলিয়ে শুরু হলো আচার আর লটারিতে আইসক্রিম খাওয়ার অভ্যাস। একদিন বন্ধুরা মিলে টিফিনে ভাড়ার টাকা সাবাড় করে হেঁটে বাসায় ফিরছি, রাস্তা পার হতে গিয়ে রিকশার নিচে পড়ে গেলাম! হাঁটুতে ভালোরকম চোট পেয়েছিলাম। বাসায় পৌঁছুলে হাসপাতালে নিয়ে ক্ষতস্থান পরিস্কার করে ব্যান্ডেজ করালেন বাবা। সেই ক্ষতের দাগ এখনও অক্ষত রয়েছে ডান পায়ে। হুলিয়া জারি হলো, একা স্কুলে আসা যাওয়া বন্ধ। দু-তিন বছর পর একই পথে রংবাজদের খপ্পরে পড়ে পুরো গায়ে রঙ মেখে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছিলাম, তখন বাংলাদেশ ক্রিকেট দল জিতলেই পাড়া-মহল্লায় রঙ মাখানোর ভয়ানক রেওয়াজ শুরু হয়েছিল। বখাটেরা শুনেছি রঙের সঙ্গে গোবর মিশিয়ে মানুষের গায়ে ছিটিয়ে দিত! প্রায় বছর দশেক পর সেই একই রাস্তায় নিজের উথাল-পাথাল স্মৃতি সামাল দিয়ে বাইরের নিরুত্তাপ চেহারায় গাজীপুর দেখে মনে হলো রুক্ষ হয়ে গেছে পুরনো শহরটা, দেবদারু গাছগুলো সব উধাও।
আবার আমরা ঢাকায় ফিরলাম। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম, নতুন বন্ধু হলো। তুমুল আড্ডা দিতাম সকাল থেকে সন্ধ্যা। ধানমণ্ডি লেকে তাকস্ফওয়া মসজিদের পেছনের মাঠে বসত সেই আড্ডা। পাল্লা দিয়ে চলত গান, কবিতার আসর। পরিত্যক্ত একটা বাথটাব ছিল পার্কের মাঝে। ওটার মধ্যে বসেও বন্ধুরা ছবি আঁকত, চা খেত। এর মাঝে আমার চাকরি জীবন শুরু হলো। প্রথম চাকরি এবং সেটিও কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পাওয়ায় আমি আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলাম। এখন বুঝতে পারি, সেই আনন্দ যতটা চাকরি পাওয়ার তারচেয়ে বেশি ছিল দায়িত্ব নিতে পারার নিশ্চয়তার। আমার জীবনে যুক্ত হলো নতুন দৌড়। এই দৌড়ের চক্করে গানের চর্চা জীবন থেকে গত হলো। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ কমে গেল একেবারেই। চেনা রাস্তার পাশে টং দোকানে চায়ের কাপে বৃষ্টির ফোঁটা মিশিয়ে এক চুমুকে শেষ করার দিন গেল। আয়েশ করে বসে ঝালমুড়ি খাওয়ার দিন গেল। ইউনিভার্সিটির সেইসব আড্ডায় নানা বয়সীদের সবাই এখন যে যার কাজে ব্যস্ত। এবার দেশে গিয়ে খুব অল্প ক’জনকেই দেখতে পেলাম। রাস্তার জ্যাম, প্রচণ্ড গরম ঠেলে, কাজ গুছিয়ে চাইলেও সবাই আসতে তো পারে না! তবু যাদের দেখলাম, সেও তো কম কিছু নয়।
দেশের সেই ছুটে চলা অধ্যায়গুলোতে অনুষঙ্গ চেনাশোনাই ছিল- অন্তত পরিবেশগত, ভাষাগত কিংবা ভৌগোলিক দিক বিবেচনায়। কিন্তু মানুষ যখনই থিতু হতে চায়, তখনই প্রকৃতি মোড় ঘুরিয়ে নেয়। পরিবার, পড়াশোনা, চাকরি, ক্যারিয়ারে উত্থান নিয়ে সন্তুষ্ট আমাকে নিজস্ব বৃত্ত থেকে ছিটকে বেরোতে হয় এরপরই। চলে আসি নতুন দেশে, নতুন শহরে। কিছু মানুষের স্বপ্ন থাকে, এমন কোথাও চলে যাওয়ার, যেখানে তাকে কেউ জানে না, কেউ চেনে না। আমার এই নতুন শহরে আসা অনেকটাই তাদের সেই চাওয়ার সঙ্গে মিলে যায়। শুরুর দিকে মনে হতো, শূন্য থেকে জীবন শুরু করেছি আমি। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার ধরন থেকে শুরু করে চাকরির রিক্রুটমেন্ট কিংবা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠা, সবটাই নতুনত্বে মোড়ানো। ছকবাঁধা দিন থেকে রাত। বিদেশি বন্ধুদের কাছে হঠাৎ নিজের ফেলে আসা জীবনের আলাপের একপর্যায়ে আবিস্কার করলাম, আমি আর নিজ দেশেও নেই, নেই এই বিদেশেও। তখনই মন চলে যেতে চায় আসা যাওয়ার চেনা পথে। চোখে ভাসে, বিশ বছর আগের ফেলে আসা শহরে দেবদারু গাছের সারি। সাইকেলে বসে থাকা লাজুক ছেলেটার প্রণয় প্রস্তাব। স্কুল শেষে সব বন্ধুরা একসঙ্গে রাস্তা দখল করে বাড়ি ফেরা, প্রতি বিকেলে বাবার হাত থেকে ভাজা গরম বাদাম খাওয়ার অপেক্ষা, মায়ের বুকের ওম, ভাইয়ের সঙ্গে খুনসুটি। অফিসের কলিগদের সঙ্গে দেশ, জাতি, খেলা নিয়ে তর্ক। ইচ্ছে করে যাই চলে। দাদাবাড়িতে ছোটবেলায় যখন বেড়াতে যেতাম, ঈদের দিন সকাল থেকে বাড়ির মসজিদের পেছনে মেলা বসত। সেখান থেকে মুড়কি, নিমকি কিনে খেতাম সব ভাইবোনেরা মিলে। শ্যাওলা জমা পুকুরের মতো সবুজ মার্বেল জমাতাম। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হলে ক্ষেতের আল বেয়ে নেমে যেতাম শ্যালো ইঞ্জিন থেকে ফুলকি দিয়ে বের হওয়া ঝকঝকে পানি খেতে দুই হাত ভরে, লাটিম খেলা নিয়ে হারজিত হতো, ডাঙুলি খেলার চেষ্টা করতাম, মাঠ কাঁপিয়ে খেলতাম ইচিং বিচিং, প্রকাণ্ড ঘুড়ি বানাতাম বাড়ির উঠানে বসে, জ্যোৎস্না রাতে মসজিদের সিঁড়িতে বসে লাল পরী, নীল পরীর গল্প শুনতাম। অমাবস্যায় কুয়োর ধারে একা যেতে ভয় লাগত বলে মা পেছনে দাঁড়াত হ্যারিকেন হাতে, জোনাক পোকায় ভরে থাকা মাঠ দেখে আপল্গুত হতাম। দাদুর সিন্দুকে জমিয়ে রাখা রসালো আম, আতার আস্তানায় হঠাৎ পাওয়া আমার ছেলেবেলার সংসার, সেখানে মাটির পুতুল, শিল-পাটা, প্রতিযোগিতায় জিতে যাওয়া কাঁসার পেল্গট সব চোখে ভাসে। বাড়ির সামনে পেছনে কত যে ফলের গাছের বাহার ছিল। শীতের ভোরে খেজুর গাছ থেকে রস পাড়িয়ে দিত দাদু। আমাদের সেই মস্ত বড় পুকুরঘাটে বসে লুচিভর্তা খেতে খেতে গ্রীষ্ফ্মের দুপুর পেরিয়ে যেত। অমোঘ টান, নাড়ির টান, পিছুটানগুলোকে যেন জোর করে দমাই। ইচ্ছেঘোড়ায় লাগাম দিয়ে বছরের পর বছর নিজেকে ভেঙে, গড়ার বাজিতে টিকে থাকতে চাই।
আমি যখন বেশ ছোট, তখন আমার নানুভাই মারা যান। সেবার নানুবাড়িতে বড়ই গাছটায় সুস্বাদু বড়ইয়ে গাছ নুয়ে পড়েছে। নানুভাইয়ের কফিন থেকে তিনটে কাঠ নিয়ে আমি তাতে মা, বাবা, মেয়ের চরিত্র বসিয়ে খেলছিলাম। তার সপ্তাহখানেক আগেই কলকাতা থেকে আসা পাশের বাসার তুলির সঙ্গে আমার পুতুল মেয়ের ধুমধামে বিয়ে করিয়েছি। লুচি, সুজির পায়েস, সবজির সেই গন্ধ মনে হয় এখনও পাই। আমার পুতুল যখন সিঁদুর মেখে বউ সেজে চলে গেল, আমি কিন্তু কেঁদেছিলাম অনেক! আমার সেই পুতুল মেয়েটাকে মিস করি আজও। তুলিও নিশ্চয়ই আমার মতো বড় হয়েছে, তারও সত্যি এক সংসার হয়েছে নিজের! জীবন নিয়ে সেও দৌড়াচ্ছে! নানুবাসার সামনে একটা বাড়ি ছিল একেবারে মসজিদের মত ডিজাইন। সেই বাসাটার বারান্দায় আমরা পাড়ার ছেলেমেয়েরা কত লুকোচুরি খেলেছি, মাঠে খেলেছি গোল্লাছুট। নানুর বাসার বড়ই গাছের বড়ইগুলো গোগ্রাসে গিলতে গিয়ে সেবার একটা বিচি পেটে চলে গিয়েছিল, আমি ভয়ে সে রাতে ঘুমাতে পারিনি। মনে হচ্ছিল, পেট, কান ফুঁড়ে গাছ গজালে মা তো জেনে যাবে আমি তার কথা শুনিনি! তখন উপায় হবে কী? হঠাৎ এক ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে আমি বুঝতে পেরেছিলাম মা পাশে নেই, নানু, খালামণি কেউ নেই! কান্না শুরু করতেই তুলির খালামণিরা এসে আমাকে তাদের বাসায় নিয়ে বুকে জাপটে ধরেছিল। ওদের ঘরজুড়ে ছিল গণেশ আর দেবী সরস্বতীর সাদা নীল সোনালি রঙের পোস্টার, আমি চোখ বড় বড় করে মৃদু আলোয় তাদেরই দেখেছি সকাল পর্যন্ত। নানুভাইয়া ওপারে চলে গেল, জামালপুরে শেষ হলো সেইসব রাস্তায় আমার যাওয়া আসা। দাদুভাইকে হারালাম বেশ অনেকটা বড় হয়েই। সেইসঙ্গে দাদুর সিন্দুকে জমিয়ে রাখা আমার শৈশবও। আমার নিজস্ব বাড়িটা আগের মতো নেই। সেই বাঁধানো পুকুর, ঢেঁকিতে নতুন ধানের গন্ধ কিচ্ছু নেই এখন আর।
কিছুই হয়তো আগের মতো থাকে না। স্মৃতি থেকে যায়। আসা যাওয়ার মাঝে কিছু সৎকর্ম টিকে থাকে। অনেক বছর পর মায়ের কাছে ফিরব বলে এবার সত্যি আকাশে উড়লাম। মা তখন জীবন-মৃত্যুর মাঝে যুঝছে। নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাস নিয়ে যাচ্ছিলাম দেশে, ভেবেছিলাম, আমি যাওয়া পর্যন্ত মা অপেক্ষা করবে, আমি গিয়ে তার হাত স্পর্শ করলে সে চোখ মেলে তাকাবে। ঠোঁট নড়ে উঠবে তার। বলবে, ‘বাবা, এসেছ?’ তারপর মা সুস্থ হয়ে গেলে আমরা সবাই মিলে বেড়াতে যাব চেনাশোনা জায়গাগুলোয়। তারপর মাকে জড়িয়ে ধরে তার গন্ধ নেব। এই গন্ধের জন্য, মায়ের আদরের জন্য, তার হাতে রান্না করা খাবারের জন্য দিনের পর দিনের অপেক্ষা শেষ হতে না দিয়ে, মা আমাকে কিচ্ছুটি না বলে চলে গেল। কোথায় গেল? ভাবি, ভেবে কোনো আদি-অন্ত পাই না। শুনেছি, মা যেখানে আছে সেখান থেকে আসার আর পথ নেই। তবু মনে হয়, এখানেই কোথাও তার উপস্থিত থাকার কথা! তাকাই, চোখ পরিস্কার করে আবার তাকাই। ডাকি, স্বর স্পষ্ট করে আবার ডাকি। তার দেখা নেই, তার শব্দও নেই। সে কি আর আসবে? আবার দেখব তাকে? কোনো একদিন আসা যাওয়ার পথে আবার মিলব আমরা? যদিও পড়েছি, মানুষের মৃত্যু মানেই সমাপ্তি, পুনরুত্থান বলে কিছু নেই! তবু আলো-আঁধারে কান্না হাসির সমীকরণে, কী এক মায়াজালে ঘুরপাক খাই, করি একই পথ পরিভ্রমণ। চাইলেও যা হওয়ার নয়, তাই চাই।