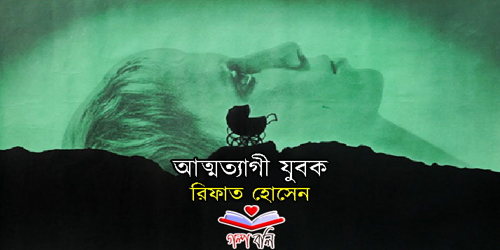এখনও কোনো গাড়ি গভীর রাতে বাড়ির গেটে থামলে আঁতকে ওঠেন ফিরোজ। গেটে এসে পড়া গাড়ির আলোকে মনে হয়- একটা রাক্ষুসে দানবের দুটো জ্বল জ্বলে চোখ। আর এক্ষুনি গাড়ি থেকে নামবে ক্যাপ্টেন আর সিপাহিরা। তাদের বুটের শব্দ রাতের নীরবতার ভেতরে বেজে উঠবে। গাড়ি থেকে নামবে একটা কফিন। আর একটু পরে বলবে, ইয়ে লোগ গাদ্দার।
এখন আর সেই বাড়ি নেই। পুরো বাড়িটা গায়েব হয়ে অন্য বাড়ি। এটা আর বাড়ি তো নয়, অ্যাপার্টমেন্ট। তিনি দোতলার সামনে দিকে একটা ফ্ল্যাটে থাকেন। আশেপাশে কোনো বাড়ি আর আগের মতো নেই। ডেভেলপারদের পাল্লায় পড়ে, এখানকার জমি আর যাদের নিজের বাড়ি ছিল, তাদের সবারই কপালই খুলে গেছে। কিন্তু আগের সেই ছায়া ঢাকা, পাখি ডাকা ধানমন্ডির কথা দিনের এমন কোনো ক্ষণ নেই যে মনের ভেতরে হানা দিয়ে যায় না। যদিও নির্জনতা এপাশটায় এলাকার অন্য জায়গার থেকে একটু বেশিই আছে। কোনো কোনো জায়গা তো এখন একেবারে বাণ্যিজিক। হাসপাতাল, বেসরকারি বিশ্বাবিদ্যালয় আর কত কি। লেকের অবস্থাটাও বাণ্যিজিক। আগের সেই প্রাকৃতির স্নিগ্ধতার জায়গায় এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া, হালজামানার নানান স্থাপনা, আছে রেস্তোরাঁ, লেকে ঘুরে বেড়ানোর নতুন ব্যবস্থা। ছেলেমেয়েদের হালচালও আলাদা। এরা প্রাইভেট কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, আর পুরো ধানমন্ডিটা হয়েছে এদের ক্যাম্পাস।
তার পরও ধানম-ির মতো জায়গায় বাড়ি আর জমি ছিল। বুদ্ধিটা অবশ্য ফরিদ ভাইয়ের। নইলে আবার কুষ্টিয়া গিয়েই শেষ জীবন কাটাতে হতো। এখন ঢাকায় থাকা হতো না। কারণ বাড়ি করার মতো ধৈর্য তার অন্তত ছিল না কোনোদিন। শেষ বয়সে ফিরোজদের মতো লোকের হাতে কিছু টাকা। কয়েকটা ফ্ল্যাটের ভাড়া। সবমিলিয়ে শেষ বয়সে স্বস্তিই মিলবার কথা ছিল। কিন্তু তা আর মিলল কোথায়? আসলে সব হিসাবের গোলমাল বাধিয়ে দিল এরশাদের আমল। বড় ভাই ফরিদ বার বারই বলেছিলেন, জীবন আমাদের জন্য যে-ফাঁদ পেতেছে- সেখানে যদি পা দিস-ও, আগে থাকতে ফঁাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার সব উপায় জেনে রাখিস। ভাইবোন, নিজের সবার ছেলেমেয়েদেরই, প্রায় সবাইকে হয় কানাডা, নয়তো অস্ট্রেলিয়া, নয়তো আমেরিকা কি ব্রিটেনে পাঠানো হয়ে গেছে বহুদিন আগে। নিজের ছোটছেলেটা কদিন হলো জার্মানি থেকে এসেছে। এবার অনেকদিন থাকবে বলেছে। আর্ট কলেজে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে যাচ্ছে প্রতিদিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের নানান বিভাগে তার আরো আরো বন্ধুবান্ধব পড়াচ্ছে। এই কদিন তাদের সঙ্গে গিয়েই আড্ডা, খাওয়াদাওয়া হচ্ছে।
একদিন এর ভেতরে আর্ট কলেজের দেয়াল ঘেঁষে থাকা ফুটপাত থেকে একটা বই কিনে এনেছে। জন পিলজারের ‘হিরৌজ’। বইটা উলটাপালটা করে, কিছুক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি পর থেকে একটা চিনচিনে ব্যথা মাথায় সেই যে সন্ধ্যায় দেখা দিয়েছে এখনও যাচ্ছে না। বইটিতে থাকা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ কীভাবে সাজানো হয়েছে, তার বদলে প্রথমে নজর পড়েছিল ছবিগুলোর দিকে। সাদাকালো ছবি। এর ভেতরে বাংলাদেশের এ ইউ এম ফকরুদ্দিন, ‘ডেইলি মিররে’ কাজ করা সেই সাংবাদিকের ছবিটা দেখেই নাকি অর্পণ বইটা কিনেছিল।
দেখ তো আব্বু তোমার কাজে আসে নাকি।
ওই ছবিটা দেখেই সূচিপত্রে অর্পণের চোখ যায়। তাহলে বাংলাদেশের কথা কোথায় আছে?
জন পিলজার দেশ অস্ট্রেলিয়া। তাই প্রথমেই অস্ট্রেলিয়ার কথা, তারপর ব্রিটেন, আমেরিকা, ভিয়েতনাম, আফ্রিকা, এবং এরপর বাংলাদেশ, কিন্তু এখানে নাম ‘জয় বাংলা’ নিচে ফার্স্ট ব্র্যাকেটে লেখা ‘লং লিভ বেঙ্গল’; এরপর প্যালেস্টাইন, কম্বোডিয়ার কথা, পরের দুটোতে শিরোনাম অন্য- সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকার প্রসঙ্গ হয়ে ফের অস্ট্রেলিয়া দিয়ে শেষ। ‘জয় বাংলা’র কথা ১৯৭০-এর জলোচ্ছ্বাস দিয়ে শুরু। অধ্যায়টির শেষে ফকরুদ্দিনের কথা ছিল,‘উই স্টিল অ্যাওয়েট সিম্পল ডেমোক্রেসি। উই আর আনডিটার্ড।’ হা গণতন্ত্র! এমন বহুবার হয়েছে। গণতন্ত্র কথাটা কানে এলেই তিনি প্রায়ই বুটের শব্দ শুনতে পান। আবার একটু পরেই নাগিসা ওসিমার দুটো ডকুমেন্টরি- ‘জয় বাংলা’ এবং ‘দ্য ফাদার অব বাংলাদেশ’- কোনো একটায় থাকা ধারাভাষ্যের সেই কথাটা মনে ঘাই দেয়- যেখানে নাগিসাও বলেছেন- এত মৃত্যু, হানাহানি, রক্তপাত, বিপর্যয়ের পরও বাংলাদেশের মানুষ কখনোই হতাশ হয় না। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন খালেদ মোশাররফ, জিয়াউর রহমান, আবু তাহের, সি আর দত্ত, সফিউল্লাহ, আবু ওসমান চৌধুরী, কাজী নূরুজ্জামানসহ সব সেক্টর কমান্ডারের ছবি। কত না নাম না-জানা মুক্তিযোদ্ধার মুখও হানা দিতে থাকে। আর সবকিছু ছাপিয়ে কেবল ‘জয় বাংলা’, ‘জয় বাংলা’ বাজতে থাকে মনের ভেতরে।
এ ইউ এম ফকরুদ্দিনের ছবিটা তোলা হয়েছে ১৯৭৪ সালে। ছবিটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলেন ফিরোজ। ফকরুদ্দিনের কথা মনে করার চেষ্টা করেছেন। পিলজার বইজুড়েই সেই সময়ের পৃথিবী জোড়া নানান সংকটের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া মানুষদের কথা বলেছেন। আসলে তো হিরো পিলজার নিজেও। পিলজারের বইটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন ফিরোজ। মাথাটা নীচু হয়ে যায়। হাতটা একটা শঙ্খমুদ্রার মতো, সব আঙুলের ডগা একসঙ্গে হলে যেমন হয়, সেভাবে করে, সেটা তো আপনা আপনি হয়ে গেছে। সেই শঙ্খময় হাতের মুদ্রাটি কাপলে ঠেকিয়ে মাথাটা নিচু করে থাকেন। আর টের পান মনে ভেসে উঠছে- সাতই মার্চের ভাষণ, ২৫ মার্চের রাতের গোলাগুলি, আর জয় বাংলা জয় বাংলা। এইসব শব্দে ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে তার নিজের পুরো অতীতের আকাশ।
২.
চল্লিশ বছর আগে মার্চ মাসের শেষ দিক থেকে এই আঁতকে ওঠার পালা সেই যে শুরু হয়েছে এখনো থামেনি। অথচ বয়স সত্তর পর হয়ে গেছে কবেই। আশি হবে কদিন পর। দেখতে যদিও ষাটের বেশি মনে হয় না। তারপর কত জায়গায় কত জল গড়াল, কত গড়ানো জল শুকিয়ে গেল; মরে গেল কত নদী, পুকুর, জলাজমি, দিঘি; কিন্তু রাতের বেলা বাড়ির গেটে কোনো গাড়ি এলেই সেটা ধাঁ করে এক নিমিষে তাকে চল্লিশ বছর পেছনে নিয়ে যায়।
সেদিন ছিল পর পর তিনটি গাড়ি। প্রথমে একটা জিপ, তারপর একটা ট্রাক তারপর আরেকটা মিলিটারির গাড়ি। সে-সময়ের রাত নয়টা মানে বেশ রাত। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। কারফিউ চলছে। চারদিক নীরব নির্জন। মাঝে মাঝে দূরে কোথায় একটা দুটো কুকুর ডেকে উঠছে। বাড়ির গেটা বন্ধ ছিল। গেটে বা বাড়ির ভেতরটা ছাড়া কোথাও আলো ছিল না। গাছের পাতা বেয়ে পড়ছে টুপটাপ বৃষ্টির পানি।
জিপটা থামার পরও তার আলো জ্বলছিল। গেটের তালা খুলে দেন আনসারুদ্দিন ভাই। তখন তিনি ছিলেন এ বাড়ির একমাত্র গাড়িচালক। আগে বাড়ি ছিল বর্ধমানে। আমৃত্যু দেশ বলতে ওই বর্ধমানকে বুঝতেন। কেউ বাড়ির কথা জানতে চাইলেই জবাব- বর্ধমান, বা বাড়ি তো ছিল বর্ধমান, এখন আর কোনো বাড়ি নেই। তখনই বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। কত আশা নিয়ে এদেশে এসেছিলেন। তার ছেলে আরমানউদ্দিন নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে এখন আমেরিকার একটা বিশ্বাবিদ্যালয়ে পড়ায়। মাসে একদিন সে ফোন করবেই। তিনি বলেন, আরমান দেশে আসবে না?
সে বলে, চাচা, বাবা দেশ ছাড়া হয়েছিল একভাবে। আমি দেশ ছাড়া আরেকভাবে। পাকিস্তান বাবার দেশ হতে পারেনি। বাংলাদেশও আমাদের দেশ হতে পারল না, যে বাংলাদেশ আমরা চেয়েছিলাম। আর আমি ভারত-পাকিস্তানে কোনোদিন নিজের ইচ্ছায় বেড়াতে যাব না।
কেন?
এই দেশ দুটো আমাকে দুই বার দেশ ছাড়া করেছে। দেশহীন করেছে। এখন আমেরিকাই আমার দেশ। আমি নিজেকে এই দেশের খিদমদগার হিসেবেই পুরো তৈরি করে ফেলেছি। আমার কোনো পিছু টান নেই চাচা। কেবল আপনাদের দেখতে ইচ্ছা করে। আমার প্রতিটা কাজে আমি আপনাদের কথা স্মরণে রাখি। কোনোদিন আপনাদের কোনো কাজে আসব কিনা জানি না- সেই সাহসই আমার হয় না, চাচা। ফোনের অন্যপ্রান্তে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠাটা লুকানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিল আরমান, কিন্তু ফিরোজ ঠিকই বুঝতে পারেন।
সেদিন আরমানও ছিল ফিরোজের পেছনে দাঁড়িয়ে। বাড়ির পেছনে সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে থাকতো আনসার ও তার বৌ আর এই এক ছেলে। স্কুল ঘরের মতো এল আকৃতির সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে সে ছাড়াও দুটো কাজের মানুষ থাকত।
তিনটা গাড়ির শব্দে বাড়ির ভেতরটাও কেমন ভারী হয়ে উঠেছিল। সেই ভার যেন কেউ সহ্য করতে পারছিল না। এজন্যই কি বাড়ির সবাই একরকম ছুটে বেরিয়ে আসে? সবাই মনে করেছিল যশোর থেকে কর্নেল দুলাভাই বাড়ির বড়মেয়ের পরিবারকে, মানে তার স্ত্রী আর দুই ছেলে এক মেয়েকে, ঢাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ? একটা ফোন করেও তো জানাতে পারতেন। তবে দেশের যা অবস্থা তখন সব কিছুই হঠাৎ। এক মুহূর্তের ভেতরেই বদলে যেতে পারে এক একটা মানুষের পৃথিবী। ¯্রফে ‘আছি’ থেকে ‘নাই’ হয়ে যেতে পারে, যে কেউ যেকোনো সময়। ২৫ মার্চ রাত থেকে এ-ই চলছে। বাড়ির বাইরে গিয়ে ফিরে আসেনি কত হাজার লোক। তখনো অনেকে ঠিকমতো জানে না দূরের লোকজন কে কোথায় কেমন আছে। সেদিন মার্চের ত্রিশ তারিখ! টিপটিপ বৃষ্টির রাত।
বাড়ির সবাই নেমে দেখে জিপ থেকে নেমে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে ফাতিহা বুবু। চোখে মুখে এক ভাষাহীন প্রচ- স্তব্ধতা। একদিনেই ফাতিহাকে চেনা যাচ্ছে না। কী উচ্ছল ছিল বুবু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের ছাত্রী। বিয়ের পরও কত কষ্ট করে ঢাকা-যশোর করে লেখাপড়া শেষ করেছে। একটুর জন্য দর্শনে ফার্স্ট ক্লাসটা পায়নি। লম্বায়, স্বাস্থ্যে, চেহারায় আদর্শ নারী বলতে যা বোঝায় ফাতিহা ঠিক তা-ই। সেই কত সম্বন্ধ আসতে শুরু করেছিল ক্লাস সিক্সে ওঠার পর থেকে। আর কর্নেল দুলাভাই তো একেবারে রাজপুত্র। বাঙালি বলেই মনে হতো না। কী গায়ের রং, কী স্বাস্থ্য, সাহেবদের মতো ঈগলনাসা। কী সুখের সংসারই না ছিল ফাতিহার! ফিরোজ যখনই যশোর গেছে পরম এক শান্তি নিয়ে ঢাকা ফিরেছে। ভরভরন্ত সংসার বলতে যা বোঝায়। আর কী আমুদে ছিলেন কর্নেল দুলাভাই। শেষ বার খুব বদরুদ্দীন উমরের কথা বলছিলেন। তাঁর লেখা চোখ খুলে দিয়েছে। ব্রিটেনে থাকা তার ছোটবেলার বন্ধু, নটিংহাম ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়, সে তাকে লিখেছিল এক জার্মান লেখকের কথা মতো, লেখকটার নামই মনে করতে পারছিলেন না তিনি, কথাটা চিঠি থেকে পড়ে শুনিয়েছিলেন তিনি-‘আই থিঙ্ক উই অট টু রিড ওনলি দ্য কাইন্ড অব বুকস দ্যাট উড ওউন্ড অ্যান্ড স্ট্যাব আস। ইফ দ্য বুক উই’আর রিডিং ডাসন্ট ওয়েক আপ আস উইথ অ্যা ব্লো অন হেড, হোয়াট আর উই রিডিং ইট অফ?’ লেখা খেলার জিনিস নয়, লেখা হলো আগুন, যে আগুনে আলো জ্বলে। হঠাৎ করে বলেছিলেন কথাটা একদিন। সেই চোখ দুটো কাফনের কাপড়ে ঢাকা।
সবার ভেতরে থেকে আম্মা এগিয়ে গেলেন। প্রত্যেকটি শব্দ আলাদা আলাদা করে কিন্তু স্পষ্ট করে উচ্চারণে ফাতিহা বলে, ‘আম্মা, আমার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে।’ তখনো ধাঁধা কাটেনি। রাতের এই সময়ে জগতের সবকিছু যেন এক অসহনীয় নীরবতা জমাট কালো বরফ। সেই বরফের চাঁইয়ে এবার প্রথম কুড়ালের ঘা পড়ে। পেছনের গাড়িটা যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে না-কোথা থেকে এগিয়ে আসে তমাল, দুলাভাইয়ের বড় ছেলে। বয়স চৌদ্দ। সে এসে আম্মার কাছে দাঁড়ায়। আম্মা তখনো ফাতিহাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে। তমাল বলে, নানুজান ওই গাড়িতে আব্বুর কফিন। বলে সে আঙুল দিয়ে গাড়িটা দেখায়।
ফিরোজের গায়ে গাছের পাতা বেয়ে মনে হয় অনেকক্ষণ ধরে গোল্লাপাকানো একটা জলের ফোঁটা গালের ওপর পড়ে। তার মনে হল একটা রক্তের গরম ফোঁটা যেন তার গালে পড়েছে। এরপর যত ফোঁটাই গায়ে লেগেছে, মনে হচ্ছে টুপটাপ করে রক্তই পড়ছে।
এ-সময় দশ-বারোজনের মতো লোক নেমে আসে। এর ভেতরে এক ক্যাপ্টেনকে দেখা যায়। প্রত্যেকের গায়ে উর্দি। তাদের কয়েকজন মিলে কফিনটা নামায়। এর ভেতরে একজনের কণ্ঠ চাপা স্বরে বলে, সব লোগ অন্দর চলিয়ে। লোকটার কথায় একেবারে চাবি দেওয়া পুতুলের মতো সবাই পায়ে পায়ে বাড়ির ভেতরে চলে আসে।
বসার ঘরটা অনেক বড়। ছয়জন কফিনটা নিয়ে বসার ঘরের মাঝখানে রাখে।
এতক্ষণে কথা বলেন ফরিদ, কী হয়েছে, কেন হলো। এসবের মানে কী?
ইয়ে এক গাদ্দার হ্যায়। লোকগুলোর মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠে।
ফাতিহাকে এতক্ষণ জড়িয়ে ধরা আম্মাও ভাষাহীন। ফাতিহার পাথর হিম শরীর থেকে শীতলতা যেন আম্মার শরীরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকটা কথায় সেখানে ধাঁ করে আবার একটা কোপ পড়ে। আম্মা যেন সেই কোপে ঝুপ করে কফিনের একটা দাঁড়া ধরে মাটিতে ঝুঁকে পড়তে যাচ্ছিলেন। একটা লোক চট আম্মার দুই বাহু ধরে ফেলে। আম্মা শাড়ির আঁচল মুখে দিয়ে প্রবলভাবে ফুঁপিয়ে ওঠেন। আঁচল মুখে না দিলে হয়তো হু হু শব্দ হতো।
আরেকটা লোক বলে, আপনি কোনো শব্দ করবেন না, কেউ কোনো শব্দ করবেন না। একটা টুঁ শব্দও যেন এই ঘরের বাইরে না যায়। কোনো শব্দ করবেন তো আমরা এই লাশ নিয়ে যাব।
না, রুখে দাঁড়ায় ফাতিহা। ফাতিহার চোখে মুখে তীব্র এক গনগনে আভা ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে কান্নাটান্নার কোনো আভাস নেই। ফাতিহা বলে, আমার স্বামীর লাশ কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। নিতে হলে আমাদের চারজনের লাশও নিয়ে যেতে হবে।
ফরিদ তখন আরো একবার বলে, কী হয়েছিল, কেন হলো এটা?
আমরা কিছু জানি না, একজন সিপাহি বলে, তবে ইনি একজন গাদ্দার। বাড়ির পেছনেই এই মুর্দার দাফন দিতে হবে। যদি না চান তো আমরা আবার ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাব।
কেন? ফিরোজ বলে।
ক্যাপ্টেন বলে, কারণ এর বাইরে কোনো কবরস্থানে এর দাফন করতে চাইলে মার্শাল ল’ কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগবে। আপনি যদি আগামীকাল বিকাল পাঁচটার ভেতরে অনুমতি আনতে পারেন, তাহলে টেলিফোন করে আমাকে জানিয়ে দেবেন। নইলে বিকালে এসে আমরা লাশ ফিরিয়ে নিয়ে যাব। আর যদি কবরস্থানের দাফন করার অনুমতি পান তাহলে আমরাই নিয়ে যাব। কিন্তু বাসার কোনো শব্দ যেন বাইরে না যায়। কান্নাকাটির কোনো শব্দ কেউ করবেন না। মহল্লার লোকজন যেন কোনো খবর না পায়। আর এ নিয়ে কাউকে কিছু জানানো যাবে না।
আনসারুদ্দিন চোস্ত উর্দু বলতে পারতেন। তিনি এবার শান্ত কণ্ঠে উর্দুতে বলে ওঠেন, ইনি মুসলমান। মুসলমান মুর্দার পাশে কোরআন তেলওয়াত করতে হয়। আমি পাশের মসজিদ থেকে দুজন মওলানাকে নিয়ে আসি।
দুজন সিপাহির সঙ্গে আনসারুদ্দিনকে যেতে দেওয়া হয়। অল্পক্ষণ পরেই তিনি দুজন মওলানা নিয়ে ফিরে আসেন।
এসময় সিপাহিদের পক্ষে দুয়েকজন বাঙালি সে রাতে কোনো এক ফাঁকে চুপি চুপি বাড়ির ছোটোছেলে ফয়সলকে বলে, ভয় করবেন না কোনো। আমরা আপনাদের পাশে আছি।
৩.
আজিমপুরের দাফনের অনুমতি আনতে ফিরোজকে কম ঝক্কি পোহাতে হয়নি। বাবার কবরের পাশে মায়ের জন্য জায়গা কিনে রাখা ছিল। সেখানে দুলাভাইয়ের দাফনের কথা। মার্শাল ল’ কর্তৃপক্ষ দাফনের সঙ্গে মাত্র চার পাঁচজন আত্মীয়ের বেশি কাউকে থাকার অনুমতি দেয়নি। আর সঙ্গে তো রাইফেলওয়ালা সিপাহি। গোরস্তানেই জানাজা হয়। সিপাহিরা কেউ জানাজা পড়েনি। আনসারুদ্দিন এবারও উর্দুতে তাদের আহ্বান করে জানাজা পড়ার জন্য।
না, আমরা এর জানাজা পড়তে পারি না। ইনি গাদ্দার। ঠান্ডা গলায় বলে এক সিপাহি।
ইনি গাদ্দার নন, ইনি মুসলমান, একজন সৈয়দ।
বেয়নেট উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে তারা। তাদের চোখমুখে কোনো ভাবলেশ নেই। ওদের ওমন দাঁড়ানোর ভঙ্গি কোনোদিন ভুলবেন না ফিরোজ। আর ফিরোজ কেবলই অবাক হয়েছিলেন আনসারুদ্দিনের সাহস দেখে।
আনসারুদ্দিন পরে তাকে বলেছিলেন, তার কাছে যখন সাহসের কথা জানতে চেয়েছিলেন তিনি, ইমান, মেজো সাহেব। ইমানদারের কোনো ভয় নাই। যার ভয় নাই, তার ক্ষয় নাই। স্বাধীন হতে গেল, মুক্ত হতে চাইলে, জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি চাইলে সাহস লাগে, ইমান লাগে। যে সময় এই কথা হচ্ছিল দেশ তখন স্বাধীন। ফিরোজ সচিবালয় থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেদিন গাড়ি থেকে নেমে দেখেন বৃষ্টি শুরু হয়েছে- ওইদিন রাতের মতো- কর্নেল দুলাভাইকে আনার দিন যেমন পড়ছিল।
আনসারুদ্দিনকে বলেছিল, মনে পড়ে আনসার ভাই, সেদিন রাতে এমন বৃষ্টি ছিল?
সেদিন কি কোনো দিন ভোলা যায়। সোনার মানুষ ছিলেন কর্নেল সাহেব- তাকে এভাবে মারল! সেদিনই আমি বুঝেছিলাম, গাদ্দার তিনি নন, ওরাই গাদ্দার। ধর্মের নামে পাকিস্তান করে আমাদের সঙ্গে কত বড় গাদ্দারিটাই না হয়েছে। ওরাই বেইমান। বেইমানরা কখনো জিততে পারে না।
আনসারুদ্দিন এখন আর বেঁচে নেই। তবু এমন বৃষ্টি পড়লে অনেক কিছুর সঙ্গে তার কথাও মনে পড়ে। বুটের শব্দও তখন কানে এসে লাগে, যদিও সেই শব্দ এখন আর আগের মতো স্পষ্ট নয়।