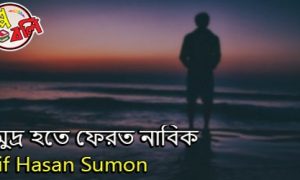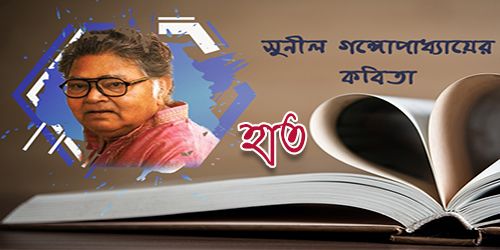বিপাশা বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। ওপাশে রিক। নীল ডিম বাতির আলোয় ওর ফর্সা মুখটা নীলাভ দেখাচ্ছে। ঠোঁটের কোণে লালা। আমি আঙুলের ডগা দিয়ে মুছে দিই। ও একটু নড়ে ওঠে আবার ঘুমায়। জীবনানন্দ দাশের কবিতাটি মনে পড়ে,
বধূ শুয়ে ছিল পাশে – শিশুটিও ছিল;
প্রেম ছিল, আশা ছিল – জ্যোৎসনায়,
আজ চাঁদ ওঠেনি। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার।
সে-রাতেও এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল। অস্বাভাবিক কোনো আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সম্ভবত ভারী কিছু আছড়ে পড়ার শব্দ। খাটে বসে শোনার চেষ্টা করলাম। মায়ের ঘর থেকে পুরুষকণ্ঠের চিৎকার ভেসে আসছে।
আমার ঘরের সামনে কমন সরু প্যাসেজ। প্যাসেজের শেষ মাথায় মায়ের কামরা। মায়ের অর্থাৎ মা এবং তাঁর নতুন স্বামীর।
খুব সাবধানে দরজা খুলে প্যাসেজে গিয়ে দাঁড়ালাম। সবকিছু স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ঝগড়ার কারণ আমি। নতুন বাবা চাচ্ছেন না আমি এ-বাসায় থাকি। মাকে বলছেন আমাকে যেন আমার আসল বাবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমি মায়ের সঙ্গে থাকব না? অকস্মাৎ মনে হলো, কোনো ট্রেন ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেল। ঝিকঝিক ঝিকঝিক। ঘরবাড়ি দুলছে। সীমাহীন কোনো দূরত্ব পর্যন্ত ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত একা আমি। কোথাও কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিনে। এত রাতে কোন ট্রেন হতে পারে! অনেক কষ্টে গলার কাছে উঠে আসা হেঁচকি গিলে নিলাম।
‘আমি বলেছি তো, বিপু আমাকে ছেড়ে কোত্থাও যাবে না।’
প্রতিটা শব্দ মনে হলো মা আলাদাভাবে উচ্চারণ করলেন।
‘তুমি বললেই হলো? এ-বাড়ি আমার। ওই ছেলেসহ তুমি এ-বাড়িতে থাকতে পারবে না।’
লোকটি চিৎকার করল।
‘ঠিক আছে। থাকব না।’
মায়ের কণ্ঠে একদম উত্তেজনা নেই।
আমি জানি এরপর কী ঘটবে। দৌড়ে নিজের ঘরে এলাম। দ্রম্নত বই, কাপড়-চোপড় দলামোচড়া করে স্কুলব্যাগে ঢুকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘড়ঘড় আওয়াজে আমি কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে এলাম। মায়ের বাঁ-হাতে লাল ট্রলি সুটকেস। তিনি অন্য হাতে আমার হাত ধরলেন। কেউ কোনো কথা বললাম না।
ঘর ছেড়ে যখন বেরিয়ে এলাম তখন রাত দুটো প্রায়। নিস্তব্ধ ঘরবাড়ির ফাঁকে সরু গলি। রাস্তা অসমান থাকায় ট্রলি টানতে মায়ের সমস্যা হচ্ছিল। আর ঘড়ঘড় শব্দটিও বড় বেশি কানে লাগছিল। আমার ভয় হচ্ছিল লোকজন দরজা খুলে দেখবে, এই গভীর রাতে মা-ছেলে কোথাও পালিয়ে যাচ্ছি; কিন্তু কেউ এলো না।
গলির মধ্যে এখানে-ওখানে দু-তিনটে কুকুর কু-লী পাকিয়ে ঘুমিয়ে ছিল। ওরা মুখ তুলে আমাদের দেখল। একটা কুকুর কিছুদূর পর্যন্ত আমাদের পেছন পেছন এলো। অন্য কুকুরগুলো কেন এলো না ভাবছিলাম। হয়তো ওরা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। গলি পেরিয়ে তেরো নম্বর স্ট্রিট। সামনে-পেছনে কোনো মানুষ বা যানবাহন দেখা যাচ্ছে না। এমনিতেই এ-এলাকা একটু বেশি নির্জন। কালো পিচের রাস্তা ঝিমঝাম অলস শুয়ে। ডাইভারশনে লাগানো ছোট ছোট গাছের পাতা হালকা নড়ছে। সব নিস্তব্ধতা ভেঙে মায়ের হাতের সুটকেস টানার শব্দই শুধু প্রকট। একটা নির্দিষ্ট তালে ঘড়ঘড়… ঘড়ঘড়…।
স্ট্রিটলাইটগুলো বোধহয় নতুন লাগানো হয়েছে। ঝকঝকে আর উজ্জ্বল। আগে সোডিয়াম আলো ছিল। সবকিছু হলুদ মনে হতো। এই আলোয় আমার আর মায়ের ছায়া খুব লম্বা দেখাচ্ছিল। যেমনটি শেষ বিকেলে দেখা যায়। চুলে খোঁপা করা একজন নারীছায়া, পাশাপাশি তার কাঁধ অবধি হাফপ্যান্ট পরা ঝাঁকড়া চুলের বালক। ছায়ায় সুটকেসটাকে চারকোনা টিনের বাক্সের মতো লাগছে। ছায়াগুলো হেলেদুলে সামনের দিকে এগোচ্ছে।
সে-সময় কেন লাইট, ছায়া এসব নিয়ে চিন্তা হচ্ছিল এ-মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। মনে হয়েছিল আগামীকাল স্কুলে রাতুলের কাছে শুনতে হবে এ-বাতির নাম কী। ওর বাবা সিটি করপোরেশনে চাকরি করে। এ নিয়ে বড়বড় গল্প শোনায়। কী চাকরি জানি না। নিশ্চয় বড় কিছু হবে। যেহেতু রাতুল সিটি করপোরেশনের
স্টিকার-লাগানো ঢাউস এক গাড়ি চড়ে স্কুলে আসত। পরক্ষণে অবশ্য আন্দাজ করলাম, কাল থেকে আর স্কুলে যাওয়া হবে না। আগে যেমন দুটো স্কুল ছেড়েছি।
মায়ের নতুন এই স্বামীর বাসায় আমরা মাত্র ন-মাস ছিলাম। ভদ্রলোক অনেক টাকার মালিক। মা আমাকে নামিদামি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের জন্য একটা গাড়ি ছিল যেটি আমাকে প্রতিদিন স্কুলে পৌঁছে দিত। বাড়ির আসবাব, খাবার সবকিছুই দামি। তবে ভদ্রলোক সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকতেন না। মাঝেমধ্যে আসতেন। যতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন, মাকে তার ঘর থেকে সহসা বের হতে দিতেন না। আমার সঙ্গে সরাসরি তেমন কথা বলতেন না। তবে তার দৃষ্টির মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবহেলা ছিল। তিনি বাড়িতে এলে আমি কুঁকড়ে থাকতাম। একবার কোনো কারণে পাশের বাসার আন্টি মায়ের ওপর রেগে গিয়ে বলেছিলেন,
‘আমি তো স্বামীর একমাত্র বউ, তোমার মতো তিন নম্বর নই। আমি সেদিনই বুঝে গিয়েছিলাম ওই বাসা ভদ্রলোকের আসল বাড়ি নয়।’
খানিকটা হাঁটার পর মা আমার কাছে পরামর্শ নেওয়ার মতো করে জানতে চাইলেন, ‘আজকের রাতটা তোর মামার বাসায় থাকি, কী বলিস?’ আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলাম। মামার বাড়ির প্রতি আমার আগ্রহ ছিল সম্মতি জানাবার সেটা কোনো কারণ নয়। আসলে আমার তখন প্রচ- ঘুম পাচ্ছিল। কাঁধে ছিল স্কুলব্যাগ। ব্যাগটি এমন বড় যে, কাঁধে নিলে প্রায় হাঁটুর কাছে এসে পড়ত। নীল রঙের ব্যাগের ওপর ইংরেজিতে লেখা ছিল উইলসন। বই ছাড়াও ওই ব্যাগে আমার কিছু কাপড়চোপড়, স্টিলের দুটো ছোট্ট গাড়ি, আর একটা পাজল কিউব ছিল। গাড়ি আর পাজল কিউব আমার নিজের বাবার দেওয়া। যখনই আমার মন খারাপ হতো পাজলের নানা ফর্মুলা মেলানোর চেষ্টা করতাম। যদিও এসব ফর্মুলা আমার কাছে খুবই জটিল মনে হতো।
রাত তখন দুটোর বেশি বাজে। রাস্তায় যানবাহন নেই বললেই চলে। আমরা আরো অনেকটা হেঁটে একটা সিএনজিচালিত অটোরিকশা পেলাম। লোকটা খুব বাজে দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকাচ্ছিল; কিন্তু মা পাত্তা দিলেন না। দরদাম না করেই উঠে পড়লেন। মামাবাড়ির সবাই অনেক দেরিতে ঘুমায়। রাত
দুটো-তিনটে যে-কোনো সময় গেলেও কাউকে না কাউকে জেগে থাকতে দেখা যায়। মামা ছাড়া সবাই জেগে ছিল। মামি সাড়ম্বরে মামাকে ডেকে তুললেন,
‘এই ওঠো। দেখো, নিনা আবার বরের বাসা থেকে ভেগে এসেছে।’
মামি সরল ধরনের এবং অত্যধিক কৌতূহলপ্রবণ। সেই ভোররাতে আমাকে ইগলু আইসক্রিম খাইয়ে মামি ভেতরের সব কাহিনি টেনে বের করতে চাইলেন এবং খুব অল্প ইনফরমেশন পেয়ে বেশ হতাশ হলেন!
মামা ঘুমঘুম চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন,
‘সকালে উঠে যেন তোমার মুখ আমাকে না দেখতে হয়।’
দুই
এর আগেও মায়ের হাত ধরে দুবার ঘর ছেড়েছি। প্রথমবার আমার আসল বাবার ঘর, পরেরবার মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর ঘর থেকে। আমার আসল বাবা অন্য বাবাদের মতোই ছিলেন। রাতুল, ইতি, রিশাদের বাবাদের মতো। জড়িয়ে আদর করতেন, কোলে করে দোকানে নিয়ে আইসক্রিম কিনে দিতেন। মা, বাবা, আমি ঘুরতেও যেতাম খুব। শিশুপার্ক, চিড়িয়াখানা। সব জায়গার কথা মনেও নেই। জন্মদিনে কেক কাটা হতো, বেলুন দিয়ে ঘর সাজানো হতো। আমরা তিনজন মিলে গিফট বক্স খুলতাম। কোনোটাতে গাড়ি, কোনো বক্সে বল, রোবট। আমার হাতের তালি ছাপিয়ে বাবা-মায়ের হাসি রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে পড়ত বেশি।
মা এমনিতে খুব কম কথা বলতেন। বাবার সঙ্গে মায়ের কখনো ঝগড়া হতে দেখিনি; কিন্তু একদিন রাতে প্রচ- চেঁচামেচিতে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দেখলাম, মা ঘরের জিনিসপত্র আছড়ে ভাঙছেন। বাবা মুখ নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের বাসায় কাজ করতেন মারজিনা খালা। আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে বললেন, ‘তোমার বাপে লিজা আপারে বিয়া করছে। হ্যার বাবু হইব।’
লিজা আন্টি আমার টিউটর। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমাকে পড়াতে আসে। একদিন মা বাসায় ছিলেন না। আমি লিজা আন্টির কাছে পড়ছিলাম। বাবা এসে বললেন, ‘যাও রিশাদের বাসা থেকে একটু খেলে আসো।’ আমাদের ফ্ল্যাটের উলটোদিকে রিশাদের ফ্ল্যাট। ওদের ঘরে তালা দেওয়া ছিল। আমি ঘরে ফিরে দেখলাম, বাবা লিজা আন্টিকে দেয়ালে চেপে ধরে রেখেছেন। তাঁরা পরস্পরকে চুমু খাচ্ছিলেন। আমি খুব ভয় পেয়ে দৌড়ে মায়ের ঘরে চলে এলাম।
সে-ঘটনার কথা আমি আজ পর্যন্ত কাউকে বলিনি। ঝগড়ার কিছুক্ষণ পর মা লাল রঙের সুটকেস টেনে বেরিয়ে এলেন। তাঁর অন্য হাতে আমার হাত। কেন জানি না, সেদিন আমি আমার স্কুলব্যাগে বই-কাপড়ের সঙ্গে বাবার দেওয়া পাজল কিউব, খেলনা ঢুকিয়ে নিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে মা এগুলো নেড়েচেড়ে দেখতেন। সে-মুহূর্তে মাকে খুব অন্যরকম লাগত। ঢেউহীন স্থির নদীর মতো।
মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর নাম ছিল আবদুল লতিফ। ভদ্রলোকের আগের স্ত্রী মারা গেছেন। তাকে আমার বেশ ভালো লাগত। আমাকে খুব আদর করতেন। ডাকতেন বিপুল বাপজান। অনেকদিন বলেছি, আমার নাম বিপস্নব; কিন্তু তাঁর মতে বিপস্নব নামের মধ্যে যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব আছে বরং বিপুল মানে বিশাল। এটাই সুন্দর। ওই বাড়িতে আমরা তিন বছর ছিলাম। একদিন হুট করে মায়ের সেই স্বামী মারা গেলেন। মা বলেছিলেন হার্ট-অ্যাটাক করেছে। খুব অদ্ভুত ব্যাপার হলো, তিনি মারা গেলে আমার তেমন কষ্ট হলো না যেমনটি আমার নিজের বাবার জন্য হয়, এখন অবধি হয়। কিছুদিন পর আমরা ওই বাসা ছেড়ে এলাম।
আমার আসল বাবার বাসা ছাড়ার পর মা খুব বেশি চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। প্রায়ই মায়ের চেহারায় এমন নারী নেমে আসত যাকে আমি চিনতাম না। আবার কখনো কখনো আমার পাশে শুয়ে নিজের পেট দেখাতেন,
‘জানিস তো বিপু, এই যে পেট দেখছিস না? চোখের মতো দাগ, চাষ করা ক্ষেতের মতো এবড়ো-খেবড়ো। এটাই কিন্তু তোর জন্মভিটে। জন্মভিটে বুঝিস তো? যেখানে শেকড় পুঁতে থাকে, নাড়ির যোগ থাকে। এই ভিটেতেই তুই জন্মেছিস, রক্ত-পানি খেয়ে বড় হয়েছিস, তারপর বাইরের দুনিয়ায় এসেছিস। এই ভিটে না থাকলে তুই বেড়ে উঠতে পারতি বল? গাছের শেকড় দেখা যায়; কিন্তু একে দেখা যায় না, অদৃশ্য থাকে। সেই শেকড় ছেড়ে কোনোদিন চলে যাবিনে তো? এই জন্মভিটে থেকে?’
কখনো বলতে,
‘দেখিস তুই বড় হবি, মস্তবড় চাকরি করবি, তখন আমরা একটা সমুদ্রসৈকত কিনব। তোকে পুতুলের মতো একটা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবো। তোদের আর একটা পুতুল হবে। আমরা সবাই মিলে বালু দিয়ে ঘর বানাব। ঝিনুক নিয়ে খেলব। সবুজ শৈবালের দ্বীপে পা ডুবিয়ে বসব। মনে থাকবে?’
বেশিরভাগ সময় মায়ের এসব কথার মানে আমি বুঝতাম না। তবে কখনো কখনো কথা বলতে গিয়ে মা উদাস হয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতেন। চোখের কোণে চিকচিক করত সন্ধেবাতি।
প্রতিবার নতুন বাবার ঘরে যাওয়ার আগে আমরা একটা ট্রানজিশন পিরিয়ড কাটিয়েছি। এই সময়ে আমাদের জায়গা হতো মামার বাসায়। প্রথমবার প্রায় এক বছর মামার বাসায় ছিলাম। দ্বিতীয়বার ছয় মাসের মতো। সে-সময়ে মা আপ্রাণ চেষ্টা করতেন মামিকে কীভাবে খুশি রাখবেন। রান্নাবান্না ও ঘরের কাজ দৌড়ে দৌড়ে করতেন। মামি অবশ্য আমাদের সঙ্গে কোনোদিন খারাপ ব্যবহার করেননি। তবে মা বলতেন,
‘আমরা অন্য কোথাও চলে যাবো, বুঝেছিস বিপু? তোর মামার আয় তো বেশি নয়। বাড়তি দুজন মানুষের খরচ…।’ কী জানি, এই কারণে মা বারবার বিয়ে করতেন কিনা। আমি ছোট ছিলাম। কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারতাম না; কিন্তু আমিই একমাত্র মায়ের কাছের ছিলাম। এজন্য হয়তো আমাকে শুনিয়ে মা নিজে নিজেই সব ধরনের সিদ্ধান্ত নিতেন।
অন্য যে-দুবার মামাবাড়ি এসেছি, মামা এভাবে কখনো বলেননি। সে-রাতে কেন বললেন জানি না। কেবল চোখদুটো লেগে এসেছিল। মা আমাকে ধাক্কা দিয়ে তুললেন,
‘বিপু ওঠ, বেরোতে হবে।’
চোখ খুলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। তবু ধড়ফড় করে উঠলাম। ব্যাগটা কাঁধে ফেলে মায়ের পিছুপিছু যখন মামার বাসা থেকে বেরিয়ে আসি, তখন রাত আর সকালের সন্ধি-সময়। মামার বাসার সবাই ঘুমুচ্ছে। পাশের মসজিদে নামাজিরা একজন-দুজন করে আসতে শুরু করেছেন কেবল।
তিন
‘আজ রিমি আন্টির বাসায় যাব বুঝলি বিপু। সেখানে মাসখানেক থাকব। তারপর কিছু একটা হবে। এ কদিন বাসায় পড়িস। আগের স্কুলে তো ভর্তি করতে পারব না। সে অনেক খরচ। তোকে আমি নতুন একটা স্কুলে ভর্তি করে দেবো। তবে তোকে খুব মন দিয়ে পড়তে হবে। পড়বি তো বিপু?’
মা জানেন, তিনি যা বলবেন আমি তাই করব। তবু আমার সম্মতি সবসময় যেন দরকার। আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বলি, পড়ব। তবে ভেতরে ভেতরে আমি মূলচ্ছেদের শব্দ শুনি। স্কুল, বন্ধু। ঝাপসা হয় চোখ।
‘বিয়ের পরেও যদি পড়াটা চালিয়ে যেতাম তাহলে এখন আমাদের এ-অবস্থায় পড়তে হতো না। কিছু একটা চাকরি জোগাড় করে ফেলতাম। ইন্টার পাশ করতেই ব্যবসায়ী দেখে তোর মামা বিয়ে দিয়ে দিলো। তোর বাবা বলল, মেয়েদের পড়া দিয়ে কী হবে? ঘরে থাকো, সংসার দেখো। এটাই মেয়েদের কাজ। এরপর তুই এলি আর পড়া হলো না।’ মা একা একা বলতে থাকেন।
রিমি আন্টি মায়ের বান্ধবী। কলেজে একসঙ্গে পড়েছেন। বাড্ডার একদম শেষ প্রামেত্ম লম্বা স্কুলঘরের মতো তার বাসা। অনেকগুলো রুম। রিমি আন্টি আমাদের দেখে ততটা খুশি হলেন না বরং বেজার মুখে খসখসে গলায় বললেন,
‘চলে এসেছিস? এই নিয়ে কটা বর ছাড়লি রে? এত ঘনঘন কেমনে বর বদল করিস কে জানে বাবা! রুচিও বটে!’
রিমি আন্টির কথায় মা কোনো কথা বলছেন না।
‘তোদেরকে কোথায় থাকতে দিই বল তো? দেখছিস তো বাসা কত ছোট। তার ওপর শাশুড়ি থাকেন আমার সঙ্গে। আচ্ছা আয় দেখি।’
আমি আর মা চুপচাপ লম্বা বারান্দা ধরে রিমি আন্টির পেছনে পেছনে হাঁটছি। মায়ের হাতের সুটকেস সড়সড় করে এগোচ্ছে। আমরা বারান্দার প্রামেত্মর একটা বন্ধ দরজার সামনে থামলাম। অনেক কসরত করে রিমি আন্টি মরচেপড়া সিটকিনি খুললেন।
দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বহুকাল ধরে আটকে থাকা বাতাস ঝড়ো বেগে বেরিয়ে গেল। ভ্যাপসা গন্ধ। আবছা আলোয় ঘর দেখে যা বুঝলাম তাতে অনেককাল এ-ঘরে কেউ পা দেয়নি। পুরনো ভরুগা খাট, আলনা, সাইকেল, বাচ্চাদের নানা ধরনের রাজ্যের খেলনা, ঘরের মধ্যে ডাঁই করা। এক কোণে সেমি ডবল খাট। চাদরে থিকথিকে ময়লা। রিমি আন্টি সামান্য বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন,
‘এখানেই কষ্ট করে থাকতে হবে রে। আর শোন, তুই ডিভোর্সি এ-কথা কাউকে বলিস না। আমি বলেছি খুলনা থেকে আমার বান্ধবী বেড়াতে আসবে। বুঝতে তো পারছিস, ডিভোর্সি মহিলাদেরকে কেউ ভালো মনে করে না। আচ্ছা আমি আসছি। তোরা কি নাস্তা করে এসেছিস? নাকি খাবি?’
মা বললেন,
‘না না, খেয়ে এসেছি। সে নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না।’ আমি মায়ের মুখের দিকে তাকাই। আমরা তো কিছু খাইনি। মা চোখ ইশারা করেন।
রিমি আন্টি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর বেশকিছু সময় মা খাটের এক কোণে চুপচাপ বসে ছিলেন। চোখ মেঝের দিকে। আমি দেখলাম টুপটুপ করে পানি পড়ছে মেঝেতে। খানিক বাদে আমাকে বসতে বলে বাইরে গেলেন। ফিরে এলেন বাঁশপাতা রঙের কাগজের ঠোঙা হাতে। আমার মনে আছে, একটা পরোটা আর একটা ডিম ভাজি ছিল ঠোঙায়। আমি এত ক্ষুধার্ত ছিলাম যে, মা খেয়েছিলেন কিনা সেটা আর জানা হয়নি।
মা বলেছিলেন রিমি আন্টির বাসায় একমাস থাকবেন; কিন্তু পাঁচদিন না যেতেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, সেখানে আর থাকা সম্ভব নয়। মা সকালে আমাকে নাস্তা খাইয়ে বেরিয়ে যেতেন। ফিরতেন রাতে। রিমি আন্টির বাসার কাজের মেয়ে দুপুরে আমাকে একটা পেস্নটে ভাত-তরকারি দিয়ে যেত। কখনো কখনো বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতাম রিমি আন্টির পরিবারের সবাই মিলে টেবিলে খাচ্ছে। হাসাহাসি করছে। বিকেলের দিকে আরো কিছু মহিলা বারান্দার ডাইনিং টেবিলে বসে গল্প করছে। কিন্তু আমার মায়ের সঙ্গে কখনো গল্প করতে দেখিনি।
এক ঘর ছেড়ে আসার পর আমি মায়ের নতুন কোনো স্বামীর ঘরে যাওয়ার জন্য মানসিক প্রস্ত্ততি নিতাম, যাদের কেউ আসলে আমার বাবা নয়। এবারো সেভাবেই প্রস্ত্ততি নিয়েছিলাম; কিন্তু বাস্তবে সেটা ঘটল না। একদিন সন্ধ্যায় মা এসে বললেন,
‘আমি একটা বেসরকারি অফিসে চাকরি পেয়েছি বাবা। আমরা এখন থেকে নিজেদের বাসায় থাকব। ভালো হবে না?’
কোথায় বা কী চাকরি কিছু না বুঝলেও নিজেদের বাসায় থাকার কথা জেনে খুশি হয়ে বললাম,
‘খুব ভালো হবে মা।’
রিমি আন্টির বাসা থেকে আমরা যেদিন চলে আসি, সেদিনই আন্টি প্রথম বোধহয় আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন,
‘আবার এসো বাবা।’
আর কখনো রিমি আন্টির বাসায় যাওয়া হয়নি আমার।
চার
বেগুনবাড়ির দিকে কোথাও একটা ফ্ল্যাটে আমরা উঠলাম। ফ্ল্যাটটিতে অনেকগুলো ছোট ছোট রুম ছিল। প্রত্যেক রুমে কয়েকজন করে মেয়ে থাকে। কোনার দিকে সবচেয়ে বড় রুমটিতে আমি আর মা। আসলে ওই বাসাটিও আমাদের ছিল না।
বাসা থেকে হাঁটা দূরত্বে একটা স্কুলে মা আমাকে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। আমার আগের স্কুলগুলো থেকে একদম আলাদা। ক্লাসরুমগুলো অন্ধকার খুপরি ঘরের মতো। স্যার-ম্যাডাম খুব অদ্ভুত আর অন্যরকমভাবে কথা বলতেন। ছেলেরা মেয়েদেরকে নিয়ে অশস্নীল আলাপ করে। অনেকেই স্কুলের পেছনে গিয়ে সিগারেট খায়। খুব কষ্ট হতে লাগল আগের স্কুল আর বন্ধুদের জন্য। তবু মাকে কিছু বললাম না।
আমাদের ফ্ল্যাটের অন্য রুমগুলোতে যে-মেয়েরা থাকত মা তাদের সঙ্গে বেশি কথা বলতেন না। আমাকেও ওইসব রুমের দিকে যেতে নিষেধ করতেন। কিন্তু মা বাসায় না থাকলে আমি চুপিচুপি অনেকদিন গেছি। ওরা আমাকে বলত,
‘এইখানে আইছ ক্যান রাঙা মিয়া? তুমার মা কইলাম পিটাইব।’
ফরসা ছিলাম বলেই হয়তো রাঙা মিয়া বলত। অনেক পরে বুঝেছিলাম ওরা সবাই গার্মেন্টে কাজ করে।
আমাদের পাশের রুমে ছিলেন ফরিদা আন্টি। তিনি একটা স্কুলে পড়াতেন। মায়ের সঙ্গে তার কিছুটা ভাব ছিল। মা সকাল আটটায় বেরিয়ে রাত আটটার দিকে ফিরতেন। আমার টিফিন বলতে প্রতিদিন দু-পিস পাউরুটি আর এক বোতল পানি। এমনিতেই স্কুল থেকে খড়িকাঠের জ্বলন্ত ক্ষুধা নিয়ে ঘরে ফিরতাম, তারপর নিজে ঠিকমতো খাবার নিয়ে খেতে পারতাম না। কখনো কখনো পাতিল থেকে একমুঠো ঠান্ডা ভাত হড়বড় করে গিলে খেতাম। এগুলো এপিটাইজারের কাজ করত আর ক্ষুধার পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়ে দিত। মা ফরিদা আন্টির ওপর দায়িত্ব দিলেন দুপুরে আমাকে খাবার দেবার। ধীরে ধীরে আমার অনেক কাজ ফরিদা আন্টি করে দিতে লাগলেন। কাপড় ধুয়ে দেওয়া, বিকেলের নাস্তা, সন্ধ্যায় পড়া দেখিয়ে দেওয়া ইত্যাদি।
বেশিরভাগ দিন ফরিদা আন্টি দুপুরের খাবারের পর আমাদের ঘরে ঘুমুতেন। আমার দুপুরে ঘুমের অভ্যাস ছিল না। কিন্তু ফরিদা আন্টি একরকম জোর করে তার পাশে শুইয়ে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। এক সময় আমারও ঘুমের অভ্যাস তৈরি হলো।
প্রথম প্রথম ফরিদা আন্টিকে আমার কাছে মায়ের মতোই আর একজন মনে হতো। কিন্তু খেয়াল করলাম, তার স্পর্শ ঠিক মায়ের মতো নয়। খুব অস্বসিত্ম বোধ করতাম। আর কী আশ্চর্য! সেই অস্বসিত্ম একদিন ভালো লাগায় বদলে গেল। আমি বুঝতে শিখলাম, শরীরের আলাদা একটা ভাষা আছে। শেষে এমন হলো, দুপুরের সেই ঘুমের সময়টুকু আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হতে লাগল। নারীশরীরের ইতিবৃত্ত আমি সেই কৈশোরে ফরিদা আন্টির কাছে জেনেছিলাম। সম্ভবত মা কোনো কারণে বিষয়টা বুঝতে পেরেছিলেন। একদিন আড়াল থেকে শুনলাম – মা চাপাস্বরে ফরিদা আন্টিকে বলছেন,
‘ছি, একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে…।’
এর কয়েকদিন পরেই আমরা বেগুনবাড়ি ছেড়ে পূর্ব হাজীপাড়া চলে এলাম। একটা টিনশেডের বাসা। ঝিলের পাশে দেড়খানা রুম। সামনে একচিলতে খোলা জায়গা। দিন-রাত দুদ্দাড় প্রকৃতির হাওয়া খেলে। আমার পছন্দ হলো। গায়ে গায়ে লাগানো গোটাসাতেক এমন টিনশেড। বাসিন্দাদের সকলেই ছাপোষা চাকরিজীবী। খোলা জায়গায় কয়েকটা ফুলের গাছ লাগিয়ে দিলেন মা। একটা নিমগাছ।
প্রায়ই শুনতাম, জায়গার মালিক এই জায়গা ডেভেলপারকে দিয়ে দেবেন। মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং উঠবে এখানে। বাসিন্দাদের সেই নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না। কারণ দশ বছর ধরে তারা এমনটাই নাকি শুনে আসছেন। জমির আসল মালিক বেঁচে থাকলে হয়তো কথাটি ফলে যেত; কিন্তু তিনি অকস্মাৎ কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন, সেও প্রায় সাত-আট বছর হলো। বিধবা স্ত্রী একমাত্র মেয়েকে নিয়ে আমাদের বাড়ি-সংলগ্ন রাস্তার পাশের একটা ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকেন। মা যখন ভাড়া দিতে যান, সঙ্গে দু-একবার গিয়েছি।
নিমগাছের সঙ্গে সঙ্গে আমি বড় হতে থাকি। আমাদের সঙ্গে অন্য আর একটি গাছ বড় হচ্ছিল, যেটিতে একসময় হলুদ হলুদ ফুল ঝুরি হয়ে ঝুলে থাকত। কিছুদিন পর সেগুলো সাদা বর্ণ ধারণ করত। হলুদ ফুলগুলো আমাদের ঘরের সৌন্দর্য বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। মা এই ফুলের নাম বলেছিলেন সোনালু।
পাঁচ
আমাদের সংসার থেকে অতীতের অনেক ঘটনা, অনেক সম্পর্ক ধীরে ধীরে মুছে গিয়েছিল। আমরা নিজেরাই ঘটমান বর্তমানে অবস্থান করে পুরাঘটিত অতীতে ফিরতে বা ভবিষ্যতেও তাকাতে চাইনি। আমি বড় হয়েছিলাম। মায়ের ইচ্ছানুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্সে ভর্তি হলাম। কিন্তু এর কিছুদিন পর আমার জীবনে সে-মেয়েটি এসে গিয়েছিল, যাকে ছাড়া আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ছক মেলা সম্ভব ছিল না। মেয়েটি বাড়িওয়ালি আন্টির মেয়ে বিপাশা।
ওর সঙ্গে পরিচয়ের পেছনে চমকপ্রদ কোনো কাহিনি নেই। মায়ের সঙ্গে ওদের বাড়িতে যাওয়া-আসার কারণে কয়েকবার দেখা হয়েছিল। এরপর রাস্তায় দেখা হলে হাসি বিনিময় ছাড়া তেমন ঘটনা ঘটেনি। তবু কীভাবে কীভাবে যেন আমরা একসময় দেখলাম দুজনের কাছে দুজন সহজ হয়ে গেছি। সেটা আরো বেশি সহজ হলো, যখন ওর মা আমাকে ওর অঙ্ক পড়াটা দেখিয়ে দিতে বললেন। সপ্তাহে তিনদিন সন্ধ্যায় পড়াতাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে বুঝলাম বইয়ের অঙ্কের তুলনায় আমরা পরস্পরের সমীকরণ মেলাতে বেশি আগ্রহী।
পড়ানোর সময় ওর মা কখনো সেই ঘরে আসতেন না। অবাধ স্বাধীনতা। ফলে আমাদের রসায়ন ধীরে ধীরে জমে উঠল। বুঝতে পারলাম, বিপাশা আর আমি যে পরস্পরের দিকে প্রবল বেগে ধাবিত হচ্ছি। ফোনে রাত কাবার করে ফেলতাম দুজনে। সেসব ফোন অবশ্য ইনকামিং ছিল আউটগোয়িং নয়। বাইরেও ঘুরতে গিয়েছি কয়েকবার। ওর সঙ্গে যত বেশি জড়িয়ে পড়ছিলাম, ভেতরে ভেতরে তত বেশি করে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলাম। ওর মায়ের কথা ভেবে নয়, আমার মায়ের কথা ভেবে। মা বিপাশা বা ওর মাকে একদম পছন্দ করতেন না। বলতেন,
‘মা-মেয়ে প্রচ- অহংকারী, ওদের খুব কাছে যাসনে বাবা।’
এই কাছে যাওয়া বলতে কী বুঝিয়েছিলেন সেটা আমি জানি। তবু শেষ রক্ষা হলো না। মন তো এমনই, শরীরও না মানে বাধা না মানে ব্যাকরণ।
সেদিন ভার্সিটি যাইনি। মা চলে গেছেন অফিসে। ভরদুপুরে ফোনে বিপাশার আবদার। ওর হায়ার ম্যাথের প্রবাবিলিটি চ্যাপ্টারটা বুঝিয়ে দিতে হবে। ঘরে ঢুকে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি ভয় পেলাম। এ-চোখ প্রবাবিলিটি নয়, অন্য কিছু ইশারা করছে। বাড়ি মানুষশূন্য। যে-বালকটির শরীরে ফরিদা আন্টি নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন, সে আজ তরুণ। সুতরাং প্রেমিকার আহবানে তার জাগতে সময় লাগেনি। এরপর থেকে মাঝেমধ্যেই আমার ভার্সিটি কামাই হতে লাগল। আর বিপাশার অনেক পড়া বুঝতে বাকি ছিল।
এর মাসদুয়েক পর বিপাশার বাড়িতে একটা নাটক মঞ্চস্থ হলো। আসামি আমি। ফরিয়াদি বিপাশা। বিচারক এবং উকিল উভয় ভূমিকায় ওর মা। আর পর্যবেক্ষক আমার মা। বিচারকের আঙুল ঘূর্ণনে বাতাসে শিস কেটে যাচ্ছিল।
‘অস্বীকার করতে পারবে, ওর পেটের সন্তানের জন্য তুমি দায়ী নও?’
আসামির অধোবদন মুখ দেখে উপস্থিত কারো আর বুঝতে বাকি রইল না যে, অভিযোগ প্রমাণিত।
মা একটা কথাও বললেন না। এক মাসের মধ্যে ধুমধাম করে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। মায়ের সাধ্যমতো সবকিছু করলেন; কিন্তু বদলে তাঁর মুখের হাসিটি আমার কাছ থেকে সযত্নে সরিয়ে নিলেন। টিনশেডের মানুষগুলো সব জানল, সব বুঝল। কেউ কেউ মাকে শুনিয়ে বললেন,
‘চালাক মহিলা, ছেলেকে দিয়ে ঠিকই রাজত্বসহ রাজকন্যা বাগিয়ে নিয়েছে।’
বিয়ের রাতে বিপাশাকে আমাদের টিনশেডে নিয়ে এসেছিলাম। মা তাঁর বড় রুমটি আমাদের জন্য ছেড়ে দিয়ে আমার ছোট রুমে চলে গেলেন; কিন্তু বিপাশা সারারাত ঘুমুতে পারল না। এসি ছাড়া ওর ঘুম আসছে না। ভোরে আমি নিজেই মাকে বলে ওকে ওর বাড়িতে দিয়ে এলাম। সেই যে দিয়ে এলাম আর কোনোদিন ও টিনশেডে ফিরে এলো না।
ধীরে ধীরে আমি শ্বশুরবাড়ির কর্তা বনে গেলাম। বাজারঘাট, বিপাশা, ওর মায়ের ডাক্তার, ওষুধ, পথ্যি এগুলো আমাকে ছাড়া চলে না। শাশুড়ি কানের কাছে এক রেকর্ড চালিয়ে রাখেন,
‘বিপস্নব, এসব সম্পত্তির মালিক তো তোমরাই। আমি আর কতদিন! সব বুঝে নাও।’
কখনো কখনো ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বলেন,
‘তোমার বাবার শখ ছিল বারোতলার বিল্ডিং বানাবেন। লোনের জন্য ব্যাংকের সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। তাঁর সে-স্বপ্ন তোমাকে পূরণ করতে হবে।’
লোন, বাড়ির পস্ন্যান এসব নিয়ে এ-অফিস সে-অফিস, এ-ব্যাংক সে-ব্যাংক করতে গিয়ে বেশিরভাগ সময় ফিরতে রাত। ফিরে আবার সারাদিনের সব ফিরিসিত্ম শোনাতে হয় বিপাশার মাকে। তারপর বিপাশার শরীর ভালো যাচ্ছে না। স্বামী হিসেবে সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেন শাশুড়ি। আমার আর আমার মায়ের কাছে থাকা হয় না। তবে যত রাত হোক মাকে একবার না দেখলে কীভাবে ঘুমাই? মা না খেয়ে জেগে থাকেন। আমি মায়ের সঙ্গে আবার খাই। আমাদের মধ্যে তেমন কোনো কথা হয় না। মাকে একা ঘরে রেখে যখন স্ত্রীর কাছে ফিরে আসি, তখন আমার কাঁধে হাজার মণের বোঝা চেপে বসে। আমাকে কুঁজো বুড়ো করে দেয়। মাকে অনেকবার বিপাশাদের বাড়িতে এসে থাকতে বলেছি; কিন্তু তিনি আসবেন না। আর বিপাশা বা ওর মা না বললে আসবেনই বা কীভাবে?
বিয়ের সাত মাসের মাথায় বিপাশা একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিলো। টিনশেডের মানুষগুলো মুখ টিপে হাসল। এতে অবশ্য আমার মনে দাগ কাটল না; বরং আমার বিয়ের পর এই প্রথম মায়ের হাসিমুখ দেখলাম। হাসপাতালে নাতিকে আমার কোলে দিতে দিতে বললেন, ‘ওর নাম রাখলাম ‘বিস্ময়’। দ্যাখ তুই আবার ফিরে এসেছিস!’
আমি মুচকি হাসি, ‘এভাবেই সবাই ফিরে আসে মা। সবকিছুর পুনরাবৃত্তি ঘটে।’
মায়ের রাখা বিস্ময় নামটি অবশ্য বিপাশা এবং আমার শাশুড়ি দুজনেই নাকচ করে দিলেন। শাশুড়ি তার পছন্দের কোনো এক নায়কের নামে আমার ছেলের নাম রাখলেন ‘রিক’।
ছয়
নাতির কাছাকাছি থাকার জন্য হোক বা বিপাশার মায়ের অনুরোধে হোক মা বিপাশাদের বাড়িতে থাকতে রাজি হলেন। হয়তোবা আমাকে রেখে আর একা থাকতে পারছিলেন না বা আমার মনঃকষ্ট সইতে পারছিলেন না। বয়স হয়েছে। বললাম, ‘এবার চাকরিটা ছাড়ো।’ মা রাজি হলেন না।
আমার অনার্স, মাস্টার্সের রেজাল্ট ভালো হয়েছিল। মায়ের খুব ইচ্ছা ছিল, আমি বিসিএস অফিসার হব; কিন্তু বিপাশা আর ওর মায়ের ঘোর আপত্তি! চাকরি করতে গেলে এই সম্পদ দেখাশোনা করবে কে? বিপাশা জয়ী হলো।
লোন পাশ হলো। বারোতলা বিল্ডিংয়ের পস্ন্যানও রাজউক পাশ করে দিয়েছে। বিপাশা এবং তার মা দুজনেই খুশি। টিনশেড ছেড়ে দেওয়ার জন্য ভাড়াটেকে নোটিশ দিয়ে দিলাম। এর কদিন বাদেই বিল্ডিংয়ের কাজ পুরোদমে শুরু হলো। মায়ের সঙ্গে খুব একটা দেখা হয় না। সকালে ঘুম ভেঙে দেখি আগে, মা অফিসে চলে গেছেন আবার যখন ফিরি মা তখন ঘুমে। তাঁর ছুটির দিনে দু-একটা কথা হয়। কিন্তু কোথায় যেন একটা অসংগতি, এক ধরনের ছন্দপতন। মা বরাবরই অন্তর্মুখী। জীবনে মুখ ফুটে অভিযোগ খুব কমই করেছেন। কতবার বলেছি,
‘মা এখানে তোমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো’? তাঁর এক জবাব, ‘খুব ভালো আছি’। কিন্তু মায়ের মুখের কথা আর চোখের কথার মধ্যে মিল খুঁজে পাই না।
বিপাশার কাছে জানতে চাই,
‘মায়ের কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো? মাকে কখনো হাসতে দেখি না।’
বিপাশা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে,
‘কেন তোমার মা কোনো নালিশ করেছেন বুঝি ছেলের কাছে? তিনি এখানে রাজরানী হয়ে আছেন। এত আরামে জীবনে কোনোদিন ছিলেন তোমার মা? কখনো কোনো কাজে হাত দিতে দেখেছ? শাড়িতে ফুল তুলে বসে থাকেন। হাসবেন কেমনে? মনভরা ঈর্ষা।’
মায়ের ওপর এত ক্ষোভ বিপাশার! কেন? আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম,
‘মায়ের মনে ঈর্ষা? যা বলছ, ভেবে বলছ? কার সঙ্গে ঈর্ষা করবেন?’
‘আমার মায়ের সঙ্গে। আমার সঙ্গে। জীবনে তিনি সুখ পাননি তো, আমাদের সুখ দেখে তাঁর মনে শান্তি চলে গেছে।’
বিপাশার যুক্তির সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না। বুঝতে পারি ভেতরে ভেতরে কিছু চলছে। কিন্তু দুপক্ষ থেকেই কিছু আর জানা হয় না।
সারাদিন লেবার, ইঞ্জিনিয়ার, কন্ট্রাক্টর, সিমেন্ট, রড, এটা-সেটা। নির্মাণাধীন বিল্ডিংয়ের ছোট্ট অফিসটার মধ্যে এসব নিয়ে দেনদরবার চলে সকাল থেকে রাত অবধি। মাস দুই হলো মা চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। প্রতিদিন মনে হয় মায়ের কাছে গিয়ে খানিকটা সময় বসি, গল্প করি; কিন্তু সময়ে কুলোয় না। রাতে মায়ের ঘরে গিয়ে শুধু একবার খোঁজ নিয়ে আসা, সকালে নাস্তার টেবিলে দু-একটা কথা।
ঘরজামাই আর গৃহকর্তার মুখোশে মায়ের বিপু ধীরে ধীরে কোথায় হারিয়ে যেতে লাগল। পুতুলের মতো বউ এলো, তাদের ছোট আর একটা পুতুল হলো; কিন্তু মায়ের আর সমুদ্রসৈকত কেনা হলো না।
আজ সন্ধ্যা থেকে শরীরটা ভালো লাগছিল না। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে অন্ধকার ব্যালকনিতে চুপচাপ বসে ছিলাম। বিপাশা বাইরে কোথাও গিয়েছিল। উলটা পাশের ঘরটি মায়ের। বারান্দায় আলো জ্বলছে। হঠাৎ খেয়াল করলাম, মা রিককে কোলে করে বারান্দায় এলেন। এদিক-ওদিক সন্ত্রস্ত হয়ে তাকাচ্ছেন। তাঁর কাপড়ের ভেতর থেকে একটা চকোলেট বার বের করে রিকের হাতে দিয়ে বললেন,
‘খাও, দাদু তাড়াতাড়ি খাও।’
রিক খুব দ্রম্নত কড়মড় করে চকোলেট খাচ্ছে। আমার ভীষণ হাসি পেল। আবার মায়ের চোরের মতো চাহনি দেখে অবাক হলাম। মা কি কাউকে ভয় পাচ্ছেন? কেন?
একটু পরেই বিপাশা ঝড়ের বেগে বারান্দায় এসে হ্যাঁচকা টানে মায়ের কোল থেকে রিককে ছিনিয়ে নিল। ও চিৎকার করছে,
‘আপনাকে কতদিন নিষেধ করেছি আমার ছেলেকে আপনি কোলে নেবেন না। ওকে এই দেশি চকোলেট দেবেন না?’
‘এটা দেশি চকোলেট নয় মা।’
মা নিজের পক্ষে কিছু সাফাই দিতে যাচ্ছিলেন হয়তো; কিন্তু বিপাশা ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়।
‘থামেন। এ-বাড়িতে কিসের আশায় পড়ে আছেন? আপনার ছেলে ঘরজামাই থাকে। আপনি নন। ছেলেকে বলবেন বৃদ্ধাশ্রমে আপনাকে দিয়ে আসবে। খরচ যা লাগে আমি দেবো।’
বিপাশার এই চেহারা, এই ভেংচির সঙ্গে আমি একদম পরিচিত নই। ওরা কেউ জানে না আমি ঘরে ফিরেছি। মা গ্রিলে মাথা রেখে ন্যুব্জ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। আঁচল দিয়ে ঘনঘন চোখ মুছছেন। হয়তো হেঁচকি উঠছে। আমি স্থবির হয়ে বসে থাকি। বহুদিন আগে বলা মায়ের একটি কথা মনে পড়ে,
‘এই যে পেট দেখছিস না? চোখের মতো দাগ, চাষ করা ক্ষেতের মতো এবড়ো-খেবড়ো। এটাই কিন্তু তোর জন্মভিটে।’
আমি আমার জন্মভিটের দিকে চেয়ে থাকি, নিজেকে সেই ভিটে থেকে উন্মূল হতে দেখি।
সাত
মা মা করে ঘুমের মধ্যে কেঁদে ওঠে রিক। আমার ভাবনার সুতো কেটে যায়।
‘বাবা, আমার সোনা কাঁদে না, এই যে তোমার মা।’
আমি উঠে ওকে থামানোর আগেই বিপাশা ছেলেকে টেনে বুকের ভেতর নিয়েছে। মা-ছেলের এই ছোট্ট সংলাপটুকু আমার মনের গহিনে ঝড় তোলে। আমি ওদের দিকে আবার তাকাই। রিকের ক্ষুদ্র শরীরটা মায়ের শরীরের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। এই রিকের মতো ছোট্ট কি আমি কখনো ছিলাম? আর মা?
ঘরের এক কোণে সেগুন কাঠের বিশাল আলমারি। ওর একটা তাক আমার, একটা রিকের, বাকিগুলো বিপাশার জন্য বরাদ্দ। আমি বিছানা ছেড়ে উঠে আলমারির কাছে যাই। তারপর খুব সাবধানে নিঃশব্দে আলমারির পালস্না খুলে ফেলি। একদম নিচের তাকের এক কোণে আমার সে-ব্যাগটি। রংচটা। উইলসন লেখাটি ভালো বোঝা যায় না। একটা চেইন নষ্ট। সেখানে মা সেলাই করে আটকে দিয়েছিলেন। ব্যাগটা বিপাশা অনেকবার ফেলে দিতে চেয়েছে, আমি ফেলতে দিইনি। হালকা নীলাভ আলোয় ভালো দেখা যাচ্ছে না। তবু চেইন খুলে হাতড়ে পাজল কিউব আর স্টিলের ছোট্ট গাড়িদুটো স্পর্শ করি। দুটো প্যান্ট, দুটো শার্ট সেই ছোটবেলার মতো দলামোচড়া করে ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে নিই।
কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসি, তখন বুকের ভেতর চাপ চাপ ব্যথা। কিন্তু বিপাশা বা রিক কারো দিকেই আর তাকাই না। বারান্দার শেষপ্রামেত্ম মায়ের ঘর। মা কখনো দরজা বন্ধ করেন না। আমিই নিষেধ করেছি। প্রতি রাতে মায়ের ঘরে একবার এসে দেখে যাই। নাকের কাছে হাত দিয়ে পরখ করি। আজো দরজা ভেজানো ছিল। আমি আলগোছে দরজাটির পালস্না খুলে ভেতরে উঁকি দিই। খাটের এক কোণে বসে আছেন মা। মাথা নিচু। পাশে সেই লাল সুটকেসটি, যদিও রংটি এখন আর ভালো করে চেনা যায় না। মায়ের চোখ মেঝের দিকে। একদিন রিমি আন্টির বাসায় ঠিক যেভাবে বসেছিলেন। মেঝেতে কি টুপটুপ করে পানি পড়ছে? সবুজ রঙের আবছা আলোয় বুঝতে পারি না। আমি কিছু বলি না। শুধু একহাতে সুটকেস আর অন্য হাতে মায়ের হাতটা শক্ত মুঠো করে ধরি। মা কিছুটা ইতস্তত করেন। হয়তো কিছু বলতে চাচ্ছিলেন; কিন্তু পারলেন না। কলের পুতুলের মতো ছেলের হাত ধরে উঠে এলেন।
নিস্তরঙ্গে ডুবে থাকা রাত ভেদ করে দূরের কোনো বাসা থেকে গান ভেসে আসছে,
‘যাক যা গেছে তা যাক না’…!
পিচ উঠে যাওয়া এবড়ো-খেবড়ো গলিপথ। সুটকেসের ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বড় বেশি কানে লাগছে। হয়তো পাড়ার মানুষ জেগে যাবে। ওরা দেখবে এই গভীর রাতে মা-ছেলে ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে; কিন্তু কেউ এলো না। আমরা কেউ কোনো কথা বলছি না। রাস্তায় গোটা দু-তিন কুকুর শুয়ে ছিল। ওরা মুখ উঁচু করে আমাদের দেখল। তবে কেউ পিছু নিল না। সেদিনের মতো আজ অবশ্য আমি সে নিয়ে কিছু ভাবলাম না।
মেইন রোডে এসে এক মুহূর্ত ভেবে আমি ডানে মোড় নিলাম। মা কিছু বললেন না। স্ট্রিট লাইটের উজ্জ্বল আলোয় আমার আর মায়ের ছায়া খুব লম্বা দেখাচ্ছে, যেমনটি শেষ বিকেলে দেখা যায়। হাফ হাতা শার্ট পরা ঝাঁকড়া চুলের একজন স্বাস্থ্যবান যুবকের ছায়া, পাশাপাশি তার কাঁধ অবধি ঘোমটা-মাথায় একজন নারীর ছায়া। ছায়ায় সুটকেসটাকে চারকোনা টিনের বাক্সের মতো লাগছে। ছায়াগুলো হেলেদুলে সামনের দিকে এগোচ্ছে। রাস্তায় কোনো জনমানবের চিহ্ন নেই। ডাইভারশনে লাগানো গাছগুলো ঝিরঝিরে বাতাসে হালকা নড়ছে। সুনসান রাতে একটা শব্দই ধীরে ধীরে প্রকট থেকে প্রকটতর হয়, ঘড়ঘড়… ঘড়ঘড়… ঘড়ঘড়…।