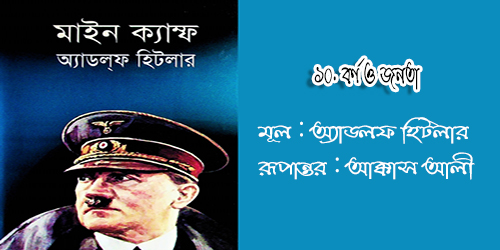১০. বর্ণ ও জনতা
কতগুলি সত্য আছে যা মানুষের পথের ধারে এমন সহজভাবে ছড়িয়ে থাকে যে তা প্রতিটি পথিকেরই চোখে পড়ে। কিন্তু তাদের সর্বদাই দেখা যায় বলেই মানুষ সেই সব সত্যগুলোকে বুঝতে বা তাদের বিশেষ বিষয়বস্তু বলে গণ্য করতে চায় না। সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনের কতগুলো অতি সরল ও সাধারণ ঘটনা সম্বন্ধে এমনি অবহিত যে যখন কেউ সেই বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষন করে তখন আশ্চর্য হয়ে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কলম্বাস ও ডিমের ঘটনাটার উল্লেখ করা যায়। ঘটনাটি খুবই সহজ, সকলেই তা জানে। কিন্তু কলম্বাসের মত পর্যবেক্ষক সত্যই বিরল।
প্রকৃতির বাগানে বেড়াতে বেড়াতে অনেকে অহংকারের সঙ্গে ভাবে তারা প্রকৃতির সবকিছু জেনে গেছে। কিন্তু তাদের কেউ-ই প্রকৃতির জগতের এক বিশেষ নীতির কথা জানে না। সে নীতি হল এ যে জগতের সকল জীবন্ত প্রাণীর মধ্যেই এক বিচ্ছিন্নতাবোধ নিহিত আছে।
এ নিয়মের বশেই প্রতিটি প্রাণী তার আপন জীবন বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ থেকে তার প্রজাতি বৃদ্ধি করে চলে। প্রতিটি প্রাণী তার স্বজাতীয় স্ত্রী প্রাণীর সঙ্গে সহবাস করে থাকে। যেমন ঘরের ইঁদুর কখনো মেঠো ইঁদুরের সঙ্গে সহবাস করে না। সে কাজে তার একমাত্র সঙ্গী ঘরের ইঁদুর। নেকড়ের স্ত্রী নেকড়ের সঙ্গেই সহবাস করে।
একমাত্র বিশেষ অবস্থার বশেই প্রাণীরা এ যৌন প্রকৃতির নিয়ম হতে বিচ্যুত হতে বাধ্য হয়। কোন জায়গায় বন্দী থাকাকালীন অথবা যখন স্বজাতীয় প্রাণীর সঙ্গে কোনক্রমে সহবাস সম্ভবপর হয় না, তখনি কোন প্রাণী ভিন্ন জাতীয় প্রাণীর সঙ্গে বাধ্য হয়ে সহবাস করে থাকে। কিন্তু এ ধরনের সহবাস প্রকৃতি ঘৃণা করে এবং এর বিরুদ্ধে প্রকৃতির নীরব প্রতিবাদ বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে পরিব্যাপ্ত হয়। যেমন ভিন্ন জাতির দুই প্রাণী হতে উৎপন্ন বর্ণসংকর কোন প্রাণী সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে প্রজনন ক্ষমতা হতে বঞ্চিত। এ বর্ণসংকর কোন প্রাণীর অনেক রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা ও বহিরাক্রমণ হতেও আত্মরক্ষার ক্ষমতায় বঞ্চিত হয়।
প্রকৃতির এ বিধান খুবই যুক্তসঙ্গত। দুটি অসম স্তরভুক্ত ভিন্নজাতীয় প্রাণী তার পিতামাতার থেকে কিছুটা উন্নত হলেও তাদের থেকে উন্নত কোন প্রাণীর আক্রমণে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। এ কারণেই ভিন্ন জাতীয় দুই প্রাণীর সহবাস প্রাণধারার নির্বাচন যুক্ত বিবর্তন সম্পর্কিত প্রকৃতির ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধী; বলবান প্রাণীও দুর্বল দুই ভিন্ন জাতীয় প্রাণীর মিলন প্রাণের উন্নত বিবর্তনধারার পরিপন্থী। কারণ এসব সহবাসের ক্ষেত্রে বলবান প্রাণীকে কিছুটা নতি স্বীকার করতে হয় এবং এ মিল হতে যে প্রজাতির জন্ম হয়, তার প্রকৃতি ও মান দুর্বল হয়। সুতরাং এক অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা প্রাণের বিবর্তনধারাটা নিয়ন্ত্রণ না হলে জৈব জীবনের উন্নয়নমূলক বিবর্তন মোটেই সম্ভব হত না।
অমিশ্রিত রক্তবিশিষ্ট অর্থাৎ সমজাতীয় দুই প্রাণীর মিলনের এ নীতিটি তাই প্রকৃতি জগতের সর্বত্র পালিত হয়, এবং এ মিলনের ফলে যে প্রাণীর জন্ম হয় তা শুধু দেহগত আকৃতি নয়, চরিত্র ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অন্য জাতীয় প্রাণী হতে সম্পূর্ণ পৃথক হয়। শেয়াল ও বাঘের চরিত্র কখনো কি এক হবে? তাদের জাতীয় চরিত্র ভিন্ন থাকবেই। শেয়াল কখনো রাজহাঁসের প্রতি আর বিড়াল কখনো ইঁদুরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হতে পারে না।
প্রকৃতি আবার প্রতিটি জাতির জীবনধারাকে উন্নত করার জন্য প্রতিটি জাতির প্রাণীদের মধ্যে ক্ষুধা ও প্রেমগত প্রতিযোগীতা ও জীবন সংগ্রামের এক তাগিদ সঞ্চারিত করে দিয়েছে। দৈনন্দিন জীবিকার্জন ও স্ত্রী প্রাণীদের ওপর অধিকার ও কর্তৃত্ব নিয়ে সমজাতীয় প্রাণীরা ঝগড়া ও সংগ্রাম করে পরস্পরের মধ্যে। সংগ্রামে বলবানরাই প্রাধান্য লাভ করে দুর্বলের ওপর।
তা’ যদি না হত তবে বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীদের উন্নতির বা বিবর্তনের ধারাটা বন্ধ হয়ে যেত একেবারে। তাহলে অগ্রগতির পরিবর্তে শুরু হত পশ্চাদ্গতি। প্রাণীদের মধ্যে যারা দুর্বল, যারা অযোগ্য, তারা সংখ্যায় বেশি। তারা যদি অবাধে যা ইচ্ছেমত বংশবৃদ্ধি করে যেতে পারে তাহলে সব জাতির প্রাণীর মধ্যে অযোগ্য ও দুর্বলের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তাদের মধ্যে ভাল গুণগুলো কমে যাবে। তাই অযোগ্য ও দুর্বলদের সংখ্যাকে সীমায়িত ও তাদের অবাধ বংশবৃদ্ধিকে খর্ব করার জন্য প্রকৃতি এমন এক কঠোর নির্বাচনমূলক নীতি ও নিয়মের প্রবর্তন করেছে, যার ফলে প্রজননের ক্ষেত্রে অযোগ্য ও দুর্বলদের সব সময় স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমানদের কাছে নতি স্বীকার করে চলতেই হবে।
|||||||||| প্রকৃতির রাজ্যে এ নিয়ম যদি প্রতিষ্ঠিত না থাকত, যদি যোগ্য-অযোগ্য, দুর্বল ও শক্তিমান অবাধে সহজভাবে মেলামেশা করত, তাহলে প্রকৃতি শত শত হাজার হাজার বছর ধরে সকল জাতির প্রাণীর বংশধারাটিকে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে উর্ধ্বতন স্তরের দিকে নিয়ে যাবার যে প্রমাণ পাচ্ছে, সে প্রমাণ ব্যর্থ হয়ে যেত।
ইতিহাসের মধ্যে এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যার মধ্যে এ প্রকৃতির নিয়মটি অভ্রান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাসে দেখা যায় যে আর্যরা একদিন এক উন্নত ধরনের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিল, সেই আর্যদের রক্ত যখন নিকৃষ্ট জাতির রক্তের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়, তখন তাদের পতন ঘটতে থাকে। উত্তর আমেরিকার অধিবাসীরা ছিল প্রধানত টিউটন জাতীয়। কিন্তু তারা যখন নিকৃষ্ট জাতির লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে থাকে তখন তারা মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীদের থেকে পৃথক হয়ে পড়ে, এবং তাদের সভ্যতার মান কমে যায়। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার লাতিন জাতীয় অধিবাসীরা আবার অদিবাসীদের রক্তের সঙ্গে তাদের রক্ত বহু পরিমাণে মিলিয়ে ফেলে। বিভিন্ন জাতির রক্তগত সংমিশ্রনের ফল কি হতে পারে তা আমরা এ দৃষ্টান্ত থেকে বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু উত্তর আমেরিকার নিউটনজাতীয় যেসব লোকেরা তাদের জাতিগত সত্তা ও রক্তের পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়, যারা তাদের রক্তকে অন্য জাতির রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেনি, তারাই সমগ্র আমেরিকার ওপর কর্তৃত্ব করতে থাকে এবং তাদের রক্ত সংমিশ্রিত বা দূষিত না হওয়া পর্যন্ত তারা এভাবে প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব করে যাবে।
জাতিগত সংমিশ্রণের কুফল সাধারণত দু’ভাবে দেখা যেতে পারে;
(ক) উৎকৃষ্ট জাতির গুণগত মান কমে যায়;
(খ) তাদের দৈহিক ও মানসিক ক্রমাবনতির জন্য তাদের প্রাণশক্তি কমে গিয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে।
জাতিগত রক্তের এ দুষণ ক্রিয়া পরম স্রষ্টার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক ঘোরতর পাপ এবং এ পাপের ফলভোগ করতেই হবে।
মানুষের এ কাজ যেসব নীতির ওপর তার অস্তিত্ব নির্ভর করে, সেইসব নীতির বিরুদ্ধে সংঘাতে প্রবৃত্ত করে তোলে তাকে। এভাবে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ করে সে নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনে।
এ বিষয়ে ইহুদি ও আধুনিক শান্তিবাদীদের কাছ থেকে এক ঔদ্ধতামূলক আপত্তির সম্মুখীন হই। তারা বলেন, মানুষ প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করতে পারে। ইহুদীদের অনুসরণ করে বহু লোক এ ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে যে তারা প্রকৃতিকে জয় করতে পেরেছে। কিন্তু এটি শুধু তাদের এ বিপজ্জনক ধারণামাত্র। কারণ তাদের এ বিপদজনক ধারণাটাকে যদি সকলে স্বীকৃতি দান করে তাহলে জগতের অস্তিত্বই একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
আসল কথা এ যে মানুষ প্রকৃতিকে যে কোন ক্ষেত্রে জয় করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃতি যে বিশাল অবগুণ্ঠন বা আবরনের দ্বারা তারা অন্তর্নিহিত গোপন রহস্যগুলোকে অনন্তকাল ধরে ঢেকে রেখেছে, মানুষ শুধু সেই অবগুণ্ঠনের সামান্য এক অংশমাত্র অপসারিত করতে পেরেছে। মানুষ কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। সে শুধু কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম। মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে পারে না, তারা শুধু সেই সব প্রাণীদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পেরেছে যারা প্রকৃতির নিয়ম কানুন ও রহস্যের গভীরে প্রবেশ করার মত উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন করতে পারেনি। যে কোন ভাব বা ধারণার জন্ম হয় মানুষের মনের মধ্যে। তাই মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য যে সব ঘটনা অত্যাবশ্যক, সেই ঘটনাগুলিকে কোন ভাব বা ধারণা কখনো ধ্বংস করতে পারে না। মানুষকে দিয়ে কোন ভাব বা ধারণা কখনো জন্মলাভ করতে পারে না। সুতরাং যে কোন ভাব বা ধারণা মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অবশ্যই সেই ঘটনাগুলোর ওপরে নির্ভরশীল হবে।
শুধু তাই নয়। কতগুলো ভাব বা ধারণা আবার কতগুলো মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিশেষ করে যেসব ভাব বা ধারণা একান্তভাবে অনুভূতি সম্পন্ন। যেগুলো বস্তু সাপেক্ষ বৈজ্ঞানিক সত্য হতে উদ্ভূত নয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে একথা সমধিক প্রযোজ্য। অনেকে বলে এ সব ভাবগুলো নাকি মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনের প্রতিফলন। তাদের মত এসব আত্মগত ভাবগুলোর নীরস যুক্তিতর্কের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। এগুলো মানুষের নৈতিক ধারণার প্রকাশ মাত্র। তারা আরও বলে মানুষের অন্তরে সৃষ্টিশীল শক্তিই এ সব ভাবগুলোর উত্স। বিশেষ তাবধারা বা ধারণাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সেই বিশেষ জাতিকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ; যদি কেউ মনে করে শান্তিবাদী ভাবধারার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, তাহলে তাকে জার্মান জাতির বিশ্বজয়ে সর্বপ্রকার যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত। এর উল্টোটা হলে সমগ্র জার্মান জাতির সঙ্গে সব শান্তিবাদীদেরও মরতে হবে। আমি একথা বলছি কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের জার্মান জাতি এ ভাবধারার অধীন হয়ে পড়ে। কেউ যদি শান্তিবাদী আদর্শে দীক্ষিত হতে চায় তাকে তবে যুদ্ধের কথা একেবারেই ভুলে যেতে হবে। আমেরিকার বিশ্ব-সংস্কারপন্থী নেতা উড়া উইলসনের এ ধরনের এক পরিকল্পনা ছিল। এ আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে আমাদের দেশের অধিবাসীরাও ভাবত এ পরিকল্পনার মাধ্যমেই তারা তাদের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবে।
শান্তিবাদ ও মানবতাবাদ এক উক্তৃষ্ট ভাবাদর্শ হিসেবে বিবেচিত হবে সেইদিন, যেদিন মানুষ পৃথিবীতে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করবে এবং সেই মনুষ্যত্ব এক অবিসম্বাদী প্রাধান্য বিস্তার করবে সারা বিশ্বে। কিন্তু কেউ যদি অপরিণামদিৰ্শতার বশে এ ভাবাদর্শ জোর করে কারোর ওপর চাপাতে চায়, তবে তা ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে বাধ্য। তাই চাই আগে যুদ্ধ, তারপরে শান্তি। যদি তা না হয় তাহলে বুঝতে হবে মানুষ আগেই উন্নতির সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে। অপরিণামদর্শিতার বশে এ ভাবধারা চালিত করলে নৈতিক আদর্শ এবং প্রাধান্য স্থিতি হবে না; বরং মানুষ নিচুস্তরে নেমে যাবে। আর তার ফলে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে সারা বিশ্বে। এ কথায় অনেকে হয়ত হাসতে পারে। আমাদের এ পৃথিবীর মানুষ আমাদের আগে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মহাশূন্যে একা একা ঘুরে চলেছিল। ভবিষ্যতে কোনদিন আবার হয়ত তাকে সেভাবে জনমানবশূন্য অবস্থায় ঘুরতে হবে, যদি মানুষ একথা ভুলে যায় যে স্বপ্নপ্রবণ অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিত্বের ভাবধারাকে ভিত্তি করে নয়, প্রকৃতির নিয়ম কঠোরভাবে মেনে তবেই মানুষ বড় হতে পারে; যে কোন জায়গায় তারা তাদের অস্তিত্বকে সমৃদ্ধ ও মহান করে তুলতে পারে।
আমরা সারা বিশ্বের বিজ্ঞান, কলা ও কারিগরী বিদ্যার যে সব আবিষ্কার ও উন্নতির প্রশংসা করি তা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের সৃষ্টিশীল প্রতিভার ফল। জাতিগত ভিন্নতা সত্বেও এসব প্রতিভাবান ব্যক্তিরা বুদ্ধিগত যোগ্যতার দিক থেকে যেন একই জাতীয়। মানব সভ্যতার অস্তিত্ব আসলে এসব প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের ওপরেই নির্ভরশীল। এসব ব্যক্তিত্বের ধ্বংস হলে পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর তা’ সব তাদের সঙ্গে চলে যাবে ধ্বংসের সমাধিগহ্বরে।
কোন দেশের ভূ-প্রকৃতির প্রভাব যতই বেশি হোক সে প্রভাব নির্ভর করে সে দেশের অধিবাসীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের ওপরে। কোন দেশের ভূমির পরিমাণ কম হলে সে দেশের মানুষেরা খুব পরিশ্রমী হয়, ভূমির অভাব অন্যদিক থেকে পুরণের চেষ্টা করে। আবার কোন কোন দেশে দেখা যায় ভূমির অভাবের ফলে সে দেশের লোকেরা চরিত্র হারিয়ে ফেলে এবং স্বাভাবিকভাবেই অপুষ্টি প্রভৃতি দারিদ্র্যগত কুফলগুলোয় ভুগতে থাকে। সুতরাং কোন দেশের অধিবাসীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যই পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশ প্রভাবের গতি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। কোন দেশের ভূমির ঘাটতি জাতিকে দারিদ্রতা ও অনশনের পথে ঠেলে দেয়, আবার অন্য এক জাতিকে কঠোর পরিশ্রমের পথে নিয়ে যায়।
অতীতের বড় বড় সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হল প্রতিভাবান শ্রেণীর রক্তে সংমিশ্রণ ও দূষণের ফলে অবনতি ঘটে এবং তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।
এ সব ধ্বংসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তখনকার মানুষ একটা কথা ভুলে গিয়েছিল; ভুলে গিয়েছিল সকল সভ্যতা ও সংস্কৃতি সেইসব মানুষের ওপরে নির্ভরশীল যারা সেই সব সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্রষ্টা। সুতরাং কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাদের স্রষ্টাদেরও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এ বাঁচিয়ে রাখার নীতির সঙ্গে আর একটা অমোঘ নীতি জড়িয়ে আছে, সে নীতি হল এ যে যারা অধিকতর শক্তিমান ও যোগ্যতম তাদের প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা স্বীকার করতেই হবে। তাদের বেঁচে থাকার অধিকার দিতেই হবে।
এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে লড়াই করতে হবে। যে পৃথিবীতে নিরন্তর সংগ্রামই জীবনের নীতি ও নিয়ম, সেই পৃথিবীতে কেউ যদি লড়াই করতে না চায়, তার বেঁচে থাকার কোন অধিকারই নেই।
একথা রূঢ় শোনালেও প্রকৃত অবস্থা এটাই। তবে তাদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে ওঠে যারা প্রকৃতিকে জয় করার দম্ভ দেখিয়ে প্রকৃতিকে অপমান করে। ফলে তাদের ভাগ্যে ঘটে অশেষ দুঃখকষ্ট।
বিভিন্ন জাতির রক্তগত প্রকৃতিক নিয়মকে কেউ যদি উপেক্ষা বা ঘৃণা করে তাহলে সম্ভাব্য সুখ থেকে বঞ্চিত করবে নিজেকে। যোগ্যতম ব্যক্তিত্বের জয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করে এ ধরনের ব্যক্তিরা সমগ্রভাবে মানবজাতির উন্নতির পক্ষে আবশ্যকীয় বস্তুগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। মানবতাবাদের এবং ভাবালুতার বশবর্তী হয়ে তারা আবার মানুষের স্তরে নিজেদের নামিয়ে নিয়ে যায়, যারা ভেবেছিল নিজেদের তুলে নিয়ে যেতে পারবে না কোন উন্নতির স্তরে।
মানবজাতির প্রথম সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক কারা ছিল এবং তারা কোন জাতিভুক্ত ছিল, সেকথা আলোচনা অর্থহীন। আজ আমরা মনুষ্যত্ব বলতে যা বুঝি, আমাদের সে ধারণা একদিন তারাই বপন করেছিল আমাদের মনে। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আজ খুব সহজ। সভ্যতার আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানব সংস্কৃতির যেসব বিচিত্র বিকাশ ঘটেছে, আমরা আজ বিজ্ঞান, কলা, কারিগরী বিদ্যার যেসব অভাবনীয় উন্নতি চোখের সামনে দেখতে পাই, তা নিঃসন্দেহে আর্যদের সৃষ্টিশক্তিরই ফল। এ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে একমাত্র আর্যরাই এক উন্নত ধরনের মুনষ্যত্ব বোধকে প্রতিষ্ঠিত করে। আমরা আজ প্রকৃত মানুষ বলতে যা বুঝি সে ধারণা তাদেরই সৃষ্টি। আর্যরা হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির সেই প্রমিথিউস যার জ্বলন্ত জযুগল হতে আসে অলৌকিক প্রতিভার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সেই সব অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্ঞান বিকাশের বিচিত্র অনেক রূপ ধরে সর্বব্যাপি অজ্ঞতার রহস্যময় অন্ধকার অপসারিত করে। এ আলোই মানুষকে প্রথম উন্নতির পথ দেখায় এবং পৃথিবীর অন্য সব প্রাণীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সহায়তা করে। সেই আর্যরা যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে আবার সেই অজ্ঞতার গভীর অন্ধকার নেমে এসে পরিব্যপ্ত করে ফেলবে সমস্ত পৃথিবীতে। কয়েক হাজার বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাবে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। মরুভূমি হয়ে পড়বে সারা বিশ্ব।
সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা, সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এবং সংস্কৃতির ধ্বংসকর্তা— এ তিন শ্রেণীতে যদি সমগ্র মানবজাতিকে ভাগ করা হয় তাহলে আর্যরা অবশ্যই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত হবে। এ আর্যরাই মানব সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি রচনা করে। তার ওপরে তার প্রতিটি স্তম্ভ ও কাঠামো করে। শুধু বিশ্বের বিভিন্ন জাতি তাদের আপন আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে সংস্কৃতির সেই কাঠামোতে রঙ ও রূপ দান করে। এ আর্যরাই মানবজাতীর উন্নত সৌধ রচনার উপযুক্ত পরিকল্পনা ও মাল মসলা সরবরাহ করে। বিভিন্ন জাতি তাদের আপন আপন মান অনুসারে এক একটা বিশেষ পদ্ধতিতে সেই উন্নতির সৌধ রচনা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে কয়েক দশকের মধ্যে সমগ্র পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীরা একটি সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করে সেই সংস্কৃতিকে নিজেদের বলে অভিহিত করে। আসলে কিন্তু আমরা জানি এ সংস্কৃতির ভিত্তি গ্রীকদের রচিত এবং তা তাদের কলাকৌশলের সৃষ্টি। শুধু সেই সংস্কৃতিটির বহিরঙ্গটি অন্তত কিছু পরিমাণে এশিয়ার জাতিগুলোর নিজস্ব অর্থরেখার সৃষ্টি। অনেকে বলে থাকে যে জাপান তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু বাস্তবে জাপান ইউরোপীয় সংস্কৃতি, জ্ঞানবিজ্ঞান ও তার প্রয়োগ পদ্ধতিকে পুরোপুরি গ্রহণ করে তার ওপর আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্যের রঙ দিয়ে সেগুলোকে অলংকৃত করে। জাপানের জাতীয় জীবনের বহিরঙ্গটিতে তার নিজস্ব সংস্কৃতির কিছু নিদর্শন থাকলেও তার বর্তমান জাতীয় জীবনের আপন ভিত্তিটির সঙ্গে কিন্তু তার নিজস্ব দেশীয় সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক নেই। জাপানের সমসাময়িক জীবন-ধারার বাস্তব রূপটি ইউরোপীয় ও আমেরিকান জ্ঞান বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির খাতেই বয়ে চলেছে। এ সংস্কৃতি হল মূলত আর্য সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের সুফলগুলোকে তাদের উন্নতির মূল ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করার ফলেই প্রাচ্যের জাতি আধুনিক বিশ্বের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে; ইউরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিদ্যার উজ্জ্বল কৃতিত্বগুলোকে ভিত্তি করেই প্রাচ্যের জাতিগুলোর দৈনন্দিন জীবন সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের জাতিগুলোর জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার জোগায়। তবে সেই সব হাতিয়ারের বহিরঙ্গটি জাপানীদের জীবন যাত্রার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে ধীরে ধীরে।
জাপানের ওপর এ আর্য সংস্কৃতির প্রভাব স্তব্ধ হয়ে যাবে যদি ইউরোপ আমেরিকা অকস্মাৎ ধ্বংস হয়ে যায়। তাতে জাপানের উন্নতির স্রোতটা মাত্র কয়েক দশক অব্যাহত থাকবে, পরে শুকিয়ে যাবে একেবারে। তাহলে জাপানের প্রাচীন স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য লাভ করবে এবং বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি সেই বিদ্যার জড়তার মধ্যে স্তরীভূত হয়ে পড়বে। আজ হতে কুড়ি বছর আগে যে দ্রিা থেকে একদিন অপসংস্কৃতির ডাকে তারা জেগে উঠেছিল। সুতরাং আমরা এ সিদ্ধান্তে যেতে পারি যে জাপানের বর্তমান। উন্নতির ধারাটা যেমন জনপ্রভাব থেকে উৎসারিত, তেমনি তার প্রাচীন সভ্যতার রূপচিত্ত বহিরাগত কোন প্রভাব হতেই উদ্ভূত হয়। একথা মনে করার যুক্তি এ যে প্রাচীন জাপানী সভ্যতার ধারাটা চলতে চলতে স্তব্ধ ও প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। সভ্যতার এ অবক্ষয় ধরা হয় তখনই যখন কোন জাতি তার সৃষ্টিশীল সত্তা হারিয়ে ফেলে অথবা বহিরাগত যে প্রভাব একদিন জাতিকে জাগিয়ে তোলে, তার সংস্কৃতিকে উন্নতি ঘটায়, সেই প্রভাব সহসা প্রত্যাহত হয়। যদি দেখা যায় কোন দেশ তার সংস্কৃতির মূল উপাদান অন্য কোন বিদেশী সংস্কৃতি থেকে সগ্রহ করে এবং বাইরে থেকে সেই উপাদান আসার পথ বদ্ধ হয়ে গেলেই সেই জাতির সংস্কৃতির ধারাটা স্তব্ধ ও প্রস্তরীভূত হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে সে সংস্কৃতির সংরক্ষকমাত্র, সংস্কৃতির স্রষ্টা নয়।
এদিক দিয়ে আমরা যদি বিশ্বের বিভিন্ন জাতিকে বিচার করি তাহলে দেখতে পাব তাদের মধ্যে বেশির ভাগই মূল্যগতভাবে কোন সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে পারেনি। অন্য কোন দেশে সৃষ্ট কোন সংস্কৃতির ধারাটিকে গ্রহণ ও আত্মসাৎ করেছে মাত্র।
নিম্নে দৃষ্টান্ত থেকে ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারি।
আর্যজাতি সংখ্যায় স্বল্প হয়েও বিশ্বের বহু দেশ ও জাতিকে জয় করে এবং সেইসব বিজিত দেশের ভূমির উর্বরতা, জলবায়ুর ও কায়িক শ্রমের প্রাচুর্য প্রভৃতি এমন কতগুলো জীবনযাত্রাগত সুযোগ সুবিধা পায় যাতে তারা তাদের বুদ্ধি ও সংগঠন প্রতিভাকে আরো ভালভাবে বিকশিত করে তুলতে পারে। কয়েক শত বা কয়েক হাজার বছরের মধ্যে বিজেতারা বিজিত জাতির আদিম প্রাণহীন সংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। তবে এ নতুন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে গিয়ে বিজিত জাতিরা তাদের দেশ ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে রূপটা কিছু পরিবর্তিত করে ফেলে। কিন্তু পরিশেষে দেখা যায় বিজেতারা তাদের জাতিগত রক্তকে অবিমিশ্র রাখার প্রাকৃতিক নিয়ম ও নীতি হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তারা বিজিত জাতিদের সঙ্গে তাদের রক্তগত সংমিশ্রণ ঘটাতে থাকে। এভাবে তাদের পৃথক সত্তাটি তার সব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে।
এক হাজার বছরের মধ্যেই দেখা যায় বিজিত জাতিগুলো বিজেতাদের রক্ত হতে তাদের ত্বকের যে যে অংশ উজ্জ্বলতা লাভ করেছিল, সে রঙ ও উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে গেছে অনেকখানি। বিজেতা জাতির যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও সত্তার দীপ্তি হতে বিজয়ী জাতি সংস্কৃতি ও জাতীয় উন্নতির মশালটি জ্বলে ওঠে, বিজেতা জাতির রক্ত ম্লান হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেই আভার দীপ্তিও ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু বিজেতাদের প্রভাব কালক্রমে ম্লান হয়ে গেলেও বিজেতাদের রক্তের মধ্যে বিজয়ীদের রক্তের রঙ কিছুটা রয়ে যায়। তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বলতায় একটা ক্ষীণ অংশ যা বিজেতাদের ওপর নেমে আসা সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ও বর্বরতার অন্ধকারকে ঘন হতে দেয় না কিছুতে। যে অন্ধকার নতুন করে আচ্ছন্ন করে বিজিতদের, সেই অন্ধকারের মাঝে বিজয়ীদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অতীত উজ্জ্বলতার অংশটি কিরণ দিতে থাকে। সেই কিরণের আভায়। বর্তমানের কোন ভাবমূর্তি নয়, বিস্মিত অতীতের একটা দিক প্রতিফলিত হয়ে ওঠে শুধু।
তবে এমনও হতে পারে যে কালের বিবর্তনে ভবিষ্যতে কোন এক সময় বিজিত জাতি তাদের সংস্কৃতির সুপ্রাচীন স্রষ্টাদের সংস্পর্শে আবার আসতে পারে। তখন হয়ত তারা অতীত ঋণের কথা ভুলে যায়। তথাপি তাদের রক্তের মধ্যে বিজয়ীদের রক্তের যে একটা অংশ রয়ে যায়, সেই রক্তের প্রভাব তাদের প্রবৃত্তিকে আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে বিজেতাদের দিকে। সুতরাং অতীতে যে জাতিগত সংমিশ্রণ বাধ্যবাধকতার মধ্য দিয়ে বয়ে ছিল, এবার তা হবে স্বচ্ছন্দে ও স্বেচ্ছায়। ফলে এক সাংস্কৃতিক উন্নতির ঢেউ নতুন করে প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তা’ এ সংমিশ্রণের জন্য বিজেতা জাতির রক্ত নতুন করে দূষিত না হওয়া পর্যন্ত এভাবে সবকিছু চলতে থাকবে।
যারা বিশ্বের ইতিহাস ও গতিপ্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করতে চান তাদের এ দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করতে হবে।
সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে সব পরিবর্তন ঘটছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে সব জাতির নিজস্ব কোন সংস্কৃতি নেই, যারা বহিরাগত কোন সংস্কৃতির ধারক বা সংরক্ষক মাত্র তারা বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতি করছে, আর আর্যদের মত যেসব জাতি এক উন্নত ধরনের স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা তারা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।
আমাদের জীবনে দেখা যায় প্রতিভাবান ব্যক্তি তাদের দেখে সাধারণত আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতই মনে হয়; কোন বিশেষ ঘটনা বা উপলক্ষ্য ছাড়া তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটে না। যখন জাতীয় জীবনে এমন কোন বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার সৃষ্টি হয় যা দেখে সাধারণ মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে, তখনি আপাত সাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তিরা তাদের প্রতিভার পরিচয় দেয়। এ কারণেই কোন জাতির জীবনে মাঝে মাঝে এতজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। যুদ্ধও এমন এক বিশেষ ঘটনা যার মাধ্যমে বুদ্ধিমান, শক্তিমান ও প্রতিভাবানরা তাদের অসাধারণত্বের পরিচয় দান করতে পারেন। কোন বিপর্যয়কালে দেখা যায় অনেক নিরীহ যুবক হঠাৎ সামনে এসে দৃঢ়সংকল্প ও স্থিরবুদ্ধির মাধ্যমে সেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে তাদের আশ্চর্য প্রতিভা শক্তির পরিচয় দেয়। এ ধরনের কোন পরীক্ষামূলক ঘটনা ছাড়া কেউ বুঝতেই পারবে না কার মধ্যে এ আশ্চর্য এক বীরের শক্তি লুকিয়ে আছে। কোন প্রতিভা বা বীরত্বের সর্বসমক্ষে প্রকাশ ঘটাতে হলে বিশেষ কার্যপ্রেরণা ও প্রবৃত্তির দরকার। ভাগ্যের হাতুড়ীর যে নিষ্ঠুর আঘাত একজন সাধারণ মানুষকে সহজেই ভেঙে চুরমার করে দেয়, সে আঘাত কোন বীর বা প্রতিভাবান ব্যক্তির মাঝে এক ইস্পাতকঠিন প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়। প্রথমে প্রকৃত ঘটনার আঘাতে বীরদের ওপর থেকে সাধারণের খোলস খসে যায় আর তখন তাদের অন্তর্নিহিত অসাধারণ সত্তার কঠিনতম অংশটি বেরিয়ে পড়ে। তা দেখে সারা জগৎ বিস্মিত হয়ে যায়। জগতের লোকের ধারণা তাদের মতই এক আপাত সাধারণ লোকের মধ্যে এমন অসাধারণ গুণ ও শক্তি লুকিয়ে থাকতে পারে। যতবারই কোন প্রতিভার আবির্ভাব হয়, ততবারই এ নিয়মের পুনরাবৃত্তি ঘটে।
যে ব্যক্তি কোন সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী, জন্মের পর থেকে তার সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গটি ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত তার অন্তরের মধ্যে চাপা ছিল। যে কোন প্রতিভাই এমনি এক অন্তর্নিহিত সহজাত শক্তি। প্রতিভা কখনো কোন শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের সৃষ্টি নয়।
আমি আগেই বলেছি, আবার বলছি, এটা শুধু ব্যক্তির পক্ষে নয়, সমগ্র জাতির পক্ষেও প্রযোজ্য। যে সব জাতি বিভিন্ন সৃষ্টিশীল শক্তির পরিচয় দেয়, তারা জন্মগতভাবেই সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী। আপাত দৃষ্টিতে লোকে দেখতে না পেলেও তাদের স্বভাবের মধ্যেই সে শক্তি নিহিত থাকে। উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যেমন কোন বিশেষ অবস্থা ছাড়া তার সহজাত প্রতিভার বিকাশ সাধন করতে পারে না, তেমনি কোন জাতিও উপযুক্ত কর্মপ্রেরণা বা অবস্থা ছাড়া তাদের সৃজনশীল প্রতিভাকে কার্যে রূপায়িত করতে পারে না।
এ সত্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল সেই আর্যজাতি যারা আজও মানবজাতির সকল উন্নতি ও প্রগতির ধারক ও বাহক। ভাগ্য যখনি তাদের কোন বিশেষ অবস্থার ওপরে উপস্থাপিত করে, তখনি তাদের সহজাত শক্তি এক বিশেষ রূপে বিকাশ লাভ করে থাকে। এ সব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা যেসব বিশিষ্ট সংস্কৃতি সৃষ্টি করে, সে সব সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট বিজিত দেশের ভূমি, প্রকৃতি, জলবায়ু ও অধিবাসীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর মধ্যে দেশের অধিবাসীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কোন দেশের উন্নতি করতে গিয়ে যদি দেখা যায় সেখানে যন্ত্রপাতি ও কারিগরী বিদ্যার অভাব আছে, তাহলে সেখানে প্রচুর শ্রমশক্তির দরকার হয়। আর্যরা যদি তাদের বিজিত জাতিগুলোর যৌবনের শ্রমশক্তির সাহায্য না নিত, তাহলে পরবর্তীকালে তারা উন্নত ধরনের সংস্কৃতির সৃষ্টি করতে পারত না। যেমন প্রথমে অশ্ব ও বিভিন্ন পশুর সাহায্যে পরিবহন কার্য সম্পন্ন করার পর মানুষ যন্ত্রপাতি আবিস্কার করে।
উন্নত ধরনের সভ্যতার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অনুন্নত জাতিগুলো এক অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে কাজ করে; তারা নিজেদের শ্রমশক্তির দ্বারা যন্ত্রের অভাব পূরণ করে। সভ্যতার প্রথম স্তরে পোষা পশুর পরিবর্তে বিজিত নিকৃষ্ট জাতির লোকদের বিভিন্ন কাজে লাগানো হত।
প্রথম প্রথম বিজিত লোকদের ক্রীতদাস হিসেবে যেসব কাজে লাগানো হত, পরে পোষণ মানানো পশুদের সেইসব কাজে লাগানো হয়। প্রথমে যেসব শক্রদের জয় করা হত তাদের লাঙল টানার কাজে নিযুক্ত করা হত, পরে এ কাজে বলদ ও ঘোড়াদের লাগানো হয়। একমাত্র অপদার্থ শান্তিবাদীরাই এটাকে মানবজাতির অধঃপতন বলে অভিহিত করতে পারে। আজকের মানুষের সভ্যতার যে উন্নতি হয়েছে সেখানে ওঠার জন্য এ ধরনের বিবর্তনের প্রয়োজন ছিল।
অসংখ্যা ক্রম বিবর্তন ও ক্রম পর্যায় সমন্বিত মানবজাতির উন্নতি বা অগ্রগতির ব্যাপারটাকে একটা খণ্ডহীন মইয়ের ওপরে ওঠার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। একটি মইয়ের মধ্যে অনেক অংশ বা সিঁড়ি আছে। কিন্তু নিচের অংশটি অতিক্রম না করে কেউ উজ্জ্বলতার অংশটায় উঠতে পারে না। আর্যরা তখন তাদের বাস্তবতা চোখের বশবর্তী হয়ে যেসব গ্রহণযোগ্য মনে করেছিল সেই সবই গ্রহণ করেছিল; আধুনিক শান্তিবাদীদের কথা মত চলেনি। তবে এ বাস্তব নির্ণয় করা ও সেই মতে চলা খুবই কঠিন। একমাত্র এ পথই মানুষকে নিয়ে যেতে পারে তার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।
কিন্তু এমন অনেক লোক আছে যারা মানুষকে শুধু স্বপ্নের রাজ্যে নিয়ে যায়। এ সব স্বপ্নদর্শীরা মানুষকে তাদের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।
সুতরাং দেখা যায় আর্যরা কোন নিকৃষ্ট অনুন্নত জাতির সংস্পর্শে আসামাত্র সভ্যতার প্রথম স্তরটি গড়ে ওঠে। এ স্তর গড়ে ওঠে তখনি যখন সেই অনুন্নত জাতির লোকেরা ক্রমবর্ধমান মানব সভ্যতার এক যান্ত্রিক উপাদান হিসেবে কাজ করতে থাকে।
এভাবে আর্যরা এক সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান পায়। বিজেতা হিসেবে তারা নিকৃষ্ট অনুন্নত জাতিগুলোকে জয় করে তাদের নেতৃতাধীনে তাদের কর্মশক্তিকে এক সুসংগঠিত পদ্ধতিতে গঠন করতে থাকে। পরাজিতরা বিজয়ীদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য অনুসারে চলতে বাধ্য হয়। কিন্তু পরাজিতদের ওপর আর্যরা তাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য জোর করে চাপিয়ে দিলেও এর ফলে তাদের স্বার্থ প্রথমে রক্ষা পায়নি। আগের যুগের থেকে তাদের জীবনযাত্রা আরো সহজ হয়ে উঠেছিল। তারা শুধু বিজয়ী হিসেবে বিজেতাদের প্রভূতুই রক্ষা করে চলেনি, তারা তাদের মাঝে সভ্যতারও বিস্তার করেছিল। এটা আর্যদের সহজাত কর্মক্ষমতা, যোগ্যতা, প্রতিভা ও জাতিগত রক্তের সংরক্ষণ থেকে সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু যখনি বিজিতরা বিজেতাদের স্তরে ধীরে ধীরে তাদের ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে পৌঁছে যায়, তখনি এতদিন ধরে বিজেতা ও বিজিতদের মধ্যে যে বাধা ও ব্যবধান বিরাজ করেছিল তা’ সব অবলুপ্ত হয়ে যায়। আর্যরা তাদের জাতীয় সত্তা ও রক্তের পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ণ ও অমিশ্রিত করে রাখতে না পারায় তাদের নিজেদের হাতে গড়া স্বর্গ বিজেতাদের কাছেই হারিয়ে ফেলে। এভাবে তারা জাতিগত সংমিশ্রণের মধ্যে ডুব দিয়ে তাদের সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতাকে বাড়িয়ে ফেলে। তারা তাদের উত্তর পুরুষের বংশধারা হতে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে দেহ ও মনের দিক থেকে তাদের দ্বারা আদিম অধিবাসীদের মত হয়ে ওঠে, তারা অবশ্য কোনরকমে তাদের দ্বারা নির্মিত সৌধটিকে টিকিয়ে রাখে। কিন্তু তাদের সেই মূল সংস্কৃতির প্রাণসত্ত্বাটা প্রস্তরীভূত হয়ে যেতে থাকে ধীরে ধীরে এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত প্রাণশক্তির সকল গৌরব বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যেতে থাকে; এভাবেই সমস্ত সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যের ধ্বংস নেমে আসে। রক্তগত সংমিশ্রণজনিত জাতীয় অধঃপতনই প্রাচীন সভ্যতাগুলোর পতনের প্রধানতম কারণ। যুদ্ধে দ্বারা কখনো কোন জাতি ধ্বংস হয় না। সম্পূর্ণরূপে জাতিগত রক্তের অমিশ্রিতা ও শুচিতা হতে যে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে, সেই প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলায় ধ্বংস ও অধঃপত ঘটে প্রাচীন আর্যদের। যুদ্ধ, বড় ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো জাতিগত অবক্ষয় প্রবৃত্তির এক বাস্তব প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।
আর্যদের প্রভুত্বের কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে আর্যদের মধ্যে আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি শুধু প্রধান নয়, তাদের প্রবৃত্তির প্রকাশের রীতিনীতিটিও বড় অদ্ভূত। আত্মগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় বাচার প্রবৃত্তি সকল প্রাণীর মধ্যেই সমান— শুধু তার প্রকাশের পদ্ধতিটি ক্ষেত্রবিশেষে আলাদা। আদিম প্রবৃত্তিগুলির অন্যতম আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি মানুষের ব্যক্তিগত অহংবোধের বাইরে কোন কাজ করতে পারে না। আমরা এ প্রবৃত্তিকেই অহংবোধ নাম দিয়েছি। এ অহংবোধের মধ্যেই মানুষের সমস্ত কালচেতনাও সীমাবদ্ধ। এ কালচেতনার অর্থ হল এ যে বর্তমানকালই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষের জীবনে। অহংভিত্তিক এ কালচেতনার মধ্যে ভবিষ্যতের কোন স্থান নেই। সকল জীব শুধু নিজের জন্য বাঁচে, তারা একমাত্র যখন ক্ষুধা অনুভব করে তখনি খাদ্যের অনুসন্ধান করে। একমাত্র আত্মরক্ষার কারণ ছাড়া তারা যুদ্ধ করে না। যতদিন এ আত্মরক্ষণ প্রবৃত্তি মানুষের মনে প্রবল থাকে ততদিন কোন জনসমাজ বা সম্প্রদায় গড়ে উঠতে পারে না। এমন কি এ অবস্থায় কোন পরিবারও গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। কারণ নরনারীর যে সম্পর্ক কোন পরিবারকে গড়ে তোলে সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিটা ব্যক্তিগত সীমানা পার হয়ে যায় আর একটি জীবন পর্যন্ত প্রসারিত হয়। অর্থাৎ মানুষ সবসময় নিজের সঙ্গে তার জীবনের সাথীর জীবনকেও রক্ষা করে চলার চেষ্টা করে। পুরুষ নারীর জন্য খাদ্যসংগ্রহ করে এবং নারী পুরুষ উভয়ে মিলে তাদের সন্তানদের আহারের ব্যবস্থা করে থাকে। তারা সব সময় একে অন্যকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হয়। এভাবে আমরা সংকীর্ণ পথে হলেও এক একটি পরিবারের মধ্যে মানুষের আত্মত্যাগের প্রথম পরিচয় পাই। এ প্রবৃত্তি যখন পরিবারের সীমানা অতিক্রম করে সমাজ সম্পর্কের বৃহত্তর ক্ষেত্রের মধ্যে প্রসারিত হয়, তখনই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়ে ওঠে।
মানব জাতির মধ্যে যারা নিকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত তারা তাদের পরিবারের বাইরে আত্মত্যাগের প্রবৃত্তির পরিচয় দিতে পারে না। ব্যক্তিস্বার্থকে পেছনে সরিয়ে কারোর জন্য কিছু করার ও আত্মত্যাগের প্রবৃত্তিটির যত বেশি সম্প্রসারণ ঘটে ততই বড় বড় সমাজ ও সম্প্রদায় গড়ে ওঠে।
পরের জন্য ব্যক্তিগত কাজকর্ম, কামনা বাসনা ও প্রয়োজন হলে নিজের জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করার নীতি আর্যদের মধ্যেই পুর্নমাত্রায় বিকাশ লাভ করে। আর্যদের মহত্বের ভিত্তিভূমিটি কোন বুদ্ধিগত উর্ষকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠেনি। সমাজের স্বার্থেই আপন আপন বুদ্ধিগত শক্তি ও উৎকর্ষকে ত্যাগ করার সুমহান বাসনাই হল সেই মহত্বের ভিত্তি। এখানে দেখা যায় আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিটি এক মহত্তম রূপ পরিগ্রহ করেছে। কারণ আর্যরা স্বেচ্ছায় সমাজের সুখ ও স্বার্থের কাছে তাদের ব্যক্তিগত অহংবোধকে বিলিয়ে দেয় এবং প্রয়োজনবোধে নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়।
আর্যদের সংগঠন ক্ষমতা এবং বিশেষ করে কোন সংস্কৃতিকে গড়ে তোলায় তাদের আশ্চর্য ক্ষমতার মূল উৎসটি একান্তভাবে বুদ্ধিগত নয়। তা যদি হত তাহলে তাদের বুদ্ধিগত শক্তি ও উৎকর্ষ ধ্বংসাত্মকও হতে পারত, তাহলে তারা এতখানি সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারত না। কারণ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ ও সেবায় ব্যক্তিগত স্বার্থ ও মতামত বিসর্জন দেবার অকুণ্ঠ প্রস্তুতি ও প্রবৃত্তির ওপরেই নির্ভর করে মানুষের সকল সাংগঠনিক ক্ষমতার সার্থকতা। সমাজের উন্নতি ও সেবায় আত্মনিয়োগ করার প্রশিক্ষণ সে পায়। এক্ষেত্রে সে প্রত্যক্ষভাবে নিজের জন্য বা ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের জন্য কাজ করে না। তাদের সকল উৎপাদক কর্মশক্তি সমাজের সকল মানুষের কর্মের একটি অংশ বলে মনে করে। সে নিজেকেই এ সাজের এক অংশ হিসেবে ধরে নেয়। কম’ শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ–নিজের উপার্জনের জন্য কোন কাজ করা নয়, এ শব্দের অর্থ হল এমন কিছু করা যাতে ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের স্বার্থও পূরণ হবে। যখন কোন মানুষের কোন কর্ম একান্তভাবে আত্মরক্ষণ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ পুরণের জন্য পরিচালিত হয়, তখন তার সে কাজকে চৌর্যবৃত্তি বলে।
সমাজের স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলার এ নীতি ও প্রবৃত্তিই প্রকৃত মানব সভ্যতার প্রধানতম ভিত্তি। এ নীতি ও প্রবৃত্তির ফলে বিশ্বের এমন অনেক অক্ষয় কীর্তি গড়ে উঠেছে যার জন্য তার স্রষ্টারা জীবিতকালে কোন প্রতিদান বা প্রতিফল লাভ করে যেতে পারেনি; তাদের মৃত্যুর পর তাদের বংশধরেরা সেইসব কীর্তির সুফল ভোগ করে। এ নীতি ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই মানুষ এমন অনেক কাজ করে যার জন্য সৎ ও দীনহীন জীবিকা ছাড়া প্রতিদানে কিছুই সে পায় না। কিন্তু এ সৎ জীবিকাই সমাজের ভিত্তিভূমিকে দৃঢ় করে তোলে। কোন কৃষক, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কর্তা বা সরকারি কর্মচারী যিনিই হোন না কেন— যখন কোন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত সুখ সমৃদ্ধির কথা চিন্তা না করে সমগ্র সমাজের বা মানবজাতির জন্য কাজ করে তখন তারাই এক সুমহান নিঃস্বার্থ কর্মপ্রবৃত্তির মূর্ত প্রতীক। অনেক সময় মানুষ তার এ প্রবৃত্তিও কর্মতৎপরতার তাৎপর্য না জেনেই তার পরিচয় দিয়ে থাকে।
খাদ্যসংগ্রহ, মানবজাতির উন্নতির প্রাথমিক ভিত্তি রচনা বা মানব সভ্যতা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ প্রভৃতি যে কোন কাজের ক্ষেত্রে মানুষ নিঃস্বার্থভাবে যা কিছু করে তাতেই তার ত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের স্বার্থে প্রাণ বিসর্জনই হল এ ত্যাগের সুমহান প্রবৃত্তির সর্বশ্রেষ্ঠ বাস্তবরূপ। একমাত্র এ ত্যাগের মাধ্যমেই মানুষ যুগ যুগ ধরে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছে, সে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সে রক্ষা করে যেতে পারবে। এভাবে কাজ করে গেলে মানুষের সভ্যতাকে প্রকৃতি বা মানুষ কেউ কখনো ধ্বংস করতে পারবে না।
জার্মান ভাষায় একটি শব্দ আছে যার অর্থ হল ব্যক্তিস্বার্থ থেকে সমাজের সর্বসাধারণের স্বার্থ সবসময় বড়। যে মৌন প্রবৃত্তি থেকে এ ধরনের কর্মের উদ্ভব হয়, অহং ও আদর্শের পার্থক্যই সেই প্রবৃত্তির উৎস। এর অর্থ সমাজের স্বার্থে যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকার এক স্বীকৃত বাসনা।
এ বিষয়ে একটি কথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হল এ যে আশীবাদের অর্থ ভাবানুরাগের উচ্ছসিত প্রকাশ নয়, আদর্শবাদের প্রকৃত অর্থ হল মানব সভ্যতার জন্য অত্যাবশ্যক এক ভিত্তি। এ আশীর্বাদ হতেই মানবিক’ শব্দটির উৎপত্তি। এ মনোভাবের জন্য সারা বিশ্বে আর্যদের এত প্রতিষ্ঠা। মানবজাতি এ ধারণাটির জন্য সারা বিশ্ব আর্যদের নিকট ঋণী। মানবতার এ আদর্শ থেকে এমন একটি সৃষ্টিশীল শক্তির উদ্ভব হয় যে শক্তির সাহায্যে মানুষ তার দেহগত শক্তির সঙ্গে বুদ্ধিগত শক্তির মিলন ঘটিয়ে মানব সভ্যতার সৌধটিকে গড়ে তোলে।
এ আদর্শবাদ ছাড়া মানুষের সকল বুদ্ধিবৃত্তি সৃষ্টি শক্তিহীন বন্ধ্যা বাইরের ঘটনায় পর্যবসিত হবে এবং ঘটনার কোন বিশেষ মূল্য বা বৃহত্তর কোন তাৎপর্য থাকবে না।
প্রকৃত আদর্শবাদের অর্থই হল ব্যক্তি স্বার্থকে সমষ্টি স্বার্থের অধীনস্থ করে তোলা। তাই সমাজের বৃহত্তর স্বার্থপূরণের আদর্শ প্রকৃতির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য পূরণের পথে নিয়ে যায় মানুষকে।
যে আদর্শবাদ যত বিশুদ্ধ, তা তত গভীর জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত। একটি বালককে ভাববাদী শান্তিবাদীরা যতই বোঝাক না কেন, সে তাদের কথা ভালোভাবে না বুঝলে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তার জাতির আদর্শের খ্যাতিরে প্রাণ বিসর্জন দেবে।
কোন কিছু না বুঝলেও বালকটি অন্তত এ কথাটা বেশ বোঝে যে প্রয়োজন হলে কোন ব্যক্তিজীবনের বিনিময়ে একটি প্রজাতিকে বাঁচাতে হবে। সে তাই ভাববাদী শান্তিবাদের নীতিকথার প্রতিবাদ করবে। যে স্বার্থবাদীরা এক একজন ছদ্মবেশী ব্যর্থতান্ত্রিক অহংবেশী কাপুরুষকে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধিতা করে চলেছে। মানবসভ্যতার বিবর্তনের জন্য যা অত্যাবশ্যক তাহল এ যে সমাজের স্বার্থে আত্মত্যাগের আদর্শে একটি ব্যক্তি উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। এ আদর্শকে ত্যাগ করে কোন মানুষ কখনই সেই ভণ্ডদের কথা শুনবে না বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে না যারা প্রকৃতির থেকে বেশি জানার ভান করে এবং যারা ধৃষ্টতাবশত প্রকৃতির বিধানের সমালোচনা করে।
একমাত্র যখন এ আদর্শ লুপ্ত হয়ে যেতে বসে, তখনি সেই শক্তির মধ্যে আমরা একটি চিত্র দেখতে পাই যে শক্তি ছাড়া কোন সভ্যতাই টিকে থাকতে পারে না। যে মুহূর্তে মানুষের স্বার্থপরতা ও অহংবোধ সমাজে প্রাধান্য লাভ করে, সেই মুহূর্তে সমাজ সম্পর্কের বন্ধনটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তখন মানুষ সমাজকে বাদ দিয়ে আত্মসুখের সন্ধান করতে গিয়ে স্বর্গ থেকে নরকে পতিত হয়।
যারা সারাজীবন সুখের সন্ধান করে যায়, ভবিষ্যত বংশধরেরা তাদের মনে রাখে না। তারা মনে রাখে তাদেরই কথা, সেইসব বীরদের কথা, যারা তাদের ব্যক্তিগত সুখ জলাঞ্জলী দিয়েছিল।
ইহুদিরা জাতি হিসেবে আর্যদের সম্পূর্ণ বিপরীত। সারা পৃথিবীতে আর এমন একটি জাতিও নেই যাদের মধ্যে আত্মসংরক্ষণের প্রবৃত্তিটি এতখানি প্রবল। যারা মনে করে তারা ঈশ্বরপ্রেরিত জাতি। পৃথিবীতে এমন কোন জাতি আছে হাজার বছরের মধ্যেও যে জাতির চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি। আর কোন জাতি সর্বাত্মকভাবে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছে? কিন্তু এত বিরাট পরিবর্তন সত্ত্বেও ইহুদি জাতি যেখানে ছিল সেখানেই আছে, তাদের মনপ্রাণের কোন পরিবর্তনই হয়নি। তাদের জাতিগত সংরক্ষণ ও বাঁচার প্রবৃত্তি এমনই দুর্মর।
ইহুদিদের বুদ্ধিগত কাঠামোটা হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে উঠেছে। আজকাল লোকে ইহুদিদের ধূর্ত বলে। অবশ্য একদিক দিয়ে ইহুদিরা বহু যুগ থেকে তাদের ধূর্তামীর পরিচয় দিয়ে আসছে। তাদের বুদ্ধিগত শক্তি ও চাতুর্যের কাঠামোটি তাদের কোন অন্তর্নিহিত বিবর্তনের ফল নয়, যুগে যুগে বাহিরের অভিজ্ঞতা ও ঘটনা থেকে যে বাস্তব শিক্ষা লাভ করেছে, তার উপাদানেই গড়ে উঠেছে তাদের বুদ্ধিগত কাঠামোটি। মানুষের মন বা আত্মা পর পর ক্রমপর্যায়ের স্তরগুলো পার না হয়ে কখনো ওপরে উঠতে পারে না। ওপরের যে কোন স্তরে উঠতে হলে আগে তার নিচের স্তরটি অতিক্রম করতে হবে। যে কোন সভ্যতার ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে অতীতের একটি জ্ঞান আছে। মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই তার সকল চিন্তাভাবনার উদ্ভব হয়। যুগ যুগ ধরে সখি পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষের বেশি চিন্তা ভাবনা গড়ে ওঠে। সভ্যতার সাধারণ স্তরের কাজ হল প্রতিটি মানুষকে এমন এক প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা, যার ওপর ভিত্তি করে সে সকলের সঙ্গে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির মান এগিয়ে নিয়ে চলতে পারে। যারা আজকের যুগের অগ্রগতিকে বুঝতে চায় ও সেই অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে চায়, তাদের কাছে এসব জীবন-জিজ্ঞাসা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কোন প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ বা মনীষী সহসা তার কবর থেকে যদি উঠে আসেন, তিনি এ যুগের অগ্রগতির কথা কিছুই বুঝতে পারবেন না। অতীতের কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে এ যুগে এসে এ যুগের গতিপ্রকৃতি বুঝতে হলে তাকে অনেক প্রাথমিক জ্ঞান সঞ্চয় করতে হবে, যে জ্ঞান আজকের যুগে ছেলেরা আপনা থেকে খুব সহজ ভাবে পেয়ে যায়।
ইহুদি জাতির নিজস্ব কোন সভ্যতা ছিল না। কেন ছিল না তা আমি পরে বলব। যেসব সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব বিভিন্ন দেশ চোখে দেখেছে বা হাতের কাছে পেয়ে গেছে–সেই সব কৃতিত্বের দ্বারাই তাদের এ বুদ্ধিবৃত্তিকে উন্নত করেছে।
এর উল্টো ঘটনা কখনো দেখা যায়নি।
যদিও ইহুদিদের আত্মোন্নতির প্রকৃতি অন্যান্য জাতির থেকে আরো প্রবল এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তি অন্যান্য জাতির থেকে কিছুমাত্র কম নয়, তথাপি একটা দিক দিয়ে বড় রকমের একটা অভাব দেখা যায় তাদের জাতীয় চরিত্রে। সাংস্কৃতির উন্নতির জন্য যে জিনিসটার সবচেয়ে বেশি দরকার সেই আদর্শবোধ তাদের একেবারেই নেই। ইহুদিদের মধ্যে দেখা যায় তাদের আত্মত্যাগের প্রবৃত্তিটি আত্মসংরক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার উর্ধ্বে উঠতে পারে না তারা কখনো। তাদের মধ্যে যে জাতীয় সংহতি দেখা যায় তা আদিম সঙ্গপ্রবণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা উল্লেখযোগ্য যে, যতদিন কোন বিপর্যয় তাদের জাতীয় অস্তিত্বকে বিপন্ন করে দেবার ভয় দেখায়, ততদিনই তারা পারস্পরিক নিরাপত্তার জন্য ঐক্যবদ্ধ ও সংহত থাকে। এ জাতীয় বিপর্যয়ই তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাবকে অপরিহার্য করে তোলে। একদল নেকড়ে যেমন একযোগে তাদের শিকারের বস্তুকে আক্রমণ করার পর তাদের ক্ষুধা মিটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দল থেকে পৃথক হয়ে পড়ে, তেমনি ইহুদিরাও ঠিক তাই করে।
ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার জন্য যেটুকু দরকার সেইটুকু ত্যাগ করতেই তারা প্রস্তুত সব সময়। তার বেশি নয়। ইহুদিরা একমাত্র তখনই ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে যখন কোন সাধারণ এক বিপদ তাদের সামনে এসে দাঁড়ায় অথবা কোন সাধারণ শিকারের বস্তু তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু যখন সেই বিপদ কেটে গিয়ে শিকারের বন্ধু হাতের মুঠোয় এসে পড়ে, তখন তাদের আপাতদৃষ্ট সাময়িক সংহতি বোধ উবে যায় মুহূর্তে। তখন দেখা যায় যে জাতি একদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেছে আজ তারাই পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে মত্ত হয়ে উঠেছে।
ইহুদিরা ছাড়া পৃথিবীতে যদি অন্য কোন জাতি না থাকত তাহলে তারা নিজেরা মারামারি করে একে অন্যকে ধ্বংস করে ফেলত; অবশ্য যদি হঠাৎ কোন আত্মত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও দীক্ষিত হয়ে সব ঝগড়া মারামারি নিজেরা বন্ধ করে ফেলত তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র। সুতরাং কেউ যদি ইহুদিদের পারস্পরিক সহযোগিতার সাময়িক নীতিটাকে আত্মত্যাগের আদর্শ বলে মনে করে বা ব্যাখ্যা করে তাহলে সে ভুল করবে।
তারা যা কিছু করে ব্যক্তিগত অহংবোধের দ্বারা প্রণোদিত হয়েই করে। আর এ জন্যই দেখা যায় ইহুদিদের রাষ্ট্রের কোন নির্দিষ্ট ভৌম সীমানা নেই। যে রাষ্ট্রের কোন ভৌম সীমানা নেই, সে রাষ্ট্র কখনো প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। যদি না সে রাষ্ট্রের নাগরিকদের সকল মর্মপ্রেরণা ও কর্ম প্রবণতা কোন ত্যাগের আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়। এ আদর্শ যে জাতির নেই সে জাতির সভ্যতাও তার ভিত্তিভূমি হারিয়ে ফেলে।
এ কারণে ইহুদিদের বুদ্ধিবৃত্তি যথেষ্ট থাকলেও তাদের নিজস্ব কোন সংস্কৃতি নেই। ইহুদি জাতির মধ্যে আজ যে সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, সে সংস্কৃতি তাদের নিজস্ব সৃষ্টি নয়, তা অন্য সব জাতির দান। শুধু তাই নয়, তাদের হাতে পড়ে সেই সংস্কৃতির মানের অধোগতি ঘটেছে।
মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে ইহুদিদের স্থান কোথায় এ বিষয়ে যদি আমরা আলোচনা করতে যাই, তাহলে আমাদের একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে শিল্পের ক্ষেত্রে ইহুদিদের কোন নিজস্ব সৃষ্টি নেই। স্থাপত্য ও সঙ্গীতবিদ্যা কলাবিদ্যার এ দু’টি প্রধান ক্ষেত্রে ইহুদিদের কোন মৌলিক সৃষ্টিশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। শিল্পের ক্ষেত্রে যখনি তারা কিছু সৃষ্টি করতে আসে তখনি তারা অন্য জাতির কোন না কোন শিল্পরীতিকেই ভিন্ন উপায়ে তৈরি করার চেষ্টা করে। যেসব জাতি সভ্যতার স্রষ্টা ও প্রবর্তক, যারা সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী, তাদের যেসব গুণ আছে ইহুদি জাতির তা নেই।
কি পরিমাণে ইহুদিরা অপর জাতির সভ্যতাকে আত্মসাৎ করতে পেরেছে বা তার অবনতি ঘটিয়েছে তা বোঝা যাবে একটা বিষয়ে। তারা বানরদের মত শুধু অনুকরণ প্রবৃত্তিরই পরিচয় দিয়ে থাকে। যে গতিশীল সৃষ্টিশীলতা কোন মহৎ নাট্যসৃষ্টির জন্য একান্তভাবে আবশ্যক তা তাদের নেই। ওপরে যে যত কলাকৌশলই দেখাক না কেন, তাদের সৃষ্ট শিল্পবস্তুর কোন প্রাণ নেই। অথচ তাদের সংবাদপত্রগুলো তাদের এ অপূর্ণতাকে ঢাকার জন্য এগিয়ে আসে। এ অপূর্ণতা ঢাকা দেবার জন্য এক মিথ্যা সাফল্যের জয়ঢাক পেটায়। তখন পৃথিবীর সবাই মনে করে যে শিল্পীর এত প্রচার তার মধ্যে নিশ্চয় কোন বস্তু আছে। অথচ আসলে সে শিল্পী কুশলী নকল-নবীশমাত্র।
যে সৃষ্টিশীল শক্তি কোন সভ্যতার প্রবর্তন বা মানব জাতির উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক ইহুদিদের তা নেই। ইহুদিদের কোন আদর্শ না থাকায় তারা সৃজনাত্মক কোন কাজে নিযুক্ত না হয়ে ধ্বংসাত্মক খাতেই প্রবাহিত হয়ে থাকে।
ইহুদিদের কখনো কোন স্থায়ী রাষ্ট্র ছিল না বলেই তাদের কোন নিজস্ব সভ্যতা গড়ে ওঠেনি। অথচ ইহুদিরা আবার ঠিক যাযাবরও নয়। যাযাবরেরা এক-এক সময়ে এক এক জায়গায় বাস করে, যদিও সে জায়গা কোন ভৌম সীমানা দিয়ে ঘেরা যাবে না। তারা সে জায়গায় চাষ আবাদ করে না। তার স্বপক্ষে তাদের যুক্তি এ যে ভূমি উর্বর না হওয়ায় প্রতি বছর সমান ফসল ফলান যেতে পারে এমন কোন কথা নেই। এক নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের নিশ্চয়তা না থাকলে কোন মানুষের পক্ষে এমন কোন জায়গায় বসবাস করা সম্ভব নয়। আর্যরাও প্রথমে যাযাবর জীবন-যাপন করত। আমরা জানি আমেরিকায় উপনিবেশিক যুগের প্রথম যুগে মানুষ শিকারের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করত। পরে তারা আরো শক্তিবৃদ্ধি করে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে আদিম অধিবাসীদের তাড়িয়ে দেয়। এভাবে ধীরে ধীরে তারা সারা দেশ জুড়ে বসতি স্থাপন করে।
কিন্তু আর্যরা প্রথমে যাযাবর জীবনযাত্রা করলেও তারা ইহুদিদের মত ছিল না। ইহুদিরা কোনদিন ঠিক যাযাবর ছিল না।
ইহুদীরা যাযাবর নয়, তারা পরগাছা বা পরজীবি। তারা একটির পর একটি রাজ্য ত্যাগ করে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গেছে; তার কারণ এটা নয় যে কোন এক নীতির বশবর্তী হয়ে গেছে। স্বেচ্ছায় তারা স্থান ত্যাগ করেছে। স্থানীয় অধিবাসীদের চাপে পড়েই সেইস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে তারা।
ইহুদিরা কখনো কোনদিন যাযাবর ছিল না, কারণ তারা যে জায়গা দখল করতে পারত, সে জায়গা ছাড়ার কথা মনেও ভাবত না। ক্রমে একটু সুযোগ পেলেই আশেপাশের জায়গা দখল করে ফেলত। তখন তাদের সে জায়গা থেকে বিতাড়িত করা অন্য জাতির পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। তারা এমন এক দুষ্ট জাতি যারা তাদের আশ্রয় দেয় তাদের অবিলম্বে মেরে ফেলে।
এভাবে দেখা যায় ইহুদিরা সব সময় পরের রাজ্যে বাস করে এসেছে এবং আশেপাশের আরো কিছু রাজ্য দখল করে নিয়েছে। কিন্তু এ সব রাজ্যগুলোর মধ্যে তারা ধর্মসম্প্রদায়ের মুখোস পরিয়ে তাদের একটা নিজস্ব রাষ্ট্র গড়ে তুলত। যখন তারা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন তারা সে মুখোস খুলে ফেলে আপন স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করত, তাদের এ রূপ দেখতে কেউ চায়নি।
যে জীবন ইহুদিরা যাপন করত সে জীবন হল পরগাছার জীবন। এ জন্য এক বিরাট মিথ্যার ওপরে গড়ে উঠেছিল ইহুদিদের জীবন। দার্শনিক শোপেন হাওয়ারের মতে ইহুদিরা বিরাট মিথ্যাবাদী।
তারা অন্যান্য জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে বাস করতে পারত যতদিন তারা এ কথা বলে ভুল বুঝিয়ে রাখতে পারত যে তারা কোন পৃথক জাতি নয়, তারা এক বিশেষ ধর্মমতের প্রতিনিধিমাত্র।
যাতে অন্যের মধ্যে পরগাছা হয়ে থাকতে পারে সেজন্য ইহুদিরা নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করত না। তারা জানত ব্যক্তিগতভাবে তারা যত বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে ততই তারা অপরকে ঠকাতে পারবে। তারা এতদূর মানুষকে প্রতারিত করতে সফল হত যে তারা যে জাতির আশ্রয়ে থাকত তাদের এ ধারণা হত যে ইহুদিরা ফরাসী হতে পারে, আবার ইংরেজও হতে পারে। ওদের জাতিভেদ বলে কোন জিনিস নেই। ওদের সঙ্গে তাদের একমাত্র অর্থ ছাড়া অন্য বিষয়ে কোন সার্থকতাই নেই। যে সমস্ত রাষ্ট্রের প্রশাসন যন্ত্রে কার্যরত লোকদের কোন ঐতিহাসিক কাল নেই, ইহুদিরা হল সেই জাতের। ব্যাভেরিয়ার সরকারের অনেক কর্মচারী জানে না যে ইহুদিরা এক স্বতন্ত্র জাতি, তারা শুধু এক বিশেষ ধর্মমতের প্রতিনিধি মাত্র। কিন্তু ইহুদিদের পত্র-পত্রিকাগুলি একথা মানতেই চায় না। বহু প্রাচীনকালে ইহুদিরা সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে গিয়ে এমন সব উপায়ের আবিষ্কার করে যার দ্বারা তারা যেখানে থাকে সেখানকার মানুষের কাছে থেকে সহানুভূতিটুকু লাভ করে।
কিন্তু ধৈর্যের ক্ষেত্রেও ইহুদিরা পরের অনুকরণ করেছে। তাদের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্র জুড়ে প্রসারিত হয়। ইহুদিদের চেতনা ও অনুভূতি হতে স্বতস্ফুর্তভাবে উদ্ভূত কোন ধর্ম বিশ্বাস গড়ে ওঠেনি। এ পার্থিব জীবন ও জগতের বাইরে এক মহাজীবনে বিশ্বাস একেবারে অপরিচিত তাদের কাছে। আর্যদের মতে মৃত্যুত্তীর্ণ এক মহাজীবনের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া কোন ধর্মমতের বন্দনা সম্ভব নয়। ইহুদিদের ধর্মশাস্ত্রে এ মৃত্যুত্তীর্ণ মহাজীবনের কোন কথা লেখা নেই। তাতে শুধু এ পার্থিব জীবন-যাপনের জন্য কতগুলো আচরণবিধি লেখা আছে।
ইহুদিদের ধর্মশিক্ষার মূল কথা হল এমন কতগুলো নীতি-উপদেশ যার দ্বারা তারা তাদের জাতিগত রক্তের শুচিতা অক্ষুণ্ণ রেখে জগতের অন্যান্য জাতিদের সঙ্গে মিশতে পারে। ইহুদি অ-ইহুদিদের সঙ্গে কিভাবে মেলামেশা করবে তার কথা সব বলা আছে। কিন্তু ইহুদিদের ধর্মশিক্ষার মধ্যে কোন নীতিকথা নেই, আছে শুধু অর্থনীতির কথা। এ কারণে ইহুদিদের ধর্ম আর্যদের ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ কারণেই খৃষ্টধর্মের প্রবর্তক ইহুদি জাতি সম্পর্কে যথাযোগ্য মূল্যায়ন করে এবং সমস্ত মানবজাতির শত্রু এ জাতিকে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য হতে বিতাড়িত করে। তার কারণ ইহুদিরা সব সময় ধর্মকে ব্যবসা ও কাজকারবারের কাজে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ইহুদি জাতির লোকেরা খৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে, সেই খ্রিস্টানরা পর্যন্ত ইহুদি জাতির লোকদের কাছে নির্বাচনের সময় ভোটভিক্ষা করতে যায়। এমন কি তারা নাস্তিক ইহুদি জাতির সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করে সমগ্র খ্রিস্টান জাতির বিশুদ্ধিকরণ করে থাকে।
ইহুদিদের এ ধর্মগত ভণ্ডামীর ওপর আরো অনেক মিথ্যা পরবর্তীকালে জমা হতে থাকে। এসব মিথ্যা অন্যতম হল ইহুদিদের ভাষা। ইহুদিদের কাছে ভাষা মানুষের মনের গভীর ভাব ও চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের মাধ্যমে নয়। সে ভাব ও ভাবনা ঢেকে রাখার উপায়মাত্র। ইহুদিরা যতদিন অন্য কোন জাতিকে জয় করতে পারে না ততদিন তাদের দেশে গিয়ে তাদের ভাষা রপ্ত করে।
ইহুদি জাতির সমগ্র অস্তিতুটি যে মিথ্যায় ভরা তার প্রমাণ হল ইহুদিদের ধর্মশাস্ত্র কোন্ ধ্যানতন্ময়তা থেকে এ শাস্ত্ৰবাক্যের উদ্ভব তা কেউ জানে না। তবে এর থেকে ইহুদিদের ভাবধারা ও জাতীয় চরিত্রের অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা জানা যায়। তার সঙ্গে যে লক্ষ্যের দিকে তাদের সকল জাতীয় কর্মধারা প্রবাহিত হচ্ছে তাও জানা যায়। এমন কি তাদের সংবাদপত্রগুলোও এ শাস্ত্রের কোন মহত্ত্ব স্বীকার করতে চায় না। যে মুহূর্তে বিশ্বের মানুষ এ শাস্ত্র হাতে পাবে এবং তাতে কি আছে তা সব জানতে পারবে সেই মুহূর্তে ইহুদি জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এ পৃথিবী থেকে।
ইহুদিজাতিকে ভাল করে জানতে হলে কয়েক শতাব্দী আগে থেকে তাদের গতিবিধির কথা জানতে হবে। তাদের এ গতিবিধির ইতিহাসটিকে কয়েকটা স্তর বা পর্যায়ে ভাগ করে দেখালে ভাল হয়।
জার্মানিয়া নামে অভিহিত প্রথম কয়েকজন ইহুদি আসে রোমান আক্রমণের সময়। তারা আসে বণিকের বেশে, আপন জাতীয়তা গোপন করে। ইহুদিরা যখন আর্যদের ঘনিষ্ট সম্পর্কে আসে একমাত্র তখনি তাদের কিছু উন্নতি দেখা যায়।
(ক) স্থায়ী বসতি স্থাপিত হওয়া মাত্র ইহুদিরা সেখানে বণিকের বেশে উপস্থিত হয়। তারা তখন সাধারণত দু’টি কারণে তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়। প্রথমত তারা অন্যান্য জাতির ভাষা জানত না। একমাত্র ব্যবসাগত ব্যাপার ছাড়া আর অন্য বিষয়ে কোন কথা বলত না বা মিশত না কারো সঙ্গে। দ্বিতীয়ত তাদের স্বভাবটা ছলচাতুর্যে ভরা ছিল বলে কারো সঙ্গে মিল হত না তাদের।
(খ) ধীরে ধীরে তারা স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে তারা কোন উৎপাদকের ভূমিকা গ্রহণ করেনি, গ্রহণ করে দালালের ভূমিকা। হাজার হাজার বছর ধরে ব্যবসা করা সত্ত্বেও তাদের ব্যবসাগত চাতুর্য আর্যদের হার মানিয়ে দেয়। কারণ অর্থনীতির ক্ষেত্রেও আর্যরা সবসময় সততা মেনে চলত। কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারটা যেন ইহুদিদেরই একচেটিয়া কারবারে পরিণত হয়। তাছাড়া তারা চড়া সুদে টাকা দিতে থাকে। ধার করা ঢাকায় সুদের প্রবর্তন তাদেরই কীর্তি। এ সুদপ্রথার অন্তর্নিহিত জটিলতার কথাটা ভেবে দেখা হয়নি, সাময়িক সুবিধার জন্য এ প্রথা তখন মেনে নিয়েছিল সবাই।
(গ) এভাবে ইহুদিরা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে নিজেদের। ছোট বড় বিভিন্ন শহরের এক একটা অংশে বসতি গড়ে তোলে তারা। এক একটা রাষ্ট্রের মধ্যে গড়ে ওঠে এক একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। তারা ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারটাতে যেন একমাত্র তাদেরই অধিকার, আর এ অধিকার বশে প্রমত্ত হয়ে তার স্বর্ণ সুযোগ নিতে থাকে।
(ঘ) ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য লাভ করলেও ইহুদিরা যুদ্ধের কারবারের জন্য হেয় হয়ে ওঠে জনগণের কাছে। ক্রমে ইহুদিরা ভূ-সম্পত্তি অর্থাৎ জমি জায়গা প্রভৃতি নিয়েও কেনাবেচা করা শুরু করে। তারা অনেক জমি কিনে কৃষকদের খাজনার বন্দোবস্ত করে বিলি করতে থাকে। যে কৃষক তাদের বেশি খাজনা দিত, সেই কৃষক জমি চাষ করতে পারত। ইহুদিরা কিন্তু নিজেরা জমি চাষ করত না। তারা শুধু জমি নিয়ে ব্যবসা করত। ক্রমে ইহুদিদের অত্যাচার বেড়ে উঠলে ঋণগ্রস্ত জনগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তাদের বিরুদ্ধে। তৎক্ষণাৎ স্থানীয় অধিবাসীরা ইহুদিদের স্বরূপ বুঝতে পারে। তাদের সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। ইহুদিদের জাতীয় চরিত্রের অশুভ বৈশিষ্ট্যগুলোকে তখন তারা খুঁটিয়ে দেখতে থাকে।
চরম দুরবস্থার মধ্যে পড়ে জনগণ প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং ইহুদিদের বিষয়সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নেয়। তখন তারা ইহুদিদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করতে থাকে এবং তাদের দেশে ইহুদিদের উপস্থিতি বিপজ্জনক বলে ভাবতে শুরু করে।
(ঙ) ইহুদিরা এবার খোলাখুলিভাবে আপন স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তারা সরকারকে হাত করে, তোষামোদ দ্বারা প্রশাসনের লোকজনদের বশীকৃত করে টাকা উৎকোচ দ্বারা অনেক অসৎ কাজ করিয়ে নেয়। এভাবে তারা শোষণের সুবিধা করে নেয়। ক্রুদ্ধ জনগণের কোপে পড়ে তারা একসময় বিতাড়িত হতে বাধ্য হলেও আবার তারা ফিরে আসে। আবার তারা সেই ঘৃণ্য ব্যবসা শুরু করে দরিদ্র জনগণকে শোষণ করতে থাকে।
এ ব্যাপারে ইহুদিরা যাতে বেশি দূর এগোতে না পারে তার জন্য আইন প্রণয়ন করে কোন ভূ-সম্পত্তির অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়।
(চ) রাজা মহারাজাদের শক্তি যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে ইহুদিরা তাতেই তাদের দিকে ঢলে। তাদের তোষামোদ করতে থাকে। তাদের কাছ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ ও সুবিধে লাভের চেষ্টা করে। মোটা মোটা টাকার বিনিময়ে রাজা রাজরাও তাদের সেইসব সুযোগ দিতে থাকে। কিন্তু ধূর্ত ইহুদিরা রাজাদের যত টাকাই দিক, অল্প সময়ের মধ্যে তারা কম শোষণ করে না। রাজাদের টাকার দরকার হলেই নতুন সুবিধাভের জন্য ইহুদিরা আবার তাদের টাকা দিত। এভাবে রক্তচোষা জেঁকের মত একধার থেকে সকল শ্রেণীর লোককে শোষণ করত তারা।
এ বিষয়ে জার্মান রাজাদের ভূমিকা ইহুদিদের মতই ছিল সমান ঘৃণ্য। তাদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই এতখানি উদ্ধত হয়ে ওঠে ইহুদিরা এবং তাদের জন্য জার্মান জনগণ ইহুদিদের শোষণ থেকে মুক্ত করতে পারছিল না নিজেদের। পরে অবশ্য জার্মান রাজারা শয়তানদের কাছ থেকে নিজেদের বিক্রি করে বা চিনে নিয়ে তার প্রতিফল হাতে হাতে পায়। শয়তানদের প্রলোভনে তাদের দেশের জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে একথা বুঝতে পারে।
(ছ) এভাবে জার্মান রাজারা ইহুদিদের প্রলোভনে ধরা দিয়ে শ্রদ্ধা ও সম্মান হারিয়ে ফেলে। শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভের পরিবর্তে তাদের ঘৃণা করতে থাকে দেশের জনগণ। কারণ রাজারা তাদের প্রজাদের স্বার্থ রক্ষা করতে সমর্থ তো হয়ইনি, বরং প্রকারান্তরে দেশের জনগণকে শোষণ করতে সাহায্য করত ইহুদিদের। এদিকে চতুর ইহুদিরা বুঝতে পেরেছিল জার্মান রাজাদের পতন আসন্ন। অমিতব্যয়ী জার্মান রাজারা যে অর্থ অপব্যয় করে উড়িয়ে দিয়েছে, সেই অর্থ জোগাড়ের জন্য তাদের একজনকে ধরে নিজেদের উন্নতি ত্বরান্বিত করে তুলতো তারা। টাকা দিয়ে তারা বড় বড় সম্পদও লাভ করতে থাকে। সমগ্র জার্মান সমাজ দুষিত হয়ে পড়ে ঘরে বাইরে।
(জ) এ সময় হঠাৎ এক রূপান্তর দেখা দেয় ইহুদিদের জগতে। এতদিন তারা সবদিক দিয়ে তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলেছিল। কিন্তু এবার তারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। খ্রিস্টান চার্চের যাজকেরা এক নতুন মানবসন্তান লাভ করে। ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট-এর আমলে কিন্তু জার্মান জনসাধারণ ইহুদিদের ইহুদি বলেই জানতো। সরকার গঠন করে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মধ্যে বিবাহ বন্ধ করতে না পারায় প্রতিবাদে ফেটে পড়ে গ্রেট। গ্রেটকে এককথায় কিছুতেই প্রতিক্রিয়াশীল বলা যেতে পারে না। রাজসভাতে ইহুদিরা যতই সম্মান পাক দেশের জনগণ কিন্তু তাদের বিদেশী বলেই মনে করত।
কিন্তু ইহুদি এবার জার্মান ভাষা শিক্ষা করতে শুরু করে। ব্যক্তিগত রক্তের সংমিশ্রণ না ঘটিয়েও তারা অপর জাতির ভাষা শিক্ষা করতে থাকে। কিন্তু এ ভাষা শিক্ষার ফলে তাদের অন্তরসত্তার বা স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয় না। তারা এ নতুন ভাষার মাধ্যমে তাদের প্রাচীন ভাবধারা প্রকাশ করতে থাকে।
কিন্তু ইহুদিরা কেন জার্মান ভাষা শিক্ষা করতে গেল তার কারণটা খুঁজে বার করা এমন কিছু কঠিন নয়। ইহুদিরাই জার্মান রাজশক্তির পতন ঘটিয়েছিল। এখন শুধু তাদের ওপর নির্ভর করে থাকাটা উচিত হবে না। তখন তারা যদি সমাজের সর্বস্তরে তাদের অর্থনৈতিক আধিপত্যকে প্রসারিত করে দিতে চায় তাহলে দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করতে হবে। সমাজের বুকে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবার জন্য এক নতুন ভিত্তিভূমি খাড়া করতে হবে আর এ জন্য চাই ভাষাশিক্ষা।
তারা একই সঙ্গে তাই আত্মসংরক্ষণ এবং আত্মপ্রসাদের নীতি অবলম্বন করতে চায়। তারা যতই ওপরে উঠতে থাকে ততই তাদের উচ্চাভিলাষের উচ্চতাটা মোহময় হয়ে ওঠে তাদের চোখের সামনে। একদিন প্রাচীনকালে বিশ্বজয়ের ও বিশ্বশাসনের যে অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি তাদের গোচর হয়েছিল, তখন সেই সুযোগের অপূর্বক্ষণ এসে গেছে বলে মনে হয় তাদের।
এভাবে রাজসভা থেকে জাতীয় জীবনের স্তরে ছাড়পত্র পায় ইহুদিরা। কিন্তু রাজসভা থেকে ইহুদিরা বিদায় নিলেও সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ রেখে যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মানসিক রূপান্তরের কথাটা জনসাধারণকে জানাতে চাইল যে তারা জনসাধারণের মঙ্গল এবং উন্নতি চায়। তারা তখন সারা পৃথিবী জুড়ে ঢাক পিটিয়ে প্রচার করতে লাগল তারা জনগণের দুঃখ কষ্টে গভীরভাবে দুঃখিত এবং আন্তরিকতার সঙ্গে তারা এর প্রতিকার করতে ইচ্ছুক। আরো বলতে লাগল যে তাদের ওপর সকলে অবিচার করে এসেছে। অত্যাচার করে এসেছে। অনেক নির্বোধ লোক তাদের এ কথায় বিশ্বাস করে তাদের করুণার চোখে দেখতে লাগল।
ফলে অল্পদিনের মধ্যে জগতের সবাই জানল ইহুদিরা একেবারে বদলে গেছে। রূপান্তরিত হয়ে গেছে তাদের সত্তা। এমন উৎসাহের সঙ্গে ইহুদিরা মানব জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির কথা বলতে লাগল যে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল জগত্বাসী। কিন্তু সেই বিশ্বাসপ্রবণ নির্বোধেরা বুঝল না তাদের এ কপট পরদুঃখকাতরতা ও পরোপকার প্রবৃত্তিগুলো ইহুদিরা দামী সারের মত জগৎ জুড়ে ছড়িয়ে রেখেছে এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে। এ সারের ফলস্বরূপ তারা একদিন সেই জমিতে অনেক ভাল ফসল তুলবে।
ইহুদিরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঢোকার পর থেকে নানারকমের সমস্যা দেখা দেয়। তারা বিভিন্ন দেশের স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার কেনাবেচা শুরু করে। যৌথ কারবারের অংশীদার হয়। অতি লাভের আশায় তারা জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে মালিক শ্রমিকের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দেয়। এ বিরোধ কালক্রমে রাজনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে।
সর্বশেষে ইহুদিরা স্টক এক্সচেঞ্জে তাদের প্রাধান্য থাকার জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। বিভিন্ন কাজ কারবারের মালিকানা না পেলেও বিভিন্নভাবে এবং কৌশলে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রিত করতে লাগল।
শুধু অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয়, রাজনীতির ক্ষেত্রেও এবার প্রভাব বিস্তার করতে থাকে ইহুদিরা এবং এ উদ্দেশ্যে তারা জাতিগত ও নাগরিক বাধাগুলো দূরীকরণের কাজে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার ধর্মগত সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে থাকে। এ ব্যাপারে তাদের দ্বারা গঠিত ভ্রাতৃত্ব সংঘ তাদের সহায়তা করে। সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে অনেক বুর্জোয়া শিল্পপতিও তাদের ফাঁদে ধরা দেয়।
ইহুদিদের এসব পাতা ফাঁদে এতদিন শুধু সমাজে উঁচু তলার লোকরাই ধরা দিয়ে আসছিল। যে সাধারণ জনগণ নিজেদের বুঝতে চেষ্টা করেছিল, নিজেদের স্বাধীনতা ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামশালী হয়ে উঠছিল, সদাজাগ্রত এ জনগণ এতদিন দূরে ছিল তাদের পাতা ফাঁদ থেকে। কিন্তু ইহুদিরা জানত সমাজের গভীরতর স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হতে হলে এ বৃহত্তর জনসাধারণের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে।
এ উদ্দেশ্যে তারা ভ্রাতৃত্ব সংঘের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রগুলোও করায়ত্ত করতে চায়। জনমত প্রচারের যন্ত্রকে হাত করে কৌশলে লেখকের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে তারা। তারা কোন খ্রিস্টান মেয়েকে কিছুতেই বিয়ে করত না, অথচ খ্রিস্টানরা ইহুদি মেয়ে বিয়ে করত এবং সেক্ষেত্রে সেই বিয়ের ফলে জাত সন্তানদের ইহুদি বলে চালানো যেত। এভাবে তারা সব জাতের গর্ব খর্ব করতে চাইছিল। নিজেরা অন্য কোন জাতির মেয়ে ঘরে না এনে নিজেদের জাতিগত রক্তের শুচিতা রক্ষা করে যাচ্ছিল।
ইহুদিদের চাতুরী ও ধুর্তামি সত্ত্বেও সংবাদপত্রগুলো প্রচার করে বেড়াচ্ছিল যে ইহুদিরা মূলগতভাবে সৎ লোক, জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য তারা গণতন্ত্রের প্রসারের জন্য জোর প্রচার চালাতে লাগল। কারণ তারা জানত একমাত্র সংসদীয় গণতন্ত্রই তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সহায়ক হয়ে উঠবে। একমাত্র এ শাসনযন্ত্রেই ব্যক্তিগত গুণাবলীর কোন দাম দেওয়া হয় না। এবং অপদার্থ ও অযোগ্য লোকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।
এর ফলে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটে।
এক অভাবনীয় অর্থনৈতিক পরিবর্তন সমাজের কাঠামোটাকেই পাল্টে দেয়। আগে যেসব কর্মী কুটিরশিল্পে কাজ করত তারা কারখানা শ্রমিকের কাজ করতে এসে নিজেদের স্বাধীনতা হারিয়ে সর্বহারায় পরিণত হয়। কারখানা শ্রমিকের জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হল এ যে ভবিষ্যত বার্ধক্য জীবনের জন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারে তারা।
শিল্প বিপ্লবের ফলে যেসব কলকারখানা গড়ে উঠতে লাগল তাতে গ্রাম থেকে দলে দলে লোক এসে যোগদান করতে থাকে শ্রমিক হিসেবে। এরা আগে গ্রামে কুটিরশিল্পের কাজ করত। শহরের শ্রমিক জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত ছিল না তারা। তার ওপর কারখানার মালিকদের কাছ থেকে কোন সহানুভূতি পেত না। গ্রামের জমিতে যে সকল কৃষক মজুর কাজ করে তাদের সঙ্গে জমির মালিকদের সম্পর্ক ভালো; যেখানে মালিকরাও শ্রমিকদের সঙ্গে একসঙ্গে চাষের কাজ করে। মালিক শ্রমিকের কোন ভেদাভেদ নেই। কিন্তু শহরে কায়িক শ্রমকে ঘৃণার চোখে দেখা হয় বলে সেখানে কলকারখানার মালিকেরা শ্রমিকদের ঘৃণার চোখে দেখে, তাদের মানুষ বলে মনেই করে না।
কিন্তু কায়িকশ্রমের এ ঘৃণা আর শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের মধ্যে ভেদজ্ঞানের প্রবর্তন একান্তভাবেই ইহুদিদের অবদান। এ ধরনের ভেদনীতি জার্মানজাতির মধ্যে কোনদিন ছিল না।
এর ফলে যে শোষিত ও অবহেলিত শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব হল সমাজে, তারা কিন্তু মানুষ হিসেবে নিকৃষ্ট নয় মোটেই। তারাও যে বৃহত্তর সমাজের এক বিশেষ অপরিহার্য অঙ্গ একথা আমাদের অবশ্যই অচিরে একদিন বুঝতে হবে। তাদের কাছে টেনে নেব আপন করে, অথবা দূরে ঠেলে দেব, সরিয়ে রাখব অন্ত্যজশ্রেণী হিসেবে সে প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে।
এ শ্রমিকশ্রেণীর ওপর আধুনিক সভ্যতার ঘৃণ্য কুফল এ যুগে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কায়িক শ্রমের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল এসব লোক এ যুগের শান্তিবাদীদের অপ্রকৃতিস্থ দুর্বলতার শিকার হয়ে পড়েনি। তাদের মধ্যে যথেষ্ট সংগ্রামশীল প্রবৃত্তি আছে।
আমাদের সমাজের বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এ নতুন অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন থাকার জন্য ইহুদিরা এর পূর্ণ সুযোগ নিতে ছাড়ে না। তারা পুঁজিবাদী শোষণের এমন যন্ত্র গড়ে তোলে যার ফলে শ্রমিক মালিকের সম্পর্কে আরো অবনতি ঘটে। তখন মিথ্যাবাদী ইহুদিরা নির্দোষিতার নামাবলী গায়ে দিয়ে বেড়াতে থাকে।
একদিন এ ইহুদিরাই সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে পুঁজিবাদীদের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিল; সেই ইহুদিরাই আজ শ্রমিক মালিকের মধ্যে ভেদনীতি জাগিয়ে বুর্জোয়া মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তোলে। ভাবে এর দ্বারা শ্রমিক সমাজের সমর্থন ও শ্রদ্ধা লাভ করে তাদের ওপর সর্বদা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে।
অথচ শ্রমিকেরা বুঝতে পারে না এক্ষেত্রেও তারা ধূর্ত ইহুদিদের উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হয়ে কাজ করেছে। স্টক এক্সচেঞ্জের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে যে আন্তর্জাতিক পুঁজিকে হাত করেছে ইহুদিরা; বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণী স্বদেশের জাতীয় পুঁজির গায়ে আঘাত হেনে প্রকারান্তরে আন্তর্জাতিক পুঁজির পুষ্টি ও সহায়তা সাধন করে চলেছে।
প্রথম প্রথম ইহুদিরা এক বিরাট ভণ্ডামীর সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর দুঃখে মায়াকান্না কেঁদে তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর ভাণ করে। যে পরদুঃখকাতরতা ও সামাজিক মঙ্গলের জন্য ব্যাকুলতা আর্যদের জাতীয় চরিত্রের একটি মহৎ গুণ, সেইগুণের প্রমাণ দেবার চেষ্টা করে তারা। তারপর তাদের তথাকথিত সামাজিক অন্যায় অপসারণের জন্য সংগ্রামকে এক দার্শনীক রূপ দান করার মতলব নেয়। আর তার জন্যই মার্কসবাদের উদ্ভাবন।
ইহুদিরা এ তত্ত্ব সমস্বরে বিশ্বে প্রচার করে বেড়ালেও অনেক বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত ব্যক্তি এ তত্ত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করে। কারণ তারা বলে এ দার্শনিক তত্ত্বকথার অন্তরালে এক শয়তানসূলভ প্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে। এ তত্ত্বের মধ্যে মানবিক যুক্তি, মানবিক অবাস্তবতা ও অযৌক্তিকতা এমনভাবে মিশে আছে যাতে অবাস্তব অযৌক্তিক দিকটির প্রকাশ দেখা যায় সর্বত্র। যে ব্যক্তিগত ও জাতিগত যোগ্যতা মানবসভ্যতার মূল ভিত্তি, সে যোগ্যতার সকল গুরুত্বকে অস্বীকার করে এ তত্ত্ব সভ্যতার ভিত্তিমূলেই আঘাত হানে। এভাবে ব্যক্তিগত ও জাতিগত ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্যের ধারণাকে নস্যাৎ করে দেওয়ায় ইহুদিদের সামাজিক আধিপত্যলাভের সঙ্গে বাধাগুলোও অপসারিত হয়।
মার্কসবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকগুলো অবাস্তব। এর মধ্যে যে যুক্তি আছে তা আপাত দৃষ্টিতে জোরালো মনে হলেও আসলে তার কোন ভিত্তি নেই, যাদের বুদ্ধিবৃত্তি কম, অর্থনীতি সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, তারাই এ মতবাদের সমর্থক।
এ মতবাদকে অবলম্বন করে ইহুদিদের নেতৃত্বে এক শ্রেণীর শ্রমিক এক ধরনের আন্দোলন শুরু করে। ওপর ওপর এ আন্দোলন শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে চাইলেও আসলে অ-ইহুদি জাতিদের ধ্বংস করাই ছিল সেই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।
একদিন ভ্রাতৃত্ব সংঘের লোকেরা বিশ্বপ্রেম প্রচারের মাধ্যমে জাতীয় আত্মরক্ষার নীতিকে বিকল করে দেয়। আজ ইহুদিদের পরিচালিত সংবাদ পত্রগুলি সেই প্রচারের ভার নিয়েছে। এবং শ্রমিক ও বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্পর্ককে দূষিত করার চেষ্টা করছে। তার ওপর মার্কসবাদী উগ্রপন্থীরা তাদের বিরোধী পক্ষের ওপর নির্মমভাবে আঘাত চালিয়ে আসুরিক শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। মার্কসবাদী শক্তিলাভের সম্মিলিত আক্রমণের ফলে অনেক রাস্ত্রীয় শক্তির ভিত্তি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর ওপরে ইহুদিরা কৌশলে প্রভাব বিস্তার করে। এসব অত্যুৎসাহী উগ্রপন্থী মার্কসবাদী সমাজের ছোট বড় কাউকেই মানতে চায় না; কাউকেই মানুষ বলে জ্ঞান করে না।
ইহুদিদের দ্বারা পরিচালিত শ্রেণী-সগ্রামের রূপটি প্রকাশ করতে গেলে এ দাঁড়াবে; সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক আধিপত্য লাভ করে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হতে পারেনি ইহুদিরা। তারা রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এ উদ্দেশ্যে তারা মার্কসীয় তত্ত্বটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেখে। সেই দুটো ভাগ হল রাজনৈতিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এ দুটি আন্দোলন আলাদা হলেও আসলে কিন্তু তারা একই উদ্দেশ্যসঞ্জাত।
স্বার্থপর, অর্থলোভী, সংকীর্ণমনা পুঁজিপতি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে পরিচালিত শ্রমিকশ্রেণীর সগ্রামে ট্রেড ইউনিয়নগুলো শ্রমিকদের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে চলে। শ্রমিকেরা যতদিন না মানুষের মত বাঁচার জন্য যা দরকার তা না পায় ততদিন তারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। শুধু তাই নয় শ্রমিকদের কাজের সময় কম করে দেওয়া, শিশু শ্রমিক নেওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে আইন প্রণয়নে বাধা দেয় তারা। বুর্জোয়ারা যখন এভাবে শ্রমিকদের সংগ্রামে বাধা দিতে থাকে তখন কঠিন প্রকৃতির ইহুদিরা নিপীড়িত শ্রমিক-শ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করে সমগ্র ব্যাপারটা নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ায় রাতারাতি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার নেতা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তারা জানত এভাবে তারা বিরাট শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের সমর্থক হিসেবে কাজে লাগাতে পারবে। কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু শ্রমিকদের উন্নতির বা অগ্রগতি ছিল না; তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের অর্থনৈতিক যুদ্ধে এক সশস্ত্র হাতিয়াররূপে ব্যবহার করে জাতীয় অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র ও উন্নতিকে ধ্বংস করে দেওয়া। তাদের এ উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে তারা শ্রমিকদের কাছে এমন সব শর্ত উত্থাপন করত যে সেসব শর্ত মেনে নেওয়া কখনই কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তারা জানত এসব শর্ত কেউ পূরণ করতে পারবে না। তা করা সম্ভবও নয়। তবু শ্রমিকদের সংগ্রামকে ধ্বংস করার জন্যই তারা এমন সব অসঙ্গত দাবি তোলে। এভাবে আসলে তারা জাতীয় পর্যায়ে এক বিরাট অশান্তি জাগিয়ে রাখতে চায়।
ইহুদিরা তাই ট্রেড ইউনিয়নের অবিসম্বাদিত নেতা হয়ে যায়। যতদিন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে জোর প্রচারকার্য চালানো না হয়, ততদিন তারা এভাবেই নেতা হয়ে যাবে। যতদিন না জনগণ ঠিক মত বুঝতে পারে এবং ইহুদিদের ছল চাতুরীর কথা জানতে না পারে ততদিন ইহুদিদের বড় বড় প্রতিশ্রুতির কথায় বিশ্বাস করে যাবেই।
সহজে এবং স্বাভাবিকভাবেই ইহুদিরা তাদের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরিয়ে দেয় এ ক্ষেত্র থেকে। ক্রমে তারা তাদের স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার বশে ট্রেড-ইউনিয়ন সংস্থাগুলোকে বলপ্রয়োগের মাধ্যম হিসেবে পরিণত করে। ইহুদিদের একনায়কতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ না করে যারা তাদের বাধা দেয়, এক ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয় ইহুদিরা।
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন মূলত অর্থনৈতিক আন্দোলন হলেও এ আন্দোলনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে থাকে ইহুদিরা। ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার সদস্যরা রাজনৈতিক মিছিল বার করে এবং রাজনৈতিক কার্যাবলীতে তৎপর হয়ে ওঠে। অবশেষে শ্রমিকরা ধর্মঘট ঘোষণা করে তাদের অর্থনৈতিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দালনে পরিণত করে।
এ কাজে তাদের ইহুদিদের দ্বারা প্রভাবিত সংবাদপত্রগুলি সাহায্য করে। সংবাদপত্রগুলি জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের কোন চেষ্টা না করে তাদের মধ্যে কু-প্রবৃত্তি সঞ্চারিত করার চেষ্টা করে। এ সংবাদপত্রগুলোই নানারকম মিথ্যা প্রচারের দ্বারা জাতীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তিটিকে বিপর্যস্ত করে দেয়।
সুচতুর ইহুদিদের কেউ আক্রমণ করার আগেই তারা ওদের আক্রমণ করে। যারা ওদের আক্রমণ করতে আসে ওরা শুধু ওদের আক্রমণ করে না, যারা ওদের আক্রমণে বাধা দেয় আত্মরক্ষার খাতিরে ওরা তাদেরও শক্ত বলে মনে করে। ইহুদিদের আসল মনোভাব ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণ জনগণের কোন জ্ঞান না থাকার ফলে তারা সহজেই ইহুদিদের কু-প্রকৃতি ও কু-অভিসন্ধির শিকার হয়ে ওঠে। সরলতা ও অজ্ঞতাবশত সাধারণ মানুষ বিশ্বাসপ্রবণ হয়ে থাকে এবং তারা সহজে যে কোন প্রচারে কান দেয় ও তা বিশ্বাস করে। তারা বুঝতে পারে না ইহুদিরা মার্কসবাদকে তাদের এক অশুভ উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়।
তখন ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে এক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করে এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে নিজেদের যে তারা তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ ও তথ্য ধারাগুলো স্বাচ্ছন্দে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করে চলে। আসলে তারা নিজেদের ফরাসী জার্মান প্রভৃতি ভিন্ন জাতির লোক বলে সরলমনা সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করতে চাইছে। কিন্তু রাষ্ট্রের খাতিরে তারা রাষ্ট্র গঠন করতে চায় না। বস্তুত তারা রাষ্ট্রের নামের একটি বৈধ ও সার্বভৌম সংগঠনের মাধ্যমে সারা বিশ্বব্যাপী প্রতারণা ও জুয়াচুরির জাল বিস্তার করতে চায়। জুয়াচুরি ও প্রতারণার এক বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে আগ্রহী।
তার ওপর কৃষ্ণকেশ ব্যভিচারী ইহুদী যুবকেরা পথের ধারে ঘন্টার পর ঘণ্টা ধরে বসে থেকে বিজাতীয় মেয়েদের শালীনতা নষ্ট করতে চায়। তাদের জারজ নানা সংমিশ্রিত গরল ঢেলে সেইসব নিরীহ মেয়েদের রক্তকে কলুষিত করার চেষ্টা করে। কারণ তারা জানে যে জাতি তাদের জাতিগত রক্তের শুচিতা সম্পর্কে সচেতন তারা কখনই ইহুদীদের আদিপত্য মেনে নেবে না। অবৈধ জারজ সন্তানে পরিপূর্ণ কোন জাতি ছাড়া অন্য কোন জাতির ওপর ইহুদীরা কখনই প্রভূত্ব করতে পারবে না।
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহুদীরা গণতন্ত্রের জায়গায় সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। কারণ তারা জানে মার্কসবাদের পতাকাতলে সাধারণ জনগণকে সংঘবদ্ধ করে একনায়কতন্ত্রের ধাঁচে তাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে আসুরিক শক্তির দ্বারা দেশ শাসন করা সহজ হবে তাদের পক্ষে। যেসব শক্তিশালী জাতি ইহুদীদের প্রভাব মানতে চায় না, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে সেইসব জাতির চারদিকে শত্রু খাড়া করে তুলেছে।
অর্থনীতি ও রাজনীতি দুদিক থেকেই বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতিগুলির বনিয়াদ ধ্বংস করতে চায় ইহুদী। রাষ্ট্রায়ত্ত শরিকানা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষতিসাধন করে তারা যেমন জাতীয় অর্থনীতির ধ্বংস করতে চায়, তেমনি সরকার ও জনগণের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে জাতির প্রতিরক্ষাগত শক্তির ভিত্তিকে নষ্ট করে ফেলতেও সচেষ্ট থাকে।
জাতীয় সংস্কৃতির মূলেও আঘাত হানতে চায় তারা। শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুন্দর ও মহত্বের ধারণাটিকে জাতিপ্ৰীতির নাম করে নষ্ট করে ফেলে সাধারণ মানুষের মনকে তাদের মত নিচ ও সংকীর্ণ করে তোলে।
ধর্মের ক্ষেত্রটিও তারা প্রহসনের এক রঙ্গভূমিতে পরিণত করে। নীতিবোধ ও শালীনতাবোধ প্রভৃতিকে প্রাচীন কুসংস্কার বলে অভিহিত করে জাতির নৈতিক ধারণাকে নামিয়ে আনতে চায় তারা।
যখনি ইহুদীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে, তখনই তারা সব অবগুণ্ঠন ঝেড়ে ফেলে স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। তখন তারা জনগণের হর্তাকর্তা সেজে জনগণের ওপর অত্যাচার করতে শুরু করে। সমগ্র জাতির বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে।
রাশিয়া হল এ অত্যাচারের ভয়ঙ্কর লীলাভূমি। এ দেশে ইহুদীরা তিন কোটি লোককে হত্যা করে অথবা না খেতে দিয়ে শুকিয়ে মারে। এদের মধ্যে কিছু লোককে পীড়নমূলক কাজ করিয়ে মারা হয়। ওইসব কিছুর মূলে ছিল কিছু সংখ্যক ইহুদী যারা দেশের ওপর প্রভূত্ব করবে।
কিন্তু এর শেষ পরিণাম বড় ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এর ফলে জনগণ অবশ্য ইহুদীদের ক্ষমতাধীনে আসে; কিন্তু পরে সেইসব অত্যাচারী ইহুদীদেরও বিদায় দেয়। শিকারের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে নেমে আসে শিকারীর মৃত্যু।
আমরা যদি আমাদের জার্মান জাতির অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান করি তাহলে দেখব সেই কারণটা হল জার্মানরা ইহুদি সমস্যাটাকে তত গুরুত্ব দেয়নি। ইহুদী সমস্যা সঞ্জাত যে বিপদ সমগ্র জাতির পক্ষে এত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে সে বিপদের কথা তারা মোটেই ভাবেনি। তা যদি আগে থেকে ভাবত তাহলে ১৯১৮ সালের আগস্ট মাসের প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করাটা খুব একটা কষ্টকর হত না। আমাদের পরাজয়ের কারণ শুধু যুদ্ধক্ষেত্রের হার নয়, যে রাজনৈতিক প্রেরণা ও প্রবৃত্তি এবং নৈতিক শক্তি জাতির জীবন সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে, জাতির অস্তিত্বকে সমৃদ্ধ করে তোলে সর্বতভাবে, কয়েক দশক ধরে সুপরিকল্পিতভাবে সেই জাতীয় রাজনৈতিক প্রবৃত্তি ও নৈতিক শক্তির মূলে কুঠারাঘাত হানা হচ্ছিল।
যে শক্তি ও গুণাবলী জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি সে শক্তি ও গুণাবলীকে অবহেলা করে তাদের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা না করে জার্মানরা ভুল করেছিল। অথচ এ শক্তি ও গুণাবলী তাদের সহজাত, প্রকৃতিদত্ত।
কিন্তু যে কোন পরাজয়ই অপূরণীয় ক্ষতির বাহক নয়। যে কোন খারাপ থেকে অনেক কিছু ভাল করা যায়। যে কোন পরাজয়কে ভিত্তি করে ভবিষ্যতে জয়ের সৌধ গড়ে তোলা যায়। যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে অনেক জাতি পরবর্তী যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। অনেক দুঃসহ অত্যাচারের ভেতর থেকে এমন এক অদম্য শক্তি জন্মলাভ করে যা একদিন সমস্ত অধঃপতিত জাতিকে মুক্তি এনে দেয়।
কিন্তু যে জাতি তাদের জাতিগত রক্তের শুচিতা হারিয়ে ফেলে, সেই জাতি একবার অধঃপতিত হলে আর কোনদিন উঠে দাঁড়াতে পারে না। এ রক্তের শুচিতা হানি থেকে যে ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি আর পূরণ হয় না কোনদিন। যে কোন জাতি বা সভ্যতার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক অবক্ষয় বা অবনতির মূলে আছে এ একই কারণ। জাতিদের অন্তনিহিত শক্তি একেবারে ক্ষয় হয়ে গেলে সে জাতিকে তখন আর বাঁচানো যায় না।
এ কারণেই কোন রাজনৈতিক তৎপরতা, অর্থনৈতিক উন্নতি, সংস্কৃতির সংস্কার বা জ্ঞানের সঞ্চয়-কোন কিছুই বাঁচাতে পারেনি জার্মান জাতিকে। কোন সুফলই দান করতে পারেনি এসব কিছু। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের কপট উজ্জ্বলতা, তার কপট দৈন্য বা দূর্বলতাকে সমস্যার মূলে সে যেতে পারেনি বা তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনি।
জার্মানির যে সব রাজনৈতিক দল দেশের জাতীয় দুরবস্থার উন্নতি ঘটাবার চেষ্টা করেছিল, তারা রোগের মূল ধারাটিকে ধরতে না পেরে শুধু তার উপসর্গগুলি সারাবার চেষ্টা করেছিল। নির্বাচনে বুর্জোয়া দলগুলি জয়লাভ করলেও মার্কসবাদী ভোটের সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে থাকে। মার্কসবাদের বিষ সারা দেশে সব দলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।
১৯১৪ সালে যে জার্মান জাতি মহাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সে জাতি এক সুদৃঢ় জাতীয় প্রেরণার বশবর্তী হয়ে ছুটে যায়নি। এক নির্বাপিত-প্রায় আত্মরক্ষা প্রবৃত্তির শেষ উজ্জ্বলতা ও অগ্নি-প্রেরণার বশেই সে জাতি যুদ্ধে যোগদান করে। শান্তিবাদী ও মার্কসবাদী নীতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জাতির গভীরে যে অবক্ষয় ও পক্ষাঘাত ঘিরে ধরেছিল তার বিরুদ্ধে জার্মান জাতি বাইরে জেহাদ ঘোষণা করলেও ভেতরে ভেতরে তারা ক্রমশ ক্ষয় হয়ে আসছিল।
অবশ্যই এ যুদ্ধের বিজেতাদের ঈশ্বর বিশেষ কোন পুরস্কারে ভূষিত করেনি। বরং অনুশোচনার যন্ত্রণায় ভরে ওঠে তাদের মন। আর তখনই আমরা সেই আসল সত্যটি বুঝতে পেরে তাকে স্বীকার করে নেই। এবং নতুন উদ্যমে এক প্রস্তর কঠিন ভিত্তির ওপর জাতীয় উন্নতির নতুন সৌধটির প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করি।