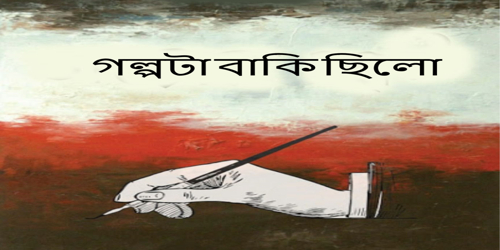০৯. দ্বিতীয় রাইখের বিপর্যয়ের কারণ
পতনের গভীরতার পরিমাপ হল তার আসল জায়গার উচ্চতার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার বিয়োগাঙ্ক। একটা জাতির এবং রাষ্ট্রের পতনের পরিমাণের ক্ষেত্রেও এ কথাটা সত্য। স্থানের উচ্চতার পরিমাপ, অথবা সোজাসুজি বলতে গেলে বলতে হয় অবরোহণের পূর্বে তার সবচেয়ে উচ্চস্থানে অবস্থানের অঙ্কটা।
যা সবচেয়ে উঁচু জায়গায় একদা আরোহণ করেছিল, সেখান থেকেই পতন বা বিপর্যয়ই প্রত্যক্ষদর্শীদের সবচেয়ে বিস্ময়কর লাগে। দ্বিতীয় রাইখের বিপর্যয় তাদের উদ্ভ্রান্ত করেছিল যারা এটাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত এবং এর পতনকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিল। কারণ এ রাইখ এত উঁচু জায়গা থেকে অবরোহণ করে যা কল্পনাতেও আনা যায় না। আর এ পতন জাতি এবং দেশের চরম দুর্দশা আর লাঞ্ছনা ডেকে এনেছিল।
দ্বিতীয় রাইখের প্রভা এত উজ্জ্বল আর প্রখর ছিল যে সমগ্র জাতি এ জন্য গৌরববোধ করত। পর পর অনেক অসমতল যুদ্ধ জয়ের পর, সম্রাট সেইসব যুদ্ধ বিজয়ী নায়কদের পুত্র এবং প্রপৌত্রদের হাতে এমন এক পুরস্কার তুলে দিয়েছিলেন, যা অকল্পনীয়। তারা অবশ্য এ বিষয়ে সচেতন বা অচেতন ছিল সেটা কোন কাজের কথা নয়। যাই হোক সমগ্র জার্মান জাতি এটা অনুভব করত যে এ পুরস্কার ধারাবাহিকভাবে কতগুলো আলোচনার মাধ্যমে আসেনি। এ রাষ্ট্রের সংস্থাপনা হয়েছে অন্যভাবে, যা নাকি আলোচনার মাধ্যমের চেয়ে অনেক মহৎ। এ রাষ্ট্রের যখন ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়, তখন সংসদীয় গুণশুনানির মধুর সঙ্গীত একে সঙ্গ দেয়নি। বরং প্যারীকে ঘিরে যে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছিল, সেই সঙ্গীতের মধ্যেই হয়েছে এর অভিষেক। এ পথ বেয়েই রাষ্ট্রনেতারা অভ্যর্থিত হয়েছিল সমগ্র জাতির কাছে। ভবিষ্যত রাইখেরও প্রতিষ্ঠা এখানেই। এর মাধ্যমেই রাজকীয় মুকুট মাথায় উঠেছিল। বিসমার্কের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়নি কতগুলো বিশ্বাসঘাতক আর কর্তব্যে অবহেলা করা লোকের দ্বারা। এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সত্যিকারের সৈনিক দিয়ে–যারা রক্ত ঢেলে সীমান্তে সংগ্রাম করেছে। এ অবাক করা জন্য এবং পবিত্রতার দীক্ষিত আগুন দ্বিতীয় সম্রাট সম্পর্কে ধর্মান্ধে আত্মবিসর্জনকারী ব্যক্তি স্বর্গীয় মুকুট তুলে দিয়েছিল, যার ঐতিহাসিক গৌরব অল্প কয়েকটা পুরনো রাষ্ট্রেরই অধিকারে ছিল।
কী তীব্র গতিতে এ আরোহণ ক্রিয়া শুরু হয়েছিল। স্বাধিনতা দেশের মধ্যে জীবিকার গ্যারান্টি দিয়েছিল। জাতি লোকসংখ্যার দিক থেকেও বেড়ে চলেছিল এবং জাগতিক সম্পদেরও সমৃদ্ধি হচ্ছিল। রাষ্ট্রের সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে জাতির সম্মানেরও নিরাপত্তা ছিল এবং সৈন্যবাহিনীর দ্বারা তা সুরক্ষিত ছিল; এটাই ছিল নতুন রাইখ আর পুরনো জার্মান জাতির পার্থক্য।
কিন্তু দ্বিতীয় সম্রাটের এবং জার্মান জাতির পতন এত সুগভীর হয়েছিল যে সবাই একেবারে হতবুদ্ধি অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল। এবং যার অবশ্যম্ভাবী প্রতিচ্ছায়া জনসাধারণের চোখে ধরা দিয়েছিল। সবকিছু দেখে মনে হয় সম্রাট এত উঁচুতে গিয়ে পৌঁছেছিল যে সাধারণ লোকে তা চিন্তার মধ্যেই আনতে পারেনি। বর্তমান দিনের তুলনায় গৌরবের সেই দিনগুলো কাল্পনিক এবং অবাস্তব বলেই মনে হয়। এসব মনে রাখলে আমরা বুঝতে পারব কেন লোকেরা এত হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। যখন তারা সম্ভ্রমের সঙ্গে অতীতটাকে চিন্তা করত, তখন পতনের লক্ষণগুলো নিশ্চয়ই তাদের নজর এড়িয়ে গেছে, যেগুলো নিশ্চয়ই কোন একপ্রকার অবয়বে ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে উপস্থিত ছিল। অবশ্যই এ কথাগুলো তাদের ক্ষেত্রে সত্য, জার্মানি যাদের কাছে শুধুমাত্র বাসস্থান বা জীবিকা আহরণের ক্ষেত্রমাত্র ছিল না। তাদের পক্ষেই একমাত্র বর্তমান অবস্থা প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে বোধ হবে। আর অন্যদের চোখে এটা হবে নীরবে এতদিন ধরে তারা যে ইচ্ছে করে এসেছে, সেই ইচ্ছাপূরণ।
ভবিষ্যতের বিপর্যয়ের লক্ষণ বলে নিশ্চয়ই সেই দিনগুলোতে অনুভূত হয়েছে, যদিও খুবই অল্প সংখ্যক লোক এ রহস্যভেদের চেষ্টা করেছে। কিন্তু বর্তমানে অন্যকিছুর চেয়ে সেই লক্ষণগুলোই খুঁজে বার করার অত্যধিক প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শারীরিক রোগ নির্ণয় যেমন তখনই সম্ভব, যখন তার লক্ষণগুলো ধরা যায়; তেমনি রাজনীতির ক্ষেত্রেও এটা একই রকমের সত্য। বাইরের ফুটে ওঠা রোগের কারণগুলো খুঁজে বার করা ভেতরের কারণগুলোর থেকে যেমন সহজ, কারণ সেগুলো সোজাসুজি চোখকেআকর্ষণ করে। এ কারণেই অনেকে বাইরের লক্ষণগুলো দেখে রোগ নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছিল। এবং বলাবাহুল্য তারা ব্যর্থও যে হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সত্যি বলতে কি অনেক সময়েই তারা চেষ্টা করে এ অন্তনিহিত কারণগুলোর অস্তিত্ব এড়িয়ে যেতে। এবং এ কারণেই আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোক অর্থনৈতিক দুর্দশাই এ পতনের মূল কারণ বলে ধরে নিয়েছিল। প্রত্যেকেই তার অংশের দায়টুকু বহন করতে হয়েছে এবং সেই কারণে অর্থনৈতিক দুর্ঘটনাই বর্তমানের শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী বলে ভেবেছে। সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক অধঃপতনই এ বিপর্যয়ের কারণ। অনেকেরই এ দুই জিনিস বোঝার ক্ষমতা অর্থাৎ প্রয়োজনীয় অনুভূতি এবং বোঝার মত জ্ঞান থাকে না।
এ জন্যই জার্মানির পতনকে জনসাধারণের বিরাট গোষ্ঠী কিসের জন্য মেনে নিয়েছিল তা বোঝা যায়। কিন্তু এর চেয়ে সত্য হল বুদ্ধিমান গোষ্ঠীও জার্মানির এ পতনের কারণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় বলে ধরে নিয়েছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা ধারণা করেছিল এর আরোগ্য সম্ভব একমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতিতে। আমার মতে এ কারণেই জার্মানির কোনরকম উন্নতি সাধিত হয়নি। কোন উন্নতিই সম্ভব নয় যতক্ষণ না জাতি বুঝতে পারছে যে অর্থনৈতিক চেতনা জাতির উন্নতির দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের বিষয়। এবং জাতির উন্নতির মূল কারণ হল রাজনৈতিক, নৈতিকতা এবং সম্প্রদায়গত কারণগুলো। একমাত্র বর্তমানের শয়তানগুলোকে বোঝা সম্ভব, যখন এ কারণগুলো উপলব্ধি করা যাবে এবং তখনই তার রোগ নিরাময়ের প্রতিশোধের ও খুঁজে বার করা সম্ভব হবে।
সুতরাং জার্মানির পতনের রহস্যটা ভেদ করা অতীব প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে এ বিপর্যয়কে যদি অতিক্রম করতে রাজনৈতিক কোন আন্দোলন আরম্ভ করতে হয়, তবে এটা জানা থাকা তো অতি আবশ্যক।
জার্মানির টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে অতীতকে বিশ্লেষণ করার সময় সতর্ক থাকার প্রয়োজন এ কারণে যে বাইরের রোগের লক্ষণগুলো যেন আমাদের প্রতারণা করতে না পারে। কারণ সেগুলোই আমাদের চোখে প্রথমে ধরা পড়ে অব্যক্ত কারণগুলোকে আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবে।
অত্যন্ত সহজবোধ্য বলে এবং সেই কারণে বেশিরভাগ লোকের বর্তমানের দুর্দশা মেনে নেওয়া কারণগুলো হল যুদ্ধে পরাজয়। এবং সত্যি বলতে কি এটাই বর্তমান দুর্ভাগ্যের মূল কারণ। সম্ভবত অনেকেই এটা মনপ্রাণ থেকে বিশ্বাস করে থাকে। আবার অনেকে সচেতন মনে এবং ইচ্ছে করে মিথ্যা জেনেও বিশ্বাস করার ভাণ করে। বিশেষ করে সরকারি ঢাকনাবিহীন ভাণ্ডার যারা লুটে খাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বিপ্লবের অবতারণা বারে বারে জনতাকে বুঝিয়েছে যে যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, জনসাধারণের কাছে তার কোন মূল্য নেই। উপরন্তু তারা এক হয়ে বলেছে ধনীরা হল এ মহাযুদ্ধের জয়লাভের স্বপক্ষে। সাধারণ জার্মান নাগরিক এবং শ্রমিক শ্রেণীর কোন উৎসাহ-ই নেই এ ব্যাপারে, যুদ্ধের ফলাফল যাহোক না কেন। সত্যি করে বলতে গেলে, এ অবতাররা নিশ্চিত হয়ে বলেছে যে জার্মানির পতনের কোন সম্ভাবনা নেই, বরং উন্নতির সম্ভাবনাই সমধিক। একবার যদি সামরিক ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া যায় তবে জার্মানির পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। এ চক্র কি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রীর গানে চারিদিক মুখরিত করে এ রক্ত পিপাসু যুদ্ধের অপরাধ জার্মানির কাঁধে চাপিয়ে দেয়নি? এ ব্যাখ্যা ছাড়া কি তারা এ তত্ত্ব প্রকাশ করতে পারত যে সাময়িক পরাজয়ের কোন প্রতিক্রিয়া রাজনৈতিক জগতে দেখা দেবে না, বিশেষ করে জার্মানদের ক্ষেত্রে? পুরো বিপ্লবটাকে কি ভোজ পানোৎসবে পরিণত করে জার্মানদের অগ্রগতি ব্যাহত করা হয়নি, যাতে স্বদেশে এবং বিদেশে জার্মানি বিজয়ীর সম্মান না পায়। মিথ্যাবাদী প্রতারকের দল, এটা কি সত্যি বলিনি?
এ ধরনের ধৃষ্টতা যা নিছক ইহুদী সৈন্যদের পরাজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল, এবং তা-ই হল জার্মানদের পরাজয়ের কারণ। বাস্তবিকপক্ষে বার্লিন ভোরওয়ার্থ ছিল রাজদ্রোহের প্রধান হোতা; তারাই সে সময়ে লিখেছিল যে জার্মান সৈন্যদের বিজয়ী হয়ে দেশে ফিরতে দেওয়া হবে না। এবং এসব সত্ত্বেও তারা আমাদের সামরিক পরাজয়ের জন্য দোষারোপ করে।
এ সব মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে কোনরকম বিতর্কে যাওয়া অনর্থক। যারা এ মুহূর্তে যা বলে পরের মুহূর্তেই তা অস্বীকার করে। এদের সম্পর্কে আমি আর কোন শব্দ ব্যয় করব না। কারণ তোতা পাখির মত অনেক চিন্তাহীন লোক আছে যাদের এটাই হল কাজ। এবং যারা এ কাজ করবে কোন খারাপ মতলব ছাড়াই। কিন্তু আমি যে পর্যবেক্ষণ করেছি তা হল আমাদের সগ্রামীদের জন্য; কারণ তারা তো কার্যক্ষেত্রে দেখতে পারে এ মুহূর্তে যা বলছে, পরের মুহূর্তেই তা ভুলছে এবং নিজের মত করে সেই কথাটা ঘোরাচ্ছে।
যুদ্ধে পরাজয়ই যে জার্মানির পতনের কারণ তার উত্তর ঠিক মত নিচে দেওয়া হল।
এটা সত্যি যে যুদ্ধে পরাজয় জার্মানির ভবিষ্যতের ওপর দুঃখজনক বিরাট একটা আঘাত হেনেছিল। কিন্তু যুদ্ধে পরাজয়টাই এর একমাত্র কারণ নয়। বরং অন্য কারণের ফলাফল হল এটা। এ জীবন মৃত্যু সংগ্রামের বিপর্যয়কর সমাপ্তি হল আকস্মিক ট্রেন দুর্ঘটনার মত; সুতরাং যাদের স্বচ্ছ এবং সোজাসুজি চিন্তাক্ষমতা আছে, তাদের পক্ষে ব্যাপারটা বোধগম্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তেমন লোকও বর্তমান ছিল, যারা সেই ভয়ানক মুহূর্তে তাদের চিন্তাক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছিল। এবং বাকিরা প্রথমে সত্যটাকে বোঝার চেষ্টা করেছে, তারপর পুরো ব্যাপারটাকে অস্বীকার করে বসেছে। অন্যান্যরা তাদের গুপ্ত বাসনা চরিতার্থের পর বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে দেখেছে যে পুরো ব্যাপারটাই ঘটেছে তাদের যৌথ সম্মেলনে। এরাই হল এ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। এবং যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যই কারণ নয়। যদিও তারা এখন সমস্ত বিপর্যয়ের জন্য যুদ্ধ পরাজয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিচ্ছে। সত্যি বলতে কি, তাদের কার্যের ফলাফল হল যুদ্ধে পরাজয়। এবং তাদের বর্তমানে দোষারোপের কেন্দ্র খারাপ নেতৃত্ব মোটেই এর জন্য দায়ী নয়। আমাদের শত্রুরা একেবারেই কাপুরুষ ছিল না। তারা এটাও জানত কি করে বীরের মতন মৃত্যুবরণ করতে হয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম দিনেই তারা জার্মানিকে পিছু হটিয়ে দিয়েছিল; দুনিয়ার অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা এবং গুদাম তাদের ব্যবহারের জন্য মজুদ ছিল; যার দ্বারা সাময়িক ক্ষয়ক্ষতি তৎক্ষণাৎ পূরণ করা যায়। বাস্তবিক পক্ষে সারা পৃথিবী স্বীকার করে নিয়েছে যে সুদীর্ঘ চার বছর ধরে জার্মানির জয় সমানুপাত হারে সম্ভব হয়েছে একমাত্র নেতৃত্বের দরুণ, সৈন্যদের বীরত্ব তো এর সঙ্গে আছেই। যা কিছু কমতি ছিল তা পূরণ করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়; এবং তা-ই স্বাভাবিক। তাই সেই সৈন্যদের বিপর্যয় আমাদের দুর্দশার কারণ নয়। এটা হল অন্য দোষগুলোর ফলাফল। এবং এগুলোই পতনটাকে আরো গভীরে টেনে নামিয়েছে; যা খোলা চোখে স্পষ্ট দেখা সম্ভব। এ সত্যিকারের কারণগুলো নিচে এভাবে দেখানো যেতে পারে :
সামরিক পরাজয় কি জাতি এবং দেশকে এভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে? যখন এটা দুর্ভাগ্যজনক কোন দুঃখের ফলাফল হয়? বাস্তবিকপক্ষে একটা যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য কি একটা জাতি ধ্বংস হয় এবং সেটাই কি একমাত্র কারণ হতে পারে?
এর উত্তর সংক্ষেপে দিতে গেলে বলতে হয়, অন্তদেশীয় ক্ষয়ই সামরিক পরাজয়ের কারণ। এবং তার সঙ্গে কাপুরুষতা, চরিত্রহীনতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা তো আছেই। এ কারণগুলো যদি সামরিক পরাজয়ের কারণ না হয়, তবে সামরিক পরাজয় জাতির পুনরুত্থানের সাহায্য করে এবং জাতিকে উন্নতির ওপরে স্তরে ক্ষেপন করে। সামরিক পরাজয় জাতির জীবনে কবরের স্মৃতি নয়। ইতিহাস খুঁজলে এ কথার যথার্থতার উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যাবে।
দুর্ভাগ্যজনকভাবে জার্মানির সামরিক পরাজয় আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা নয়। এটা হল চিন্তা-ভাবনা করে পাওয়া শাস্তি যা হল গিয়ে এ ব্যাপারের চিরন্তন প্রতিদান। এ পরাজয়ের আমাদের প্রয়োজন ছিল। কারণ এটা বাইরের কারণগুলো ত্যাগ করে ভেতরের কারণগুলোকে বিশ্লেষণ করতে শেখাবে। যদিও তারা প্রত্যক্ষ, কিন্তু বেশিরভাগ লোকই তা স্বীকার করে নেয়নি। যারা উটপাখির পন্থা অবলম্বন করেছে, যা দেখতে চায় শুধুমাত্র সেটাই দেখেছে।
জার্মানির লোকেরা যখন এ পরাজয় মেনে নিয়েছিল তখন যে লক্ষণগুলো জার্মানির গণজীবনে ফুটে উঠেছিল, আমরা এবার সেগুলোকে পরীক্ষা করে দেখি। এটা কি সত্যি নয় যে অনেকেই পিতৃভূমির এ দুর্বাগ্যে লজ্জাজনকভাবে উস্ফুল্ল হয়ে উঠেছিল? যদি তাদের ইচ্ছায় এ প্রতিশোধ না নেওয়া হয়ে থাকে, তবে এ ব্যাপারে কে এত উৎসাহী হবে? তেমন লোকও কি তাদের মধ্যে ছিল না, যারা এ বলে অহংকার করত যে তারাই সীমান্তকে দুর্বল করে দিয়ে জার্মানির এ বিপর্যয় ডেকে আনতে সাহায্য করেছে। সুতরাং শত্রুরা এ অসম্মান আমাদের কাঁধের ওপর চাপিয়ে দেয়নি, বরং আমাদের দেশবাসীই তা ডেকে এনেছে। তার জন্য যদি তারা পরে দুর্ভোগ বহন করে, তবে তা কি অনুপযুক্ত। পৃথিবীর ইতিহাস মন্থন করলেও কি এমন একটা দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে, যেখানে দেশবাসী নিজেরাই নিজেদের যুদ্ধপরাধী বলে গণ্য করেছে–সজ্ঞানে এবং ব্যাপারটা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও!
না, এর আর পুনরাবৃত্তি নয়। যেভাবে জার্মান জাতি এ পরাজয়বরণ করেছে, আমাদের কাছে এটা প্রত্যক্ষ যে সত্যিকারের কারণ অন্য কোথাও সামরিক পরাজয়ের দরুণ কয়েকটা সীমান্ত হারানো বা আত্মরক্ষা না করতে পারা নিশ্চয়ই নয়। যদি সীমান্ত হারানোর জন্য এ বিপর্যয় আসত, তবে জার্মান জাতি তা সম্পূর্ণরূপে অন্যভাবে ব্যাপারটাকে গ্রহণ করত। তারা এই দুর্ভাগ্যকে দৃঢ়ভাবে দাঁতে চেপে থাকত, অথবা দুঃখে ভারাক্রান্ত অবস্থায় ভেঙে পড়ত। শত্রুর বিরুদ্ধে বিদ্বেষে এবং উন্নত্ততায় তাদের হৃদয় ভরে উঠত। হঠাৎ ঘটনার প্রবাহে অথবা ভাগ্যের আদেশে যাদের কপালে বিজয় তিলক পড়েছে, এবং সেক্ষেত্রে জাতি রোমের ব্যবস্থাপক সভার* অনুসরণে পরাজিত সৈন্যদের বরণ করত ও তাদের ধন্যবাদ জানাত উৎসৰ্গতার জন্য। এবং আরো অনুরোধ জানাত সম্রাটের প্রতি যেন তারা আনুগত্যতা না হারায়। এমন কি শর্তহীন আত্মসমর্পণও স্বাক্ষরিত হত আন্দোলিত না হয়ে স্থিরভাবে, যখন হৃদয় মথিত হত চরম প্রতিহিংসার তাড়নায়।
এ হল সামরিক পরাজয়ের সত্যিকারের অভ্যর্থনার নমুনা, যা নাকি ভাগ্যের আদেশে আরোপিত; যেখানে উল্লাস বা নাচ গানের অবকাশ থাকত না। থাকত না কাপুরুষদের অহংকার, আর পরাজিতদের সম্মান দেখানোর তো কোন প্রশ্নই আসে না। সীমান্ত ফেরা সৈন্যদের উপহাস করাও হত না। এবং তাদের মানসম্মানও ধূলায় ছুঁড়ে ফেলা হত না। কিন্তু সবচেয়ে বড় হল, সেই লজ্জাকর পরিস্থিতি বৃটিশ অফিসার কর্নেল রেপিংটনকে প্রবৃত্ত করত না জার্মানির প্রতি উপেক্ষামিশ্রিত অবজ্ঞা ছুঁড়ে দিয়ে বলতে, যে প্রতি তিনজন জার্মানের একজন হল বিশ্বাসঘাতক। না, এক্ষেত্রে এ রোগ প্রকৃত বন্যার রূপ কিছুতেই নিতে পারত না; যার জন্য গত পাঁচবছর ধরে বহির্জগতের কাছে প্রতিটি সম্মানের পদচিহ্ন মুছে গেছে।
এটা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে জার্মানি টুকরো হয়ে যাওয়ার জন্যই যে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল তা কত বড় মিথ্যা। সামরিক পরাজয় হয়েছিল ধারাবাহিক ঘটনাগুলোর দ্বারা সৃষ্ট ব্যাধির জন্য এবং যার সক্রিয়তা যুদ্ধের পূর্বেই জার্মান জাতির গায়ে ফুটে ওঠে। এ যুদ্ধকেই আকস্মিক দূর্ঘটনা বলা চলে, যা দিবালোকের মত লোকের চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল যে ব্যক্তিগত এবং জাতীয় জীবনে নৈতিকতা কতখানি বিষ বাষ্পের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন এবং আত্মরক্ষণতার অধঃপতন হয়েছে। এগুলোই হল প্রাথমিক কারণ যা নাকি বহুদিন ধরেই জাতির এবং সম্রাটের ভেতরে গোড়ায় সুড়ঙ্গ কেটে চলেছে।
কিন্তু ইহুদীরা তাদের মিথ্যা এবং সংগ্রামশীল সহকর্মীদের নিয়েই পড়ে থাকে। মার্কসবাদীরা সমস্ত দোষ সেই লোকটার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, যে একা অতি মানবের লৌহ কঠিন ইচ্ছা এবং অদম্য উৎসাহ নিয়ে জাতিকে সেই দুর্ঘটনা এবং লজ্জাকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল। মহাযুদ্ধের পরাজয়ের দায়ভাগ লুডেনৰ্ডফের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তারা নৈতিক অস্ত্রটা (যা নাকি শত্রুদের পক্ষে বিপদজনক) দূরে সরিয়ে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকদের পিতৃভূমির প্রতি বিচারের পথ প্রশস্ত করে দেয়। ওসবগুলোর পেছনের উদ্দেশ্যটা হল–যেটা সর্বতভাবে সত্য, যদিও এটা হল একটা বিরাট বড় মিথ্যা যে পেছনে একটা মহৎ শক্তি কাজ করে যাচ্ছে। কারণ সাধারণ জনতার বিরাট একটা অংশকে তাদের অনুভূতির স্তরকে ভুল বোঝানো সম্ভব, কিন্তু তা সচেতনে বা সজ্ঞানে সম্ভব নয়। সুতরাং তাদের এ মানসিক অবস্থাতে তারা বিরাট মিথ্যার কাছে যত সহজে বলি হয়, ছোটখাটো মিথ্যার কাছে ততটা নয়। কারণ জীবনের প্রসঙ্গে তারা ছোটোখাটো মিথ্যা বলেই থাকে। কিন্তু তাদের জীবনে বড় মিথ্যার কোন স্থান নেই। প্রকাণ্ড মিথ্যা তাদের কাছে মাথা তুলতেও সক্ষম হয় না, এবং তাদের পক্ষে একটা অবিশ্বাস্য যে অন্য কেউ সত্যটাকে বিকৃত করার ধৃষ্টতা রাখে। তাদের মন সব সময়ই সন্দেহের দোলায় দোলে যে এর পেছনে নিশ্চয়ই অন্য কোন ব্যাখ্যা আছে। বিরাট মিথ্যা সব সময় পেছনে একটা ছাপ রেখে যায়। এবং সেই ছাপ মুছে ফেলে দিলেও নিশ্চিহ্ন হয় না; এটা পৃথিবীর সমস্ত মিথ্যাবাদী বিশেষজ্ঞদের জানা। বিশেষ করে মিথ্যার বেসাতি নিয়ে যাদের নিত্য ঘরসংসার, তারা ভাল করেই জানে কি করে মিথ্যাটাকে জঘন্যতম উপায়ে ব্যবহার করতে হয়।
স্মরণাতীত কাল হতে ইহুদীরা অন্যান্যদের থেকে খুব ভাল করে জানে কি করে মিথ্যা এবং মিথ্যা অপবাদকে চরমভাবে কাজে লাগাতে হয়। তাদের নিজেদের অস্তিত্বই কি চরম মিথ্যার ওপরে নয়? বলা হয়ে থাকে তারা ধর্মীয় জাতি। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দেখতে গেলে আদৌ কি ইহুদীরা একটা জাতি? এবং তা যদি সত্য হয় তবে কি জাতি? মানবজাতি যে মহান চিন্তানায়কের জন্ম দিয়েছিল ইহুদীদের সম্পর্কে তার বিবৃতি সর্বাংশে সত্য। সোপেনহাওয়ার ইহুদীদের বলত মিথ্যাবাদীর চরম শুরু। যারা এ বিবৃতির সত্যাসত্য দিকটাকে অনুধাবন করে না বা বিশ্বাস করতে চায় না, তাদের পক্ষে সত্য প্রতিষ্ঠা করা কিছুতেই সম্ভব নয়।
আমাদের জার্মান জাতির পরম সৌভাগ্য বলব যে এ চরম দুর্দশার দিনগুলোর হঠাৎ ঘটনাচক্রে ছেদ পড়ে এবং তা ভয়ানক বিপর্যয়ে পরিবর্তিত হয়। যদি ব্যাপারটা ধীর গতিতে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলত, আস্তে হলেও জাতি নিশ্চিত ধ্বংসের গর্ভে নিক্ষেপিত হত। রোগটাও হত দীর্ঘস্থায়ী; যেখানে রোগটা কঠিন হওয়াতে বাইরের সবার চোখে ধরা পড়ে গেছে; এটা কোন দুর্ঘটনা নয় যে মানুষ কালো প্লেগ রাজরোগের চেয়ে তাড়াতাড়ি নিরাময় করতে শিখেছে। কারণ প্রথমটা মৃত্যুর ভয়াল রূপ ধরে আসে, যা দেখে সমগ্র মানবজাতি শিউরে উঠে; আর অন্যটি আসে কপটতার ভাণ করে। প্রথমটা চরম ভয় ধরিয়ে দেয়, অন্যটা ভেতরে গোপনে কাজ করে চলে। ফলাফল হল, মানুষ প্রথমটার বিরুদ্ধে ভয়ানকভাবে ভয় পেয়ে গিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করে, অপরদিকে রাজরোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থা অনেক দুর্বলতার। এভাবে মানুষ প্লেগকে নির্মূল করতে সক্ষম হলেও রাজরোগ নির্মূল করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।
জাতির জীবনে রোগের ক্ষেত্রেও এটা সর্বাংশে সত্য। যতদিন না পর্যন্ত এ রোগ বিপর্যয়-স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, জনসাধারণ এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে বশবর্তী হয়ে যায়। তখন ভাগ্যের একটা ধাক্কায়, যদিও সেটা তিক্ত–ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয় ধীর গতিতে তা হ্রাস পাবে, নাকি বলির জন্য উৎসর্গীকৃত মানুষগুলোকে সেই রোগের শেষ পর্যায়ে এনে দাঁড় করাবে। বেশির ভাগ এ আকস্মিক দুর্ঘটনা তৎক্ষণাৎ সারানো না গেলেও দীর্ঘদিন ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়।
কিন্তু এক্ষেত্রেও সর্বপ্রথমে প্রয়োজন ভেতরকার গুপ্ত কারণটাকে টেনে বার করা যা থেকে এ রোগের উৎপত্তি।
সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রশ্নটা হল মূল কারণ থেকে যে পরিবেশে এটা বেড়ে উঠেছে তাকে আলাদা করা। আর যতদিন পর্যন্ত এ রোগের জীবাণু দেহে থেকে যায়, ততদিন পর্যন্ত এটাকে রোগ মুক্ত করা সত্যই কষ্টকর। দীর্ঘদিন ধরে থাকায় এটা দেহের একটা অঙ্গ বিশেষ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময়েই দেখা যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ বিষাক্ত বীজ জাতির একটা অঙ্গে পরিণত হয়ে গেছে, তখন কিছুতেই এটাকে মুক্ত করা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। তখন এটাকে প্রয়োজনীয় একটা শয়তান বলে ধরে নেওয়া হয়। সুতরাং এ বিদেশী জীবাণু শরীরের ভেতর থেকে খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা থেকেই মানুষ বিরত থাকে।
যুদ্ধ পূর্বের দীর্ঘ শান্তির দিনগুলোতে এ শয়তানের উপস্থিতি নিশ্চয়ই ছিল। কি : একবার বা দুবারের বেশি তাদের খুঁজে বার করার কোন প্রচেষ্টাই হয়নি। এখানেও আবার সেই অর্থনৈতিক অবস্থাটাই নজরে এসেছে যা নাকি সহজে দৃশ্যমান। অপর যে শয়তানগুলো নীরবে দেহের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে আছে তার চেয়ে।
ক্ষয়রোগের অনেকগুলো চিহ্নই সেদিন বর্তমান ছিল যার ওপরে বিশেষভাবে চিন্তা করাটা উচিত ছিল। অর্থনৈতিক দুরবস্থা সম্পর্কে নিচের কথাগুলো বলা যায় :
যুদ্ধের আগে বিপুল পরিমাণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উন্নতির চেয়ে দৈনন্দিন রুটি জোগাড়ের সমস্যাটাই বড় হয়ে ওঠে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যারা এজন্য দায়ী, তাদের মাথায় কিছুতেই সঠিক সমাধানটা আসে না; তাই তারা সস্তায় বাজীমাৎ করার রাস্তাটাই বেছে নেয়। নতুন সীমান্ত দখলের ধারণাটাকে পরিত্যাগ করে তার পরিবর্তে এদের ব্যবসার তালে দুনিয়া জয়ের প্রচেষ্টাটাকেই শেষমেষ ক্ষতিকারক শিল্পকেন্দ্রীক করে তুলেছিল।
তার সর্বপ্রথম এবং প্রধান ভয়াবহ ফলাফল হল কৃষিজীবী সম্প্রদায়কে দুর্বল করে দেওয়া।
ধনী এবং দরিদ্রের পার্থক্যটা এতই প্রকট হয়ে পড়ে যে সেটা চোখে পড়ার মত। বিলাসিতা এবং দারিদ্রতার এত ঘেঁষাঘেষি সহাবস্থান যে তার ফলাফল শোচনীয় হতে বাধ্য। অভাব এবং বেকারত্ব আশ্চর্যজনক খেলা দেখাতে শুরু করে, যার পরিণতি চরম অসন্তোষ এবং পরস্পরের তিক্ততায়। তার ফল হয় জনসাধারণ রাজনীতিতে বিভিন্নমুখী হয়ে পড়ে। ব্যবসায়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অসন্তোষও বেড়ে চলে। ব্যাপারটা এমন এক জায়গায় এসে ঠেকে যে আর চলতে পারে না, সকলেরই মনে এ ধারণাটা জন্মায়। যদিও কারোরই ধারণা ছিল না যে সত্যিকারের কি ঘটতে যাচ্ছে।
ছড়িয়ে থাকা অসন্তোষ যে জনজীবনে কত গভীরে পৌঁছেছিল এগুলোই হল তার। টিপিক্যাল এবং দৃশ্যমান চিহ্ন।
শিল্পই দেশকে চালনা করতে শুরু করে এবং অর্থ ঈশ্বরের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটা দখল করে এমনভাবে বসে যে তা দিয়ে শুধু যে যা ইচ্ছা করা সম্ভব তা নয়, সবাই তার কাছে মাথা নত করতেও বাধ্য হয়। স্বর্গের ঈশ্বর যেন পুরনো দিনের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় এবং তাকে তার জায়গা কুবেরের জন্য ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হয়। এভাবেই চরম অধঃপতনের দিন ঘনিয়ে আসে যা প্রকৃতই জাতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তৎকালীন অবস্থা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল যখন জাতির ভাগ্যে প্রশংসাটা জোটা উচিত। কারণ দুঃসময়ের লগ্ন তখন ঘনায়মান। জার্মানির উচিত ছিল তরবারীর দ্বারা রুটি জোগাড় করা, যাতে সে তার প্রয়োজনীয় রুটি পেতে পারে।
দুর্ভাগ্যবশত অর্থের এ প্রাধান্য জাতির প্রত্যেক অংশের স্বীকৃতি পায়, যার বিরোধীতা করা একান্তভাবেই উচিত ছিল। মহামান্য কাইজার একটা ভুল করেছিল যখন তার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে এ সমস্ত কুবেরদের জায়গা করে দেয়। স্বীকৃতভাবে যদিও ক্ষমা চেয়েই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এমন কি বিসমার্ক পর্যন্ত এ ব্যাপারটার বিপদ বুঝতে সক্ষম হয়নি। বাস্তবে সব আদর্শগুলোকে অর্থের পরিমাপে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়। কারণ এটা তো পরিষ্কার যে এ রাস্তায় হাঁটতে অর্থের নিকট তরবারীর স্থান দ্বিতীয় পর্যায়ের।
অর্থনৈতিক বিলি ব্যবস্থা যুদ্ধে চেয়ে অনেক সহজ। সুতরাং কাছাকাছি ইহুদী ব্রাঙ্কের সংস্পর্শে আসা কোন সত্যিকারের বীর বা রাষ্ট্রনেতার পক্ষে আর আশ্চর্যের কি আছে! সত্যিকারের প্রতিভা কখনই সস্তা হাততালি চায় না; সুতরাং এটাই তো স্বাভাবিক যে সে তা’ ধন্যবাদের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করবে।
অর্থনৈতিক চরম সংকট ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত স্বার্থটাকে বড় করে তুলে পুরো অর্থনীতিটাকেই যৌথবদ্ধ কোম্পানিগুলোর হাতে সঁপে দেয়।
এভাবে অসৎ প্রতারকদের হাতে শ্রমিকদের জীবনজুয়ার পাশা হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা ভয়াবহভাবে বেড়ে ওঠে। অর্থনৈতিকচক্র জয়ের পথে ঘোরে এবং ধীরে হলেও জাতীয় জীবন পরিচালিত করতে শুরু করে।
যুদ্ধের আগেই ঘোরাল পথে শেয়ার কেনাবেচায় জার্মান অর্থনীতির ওপর আন্তর্জাতিক স্পষ্ট ছাপ মেরে দিয়েছিল। এটা সত্যি যে কয়েকজন জার্মান শিল্পপতি বিপদের চাকাটা উল্টোভাবে ঘোরাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষমেষ যখন সমবেতভাবে অর্থনীতিকে কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টা প্রবলতর হয়ে ওঠে মাকর্সবাদের কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরদের দ্বারা, তখন তারা একরকম বাধ্য হয়েই সরে আসে।
জার্মান ভারি শিল্পের ওপর ক্রমাগত যুদ্ধই হল মার্কসবাদীরা যে জার্মান অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিকতার রূপ দিতে চেয়েছিল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু শেষে এটাকে সাফল্যের চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি যখন মার্কবাদীরা বিপ্লবে জেতে। এ কথাগুলো লেখার সময়ে, বিশেষ করে আমার মনে হয়েছে জার্মান রেলওয়ের ওপর যে আক্রমণ করা হয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদীর খপ্পরে গিয়ে পড়ে। এভাবে ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি আবার তাদের লক্ষ্য পথে চূড়ান্তভাবে এগিয়ে চলে।
জার্মান জাতিকে কতখানি পরিমাণে বেনিয়া করে তোলা হয়েছিল, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল যুদ্ধ শেষে জার্মান শিল্পপতিদের একজন মন্তব্য করেছিল যে ব্যবসাই একমাত্র শক্তি যার দ্বারা আবার জার্মান জাতির পুনর্গঠন সম্ভব। এ অনর্থক কথাগুলো বলা হয়েছিল ফ্রান্স যখন মনুষ্যত্বের পরিমাপে লোক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্যস্ত; এটা বলার অর্থ হল যে জাতীয় জীবনে আদর্শের চেয়ে টাকার মূল্য অনেক বেশি। স্টাইনস্ যা পৃথিবীব্যাপি রেডিওর মাধ্যমে বলেছিল তা এক চরম অবিশ্বাস্য সন্দেহের দোলায় পুরো জাতিকে দোলায়। মতামতটাকে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে তারা উদ্দেশ্যটাকে বাচাল এবং মতলববাজের দল প্রধান উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করতে শুরু করে–যে ভাগ্য রাষ্ট্রনেতাদের বিপ্লবের পরে জার্মানিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।
ক্ষয়িত জার্মানির সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল যুদ্ধের আগে কাজ অর্ধেক করার অভ্যাস। এর ফলাফল হল অনিশ্চিয়তা, যা জীবনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। নির্দিষ্ট একটা কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় দিয়ে ফলাফলে পৌঁছেছিল এক একটা কারণে। এবং শেষ পর্যন্ত এসব পীড়া শিক্ষাপদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে।
প্রাক যুদ্ধের জার্মান শিক্ষা ব্যবস্থায় কতগুলো বিরাট গলতি ছিল। এক, সীমাবদ্ধতা ছিল পুরোপুরি জ্ঞান নির্ভর এবং প্রত্যক্ষ কাজে লাগতে পারে সেদিকে নজরই দেওয়া হয়নি। তার চেয়েও অনেক কম নজর দেওয়া হয়েছিল ব্যক্তিগত চরিত্র গড়ায়; যতখানি সম্ভব শিক্ষার এ বিশেষ দিকটাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। এবং দায়িত্বজ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি ও বিচার ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে এ শিক্ষা একেবারেই সাহায্য করে না। তার ফলে যে সব লোক এ শিক্ষা ব্যবস্থায় তৈরি হয়, তারা হল আদবকায়দা আর ভাবাবেগ সর্বস্ব। যুদ্ধের আগে জার্মানদের আদব-কায়দা আর ভাবাবেগ সর্বজাত বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। জার্মানদের লোকে ভালবাসত কারণ তাদের ব্যবহার করা চলত বলে। কিন্তু তাদের চারিত্রিক এ দুর্বলতার দরুণ সম্মান বলতে কিছু পেত না। যাদের এ রহস্যের গভীরে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র জার্মানরাই সর্বপ্রথম তাদের জাতীয়তা ত্যাগ করে নিজ ভূমে পরদেশীর মত বসবাস করতে শুরু করে। এবং তখন সমস্ত পৃথিবীতে একটা কথা অতি প্রচলিত ছিল যে, একটা টুপি হাতে করে যে কেউ সমগ্র দেশটার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে পারে।
এ ধরনের সামাজিক শিষ্টাচার বিপর্যয় ডেকে আনে, বিশেষ করে যখন নির্দেশ আসে মহামান্য রাজার উপস্থিতিতে কতগুলো বিশেষ শিষ্টাচার দেখাতে হবে। এ নির্দেশ হল আদব-কায়দা পরস্পর বিরোধী হতে পারব না, এবং মহামান্য সম্রাট যা পছন্দ করেন। সেই ধরনের আদব-কায়দাই মেনে চলতে হবে।
এটা হল পরিষ্কার ব্যাপার যে মর্যাদার মূল্য দিতে হবে, যে আদব-কায়দা শুধু লক্ষ্য সাধনের জন্য তা বরদাস্ত করা হবে না। সম্রাটের উপস্থিতিতে দাসের মত ব্যবহার হয়ত বা যথেষ্ট পরিমাণে উপযোগী, অবশ্যই পেশাগত দাসদের এবং জায়গা খোঁজার। লোকদের পক্ষে সত্যি বলতে কি এ ক্ষয়িষ্ণু জীবগুলোর পরিক্রমণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ওপরের স্তরে ব্যপ্ত; সাধারণ সৎ নাগরিকদের মধ্যে এদের ঘোরাফেরা নেই বললেই চলে। এ অতিশয় বিনীত জীবেরা তাদের প্রভু এবং রুটি জোগানোর কর্তার কাছে সাষ্টাঙ্গে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ত, কিন্তু অন্যদের কাছে তাদেরই ব্যবহার ছিল উদ্ধত, বিশেষ করে তাদের ধৃষ্টতা এত বেশি ছিল যে তারা একমাত্র নিজেদেরই মানুষ বলে জ্ঞান করত। এবং নিজেদের রাজকীয় মহিমা সম্পন্ন বলে ঘোষণা করতেও দ্বিধা ছিল না তাদের।
এ কাজগুলোর সাহায্যে তারা রাজার এবং রাজকীয় আদর্শগুলোর পতন ঘটাবার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে; এছাড়া আর কিছু হতে পারে না। একটা মানুষ যখন যে কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে, তখন সে কখনই তাদের সামনে মাটিতে উপুড় হয়ে সাষ্টাঙ্গে ধুলোয় পড়ে তাকে প্রণাম করবে না। সে যদি কোন প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধির জন্য সত্যিকারের শুভাকাক্ষী হয়, তবে সে কিছুতেই নিরুৎসাহ হবে না, কোন সদস্য সেই প্রতিষ্ঠানের দোষত্রুটি যতই দেখিয়ে তাকে নিরুৎসাহ করার চেষ্টা করুক না কেন। এবং এটাও সত্যি যে সে সারা পৃথিবী ঘুরে ঢাক পিটিয়ে এ বিষয় বলে বেড়াবে না, যা নাকি তথাকথিত গণতন্ত্রের কয়েকজন বন্ধু করে বেড়িয়েছে। তার পরিবর্তে সে তার রাজার কাছে আবেদন জানাবে, এবং সেই রাজার নিকট তার কাজ হল পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝিয়ে বলে সেভাবে কাজ করিয়ে নেওয়া। উপরন্তু তার পক্ষে এ ধরনের চিন্তাধারা গ্রহণ করা অনুচিত যে রাজা যা ভাল বুঝবে তাই করবে; এমন কি যদি তার নির্দেশিত পথ দেশ এবং জাতিকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমি যে মানুষের স্বপ্ন দেখি, তার কর্তব্য হল রাজার কার্যকলাপের বিরোধিতা করে হলেও প্রয়োজনে রাজকীয় ব্যবস্থাকে রক্ষা করা। রাজকাজ করতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে তাকে যত বড় দায়িত্বের মুখোমুখি হতে হোক না কেন; যদি রাজকীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রাজার কার্যকলাপের ওপরে নির্ভর করে, তবে এর চেয়ে শোচনীয় প্রতিষ্ঠান আর হতে পারে না। কারণ খুব কর্মক্ষেত্রেই আদর্শ রাজা জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতীক এবং পূর্ণ চরিত্রের লোক দেখা যায়, যদিও আমরা অন্যরকম চিন্তা-ভাবনা করতেই অভ্যস্ত। কিন্তু ওই সত্য পেশাগত জোচ্চর এবং গোলামদের কাছে স্বাদহীন ঠেকবে। তবু মাথা উঁচু করা সবাই, যারা হল একটা জাতির মেরুদণ্ড বিশেষ, জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি এ অর্থহীন বাচাল চিন্তাধারা ত্যাগ করে থাকে। কিন্তু যদি একটা জাতির সৌভাগ্য হয় মহান রাজ্য বা মহান কোন ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হবার, তবে এটা মেনে নিতেই হবে যে সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে সেই জাতির সৌভাগ্যের তারা জ্বলজ্বল করছে; এবং তাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত যে খুব খারাপ অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য ভাগ্য তার প্রতিকূলে নয়।
এটা পরিষ্কার যে রাজকীয় আদর্শগুলোর মূল্যায়ন এবং স্বার্থকতা শুধু রাজার ওপরেই নির্ভরশীল নয়। অবশ্য যদি না সেই মুকুট স্বর্গের আদেশপ্রাপ্ত হয়ে বীর দ্য গ্রেট ফেডারিক বা বিচক্ষণ ব্যক্তি উইলিয়াম ফার্স্টের শিরে বসানো না হয়। এটা অবশ্য কয়েক শতাব্দীতে একবারই ঘটে থাকে। এর পুনরাবৃত্তি তার থেকে বেশি ঘটে না। রাজকীয়তার আদর্শ ব্যক্তির মানক্রমে হয়ে থাকে। অর্থাৎ মুকুটধারীর মানসিকতার উপরে নির্ভরশীল। আর প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের ভেতরেই নিহিত থাকে। এভাবে রাজাও সেইসব দায়িত্বশীল লোকদের পর্যায়ে পড়ে যাদের কর্তব্যকর্ম হল প্রতিষ্ঠানের সেবা করা। রাজা পর্যন্ত এ যন্ত্রের চাকা বিশেষ এবং তাকেও তার কর্তব্যকর্ম করে যেতে হবে। সেই উঁচু আদর্শের পরিপূর্ণতার জন্য তারও একান্তভাবে কাজ করে যাওয়া উচিত। সুতরাং এ আদর্শের সঙ্গে এর অর্থ যদি জড়িত না থাকে তবে সমস্ত কিছুই সেই তথাকথিত পবিত্র ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। তখন আর সেই ক্ষীণ দুর্বল লোকের পক্ষে যোগ্যতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়।
বর্তমানে সেই সত্যযুগের ওপরে জোর দেওয়া উচিত, কারণ এখন সেইগুলোই আবার ফিরে এসেছে; এবং রাজকীয় ব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য এগুলো খুব কম দায়ী নয়। বেশ কিছুটা ধৃষ্টতার সঙ্গে এ লোকগুলোই আবার তাদের রাজার কথা বলে; একেই তারা কয়েক বছর আগে নির্লজ্জের মত পরিত্যাগ করেছিল যখন তার সত্যিকারের সঙ্গীন সময় উপস্থিত। যারা এ মিথ্যে কথার কোরাসে নিজেদের গলা মেলায়নি, তাদেরই খারাপ জার্মান নামে অভিহিত করে ধিক্কার জানানো হয়েছে। যারা এ আখ্যা দিয়েছিল তারা হল ১৯১৮ সালের ন্যায় পলায়নবাদী এবং নিজেদের স্বার্থের তাগিদায় লাল ব্যাজ ধারণ করতে শুরু করে। তাদের চিন্তায় পরিণামদর্শিতা শৌর্যের চেয়ে অনেক শ্রেয়। কাইজারের কি ঘটছে তা নিয়ে তাদের মাথা ব্যাথা নেই। তারা এমন ভাণ করত যেন তারা শান্তিপূর্ণ নাগরিক; কিন্তু প্রায়ই দেখা যেত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তারা দল বেঁধে অদৃশ্য। হঠাৎ এ রাজমর্যাদার বাহকদের প্রয়োজনের সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। পরিবেশ অনুযায়ী এ দাসের দল এবং সদস্যরা একে একে আবার নাট্যমঞ্চে আবির্ভূত হয়, যাতে আবার তারা রাজার উদ্দেশ্যে জিহ্বা চালনা করতে পারে। অবশ্যই যখন অন্যান্য রাজার বিরোধিতা করার প্রয়াসকে দমন করে ফেলেছে। আবার তারা একত্রিত হয়ে মিশরের ভাল খাদ্যদ্রব্য ও স্বাচ্ছন্দ বিলাসের কথা স্মরণ করে। এবং রাজার আনুগত্যে বিভোর হয়ে পড়ে। ব্যাপারটা এ গতিতেই চলতে থাকে, যতদিন না পর্যন্ত লাল ব্যাজের দিন প্রবল হয়ে ওঠে। তখন আবার পুরনো ঝরঝরে সদস্যদের যারা রাজকীয় মহিমার গুণগানে মুখর পুনশ্চ কয়লা রাখার বদলী পাত্রের মত পলায়ন করে। ঠিক যেমন করে বিড়ালে মুখে করে ইঁদুর নিয়ে ছুটে পালায়।
যদি সম্রাট নিজে এসব ব্যাপারে দায়ী না হয় তবে প্রত্যেকেই তার প্রতি সহানুভুতি দেখবে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদেরও উপলব্ধী করা উচিত যে তাদের সাহায্যে সিংহাসনই একমাত্র হারানো সম্ভব, ফিরে পাওয়া নয়।
এসব ভক্তি সম্ভ্রম হল আমাদের ভুল শিক্ষাপদ্ধতির ফলাফল, যা এ ক্ষেত্রে বিদ্বেষ বশে চরম শাস্তি দিয়েছিল। এ শোচনীয় সারবিহীন বস্তু জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়ে রাজকীয় মর্যাদার গোড়ায় সুড়ঙ্গ কাটে। শেষ পর্যন্ত তা নড়ে চড়ে উঠলে সমস্ত কিছু তার গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। স্বভাবতই জঘন্য এবং অতি নিচু তোষামোদকারী গলগ্রহরা কিছুতেই তাদের প্রভুর জন্য মরতে ইচ্ছুক ছিল না; রাজার পক্ষে এটা উপলব্ধী করা সম্ভব ছিল না এবং বুঝতে গেলে যতখানি কষ্ট সহ্যের প্রয়োজন, তার পক্ষে তত ক্লেশ বরণ করে নেওয়াটা অসম্ভব।
ভুল শিক্ষা পদ্ধতির একটা ভুল ফলাফল হল যা সততাই দৃশ্যমান তা কাঁধে দায়িত্ব নেওয়ার ভীতি এবং তার ফলপ্রাপ্তি হিসেবে অস্তিত্বসম্পন্ন মূল সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হওয়ার দুর্বলতা।
এ মড়কের শুরুর বিন্দু হল আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, যেখানে বিশেষ করে দায়িত্ব বিমুখতা পরিপুষ্ট লাভ করে। দুর্ভাগ্যবশত ধীরে ধীরে এ অসুখ প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে; বিশেষ করে তা আঘাত হানে গণজীবনের ব্যাপারগুলোতে। সবদিক থেকেই দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দেওয়া হয়, যার জন্য প্রতিটি ব্যাপারেই আসে দোমনাভাব। ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ প্রায় শূন্য হয়ে আসে।
আমরা যদি গণজীবনে বিভিন্ন সরকারের অনিষ্টকর ঘটমান বিষয়গুলোর বিচার বিবেচনা করে দেখি, তবে তৎক্ষণাৎ এ অর্ধেক হৃদয় দিয়ে দায়িত্ব নেবার কাপুরুষতার ভয়াবহ ফলাফল দেখতে পাব। অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে আমি মাত্র কয়েকটা উদাহরণ এখানে পেশ করব।
সাংবাদিকচক্র রাষ্ট্রের মধ্যে সংবাদপত্রকে বিরাট একটা শক্তি বলে বর্ণনা করেছে।
সত্যি বলতে কি এর উপযোগীতা অসাধারণ। কারোর পক্ষে এটা সহজে হিসাব করা সম্ভব নয়। কারণ সংবাদপত্র শিক্ষা পদ্ধতির একটা দিক। এমন কি প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনেও। বিশেষ করে সংবাদপত্র পাঠকদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, যারা যা কিছু পড়ে, তাতেই বিশ্বাস করে। দ্বিতীয়ত, যারা যা কিছু পড়ে, তারা কিছুতেই বিশ্বাস করে না। তৃতীয়দল হল, যারা পড়ে প্রচণ্ড সমালোচনার পর বিচার বিবেচনা অনুসারে সার বস্তুটি গ্রহণ করে। সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে প্রথম দলটি অতি শক্তিশালী। কারণ গণসংখ্যার বেশির ভাগই এদের সমষ্টি। বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে জাতির তরফে এরা অত্যন্ত সহজ অংশের লোক। পেশাগত দিক থেকে পুরো জাতিটাকে ভাগ করা অসম্ভব; বরং বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে এদের বাছবিচার করা যেতে পারে। এ পতাকার তলে তারাই জড়ো হয়, যারা শুধু নিজেদের চিন্তা-ভাবনা করার জন্য এ পৃথিবীতে আসেনি; অথবা যার এ শিক্ষা হয়নি কারণ এরজন্য কিছুটা তাদের অক্ষমতা এবং কিছুটা অজ্ঞতা; সেই কারণে তারা তাদের সামনে ছাপার অক্ষরে যে দেখে সেটাকেই বিশ্বাস করে বসে। এর মধ্যে আমরা সেই ধরনের অলসদেরও যোগ করব, যারা নিজেদের পরিপূর্ণ চিন্তা করার ক্ষমতা থাকা সত্বেও নেহাত আলসেমির জন্য অন্যের চিন্তাধারাটাকে গ্রহণ করে বিষয়গত এ ভেবে যে চিন্তাধারাগুলো পরিপূর্ণ। সুতরাং এ সবগুলোকে বিচার বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে সংবাদপত্রের প্রভাব জনজীবনে সুদূর প্রসারী। কারণ জনসাধারণের বিরাট একটা অংশের ওপর এ সংবাদপত্র প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কিন্তু যে কারণেই হোক অথবা অনিচ্ছুক বলে তারা এগুলোকে মানসিক চালুনি দ্বারা ঝেড়ে পার্থক্য করে না। সেই কারণে প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যাগুলো হল এ স্বতন্ত্র প্রভাবের ফলাফল। গণজীবনের জ্ঞানলোক যদি সৎ চরিত্রের এবং দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হয়, তবে এগুলোর একটা সুবিধাগত দিক আছে; কিন্তু যখন বদমায়েস এবং মিথ্যাবাদীরা এগুলোকে কাজে লাগায়, তখনই জাতির চরম ক্ষতি নেমে আসে।
সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় দলটি সত্যই ছোট। কারণ এর সমষ্টি হল প্রথম দলের যারা সারি সারি ঘটনা প্রবাহে তিক্ত হয়ে শেষমেষ ছাপার অক্ষরে যা দেখে তাকে অবিশ্বাস করে চলে। তারা সমস্তরকম সংবাদপত্রকে ঘৃণা করে থাকে। হয় তারা সংবাদপত্রে সবকিছু পড়ে না, অথবা বিষয়বস্তুর ওপরে তাদের চরম একটা রাগ থাকে। তারা সেগুলোকে মিথ্যার স্থূপ এবং ভুল বক্তব্য বলে ধরে নেয়। কারণ তাদের সবসময়েই সত্যের প্রতি একটা অবিশ্বাস থাকে। সেই কারণে কোন ইতিবাচক কাজকেই তারা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে।
তৃতীয় দলটি হল সত্যি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কারণ সত্যিকারের বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন লোক দ্বারা এটা সৃষ্ট, যাদের স্বাভাবিক ধ্যান-ধারণা এবং শিক্ষা তাদের নিজেদের জন্যই চিন্তা করতে শেখায়, এবং এরা প্রতিটি বিষয়েই নিজেদের একটা মতামত খাড়া করতে সচেষ্ট হয়ে থাকে। তারা এমন কোন সংবাদপত্র পড়ে না যেখানে তাদের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সংযোগকারী লেখকের বক্তব্যের মিল থাকে। এবং স্বভাবতই লেখকদের পক্ষে এটা খুব একটা সহজ কাজ নয়। সাংবাদিকরা এ ধরনের পাঠকদের বেশ কিছুটা পৃষ্ঠপোষকতাই করে থাকে।
সুতরাং এ কাজে সংবাদপত্রগুলোর বিপদজনক ক্ষমতা অতি অল্প, অপ্রয়োজনীয়ও বটে। বিশেষ করে তৃতীয় দলের সদস্যদের নিকট। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ পাঠকবর্গ প্রত্যেক সাংবাদিককে অত্যন্ত অশ্রদ্ধার চোখে দেখে যারা কদাচ সত্য কথা বলে থাকে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হল এসব পাঠকবর্গের মূল্যায়ণ বুদ্ধিমত্তায়, তাদের সংখ্যার দ্বারা নয়, অসুখীজনক ব্যাপারটা হল সংখ্যাটাকেই গণনার মধ্যে ধরা হয়। বুদ্ধিমত্তাকে নয়। বর্তমান সময়ে যখন জনসাধারণের ক্ষেত্রে ভোটপত্রটাই কিছু স্থির করার মানদণ্ড, সেখানে পুরো ব্যাপারটাই হল গরিষ্ঠ সংখ্যা গোষ্ঠীর হাতে; অর্থাৎ প্রথম দলের। যারা নির্বোধ এবং সহজে বিশ্বাসী দলের লোক।
এটা হল একটা দেশের জাতীয় স্বার্থ যে এ দলটা যাতে কোন ধাপ্পাবাজের হাতে গিয়ে না পড়ে, যারা অজ্ঞ অথবা শয়তানি মতলবী কোন তথাকথিত শিক্ষক। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হল শিক্ষাপদ্ধতির উপর নজর রাখা যাতে এ ধরনের কোন অপরাধ সংগঠিত হতে না পারে।
বিশেষ করে সংবাদপত্রগুলোর ওপর যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে; কারণ এদের প্রভাব শুধু শক্তিশালীই নয়, সর্বব্যাপীও বটে। যেহেতু এর ফলাফল কিছু সময়ের জন্য নয়, বরং ক্রমাগত বলা চলে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নামে যা হোক করে ব্যাপারটাকে কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না, বা এ কর্তব্যে অবহেলা করাটাও সঙ্গত নয়। সমস্ত ব্যাপারটাই জাতির কাছে তুলে ধরা উচিত। কেন ভাল এবং কি করলে আরো ভাল হতে পারে তা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। নির্দয়তার সঙ্গে রাষ্ট্রের উচিত শিক্ষা পদ্ধতির এ যন্ত্রটাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখা এবং জাতির ও দেশের সেবায় একে নিয়োজিত করা।
কিন্তু যুদ্ধ পূর্ব জার্মানিতে জার্মান সংবাদপত্রগুলো কি ধরনের খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করেছিল? এটা কি সবচেয়ে বিষাক্ত বিষ যা কল্পনায় আনা যায়। এটা কি বিশ্বজনীন শান্তিবাদের নিকৃষ্টরূপ নয় যা আমাদের দেশের লোকের ভেতরে ছুঁচের সাহায্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়নি? যখন অপরেরা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতরূপে বাজপাখির ধারালো নখ দিয়ে জার্মান জাতির ওপরে ঝাপিয়ে পড়তে উদ্যত? এ সংবাদপত্রগুলোই শান্তির সময়ে বিন্দু বিন্দু করে সন্দেহের বীজ জনসাধারণের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে, যা নাকি আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। এভাবেই রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার হাত দুটোয় হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে। এ জার্মান সংবাদপত্রগুলোই আমাদের জনসাধারণের কাছে পরিবেশনা করেনি যে পশ্চিমী গণতন্ত্র কত বড় নিরর্থক? যতদিন পর্যন্ত না প্রচুর আগাছা তাদের ভবিষ্যত লীগ অব নেশানসের হাতে সুরক্ষিত বলে ভেবেছে? এ সংবাদপত্রগুলোই আমাদের লোকদের নৈতিক অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিয়ে জনগণের সৌন্দর্য জ্ঞান এবং নৈতিকতাকে হাস্যস্পদের পর্যায়ে নিয়ে গেছে।
ক্রমাগত আক্রমণে সংবাদপত্রগুলো কি রাষ্ট্রের অধিকারের গোড়ায় সুড়ঙ্গ কাটেনি যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে একেবারে ধূলিসাৎ না করা যায়। সংবাদপত্রগুলো কি রাষ্ট্রের সম্পত্তি রাষ্ট্রকে দেওয়ার ব্যাপারে বারবার আপত্তি জানিয়ে আসেনি? ক্রমাগত সমালোচনায় সৈন্যদলের নাম-যশ টেনে নিচে নামিয়েছে, সাধারণের জ্ঞান বুদ্ধিকে পেছনে থেকে ছুরি মেরেছে এবং সামরিক বাহিনীর সুখ্যাতিকে অস্বীকার করেছে— যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের প্রচারকার্যে সফলতা এসেছে।
তথাকথিত এ সংবাদপত্রগুলোর কাজ ছিল জার্মান রাষ্ট্র এবং তার জনসাধারণের জন্য কবর খোঁড়া। মার্কসীয় সংবাদপত্রগুলোর মিথ্যার বেসাতি সম্পর্কে কিছুই বলা চলে না। তাদের কাছে বিড়ালের নিকট ইঁদুরের যেমন প্রয়োজন, মিথ্যা প্রচারটাও তাদের সেইরকম মূল আদর্শ। তাদের একমাত্র এবং সর্বপ্রধান কাজ ছিল জাতির মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করা, যাতে পুরো জাতটা আন্তর্জাতিক অর্থনীতির এবং তাদের প্রভু ইহুদীদের গোলাম হতে পারে।
জনগণের মনকে বিষাক্ত করে তোলার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রই বা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল?, কিছুই করেনি। এ নীতিতেই তারা ভেবেছিল এ মহামারীর হাত থেকে রেহাই পাবে। চাটুকারিতা আর সংবাদপত্রের মূল্যায়ণের অগ্রাধিকার স্বীকার করে। ইহুদীরা জেনেশুনেই মৃদু হেসে এগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছিল ধন্যবাদের সঙ্গে।
রাষ্ট্রের এ অসম্মানজনক ব্যর্থতার কারণ হল,–বিপদটাকে বুঝতে না পারা, তার চেয়ে বেশি হল কাপুরুষতার এবং ত্রুটিপূর্ণ অর্ধেক হৃদয় দিয়ে পুরো বিষয়টার মোকাবিলা করার। কারোর কোন মৌলিক এবং উৎসাহপূর্ণ পদ্ধতি ছিল না যার দ্বারা এর মোকাবিলা করা যেতে পারে। সবাই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিয়েছে; অর্থাৎ এ পথ বেছে নিয়েছে। সোজাসুজি আঘাত করার পরিবর্তে বিষধর সাপকে খালি উত্তেজিতই করে তুলেছে। এর ফলাফল হয়েছে যে যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে থেকেছে এবং এ প্রতিষ্ঠানের সংগ্রাম করার ক্ষমতা বছরের পর বছর বেড়েই গেছে।
যে ইহুদী সংবাদপত্রগুলো ধীরে ধীরে জাতিকে দুর্নীতির গ্রাসে জড়িয়ে ফেলেছিল তাদের বিরুদ্ধে তৎকালীন রাষ্ট্র যে আত্মরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তাতে কোনরকম নির্দিষ্ট পন্থা ছিল না। এর পশ্চাতে যেমন সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি ছিল না, তেমনি নির্দিষ্ট কোন বিষয়বস্তুও ছিল না যাকে অবলম্বন করে এ আত্মরক্ষামূলক প্রয়াস গড়ে তোলা যেতে পারে। আসলে পরিস্থিতিটাকে বুঝতেই তারা অসফল হয়েছে, যে কারণে সংগ্রামের গুরুত্ব, উপায় বা কোনরকম পরিকল্পনা করাই তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। খালি সমস্যাটাকে নিয়ে টুং টাং শব্দ করেছে মাত্র। যখন কামড়টা জোরে বোধ হয়েছে, তখন এক আধজন সাংবাদিক বিষধর সর্পকে ধরে কয়েক সপ্তাহ বা মাসের জন্য জেলে পাঠিয়েছে; কিন্তু পুরো বিষের পাত্রটাকে শান্তিতে বয়ে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়েছে।
এটাকে স্বীকার করে নিতেই হবে যে এটা হল একদিকে ইহুদীদের ধূর্তামীর ফল; অপরদিকে রাষ্ট্রের নির্বুদ্ধিতা এবং অকপট সরলতার পরিচয় মাত্র। ইহুদীরা চালাকির জন্য সংবাদপত্রগুলোর ওপরে সম্মিলিতভাবে এ আক্রমণ করতে দিয়েছিল। একে অন্যকে আচ্ছাদন দিতে চেষ্টা করেনি। অন্যদিকে গোপনীয় সমস্ত তথ্য মার্কসীয় সংবাদপত্রগুলো অত্যন্ত জঘন্য উপায়ে উদ্ঘাটিত করে সবার সামনে তুলে ধরেছিল, ভয়াবহরূপে সরকার এবং রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেছিল এবং এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। এ মধ্যবিত্তিক গণতান্ত্রিক সংবাদপত্রগুলোও ইহুদীদের হাতে ছিল এবং তারা ভালভাবেই জানত কি করে ছদ্মবেশ ধারণ করে সত্যিকারের বিষয়বস্তুটাকে লুকোতে হয়। তারা যত্নের সঙ্গে কর্কশ ভাষার ব্যবহার পরিত্যাগ করত; কারণ তারা জানত বোকারা ওপর ওপর দেখেই বিচারপৰ্ব সমাধা করে এবং সত্যিকারের কোন বিষয়বস্তুর গভীরে তারা প্রবেশ করতে পারে না। তারা বিষয়বস্তুর পরিমাপ করে বাইরের রূপটা দেখে। ভেতরে কি আছে তা দেখে না বা দেখার মত ক্ষমতাও তাদের নেই। এক ধরনের মানসিক দৌর্বল্যকে সংবাদপত্রগুলো ভাল করে বুঝত এবং তার পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল।
এ মাথা মোটাদের কাছে ফ্রাংকফুর্টার ঝাউটুং নামক সংবাদপত্রটি সম্মানের সঙ্গে সমাদৃত হত। এরা সব সময় বেলচাকে সোজাসুজি বেলচা বলেনি। এরা সবরকম দৈহিক শক্তি প্রয়োগের বিরোধিতা করেছে এবং ক্রমাগত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মহৎ যুদ্ধের জয়ঢাক পিটিয়ে গেছে। কিন্তু এ সংগ্রামের বিষয়টা অদ্ভুত ব্যাপার, তথাকথিত কম বুদ্ধিমানদের মধ্যে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির এটাও একটা ভুল দিক; যা আমাদের দেশের যুবকগোষ্ঠীকে তাদের স্বাভাবিক প্রকৃতির পথ থেকে বিচ্যুত করে নিয়েছিল। সত্যিকারের জ্ঞানের বদলে কিছু এ ধরনের জ্ঞান তাদের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যার সঙ্গে সত্যিকারের জ্ঞানের কোন সামঞ্জস্য ছিল না। এ ধরনের বুদ্ধিমত্তা এবং শুভেচ্ছার শেষ প্রান্তে কিছুই মেলে না যদি সত্যিকারের লক্ষ্যবস্তু থেকে মানুষ পিছু হটে আসে। সত্যিকারের জ্ঞান তাকেই বলা যেতে পারে যা নাকি মানুষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অনুভব করতে সক্ষম হবে।
ব্যাপারটার আরো বিস্তারে যাই : মানুষের চিন্তাধারায় এ ভুল থাকা উচিত নয় যে সে প্রকৃতির প্রভু হওয়ার জন্যই এসেছে। শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োজনীয় দিকটা তাকে এ ধরনের মিথ্যা আশা দেখাতে সাহায্য করেছে। মানুষের বোঝা উচিত যে প্রয়োজনের গোড়ায় আইন-কানুনই যা নাকি প্রকৃতির রাজ্যে সর্বত্র বলবৎ তা হল যে তার অস্তিত্ব রাখার জন্য নিরবধি সংগ্রাম এবং দ্বন্দ্ব করে যেতে হবে তাকে। তখনই সে অনুভব করতে সক্ষম হবে যে মানব জাতির জন্য আলাদা কোন কানুন যে আইনের বাইরে সূর্য এবং গ্রহ-নক্ষত্র তাদের আপন কক্ষপথ পরিক্রমণ করে। চন্দ্র এবং তারকারাজি তাদের নির্দিষ্ট পথে বেয়ে চলে। সবল সর্বদাই দুর্বলের প্রভু। সুতরাং এগুলো থেকেই দেখা যাচ্ছে যাদের জন্য এসব আইন-কানুন নির্দিষ্ট, তাদের সেগুলো মেনে চলতেই হবে, অন্যথায় ধ্বংস হল অনিবার্য ফলাফল। এ চরম জ্ঞানের কাছে মানুষের উচিত নিজেকে সমর্পণ করা। সে বড়জোর তাকে বুঝতে চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু তার নির্দিষ্ট পথ থেকে সে কিছুতেই সরে আসতে পারবে না।
আমাদের বুদ্ধিমত্তার বেশ্যাবৃত্তির জন্যই ইহুদীরা এসব সাংবাদিকতা এবং সংবাদপত্রগুলোকে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন বলে আখ্যা দিয়ে থাকে। তাদের জন্যই ফ্রাংকফুর্টার ঝাইটুং আর বালিয়ান টাগোটে নামক সংবাদপত্রদ্বয় লিখিত। এর বক্তব্যের উদ্দেশ্যও তারাই এবং এ পত্রিকা দু’টোর প্রভাব তাদের মধ্যেই পড়েছে। অতি যত্নের সঙ্গে কর্কশ ভাষাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে; অন্যান্য শিশির থেকে বিষ বার করে এসব অনুগত জনমণ্ডলীর দেহে অতি সতর্কভাবে সেই বিষ প্রয়োগ করেছে। টগবগে স্বর এবং সুন্দর সুন্দর নির্বাচিত শব্দগুচ্ছ দ্বারা পাঠকদের জ্ঞান এবং নৈতিকতাই যে একমাত্র এসব পত্রিকার আদর্শ হওয়া উচিত সেই বিশ্বাসের পথ থেকে তাদের বিচ্যুত করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে এসব ব্যাপারগুলো অতি ধূর্ততার সঙ্গে যে কোন বিরোধিতাকে সমূলে নষ্ট করেছে যা নাকি ইহুদী এবং তাদের সংবাদপত্রগুলোর বিরুদ্ধে যেতে পারত।
তারা পুরো ব্যাপারটাকে এমনভাবে সম্ভ্রমের সঙ্গে রূপ দিত যাতে সবাই মনে করে অন্যান্য সংবাদপত্রগুলো যে প্রশ্রয় দিত, তা যেন অত্যন্ত মৃদু বলে বোধ হয়; এবং যাতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানাজারী করে তাদের বিরুদ্ধে কোনরকম আইনগত অধিকার প্রয়োগ না করা হয়। বাস্তবিকপক্ষে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা সংবাদপত্রের স্বাধীন আঙিনায় অনধিকার প্রবেশেরই সমতুল্য। এ অভিব্যক্তিটা শ্রুতিকটু পদের পরিবর্তে কোমলতর বলে এ পথেই আইনের শাস্তিটাকে এড়িয়ে যেত এবং জনসাধারণকে প্রতারণা আর গণমানসকে বিষিয়ে দেওয়ার জন্যই তারা এ পথ বেছে নিয়েছিল। এভাবে শাসকবর্গ অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন হয়ে উঠেছিল; বিশেষ করে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আইনগত কোন ব্যবস্থা–এসব সাংবাদিক দস্যুদের বিরুদ্ধে নেওয়ার ব্যাপারে। কারণ সব সময়ই তাদের একটা ভয় যে এসব সাংবাদিক দস্যুদের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়া হলে পরে জনসাধারণের সহানুভূতি যদি তথাকথিত শ্রদ্ধেয় সংবাদপত্রগুলোর ওপর গিয়ে বর্তায়! অবশ্য এ ভয় একেবারে অনর্থক ছিল তা নয়, কারণ সেই মুহূর্তে পুরো ব্যাপারটা এমন হয়ে উঠেছিল যে এ নোংরা সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে যে কোন একটার বিরুদ্ধে কোনরকম আইনগত ব্যবস্থা নিলেই অন্যান্যরা তার সাহায্যে তৎক্ষণাৎ ছুটে আসত। এ ছুটে আসার কারণ অবশ্য এর নীতিগত সমর্থনের নিমিত্ত নয়; এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল সংবাদপত্রের তথাকথিত স্বাধীনতা এবং জনসাধারণের মুক্ত মতামত প্রকাশের অধিকারের জন্য। এ তীক্ষ্ণ আর্তনাদ অনেক বলবান পুরুষকেই কাপুরুষে পরিণত করে; কারণ এগুলো তো নির্গত হয় তথাকথিত ভদ্রসাংবাদিক গোষ্ঠীর মুখ থেকে।
এবং এভাবেই এ বিষ জাতির জীবনের রক্তে প্রবেশ লাভ করে ও গণজীবনকে বিষাক্ত করে তোলে। সরকারের তরফ থেকে এ রোগের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। দ্বিমত নিয়ে যা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা সামগ্রিকভাবে পুরো ব্যাপারটাকে টেনে নিচে নামিয়েছে এবং পুরো সাম্রাজ্যটাকেই ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। যখন কোন প্রতিষ্ঠান তার কাছে যে অস্ত্র গচ্ছিত তা দিয়ে আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ হয়, তখন তার অস্তিত্বটাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। প্রতিটি দ্বিমত হল ভেতরকার ক্ষয়প্রাপ্ত উদাহরণ মাত্র যা সময়ে আজ অথবা কাল বাইরে বিপর্যয় ডেকে আনতে বাধ্য।
আমার দৃঢ়বিশ্বাস আমাদের বর্তমান বংশধরেরা এ বিপদের ওপরে প্রভুত্ব করতে অবশ্যই পারে যদি তাদের সঠিক পথে পরিচালনা করা যায়। কারণ এ বংশধরেরা এমন কতগুলো অভিজ্ঞতার রাস্তা অতিক্রম করেছে যা তাদের স্নায়ুকে শক্ত করে তুলতে সক্ষম।
আমার দৃঢ় অভিমত হল এ কাজ পূর্ব পুরুষদের চেয়ে আমাদের পক্ষে করা অনেক সহজ। বারো ইঞ্চি একটা অস্ত্রের ভেদ ক্ষমতা হাজার ইহুদী সংবাদপত্রের সর্প-শব্দের চেয়ে অনেক বেশি তীব্র।
জার্মানিতে প্রধান এ সমস্যাগুলোকে কী ধরনের দুর্বল এবং সন্দেহপূর্ণ চিত্তে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল : পরস্পর হাতে হাত দিয়ে রাজনৈতিক এবং নৈতিক জীবনকে বিষাক্ত করে তোলা। বহু বছর ধরে এ তুলনামূলক বিষাক্ত পদ্ধতি গণমানসকে অসুস্থ করে তুলেছে। বড় শহরে বিশেষ করে ছড়িয়ে পড়েছে সিফিলিসের মত ভয়ঙ্কর রোগ; দেশের সর্বপ্রান্তে রাজরোগ ধীরে ধীরে পা রেখে জীবনকে কেড়ে নিচ্ছে। অর্থাৎ তার নির্দিষ্ট ফসল সে নিশ্চিন্তে ঘরে তুলে চলেছে।
যদিও এ দুই ক্ষেত্রেই জাতির জীবনে বিপদের সংকেত জানিয়ে চলেছে; পুরো ব্যাপারটা দেখে শুনে মনে হয় যে কেউই এ প্রতারণার ব্যাপারে কোনরকম সক্রিয় ব্যবস্থা নেয়নি। বিশেষ করে সিফিলিসের ব্যাপারে তো মনে হয় সমগ্র রাষ্ট্র এবং গণমানস পুরোপুরি এর কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে।
এ পরিস্থিতির বিরোধিতার মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন ছিল সত্যিকারের যতটুকু পরিষ্কার করা হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি জোরের সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটাকে ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করার। এখানেও একমাত্র রোগকেই সোজাসুজি আক্রমণ করা শ্রেয়, রোগের উপসর্গগুলোকে নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও প্রধান কারণটা এভাবে নির্ণীত হওয়া উচিত যাতে ভালবাসাটাকে বেশ্যাবৃত্তির নামান্তর বলেই প্রতিভাত হয়। যদিও এ পথে ভয়ানক এ ব্যাধিকে আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়, জাতিকে আরো অনেক বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। কারণ এ বেশ্যাবৃত্তির থেকে যে নৈতিক অধঃপতরেন সৃষ্টি তা জাতিকে আরো বেশি নিচে টেনে নামাবে। ধীরে হলেও নিশ্চিতরূপে। আমাদের আধ্যাত্মিকতাবাদকে ইহুদীকরণ এবং আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিকে ধনলোভী করে তোলার ফলাফল আজ হোক কাল হোক আমাদের ভাবীকালের ওপর তা’ আঘাত হানতে বাধ্য। দৃঢ় এবং স্বাস্থ্যবান সন্তান, যারা প্রকৃতির আশীর্বাদধন্য, তাদের পরিবর্তে আমাদের ঘর-সংসার ভরবে এমন কতগুলো সন্তানে যারা এ অর্থনৈতিক হিসেবের ফলশ্রুতি হিসেবে মানবজাতির নমুনাস্বরূপ হবে। অর্থনৈতিক কারণও দিনের পর দিন বিবাহের ভিত্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভবিষ্যতে বিবাহের এটাই একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ভালবাসা তখন তার বহিঃপ্রকাশের জন্য অন্য পথ খুঁজে নেবে।
এখানেও অন্যান্য ক্ষেত্রের মত প্রকৃতিকে কিছু সময়ের জন্য অস্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু আজ হোক কাল হো সে তার নির্মম প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বে। এবং মানুষ যখনই এ সত্য উপলব্ধি করবে, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।
আমাদের নিজস্ব উদারতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ যে প্রাথমিক বিবাহবন্ধনের কারণগুলোকে আমরা কিভাবে লুণ্ঠন করেছি ক্রমাগত সেইগুলোকে অস্বীকার করে। এখানেও মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে সেই আমাদের চিরাচরিত অভ্যাস; একদিকে সামাজিক সমস্যার চাপ, অপরদিকে অর্থনৈতিক অবস্থা। একটা আমাদের নিয়ে গেছে বংশগত দুর্বলতার পথে, আরেকটা মিশ্রিত রক্তে। বড় বড় দোকানের ইহুদী মালিকদের কন্যারা মহাপ্রভুদের বংশবৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সঙ্গিনী বলে বিবেচিত এবং এ সঙ্গিনীদের সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি সত্যই অত্যন্ত প্রখর। এ সমস্তই সমাজকে অধঃপাতে নিয়ে চলেছে। বর্তমানে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজও সেই পথেই এগিয়ে চলেছে। তাদের যাত্রাপথের শেষে বিন্দুর লক্ষ্যও সেই একই বিন্দুতে।
এ অস্বস্তিকর সত্যটাকে তড়িঘড়ি এবং উত্তেজনাহীন অবস্থায় মার্জনা করে সরিয়ে একপাশে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এমনভাবে পুরো ব্যাপারটাকে রূপ দেওয়া হয়েছে যে এভাবে সমস্ত ব্যাপারটাকেই মুছে ফেলা সম্ভব।
কিন্তু না এটাকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমাদের শহর এবং নগরগুলোর লোকসংখ্যার বিরাট একটা অংশ বেশ্যাবৃত্তিতে আসক্ত হয়ে পড়েছে; কারণ হল প্রণয়ের প্রতি তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। এবং তাদের নিজেদের জীবন বিভিন্ন যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কলুষিত হয়ে চলেছে। ঘরের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যেই তা স্পষ্ট প্রতিভাত। এগুলো হল দুঃখজনক এবং বিষাদময় ঘটনার সাক্ষ্য যে আমাদের যৌনজীবনে কষাঘাত কত তীব্র হয়ে উঠছে। এ যন্ত্রণায় প্রত্যক্ষ ফলাফল হল পিতামাতার পাপ।
এ অস্তিত্বময় এবং চরম সত্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার অনেক পথ আছে। বহু লোকই অন্ধভাবে জীবনের পথ চলে। অথবা চোখ খোলা রাখলেও চারপাশের অনেক কিছু দেখতে চায় না। কিছু লোক আবার নিজস্ব মতবাদের জালে নিজেদের আবদ্ধ রাখে। এটাই হল জীবনের কদর্যময় দিকগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার সস্তা এবং সোজা পথ। পুরো ব্যাপারটাই যেন মিথ্যা এবং হাসির ঘটনা। যখন পুরো ব্যাপারটা এর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, তারা সমস্ত ব্যাপারটাকে পাপ-পূর্ণ এবং জীবিকাবিহীন বলে। আক্ষেপ করে।
শেষে যারা এ চাবুকের দ্বারা কি ভয়ঙ্কর ফলাফল হবে বুঝতে পেরেছিল তারাও শুধু কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে তাদের দায়-দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলেছে; কারণ তারা বুঝেছে এ ধ্বংসের সামনে তারা সম্পূর্ণ অসহায়। সুতরাং পুরো ব্যাপারটাই তার আপন গতি পথে এগিয়ে চলে।
সন্দেহ নেই সমস্ত ব্যাপারটাই সুবিধেজনক এবং সহজ; শুধু এর সুবিধাজনক দিকটাই আমাদের জাতীয় জীবনে চরম বিপদ ডেকে এনেছে। অন্যান্য জাতিরা আমাদের থেকে উন্নত নয়, এর দোহাই দিয়ে আমাদের জাতির অধঃপতন কোনরকমেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। শুধু যন্ত্রণাটার ওপর সহানুভূতির প্রলেপ মাখিয়ে সহ্য করার পথটাকে সুগম করে তোলা যায় মাত্র। কিন্তু প্রয়োজনীয় যে প্রশ্নটা এখানে থেকে যায় : কোন্ জাতি এ চাবুকের কষাঘাতের আঘাত প্রথমে এড়িয়ে উঠবে, এবং কোন জাতি এর বশ্যতা স্বীকার করবে। সেটাই হবে জাতির পক্ষে সমস্ত পরিস্থিতির চূড়ান্ত পরিণাম। বর্তমানে জাতির মূল্যায়নের পরীক্ষার সময় চলেছে। যে জাতি এ পরীক্ষায় পাশ করতে অক্ষম, তাদের মৃত্যু অনিবার্য এবং তাদের জায়গা তাদের চেয়ে অধিকতর বলবান এবং স্বাস্থ্য সম্পন্ন জাতি দখল করবে; যারা আরো বেশি দুঃখ কষ্ট সহ্য করে নিতে সক্ষম। যেহেতু বিশেষ করে এ সমস্যা ভাবীকালের, সেইহেতু যে কোন পিতা মাতার পাপ তার বংশের দশম পুরুষেও গিয়ে পর্যন্ত বর্তায়। রক্ত এবং জাতির পবিত্রতা লঙ্ন করার ফলাফল এ চরম দুর্দশা।
এ রক্ত এবং জাতির বিরুদ্ধে পাপ হল এ পৃথিবীতে বংশানুক্রমে এবং যে জাতি এ পাপে পাপী তার ধ্বংস অনিবার্য।
যুদ্ধ পূর্ব–জার্মানিতে এ প্রধানতম সমস্যাটার প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছিল তা’ রীতিমত লজ্জাজনক। আমাদের যুবকদের একটা বিরাট অংশ যাদের বড় বড় শহরে বাস, তাদের ভেতরে এ জীবাণুর অনুপ্রবেশ বন্ধ করার কি কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল? অথবা, আমাদের যৌনজীবনকে কলুষিত এবং ধ্বংস করার বিরুদ্ধেই বা কি করা হয়েছিল? অথবা, আমাদের সমর্থ জাতীয় জীবনে এবং সিফিলিস রোগ ছড়িয়ে পড়ার বিরুদ্ধেই বা কতটুকু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল? এর সবচেয়ে ভাল উত্তর হল কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল?
এলোমেলো পথে এ সমস্যার মোকাবিলা করার চেয়ে শাসকবর্গের চিন্তা করা উচিত ছিল যে এ সমাধানের ওপরেই ভবিষ্যত বংশাবলীর কল্যাণ নিহিত। তবে এটাও স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে এ সমস্যার মোকাবিলা একমাত্র নির্মম পথেই করা চলে। প্রাথমিক কাজ হল সমস্ত জাতির একাগ্রতা এ বিপদের দিকে নিবদ্ধ করা উচিত; যাতে প্রত্যেকটি ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে সন্ত্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে। ব্যক্তিগত কোন চরিত্রের ওপর বাধা নিষেধ আরোপ করাটাও অনর্থক, বা তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরো ব্যাপারটাকে জনসাধারণ মেনে নিচ্ছে। সর্বব্যাপী এবং শৃখলাবদ্ধভাবে এ সমস্যার এমন মোকাবিলা করতে হবে যাতে সমস্ত গণমানসের নজর এদিকেই পড়ে। এবং অন্যান্য দৈনিক সমস্যাগুলোকে কিছু সময়ের জন্য সরিয়ে পিছু হটিয়ে দেয়।
প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে দেখা যাবে যে গণমত তৈরির ব্যাপারে সমস্যাটা যথেষ্ট পরিমাণে জটিল, সেখানে উচিত একটা সমস্যার প্রতি মনোনিবেশ করা; সে মনোযোগ এমন হওয়া উচিত যে যাতে এটা জীবন মরণ সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়। একমাত্র এ পথেই গণমানসকে এমন একটা উঁচু ধাপে জাগরিত করা সম্ভব যে জনতার অদম্য ইচ্ছার সঙ্গে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রচেষ্টা মিলিত হয়ে ফলাফল যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতি ঘটাবে।
ব্যক্তিগত জীবনেও এ সত্য কার্যকরী, অবশ্য যদি সে জীবনে মহান কিছু অর্জন করতে সচেষ্ট হয়। সে তার অগ্রগতির নির্দিষ্ট একটা ধাপে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে এবং সেই ধাপ পার হওয়ার পরেই একমাত্র পরের ধাপে আরোহণের চেষ্টা করবে। যারা তাদের উদ্যম ধাপে ধাপে ওঠার চেষ্টায় ব্যয়িত করে না, এবং সমস্ত শক্তি প্রতিটি ধাপ অতিক্রমের নিমিত্ত ব্যয়িত হয় না তাদের পক্ষে শেষ এবং কাম্য বস্তু অর্জন করা সম্ভব নয়।
সুতরাং ওপরের বক্তব্য অনুসারে দেখা যাচ্ছে মানবজীবনের রাস্তাটা অতিক্রম করতে হলে জনতাকে বোঝানো উচিত যে তাদের সংগ্রামের পরবর্তী বস্তু হল মাত্র একটাই; এবং তার ওপরেই পরের ধাপে সমস্ত কিছু নির্ভরশীল। জনতার পক্ষে তাদের সামনের বিস্তীর্ণ রাস্তাটা নজরে আনা কিছুতেই সম্ভব নয়। যাতে তারা সেই বিস্তীর্ণ রাস্তা অতিক্রম করতে গিয়ে ক্লান্ত এবং অবসন্ন না হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের লব্ধ বস্তু মনে রাখতে সক্ষম; কিন্তু ছোট ছোট ধাপ ছাড়া পুরো রাস্তা অতিক্রম করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়; যেমন পথিক জানে তার পথের শেষ কোথায়! কিন্তু অনাদি পথ তো চিন্তার জগতের বাইরে। একমাত্র এভাবে আমরা তার লক্ষ্য বস্তুতে পৌঁছানো পর্যন্ত সেটার উদ্যম বজায় রাখতে পারি।
এ পথে সমস্ত প্রচারকার্যকে কেন্দ্রীভূত করেই যৌনরোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাটাকে আমরা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে পারি। এবং এটাকে এমনভাবে করতে হবে যে জাতির জন্য এটা একটা কাজ বলে নয়; জাতির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ, বর্তমানে এ মনোভাব জনতার মধ্যে তৈরি করে। গণমানসের কাছে এ সত্যতাকে স্পষ্টরূপে তুলে ধরার জন্য সমস্ত রকমের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজন, যতক্ষণ না পর্যন্ত সমস্ত জাতি চিন্তা করে যে এ সমস্যার সমাধানের ওপরেই সমগ্র জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করছে; এককথায় বলা যেতে পারে উজ্জ্বল ভবিষ্যত অথবা জাতির অবলুপ্তি।
একমাত্র এ প্রাথমিক আয়োজনের পর–প্রয়োজনে এ সময়ের ব্যাপ্তি কয়েকমাসও হতে পারে, গণমানস এবং সংকল্পকে পরিপূর্ণরূপে জাগরিত করা সম্ভব। একমাত্র তখনই গভীর এবং নির্দিষ্ট একটা পন্থা নেওয়া যাবে, কারণ তখন তো গণমানস সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার জন্য সম্পূর্ণভাবে তৈরি; তাই জনসাধারণের ইচ্ছাশক্তির ঘাটতি তাতে থাকবে না। স্পষ্ট মনে রাখা উচিত এসব আবর্জনা ঝেটিয়ে সরানোর জন্য প্রয়োজন প্রচুর আত্মত্যাগ এবং প্রচণ্ড রকমের পরিশ্রমের। যৌনরোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অর্থ হল বেশ্যাবৃত্তি, ভুয়া সংস্কার, মিথ্যা জনমত ইত্যাদির বিরুদ্ধে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর ভেতরে সংগ্রাম বিশেষ।
রাষ্ট্রের এ সংগ্রামে নামার আগে প্রথমেই দেখে নিতে হবে যুবক সম্প্রদায় যেন ছোট বয়সে বিয়ে-সাদীর সুযোগ পায়; বেশি বয়সের বিয়ের আমরা যত যুক্তিই দেখাই না কেন, মানবজাতির কাছে ব্যাপারটা লজ্জাকর।
বেশ্যাবৃত্তি মনুষ্যত্বের পক্ষে কলঙ্কবিশেষ। এবং এ বৃত্তি দয়াদাক্ষিণ্য বা শিক্ষা দ্বারা দূর করাও সম্ভব নয়। এর সীমাবদ্ধতা এবং দূরীকরণ একমাত্র সম্ভব, যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে এ বৃত্তিকে মুক্ত করা যায়। তার জন্য প্রয়োজন যুবক যুবতীদের অল্প বয়সে বিবাহের সুযোগ দান। এটাই হল এ বৃত্তি দূরীকরণের প্রধান উপায়।
এসব কারণে মানুষ এত সহজে বিপথগামী হয় যে ইদানীং যে কোন মাকে বলতে শোনা যাবে যে তার মেয়ের জন্য সে ভাল ছেলে খুঁজে পাচ্ছে না। আর সে কারণে বেশ্যাদের প্রতি আসক্ত কোন ছেলেকেই বাধ্য হয়ে সে মেয়ে বিয়ে করে। এ সঙ্গী নির্বাচনের ফলে তাদের সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যত যা হওয়া উচিত, তাই হয়ে থাকে।
একটু চিন্তা-ভাবনা করলেই যে কেউ উপলব্ধি করতে পারবে যে পুরো পদ্ধতিটাই সার্থক বংশাবলী উৎপাদনের বিরোধী। এবং প্রকৃতিতে জেনে শুনে তার অধিকার থেকে প্রতারণা করা হচ্ছে; তা হলে একটা প্রশ্নই থেকে যায় : বিবাহ বলে ব্যাপারটার অস্তিত্ব এখনো রয়েছে কেন? এবং তার কাজটাই বা কী? এটাত তা হলে বেশ্যাবৃত্তির নামান্তর। আমাদের উত্তর পুরুষদের জন্য তবে কি আমাদের কোন মাথা ব্যাথাই নেই? অথবা লোকে বুঝতে পারছে না যে প্রকৃতি তার অভিশাপ ধীরে ধীরে তাদের ওপরে আরোপ করছে এবং ভবিষ্যত বংশাবলীকে তাদের এ নির্বুদ্ধিতার জন্য প্রকৃতির এক ভীষণ নিষ্ঠুর আইন কানুনের মুখোমুখি হতে হবে? এভাবেই তথাকথিত সভ্য জাতিরা অধঃপতনে যায় এবং একসময় ধ্বংস হয়।
বিবাহেই বিবাহের সমাপ্তি নয়; এর আরো মহৎ উদ্দেশ্য আছে। যার প্রধান কাজ হল উৎকৃষ্ট মানবজাতি তৈরি করা এবং সেই মানকে ধরে রেখে বাড়িয়ে চলা। এটাই হল বিবাহের সত্যিকারের অর্থ এবং উদ্দেশ্য।
এ অর্থ এবং উদ্দেশ্যকে যদি মেনে নেওয়া হয়, তবু লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যে পথের প্রয়োজন, তাকেও মেনে নিতে হবে। সুতরাং অল্প বয়সে বিবাহটাকে আইন করে দেওয়া উচিত। কারণ অল্পবয়সী যুবক-যুবতীদের মধ্যে এখনো সেই আদিম শক্তি বর্তমান যা নাকি সফল উত্তর পুরুষ উৎপাদনের ব্যাপারে গর্বের বস্তু এবং যে শক্তি বর্তমানেও অব্যাহত। অবশ্য বাল্যবিবাহ আইন করে করা সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন, সেগুলো মেটানো সম্ভব হচ্ছে। এমন কি তার আগে ব্যাপারটা চিন্তা করাই উচিত নয়। অন্য ভাষায় বলতে গেলে এ সমস্যার সমাধান যদিও আপাতদৃষ্টিতে সমস্যাটাকে সহজ সরল সামাজিক পটভূমিকার মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া কখনই সম্ভব না। এবং এ সমস্যার মোকাবিলা করার ব্যবস্থাটাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখে তবে প্রয়োগ করা উচিত। বিশেষ করে তথাকথিত গণতন্ত্র যখন বাড়ি ঘরের সমস্যাটাকে এখনো সমাধান করতে পারেনি।
আমাদের অর্থহীনের মত বেতন ব্যবস্থাও বাল্যবিবাহের বিরোধী, যার দ্বারা নাকি পরিবার প্রতিপালন একেবারেই অসম্ভব। অতঃপর দেখা যাচ্ছে বেশ্যাবৃত্তিকে যথার্থ উপায়ে মোকাবিলা করার জন্য মৌলিক সামাজিক পরিবর্তনের একান্ত প্রয়োজন এবং তারপরেই বাল্যবিবাহ চালু করা সহজ হয়ে দাঁড়াবে। এ সমস্যার সমাধানের এটা হল প্রাথমিক নিয়ম।
দ্বিতীয়ত, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এবং সন্তান প্রতিপালনের মূল প্রথাগুলোর অবিলম্বে মূলোৎপাটন করা-যে কারণগুলোয় কাউকেই সবিশেষ চিন্তিত দেখা যায় না। আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে ভারসাম্য আনার প্রয়োজন, বিশেষ করে মানসিক এবং দৈহিক ব্যাপারে।
আমাদের মাধ্যমিক স্কুল বলে যা আজ পরিচিত, তা গ্রীক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি অপমান ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এটা ভুলে গেছে যে একমাত্র সুগঠিত শরীরেই চরিত্রবান মানুষ পাওয়া যেতে পারে। এ বক্তব্য কিছুটা হেরফের করে সমগ্র জনতার পক্ষে উপযোগী করা যায়।
যুদ্ধ পূর্ব জার্মানিতে সময়টা এমন ছিল যখন কেউ সত্যের ওপরে কিছু চিন্তা-ভাবনা করতে চাইত না। শরীরচর্চাকে প্রচণ্ড রকমের অবহেলা করা হত; জাতির উন্নতির পক্ষে মনের একদিককার অনুশীলনকেই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হত। এ ভুলের প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই দেখা দেয়। বলশেভিক শিক্ষা যে এসব রাজ্যগুলোতে বিস্তৃতি লাভ করে, তা’ কোন হঠাৎ ঘটনার ফলশ্রুতি নয়। কারণ সেইসব প্রদেশের অধঃপতিত লোকগুলো উপবাসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ মধ্য জার্মানি, স্যাস্কনি এবং রুড় উপত্যাকার কথা বলা চলে। এসব জেলাগুলোতে কোনরকম বাধা বলতে যা বোঝায় তা এরা পায়নি। এমন কি ইহুদী-রূপ রোগ সংক্রমণের বিরুদ্ধে সমাজের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় থেকেও কোনরকম বাধা আসেনি। এর সহজ কারণ হল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় নিজেরাই শারীরিক দিক থেকে তখন অধঃপাতে গেছে; কষ্ট বা ক্লেশের দরুণ এ অধঃপতন নয়। নিছকই শিক্ষাপদ্ধতির ফল। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকটা যা আমাদের সমাজের উঁচু শ্ৰেণীর মধ্যে প্রচলিত, বর্তমান যুগের জীবন সংগ্রামের জন্য তা সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী। সুতরাং তারা তাদের নিজেদের প্রতিপালনে অক্ষম। জীবনধারণের ক্ষেত্রেও তাদের সক্ষমতা কোথায়। প্রায় প্রতিটি কাপুরুষতার ক্ষেত্রে দৈহিক অপুষ্টি হল আসল কারণ।
অবিবেচনা ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিজীবী শিক্ষা-ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। তার ফলাফল হল দৈহিক শিক্ষার অবনতি; যার পরিণতি হল অল্প বয়সের যৌন চিন্তায়। যেসব ছেলেদের খেলাধূলার মাধ্যমে শরীর গঠন হয়, তাদের যৌন প্রবণতা অন্যান্য ছেলেরা যারা শুধু ঘরে বসে মনের খোরাক জুগিয়ে চলেছে, তাদের চেয়ে অনেক কম। সত্যিকারের শিক্ষাপদ্ধতি জীবনের এ দিকটাকে অবহেলা করতে পারে না। এবং আমাদের স্মরণে রাখা উচিত যে স্বাস্থ্যবান পুরুষ এবং স্বাস্থ্যবতী মহিলা কোন দুর্বল প্রাণীর জন্ম দেবে না। যারা জন্মের পরেই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।
এভাবে আমাদের শিক্ষার সমস্ত শাখাকে ছকে বাধতে হবে যাতে ছেলেরা তাদের অবসর সময়টাকে শরীর চর্চার কাজে লাগাতে পারে। সে বছরগুলো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কাটিয়ে যেন তার শরীর গঠন করতে পারে। সিনেমা দেখে নষ্ট করার কোন অধিকার তার নেই। কিন্তু যখন তার দিনের কাজ সাঙ্গ হবে, সে যেন তার শরীর গঠন করতে পারে। কারণ প্রয়োজনের সময় যেন তার শরীর গঠনের ব্যাপারে ঘাটতি না পড়ে। আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির এটাও একটা বড় দায়িত্ব, তবু জ্ঞান বা বিজ্ঞতাই তার ভেতরে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া নয়। আমাদের স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে প্রতিটি ছাত্রের মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় যে শরীর তৈরি করার দায়িত্ব তার নিজের ওপরে অর্পিত। উত্তর পুরুষের কাছে পাপ রূপে গণ্য হয় এমন কিছু বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা তাদের নেই, কারণ তাহলে সেটা জাতির বিরুদ্ধেই কাজ করা হবে।
মনের অসুস্থতার সঙ্গে সংগ্রামের জন্য শরীর গঠনের বিশেষ প্রয়োজন। আজকের গণজীবন যেন যৌন উত্তেজনার বিরাট একটা চুল্লী। চলচ্চিত্র, নাটক এবং খেলাধূলা করার জায়গাগুলোর দিকে একনজর ফেললেই বোঝা যায় যে এগুলো আমাদের সঠিক পরিবেশ নয়। বিশেষ করে আমাদের যুবকদের পক্ষে। বিজ্ঞাপনপত্র এবং বিজ্ঞাপনের জন্য টাঙানো বিজ্ঞপ্তিগুলো জনতাকে অত্যন্ত ইতরভাবে আকর্ষণ করে। যে এখনো তার যৌবনোথ প্রবল ইচ্ছা হারায়নি, তাদের স্পষ্ট বুঝতে এতটুকু কষ্ট হবে না যে এগুলোর পরিণতি কি ভয়ানক। এ কাম যা নাকি খারাপ কাজে প্ররোচনামুলক, যুবকদের মাথায় ঘোরে। তারা বুঝতেই পারে না ব্যাপারটা কি। দুর্ভাগ্যবশত এ শিক্ষাব্যবস্থার ফলাফল কি তা আমাদের সমকালীন যুবকদের দেখলেই বুঝতে পারা যাবে। যারা অকালে পরিণত হয়, তারা সহজেই জুড়িয়েও যায়। মাঝে মাঝে আমাদের চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়স্ক ছেলেদের ওপর আইন তার আলো ফেলে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে এ বয়সের ছেলেরাও যৌন রোগগ্রস্ত। এটা কি দুঃখ এবং লজ্জাজনক নয় যে অসংখ্য দৈহিক দুর্বল এবং বুদ্ধির দিক থেকে নষ্ট যুবক ছেলেরা যারা বিয়ের নামে বড় শহরে গণিকাদের সঙ্গে বসবাস করছে।
যারা সত্যিকারের গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে সততার সঙ্গে সংগ্রাম করতে ইচ্ছুক, তাদের প্রথমেই যে কারণে গণিকাবৃত্তি প্রসারলাভ করেছে সেই কারণগুলোকে দূর করতে হবে। নির্ভর চিত্তে তাদের দূষিত নীতিগুলোকে সরাতে হবে যা নাকি আমাদের কালচারকে বিষাক্ত করে তুলেছে। এবং তার জন্য যে আর্তনাদই উঠুক না কেন, তাতে ভয় পেলে চলবে না। আমরা যদি আমাদের যুব সমাজকে আজকের এ পঙ্কিল পরিবেশ থেকে টেনে নিয়ে না আসি, তা হলে এ পঙ্কিল পরিবেশ তাদের গ্রাস করে ফেলবে। যে সব নেকি এসব দেখতে চায় না, তারা কিন্তু অপ্রত্যক্ষভাবে এ পরিবেশকে বাড়াতেই সাহায্য করে চলেছে। এবং ভবিষ্যতের আঙিনায় এ গণিকাবৃত্তি ছড়িয়ে পড়ার জন্যও তারা দায়ী। শুধু এ নয় যে তারা উত্তর-পুরুষদের কাছে এর জন্য কি জবাব দেবে! আমাদের কালচারের এ বিশুদ্ধিকরণের প্রয়োজনীয়তা জীবনের সর্বক্ষেত্রে। অভিনয়, শিল্পকলা, সাহিত্য, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে এ ছোপ লেগে রয়েছে, তার থেকে এ ছোপ মুছে ফেলে জাতির উদ্দেশ্যে তা’ উৎসর্গ করতে হবে। জনসাধারণের জীবন তথাকথিত আধুনিক প্রেম সম্বন্ধীয় ব্যাপার-স্যাপারগুলো থেকে মুক্ত করতে হবে; শুধু তাই নয় পৌরষত্যহীন এবং অতি বিনয়ী ভাবধারাগুলো থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করা উচিত। এসব করতে গিয়ে আমাদের নজর রাখা উচিত যে পদ্ধতি নেওয়া হবে তা যেন অত্যন্ত চিন্তার সঙ্গে বিবেচনা করা হয়, যাতে শরীর এবং মনকে জাতির মঙ্গলের জন্য উন্নত করা যায়। একটা জাতির রক্ষার ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দ্বিতীয় পর্যায়ের বিবেচনা।
এসব ব্যবস্থা নেওয়ার পরেই একমাত্র এ অভিশপ্ত চাবুকের বিরুদ্ধে ভেষজবিদ্যা প্রয়োগের প্রচার করা উচিত এবং তাতে কিছুটা হলেও সাফল্য লাভ করা সম্ভব। কিন্তু এখানে আবার দোমনা ভাব কিন্তু অর্থহীন। দূরদর্শিতা এবং প্রয়োজনীয় পদ্ধতিকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে এগোলে অসুস্থ এক জনের বীজ সুস্থ শরীরে ছড়িয়ে পড়ে সেই অসুস্থতা ক্রমাগত বেড়েই চলবে। এটা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াবে এক ধরনের মনুষ্যত্ব যা নাকি একজনকে বাঁচাতে গিয়ে হাজার জনের ধ্বংস অনিবার্য। অপরিপূর্ণ লোকদের ধারা পঙ্গু বংশ বাড়িয়ে চলার দাবিকে উপেক্ষা করা যে কোন জাতির পক্ষে খুবই অসম্ভব ব্যাপার, যার ভিত যথেষ্ট শক্ত মাটিতে প্রোথিত। হাজার হাজার মানুষের ক্ষেত্রে অসুখী এবং দুঃখ যন্ত্রণাটাকে কাটিয়ে ওঠা এ পদ্ধতিকে কাজে লাগালে সম্ভব হবে। এতে জাতির স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করবে। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করে গেলে তা যৌন রোধ বিস্তারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমান শতাব্দীর সাময়িক বেদনা হাজার হাজার বছরের যন্ত্রণার থেকে আমাদের দেশের মানুষকে মুক্তি দেবে।
সিফিলিস্ এবং এর পটভূমি গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম সমগ্র মানবজাতির পক্ষে বিরাট একটা কাজ।
কিন্তু আলস্য এবং কাপুরুষতার জন্য যদি এ যুদ্ধ খতম করার সগ্রামে প্রকৃত মানুষ হয়; তবে আমাদের কল্পনা করে নিতে বোধকরি কষ্ট হবে না যে পাঁচশো বছর পরে এর ফলাফল কি হয়ে দাঁড়াবে। ঈশ্বরের ছায়া মানুষের চরিত্রে অতি কম পরিমাণেই অবশিষ্ট থাকবে; একমাত্র দৃষ্টিকর্তাকে ব্যঙ্গ বা উপহাস করা ছাড়া।
তবে জার্মানিতে এ কশাঘাতের প্রতিশোধক হিসেবে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? যদি আমরা এর উত্তরের জন্য শান্তভাবে চিন্তা করি, তা আমাদের হতাশই করবে। এটা সত্যি যে সরকার যদি এ রোগের ভয়ানক প্রকৃতি এবং ক্ষতিজনক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে অবহিত ছিল। তবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তা শুধু নিরর্থকই নয়, অনর্থকারীও বটে। তারা রোগের কারণটা সম্পর্কে উদাসীন থেকে নিরাময়ের লক্ষণগুলো বেছে নিয়ে সে রোগ সাময়িক চাপা দেবার ব্যবস্থা করত। বেশ্যাদের ডাক্তারী পরীক্ষা করা হত এবং যতটা সম্ভব আয়ত্তে রাখার চেষ্টা হত; তবু রোগের লক্ষণগুলো যখন সর্বাঙ্গে ফুটে বের হত, তখন তাদের পাঠানো হত হাসপাতালে। চিৎকার আর্তনাদ জুড়ে দিলে মনুষ্যত্বের কারণে তাদের আবার ছেড়েও দেওয়া হত।
এটাও সত্যি যে সংরক্ষণ আইন যা পাশ করা হয়েছিল তাতে সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে যৌন সহবাস করাটা রীতিমত শাস্তিমূলক। অথবা যারা যৌন কোন রোগে ভুগছে। তাদেরও শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে যদি সহবাস করে। তত্ত্বের দিক থেকে ঠিকই ছিল; কিন্তু বাস্তবে সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য আদালতে উপস্থিত হত না যারা তাদের স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যত হরণ করেছে। কারণ এসব ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে মেয়েদের বেলায় অনেক বেশি অশিষ্ট মন্তব্যের আশঙ্কা। এবং যে কারোর পক্ষে সহজেই এটা অনুমেয় তাদের অবস্থা কি হয়ে দাঁড়াবে যদি তাদের মধ্যে এ রোগ স্বামীদের দ্বারা ছড়িয়ে থাকে। মেয়েরা কি এ ক্ষেত্রেও তাদের নালিশ নিয়ে এগিয়ে আসবে? অথবা তারা কি করবে?
ছেলেদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটাতে আরেকটা সত্য নিহিত, বিশেষ করে তারা যখন মাদক দ্রব্যের নেশায় থাকে তখন তাদের অজ্ঞাতসারেই এ বিপদের দিকে ছুটে চলে। তার অবস্থাই তাকে প্রণয়ের সত্যিকারের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে দেয় না। প্রতিটি রোগ এস্ত গণিকা পুরুষের এ অবস্থায় সুযোগের জন্য প্রতীক্ষা করে। এর ফলাফল হল এ যে হতভাগ্য পুরুষ পরে তার এ অবস্থার সত্যিকারের হিতকারী পৃষ্ঠপোষক যে কে তা আর স্মরণে আনতে পারে না। এটা বার্লিন বা মিউনিকের মত বড় শহরে কোন আশ্চর্যজনক ঘটনাই নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গাঁয়ের থেকে শহরে আসা লোক ব্যাপার-স্যাপার দেখে এত নির্বাক ও বশীভূত হয়ে পড়ে যে গণিকারা সহজেই তাদের লুণ্ঠন করে।
সবশেষে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে (কে বলতে পারে যে) রোগের সংক্রমণ তার মধ্যে হয়েছে কিনা? অসংখ্য ক্ষেত্রে দেখা গেছে ওপর ওপর দেখতে নিরোগ লোকেরও পরে রোগটা আবার উদয় হয়েছে এবং তার অজ্ঞাতেই তাকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে চলেছে।
সুতরাং বাস্তব ক্ষেত্রে এ সংরক্ষণ আইনের ফলাফল নেহাত-ই নেতিবাচক। গণিকাবৃত্তির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই। শেষমেষ চিকিৎসা ও নিরাময়ের ব্যাপারেও ব্যাপারটা খুব নির্ভরযোগ্য ও সন্দেহাতীত নয়। খালি একটা জিনিস দিনের আলোর মত স্পষ্ট; তা; হল এ কশাঘাত দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। যে ব্যবস্থাই নেওয়া হয়ে থাক না কেন, এ ব্যাপারটা তাদেরই অপদার্থতা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট।
বাকি ব্যাপারগুলোও একই ব্যাপারের মত নিরর্থক। মানুষের গণিকাবৃত্তি কমা দূরে থাক, কোন কিছুই ফললাভ হয়নি।
যারা এ ব্যাপারের সঙ্গে একমত নয়, তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ তারা যেন এ রোগের সংখ্যাতত্ত্বের দিকটা দেখে, গত শতাব্দীতে এর বৃদ্ধি এবং সমকালীন অবস্থায় এর বৃদ্ধির সম্ভাবনা কি রকম। সাধারণ পর্যবেক্ষক-যদি সে একেবারে নির্বোধ না হয়, তবে পুরো ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরলে ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠবে।
এ দোমনা ও ভীতু মনোভাবের দরুণ প্রাক যুদ্ধের জার্মানি দুষ্ট লোকে ভরে গিয়েছিল। সন্দেহাতীতভাবে এটা জাতির ক্ষয়ের লক্ষণ। যখন মানুষ তার নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সংগ্রামের সাহস হারিয়ে ফেলে, তখন তো তার এ পৃথিবীতে টিকে থাকার সংগ্রাম করার অধিকারই সে হারায়।
পুরনো জার্মানিতে এর একটা বাস্তব চিত্র হল ধীরে ধীরে সংস্কৃতির অবক্ষয়। কিন্তু সংস্কৃতি বলতে আজকের তথাকথিত শাসন যা নাকি সভ্যতা বলে পরিচিত তা বোঝাচ্ছি। বরং এটা আজ জীবনের উন্নতি বলতে যা বোঝায় তার বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছে।
গত শতাব্দীর মোড় ফেরার সময় পৃথিবীতে একটা নতুন জিনিসের অভ্যুদয় হয়েছে; এ ব্যাপারটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিদেশী যা নাকি আমাদের কাছে আগে অজ্ঞাত ছিল। আগে ভাল কোন জিনিস গ্রহণ করাটাকেও দোষণীয় বলে মনে করা হত; কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসনের পর থেকে তা অনেক দূরে সরে গেছে। হয়ত ভবিষ্যত পুরুষেরা এর মধ্যে কোন একটা ঐতিহাসিক মূল্য খুঁজে বার করবে। কিন্তু নতুন বংশধরেরা যে শুধু শৈল্পিক সৃষ্টির দিক থেকে বিপথগামী তাই নয়, এর মধ্যে কারো কারো তো আদর্শ বলত কোন অনুপ্রেরণাই নেই। এটা হল সাংস্কৃতিক ধ্বংসের বহিঃপ্রকাশ।
বলশেভিজম মতবাদের বিশ্বাসীদের প্রতিটি শিল্পকর্ম তাদের মতবাদে জারিত এবং পুরো সংস্কৃতিটাই তাদের এ জারক রসে ডোবানো।
যাদের এ বক্তব্যে সন্দেহ আছে তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ যেসব রাষ্ট্রে বলশেভিজম প্রচলিত, যদি সেইসব ভাগ্যবান রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে লোকগুলো দেহমনে ব্যাধির দ্বারা কী ভীষণভাবে আক্রান্ত, যা শুধু তাদের পাগল করে তোলেনি, অধঃপাতেও নিয়ে গেছে। এসব শৈল্পিক বিপথগামীতা যা নাকি কিউবিজিম, ডাডজিম, প্রভৃতি নামে খ্যাত, এ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে সেগুলোই হল এসব রাষ্ট্রের বহিঃপ্রকাশ। এমন কি ব্যাভেরিয়ার ক্ষণস্থায়ী সোভিয়েত গণতন্ত্রের সময়ের এ জিনিসগুলোর প্রকাশ ঘটেছিল। সেই সময় অনেকেরই হয়ত বা স্মরণে আসবে সরকারি প্রাচীরপত্র, বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র ইত্যাদিতে শুধু রাজনৈতিক অবক্ষয়ের চিহ্নও কত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল।
প্রায় বছর ষাটেক আগে আজকের মত রাজনৈতিক ধ্বংস কল্পনাতেও আনা অসম্ভব ছিল। আজকে সাংস্কৃতিক জগতে অবক্ষয় যা নাকি কিউবিস্ট এর ভবিষ্যত ছবিগুলোতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত; ষাট বছর আগে এ ধরনের প্রদর্শনী, যা তথাকথিত ডাডেস্টি সম্পূর্ণ অসম্ভব একটা আদর্শ বলে মনে করা হত। এ ধরনের প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপকদেরও জায়গা হত গিয়ে পাগলাগারদে। অথচ আজ তাদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সভাপতির স্থান দেওয়া হচ্ছে। সেই সময়ে এ ধরনের মড়ককে বাড়তে দেওয়া হত না। জনসাধারণ ব্যাপারটাকে কখনোই মেনে নিত না, বা সমকালীন সরকার চুপ করে থাকত না। কারণ এ ধরনের বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন পাগলদের পাগলামী থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করা সরকারের কর্তব্য। কিন্তু সেই বুদ্ধিজীবী পাগলদের পাগলামী এ ধরনের শিল্পকে মেনে নেওয়া ক্রমেই বেড়ে চলেছে; মানবজাতির ইতিহাসে এটা একটা বিরাট পরিবর্তনের নিকৃষ্টতম উদাহরণ। কারণ এর মাধ্যমেই জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তির পশ্চাদগমন শুরু হয়েছে, যার পরিণতি অচিন্ত্যনীয়।
আমরা যদি আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের গত পঁচিশটা বছর অনুধাবন করি, তাহলে দেখতে পাব সাংস্কৃতিক জগতে কতখানি আমরা পেরিয়ে গেছি। সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যাবে যে এ জীবাণু ছড়িয়ে। সেই সূতীকার বৃদ্ধি আজ হোক কাল হোক আমাদের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে ছাড়বে। এখানে সন্দেহাতীতভাবে দুর্নীতির স্রোত প্রবাহিত। এবং জাতির পক্ষে এটা মর্মান্তিক যে এ ব্যাধিকে আর থামিয়ে রাখা অসম্ভব।
জার্মান শিল্প এবং সংস্কৃতির প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এ রোগ প্রতীয়মান। এখানে সবকিছুই মনে হয় সর্বোচ্চ সীমারেখা অতিক্রম করে দ্রুতগতিতে অবক্ষয়ের দিকে সেই রেখা এগিয়ে চলেছে। শতাব্দীর প্রথমপাদেই নাটকের মান নিচে নামতে শুরু করে, এবং সংস্কৃতির জগতের পটভূমি থেকে দ্রুত সরে যেতে থাকে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল রাজপ্রাসাদের নাটকগুলো। যা বারবার সাংস্কৃতিক জগতের এ বেশ্যাবৃত্তির বিরোধিতা করে এসেছে। অবশ্য এর সঙ্গে ব্যতিক্রম হিসেবে আরো কয়েকটা মুষ্টিমেয় প্রতিষ্ঠানের নাম করা যেতে পারে। সেখানে এমন কিছু নাটকের অভিনয় হত যে লোকে তা না দেখেও তার থেকে উপকৃত হত। এ অবক্ষয়ের একটা দুঃখজনক উদাহরণ হল অনেক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রবেশ দরজায় লেখা থাকত : প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য।
মনে রাখা দরকার যে এ সব প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুবকদের ভেতরে শিক্ষাবিস্তার। শুধু সর্বাধুনিক জ্ঞানসম্পন্নদের আনন্দের খোরাক জোগান নয়, অন্যকালের দিকপাল নাট্যকাররা এ ব্যবস্থা সম্পর্কে কি বলত, সর্বোপরি যার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, কুপিত হতেন, গ্যেটেও বা বিরক্তিতে কত দূরে সরে যেত।
আমাদের আধুনিক জার্মান সাহিত্যের নায়কদের সঙ্গে কি গ্যেটে বা সেক্সপীয়ারের তুলনা করা চলে? তারা হল প্রাচীন, ছাতাধরা, সেকেলে এবং সর্বোপরি নিঃশেষ। এটাই হল বর্তমান যুগের বিশেষত্ব যে শুধু এ যুগের ফসলই নিকৃষ্ট তা নয়, যারা সেই ফসলের উৎপাদনকারী এবং সেই উৎপাদনের যারা সাহায্যকারী তারাও কম নিকৃষ্ট নয়; যা সত্যই একদিন অতীতে সবদিক দিয়ে মহান ছিল। এ সব যুগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হল এগুলো। তার চেয়েও অধম এবং ক্লেশক্লিষ্ট হল মানুষ, যারা এসব যুগের ফসল। এরা যত বেশি আগেকার বংশাবলীর কৃতিত্ব অস্বীকার করবে, তত বেশি নিচে নামবে। এদের একমাত্র ইচ্ছে হল পুরনো পদচিহ্নের সমস্ত চিহ্ন পুরোপুরি মুছে ফেলা। এর কারণ আর কিছুই নয়, যাতে কারোর পক্ষে আর তুলনা করা সম্ভব না হয় যে পার্টির নামে তারা সত্যিকারের কি জিনিস নিয়ত পরিবেশনা করে চলেছে। এ কারণেই নতুন দিগন্তের নামে যে সকল এরা উৎপাদন করে চলেছে, তা শুধু জঘন্য নয়, শোচনীয়ও বটে। আর এদের প্রচেষ্টা যাতে পুরনো দিনের স্মৃতি সম্পূর্ণ মুছে ফেলা সম্ভব হয়। কিন্তু সত্যিকারের কোন পরিবর্তন যা মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর, তা সর্বদা অতীতের সঙ্গে তুলনার জন্য প্রস্তুত থাকে। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে পুরনো দিনের স্মৃতি বর্তমানের ফসলকে সাগ্রহে বরণ করে নিতে সাহায্য করে। কারণ সেক্ষেত্রে এমন কোন আশংকা থাকে না যে অতীতের তুলনায় বর্তমানের চিত্র বিবর্ণ এবং অর্থহীন দেখাবে। মানুষের সাংস্কৃতিক জগতের পরিপূর্ণতার সমুদ্রে পুরনো দিনের স্রোত সর্বদাই বরণীয়। কারণ এ স্মৃতিই তো বর্তমান উৎপাদনের নিয়ামকসূচক। একমাত্র তারাই অতীত স্মৃতির কোন মূল্যায়ণ করে না, বরং যে কোন মূল্যে তা ধ্বংস করতে চায়, কারণ তাদের দেখার মত কিছু নেই।
আর উপরের বিষয়টি শুধু সাংস্কৃতিক জগতের পক্ষেই সত্য নয়, রাজনৈতিক জগতেও এ চিরসত্য। নতুন আন্দোলন যত বেশি নিষ্ফলা, ততবেশি অতীত ঐতিহ্যের ধ্বংসের প্রতি তাদের অবহেলা দেখানোর প্রচেষ্টা। এখানে আবার তাদের সেই মনোভাবই সক্রিয়; অর্থাৎ যা পুরাতন কিন্তু সত্যিকারের তাদের উৎপাদিত ফসলের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট, তাদের বিবেচনায় নিকৃষ্ট। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যতদিন পর্যন্ত ফ্রেডারিক দ্যা গ্রেটের স্মৃতি থাকবে, ফ্রেডারিক অ্যালবার্ট ততদিন পর্যন্ত দ্বিধা মেশানো বাহবাই পেয়ে আসবে।
সূর্যের সঙ্গে চন্দ্রের যেমন তুলনা, সান্ সুসির নায়কের সঙ্গে ব্রেসেনের ভূতপূর্ব গণতান্ত্রিক নেতার তেমনি তুলনা করা চলে। কারণ সূর্যের আলো আকাশের বুক থেকে মুছে যাওয়ার পরেই একমাত্র চন্দ্রের আলোর প্রকাশের সম্ভাবনা। এ কারণেই মানুষের চন্দ্রিমারা নির্দিষ্ট চিরায়ত গ্রহকে ঘৃণা করে এসেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ভাগ্য যদি সাময়িকভাবে এদের দেশের শাসন ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করে, তবে অতীতকে এরা শুধু কলুষিতই করে না, কৌশলে এড়িয়েও যায়। এ সত্যের একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল জার্মান গণতন্ত্রের সংরক্ষণ আইন যা নাকি জার্মান রাষ্ট্র রক্ষার নিমিত্ত করা হয়েছে।
এসব কারণে যে কোন ব্যক্তির পক্ষে সন্দেহ পোষণ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে নতুন আদর্শ, মতবাদ বা দর্শন, যে কোন রকমের রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলন, যা নাকি অতীতে উৎপাদিত হয়েছে তা বর্তমানের তুলনায় নিকৃষ্ট এবং মূল্যহীন। যে কোন পরিবর্তনের শুরু হয়ে থাকে, যা সত্যিকারের মানবজাতির অগ্রগতির পরিচায়ক, শেষ ধাপে যে পাথরটা গাঁথা হয়েছিল তার থেকে। অতীতের সেইসব প্রতিষ্ঠিত সত্যকে কাজে লাগাবার জন্য লজ্জিত হবার কিছুই নেই। কারণ মানুষের সংস্কৃতির উৎস এবং মানুষ স্বয়ং হল সেই দীর্ঘ উন্নতির সরলরেখার ফসল। যেখানে প্রতিটি বংশাবলী এ বিরাট সৌধ গড়ে তোলার জন্য একটার পর একটা পাথর সাজিয়ে গেছে। বিপ্লবের লক্ষ্য বা মূল উদ্দেশ্য বাড়িটাকে ভেঙে ফেলার নয়; যেসব জিনিস খাপ খাচ্ছে না, অথবা যোগ্য নয়, সেগুলোকে সরিয়ে তার জায়গায় নতুন করে ভিত দিয়ে তারপর সৌধটার নির্মাণ কার্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
এগুলোকেই একমাত্র মানবজাতির উন্নতি বলা চলে, নইলে পৃথিবীটাকে গোলমালের হাত থেকে কিছুতেই মুক্ত করা সম্ভব নয়; কারণ প্রতিটি বংশাবলী অতীতের কাজকে বাতিল করে দিতে চাইবে, এবং পুরনোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবে, আর এটাকেই এরা নতুন কাজ শুরুর প্রাথমিক কর্ম বলে গণ্য করবে।
যুদ্ধের পূর্বে আমাদের সভ্যতার সবচেয়ে দুঃখজনক দিক হল, এর নিজস্ব কোন সৃষ্টির উৎপাদন ক্ষমতা ছিল না যার দ্বারা সাহিত্য বা সভ্যতার কিছু অগ্রগতি হতে পারে; কিন্তু অতীতের উঁচুদরের কার্যাবলীর স্মৃতি এরা মুছে ফেলতে, কলুষিত করতে এবং ঘৃণা করতে আরম্ভ করে। ব্যাপারটা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়ায় যে মনে হয় এ ক্ষয়িত যুগের মহৎ কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতাই নেই। অতীতকে বর্তমানের দৃষ্টি থেকে এমনভাবে গোপন করে রাখা হয় যে মনে হবে ভবিষ্যতের দেবতার পুরো শয়তানের দ্বারা পরিচালিত। এ কার্যকরণগুলো সবার কাছে পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত নতুন বলে নয়, এগুলো ভুল বলেই। কিন্তু যে পদ্ধতিতে মানবসভ্যতার ভিত্তি তৈরি করা হয়েছে, সেটাই ঠিক নয়। এ খামখেয়ালি শিল্পই বলশেভিক মতবাদের স্রোতটাকে বয়ে আনতে সাহায্য করে। যদি পেরিক্লিন যুগের সৃষ্টির উন্মাদনা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়, তবে বলশেভিক তার কিউবিষ্ট বিকৃত মুখভঙ্গি করে হাসাহাসি করবে।
এ প্রসঙ্গে একশ্রেণীর লোকের সাহসের অভাব; বিশেষ করে শিক্ষাদীক্ষা এবং পদমর্যাদার দরুণ তাদের উচিত ছিল আমাদের সাংস্কৃতিক এ চূড়ান্ত অবমাননার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। তারা প্রতিরোধের থেকে সরে দাঁড়ায় কারণ তারা এটাকে অনিবার্য বলে মেনে নিয়ে তার কাছে মাথা নত করেছিল। সুতরাং তাদের এ পদস্থলন প্রাপ্য, কিন্তু তাদের নিছক ভয়ই তথাকথিত বলশেভিক শিল্পের দেবতাদের রাজ্যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে। কারণ যারাই তাদের শিল্প সৃষ্টিকে মেনে নিত না, সেই দেবতারা তাদেরই প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করত এবং তাদের ভাষায় এসব মনোবৃত্তি হল সংকীর্ণমনা এবং আবদ্ধ জলা। লোকে আরো ভয় পেত এ ভেবে যে এসব প্রতারক জোচ্চরগুলো তাদের নামে বলে বেড়াবে যে তাদের শিল্পজ্ঞান বলতে কিছু নেই। এগুলো যেন এমন একটা ব্যাপার যা সত্যিকারের ভাবোচ্ছাস আর অধঃপতনের বস্তু যা নাকি কতগুলো কুখ্যাত শঠের সৃষ্ট, তা না বুঝতে পারলে সমাজ তাদের ছোট চোখে দেখবে। এসব সাংস্কৃতিক ভক্ত দলের একটা গুণ ছিল যে সহজ উপায়ে এ ভাবোসগুলোকেই অতি উৎকৃষ্ট ধরনের শিল্প বলে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে পারত। অতুলনীয় এবং চরম মাদকতাময় উপায়ে তাদের সমকালীন শিল্পকে তুলে ধরতে নিজস্ব অন্তরের অভিজ্ঞতা বলে। এ পথেই তারা তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনাকে এড়িয়ে যেত অতি অল্প আয়াসে। বলাবাহুল্য, এ অন্তরের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কেউ-ই কোনরকম সন্দেহ প্রকাশ করত না। কিন্তু সন্দেহ করা উচিত ছিল যে পাগলের সৃষ্টির পেছনের তাগিদটা সত্যিকারের কি? মারটি ভন সুইন্ড অথবা বালনের শিল্পই হল অন্তরের অভিজ্ঞতার সার্থক প্রকাশ; কিন্তু এগুলো হল ঈশ্বরের দান, কোন বিদুষকের কাজ নয়।
আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কাপুরুষতার এটা একটা চমৎকার উদাহরণ, যারা নাকি আমাদের মানুষগুলোর সহজাত প্রবৃত্তিকে বিষিয়ে দেওয়াটা কোনরকম প্রতিরোধ ছাড়াই সহজভাবে মেনে নিয়েছে সবরকম নৈতিক দায়িত্ববোধ কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে। এ অবিবেচক অর্থহীন ব্যাপারটাকে লোকের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ তারা যা ভালো বোঝে তাই করতে। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি জনসাধারণের বিচার ক্ষমতা বলতে কিছুই নেই, কারণ শিল্প জিনিসটাকেও বুঝতে অক্ষম। তারা শিল্পের নামে যে কোন ব্যঙ্গ তামাসাকেও মেনে নিয়ে থাকে; অবশ্যই যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত তারা শিল্পের ভাল বা খারাপ বিচার বোধটাকে হারিয়ে ফেলে।
এসব বিচার বিবেচনা করলে দেখা যাবে অপর্যাপ্ত চিহ্ন সেই যুগে বর্তমান যার দ্বারা সহজেই বোঝা সম্ভব যে পচনক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।
আরেকটা বিপদজ্জনক চিহ্ন বিচার বিবেচনা করা উচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের নগর এবং শহরগুলো তাদের সভ্যতা কেন্দ্রিক চরিত্র হারিয়ে ফেলে এবং মাত্র সাময়িক বসবাসকারীর চারিত্রিক রূপ নেয়। আমাদের বড় শহরগুলোতে যেসব শ্রমিকেরা বাস করত, তারা আদৌ সেই শহরগুলোকে মনেপ্রাণে ভালবাসত না। এ অনুভূতির সৃষ্টি হওয়ার পেছনের কারণ হল জায়গাগুলোতে হঠাৎ তারা বসবাস করার সুযোগ পায়, যে কারণে তাদের প্রতি কোন মায়া মমতা সেই বসবাসকারীদের প্রাণে ছিল না। অবশ্য এ অনূভূতির জন্য দায়ী হল সামাজিক কারণগুলো, যে কারণে তারা প্রায়ই বাসস্থান বদল। করতে বাধ্য হত। যে নগরে তারা বাস করত তার প্রতি এ কারণে কোন মমতাই গড়ে ওঠার সুযোগ তারা পেত না। এর আরেকটা কারণ হল আমাদের সাংস্কৃতিক শূন্যগর্ভতা এবং শহর জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা। জার্মানির মুক্তি যুদ্ধের সময়ে আমাদের নগর ও শহরগুলো সংখ্যায় শুধু কম ছিল না, আকারেও ছিল খুবই সীমিত। কয়েকটা যাদের সত্যিকারের বড় শহর বলা চলত সেগুলো ছিল তৎকালীন রাজাদের আবাসস্থল, প্রাসাদ নগরী। সেই কারণে সেখানকার সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার একটা আলাদা মূল্য ও মর্যাদা ছিল। হাজার পঞ্চাশেক অধিবাসী অধুষ্যিত সেই শহরগুলো যা প্রায় তখনকার যে কোন বড় শহরের তুল্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির কোষাগারস্বরূপ। তৎকালে যখন মিউনিকে হাজার। ষাটেক বাসিন্দা বাস করত, তখনই মিউনিক জার্মান শিল্পের একটা প্রধানকেন্দ্র বলে বিবেচিত হত। বর্তমানে অবশ্য যে কোন শিল্পাঞ্চলেই তার চেয়ে বেশি লোক বসবাস করলেও তাদের নিয়ে কোন মূল্যবোধ নেই। এগুলো হল কতগুলো বস্তী ও গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়ানো ব্যারাকের সমষ্টি, আর কিছুই নয়। সুতরাং এ অর্থহীন বাসস্থানগুলোর প্রতি যদি কারোর মমতা না গড়ে ওঠে, তবে কারোর পক্ষেই বেড়ে ওঠা সম্ভব নয়। যার নিজস্ব চরিত্র বলতে কিছু নেই এবং যেখানে সাংস্কৃতির কোন ছায়া দুঃখ কষ্টের প্রাচীর ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না।
এটাই সব নয়। বড় বড় শহরগুলোর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকারের শিল্পকর্মের সৃষ্টির ফলে স্থানটা মরুভূমি হয়ে দাঁড়ায়। এদের আবহাওয়ায় সেই শিল্প ভারাক্রান্ত শহরগুলোর প্রতিচ্ছায়া স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। আমাদের বড় শহর গুলোতে সভ্যতার দান বলতে কিছুই নেই। শহরগুলো শুধু অতীতের গৌরব আর ঐশ্বর্যের জোরে। বেঁচে আছে। আমরা যদি শহর মিউনিক থেকে দ্বিতীয় লুইড়ভিগের সমস্ত কিছু তুলে। নেই, তবে দেখতে পাওয়া যাবে এ প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম ছাড়া শহর মিউনিক কত কৃশ হয়ে পড়েছে। বার্লিন বা অন্যান্য বড় বড় শহরগুলো সম্পর্কেও এ একই কথা প্রযোজ্য।
কিন্তু নিচের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা একান্ত প্রয়োজন : আমাদের বড় বড় শহরগুলোর এমন কোন স্মৃতি নেই যা নাকি শহরের সাধারণ বিষয়গুলোর ওপরে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে এবং যা এ যুগের চিহ্নস্বরূপ উপস্থাপনা করা যায়। যদিও সুপ্রাচীন শহরগুলোর প্রত্যেকের গৌরবের স্মৃতিসৌধ ছিল। ব্যক্তিগত সৌধমালা কোন সুপ্রাচীন শহরের শিল্পকর্মের প্রদর্শনী নয়। জনসাধারণের জন্য তৈরি স্মৃতিসৌধই চিরস্থায়ী শিল্পের নিদর্শন, যার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী নয়। কারণ এগুলো মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সম্পদ প্রদর্শন করে না, এ স্মৃতিসৌধগুলো হল সমাজের গুরুত্ব এবং সংস্কৃতির চিহ্ন। এ স্মৃতিসৌধগুলো বসবাসকারীদের নিজেদের শহরের প্রতি অনুপ্রাণিত করবে, যা নাকি আজ আমাদের ধারণার অতীত। মাঝামাঝি গোছের ব্যক্তিগত মালিকানায় কতগুলো। বাড়ি নাগরিকদের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয় না, কিন্তু সমাজের সবার জন্য গড়া স্মৃতিসৌধ প্রতিটি নাগরিকের মন ভরাতে পারে।
আমরা যদি সুপ্রাচীন গণসৌধগুলোর সঙ্গে সেই যুগের ব্যক্তিগত বাড়িগুলোর তুলনা করি, তাদের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারব যে এ কাজগুলোর ব্যাপারে কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, যার প্রতিচ্ছবি সামাজিক জীবনেও গভীরভাবে পড়েছিল। এগুলো হল পরবর্তী যুগের অগ্রগামিতা।
শুধু বাণিজ্যিক প্রসাদগুলো নয়, মন্দির এবং সাধারণের জন্য নির্মিত অট্টালিকাগুলোও রাষ্ট্রের ছিল, যা সত্যি বিস্ময়কর। সমাজই এ সব বিশাল অট্টালিকার মালিক ছিল। এমন কি রোমের গৌরবের অস্ত-সূর্যের দিনেও ব্যক্তিগত ভিলা বা প্রাসাদে শহরের বিখ্যাত জায়গাগুলো পরিকীর্ণ ছিল না; ছিল মন্দির, স্নানাগার বা হামাম, পয়ঃপ্রণালী এবং রাজপ্রাসাদ। এগুলো সবই ছিল রাষ্ট্রের সম্পত্তি, সুতরাং এককথায় জনসাধারণের তার ওপর পূর্ণ অধিকার ছিল।
মধ্যযুগীয় জার্মানিতেও একই আদর্শকে মেনে চলা হত। যদিও শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ ছিল আলাদা। প্রাচীনকালে যে চিন্তাধারা এথেন্স শহরের দূর্গে অথবা প্যানথনে রূপ পেত, আজ তা রূপান্তরিত হয়েছে গথিক ক্যাথিড্রালে। মধ্যযুগীয় শহরগুলোর এ স্মৃতিসৌধগুলো ব্যক্তিগত মালিকানায় নির্মিত ছোট ছোট বাড়িগুলোর মাথা ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে ঢুড়ো আন্দোলিত করত। তাদের প্রাচীর, কাজ এবং ইট তৈরিও ছিল দ্রষ্টব্য। এবং এসব শহরে আজও তারাই প্রধান ভূমিকায় বিরাজ করছে, যদিও দিনে দিনে তারা ফ্ল্যাটবস্তীর জঙ্গলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। কারণ, তারাই স্থানীয় চরিত্র ও সৌন্দর্য লোকের সামনে উপস্থাপনা করে থাকে। গীর্জা, টাউন হল, আত্মরক্ষামূলক স্তম্ভ প্রভূতিই হল চিন্তাধারার বাইরের প্রকাশ যার তুলনা একমাত্র প্রাচীনকালেই পাওয়া সম্ভব।
আজকের জনতার জন্য নির্মিত বাড়িগুলোর আকার এবং উপাদানের অবস্থা সত্যই শোচনীয়, বিশেষ করে ব্যক্তিগত অট্টালিকাগুলোর তুলনায়।
রোমের মত বার্লিনের ভাগ্যেও যদি একই রূপান্তর হয়, তবে ভবিষ্যত বংশাবলী ইহুদীদের বহুতল দোকান, যৌথভাবে গড়া হোটেলগুলোকেই আমাদের সময়কার সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ বলে ধরে নেব। একমাত্র বার্লিনেই দেখা যাবে তুলনামূলকভাবে বাণিজ্যিক কারণে গড়া বাড়িগুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তৈরি বাড়িগুলোর কী প্রচণ্ড তফাৎ।
জনতার জন্য তৈরি অধিকাংশ বাড়ি শুধু অপ্রতুলই নয়, হাস্যকরও বটে। এ সব বাড়িগুলো তৈরির সময়ে এদের স্থায়ীত্বের দিকে নজর দেওয়া হয়নি, সাময়িক প্রয়োজনে নির্মিত হয়েছিল এগুলো। কোন সৎ চিন্তা ভাবনাকেই বাড়িগুলো তৈরির সময়ে ঠাঁই দেওয়া হয়নি। বার্লিনের দুর্গ যখন গড়া হয়েছিল, তৎকালীন চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে আলাদা ছিল, যখন বার্লিন লাইব্রেরি তৈরি হয়েছিল সেই সময়ের সঙ্গে। একটা যুদ্ধ জাহাজ তৈরির ব্যাপারে যেখানে খরচা পড়ে ষাট লক্ষ জার্মান মার্ক, সেখানে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তৈরি একটা বাড়ির জন্য তার অর্ধেকও খরচ করা হয় না। কিন্তু সত্যি বলতে কি, যার স্থায়ীত্ব এবং অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ আরো অনেক ভালভাবে হওয়া প্রয়োজন। তবু ভেতরটা সাজনোর ব্যাপারে আপার হাউস পাথরের ব্যবহারের পরিবর্তে দেওয়ালগুলো শুধু চুনকাম কার পক্ষে রায় দেয়। অবশ্য একথা বলতে দ্বিধা নেই, যে এ বিষয়ে সংসদের মতামতই সঠিক; কারণ চুনকাম করা মাথাগুলো পাথরের দেওয়ালের সৌন্দর্য বুঝতে সত্যই অক্ষম।
আমাদের সমকালীন শহরগুলোই এমন ধাঁচে গড়ে উঠেছে যে তা সামাজিক চরিত্রের প্রকাশ কোনমতেই করে না। সুতরাং সমাজ যে স্থাপত্যকলার মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে না, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। এভাবে বাস্তবিক আমরা এমন একটা জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হব, যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা বাসিন্দাদের সঙ্গে তার দেশের প্রচণ্ড রকমের গরমিল থেকে যাবে।
এসব হল আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের অবক্ষয় এবং সামাজিক অনুশাসনগুলো ভেঙে পড়ার চিহ্ন। আমাদের দিগন্ত সম্পূর্ণভাবে ছোট ছোট স্বার্থ দ্বারা ঢাকা। সত্যি কথা বলতে কি সেগুলোর কোন উদ্দেশ্যই নেই, একমাত্র টাকা রোজগার করা ছাড়া। সুতরাং এসব ঠাকুরের ভজনা করতে গিয়ে আশ্চর্যের কি আছে যে আমাদের নায়কোচিত গুণগুলো অদৃশ্য হয়ে যাবে। অতীতে যে বীজ বপন করা হয়েছিল বর্তমানে আমরা শুধু তার ফসল কেটে চলেছি।
পূর্ববর্তী যেসব ঘটনাবলী দ্বিতীয় সম্রাটের রাজত্ব ভেঙে পড়ার জন্য দায়ী, সেইগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে নির্দিষ্ট এবং সার্বজনীন মতবাদের অভাবেই এ সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর সামাজিক অবসাদ এবং অস্থিরতা তো ছিলই। বিশেষ করে এ অনিশ্চয়তা প্রচণ্ডভাবে দেখা দেয় যখন একের পর এক জীবন জিজ্ঞাসাগুলোর শুরু হয়, এবং তার প্রতি চূড়ান্ত মনোভাব দেখা যায় এদের। এ খামতির আরো একটা কারণ হল সবকাজ অর্ধেকভাবে করা। শুরু হয় শিক্ষা পদ্ধতিতে, তারপর যে কোন দায়িত্ববোধর প্রতি অনীহা, কাপুরুষের মত শয়তানকে সহ্য করা; এমন কি শেষমেষ ধ্বংসকে পর্যন্ত নীরবে মেনে নেওয়া।
কাল্পনিক মানবতাবাদ একটা স্টাইলে এসে দাঁড়ায়। এ বিপথগামীতার প্রতি আত্মসমর্পণ ও ব্যক্তির প্রতি যুদ্ধং দেহি মনোভাবের কাছে আগামী ভবিষ্যতের লক্ষ লক্ষ মানবতাবোধ উৎসর্গ করা হয়েছে।
প্রাক যুদ্ধের ধর্মীয় অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা যাবে সাধারণভাবে বিভক্তিকরণ এ পরিবেশটাকেও বিষিয়ে দিয়েছিল। জাতির একটা বিরাট অংশ জাতীয় পোশাক সম্পর্কে উদাসীন এবং সত্যিকারের আদর্শের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এ ব্যাপারে প্রাথমিক প্রয়োজনীয় এটা নয় যে বহু সংখ্যক লোক, তার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী হল লোকদের উদাসীনতা। যখন খৃষ্টধর্মের দুই সম্প্রদায় এশিয়া আর আফ্রিকার বুকে তাদের ধর্মপ্রচার করে চলেছে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী শিষ্য জোগাড় করা, কিন্তু এ দুই সম্প্রদায়ই তখন ইউরোপে লক্ষ লক্ষ অনুগামীদের বিশ্বাস হারাচ্ছে। এসব শিষ্যরা তখন তাদের জীবনশক্তির উৎসম্বরূপ যে ধর্ম, তাকে পরিত্যাগ করে চলেছে, অথবা তারা নিজের অভিমত অনুসারে সেই ধর্মকে পরিবর্তন করে চলেছে। বিশেষ করে এর ফলাফল দেশের নৈতিক জীবনে সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়েছে। কারণ কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্য না থাকায় খৃষ্টীয় বিশ্বাসের চেয়ে মুসলমান ধর্ম অনেক বেশি পরিমাণে এশিয়া আফ্রিকায় ব্যাপ্তি পেয়েছে।
এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে তথ্য নির্ভর নয় বলে এসব মতবাদ খৃষ্টীয় ধর্মের প্রতি মানুষকে আকর্ষণ করার পরিবর্তে হিংসাকেই প্রশ্রয় দিয়েছে। যদিও মানুষের এ পৃথিবী ধর্ম বিশ্বাস ছাড়া যে কী বস্তুতে পরিণত হতে পারে তা আমাদের ধারণার অতীত। কোন জাতিরই বিরাট অংশ দার্শনিক নয়। জাতির বিরাট একটা অংশের বিশ্বাস জীবনের প্রতি ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। রকমারী ব্যবস্থা যা নাকি আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের পরিবর্তে তুলে ধরা হয়েছে, তার কোন মূল্য নেই। কিন্তু যদি ধর্মীয় অনুশাসন এবং বিশ্বাস জাতির গরিষ্ঠ অংশ মেনে নেয়, তবে সে মতবাদের ভিতস্থাপনা হয় শক্ত জমিতে। জীবন ধাণের প্রাত্যহিক নিয়মগুলোকে না মেনেও হয়ত কয়েক শো বা হাজার অতি মানব আছেন, যারা তাদের জীবনটাকে কাটিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু বাকি লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে তা সম্ভবপর নয়। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা যে বাঁধাধরা খাতে বয়ে চলে, রাষ্ট্রের পথও সেই একই খাতে প্রবাহিত। আরো স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে, ধর্মীয় অনুশাসনগুলোও সেই কারণে প্রয়োজনীয়। সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় মতবাদ হল এমন একটা বস্তু, যার বিশদ ব্যাখ্যার শেষ নেই। একমাত্র মতবাদের মধ্যে আবদ্ধ নেই সেই কারণে এটা সূক্ষ্ম এবং শক্ত একটা রূপ দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া কোনরকম বিশ্বাসই গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। নইলে ধর্মীয় মতবাদ কোনক্রমেই দার্শনিক মতবাদের উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হত না। বরং সোজাসুজি একটা দার্শনিক মতবাদে গিয়ে ঠেকত। সেই কারণে এ মতবাদের ওপর আক্রমণ করা আর রাষ্ট্রের কোন অনুশাসনের প্রতি আক্রমণ একই কথা। তাই এ ধরনের কোন আক্রমণ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ডেকে আনতে বাধ্য।
রাজনৈতিক নেতাদের ধর্মের মূল্যায়ণ কখনোই এর কোন খামতির দিক বিবেচনা করে করা উচিত নয়। তার বদলে তার চিন্তা করা উচিত এর পরিবর্তে অন্য কিছু যা সত্যিকারের ভাল তার পক্ষে জনমত গঠন করা সম্ভব কিনা যতক্ষণ না পর্যন্ত ভাল, এবং গ্রহণযোগ্য কোন ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায়, ততদিন পর্যন্ত একমাত্র বোকা এবং দাগী আগামীরাই প্রচলিত ধর্মের অবলুপ্তি চাইবে।
অবশ্য এটা নিঃসন্দেহে সত্য যারা এ প্রচলিত ধর্মের গতি ব্যাহত করেছে, জাগতিক কিছু প্রাপ্তির জন্য তাদের ক্ষমা করাটা মোটেই উচিত হবে না। কারণ বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সংঘর্ষ তারাই ডেকে এনেছে। এ সংঘর্ষে বিজয়মাল্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের গলাতেই ঝুলবে। যদিও তা হবে তিক্ত সংঘর্ষের পরে, যাতে ধর্মের ক্ষতি প্রচণ্ডই হবে। কারণ কাছেই ধর্মের উচ্চতা খর্ব হবে যাদের দৃষ্টি বিজ্ঞানের ওপরের স্তর ভেদ করতে অক্ষম।
কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে ধর্মে খাদ মিশিয়ে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে সেটাকে ব্যবহার করে। বরং সোজাসুজিভাবে বলতে হয় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই ধর্মটাকে ব্যবহার করা হয়েছে। নিলজ্জ উঁচু গলায় চিৎকার করা মিথ্যুক মানুষগুলো যারা খনখনে গলায় তাদের একরাশ মিথ্যা প্রচার করে চলেছে, যা কাপুরুষ উদ্দেশ্যবিহীন লোকগুলোই শোনে। এরা কিন্তু কোন কারণেই মৃত্যুর জন্য তৈরি নয়। বরং কি করে ভালভাবে বাঁচা যায়, তার ফন্দি-ফিকির খুঁজতেই তারা সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকে। রাজনৈতিক লাভের জন্য তারা তাদের যে কোন বিশ্বাসকে বিকিয়ে দিতে পারে। মাত্র দশটা সংসদীয় আদেশের জন্য মার্কসবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাতে এতটুকু ইতস্তত করে না। যারা হল ধর্মের শত্রু, আর একটা মন্ত্রীত্বের জন্য তারা শয়তানের সঙ্গেও বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে প্রস্তুত। যদিও সেই শয়তানের চক্ষুলজ্জা বলতে কোন বস্তু নেই।
প্রাক্ যুদ্ধের জার্মানিতে খৃষ্টধর্মের আস্বাদন বহু লোকের কাছে বিস্বাদ ঠেকে। তবে তার জন্য দায়ী রাজনৈতিক দলগুলো, যারা ক্যাথলিক বিশ্বাসকে লজ্জাস্করভাবে নিজেদের দলীয় স্বার্থে কাজে লাগিয়েছিল।
এ পরিবর্তিত ব্যবস্থাটাই ছিল মারাত্মক। এটা গোটা কয়েক মূল্যহীন সংসদীয় আদেশ পাটির জন্য জোগাড় করতে সমর্থ হয়েছিল; কিন্তু তার জন্য চার্চের ক্ষতি হয়েছিল প্রচণ্ড রকমের।
এ ঘটনার ফলাফল জাতিকেই বহন করতে হয়েছিল। ধর্মীয় জীবনে অবসাদ নেমে এসেছিল, যার ফলে সমস্ত রকম বিশ্বাসের নৈতিকতার প্রচলিত আচার আচরণের ভীত নড়ে উঠেছিল-যা যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।
তবু এসব চিড় খাওয়া ফাটল ধরা সামাজিক সংগঠনগুলো হয়ত খুব একটা ক্ষতিকারক ছিল না, যদি তার ওপর দুঃখের বোঝা আর না চাপানো হত। কিন্তু জাতির কাধে এ ঝড় এমন এক সময় এসে উপস্থিত হয়েছিল যখন অন্তর্দেশীয় একতার প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি।
রাজনীতির ক্ষেত্রেও পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল জার্মান রাষ্ট্রের কাঠামোর কয়েকটি ব্যতিক্রম যা নাকি আগামী ধ্বংসটাকে দেখিয়ে দিয়েছিল, যদি সময় মত সেগুলোকে শুদ্ধিকরণ করা না হয়। জার্মান নীতির অন্ধত্ব বৈদেশিক এবং অন্তর্দেশীয় প্রায় সবার চোখে ধরা পড়েছিল। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল বাইরে থেকে ছন্দোবদ্ধ মনে হলেও এ ব্যাপারে বিসমার্কের মতামতটাই সত্য, যে রাজনীতি হল সাম্ভব্যতার শিল্প। কিন্তু পরের চ্যান্সেলারদের থেকে বিসমার্কের চিন্তাধারা কিছুটা আলাদা ধরনের ছিল। আর এ পার্থক্য থাকার দরুন বিসমার্কের পক্ষে এ তত্ত্বের নির্যাস তার রাজনীতিতে অভীষ্ট পূরণের জন্য সবরকম রাস্তা দেখা উচিত; অন্তত চেষ্টা করা উচিত। চেষ্টার প্রয়াস থাকার দরকার। কিন্তু তারা পরবর্তী উত্তরাধিকারীগণ এ কথার একটা অর্থই করেছিল যে রাজনীতিতে কোনরকম আদর্শ বা লক্ষ্যের প্রয়োজন একেবারেই নেই। সবচেয়ে বড় কথা তল্কালীন জার্মান রাজনৈতিক নেতাদের কোন দূরদর্শী নীতি ছিল না; কারণ হল পুরো ব্যাপারটাই নড়বড়ে ভিতের ওপরে দাঁড়ানো; বিশেষ করে আন্তর্জাতিকতাবাদের। শুধু তাই নয়, এসব নেতাদের রাজনীতির বিবর্তন সম্পর্কে কোন ধ্যান-ধারণাই ছিল না, যেটা রাজনৈতিক নেতাদের অবশ্যই থাকা উচিত।
তৎকালীন অনেকেই যারা পুরো ব্যাপারটাকে হতাশার দৃষ্টিতে দেখত, তারা দোষারোপ করত যে আদর্শ এবং দিগদর্শনের অভাবেই জার্মান রাষ্ট্রের এ দুরবস্থা। তারা এজন্য দায়ী করত ভেতরের দুর্বলতা এবং আদর্শের অনুর্বরতাকে। যাদের দ্বারা সরকার পরিচালিত, তাদের ধ্যান-ধারণার চিন্তানায়ক হুসটন স্টুয়ার্ট চেম্বারলিন, আজকের যারা প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা তাদের থেকে আলাদা ছিল। আসলে এ লোকগুলো তাদের সময়কালের উন্নতির জন্য চিন্তা করতে অন্যের উপদেশ নিতেও তাদের অহংকারে বাজত। গুস্তোভাস্ অ্যাডফুসের মৃত্যুর পর সুইডিস্ চ্যান্সেলার অস্পেনস্ট্যারিন কিছু সত্যের সন্ধান দিয়েছিল যা নাকি স্মরণাতীত কাল পর্যন্ত সত্য ছিল। সে বলেছিল এ পৃথিবীর শাসন একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই করা সম্ভব। সুতরাং আশা করা যায় সংসদীয় সদস্যদের ভেতরে এর একটা অণু হলেও থাকা উচিত ছিল। কিন্তু জার্মানিতে গণতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার পরে এক যৎকিঞ্চিত দেখা পাওয়া যায়নি। তার জন্যই তাদের গণতন্ত্রের রক্ষার আইন পাশ করতে হয়েছে, যার দ্বারা স্বাধীন কোন মতবাদ ব্যক্ত করাই নিষিদ্ধ। অস্পেনস্ট্যারিনের পক্ষে এটা সৌভাগ্য বলতে হবে যে সে তক্কালে জীবন ধারণ করেছিল, এ গণতন্ত্রের কালে নয়।
ইতিমধ্যেই যুদ্ধের আগে এ প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত ছিল,-সংসদ, জার্মান রাষ্ট্রসভা কিন্তু রাষ্ট্রের পর্যায়ে সবচেয়ে দুর্বলতম স্থান বলে ইতিমধ্যেই পরিচিতি লাভ করেছিল।
সবচেয়ে নোংরা একটা কথা যা এখন শোনা যায় যে বিপ্লবের সময় থেকে জার্মান সংসদীয় গণতন্ত্র আর কার্যকরী নয়। এ কথায় এ ধারণাই সবার হবে যে বিপ্লবের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল। কিন্তু বাস্তবে সত্য হল দেশকে টেনে নিচে নামানো ছাড়া অন্য কাজ এ তথাকথিত সংসদীয় প্রতিষ্ঠানের ছিল না। জার্মানির পতনের জন্য এ প্রতিষ্ঠানও কম দায়ী নয়।
এ বিশাল বিধ্বংসকারী শয়তানের দল যারা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সংসদে ভিড় করেছিল, এরা হল এ সংসদের একটা টিপিক্যাল উদাহরণ, যাদের কোন যুগেই দায়িত্ববোধ বলে কিছু থাকে না। যে শয়তানের কথা আমি বলছি, তা অন্তর্দেশীয় শাসনভার ঢিলেঢালা এবং বৈদেশিক নীতিতেও দৃঢ়তা ছিল না; এগুলোই হল রাজনৈতিক বিপর্যয়ের প্রধান কারণ।
সংসদীয় সমস্ত কাজই অর্ধেক করা হয়েছে এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এ কাজ সম্পূর্ণ না করার নীতি সব ব্যাপারেই মেনে চলা হয়েছে।
মৈত্রীর ব্যাপারে জার্মান রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি একেবারেই নিকৃষ্টতম। তাদের ইচ্ছে ছিল শান্তি স্থাপনের, কিন্তু সোজা গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে যুদ্ধে।
পোল্যান্ডের ব্যাপারেও এ বৈদেশিক নীতি মনপ্রাণ দিয়ে লাগানো হয়নি। যার ফলে
পেরেছে জার্মানি যুদ্ধে জিততে অথবা পোল্যান্ডকে টেনে নিজের স্বপক্ষে আনতে, বরং রাশিয়াকে শত্রু বানিয়ে ছেড়েছে।
অ্যালসেস-লোরাইনের প্রশ্নটাকে সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছিল মাত্র, কিন্তু পুরোপুরি মন ঢেলে দেওয়া হয়নি। ফরাসী বহু মস্তক বিশিষ্ট জলচর সাপটার মাথা চূর্ণ করার পরিবর্তে শুধু আস্তে একটু ছোঁয়া এবং অ্যালসেস-লোরাইনের তত্ত্ব অনুসারে অন্যান্য জার্মান প্রদেশের সঙ্গে সমান অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তারা এক নয় একের সঙ্গে আরেক জনের তুলনা করা চলে না। যাহোক এছাড়া তাদের অন্য কোন গতিও ছিল না, কারণ দেশের মধ্যে তারাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক; বিশেষ করে মিষ্টার ভিটারলে তো কেন্দ্রের মধ্যমণি।
তবু দেশ এ সব পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারত, যদি না, তাদের সেই প্রতিরোধ করার শক্তিটাকে দোদুল্যমান নিয়তির দ্বারা হত্যা না করা হত। আর এটাই ছিল শেষ পন্থা; সম্রাটের অস্তিত্ব নির্ভর করে তার সৈন্যবলের ওপর।
তৎকালীন জার্মান রাষ্ট্র জাতির প্রতি যে অপরাধ করেছে তাকে নিচে নামিয়ে নিয়ে এসে তার জন্য সারাজীবন জাতির অভিশাপ তাদের প্রাপ্য। এ সংসদীয় দলের সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল এদের রাজনৈতিক সমর্থক দ্বারা এরা জাতির আত্মরক্ষার সবচেয়ে বড় অস্ত্রটাকে অপহরণ করে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। যার জন্য জাতির অস্তিত্ব, স্বাধীনতা সবকিছুই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আজ যদি কবর খোঁড়া হয়, তবে রক্তস্নাত সেইসব ফরিয়াদীরা বেরিয়ে পড়বে, হাজার হাজার জার্মান যুবকের ভবিষ্যতের জন্য দায়ী এ সব রাজনৈতিক ডাকাতগুলো অথবা স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে তাদের ভুল শিক্ষা আর কুশিক্ষাই দায়ী। এ লক্ষ লক্ষ লোকের নিধন বা অঙ্গ ছেদন করা হয়েছিল মাত্র কয়েকশ লোকের রাজনৈতিক কৌশলে ও জোর করে তাদের উপর রাজদ্রোহাত্মক মতবাদ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য।
মার্কসবাদী এবং গণতান্ত্রিক সংবাদপত্রগুলো দ্বারা ইহুদীরা সারা পৃথিবীতে জার্মান সামরিক বাহিনী সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করে। কিন্তু আমাদের জাতীয় বাহিনীর শিক্ষা ব্যবস্থা যে অপ্রতুল, তার কোন ব্যবস্থাই মার্কসবাদী বা গণতান্ত্রিক দলগুলো করেনি। এ ভয়াবহ অপরাধের জন্য যুদ্ধের সময়ে প্রত্যেকের ডাক পড়ে, কারণ এ লোকগুলোর ফেরিওয়ালা মনোবৃত্তির জন্য লক্ষ লক্ষ জার্মানকে তার জন্য অনেক নিম্নমানের অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্ধেক সময়ে-ডিক্ষা নিয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সামরিক শিক্ষায় পারদর্শী শক্রর মুখোমুখি হতে হয়। নির্দয় নিষ্ঠুর রকমের বিবেক-বুদ্ধির অভাবও এ সংসদীয় বদমায়েসদের কম ছিল না। এবং এটা পরিষ্কার যে সুশিক্ষিত সৈন্যের অভাবই এ যুদ্ধে পরাজয়ের অন্যতম কারণ। এবং মহাযুদ্ধের কালে এ সত্যই অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকাশ পায়।
সুতরাং জার্মান জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষমতাটাই হারিয়ে ফেলে, কারণ আর কিছুই নয় সংঘের শান্তিবাদী নীতি এবং জাতির আত্মরক্ষার নীতির শিক্ষার অভাব।
পদাতিক সৈন্যবাহিনীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈনিক খুব কম পরিমাণেই সগ্রহ করা হয়েছিল এবং সেই নৌ-বাহিনীর অবস্থাও ছিল তথৈবচ। সুতরাং জাতির আত্মরক্ষার অস্ত্রটাকে এভাবে ভোতা করে দেওয়া হয়েছিল। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক যে নৌ-বাহিনীর পদস্থ অফিসাররাও এর জন্য দায়ী। বৃটিশদের থেকে ছোট যুদ্ধ-জাহাজ জলে ভাসাবার মনোবৃত্তি দূরদৃষ্টির পরিচয় নয়। এক সারি জাহাজ বলেই তা কখনো একক জাহাজের যুদ্ধ শক্তির সমতুল্য হতে পারে না। যুদ্ধ করার ক্ষমতাটাই যুদ্ধ করার সময়ে একমাত্র বিবেচ্য। সত্যি বলতে কি, আধুনিক সমর-বিজ্ঞান এত বেশি উচ্চস্তরে পৌঁছেছে যে একই মাপের যুদ্ধ-জাহাজের যুদ্ধ করার ক্ষমতা অন্য দেশের তৈরি সেই মাপের যুদ্ধ-জাহাজের থেকে অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে; অন্য দেশের বড় যুদ্ধ জাহাজের তুলনায়।
সত্যি কথা বলতে, কি গতি এবং সমর-সজ্জার পরিবর্তে একমাত্র জার্মান নৌ-বহরের ক্ষুদ্র একটা অংশকেই প্রতিপালন করা যেতে পারে। এ নীতির সার্থকতা সম্পর্কে যেসব যুক্তি উপস্থাপনা করা হয়েছে তাতেই প্রমাণিত হয় যে শান্তির সময়ে নৌ বাহিনীর অফিসারদের চিন্তাধারা কতখানি আসার ছিল। তারা ঘোষণা করেছিল জার্মান কামানগুলো বৃটিশ ৩০.৫ সেন্টিমিটার কামানের চেয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত করার ব্যাপারে অনেক বেশি কুশলী।
এবং এ যুক্তির জোরেই তারা ৩০.৫ সেন্টিমিটার কামান তৈরি করতে শুরু করে। কিন্তু ওদের উচিত ছিল সমর-সজ্জায় বৃটিশের সমকক্ষ না হয়ে যুদ্ধের অধিক পারদর্শিতা লাভের প্রচেষ্টা করা। যদি এটা সত্যি না হয় তবে বৃথাই তারা পদাতিক বাহিনীকে ৪২ সেন্টিমিটার মটারে সাজিয়েছিল। কারণ জার্মান ২১ সেন্টিমিটার মটারগুলো ফরাসী মটারের থেকে অনেক উন্নতমানের ছিল এবং দুর্গগুলোকে ৩০.৫ সেন্টিমিটার কামানের গোলা দ্বারাই অধিকার করা যেত। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর কর্তৃপক্ষের স্থানীয় ব্যক্তিরা এ বিষয়ে কৃতকার্যতা লাভ করতে পারেনি। পদাতিক বাহিনীর অস্ত্রসজ্জায় উন্নত না করার প্রচেষ্টা আর কিছু নয়, মিথ্যা দায়িত্বের ভয়। নৌ-বহর তো শান্তির সময় থেকেই আক্রমণ বিমুখ মনোবৃত্তি নিয়ে বসে ছিল, যার জন্য যুদ্ধের শুরুর থেকেই তারা আত্মরক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু এ পথে তারা জয়ের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়, কারণ একমাত্র এগিয়ে যাবার নীতিতেই জয়লাভ করা সম্ভব।
নিম্নগতি সম্পন্ন এবং দুর্বল সমরসজ্জা বিশিষ্ট যে কোন যুদ্ধ-জাহাজ তার থেকে দ্রুতগতি সম্পন্ন এবং সমরসজ্জায় সজ্জিত জাহাজের কাছে পঙ্গু এবং আঘাত খেতে বাধ্য, কারণ তাদের পক্ষে দুর্বল জাহাজে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের বাইরের থেকে আঘাত করা সম্ভব। এক বৃহৎ সংখ্যার ক্রুজারকে এ অভিজ্ঞতার পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। নৌ বহরের অফিসারদের ধারণা যে কত ভুলে ভর্তি ছিল যুদ্ধের সময়ে তা ভালভাবেই প্রমাণিত হয়। তারা বাধ্য হয়ে পুরনো জাহাজগুলোর সমর ব্যবস্থার বদলি করে এবং সুযোগ মত নতুন জাহাজের সমর ব্যবস্থাও উন্নত করতে বাধ্য হয়। যদি জার্মান নৌ বহরের যুদ্ধ-জাহাজগুলো এবং কামানের শক্তি বৃটিশ বহরের যুদ্ধ-জাহাজের অনুরূপ হত-তবে কাগরেকের যুদ্ধে ইংরেজ নৌ-বহর জার্মান ৩৮ সেন্টিমিটার শেষে ধ্বংস হয়ে যেত, যদি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সঠিক নিশানায় আঘাত করতে পারত।
জাপান অবশ্য নৌ-যুদ্ধের নীতি অন্যরকমের নিয়েছিল। তারা প্রতিটি যুদ্ধ জাহাজ শক্তিশালী করেছিল যাতে বিরুদ্ধপক্ষের যুদ্ধ-জাহাজগুলো এককভাবে এদের শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারে। এবং এ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই পরে এগুলোকে আত্মরক্ষার কাজেও লাগানো সম্ভব হয়।
এটা সত্যই অদ্ভূত যে পুরনো জার্মানির দোস ত্রুটিগুলোকেই জনসমক্ষে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যাতে তার অন্তর্নিহিত ঐক্যে চিড় খায়। এমনকি অপ্রিয় সত্য বাক্যগুলো সরবে বারবার বিশাল জনতার কানে তুলে দেয়া হয়েছে; কিন্তু অন্যান্য বহু জিনিস চাপা দিয়ে দেওয়া হয়েছে বা ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। বিশেষ করে সেই খোলাখুলি বিতর্ক যখন জাতির উন্নতিকে টেনে আনার সম্ভাবনায় রয়েছে। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ এ ব্যাপারে হয় কিছুই অবহিত ছিল না। বা সামান্যই খবর রাখত। একমাত্র ইহুদীরাই জানত প্রচারের সেই আর্ট যার দ্বারা স্বৰ্গকেও নরক বলে তুলে ধরা যায় অথবা তার উল্টোটা। সবচেয়ে দুঃখজনক ক্লেশময় জীবনকেও স্বর্গীয় বলে মনে হত এদের প্রচারের ধরন-ধারণে। ইহুদীরা অভিনয়ও করত সেই ঢঙে। কিন্তু জার্মান, বিশেষ করে জার্মান সরকার এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করত না। যুদ্ধের সময়ে এ অজ্ঞতার জরিমানা যথেষ্ট পরিমাণেই দিতে হয়েছিল।
অসংখ্য দোষের মধ্যে যা আমি উল্লেখ করেছি, যুদ্ধ পূর্ব জার্মানির ভাগ্যে বহু লাঞ্ছনা ডেকে এনেছে, তার একটা ইতিবাচক দিকও ছিল। যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পুরো ব্যাপারটাকে বিচার করি তবে দেখতে পাব অন্য দেশ এবং জাতির মধ্যেও এ দোষ বর্তমান। আমাদের থেকে তা অনেক গভীরে। উপরন্তু আমাদের যত সুযোগ ছিল, অন্য কারোরই তা ছিল না।
জার্মানির ইতিবাচক দিকটার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল জার্মানির অর্থনৈতিক শক্ত বুনিয়াদ, যা অপর কোন ইউরোপীয় দেশের ছিল না। সেই কারণে অন্য দেশের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করা তার পক্ষে সহজ ছিল। যদিও স্বীকার করতে বাধা নেই যে এর মধ্যে খুঁতও কম ছিল না। তবু এ আধিপত্য বিপদজ্জনকও বটে। এটাই ভবিষ্যত বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
এমন কি আমরা যদিও জাতির স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অগ্রাধিকার দিতে স্বীকারও না করি, তবু রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যাপারে এর ভুমিকা যে অত্যন্ত চমকপ্রদ তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এ বিষয়গুলোই তিনটে প্রতিষ্ঠানকে উপস্থাপন করত। যারা নিয়মিত পুনঃঅভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে শক্তি জোগাত।
প্রথমদিকে তো জার্মানির আধুনিকীকরণের ব্যাপারে রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করেছে। সুতরাং আমাদের সেইসব রাজাদেরও মেনে নেওয়া উচিত তাদের কাজের গলতির জন্য আজকের গণজীবন এবং সন্তানদের জীবন দুঃখ জর্জরিত হয়ে পড়েছে। আমাদের যদি এসব ব্যাপারে সহনশীলতা না থাকে, তবে বর্তমান যুগের ছেলেরা হতাশ হয়ে পড়বে। সমকালীন কালের প্রতিনিধিদের চরিত্র, ব্যক্তিগত দক্ষতার কথা যদি বিচার করি তবে দেখতে পাব তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং নৈতিক চরিত্রের মানদণ্ড খুব একটা উঁচু ছিল না। আমরা যদি জার্মান বিপ্লবের ব্যক্তিগত মূল্যায়ণ করি, তবে দেখব ১৯১৮ সালের বিদ্রোহ সাধারণ জীবনের কোন উন্নতি সাধনই করেনি। এবং উত্তরকালের বংশধরেরা কী ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে পথ হাঁটবে যখন জার্মান সংরক্ষণ আইনের দ্বারাও তাদের মতামত চাপা দেয়া যাবে না।
আজকের রাজনৈতিক নায়কদের বুদ্ধিমত্তা, নীতিজ্ঞান বিচার করে আগামী বংশধরেরা তাদের সম্পর্কে নিচু ধারণাই পোষণ করত।
এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বেশির ভাগ জনতার কাছে সেই রাজা বিদেশী বলেই পরিগণিত হত। এর কারণ আর কিছুই নয়, রাজাদের বুদ্ধিমত্তা সব সময় সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল না এবং আরো স্পষ্ট ভাষায় বলা যায় চারিত্রিক দৃঢ়তা হয়তবা ছিল না। দুর্ভাগ্যবশত বেশির ভাগ রাজাই তোষামোদপ্রিয় ছিল এবং এসব চাটুকারের দলই তাদের গোপন খবরাখবর দিত।
শতাব্দীর শেষে একজন যুবরাণীকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে সৈন্য পরিদর্শন করতে দেখে জনসাধারণের মধ্যে আর আগেকার মত চাঞ্চল্য জাগত না। তৎকালীন উঁচুতলার বাসিন্দাদের এটাও জানা ছিল না যে এ ধরনের প্যারাড সাধারণ মানুষের ভেতরে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া জাগায়। যদি ধারণা থাকত তবে হয়ত বা এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটত না। ভাবালুতাসম্পন্ন মানবতাবাদ—যার সঙ্গে বেশিরভাগ সময়েই অন্তরের স্পর্শ থাকে, তৎকালে এ ওপর তলার বাসিন্দাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা জনসাধারণকে আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণই করত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ক’ রাজা যদি মুরগীর স্যুপ খেয়ে ভাল বলত, সবারই ভেতরে তার সেই তৃপ্তিটা ছড়িয়ে পড়ত; কিন্তু তা হত আজ থেকে অনেক আগে; আজ তা আর নেই। বরং পুরো ব্যাপারটাই উল্টে হয়ে গেছে। যদি আমরা এটা ধরেও নেই যে রাজা মহারাজাদের এসব ব্যাপারে একেবারেই কোন ধ্যান-ধারণা ছিল না, তবু এটা স্বীকার করেত হবে যে তাদের বোঝা উচিত ছিল দিনকাল বদলে গেছে। এমনকি তাদের সবচেয়ে ভাল উদ্দেশ্যটাও হাস্যকর লাগত অথবা ক্রোধের কারণ হয়ে দাঁড়াত।
সুবিদিত মিতব্যয়িতা যার মধ্যে সেই সব রাজাদের দিন কাটত, তাকে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে গভীর রাত পর্যন্ত একঘেয়ে কঠোর খাটতে হত, বিশেষ করে সদা সর্বদা তার মুকুট হারানোর আশঙ্কায়। সব মিলিয়ে লোকদের পক্ষে পুরো ব্যাপারটাই অমঙ্গল সূচক ছিল। রাজারা কতখানি খায় বা পান করে, এ সব বিষয়ে কারোরই কোন আগ্রহ ছিল না; সে পরিপূর্ণ খেল কিনা বা প্রয়োজনের পরিমাপ মত ঘুমল কিনা, এসব বিষয়ে কারোরই কোন প্রকার মাথাব্যথা ছিল না। রাজা তার ব্যক্তিত্বের জোরে যখন তার পরিবারের সম্মান নিয়ে আসত এবং যে সম্মান দেশেরও বটে; দেশের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে তার কর্তব্য করে যেত। তার সম্পর্কে যত সব গল্প কথা প্রচারিত হত, তা’ তার লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য খুব কম পরিমাণেই করত, বরং ক্ষতি করত অনেক বেশি।
অবশ্য এসব ব্যাপারগুলো একরকম খেলা ছাড়া কিছু নয়। সবচেয়ে খারাপ ছিল সেই সময়কার বিশেষ একটা অনুভূতি যে ব্যক্তিগত সবার স্বার্থ রাজা নিপুণ হাতে দেখছে এবং জনসাধারণের বিরাট একটা অংশ এ চিন্তাতেই নিশ্চিত ছিল। সুতরাং তাদের নিজস্ব স্বার্থের ব্যাপারগুলো নিয়ে তারা মোটেই ভাবিত ছিল না। যতক্ষণ দেশে ভাল সরকার প্রতিষ্ঠিত, অন্ততপক্ষে সৎ চিন্তার দ্বারা সেই সরকার সুপরিচালিত, ততদিন পর্যন্ত তো কোনরকম প্রতিবাদ উঠতে পারে না। কিন্তু যখন পুরনো সরকারের বদলে নতুন সরকার দেশের শাসনভার তুলে নেয়, যার দক্ষতা মোটেই পূর্বের সরকারের মত নয়, তখনই দেশ বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। শান্ত, বাধ্যতা এবং নির্দয়তার শৈশবস্থা যা আগের সরকারের প্রতি কোন প্রতিবাদ তোলেনি, তা সমাজের পক্ষে রীতিমত বিপদজ্জনক হয়ে দাঁড়ায় যা নাকি কল্পনাতেও আনা যায় না।
কিন্তু এসব এবং অন্যান্য দোষ ছাড়াও তাদের নিশ্চয়ই কিছু গুণ ছিল যার প্রভাব ইতিবাচক।
প্রথমত রাজতন্ত্র জনসাধারণের ব্যাপারেও তাদের স্বার্থরক্ষায় স্থির প্রত্যয় সরকার, বিশেষ করে আন্দোলনকারী উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনৈতিক নেতাদের থেকে এসব ব্যাপারে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল অনেক বেশি। উপরন্তু সুপ্রাচীন অভিযানগুলোও এ সব রাজতন্ত্রের মহিমা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করত। তার চেয়েও বড় কথা সৈন্যবাহিনী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দকে রাজনীতির উর্ধে সবসময় রাখা হত। দেশের সর্বোচ্চ শাসনভার রাজার ওপরেই ন্যস্ত থাকত। সত্যি কথা বলতে কি, সুবিদিত সাধুতা এবং জার্মান শাসনকার্যে অখণ্ডতা প্রধানত এ কারণেই বজায় ছিল। শেষমেষ রাজতন্ত্রের কারণে জার্মান জনসাধারণের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক প্রসার লাভ করে, তা’ এর অনেক দোষত্রুটি ঢাকতেই সাহায্য করেছিল। আমাদের সময় পর্যন্ত জার্মান শহর সংস্কৃতি এবং শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল; যা নাকি চরম বস্তুতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। জার্মান যুবরাজরা বারবার বিজ্ঞান এবং শিল্পকলার উৎকর্ষতার জন্য উৎসাহ দিয়ে এসেছে। সমকালীন যুগে এর কোন তুলনা নেই।
ধীরে ধীরে সামাজিক বিপর্যয়ের সময়ে এ সৈন্যদলই সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ করেছিল। জার্মান জনসাধারণের এর চেয়ে ভাল শিক্ষা আর জোটেনি বললেই হয়। এ কারণেই শত্রুদের সব ঘৃণা আমাদের জাতীয় সংরক্ষণ ও স্বাধীনতা নামক মল্লবীরের বিরুদ্ধে বর্ষিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমাদের সবচেয়ে বড় সুশিক্ষা হল এদের পি, ভয় এবং ঘৃণা; আন্তর্জাতিক মুনাফাখোরের দল যারা ভার্সালেসে জড়ো হয়েছিল জাতিকে লুণ্ঠন এবং প্রতারণা করার জন্য, তাদের সমস্ত শক্রতার লক্ষ্য ছিল প্রাচীন জার্মান বাহিনী যারা নাকি ফাটকার হাত থেকে জাতিকে এতদিন বুক দিয়ে রক্ষা করে এসেছে। যদি এ সৈন্যবাহিনী জাতীয় স্বার্থ এত নিপুণ হাতে না দেখত তবে ভার্সাইয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ অনেক আগেই তাদের স্বার্থ কার্যে পরিণত করত। একমাত্র একটা শব্দের দ্বারা এ সৈন্যবাহিনীর কাছে জার্মানদের কি ঋণ প্রকাশ করা হয়, তা হল-সবকিছু।
যখন লোকদের ভেতরে এ গুণের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে, সবাই যে যার দায়িত্ব কাঁধ থেকে ছেড়ে ফেলে দিতে উৎসুক, তখন সামরিক বাহিনী তাদের কর্তব্য স্থির প্রতিজ্ঞভাবে পারলন করে চলেছে। এবং একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে গণতন্ত্রের ঝড়ো আবহাওয়ায় তাদের এ দায়িত্ববোধ সযত্নে পালন করে চলেছে। সামরিক বাহিনী জনসাধারণকে সাহসী হতে শিক্ষা দিয়েছিল যখন ভীরুতায় সমস্ত জনসাধারণ ভুগছে এবং তা মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে। তখন সমাজের মঙ্গলের জন্য কারোর ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগটাকে পাগলামী বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। তখনকার যুগে যখন একমাত্র চালাক ব্যক্তিরাই নিজেদের স্বার্থরক্ষা করত, তখন সামরিক বিভাগই ছিল একমাত্র বিভাগ, যা নাকি জাতির মুক্তির পথ বাতলে দিয়েছে মিথ্যা আদর্শের মায়ায় আকৃষ্ট করে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃভাবে নিগ্রোদের, চাইনিজ, ফ্রেঞ্চ বা ইংরেজদের সঙ্গে জার্মানদের শেখায়নি। তাদের শিক্ষা ছিল নিজেদের জাতিকে একতা ও দৃঢ়তার বন্ধনে বাঁধা।
সামরিক বাহিনী একতা শক্তিকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করতে সাহায্য করেছে, তখনকার সময়ে যখন সন্দেহবাদ দোষে সামগ্রিকভাবে মানুষের চরিত্র দুষ্ট এবং পণ্ডিত-মূর্খের দল নকল ফ্যাসানের আদর্শে নিজেদের আবৃত করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যে কোনরকম আদেশ পালন করা কোন কিছু না করার চেয়ে অনেক ভাল। যদিও এটাকে ভাসা ভাসাভাবে স্থির প্রতিজ্ঞ ও শক্তিশালী একটা আদর্শ বলে মনে হয়, তবু সামরিক বাহিনী যদি নিয়মিত জীবনে যৌবন না জুগিয়ে যেত তবে এ ভিত্তি আদর্শের কোন প্রাণ নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যেত না। এ ব্যাপারে অনেক ভয়াবহ খামতির পরিচয় পাওয়া যায়, যা নাকি আমাদের বর্তমান সরকারের কার্যকলাপে প্রকট। তাদের ভেতরে নতুন কাজকর্মের দরুন কোনরকম উৎসাহের সাড়া বর্তমানে নেই, অবশ্যই তা যদি জার্মান জাতিকে প্রতারণার ব্যাপারে না হয়। এ ব্যাপারে অবশ্য তাদের সমস্ত দায়িত্ববোধ তারা ঝেড়ে ফেলে দেয় এবং দলিলপত্রে স্বাক্ষর দেয় এমন ভঙ্গিতে যেন সরকারি আমলামাত্র। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে যে তাদের মতামত দেবার কোন ক্ষমতাই নেই, মতামত জোর করে তাদের ওপর চেপে বসানো হয়েছে।
সারাদেশ জুড়ে যখন চলছিল লোভ লালসা আর জড় রাজ্যের প্রাধান্য, তখন সামরিক কর্তৃপক্ষ সেনাবাহিনীর সদস্যদের এক আদর্শবাদে দীক্ষিত করে তোলে। সে আদর্শ হল দেশের প্রয়োজনে জীবন বিসর্জনের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতে। এ সেনাবাহিনী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে। সেদিক দিয়ে এর একটা দোষ ছিল। দেশে সামরিক শোধনবাদের সুযোগ থাকতে দেয় না। একসময় যারা এ চিন্তা থেকে মুক্ত তারাই সে সুযোগ পেত। এটা দোষ, এজন্য যে এর দ্বারা দমনের নীতিটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কারণ এর ফলে যারা বেশি শিক্ষা লাভ করেছে তাদের সাধারণ মানুষের স্তর থেকে সরিয়ে এনে সম্পূর্ণ পৃথক এক উন্নত স্তরে আবদ্ধ করে রাখা হত। এর উল্টোটা হলেই বরং ভাল হত। যেহেতু আমাদের উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা জাতির জীবনে কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্বন্ধে কিছুই জানত না এবং এভাবে তারা জনগণের জীবন থেকে ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছিল। সেই হেতু সেনাবাহিনী যদি নিজেদের মধ্যে ভেদজ্ঞানের পরিচয় না দিত, যদি বুদ্ধিজীবীদের বেশি সুযোগ সুবিধে না দিত, তাহলে তারা দেশের অনেক উপকার সাধন করতে পারত। এ বিষয়ে অবশ্যই তারা ভুল করেছিল। কিন্তু সমগ্র জাতির মধ্যে এমন কি কোন প্রতিষ্ঠান আছে যার মধ্যে ভুল ত্রুটি নেই। কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনীর দোষত্রুটিগুলো চোখেই পড়ত না। মানবজাতির দুর্বলতাজনিত সাধারণ দোষত্রুটির তুলনায় তা অনেক কম।
কিন্তু আমাদের সেনাদলের সবচেয়ে বড় প্রসংশার কাজ হল মানুষের সমষ্টিগত মূল্যায়নের ওপরে ব্যক্তিগত মূল্যায়ণকে স্থান দেওয়া। ইহুদি ও গণতন্ত্রের প্রবক্তাদের সংখ্যাদিক্যপ্রিয়তা ও মানুষের সংখ্যাগত শক্তির ওপর অত্যধিক নির্ভরতার নীতিতে বাধা দিতে থাকে। তখন আমাদের দেশের যার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল তা সত্যিকারের মানুষের; আমাদের সেনাবাহিনী সুকঠোর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের মত মানুষ গড়ার কাজে ব্রতী হয়েছিল। দেশের মানুষ যখন নারীসুলভ দুর্বলতা ও আলস্যে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল, তখন প্রতি ঘরের থেকে একজন করে সর্বসাকুল্যে সাড়ে তিন লক্ষ সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে এসে জনগণের সঙ্গে মিশে যেত। তাদের এ দুটি বছরের প্রশিক্ষণকালে তারা সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে ইস্পাতের মত শক্ত করে তুলত তাদের দেহগুলোকে। দু’টি বছর ধরে যেসব যুবক চরম আনুগত্য শিক্ষা করে আসত, প্রশিক্ষণ পেয়ে তারা পরিচালনা কার্যের যোগ্য হয়ে উঠত সর্বতভাবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিককে তার চলন দেখেই চেনা যেত।
এ সেনাবাহিনীই ছিল সমগ্র জার্মান জাতির সবচেয়ে বড় শিক্ষালয়। এভাবে নিতান্ত সঙ্গত কারণেই আমাদের সেনাবাহিনী সেই ব্যক্তির ঘৃণার বোঝা মাতায় তুলে নিয়েছিল, যারা চাইত জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিরক্ষাহীন অবস্থায় দুর্বল হয়ে যাক; এরা নিজেরা লোভ লালসায় জর্জরিত বলে জার্মান জাতির উন্নতিতে ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠেছিল। যে কথা সমগ্র জগৎ বুঝতে পেরেছিল সেকথা অনেক জার্মান বুঝতে পারেনি, কারণ তারা দেখে শুনে অন্ধ হয়েছিল অথবা হিংসার বশে সেকথা বুঝতে চায়নি। বাধা হল এ যে জার্মান জাতির স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার এবং দেশের নাগরিকদের জীবিকার্জনের ক্ষেত্রেও এ উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতির প্রতীক।
তার মধ্যে যে প্রতিষ্ঠানের নাম করা যেতে পারে, রাজশক্তি ও সেনাবাহিনীর ওপরে যাকে স্থান দেওয়া যেতে পারে, তা হল জার্মান সিভিল সার্ভিস বা অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা।
জার্মানির শাসনব্যবস্থা অন্যান্য দেশের শাসনব্যবস্থার থেকে আরো উন্নত ও সুগঠিত। সরকারি কর্তাব্যক্তিদের আমলাতান্ত্রিক রাজনীতির বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু সে রাজনীতি অন্যদেশের তুলনায় এমন কিছু বেশি খারাপ নয়। অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে জার্মানির মত এমন ঐক্য ও অখণ্ডতা নেই। তাছাড়া জার্মানির মত অন্যান্য রাষ্ট্রের সিভিলসার্ভিসের আমলাদের মধ্যে এতখানি সততা ও নৈতিক কুণ্ঠা নেই। অহংকারী, অসৎ, দুশ্চরিত্র ও অযোগ্য সরকারি কর্মচারীদের থেকে সৎ মনোভাবাপন্ন আমলা অনেক ভাল। কেউ যদি বলেন প্রাকযুদ্ধকালীন জার্মানির শাসনব্যবস্থায় আমলারা সৎ হলেও প্রশাসনিক কাজকর্মের দিক থেকে তারা ছিল অযোগ, তাহলে আমি নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করব;
পৃথিবীর আর কোন্ দেশে জার্মানির থেকে আরও উন্নত ও সুগঠিত প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল? দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্টেট রেলওয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। তারপর বিপ্লব এসে এ প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার করে দেয়। ক্রমে এমন একদিন আসে যেদিন এ বিপ্লবের কর্ণধার পুঁজিবাদীরা জার্মানির প্রশাসন যন্ত্রটাকে আন্তর্জাতিক শিল্পপতিদের দ্বারা পরিচালিত স্টক এক্সচেঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসে।
বিপ্লবের সময় সিভিল সার্ভিসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অসৎ মনোভাবসম্পন্ন সরকারি কর্মচারীদের অবাধ স্বাতন্ত্র। দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক আবহাওয়া জার্মানির সরকারি কর্মচারীদের ওপর কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না। বিপ্লবের পরে সমগ্র পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়। কর্মচারীদের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার জায়গায় পার্টি আনুগত্য স্থান গ্রহণ করে। চরিত্রের স্বাধীনতা ও কর্মতৎপরতা সরকারি কর্মচারীদের আদর্শ গুণ হিসেবে আর স্বীকৃত হয় না। বরং এ সব গুণগুলি ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে তাদের পক্ষে।
আগে জার্মান সাম্রাজ্যের আশ্চর্যজনক বিশাল শক্তিটি প্রতিষ্ঠিত ছিল রাজতন্ত্রের ওপর। আর এ রাজতন্ত্রের নির্ভরযোগ্য ভিত ছিল সেনাবাহিনী ও সিভিল সার্ভিস। এ তিনটি ভিতের ওপর রাষ্ট্র কর্তৃত্বরূপ শক্তির যে বিশাল সৌধটি প্রতিষ্ঠিত ছিল আজ তা দেখা যায় না। পার্লামেন্ট বা প্রাদেশিক সভাগুলোর কাজকর্মের দ্বারা কখনো রাষ্ট্রের কর্তত্ব বা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। কোন দেশের সরকার ও শাসন কর্তৃপক্ষ জনগণের মনে যে বিশ্বাস উৎপাদন করে তাদের সততা ও কর্মদক্ষতার দ্বারা, সে বিশ্বাসই হল রাষ্ট্র কর্তৃত্বের মূল ভিত। দেশের সরকার ও শাসন কর্তৃপক্ষ এক নিঃস্বার্থপরতা ও সততার আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করছে। এ ধরনের এক অটল অবস্থা থেকেই জনগণের বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। শুধু সন্ত্রাসের দ্বারা কখনো কোন সরকারের শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা যায় না; জনগণের উন্নতিতে তৎপর শাসন কর্তৃপক্ষের যোগ্যতা ও নিষ্ঠায় জনগণের যে বিশ্বাস-সেই বিশ্বাসই কোন সরকারের শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে পারে। অবশ্য একথা সত্য যে প্রাকযুদ্ধকালীন জার্মানিতে এমন কিছু অসভ্য শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে শাসনব্যবস্থার মধ্যে, যা জাতির অন্তনিহিত শক্তিকে জোরদার করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে জার্মানির তুলনায় অন্যান্য রাষ্ট্রে এ ধরনের শক্তির কর্মতৎপরতা আরো বেশি। এ কথাটায় বুঝতে পারব আমাদের ধ্বংসের মূল কারণটা কোথায়।
জার্মানির পরাজয়ের প্রধানতম কারণ হল এ যে জার্মানিতে বর্ণসমস্যা এবং জাতির ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারার এ সমস্যার তাৎপর্যটিকে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করা হয়। কারণ মনে রাখতে হবে কোন জাতির জীবনে যে সব ঘটনা ঘটে তা কখনো দৈবক্রমে ঘটে না, তা হল জাতিরই কার্যের স্বাভাবিক প্রতিফল। জাতির জনসংখ্যা কিভাবে বেড়ে চলেছে এবং জাতীয় শক্তির সংরক্ষণ কিভাবে হচ্ছে তারই ওপর নির্ভর করছে জাতির ভবিষ্যত।
————–
* ৩৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সীনেনিয়ন গলরা আলিয়ার যুদ্ধে রোমান সৈন্যদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করে এবং শহর রোমে প্রবেশ করে দেখে শহরটা মরুভূমি প্রায়, শুধু ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। যাদের আশা নিজেদের উৎসর্গ করে হলেও দেশকে রক্ষা করা। সদস্যরা আদেশ দেয় তাদের হাতির দাঁতের চেয়ারগুলো মন্দিরের সামনে রাখতে, এবং এরপর তারা যে যার চেয়ারে বসে; চেয়ারের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে রেখে বিজয়ী সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করে। লিবির ভাষায়, গলরা যখন শহরে ঢোকে, দেখে মাননীয় সদস্যরা চেয়ারে উপবিষ্ট। একদল অবতার যেন তাদের জন্যই অপেক্ষা করছে। স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে শহর রোম রক্ষার নিমিত্তে। মহৎ উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই; যদিও আক্রমণকারীদের হাত থেকে এর দ্বারা শহর রক্ষা করা যায়নি। তবু পরবর্তীদের পক্ষে এটা একটা মহৎ উদাহরণ।