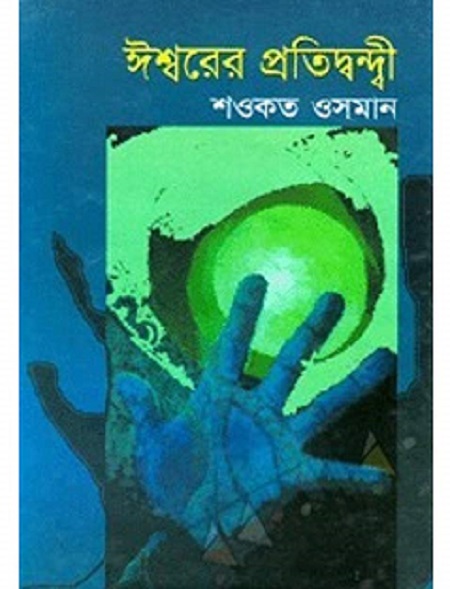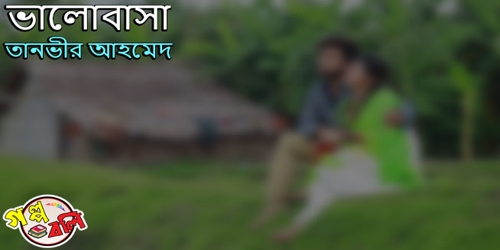কলেজে ভর্তি হয়ে মনে হলো, অঙ্কে আমার প্রাইভেট পড়া দরকার। আমি অঙ্কে একেবারে যে কাঁচা তা কিন্তু নয়। কিন্তু অঙ্ক নিয়ে আমার কিছু ভয় আছে। কিছু ঘটনা আছে।
ক্লাস নাইনের বার্ষিক পরীক্ষা আমার বেশ খারাপ হয়েছিল। এক-একটা পরীক্ষা খারাপ দিতাম আর বাড়িতে এসে আব্বা-আম্মা জিজ্ঞেস করলে বলতাম, পরীক্ষা ভালো হয়েছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আতঙ্কে মরে যাচ্ছিলাম- রেজাল্ট আউট হলে কী জবাব দেব বাড়িতে আর বন্ধুবান্ধবের কাছে মুখই-বা দেখাব কীভাবে?
আমার সঙ্গে কী নির্মম পরিহাস, সেই বছরই বার্ষিক পরীক্ষা শেষে আমাদের স্কুল থেকে পিকনিকে যাওয়ার আয়োজন করা হলো। গন্তব্য কক্সবাজার। পিকনিক প্রতিবছরই হতো আশেপাশের স্পটে। সন্দ্বীপ সীমান্তে উড়িরচরে কিংবা বড়জোর ফেনীর মুহুরী প্রজেক্টে। কিন্তু এবার একেবারে এক লাফে কক্সবাজারে! আমি কী করে যাব? কক্সবাজারে যাওয়ার মুখ কি আছে আমার! আমার যে পরীক্ষা খারাপ হয়েছে! আব্বার কাছে কোন মুখে ১২০ টাকা চাইব?
পিকনিকের বিষয়টা আব্বা জানতেন। আমি সিরাজপুর হাই স্কুলের ছাত্র। আব্বা পাশের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। টাকা জমা দেওয়ার তারিখ শেষ হয়ে গেলেও আব্বা কিছু বলছেন না দেখে আমি ধরেই নিয়েছি, আমার পিকনিকে যাওয়া আর হচ্ছে না।
একদিন সন্ধ্যায় বাজার থেকে এসে আব্বা আমার হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা পরে যাবি। আমি প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে আব্বার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আব্বা বললেন, টাকা জমা দিয়ে দিয়েছি। ক্লাসের ফার্স্টবয় পিকনিকে যাবে না, তা হয় না।
প্যাকেট খুলে দেখি একজোড়া বাটার স্যান্ডেল। চামড়ার। দাম ৪৯ টাকা। তার মানে আমাকে পিকনিকে পাঠানোর জন্য আব্বা ১৬৯ টাকা খরচ করে ফেলেছেন! এটা অনেক টাকা। ৩০ কেজি আটার দাম। আমাদের সাত দিনের খোরাকি। এই টাকা আব্বা পুষিয়ে নেবেন কীভাবে? নির্ঘাৎ আমাদের খানাদানায় কষ্ট করতে হবে। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।
এইটের বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছি মাইজদীতে গিয়ে, নোয়াখালী জিলা স্কুলে। জীবনের প্রথম ফুলপ্যান্ট তখন পরেছি। সাথে রূপসা হাওয়াই চপ্পল। চামড়ার জুতা এই প্রথম জুটল। প্যান্ট সেই একটাই। এইটেরটা। সব মিলিয়ে আমার খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু পরীক্ষা খারাপ হওয়ায় আমার মনটা মলিন হয়ে উঠল ভয় আর অপরাধবোধে। সেই মলিন মন নিয়ে পিকনিক সেরে আসার তিন দিনের মাথায় আমাদের রেজাল্ট হলো। সব বিষয়ে নম্বর ৮০, ৮১, ৮২ করে। কিন্তু অঙ্কে পেয়ে বসলাম ৭২। আর তাতেই ২ নম্বর কম পেয়ে আমি হয়ে গেলাম সেকেন্ড, ফার্স্ট হলো ইন্দ্রাণী মজুমদার।
আমি কয়েকদিন স্কুলে গেলাম না। আমার সহপাঠীরা, এমনকি দু-একজন স্যারও ইন্দ্রাণীকে জড়িয়ে আমার সঙ্গে দুষ্টুমি করা শুরু করল। ইন্দ্রাণী এবং ইন্দ্রাণীদের বিষয়ে আমার মধ্যে এক ধরনের শরম ঢুকে গেল। সেই শরম পরে একটা ঘোরে পরিবর্তিত হলেও অপরাধবোধটা একই রকম থেকে গেল।
পিকনিক থেকে এসে দেখি আব্বার পায়ে ব্যান্ডেজ। আম্মার কাছে শুনেছি, ক্লাসের ফার্স্টবয়ের জন্য পিকনিকের টাকা জোগাড় করতে আব্বা গিয়েছিলেন হারুন মেম্বারের কাছে। হাওলাত চেয়েছিলেন, পাননি। টেনশন নিয়ে ফেরার সময় সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে পা কেটে ফেলেছেন। আমাদের কাউকে বলেননি। লুকিয়েছেন। পরে ইনফেকশন হয়েছে। পিকনিকের টাকাটা পরে কীভাবে জোগাড় হয়েছে সেটা আর আম্মা বলতে পারেননি। অঙ্কে ৭২ পাওয়ার পরে আব্বা আমাকে বকাটকা কিছুই দেননি। শুধু বলেছেন, সাইকেল অ্যাকসিডেন্ট করেই আমি বুঝতে পেরেছি কোনো একটা অমঙ্গল অপেক্ষা করছে। অমঙ্গলটা যে তোর অঙ্কের ওপর দিয়ে যাবে সেটা কে জানত? পায়ের ব্যান্ডেজে হাত বোলাতে বোলাতে আব্বা বলছিলেন, ইন্দ্রাণীর কাছ থেকে জেনে নিস অঙ্কে কীভাবে ৮০ পেতে হয়।
জেনে নেওয়া দূরে থাক, ইন্দ্রাণীর সঙ্গে আমি কথা বলাই বন্ধ করে দিলাম লজ্জায়। মাঝেমধ্যে লুকিয়ে ওর দিকে তাকাতাম। দেখতাম সেও তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমার ১৬ বছরের মনটা দখিনা হাওয়ায় বাতাবি লেবুর মতো দুলে উঠত তখন। ডালে-কাঁটায় খোঁচা খেয়ে দুরন্ত বাতাবির খোসা থেকে ঝাঁঝালো ঘ্রাণ বের হতো।
অনেক চেষ্টা করেও এসএসসিতে ইন্দ্রাণীকে হারাতে পারিনি। বরং ইন্দ্রাণী আমার লাজুক অনুভূতিতে আরও জড়িয়ে গেল এসএসসিতে সমান নম্বর পেয়ে। দু’জনেরই ৭৫১। এবং কী আশ্চর্য, অঙ্কে দু’জনের নম্বর ৮৫ করে!
কলেজে আমাদের অঙ্কের স্যার বিশ্বপতি রায়কে প্রাইভেট পড়বার বিষয়টা বললাম। স্যার বললেন, আমার সময় নেই, অন্য কারও কাছে চেষ্টা কর। কিন্তু আমাকে প্রাইভেট পড়তেই হবে। আমি অঙ্কে কাঁচা নই। কিন্তু অঙ্কের কথা মনে হলে আমার ভেতরটা ইন্দ্রাণীর হাসির মতো খলখলিয়ে ওঠে। এটা অবশ্য উপভোগ্য। তবে আব্বার অমঙ্গলের কথাটা পানিয়ালার কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে মনে।
সুতরাং বিশ্বপতি স্যারের কাছে পড়তেই হবে। আমি বললাম, স্যার আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের হেড রায়হানুল হক স্যারের ভাগনে। মামাই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। বিশ্বপতি স্যার আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, আগে বলবি তো। ঠিক আছে, কাল সকাল ৮টায় চলে আসবি।
আমি বললাম, আচ্ছা স্যার।
বিশ্বপতি স্যার আমার মাথার তালুতে হাতের পিঠ ঠেকিয়ে আমার উচ্চতা মাপার ভঙ্গি করে বললেন, তুই তো দেখছি অনেক লম্বা হয়েছিস, কয়দিন পরে আমাকেও ছাড়িয়ে যাবি। হাইট কত?
পাঁচ ফুট আট স্যার। সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কত স্যার?
ছয় ফুট এক। ঠিক আছে, কাল চলে আসিস।
বিশ্বপতি স্যারের উচ্চতা দেখে আমার মাথায় একটা প্রশ্ন ঢুকে গেল। স্যারও কি রুটি খান? স্যারও কি আমাদের মতো গরিব?
রুটি খেলে মানুষ লম্বা হয়ে যায়। এটা বলেছেন শাহজাহান স্যার। কলেজে বাংলার স্যার। হৈমন্তী থেকে পড়াতেন- খোট্টার দেশে ডালরুটি খাওয়া মানুষ, তাই অমন বাড়ন্ত হইয়াছে।
আমরাও ডালরুটি খেতাম। আমাদের সব ভাইবোন তাই লম্বা। আমরা ডালরুটি খেতাম অভাবে। আব্বার চাল কেনার মতো টাকা ছিল না।
আমাদের দিন শুরু হতো রুটি দিয়ে। ফজরের নামাজ পড়ে আব্বা আটা মলতেন, রুটি বেলে দিতেন। আম্মা বসে বসে সেঁকতেন। আমরা রান্নাঘরেই গোল হয়ে বসতাম। চিংড়ি শুঁটকি দিয়ে রান্না করা বুটের ডাল দিয়ে রুটি খেয়ে আমরা স্কুলে যেতাম। রুটি ছিল হিসাব করা। একজনের জন্য দুইটা। যেদিন ডাল জুটত না সেদিন আমরা গুড়ের চায়ে চুবিয়ে গোটা দুই রুটি খেয়ে আরেকটার লোভ সংবরণ করতাম। পেটপুরে খেতে না দিতে পারায় আব্বা-আম্মার যে কষ্ট- সেটাকে আর উসকে দিতে চাইতাম না। আমরা ছিলাম এমনই চালাক।
আমাদেরকে খাইয়েদাইয়ে আব্বা স্কুলে যেতেন। আমাদের কোনো কোনো শিক্ষক আসতেন হালচাষ সেরে। গায়ে, জামায়, ঘাড়ে, কানের গোড়ায় কাদা শুকিয়ে থাকত। দুষ্টু পোলাপান হাসাহাসি করত এ নিয়ে। আমার খুব লাগত। আমার আব্বাও যখন স্কুলে যেতেন, নখের কোনায়, আঙুলের ফাঁকে আটা লেগে থাকত। শুকিয়ে শক্ত হয়ে যেত। দুষ্টু ছাত্রছাত্রীরা এসব দেখে হাসত। ক্লাস ফাইভের এক অতিসাহসী মেয়ের নাম ছিল ফেরদৌস আরা। সে নাকি আব্বার আঙুলে লেগে থাকা আটা খুঁটে খুঁটে তুলত। দিনশেষে আব্বা এসব নিয়ে আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন। কিন্তু আমরা বুঝতাম, রুটি খাওয়ার বিষয়টা সবাই তাচ্ছিল্যের চোখে দেখত। আমরা চাল কিনতে পারি না, তাই আমরা রেশনের, কন্ট্রোলের আটা খাই। বেশি খোঁটা দিতেন আমাদের প্রতিবেশী সায়রা ভাবি। তার স্বামী বন্দরে চাকরি করতেন। বড়লোক ছিলেন।
অভাবের মাঝেও কোনো কোনো বেলা আমাদের ভাত জুটত। আম্মা সেদিন সবাইকে একসঙ্গে বসাতেন। টিনের থালা নিয়ে আমরা বসে যেতাম আম্মাকে ঘিরে। নারিকেল মালার চামচ দিয়ে মেপে মেপে আমাদের সাত ভাইবোনের থালায় ভাত বেড়ে দিতেন আম্মা। এ ক্ষেত্রে খোদাদাদ খানের মতো অঙ্কবিদ ছিলেন তিনি। কিন্তু থালার একপাশে পড়ে থাকা ভাতগুলো আমাদের দিকে যেন করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। আমরা সেই সামান্য ভাত তৃপ্তি নিয়ে খেতাম। আম্মা শূন্য হাঁড়িতে মালার চামচের শব্দ করে বলতেন, ভাত আর নিবি? আমরা বলতাম, নাহ্, পেট ভরে গেছে। ক্ষুধা নিয়ে আমাদের এই লুকোচুরি আমরা সবাই বুঝতাম, কিন্তু কেউ কাউকে বোঝাতে চাইতাম না।
যেদিন ভাত খেতাম, আমরা সায়রা ভাবিকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতাম, এই ভাত খেয়েছিস? যা, তাড়াতাড়ি যা, আম্মা ভাত নিয়ে বসে আছে। ভাত খেতে পারাটা কী যে গৌরবের ছিল!
পরদিন থেকে প্রাইভেট পড়া শুরু করলাম। প্রাইভেট পড়ায় আনন্দ আছে। অঙ্ক কষতে পারা নয়, আনন্দের কারণ ভিন্ন। আমাদের ব্যাচে ইন্দ্রাণীও পড়ত।
মাস শেষ হলো। স্যার সবাইকে টাকা আনার জন্য তাগাদা দিতে লাগলেন। ৩০০ টাকা। সেই সময়ে এটা অনেক টাকা।
বাড়ি এসে আব্বাকে টাকার কথা বললাম। আব্বা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, পরশুদিন নিস।
আব্বার সামান্য বেতন। জমিজিরেত নেই। অভাবের বড় সংসার।
পরদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে আব্বার দেরি হলো। আমি বুঝে নিলাম আব্বা টাকার খোঁজে বেরিয়েছেন। আমি মনে মনে দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলাম। আব্বা আবার না জানি সাইকেল থেকে পড়ে যান!
বিশ্বপতি স্যারের জন্য যেদিন টাকা নিয়ে গেলাম, প্রাইভেট শুরুর আগে স্যার আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, তুই রায়হানুল হক স্যারের ভাগনে, মানে আমারও ভাগনে, তোর টাকা দেওয়া লাগবে না।
তখন থ্যাংক ইউ ট্যাংকিউ বলার তেমন চল ছিল না। খুশিতে আমি স্যারের পায়ের ধুলা নিলাম।
আমার খুশি হওয়ার কারণটা ছিল অন্য। গান শুনতে ভালো লাগত। গরিব ঘরের ছেলে ছিলাম বলে সাধ-আহ্লাদ তেমন একটা মেটাতে পারতাম না। বহুদিন থেকে একটা ওয়াকম্যান কেনার শখ। ইয়ারফোন লাগিয়ে শুনছি সাগর সেনের রবীন্দ্রসঙ্গীত- আহা কী দারুণ ব্যাপার!
বিশ্বপতি স্যার ৩০০ টাকা না নেওয়ায় আমার চোখ খুশিতে ঝিলিক দিয়ে উঠল। খুশির চোটে আমি ভুলে গেলাম আমার গরিব পিতার সীমাহীন অর্থকষ্টের কথা।
আম্মাকে ফুসলিয়ে আরও ১০০ টাকা নিলাম। আম্মা দিয়েছেন সুপারি বিক্রি করে। আমাদের অনেক সুপারি গাছ ছিল।
৪০০ টাকায় একটা ওয়াকম্যান পাওয়া গেল। খুশিতে আমি আটখানা। আহা, সাগর-কিশোর-মান্না-লতা-আশা এখন আমার হাতের মুঠোয়। গভীর রাতে শুয়ে শুয়ে আমি গান শুনব। আমার যখন ঘুম আসবে না, ইন্দ্রাণীর জন্য বুকটা আকুলিবিকুলি করবে যখন; সাগর সেন তখন আমার কানে কানে শোনাবেন- কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া, তোমার চরণে দেব হৃদয় খুলিয়া… কিংবা আশা গাইবেন- ফুল কেন লাল হয় সে কি বলা যায়/ ভালোবাসি এ কথা কি মুখে বলা যায় …।
দোকানিকে বললাম, একটু বাজিয়ে দেখান।
ইয়ারফোন কানে দিতেই বেজে উঠল কিশোর কুমারের গান- পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতা জগতের আলো/ তার সে চোখ দিয়ে দেখেছি মন্দভালো।…
মুহূর্তেই আমার চোখে আব্বার চেহারাটা ভেসে উঠল। আব্বার চিন্তিত চেহারা, কপালে ভাঁজপড়া চেহারা, আব্বার পায়ের সেই ব্যান্ডেজ। আমি আব্বার চোখ দিয়ে মন্দভালো দেখা শুরু করলাম। দেখতে পেলাম আমাদের অভাবি সংসারটাকে আব্বা কীভাবে ঘানির মতো টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।
ওয়াকম্যানটা রেখে আমি চলে এলাম। এখনই আমি আব্বা-আম্মার কাছে যাব। টাকাগুলো ফেরত দেবো। আব্বা-আম্মার একটুখানি হাসির কাছে সাগর সেনের রবীন্দ্রসঙ্গীত অনেক তুচ্ছ।
দোকান থেকে ফিরে এলাম। পেছন থেকে দোকানি বলল, ফাজিল ছেলে একটা। কথাটা শুনতে আমার ভালো লাগল। সেই মুহূর্তে সাগর সেন, আশা ভোঁশলের সঙ্গে ইন্দ্রাণীও আমার অনুভূতিতে আবছা হয়ে গেল।