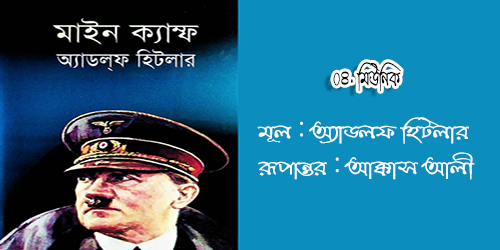দ্রোণ বলিলেন, যদি সন্তোষ করিবে।
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটা দিবে
গুরুর আজ্ঞায় সে বিলম্ব না করিল।
ততক্ষণে কাটিয়া অঙ্গুলি গোটা দিল
—দ্রোণ সমীপে অস্ত্রশিক্ষা হেতু একলব্যের আগমন, মহাভারত,/কাশীরাম দাস।
আমার নাম একলব্য। পিতার নাম হিরণ্যধনু। মায়ের নাম বিশাখা। পিতামহ অনোমদর্শী। ‘মহাভারত’ যুগের মানুষ আমি। ‘মহাভারতে’ আমাকে নিয়ে সামান্য কথা আছে। অন্য চরিত্রগুলো নিয়ে অনেক কথা বলেছেন ব্যাসদেব। তাঁরা রাজরাজড়া, যোদ্ধা, তপস্বী। কাশীরাম দাস যখন ‘মহাভারত’ বাংলায় অনুবাদ করলেন, আমার চরিত্র বংশপরিচয় নিয়ে কিছু কথাবার্তা লিখলেন। নব্বইটি পঙিক্ত লিখলেন আমাকে নিয়ে। ভুল বললাম, নব্বই নয় অষ্টাশি লাইন। শেষের দুই লাইন তো কবির আত্মঘোষণা আর পুণ্যলাভের প্রলোভন—‘মহাভারতের কথা সুধার সাগর।/কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর’ ওই অল্প কয়েকটি পঙিক্ততে, বিশাল ‘মহাভারতে’র তুলনায় অবশ্যই অল্প, কাশীরাম দাস আমার অস্ত্রবিদ্যালিপ্সা, দ্রোণাচার্যের প্রত্যাখ্যান এবং মর্মান্তিক ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। এরপর আমি বেঁচেছিলাম কি না, নিজ রাজ্যে ফিরে গিয়েছিলাম কি না, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম কি না, নিলে কোন পক্ষে যোগদান করেছিলাম—এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই ‘মহাভারতে’।
বাংলাদেশের কোন এক অর্বাচীন লেখক, নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, দাঁড়ান, একটু মনে করে নিই, হ্যাঁ মনে পড়েছে, হরিশংকর জলদাস, তো তিনি নাকি আমাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখেছেন। অনেক পড়াশোনা করেই নাকি তিনি উপন্যাসটা লিখেছেন। তিনি নাকি সেই উপন্যাসে আমার শেষ পরিণতি দেখিয়েছেন। যাকগে, নানাজনে নানাভাবে তো লিখতেই পারেন আমাকে নিয়ে। আমি আমাকে নিয়ে কী ভেবেছি, তা একটু বলতে পারি।
ব্যাধবংশে আমার জন্ম। ব্যাধদের রাজা ছিলেন হিরণ্যধনু। তাঁরই ঘরে আমার জন্মানো। মা বিশাখা আমাকে জন্ম দেওয়ার পর আর কোনো পুত্রসন্তান গর্ভে ধারণ করেননি।
পাঠশালায় পড়তে পড়তেই আমি অস্ত্রবিদ্যার দিকে ঝুঁকে পড়ি। রাজা এবং রাজন্যপুত্রদের পড়ার জন্য রাজপ্রাসাদেই আলাদা পাঠশালা ছিল। বাবা ওই পাঠশালাতেই পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দাদু অনোমদর্শী রাজি হননি। তিনি বাবার চেয়েও বেশি বাস্তববাদী ছিলেন। পৃথিবীর দিকে সাদা চোখে তাকাতেন। চোখে রঙিন আবরণ ছিল না তাঁর। তিনি বললেন, সাধারণ পাঠশালাতেই পড়বে একলব্য। বাবা দোনামনা করলেন। দাদু বললেন, সাধারণ ব্যাধদের সন্তানরাই পড়ে ওই পাঠশালায়। একলব্য তোমার একমাত্র পুত্রসন্তান। তোমার পরে ও রাজা হবে এই ব্যাধরাজ্যের। যারা তার প্রজা হবে, তাদের না চিনলে রাজ্যচালনা কঠিন হবে একলব্যের। ওই পাঠশালায় সাধারণ ব্যাধসন্তানদের সঙ্গে মেশার সুযোগ আছে। ধীরে ধীরে তাদের মনমানসিকতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠবে একলব্য। দাদুর যুক্তির কাছে হার মানলেন বাবা। রাজকীয় পাঠশালা পরিহার করে সাধারণ পাঠশালায় পাঠানো হলো আমাকে।
সেখানে আমি আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠতে লাগলাম। আমার চারপাশে অনেকে জুটে গেল। তারা সবাই সাধারণ নিষাদসন্তান। তাদের চাওয়া-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠতে লাগলাম আমি।
প্রচলিত ধারার পড়াশোনা আমার তেমন ভালো লাগত না। যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনির প্রতি আমার ঝোঁক তৈরি হতে লাগল। অস্ত্রের কথা উঠলেই আমি উত্সুক হয়ে উঠতাম। আমাদের পাঠশালায় বেশ কজন পণ্ডিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে পণ্ডিত টঙ্কারী ছিলেন আলাদা। শিষ্যদের পড়াতে পড়াতে বারবার তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনিতে চলে যেতেন। নানা অস্ত্রশস্ত্রের বিবরণ দিতেন তিনি। আর্যদের কথা বলতেন তিনি খুব। প্রত্যেক যুদ্ধকাহিনিতে ব্যাধদের প্রতিপক্ষ থাকত আর্যরা। পণ্ডিত টঙ্কারীর মুখেই আমার প্রথম আর্যদের কথা শোনা। তিনি বলতেন, আর্যরা অস্ত্রবিদ্যায় অনেক শক্তিশালী। আমাদের যে যুদ্ধবিদ্যা, তা ওদের তুলনায় ঠুনকো। বলতে বলতে তিনি একদিন এও বলেছিলেন,
কুরুকুলের এখন শ্রেষ্ঠতম অস্ত্রবিদ এবং গুরু দ্রোণাচার্য। তিনি এই সসাগরা পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধনুর্ধর। তাঁর কাছ থেকে যুদ্ধবিদ্যা গ্রহণ করতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে উঠবে।
ওই দিনই আমার মধ্যে দ্রোণাচার্যের কাছে বসে বিদ্যার্জন করার বাসনাবীজ রোপিত হয়ে গেল। আমার মন কী রকম চঞ্চল হয়ে উঠল। প্রচলিত বিদ্যা আমার ভালো লাগছিল না। বাবাকে বলায় বাবা আমাকে এনে ব্যাধ-সেনাপতির হাতে গছিয়ে দিলেন। বাবা বললেন, সেনাপতি মশাই, একলব্যকে যুদ্ধকৌশলে চৌকস করে তুলুন। পরের বেশ কয়েকটি বছর আমি সেনাপতি জগদম্ভের শিষ্য হয়ে থাকলাম। আমার বয়স বৃদ্ধি পেতে লাগল। আমি একুশে পড়লাম।
ওই সময় আমার প্রতি কেউ অনুরক্ত হয়েছিল কি না জিজ্ঞেস করছেন? হ্যাঁ, হয়েছিল। সে প্রধান অমাত্যকন্যা শৈলবালা। আঠারোর দিকেই তার বয়স তখন। আগে আরেঠারে বললেও সেদিন শৈল সরাসরি তার অনুরাগের কথা বলল। আমার সেই ক্ষণে শিহরিত হয়ে ওঠার কথা। বনময়ূরের মতো পেখম মেলে নাচ শুরু করার কথা। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, এর কোনোটাই আমি করলাম না। উপরন্তু ধীরস্থির চোখে শৈলবালার দিকে আমি তাকিয়ে থাকলাম বেশ কিছুক্ষণ। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললাম, তোমার আশা পূরণের নয় শৈল। আমাকে তুমি ক্ষমা করো। গভীর আকুলতায় কী যেন বলতে চাইল আমায়। আমি তার কথা না শুনে সে স্থান ত্যাগ করলাম।
কেন এ রকম করলাম জিজ্ঞেস করছেন? এ রকম না করে যে আমার কোনো উপায় ছিল না। তখন আমার ধ্যানে আর জ্ঞানে যে মহর্ষি দ্রোণাচার্য। কখন আমি তাঁর কাছে যাব, কখন ধনুর্বিদ্যা অর্জন করব—এই চিন্তায় তখন বিভোর আমি। তাইতো শৈলবালার প্রেমকে হেলা-অবহেলা দেখালাম।
এর পরের ঘটনা আপনাদের জানা। দ্রোণাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার অনুমতি চাইলাম আমি। বাবা কিন্তু রাজি হলেন না। কেন রাজি হলেন না, আমি জানতাম না; কিন্তু বাবা ভালো করেই জানতেন। আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্ব বহুকালের। ব্রাহ্মণরা যে শূদ্রদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন, সেটা বাবার ভালো করেই জানা ছিল। দ্রোণাচার্য যে আমাকে অস্ত্রশিক্ষা দেবেন না, তা-ও বাবার অজানা ছিল না। দাদু অনোমদর্শীও তা জানতেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! দ্রোণাচার্যের কাছে আমাকে পাঠাতে দাদু রাজি হয়ে গেলেন। শুধু রাজি হওয়া নয়, বাবাকে প্ররোচিত-প্রণোদিত করলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত আমার প্রস্তাবে সায় দিলেন বাবা।
গিয়েছিলাম আমি হস্তিনাপুরে, দ্রোণাচার্যের পাঠশালায়। রাজপুত্রদের পড়ানোতে নিমগ্ন তখন তিনি। আমি কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। সূর্যের আলোতে আমার দীর্ঘ ছায়া গুরুদেবের সম্মুখভাগ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। গুরুদেব কেন বলছি? শিক্ষাগ্রহণ না করেও? আচার্য দ্রোণ আমার তো শিক্ষাগুরুই। পণ্ডিত টঙ্কারীর কাছে তাঁর নাম শোনার পর থেকেই আমি তাঁকে আমার গুরুদেবের আসনে বসিয়েছি।
আমার গাঢ় ছায়া অনুসরণ করে গুরুদেবের দৃষ্টি আমা পর্যন্ত এলো। তিনি চমকে উঠলেন ভীষণ। এ রকম কুচকুচে কালো, ধূলিধূসরিত দেহ, অনার্য শরীর গঠন, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, নাতিদীর্ঘ আমাকে তো তিনি আগে কখনো দেখেননি। আর এই অনার্য যুবকটি এ রকম সুরক্ষিত এলাকায় ঢুকল কী করে? কী চায় সে? কোনো অশুভ উদ্দেশ্যেই কি সে এখানে এসেছে? এ রকম তিনি যখন ভাবছেন, আমি দ্রুত তাঁর সামনে এগিয়ে গেলাম এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলাম। গুরুদেব প্রায় স্তম্ভিত তখন। কী বলবেন, ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।
তখনই আমি আমার মনোবাসনা ব্যক্ত করলাম—আমি আপনার শিষ্য হতে চাই। আমি যে এক অনার্য ব্যাধসন্তান, ভাবে-চেহারায় আর পোশাকে ততক্ষণে বুঝে গিয়েছিলেন গুরুদেব। সামান্য সময় কী যেন ভাবলেন তিনি। ওই সময় সামনে সমবেত ছাত্রদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। অর্জুনের মুখেই যেন অবহেলা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বেশি। ও যে অর্জুন, বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি তেমন। মেধাবী ছাত্রের সর্বলক্ষণ তার চোখে-মুখে। তার সম্পর্কে শুনে শুনে তার একটা অবয়ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল আমার মধ্যে। আমার ব্যাকুল প্রস্তাবের উত্তরে আচার্য কী বলেছিলেন জানতে চাইছেন? উত্তরটা আপনাদের কবি কাশীরাম দাস তাঁর অনূদিত মহাভারতের আদি পর্বে লিখে গেছেন।
কী লিখেছেন?
লিখেছেন—
দ্রোণ বলিলেন তুই হোস নীচ জাতি।
তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি
দ্রোণাচার্য ছাত্র হিসেবে আমাকে গ্রহণ করলেন না। অনেকটা দূর দূর করে কুকুর-বিড়ালের মতো তাড়িয়ে দিলেন আমায়। আমি তখন অথই সমুদ্রে। কী করব আমি? রাজধানীতে ফিরে যাব? কোন মুখে ফিরব? বাবাকে যে বলে এসেছি, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ হয়ে ফিরব আমি বাবা, দেখে নিয়ো। দাদু অনোমদর্শী তো বহু আশা নিয়ে অপেক্ষা করে আছেন, আমি একদিন রণ-ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে ফিরব। খালি হাতের আমাকে দেখে তাঁরা দুজনেই তো আশাহত হবেন ভীষণ। না, না। কিছুতেই বিদ্যার্জন না করে হিরণ্যধনুর রাজধানীতে ফিরব না আমি।
গুরুর সম্মুখভাগ থেকে ফিরে আসার সময় যথাদূরত্ব বজায় রেখে দ্রোণাচার্যকে প্রণাম করেছিলাম। মাটিতে মাথা ঠেকিয়েই প্রণাম করেছিলাম আমি। ওই সময় মনে মনে বলেছিলাম, আজ যাকে নীচ জাতি বলে শিষ্যত্ব প্রদানে প্রত্যাখ্যান করলেন, একদিন আমি খ্যাতিমান ধনুর্ধর হয়ে আপনাকে, গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখিয়ে দেব। আসি। সেই দুপুরে পাঠশালাগৃহ থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। এরপর কী হয়েছিল, মহাভারতের কল্যাণে সব জেনেছেন আপনারা। জানেননি যা, তা বলছি।
গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে দ্রোণাচার্যের মৃন্ময় মূর্তি বানিয়েছিলাম আমি। ওই মূর্তির সামনেই আমার অস্ত্রসাধনা শুরু হয়। প্রথম দিকে কিছুই হচ্ছিল না। শুধু ব্যর্থতা আর বিফলতা। কোনোক্রমেই দমিনি। অস্ত্রসাধনা চালিয়ে গেছি। খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিলাম। শুধু আচার্য দ্রোণকে দুই ভ্রুর মাঝখানে রেখে কঠোর সাধনা চালিয়ে যেতে লাগলাম আমি।
সেই প্রভাতে আশ্চর্যজনক ঘটনাটি ঘটল। শয্যাত্যাগ করে ধনুটি হাতে নিলাম। অলসভাবে তীরটি ধনুতে যোজনা করে বহুদূরের একটি আম্রফলকে লক্ষ্য করে ছুড়লাম। কী অদ্ভুত! কী বিমোহন ঘটনা! তীরটি আম্রফলে গিয়ে গেঁথে গেল। আমি পর পর আমার চারপাশে বহুদূরব্যাপী ছড়ানো বস্তু লক্ষ্য করে তীর ছুড়লাম। সব তীরই লক্ষ্য ভেদ করল। আমি বুঝতে পারলাম, আমার সাধনা সফল হয়েছে। আমি আনন্দে ধেইধেই করে নেচে উঠলাম।
আমার এই চিৎকারধ্বনি গুরুদেব শুনতে পেয়েছেন কি না, জানি না। একদিন তিনি ভীম, অর্জুনাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আমার কুটিরের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। কেন? গুরুদক্ষিণার জন্য। আসলে কুরুপুত্ররা মৃগয়ায় এসেছিল। তাদের পালিত কুকুরটি আমার ছোড়া তীর দ্বারা বিদ্ধ হয়েছিল। বিদ্ধ হওয়ার ভঙ্গিটি ছিল অকল্পনীয়। তাতেই অর্জুন চটে গিয়েছিল। এই ভঙ্গিটি তো তার অজানা! তাহলে তার চেয়েও বড় ধনুর্ধর আছে? কুকুরের দেখানো পথ বেয়ে গুরু-শিষ্যরা উপস্থিত হয়েছিলেন আমার আঙিনায়। আঙিনার মাঝখানে নিজ মূর্তি দেখে ভীষণ চমকে গিয়েছিলেন দ্রোণাচার্য। এ তো তাঁরই মূর্তি। জিজ্ঞেস করেছিলেন, কে তুমি?
বলেছিলাম, একলব্য। আপনার প্রত্যাখ্যাত শিষ্য।
গুরুর মনে পড়ে গিয়েছিল আমার কথা। বলেছিলেন, ও—, ছোট জাত বলে যাকে পাঠশালায় ভর্তি করাইনি, সে-ই তুমি?
—হ্যাঁ, গুরুদেব।
—এ মূর্তি কার?
—আপনার। দেখতে পাচ্ছেন না—সেই নাক, সেই গৌরবর্ণ, সেই চোখ। সেই উপবীত?
—দেখতে পাচ্ছি।
—আমি আপনার মূর্তি গড়ে তাঁর পায়ের কাছে সাধনা করে গেছি। সফল হয়েছি।
—কী সফল হয়েছ?
—যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারি এখন। বহুদূরের, সে যতই দূরের হোক না কেন, লক্ষ্য ভেদ করতে পারি। যে বস্তুর গায়ে হাত দিই, তা-ই অস্ত্র হয়ে যায়।
—মানে?
—ওই আপনার পাশের কুকুরটিকে দেখুন। তার মুখ ভেদ করা ঘাসের ডাঁটা। আমিই ছুড়েছি। মুখে যা এসেছে, তাকেই মন্ত্র হিসেবে পড়ে গেছি। আমার ছোড়া ডাঁটা ঘেউঘেউরত কুকুরটির মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। রক্তপাত হয়নি।
গুরুদেবের চোখ দুটো বস্ফািরিত। তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, কোনো মন্ত্র পড়োনি মানে!
—হ্যাঁ, তীর ছুড়তে এখন আমার মন্ত্র লাগে না। যা মুখে আসে, তা-ই মন্ত্র হয়ে যায়।
এরপর হঠাৎ গুরুদেবের সারা মুখে চাঁদের হাসি ছড়িয়ে পড়ল। কী যেন আওড়ে গেলেন। ঠোঁট নড়ল, শব্দ হলো না।
তিনি বললেন, এসব শিখলে কোত্থেকে?
আমি বললাম, আপনার কাছ থেকে। প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে। আপনিই আমার গুরু। ওই মূর্তি তার সাক্ষী।
কঠোর-কঠিন একটা রাগের ঝিলিকে গুরুদেবের দুচোখ ঝলসে উঠল। তবে তা পলকের জন্য।
হঠাৎ তিনি বললেন, তাহলে তো গুরুদক্ষিণা দিতে হবে, বাবা।
—গুরুদক্ষিণা!
—হ্যাঁ তো, ওই যে তুমি বললে আমি তোমার গুরু, আমার কাছ থেকে তোমার সব কিছু শেখা!
আমি সামান্য সময়ের জন্য মাথা নত করলাম। কী ভাবলাম তখন? আপনারা এখন যা ভাবছেন, তা-ই ভেবেছি তখন আমি। গুরু না হয়েও গুরুদক্ষিণা চান যাঁরা, তাঁরা কী ধরনের মানুষ, এই তো ভাবছেন আপনারা?
আমি বললাম, কী চান গুরুদেব? কী পেলে আপনি আনন্দিত হবেন?
ভাবলেশহীন মুখে দ্রোণাচার্য বললেন, তোমার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি।
আমি চমকে উঠলাম ভীষণ। তবে সেই চমকানো নিজের ভেতরে রাখলাম। ধীর পায়ে কদলিবৃক্ষের দিকে এগিয়ে গেলাম। একটি পত্রের অগ্রভাগ কেটে আনলাম। গুরুর পায়ের কাছে রাখলাম। ওই পায়ের কাছেই হাঁটু গেড়ে বসলাম। কোমর থেকে টাঙ্গিটি বের করলাম। বিনা দ্বিধায় বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্তন করলাম। পত্রভাগে রাখলাম। গুরুদেব আর তিলার্ধ সময় অপেক্ষা করলেন না। সশিষ্য পেছন ফিরলেন।
আমি তাকিয়ে দেখলাম—ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য শূদ্র একলব্যের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে অপসৃয়মাণ হচ্ছেন। তীর নিক্ষেপ করার জন্য বা অসি চালনার জন্য ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি যে অপরিহার্য! সেটি কেড়ে নিয়ে শূদ্র বংশের উদীয়মান যোদ্ধাকে ধ্বংস করতে পেরে দ্রোণাচার্যের সারা অবয়বে তখন তৃপ্তির অপার উপস্থিতি।
আমি কী করলাম তখন, কী ভাবছিলাম?
কদলিপত্রের অগ্রভাবে স্থিত কর্তিত আঙুলটির দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। আঙুলটি তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আঙুলটির চারপাশে থকথকে রক্ত তখন। আর আমার ডান হাত থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরে ঝরে মাটি ভিজে উঠছিল। আমি আমার হাতের দিকে তাকাইনি, তাকিয়ে থেকেছিলাম ওই আঙুলটির দিকে। ওই আঙুল যে আমার সর্বস্ব। আমার সব কীর্তির কারিগর। ওই বুড়ো আঙুলটির কল্যাণেই তো আমার সব অর্জন। ওটি না থাকলে তো আমি ধনুতে টঙ্কার দিতে পারব না। ওটা না থাকা মানে এই পৃথিবী থেকে একলব্য নামের যোদ্ধাটির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়া।
না না, তখন আমার মধ্যে বিষাদ বা বিপন্নতা কাজ করছিল না। আমার মধ্যে তখন ঘৃণা আর ভক্তির দ্বন্দ্ব চলছিল। গুরু দ্রোণাচার্যের প্রতি যে আমার অচলা ভক্তি। সেই শ্রদ্ধার্হ মানুষটি কেন আমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি কেটে নিলেন। তিনি তো মহান মানুষ। তিনি কেন মদ ও মাৎসর্যে প্ররোচিত হলেন? আবহমান কাল ধরে উঁচু গোত্রের মানুষরা শূদ্রদের নরাধম ভেবে এসেছে, তার দ্বারাই তো তিনি প্রণোদিত হয়েছেন আমার আঙুলটি কেটে নেওয়ার জন্য।
হঠাৎ আমি চিৎকার করে উঠলাম, হে গুরুদেব বলে যান—আজ থেকে আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করব, না ঘৃণা করব?
আমার এই আর্তচিৎকার সমস্ত বনভূমির বৃক্ষে বৃক্ষে প্রতিধ্বনি তুলল। জানি না, আমার জিজ্ঞাসা দ্রোণাচার্যের কান পর্যন্ত পৌঁছল কি না!