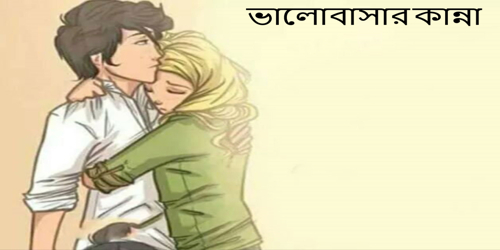রঙের ভীষণ ঝরঝরে বাসটা আমাকে চরম বিস্ময়ের মুখোমুখি নামিয়ে দিয়ে গেল । বেশ দূরে বাসটাকে এখনও দেখা যায়, লাফিয়ে-লাফিয়ে যাচ্ছে, টলমলে পেছন দিকটা পরদার বুকে ছবি কাঁপার মতো। আমি রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বাসের ড্রাইভার কিংবা কনডাক্টরদের একমুহূর্ত সময় নেই নষ্ট করার। স্টপেজে নেমেই চমকে গেলাম, ভুল জায়গায় নামিয়ে দিল ভাবছি, বললাম–আরে-আরে, এ তো রাহীপুর নয় ! ছোকড়া হেলপার বাসের দরোজায় ঝুলে থেকে বলল– বাস কি জঙ্গলের মধ্যে যাবে, একটু হাঁটলেই তো রাহীপুর।
সামনে খানিকটা হেঁটে গেলাম। এখনও অচেনা লাগছে সবকিছু। রোদ একেবারে বুক চিতিয়ে দিয়েছে, বাতাস শুকননা, যেদিকে তাকাই কোনও কূলকিনারা নেই। আমি বাতাস শুকে দেখলাম। বাতাসে রাহীপুরের গন্ধ ভেসে বেড়াত। কিন্তু না, এখন বাতাস শূন্যতার মতো গন্ধহীন। হাঁটতে-হাঁটতে মোটামুটি একটা হিসেব করি পেছনে তাকিয়ে। দু’বছর বড় অল্প সময়, এতটা বদলে যাওয়া সম্ভব নয়। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। প্রথমটায় সন্দেহ ছিল, কিন্তু বাসের হেলপার কেমন সহজে নামিয়ে দিয়ে। গেল। আজকাল নাকি বাস চলছে হরদম। অথচ দু’বছর আগে এসব কিছুই ছিল না। জিপে এসেছিলাম দল বেঁধে। আতঙ্কজনক নীরবতাকে চিরে চিরে জিপ এগিয়ে যাচ্ছিল। মনে হয়েছিল নীরবতারও নিজস্ব আওয়াজ আছে। এবড়ো-থেবড়ো অনির্দিষ্ট অসমতল রাস্তা, জিপের অবস্থা ছিল টালমাটাল। এখন টান-টান চাদরের মতো রাস্তা বিছানো।
রাস্তা পাকা হয়েছে বাসে উঠে শুনেছি, তবু সেই আগের মতো ভেবেছিলাম। পাকা রাস্তার পাশে-পাশে সেই কাঁচা রাস্তা, বড়-বড় গাছ, কাঁপা-কাঁপা পাতায় বাঁশির সুর, দু’পাশে দীর্ঘ উঠে যাওয়া বাঁশঝাড়, মন কেমন করে দেওয়া ঘুঘুর ডাক। ওসব আমার চোখের সামনে দিয়ে সার বেঁধে দ্রুত চলে গেল। চোখের সামনে এখন ঝাঁঝাঁ রোদ, শুকনো বাতাস, আর কিছু নেই। বেশ অনেকটা হেঁটে এসে মনে হল এদিকটায় একটা বিলের মতো ছিল। বুলা নাম দিয়েছিল ঝিলিমিলি ঝিল। বিলটা এখন মজে-হেজে গেছে কিংবা বুজিয়ে দিয়েছে। সেখানে এখন রাস্তা। মাছরাঙার বদলে বিরাট-বিরাট সব ট্রাক যেন উড়ে যাচ্ছে। তাদের দ্রুত গতি দেখে খুব ভয় হয়। হঠাৎ তেজি বোমার মতো আওয়াজে নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে যায় ।
প্রবল উৎসাহ এভাবে চলে আসায় নিজেকে হঠাৎ বোকা-বোকা মনে হল। বেশ খানিকটা পথ হেঁটে এসে চোখে সব কিছু বেশ কিছুটা সয়ে এল। এখন যেন কিছু-কিছু চিনতে পারছি। সার বাঁধা দীর্ঘ এলাকা ব্যাপী গাছ ছিল অনেক, সব কেটে ফেলেছে। দু’বছর আগে ছায়া দিয়েছিল আমাদের। ধু ধু মাঠ পড়ে আছে। বড় চড়া রোদ। হাঁটতে ক্লান্তি লাগছে। ঘণ্টাখানেক আসার পর পেছনে ফেলে আসা নগরীকে এখন মনে হচ্ছে প্রচণ্ড এক রণক্ষেত্র। আর আমি রণক্ষেত্র-পলাতক নিঃশেষিত এক সৈনিক। ফিরে আসছি। এই পর্যন্ত ভেবে ঘাসহীন খোলা মাঠে হাঁটতে-হাঁটতে আমার হাসি পেল।
গেল সপ্তাহে সম্পাদক সাহেব ডাক দিয়েছিলেন। তিনটে মাস পাক্কা কিছু না করার পর চাকরি এই পত্রিকা অফিসে। রোজকার দশটা পত্রিকা থেকে আমাদেরটা ভিন্ন। রোববার সন্ধ্যায় বের হয়। ছাপিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারি না। বৃদ্ধ সম্পাদক এ ব্যাপারে অভিজ্ঞজন, চটকদার সব খবর আর ফিচার ছাপা হয়। মাঝে-মাঝে আজব ধরনের এমন সব লেখা যা মানুষের মনের গভীরতা দিনদিন হরণ করে, এ ছাড়াও বিখ্যাত রমণীর গোপন জীবনী ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়, লেখা হয় ফ্রি-লাভ সম্বন্ধে, ইয়থ ফ্রাস্টেশন, ভায়োলেন্স, উইচ-ক্রাফট, মেয়েদের ইমপ্রেস করার কৌশলাদি। এছাড়া থাকে রাজনীতি, কারেন্ট-এ্যাফেয়ার্স, রেপ-কেস বৈজ্ঞানিক কাহিনী ইত্যাদি। দু-একটা ভারিক্কি প্রবন্ধ ছাপিয়ে বিদগ্ধ মহলেও তাক লাগানো হয়েছে। এবার আমার ওপর পড়েছে ফিচার-সংগ্রহের ভার । সম্পাদক ডেকে বললেন—দেখো, একবার রাহীপুর থেকে ঘুরে এসো। বছরখানেক হল যান্ত্রিক মানুষ তৈরির কারখানা চালু হয়েছে, এতদিনে কাজ বুঝি পুরোদমে চলছে। দু’একটা ছবিসহ একটা ফিচার ছাপতে পারলে বাজিমাৎ। যেদিন বললেন তার পরদিন কাজে ব্যস্ত থেকে দ্বিতীয় দিন রওনা দিলাম। আমার সারা শরীর টানছিল রাহীপুর। ভেতরে-ভেতরে চঞ্চল হয়ে পড়েছিলাম। মনের মধ্যে লাফাচ্ছিল উদ্দাম কোনও হরিণী। দু’বছর আগে দলবেঁধে পিকনিকে এসেছিলাম রাহীপুরে । উজ্জ্বল ঝকঝকে রোদে লাবণ্যময়ী রমণী রাহীপুর। দু’বছর আগের এক ধরনের আচ্ছন্নতা তখনও ছিল।
এখন এই কঠিন রাস্তা, তীব্র রশ্মির মতো রোদ পেরিয়ে যেতে-যেতে ভীষণ দমে গেছি ভেতরে-ভেতরে । আদিগন্ত বর্ণহীন। কিছু নজরে পড়ে না, যান্ত্রিক মানুষ তৈরির কারখানাটা আর কত দূর? আমার যদিওবা তার প্রতি কোনও আকর্ষণ নেই। রাহীপুরের প্রতি যে তীব্র লোভ ছিল তা উবে গেছে। রাহীপুর এখন ভীষণ উদোম। চোখে পীড়া দেয়।
হাঁটতে-হাঁটতে মরা বাতাসও ঘাম ধরিয়ে দিল। ইতস্তত হাঁটা বাদ দিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম জায়গাটা। এক পলক আমাকে দেখে নিয়ে লোকটা রোবট কারখানার দিকে আঙুল উঁচিয়ে দিল। আর একটা শূন্য মাঠ পেরিয়ে ওপারে। রাস্তার এককোণ পেরিয়ে আবার মাঠের হলুদ হয়ে আসা ঘাসে পা রাখলাম। চারদিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। না, কিছুই পরিচিত মনে হল না। মাঠের ডানধার ঘেঁষে ‘বিপদজনক’ লেখা বিদ্যুতের মিটার বক্স। পরপর তিনটে বিদ্যুতের তারবাহী উঁচু থাম। গোছা-গোছা তার ভাসতে-ভাসতে অনেক দূর চলে গেছে। মিটার বক্সের ধার ঘেঁষে অল্প এগিয়ে চোখ তুলতেই শরীরে আচমকা যেন বিদ্যুৎ আঘাত করল। অনভিজ্ঞের প্রথম চুম্বনের মতো আমার বুকের ভেতর শব্দ বাজছে দ্রুতলয়ে। অল্প দূরে সেই বাড়িটা, দেখলেই মনে হয় উড়ে যাবে, উড়ে যাবে। ঠিক বাড়ি নয়, খড় দিয়ে তৈরি আধো-ভাঙা ঘর। দু’বছরে কিছু খড় উড়ে গেছে আর বাকিগুলো আরও কালচে হয়েছে। গতবার পিকনিকে এসে লুকোচুরি খেলার সময় বুলা লুকিয়ে ছিল এই ঘরটায়। এই এতদিনেও তেমনি উদ্দেশ্যহীন টিকে আছে হয়তো শুধু আমার জন্যে। হঠাৎ আমি সেই পুরনো গন্ধ টের পেলাম, এই ক্লান্ত ঘরের আশেপাশে তা ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমি একধরনের আত্মীয়তা বোধ করলাম। এখন এই সৃষ্টিছাড়া পরিবেশের মাঝখানে ঘরটার কী বৈসাদৃশ্য। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। রাস্তার লোকজন আমাকে হয়তো পাগল ভাবছিল । কিন্তু আমি সেই বটগাছটার জন্যে চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম। খুব বিরাট বটগাছ। অল্প দূরেই ছিল। কিন্তু এখন আমার চোখের সামনে কোনও বটগাছ নেই। এখন চারদিক সমান। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর গাছটার নীচে ছায়ায় বসেছিলাম। সুদূর থেকে ভেসে আসা শান্ত বাতাস ছিল। শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলেছে। একটা বিদ্যুতের থাম বোধ হয় সেখানে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে। আশেপাশে কোনও সবুজ দৃশ্য নেই। গতবার শুনেছিলাম এখানে পিকনিক স্পট হবে। নগরীর মানুষ ক্লান্ত হলে, এখানে এসে ক্লান্তি জুড়োবে। তা আর হল কই ? নগরী তো ওই হা করে এগিয়ে এল! এখনও মনের ভেতর রঙিন। আবরণে জড়ানো গতবারের কথা; পিকনিক শেষে সবই যখন ফিরে যেতে ব্যস্ত তখন প্রায় সন্ধ্যা, বুলা আর আমি গিয়েছিলাম বটগাছের ওপাশে। … জেদাজেদিতে বুলা দ্বিতীয়বার বলেছিল ‘ভালোবাসি’। সন্ধ্যার ম্লান আলোয় বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে আলতোভাবে ঠোট ছুঁয়েছিল। লালচে আলো তখন আমাদের জড়িয়ে যাচ্ছিল। ফিরে আসার সময় বুলার মন কী খারাপ ! আমরা সবাই অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম। বুলাকে রুমালে চোখ মুছতে দেখে বলেছিলাম— কাঁদছ কেন, আবার তো আসব।
আগে জানলে আসতাম না। রাহীপুরের প্রতি যে তীব্র ভালোবাসা আমার জন্মেছিল, আচ্ছন্ন হয়েছিলাম তা আমার অটুট থেকে যেত। এভাবে আশাভঙ্গ হওয়াটা বড় দুঃখের।
দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞেস করে পথটা আবার জেনে নিলাম। নিরাসক্তভাবে হেঁটে গেলাম। স্বাদহীন, গন্ধহীন খানিকটা পথ অতিক্রম করতেই প্রথমে চোখে পড়ল সিমেন্ট রঙের কালো বাড়িটা। কারখানা সন্দেহ নেই। বিশ্রী কালো ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। অবশিষ্ট গাছের পাতাগুলোও হলুদ হবে, খসে-খসে পড়বে। … বটগাছের নীচ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা এদিকটায়ও এসেছিলাম। বড় গাছের শিকড়ে দাঁড়িয়ে বুলা আর আমি হাতে হাত রেখে সূর্যাস্ত দেখেছিলাম। বড়-বড় গাছের সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো, ও-রকম আর কেউ দেখতে পাবে না।
কী অফুরন্ত গতি ছিল সবটায়।
আশেপাশে দ্রুত আরও কারখানা উঠে যাচ্ছে। চতুর্দিক শূন্য হয়ে যাবে। এখন কারখানা হচ্ছে, দোকান বসবে, বাজার; মানুষ এসে ভিড় বাড়াবে। মানুষের চোখে হিংসা, হাতে ধ্বংস ঝলসে উঠবে। মানুষ নিজেকে লুকোবে— আর সবাই তখন দুঃখী হবে। চাঁদে মানুষ পা দিল, এক বন্ধু তখন বলেছিল— দেখেছো, একটা কবিতা লিখব প্রেমিকার মুখ নিয়ে তা-ও নষ্ট করে দিল। সে নেহাতই ঠাট্টা ছিল। আমরা খুব হেসেছিলাম। এখন মনে হল এভাবে জীবনের সবটা দখল করে নেওয়ার কী দরকার।
পৌঁছে গেলাম আরও সিকি মাইল পর। সাদা রঙের বিরাট দোতলা বাড়ি। কাঁটা তারে আবৃত। ফটকে ‘প্রবেশ নিষেধ’ ঝুলছে। দু’জন প্রহরী দাঁড়িয়ে। পরিচয় আর অনুমতিপত্র দেখিয়ে ঢুকে পড়লাম। সিমেন্টে বাঁধা টানা রাস্তা পেরিয়ে ঢুকলাম একটা বড় ঘরে। প্রায় শূন্য ঘরে একপাশে ডেস্ক রেখে বসে আছে একজন। আমি এগোতেই দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল । কথা বলল না, দৃষ্টিটাও বড় অদ্ভুত, ভাবলেশহীন মুখ। আমি আমার এখানে আসার কারণ জানাতেই খটাখট সুইচ টিপে গেল। তারপর মাথা নুইয়ে দরোজা দেখিয়ে দিল।
গাঢ় নীল রঙের স্যুট-পরা সৌম্যদর্শন একজন বসে। ফিক্ করে তার সারামুখে হাসি ছড়িয়ে গেল। ঘরের ফলকে দেখে এসেছি ‘তত্ত্বাবধায়ক’ । ফলক না-দেখলে অন্য কিছুও ভাবা যেত। বললেন— আপনার জন্যেই অপক্ষো করছি, ঠিক সময়মতো পৌঁছতে পারেননি। সুইচ টিপে দু’বোতল ঠাণ্ডা পানীয় আনতে বলে একটা চার্ট দেখতে দেখতে বললেন— এক মিনিট। একটু পর পানীয় এল। রিসিপশন ডেস্কে যে-লোকটা বসেছিল, সেরকম চেহারার এক লোক নির্বিকারভাবে দু’জনের সামনে দু’টো বোতল আর গ্লাস রেখে চলে গেল। | পানীয়ের বোতল টেনে নিতে-নিতে তত্ত্বাবধায়ক সাহেব বললেন— আমার নাম তরফদার, আহমেদ তরফদার। বাইরের ফলকে দেখেছেন বোধ হয়? আমি মাথা নাড়লাম। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন— বাইরে থেকে দেখেছেন তো কারখানাটা, কেমন লাগল? আমি তার হাসির প্রত্যুত্তর দিলাম। জবাব দিলাম অন্যভাবে বেশ গম্ভীর আর প্রাণহীন মনে হল। ভদ্রলোক এবারও হাসলেন (হাসিটা বুঝি বাতিক) প্রাণহীন ? অথচ ঠিক প্রাণ-না হলেও ও-রকম কিছু একটা আমরা এখানে বানাচ্ছি বটে। আবার সেরকম হাসি। হাসি থামিয়ে সোজাসুজি আমার দিকে তাকালেন– ঘুরেফিরে দেখার ইচ্ছেটা আপনার এখন প্রবল বুঝতে পারছি, আর দেরি করাব না। সুইচ টিপে কাউকে কিছু বলে আমার দিকে ফিরলেন– লোক ডেকে পাঠালাম, আপনাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাবে। তবে তার আগে একটা কথা বেশ নির্বিকারভাবে তিনি বললেন- রিসিপশনের লোকটা আর যে-লোকটা একটু আগে আমাদের পানীয় দিয়ে গেল, দু’জনেই এই কারখানায় তৈরি রোবট, কথা অবশ্য বলতে পারে না।
আমার একবার মনে হল আমার শরীর শিরশির করছে। কিন্তু পরমুহুর্তেই মনে হল, না, বেশ স্বাভাবিক আছি। আমি যেন এরকম কিছু শোনার জন্যে প্রস্তুতই ছিলাম। দু’কারণে এ রকম হতে পারে। রাহীপুরের শোচনীয় অবস্থা আমার মন খারাপ করে দিয়েছে, তাই কথাটা গায়েই লাগল না, কিংবা অভাবনীয় বিস্ময়ে মানুষ খুব একটা বিস্মিত হয় না বলে।
আমাকে শান্ত দেখে তরফদার সাহেব কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। পেছনের দরোজায় আওয়াজ পেলাম। আমার বয়সী, এক-মাথা উঁচু হবে আমার চেয়ে, আমার পাশে এসে দাঁড়াল । আমার দিকে অবশ্য তাকিয়ে নেই, তরফদার সাহেবের দিকেও নয়। মাছের চোখের নিশ্চল দৃষ্টি নিয়ে ভাবলেশহীন মুখে কোথায় যে তাকিয়ে, বোঝার উপায় ছিল না। তরফদার সাহেব গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন- আমার ছেলে। ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন জিয়া, ভদ্রলোক ‘রোববার’ থেকে এসেছেন। কাগজে আমাদের কারখানা সম্বন্ধে লিখবেন, ইতিহাস জানিয়ে দাও আর কারখানাটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাও। স্বাভাবিকভাবে আশা করেছিলাম এবার সে আমার দিকে ফিরবে, মাপা হাসির সঙ্গে হাতও বাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু ওসবের ধার দিয়েও গেল না। দরোজার দিকে এগিয়ে আমার দিকে সোজা ফিরে তাকাল— আসুন। লোকটা আমাকে আসুন বলল, কিন্তু চোখে কোনও দৃষ্টি আছে বলে মনে হল না। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে উঠতে-উঠতে পকেট থেকে নোটবই আর বলপেন বের করলাম। ক্যামেরার খোলস ছাড়ালাম। রাহীপুর একাই দেখব বলে সঙ্গে একজন ক্যামেরাম্যানও আনিনি, অতিরিক্ত ফিল্মও এনেছিলাম রাহীপুরের জন্যে।
লোকটা আর ফিরে তাকাল না। ঠাণ্ডা পা ফেলে হাঁটতে লাগল। বিরাট হলঘর পাশে ফেলে দোতলার সিঁড়ির মুখে হঠাৎ দাঁড়াল। শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল— আপনার এই কারখানার হিস্ট্রি জানা দরকার? হ্যাঁ— বললাম। সিঁড়ি পেছনে ফেলতে-ফেলতে জিয়া গলা খুলল— প্রথম প্রস্তাব উঠল ১৯৬৬ সালে। এ-হাত ও-হাত হয়ে ফাইলটা ৪ বছর ৭ মাস ২১ দিন চাপা পড়েছিল। তারপর আবার জোর আলোচনা উঠল। … বিদেশী দু’টো রাষ্ট্র আমেরিকা আর জাপান এগিয়ে এল। কারখানার কাজ আরম্ভ হল ১৯৭২ সালের ১৩ই আগস্ট, বেলা পাঁচটায়। জাপান এখন পর্যন্ত রোবট তৈরিতে পৃথিবীতে শীর্ষ স্থানীয়। তাদের বিজ্ঞানীর সংখ্যা এখানে নয়জন। রোবট তৈরী আরম্ভ হয়েছে ১৯৭৩ সালের ২১ শে মার্চ থেকে। আমাদের অগ্রগতি সম্বন্ধে …। আমি লিখে কুলিয়ে উঠতে পারছিলাম না। যন্ত্রের মতো অবিরাম বলে যাচ্ছে, থামছে না, ঠেকছে না; সন-তারিখ হুবহু মনে আছে। বলার ভঙ্গি শরীর শীতল করে দেওয়া নিরাসক্ত ধরনের, শ্রোতার প্রতি খেয়াল নেই। দম-দেওয়া পুতুলের মতো বলে যাচ্ছে-তো-যাচ্ছেই। গুছিয়ে অবশ্য বলছিল। আমি বললাম একটু আস্তে, পয়েন্টগুলো টুকতে তবে সুবিধে হয়। লোকটা ফিরে তাকাল না, অল্প সময় নিয়ে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করল। তারপর থেমে থেমে বলে গেল বাকি ইতিহাস। কিন্তু অভ্যেসটা বুঝি প্রকৃতিগত। তার গলার স্বর ক্রমশ দ্রুত হয়ে এল।
সব মিলিয়ে কারখানাটা অদ্ভুত। বিরাট-বিরাট সব কাণ্ড-কারখানা। একের-পর-এক ঘর পেরিয়ে এসেছি। সব যন্ত্রপাতি আর রোবটে পরিপূর্ণ। প্রতি ঘরে ভিন্ন-ভিন্ন বিস্ময় জমে আছে। আশ্চর্য রকমের প্রোগ্রেস। কিছু রোবট নিজেরাই ভ্রক্ষেপহীন কাজ করে যাচ্ছে। কিছু জমা হয়ে আছে, বিক্রি হবে। আর এত যন্ত্রপাতি শুধু যন্ত্রপাতি আর কলকব্জা। এখানে-ওখানে বোতাম আর সুইচ, বোতাম আর সুইচ। এটা টিপলে ওটা হয়, ওটা টিপলে এটা হয়। মাথা ঝিমঝিমিয়ে দেওয়ার মতো ব্যাপার। মানুষের কাজ কী আশ্চর্যজনকভাবে কমে গেছে।
সিগারেটের ইচ্ছে জেগেছিল ভীষণ। সিগারেট-কেস থেকে একটা তুলে নিয়ে দ্বিতীয়টা জিয়ার দিকে এগিয়ে দিতেই সে বলল— আমার সিগারেট দরকার নেই। চমকে উঠলাম। এই ধরনের প্রত্যাখানের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়। কী সহজে বলে দিল আমার সিগারেট দরকার নেই। দরকার না থাকলে লোকে হেসে ‘না’ বলে। কিন্তু এ কী কথার ধরণ ! একবার মনে হল সাধারণ ভদ্রতাটুকু জানা নেই। আবার অভদ্রই বা বলি কীভাবে, সাফ জবাব। নাকি বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ? প্রথম থেকে দেখছি বাইরের আর দশটা মানুষের সঙ্গে কী প্রবল বৈসাদৃশ্য ! হাঁটাচলায়, কথাবার্তায়, সমগ্র অবয়বে। কিছুটা আহত আর অপমানিত হলেও লোকটাকে নিয়ে বিস্ময় আমার বেড়ে গেল।
ঘুরতে-ঘুরতে আমি বিস্মিত হচ্ছিলাম এই ভেবে, মানুষ এখানে বেঁচে আছে। কীভাবে ? বাহ্যিক দিক দিয়ে বেঁচে থাকতে হলে কী-কী জিনিসের দরকার তা আমার জানা না-থাকলেও বুঝতে পারছিলাম এখানে তার অনেক কিছু নেই। ভেতরে আলো জ্বলছে কৃত্রিম ফ্যাকাশে, সূর্যের আলো ঢোকার কোনও উপায় নেই। দু’দণ্ড কেউ কোথাও দাঁড়াল না, একসাথে দু’জনে কখনও কোনও কথা বলছে না, ইয়ার্কি আর গানের সুর ভাজা তো দূরের কথা। কী অজাগতিকভাবে সবাই হেঁটে যাচ্ছে। সবার কী ভীষণ অনাসক্ত ভাব। নিজে যে আছে সেই অনুভূতিও যেন কারও নেই। সবাই যেন হাসি-ঠাট্টা, প্রেম-ভালোবাসা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-ইচ্ছের অনেক উর্ধ্বে।
লোকটা সম্বন্ধে আমার অন্যরকম ধারণা জন্মাচ্ছে। ইতিমধ্যে বেশকিছু ছবি তুলেছি। খুব একটা ভালো হাত আমার নয়; ফিল্মের শেষের দিকে এসে লোকটাকে বললাম- আপনার একটা ছবি তুলব। সে কিছু বলল না। আমার দিকে একবার তাকিয়ে আগের মতো হাঁটতে লাগল। সুন্দর একটা স্পট খুঁজে নিলাম। রোবটগুলো প্রায় সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যেখান থেকে বেরিয়ে এসে সার বেঁধে অন্য ঘরে চলে যাচ্ছে—সেখানে দাঁড়াতে বললাম লোকটাকে।
অনেকে ছবি তুলতে বললে দলাপাকায়, কেউ দাঁত দেখায়, কিংবা কেউ গম্ভীর হয়ে যায়, সহজে যেতে চায় না— এ এক ধরনের ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স। লোকটার মুখে কোনকিছুর চিহ্ন নেই। জায়গা দেখিয়ে দেওয়া মাত্র সহজে সার বেঁধে বেরিয়ে আসা রোবটগুলোর পাশে এসে দাঁড়াল। ডিসট্যান্স-এপ্যারচার এইসব ঠিক করে নিলাম, ছবিটা নিখুঁত করব। আসলে লোকটা আমাকে চুম্বকের মতো টানছিল। তার সবকিছু সহ প্রবল নিরাসক্ত ভাবটাও আমি ক্যামেরার মধ্যে আনতে চাচ্ছিলাম। ‘ভিউ’তে চোখ রেখে বেজায় চমকে গেলাম। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশেই লাইন ধরে একটা-দু’টো করে রোবট বেরিয়ে আসছে। আমি চাচ্ছিলাম একটা রোবট বেরিয়ে ঠিক যখন তার পাশে এসে দাঁড়াবে আমি সাটার টিপব। খুব জমকালো ছবি হবে ধারণা ছিল। কিন্তু সাটার টিপতে গিয়ে চমকে উঠে থেমে গেলাম।
এতক্ষণ এই আশ্চর্য লোকটার সঙ্গে থাকার পর আমার মনে হল— এ মানুষ তো ?
সাটার না- টিপে মারাত্মক ভুল করেছি, নইলে ‘কোন্টা রোবট’ এই জাতীয় ক্যাপশনে ছবিটা ছাপিয়ে পাঠকদের ধাঁধাঁয় ফেলতে পারতাম ! না, সবদিক দিয়ে মিল নেই। শুধু চোখের দৃষ্টি আর মুখের ভাবে কী অদ্ভুত মিল। পিছনের ঘটনাগুলো আমার দ্রুত মনে পড়ল। সবকিছু মিলিয়ে আমি অনেকটা নিশ্চিত হলাম, লোকটা হয়তো মানুষ নয়। বিশ্বের সর্বাধুনিক কোনও রোবট হতে পারে ! বিজ্ঞানের কোনও বিস্ময়কর সৃষ্টি, এই সমগ্র কারখানার সুপারিনটেনডেন্ট জাতীয় কিছু হবে সে। সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সারভিস দিচ্ছে। আসলে প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত লোকটার কথাবার্তা ভাবভঙ্গি চালচলন চোখের দৃষ্টি নিরাসক্ত ভাব— এই সবকিছু মিলিয়ে লোকটাকে আমি যান্ত্রিক মানুষ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছিলাম না।
আমি বুঝতে পারছিলাম আমার পা কাঁপছে। আমার নার্ভ বড় দুর্বল— এ-কথা অনেকেই বলেছে। লা তো প্রথমবার ঠোট ছুঁয়ে আস্তে করে বলেছিল— ‘তুমি কাঁপছ।’ তবে এ ব্যাপারটায় বুলাও চমকাত। কিছু-কিছু ব্যাপার ঘটে যা দেখে সবাই চমকায়। আমি বুঝতে পারছিলাম কঠিন এক জেদ আমার ভেতরে ক্রমশ জায়গা জুড়ছে। লোকটা কিংবা যন্ত্রটাকে বাজিয়ে দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছবার প্রবল ইচ্ছে আমাকে আঁকড়ে ধরল।
আবার ঘুরেফিরে দেখতে লাগলাম একবার দেখা জায়গাগুলো। সাংবাদিকতায় ঢুকে বেহায়ার মতো অনর্গল কথা বলা শিখেছি আর যে-কোনও লোকের সঙ্গে ভাব করে নেই সহজে। কথা বলতে লাগলাম। এরকম লোকের সঙ্গে অবশ্য কথা এগোয় না। প্রয়োজনহীন খুচরো কথাও সে এখনও বলেনি। খুব কমন আলোচনা মেয়েদের প্রসঙ্গ তুললাম, ‘আপনাদের এখানে কোনও মেয়ে কর্মচারী নেই’ এই প্রশ্ন করে। আমাকে একবারেই থামিয়ে দিল ছোট ‘না’ উত্তর দিয়ে। আরও কতক্ষণ মেয়ে প্রসঙ্গ মুখে রাখলাম। দু’টো চমৎকার জোক বললাম মেয়েদের নিয়ে যা আমাদের পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। কিন্তু তার কানের লতি, নাকের ডগা, চোখের ভ্রু কিংবা ঠোঁটের কোণে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। পছন্দ না-হলেও অনেকে হাসে বা গম্ভীর হয়। একতরফা অনেক কথা বলে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার দিকে ঝুঁকলাম। বাঙালি মাত্রই রাজনীতিজ্ঞ— এরকম প্রবল বিশ্বাস আমার ছিল। অথচ আমার সেই বিশ্বাস ভেঙে দিয়ে লোকটা তেমনি নির্বিকার রয়ে গেল। জেদ তখন আমার আরও চেপে বসেছে। জিজ্ঞেস করলাম— দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? সিঁড়ি বেয়ে আমরা নামছিলাম, লোকটা শান্তভাবে বলল— এ ব্যাপারে আমার কোনও ধারণা নেই। আমি বলে যেতে লাগলাম—মাত্র এই কদিনে কী বিস্ময়কর প্রোগ্রেস আপনাদের ! দেশের সব জায়গায় আপনাদের মতো লোক থাকলে দেশের চেহারাটাই পাল্টে যেত। সাংবাদিকরা যত রকম তোষামোদ করতে পারে, আমি তার সবকিছু প্রয়োগ করলাম। কিন্তু আমার তোষামোদ তার মুখে-চোখে কোনও উজ্জ্বল আভা আনল না। সে-রকম ফ্যাকাশে, বর্ণহীন, অনুজ্জ্বল রয়ে গেল তার মুখাবয়ব। আমি মরিয়া হয়ে পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে গেলাম. আচ্ছা, এত যে আপনাদের প্রোগ্রেস, আপনাদের রোবটগুলো আর তাদের কাজকর্ম তো দেখলাম। অদ্ভুত, ইউনিক। একেবারে মানুষের মতো। তা, আপনারা আরও অগ্রসর হওয়ার জন্যে কী করেছেন ? কোনও পরিকল্পনা কি হাতে আছে, যেমন ধরুন ঠিক মানুষের মতো, বা ঠিক আপনার মতো কোনও রোবট আপনারা বানাতে পারবেন ?
আমি প্রশ্ন শেষ করে খুব সহজ হয়ে গেলাম, যেন অনেকক্ষণ পর স্বস্তি পেয়েছি। বড় করে নিশ্বাস ফেলে তার দিকে তাকালাম। অথচ সে তেমনি বলে গেল। যেন তৈরি উত্তর—ঠিক মানুষের মতো রোবট বানানোর কথা আমরা ভেবেছি, ড. ব্রুশে আসবেন জুন মাসের সাত তারিখে। তিনি এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ।
আমি একরাশ অক্ষমতা আর অসাফল্যের মধ্যে তলিয়ে গেলাম। কূলহীন, কিনারাহীন হয়ে মনে হল কিছু পারিবারিক প্রশ্ন করলে কেমন হয়। সে সুযোগ পেলাম না। মৃদু একটা রিনরিনে শব্দ তার দিক থেকে ভেসে এল। আলগোছে পকেট থেকে ছোট একটা যন্ত্র বের করে কানে পাতল অল্পক্ষণ। আমার দিকে ঘুরে বলল— তরফদার সাহেব ডাকছেন। | আমি ফিরতে-ফিরতে সবকিছু পরপর সাজিয়ে নিচ্ছিলাম। ভাবলেশহীন মুখ। নিশ্চল দৃষ্টি। শরীরের রঙ বর্ণহীন। কথাবার্তা। কথা বলার ভঙ্গি। স্মরণশক্তি। নির্বিকার নিরাসক্ত ভাব। চাঁচাছেলা উত্তর। বোধহীন, কোনও কৃত্রিমতা নেই। মানুষের মুখে যে ছাপ থাকে, যেমন শোক-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-প্রীতি, আনন্দ-ভালোবাসার কোনও ছাপ নেই মুখে। আমার বিপক্ষে ছিল দু’টো বাধা। প্রথমত, সে কথা বলছে। এ বাধাটাকে সরালাম এভাবে বিজ্ঞানের সে এক উজ্জ্বল আবিষ্কার। বিজ্ঞান আজ বিস্ময়ের-পর-বিস্ময় সাধন করছে, সুতরাং ‘টকিং রোবট’ বানানো খুব অভাবনীয় কিছু নয়। দ্বিতীয়ত, তরফদার সাহেব তাকে ছেলে পরিচয় দিয়েছিলেন। আমার মনে হল এটা নিতান্তই হাস্যকর বাধা। আমি এ বাধা অতিক্রম করলাম এভাবে— এটা স্বাভাবিক ব্যাপার, মানুষ তার প্রিয়-পাত্রকে ছেলে বলে পরিচয় দেয়। হয়তো সে তরফদার সাহেবের বহু চেষ্টা, বহু, পরিশ্রম আর বুদ্ধির ফসল। সুতরাং তাকে ছেলে বলা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধছিল। তাকে দেখতে দেখতে আমি তত্ত্বাবধায়কের ঘরে ফিরে এলাম। আমার তুরুপের তাস তখন তরফদার সাহেব।
বিরাট এক চার্ট থেকে মুখ না-তুলেই জিজ্ঞেস করলেন– কেমন দেখলেন? আমি বলতে চাচ্ছিলাম- অদ্ভুত। কিন্তু আমাকে সে সুযোগ না দিয়ে তিনি মুখ তুললেন সত্যি কথা বলতে কি জানেন, এতদিন হয়ে গেছে কারখানা চালু হয়েছে, সেই উদ্বোধনী দিনে সাংবাদিকরা এসেছিলেন। তারপর আর কেউ দেখতে-জানতে, পাঠকদের জানাতে এলেন না। আপনিই প্রথম। আজকের দুপুরের খাবারটা এখানেই সেরে যান। আমি ‘হ্যাঁ’ বলব না ‘না’ বলব ভাবছিলাম। তিনি বললেন—‘না’ বলবেন না যেন, সব রেডি হয়ে আছে।
খেতে-খেতে তরফদার সাহেব নানা মজার কথা বলছিলেন। দু’টো ম্যাজিক দেখালেন। কারখানা সম্বন্ধে বলছিলেন। আমি একবার লোকটার (কিংবা যন্ত্রটার) কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে কথার তোড়ে ভেসে গিয়ে ভাবলাম, খাওয়ার পরেই সুস্থির হয়ে জেনে নেব। এবার রোবট সম্বন্ধে খুব অবাক-করা কথা বললেন। আমি অবাক হইনি। মনে হচ্ছিল আসল জিনিসটাই ধরে ফেলেছি, তরফদার সাহেব হয়তো আমার বুদ্ধির দৌড় পরীক্ষা করে দেখার জন্যে জিয়া নামের যন্ত্রটাকে আমার সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন।
খাওয়ার পর হেসে বললাম– তরফদার সাহেব, আপনার চালাকি আমি ধরে ফেলেছি। তিনি মুখ তুললেন, আমি বললাম— ভেবেছিলেন মানুষের মতো রোবট পাঠিয়ে আমাকে ধাঁধাঁয় ফেলবেন, পারেননি। তিনি উৎসুক হলেন— মানে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কী বলছেন। আমি তার গম্ভীর মুখ দেখে হেসে ফেললাম আপনার ছেলে বলে পরিচয় দিয়ে যাকে আমার সঙ্গে পাঠালেন, সে যে একটা রোবট তা জানতে আমার বাকি নেই।
আমি আশা করেছিলাম তার মুখের হাসি। চুপ করেছিলেন, হঠাৎ কাঁপতে আরম্ভ করলেন ভীষণভাবে। ধরা পড়ে নার্ভাস হয়ে গেলেন ? কাঁপতে-কাপতে তিনি মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতো উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে খুব চমকে দিয়ে টেবিলের ওপর প্রবল হাতের আঘাতে চারদিক কাঁপিয়ে বললেন—স্টপ ইট, হি ইজ মাই স্যন, মাই ওন স্যন । তারপরই বসে পড়ে বা হাতে মুখ ঢাকলেন।
আমি প্রথমটা কিছু বুঝিনি। কিছুক্ষণ পর টের পেলাম আমার পা কাপছে। কাঁপুনি ক্রমশ উঠে এল। প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে আমি নিঃশব্দ বসে থাকলাম। অনেকক্ষণ পর তরফদার সাহেব মুখ খুললেন—আপনাকে আমি প্রথমেই বলে দিয়েছিলাম, যেন ভুল না করেন, তবু ভুল করলেন। তার গলার স্বর জড়িয়ে যাচ্ছিল।
আমি বসে থাকলাম। জিয়া নামের লোকটাকে যখন রোবট ভেবেছিলাম তখন কি জানতাম এর চেয়েও বড় বিস্ময় আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তরফদার সাহেব ভাঙা গলায় বললেন— সবাই ভুল করে, যে দেখে সেই। আমি অনেকক্ষণ পর কথা খুঁজে পেলাম— মানে আপনি বলছেন, জিয়া আপনার ছেলে? তিনি আগের মতো রাগলেন না, শান্তভাবে বললেন– হ্যাঁ আমার ছেলে, দাঁড়ান ওকে ডেকে পাঠাই। আমি কিছু বলার আগেই তিনি সুইচে হাত দিলেন।
জিয়া এসে পৌঁছলেই তরফদার সাহেব বললেন— বসো। জিয়া বসল। তেমনি। কোনওদিকে দৃষ্টি ছিল না। তরফদার সাহেব একবার আমার দিকে চাইলেন- দেখুন তো ভালো করে। আমি দেখলাম, কিন্তু আমার কিছু বলার ছিল না। হঠাৎ করে তিনি গলার স্বর গভীরে নামিয়ে নিলেন— আপনাদের আর দোষ কী, ওকে দেখে ভুল তো করবেনই। আমি থেমে থেকে সাহস জোগাড় করে বললাম– ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন?
বুঝতে পারছেন না ?
আমি অস্পষ্টভাবে মাথা নাড়লাম।
তার গলার স্বর যেন কোনও গভীর থেকে ভেসে আসে—আমার ছেলে দিন-দিন …
আমি ভুলে গেলাম আমার পা কাঁপছে, আমি বললাম-কেন?
এবার তিনি ম্লান হেসে ফেললেন— বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে ? বলুন তো আমার না, হয় অভ্যেস হয়ে গেছে, কিন্তু আপনি এই কারখানায় কতদিন থাকতে পারবেন। আমি বললাম আমার তো দম বন্ধ হয়ে আসছিল।
জিয়ার ব্যাপরটাও সে-রকম, দম বন্ধ হয়ে গেছে। যন্ত্রপাতি ওকে ক্রমশ নিজেদের দলে টেনে নিচ্ছে। জানেন— তরফদার সাহেব থামলেন না– ওর কোনও দুঃখ নেই, ভালোবাসা নেই, কাঁদে না–হাসে না, আর, আর আমাকে বাবা বলে ডাকে না।
তরফদার সাহেব চেয়ারে ভেঙে পড়লেন, তারপর হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন— আপনাকে কী বলব, গত মাসে ওর মা মারা গেল, ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম। কতক্ষণ মাকে দেখল চাদর সরিয়ে। তারপর ছোট ভাইবোনদের। তারপর বলল— আমি এখন কারখানায় যাবো আমার হাত খামচে ধরে তিনি বললেন কিন্তু আমি তো ওর বাবা, আমি তো চেষ্টা ছাড়তে পারি না। বিয়ে দিয়েছিলাম পরিচিত এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু ওর অবহেলা মেয়েটাকে চরম অপমানই করেছে। কারখানা থেকে সরিয়ে রেখেও লাভ নেই। চলে আসে। আর কোথায় সরাব বলুন, কোথায় সরাব?
তরফদার সাহেব চেয়ারে ফিরে গেলেন শান্তভাবে। ঘরের ভেতর নীরবতা নিজেকে বিছিয়ে দিল। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে তরফদার সাহেব ভাঙা গলায় মুখ খুললেন— আমরা কোটি-কোটি টাকা ঢালছি, হাজার বিজ্ঞানীকে জড়ো করেছি, দিনরাত কাজ করে চলেছি কারণ আমরা ঠিক মানুষের মতো রোবট বানাতে চাই। কিন্তু সাংবাদিক সাহেব, মানুষ যে ক্রমশ…। তিনি কথা শেষ করতে পারলেন না, গলার স্বর বুজে গেল।
আমি জিয়ার দিকে তাকালাম। সে তাকিয়ে আছে। কিন্তু কোনদিকে, আমি বুঝতে পারলাম না ।