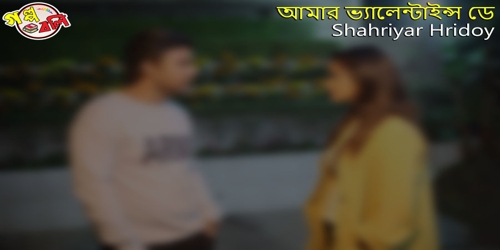তখন আমি বেশ ছোট, ফাইভে পড়ি। ১৯৯৩/৯৪ সালের কথা। আমাদের পাশের বাড়িতে একটা দরিদ্র পরিবার ছিল। দরিদ্র বলতে একেবারেই দরিদ্র কিংবা দরিদ্রও নয়, দারিদ্র সীমার নিচে বাস করত ওরা। ওরা সবদিক থেকেই গরীব ছিল। নিজেদের জমিজমা বলতে শুধু ঐ বাড়ীটাই ছিল। বাড়ীটা ছিল জসীম উদ্দিনের আসমানীদের বাড়ীর মতই। একচালা একটা খড়ের ছাউনির বাড়ী, মাঝখানে একটা চৌকির মতো। পাট খাঠির বেড়া।
সব দিক থেকে তারা গরীব থাকলেও একটা দিকে ছিল সবার চেয়ে এগিয়ে। তা হচ্ছে ছেলে মেয়ে। ‘মুখ দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি’ এই নিতীতে বিশ্বাসি বাড়ীর কর্তা হারুন চাচা মোট ছয় ছয়টা সন্তান জন্ম দিয়েছিলো। সবচেয়ে বড় মেয়ে আসমার আর আমার বয়সের পার্থক্য ছিল এক মাস ঊনিশ দিন, একথা মাকে অনেকবার বলতে শুনেছি। আশ্চর্য্যরে বিষয় এই যে, ছেলে মেয়েগুলোর চেহারা সুরত ছিল খুবই সুন্দর। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল ওদের চোখগুলো। আর গায়ের রঙ? গান কবিতা উপন্যাসে বলে না দুধে আলতা? ওদের গায়ের রং দেখে মনে হতো এমন রং দেখেই মনে হয় তারা লিখেছে ‘দুধে আলতা গায়ের বরণ’।
ছেলে মেয়েগুলো অত সুন্দর সুরত পেয়েছে তাদের মায়ের কাছ থেকে। তাদের মা খুবই রুপবতি এক মহিলা। দেখলে সবারই চোখ ধাঁধিয়ে যেত। গায়ের রংটা ছিল এক কথায় সোনালী। অমন গায়ের রং মানুষের হয় আমি আগে দেখিনি। আমরা তাকে ডাকতাম রাঙা চাচী বলে। মাঝারি উচ্চতার রাঙা চাচির স্বাস্থ ছিলো একটু বাড়ন্ত, আর বুক দেখলে ঐ কিশোর বয়সেই আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন করত। আমি এত বড় হয়েছি আজ পর্যন্ত এরকম গরীব মানুষের এত রুপ আর কোথাও দেখিনি। গরীবদের যে চেহারা খারাপ হয় তা বলছি না। সৃষ্টিকর্তা তাদের যত সুন্দর করেই পাঠাক না কেন অযত্নে আর অবহেলা আর পুষ্টি হীনতায় তাদের সুন্দর চেহারা আর সুন্দর থাকে না। এক সময় নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কি কারণে জানি না ওদের চেহারা একটুও নষ্ট হতো না বরং দিন দিন আরো ফুটে বের হত। আমাদের গ্রামের সুন্দর চেহারার উদাহরন ছিল এই রাঙা চাচি আর তার ছেলে মেয়েরা। কি রকম বলি; হয়তো কেউ বিয়ে করেছে, মা চাচীরা সবে মাত্র বউ দেখে এসে মন্তব্য করতে বসেছে। কেউ একজন বলল ‘বউ তো খুবই সুন্দর। এক্কেবারে পরীর মতন।’
কেউ একজন হয়তো বলল ‘যতই কও, হারুনের বৌয়ের ধারেকাছেও না।’
কিংবা কারো বাচ্চা হয়েছে। একজন বলল ‘ছোট্ট মনু তো দেখতে মাশাল্লাহ ভালাই হইছে। মনে হয় এক্কেবারে ইংরাজের বাচ্চা।’ সাথে সাথে পাশ থেকে কেউ হয়তো বলে বসল ‘তয় হারুনের মাইয়া পোলাগুলার মত না।’ এরকম হাজারো উদাহরণ।
রাঙা চাচী আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই ভাতের মাড় নিতে আসত।মাকে দেখতাম সবসময় একটা পরিস্কার পাত্রে মাড় গালত। ওরা মাড় ভাতের বিকল্প হিসেবে খেত।
হারুন চাচা ছিল বারো মাসের কাশের রুগি। কাশি বলতে যেই সেই কাশি না, একেবারে ভয়ানক হাঁপানি। প্রতি বৃহস্পতিবার হারুন চাচাকে ঝাড়ার জন্য আমাদের এলাকার বিশিষ্ট ওঝা লেহাজ শরিফ আসত। সে এক বিশাল ডাকসাইটে ওঝা। তার কৃত্তিকলাপ আমরা শুনতাম কিংবদন্তি হিসেবে। শুনেছি ডাক্তার যে রুগিকে মৃত বলে বাড়ি পাঠিয়েছে এমন রুগিও নাকি লেহাজ শরীফের এক ঝাড়ায় উঠে বসে বলেছে ‘হাঁসের গোস্ত দিয়া ভাত খামু’। তবে তার এমন মোজেজা কখনও নিজের চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি।
আমরা ছোটরা সব সময় সেই ‘ঝাড়া’ দেখতাম চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। কখনও হাতে একটা মড়া মানুষের হাড্ডি নিয়ে, কখনও আস্ত খুলি নিয়ে কি সব মন্ত্র পড়ত আর ঝাড়তো। যে সব মন্ত্রের বেশীর ভাগই ছিলো অশ্লীল আর অদ্ভুৎ ভাষার। নানা রকম কটু কথা বলে ভূত প্রেত পিঁশাচ, অশুভ আত্মাদের তাড়াতে হতো। শুনেছি ঐ হাড্ডি জারজ সন্তানের হাড্ডি খুলি। ভাদ্র মাসের অমাবশ্যার রাতে লেহাজ শরিফ নিজে উলঙ্গ হয়ে সংগ্রহ করেছে। ঐ হাড্ডি খুলিতে আছে ভুত তাড়ানোর বিশেষ ক্ষমতা। আমার চাচাতো বোন আকলিমা লেহাজ শরিফের বেশ কিছু মন্ত্র শুনে শুনে মুখস্ত করে ফেলেছিলো। লেহাজ শরিফ দেখতে ছোটখাট একজন মানুষ। থুতনির গোড়ায় এক গোছা দাঁড়ি, মাথায় পাগড়ী, চোখে সুরমা আর গায়ে কড়া আতর দিয়ে আসত সে। প্রতি বৃহস্পতিবার সে রোজা থাকত। রোজা মুখে ঝাড়ফুক করলে নাকি বেশী কাজ হয়। বৃহস্পতিবার যে লেহাজ শরিফ শুধু হারুন চাচাকেই ঝাঁড়ফুক করত এমন না। সে এসে বসত আমাদের পাশের বাড়ীর হাকিম চাচার উঠানে। অধিক জমির মালিক হবার কারণে হাকিম চাচা এমনিতেই একটু মোড়ল সভাবের ছিলেন।
গাঁয়ের মানুষেরা নানা সমস্যা আর উপঢৌকোন নিয়ে আসত। কারো বাচ্চা বিছানা প্রস্রাব করে, কারো বাচ্চার দাঁত উঠতে দেরী হচ্ছে, কারো হাঁপানি, কারো পেট খারাপ- সকল রোগের স্পেশালিস্ট ছিলো এই লেহাজ শরিফ। একেবারে ঘামাচি থেকে শুরু করে ক্যান্সার পর্যন্ত সব রোগীর চিকিৎসাই সে করত। কোন রোগী যদি কোন কারণে সুস্থ হয়ে যেতো তবে তার ক্রেডিট পেতো লেহাজ শরিফ আর সুস্থ না হলে সবাই বলত ‘আল্লাহ্ তার বান্দারে আরো কষ্ট দিয়া পরীক্ষা করতেছে।’ কিন্তু লেহাজ শরিফই ছিলো সকলের সকল রোগের একমাত্র চিকিৎসক। দশ গ্রামে ভরসা। বৃহস্পতিবার সকাল দশটা এগারটার দিকে সে আসত খালি হাতে। সারাদিন ঝাড়ফুক করে সন্ধায় রাজকীয় ইফতার আর রাতে ভুরিভোজ শেষে সারাদিনের আয়রোজগার কম করে হলেও দুইটা বড় বড় ঝুড়ি নিয়ে কারো সহায়তায় বাড়ি ফিরত। ঝুড়িতে থাকতো চাল ডাল, মুরগী, হাঁস, লাউ, ডিম, আতপ চাল একরকম নানা ধরনের উপহার।
হারুন চাচা রাঙা চাচী দুজনেই আমাদের বাড়িতে মাঝে মাধ্যে টুকটাক কাজ বাজ করত। কোন কোন দিন বড় মেয়ে আসমাকেও নিয়ে আসতো সাথে করে। আসমার ডাক নাম ছিল বুড়ি। ও নাকি ছোট বেলা থেকেই বুড়া বুড়া কথা বলতো। সবাই আদর করে ‘বুড়ি’ ডাকতে ডাকতে বুড়ি ওর ডাক নামে পরিনত হয়েছে। আর তা নিয়ে ওর কোন আক্ষেপ আছে বলে মনে হয়নি কোনদিন।
বুড়াবুড়া কথা বললেও ওকে আমার বেশ ভাল লাগত। দেখলে মনে হতো সিনেমার ছোট নায়িকা। ওর মাথার চুল থেক শুরু করে পায়ের নখ পর্যন্ত সবকিছুই দেখতে অনেক সুন্দর ছিলো। কেন জানি না ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেই আমার ভালো লাগত। ওকে আমি একটু কিছু হলেই চিমটি কাটতাম। জবাবে বুড়িও আমাকে চিমটি কাটতো। তবে ও যখন চিমটি কাটত তখন খুব সুন্দর করে একটা হাসি দিত, যার আশাতেই ওকে চিমটি কাটতাম। যেদিন শুধু আমিই চিমটি কাটতাম ও কাটত না সেদিন আমার ভীষণ খারাপ লাগতো। মাঝে মাঝে ওর সাথে আমি খেলতাম। তবে সব সময় না। ও আর আমি আবার এক স্কুলেই একই ক্লাসে পড়তাম। ও যে দিন স্কুলে যেতনা সেদিন বিকেল বেলা আমাদের বাড়ী আসতো আমার কাছে পড়া জানতে।
আমাদের বাড়ী থেকে স্কুল ছিল দেড় দুই কিলোমিটারের মত দূর। প্রায় সময়ই আমরা একত্রে স্কুলে যেতাম। স্কুলে যাবার পথে একটা যায়গা ছিল নাম ‘গলাকাটা জঙ্গল’। জায়গাটা আমাদের বাড়ী থেকে আধামাইলের মতো দূরে। দিনের বেলাতেও বেশ অন্ধকার থাকতো। আমরা ছোট বেলা থেকেই গলাকাটা জঙ্গল সম্পর্কে এত এত ভয়ঙ্কর কথা শুনেছি যে ও জঙ্গল নিয়ে কথা বলতেও ভয় হতো। দিনের বেলাতেও ছোটবড় কেউ ঐ জঙ্গললের পাশের রাস্তা ধরে একা হাঁটত না। শোনা যায় ১৯৭১ সালে প্রায়ই ঐ জঙ্গলের ধারের খালে অনেক গলাকাটা লাশ পাওয়া যেতো। তার পর থেকে জঙ্গলের নাম হয়ে যায় ‘গলাকাটা জঙ্গল’। নানা রকম ঘটনা দুর্ঘটনায় বিখ্যাত এই গলাকাটা জঙ্গল। এক সময় অল্প বয়সী মেয়েদের বিবস্ত্র বিক্রিত লাশ পাওয়া গেলো দুই তিনবার। শোনা যায় ‘নিশির ডাক’ পায় যাদের তাদেরকে এখানে এনে হত্যা করে খারাপ আত্মা। অন্ধকার এই গলাকাটা জঙ্গলে অনেক ভয়ানক কিছু আছে বলেই সবার দৃঢ় বিশ্বাস।
সেই গলাকাটা জঙ্গলের কাছাকাছি গিয়ে আমি ওর বই আমার স্কুল ব্যাগে ভরে নিতাম। পালা করে একদিন ও ব্যাগ নিত একদিন আমি। ঐ রাস্তাটা পার হওয়ার সময় ও শক্ত করে আমার জামা খামচে ধরত। আমার যে কি ভালো লাগত তা বলে বোঝানো মুসকিল। ক্লাস ফাইভে পড়া এক জোড়া ছেলে মেয়ে কতটুকুই বা বোঝে? কিন্তু আমরা বুঝতাম কারণ আমরা একটু বেশি বয়সেই লেখা পড়া শুরু করেছি। আমি যখন ফাইভে পড়ি তখন আমার বয়স কমপক্ষে বারো তের বছর। আমি বুঝতাম যে আমি বড় হতে শুরু করেছি। ক্লাস ফাইভের ফাইনাল পরীক্ষা এসে গিয়েছে। এক বিকেলে আমি নিজ উদ্যেগেই পড়ছি। বিকেল বেলা মা বাড়িতে থাকে না। এর বাড়ী ওর বাড়ী বেড়াতে যায় পান তামাক খেতে গল্প গুজব করতে। সাধারণত মা কাছে না থাকলে খুব একটা পড়াশুনার ধার ধারিনা। কিন্তু এখন পড়ছি। কারণ সামনে ফাইনাল পরীক্ষা এর কিছুদিন পরই আবার বৃত্তি পরীক্ষা। ছোট মামা কথা দিয়েছে ফার্স্ট হতে পারলে ঢাকা নিয়ে যাবে। ঢাকা কি একটা বেশ ভাল স্কুল আছে, সেখানে পড়াবে। বাবা বলেছে বৃত্তি পেলে সাইকেল কিনে দেবে। তাই মায়ের অনুপস্থিতেও বেশ পড়াশুনা করছি। আসর শেষ হয়েছে তাও আধা ঘন্টা। শীতকাল, চারিদকে কুয়াশা পরা শুরু করেছে। এমন সময় আসমা এলো। আজ ও স্কুলে যায়নি তাই পড়া জানতে এসেছে। আমি বাহিরে পড়ন্ত রোদের উষ্ণতায় পড়ছিলাম। আসমা সহ ঘরের মধ্যে চলে গেলাম। আসমা আর আমি পাশাপাশি বসে আছি। আসমা বই বের করে পড়া জেনে নিচ্ছে। আমি ঝুকে ওর আরো কাছাকাছি হলাম। হঠাৎ আমার শরীরের মধ্যে কেমন যেন শিহরন হল। ইচ্ছা হল আমি ওর আরো কাছে যাই। ওর শরীরের গন্ধ নেই। আমি আরো কাছে গেলাম। বেশ ভাল লাগল। হঠাৎ আমি কিছু না ভেবেই আসমাকে জড়িয়ে ধরলাম। কেমন একটা অদ্ভুৎ অনুভুতি হলো আমার। ও আচমকা ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়তে লাগল। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। আমার মনে হল ও ব্যাথ্যা পাচ্ছে। আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে বললাম ‘বুড়ি বড় হইয়া আমি তরে বিয়া করুম।’ আসমা শিশুর মত ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালো। আমি অবাক হয়ে গেলাম। তবে বেশ খুশি হলাম। এর পর ও বইখাতা গুছিয়ে চলে গেল। আমি বেশ ভয় পেলাম। কেন পেলাম বুঝিনি। প্রকৃতি মনে হয় সৃষ্টির শুরু থেকে এই সকল ব্যাপারে মানুষের মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। আসমা যাওয়ার সময় বলে গেল ‘তুই এহনও বড় হসনাই।’ বলেই ফিক করে হেসে ফেলল। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।
পরের দিনও আসমা আর স্কুলে গেল না। আমি বিকেল বেলা বসে রইলাম ও পড়া জানতে আসবে এই আশায়। কিন্তু আর এলো না। আমার বেশ মন খারাপ হল। তবে আমার ভয়ও হল। ও যদি আবার সব রাঙা চাচীকে বলে দেয়? তাহলে হয়তো রাঙা চাচী মাকে নালিশ দেবে। এরপর কয়েকদিন আমি রাঙা চাচীর সামনে পড়লাম না। কিন্তু আসমাকে দেখার জন্য মনটা কেমন জানি করতে লাগলো।
একদিন দুপুরে খাওয়া সময় মা বাবাকে বলল ‘আপনে একটু ভাত খাইয়া বুড়িগো বাড়ীতে যাইয়েন। হারুনের অবস্থা তো বেজায় খারাপ।’ বাবা বলল ‘ক্যান কি হইছে?’
‘আইজ পাঁচ দিন ধইরা বিছানা ছাইড়া উঠতে পারতাছে না। হাঁপানি তো আগে থাইক্যাই ছিল এহন নাকি কাশের লগে রক্ত পরে। আপনে ভাত খাইয়া একবার যান।’
‘আমি যাইয়া কি করুম? লেহাজ শরীফরে আইনা ঝাড়াইতে কও…’ বাবা একটু রাগ নিয়ে বলল। আমার বাবা গ্রাম্য ডাক্তার। সে এইসব ঝাড়ফুক দুই চোখে দেখতে পারেনা। দেখতে পারেনা ওঝা লেহাজ শরীফকেও। বাবা সবাইকে অনেক বুঝিয়েছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের মানুষের কিছু গোয়ার্তুমি আছে যা আমাদের দেশেকে এখনও অনেক পিছিয়ে রেখেছে। কোন শিক্ষিত মানুষ যদি কোন সুপরামর্শ দেয়, গ্রামের মানুষ তা কু পরামর্শ মনে করে। ভাবে এই শিক্ষিত মানুষটা আসলে আমার ক্ষতি করে সবকিছু হাতিয়ে নিতে চাচ্ছে। ফলে এই ওঝা ফকিরির বিরোধীতা করায় গ্রামে বাবার একটা বিরোধী পক্ষও রয়েছে। তার মধ্যে স্ব ঘোষিত মোড়ল হাকিম চাচাও একজন।
আমার বাবা পাশ করা ‘পল্লী চিকিৎক’। আমাদের এলাকায় সপ্তাহে একেক এলাকায় একেক দিনে বাজার বসে। বাবা প্রত্যেক বাজারের বড় বড় ফার্মেসিতে বসে রুগী দেখে। একেক রোগীর ভিজিট দশ টাকা করে। ছোট খাটো ফোঁড়া টোরা কাটা, পায়ের কাঁটা উঠানো, এমন কি কেউ মারামারি করে মাথা ফাটালে বাবা সেলাইও করতে পারে। সব মিলিতে বাবা পসার ভালো, আয় রোজগার খারাপ না। ফজলু ডাক্তার বললে এক নামে অনেকেই চেনে বাবাকে।
বাবা যখন যাচ্ছিল তখন আমি মাকে বললাম ‘মা আমিও যামু বুড়িগো বাড়ি।’
‘তুই কিল্লাইগা যাবি? তুই পড়তে বয়, পরশু পরীক্ষা।’
মায়ের গরম চোখ দেখে আমার বুড়িকে দেখার সাধ মিটে গেলা। হারুন চাচা সেই যে বিছানায় শুইল তারপর আর কবরে যাওয়ার আগে আর উঠতে পারেনি। দিন দিন অবস্থা আরো খারাপ হতে শুরু করল। আমি আসমাদের বাড়িতে শেষ পর্যন্ত যেতে পেরেছিলাম। মাঝে মধ্যে হারুন চাচার অসুখ দেখতে যেতাম। রাঙা চাচী হারুন চাচার পাশে সারাদিন বসে থাকতো। শেষ দিকে হারুন চাচার এমন অবস্থা হল যে প্রসাব পায়খানা সবই বিছানায় করতে শুরু করল। সন্ধ্যার পরে একদিন মায়ের সাথে গিয়ে দেখি আসমা সহ ওরা ছয় ভাই বোন গোল হয়ে বসে আছে। আর হারুন চাচা সমানে কেশে যাচ্ছে। রাঙা চাচী কতক্ষণ পর পর রসুন আর সরিষার তেল গরম করে হারুন চাচার বুকে মালিশ করে দিচ্ছে। আমি জানি সবাই না খেয়ে আছে। মা কিছু খাবার নিয়ে এসেছে। সবাই সেই খাবারের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। আসমা আমার সাথে কোন কথা বলেনি।
আমি ফার্স্ট হয়ে সিক্সে উঠেছি, বৃত্তিও পেয়েছি ট্যালেন্টপুলে। বাবা আমাকে একটা লাল রঙের সাইকেল কিনে দিয়েছে। আসামাও সিক্সে উঠেছে। কিন্তু ও নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে না। আমার কাছে মাঝে মধ্যে পড়া জানতে আসে। কেন জানি না আসমা এলে মা এখন কোন না কোন ছুতায় আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপরও আমাদের চিমটি বিনিময় হয় কথা হয় চোখের ইসারায়, সবার অগচরে।
একদিন বুড়ি আমার কাছ থেকে বাংলা দ্বিতীয় পত্র বইটা নিয়ে গেলো। যেদিন ফেরৎ দিয়ে গেলো সেদিন আমি বইয়ের মধ্যে হাতের লেখার খাতায় এক লাইনের একটা চিঠি পেলাম।
‘ঢাকায় গেলে আমাকে ভুলে যেও না।’
আমার বাবা গ্রাম্য ডাক্তার বলেই হয়তো তার ছেলেকে এমবিবিএস ডাক্তার বানানোর এতো ইচ্ছা। আমার মামা ঢাকায় থাকে। কি এক বড় সরকারী চাকরী করে। কথা ছিলো ফাইভের ফাইনাল পরীক্ষার পরেই আমাকে ঢাকায় নিয়ে যাবে। কিন্তু কোন এক সমস্যার কারণে হয় নি। মামা আসবে আমাকে নিয়ে ঢাকায় যাবে, আমি বড় স্কুলে পড়ব এ এক অন্যরকম আনন্দ! আমি আমার সে আনন্দের আগাম খবর দুয়েকবার আসমাকে বলেছি। তাই ও আমাকে এই এক লাইনের চিঠি লিখেছে। আমার জন্য ওর এ আকুলতায় আমার যে কি আনন্দ হলো বলে বোঝাতে পারব না।
রাঙা চাচীর সেই আগের রুপ অনেকটাই ম্লান হয়ে গিয়েছে। চোখের নিচ কালো হয়ে গিয়েছে। চোখ কোটোরে ঢুকে গেছে। নিশ্চই রাতে ঘুমাতে পারে না। সেদিন মাড় নিতে এসে মাকে বলছিল ‘ভাবী রাইতে একটুও চোখ বুজতে পারি না। মানুষটা সারা রাইত ধইরা খালি কাশে। মাইয়া পোলাগুলা না খাইতে পাইরা ট্যাও ট্যাও করে। কিযে করুম… বিষ খাইয়া মইরা যামু নাকি…..।’
‘কি সব আবোল তাবোল কথা কও বুড়ির মা? তুমি মইরা গেলে অগো দ্যাখবো কেডা?’
আমি বুঝতে পারি ওদের খুব কষ্ট হয়। কিন্তু আমি কি করব? আসমাকে দেখলে বড় মায়া লাগে। রাঙা চাচী যে কাজ কর্ম কিছু একটা করবে তারও সুযোগ নেই। দিন রাত হারুন চাচার পাশে পড়ে থাকে। প্রায়ই সবাই মিলে না খেয়ে থাকে। হারুন চাচা দিন দিন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে তার দিন ফুরিয়ে আসছে। যখন কাশি শুরু হয় তখন পাজরের হাড় সব কটা গোনা যায়। চিকিৎসা বলতে ঐ লেহাজ শরিফের ঝাড় ফুক। আর মাঝে মধ্যে বাবা গিয়ে একটু আধটু অষুধ পত্র দিয়ে আসে। তা খায় কিনা কে জানে?
বছরের মাঝামাঝি ছোট মামা ঢাকা থেকে এলো। আমাকে ঢাকায় নিয়ে যাবে। আমি এখন ঢাকায় গিয়ে কোচিং করব। ডিসেম্বরে ক্লাস সেভেনে ঢাকার ভালো স্কুলে ভর্তির জন্য। আমার বেশ আনন্দ লাগার কথা। কিন্তু কেন জানি আনন্দ লাগছে না। আমি যেদিন ঢাকায় যাব তার আগের দিন দিবাগত রাতে হারুন চাচা মারা গেলো। আমার আর ঢাকা যাওয়া হল না। আমি ভীষণ কষ্ট পেলাম। কিন্তু কষ্ট পেলে কি-ইবা করার আছে? রাঙা চাচী আছাড় খেয়ে কাঁদছে। রাঙা চাচীর জন্যও আমার বেশ কষ্ট হচ্ছে। আসমা সকালের দিকে বেশ কেঁদেছিল। এখন আর কাঁদছে না। গোমড়া মুখ করে বসে আছে। আমি সবার আড়ালে একবার আসমার কাছে গেলাম। আমাকে দেখেই হাউমাউ করে কেঁদে দিল। কেন জানিনা আমিও কেঁদে ফেললাম।
আল্লাহ তো সবই বোঝে। বুঝেও মানুষকে কেন এত কষ্ট দেয়? কি জানি আমি ছোট মানুষ আমি অত বুঝিনা। ইসলাম ধর্ম স্যার বলেছেন ‘আল্লাহরে নিয়া অত প্রশ্ন করবানা।’ আমাকে একদিন বেশ মেরেছেও প্রশ্ন করার জন্য। ঘটনাটা ছিল এরকম- স্যার বলছেন ‘এক ওয়াক্ত নামায না পড়লে দুই কোটি আটাশি লক্ষ বছর আল্লায় আগুনে পোড়াইবো।’
হঠাৎ আমি দাঁড়িয়ে বললাম ‘স্যার আপনে তো কইলেন আল্লাহ রহ্মানুর রহীম। দয়ার সাগর। তাইলে হে এক ওয়াক্ত নামাযের লাইগা তার বান্দারে অত কষ্ট দিব ক্যান? কেউ এক ওয়াক্ত নামাজ না পড়লে আল্লাহর ক্ষতি কি?’
সেদিন স্যার বেশ মেরেছিল ঠিকই কিন্তু আমার প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে নাই। তবে প্রশ্নটা আজও আমার মনে রয়ে গেছে।
আমাদের বাড়ী তখন ঢাকায় যাবার সবচেয়ে ভালো উপায় ছিলো লঞ্চ। আর বর্ষার সিজনে লঞ্চঘাটে নৌকা ছাড়া যাওয়ারও কোন উপায় ছিলো না। আমি লঞ্চ ঘাট যাওয়ার জন্য মামার সাথে রিজার্ভ নৌকায় উঠেছি। নৌকা ছাড়ার পর আমি ছৈয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার চোখ খালের পাড়ে। যদি আমাকে বিদায় দিতে আমার বুড়ি আসে? হঠাৎ করে দেখলাম একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমার বুড়ি চোখ মুছছে। আমার বুকটা কেমন হু হু করে উঠলো। আমার দেখে হাত নাড়িয়ে বিদায় জানালো। ইশারায় জানালো যেনো তাড়াতাড়ি ফিরি। আমি কান্না ধরে রাখতে পারলাম না। আমার নৌকা ভাটার টানে তর তর করে এগিয়ে চলছে লঞ্চ ঘাটের দিকে। আর পিছনে পড়ে আছে আমার মা, বাবা, বাড়ি, উঠান, সাইকেল, আমার শৈমব, কৈশর, আমার প্রেম- আমার প্রিয়তমা, আমার বুড়ি।
ঢাকায় মামার বাসায় গিয়ে জানলাম আমি যে স্কুলে ভর্তি হবার জন্য পড়াশুনা করছি মামি নাকি সেই স্কুলেরই টিচার। ফলে কোন কোচিং-এ আর ভর্তি হলাম না। মামা মামির কঠোর তত্বাবধানে পড়াশুনা শুরু হলো আমার। প্রথম প্রথম ঢাকায় মন টিকতো না। আমার একমাত্র মামাতো বোন আমার চেয়ে দুবছরের ছোট। আমার সাথে ভালো করে কথাই বলে না। অনেক কষ্ট হলো নিজেকে খাপখাইয়ে নিতে। ভর্তি হলাম ঢাকা আইডিয়াল স্কুলে। সব কিছু বেশ কড়াকড়ি। গ্রামের স্কুলের মতো না। নিজের স্বাধীনতা বলতে এখানে কিছুই নেই। সব ছেলেরা কেমন যেন অন্য রকম! আমি সবার কথাও ঠিক ভাবে বুঝি না! এমনকি আমার সব কথাও সবাই বোঝে না। ক্লাসে সবাই ‘বরিশাইল্লা খ্যাতার গাট্টি’ বলে ডাকে।
দিন শেষে আমার মনটা পরে থাকে আমার গাঁয়ে, আমার আমার কিশোরী প্রিয়তমা জুড়ে। আসমার কথা সারাদিনে ভুলতেই পারি না। কিন্তু সে কথা আমি কাকে কিভাবে বলব? একদিন ভাবলাম ওকে একটা চিঠি লিখি। কিন্তু কি ভাবে চিঠি ওর কাছে যাবে? আচ্ছা ওর জন্য আমার মনটা যেমন করে আমার জন্যও কি ওর মনটা এমন করে? খালি বাড়ি যেতে মন চাইছে। মামাকে বললে মামা বলে ‘দেরি আছে দেরি আছে।’ সাইকেলটাও পড়ে আছে বাড়ীর কোন এক অন্ধ কুঠুরিতে। বাড়িতে গেলে এবার আসমাকে পিছনে নিয়ে চালাবো। নদীর ধারে যাবো ওকে নিয়ে।
অবশেষে র্দীঘদিন পর ঈদের ছুটিতে মামা মামির সাথে আমার বাড়ী আসার সুযোগ হলো।
আমি যথেষ্ট খুশি হয়ে বাড়ীতে আসলাম। বেশ আনন্দ লাগছে। মনে হচ্ছে কত যুগ পরে যেন বাড়ী আসলাম! এতদিন কেউ আমাকে খাঁচায় আটকে রেখেছিলো, আজ মুক্তি হলো। আজ যে আমি আসব তা আসমা নিশ্চই মায়ের কাছে শুনেছে। ও কি আসবে না আমাকে দেখেতে? আমাকে চিমটি কাটতে? ও কি জানে যে টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে ওর জন্য আমি কি কি কিনেছি? রিক্সা থেকে নেমে বাড়ীতে ঢোকার পথে হঠাৎ আমি থমকে দাঁড়ালাম। হারুন চাচার কবরের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। সেখানে আর একটি নতুন কবর। কে মারা গেল নতুন করে? আমি ঢাকায় গিয়েছি পাঁচ-ছয় মাসের মত হবে। এর মধ্যে কে মারা গেল? আর মাও তো চিঠিতে কিছু লিখলো না। কে হতে পারে? আমি বাড়ীতে চলে এলাম।
মা আমাকে জড়িয়ে ধরে বেশ কিছু সময় কাঁদলেন। সাথে আমিও। ঢাকায় মামার বাসায় কত রাত ঘুমাতে পারিনি! খালি মায়ের কথা মনে পরত, আসমার কথা মনে পরত।
দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, বিকেল গিয়ে সন্ধ্যা। আমার প্রিয়তমার কোন দেখা নেই। ভাবলাম একবার যাব ওদের বাড়ীতে। কিন্তু তার আর দরকার হলো না। সন্ধ্যার কিছু পর আমি জানতে পারলাম আমার বুড়ির খবর, আমার প্রিয়তমার খবর। যে খবর জানার চেয়ে না জানাই বোধহয় ভালো ছিলো। হারুন চাচার কবরের পাশে নতুন কবরটা আসমার। আমার বুড়ির। যে আমকে ভালবাসত আর আমি এখনও ভালোবাসি।
আসমা মারা যাওয়ার ব্যাপারে গ্রামে দু’ ধরণের কথা প্রচলিত আছে।
একটা কথা এরকম- এক গভীর রাতে আসমা ‘নিশির ডাক’ পায় আসমা। প্রচলিত আছে নিশির ডাক যাকে ডাকা হয় সে ছাড়া অন্য কেউ শুনতে পারে না। সে রাতে নিশির ডাক পেয়ে আসমা কাউকে কিছু না বলে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। সেই ডাক কাল হয়ে ওর। পরের দিন সারা দিনে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সন্ধ্যায় লাশ মেলে গলা কাটা জঙ্গলে। পুলিশ এসে লাশ নিয়ে যায়। কাটা ছেড়া করে দুদিন পর পুলিশ এসে লাশ দাফন করে দিয়ে যায়। কেউ কারো নামে কোন অভিযোগ করেনি। পুলিশ বাদি হয়ে একটি অপমৃত্য মামলা রজু করে মাত্র। কিন্তু কেউ আর এ প্রশ্ন করে না যে আসমা যে ‘নিশির ডাক’ পেয়েছিলো তা অন্য মানুষ জানল কি করে?
আরেকটি কথা এরকম- নাসির নামে আসমার এক দূর সম্পর্কের চাচা আছে। হারুন চাচা মারা যাওয়ার পর নাসির এসে ঠাঁই নেয় আসমাদের বাড়ীতে। কেউ কেউ বলে আসমার সাথে সেই নাসিরের প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিলো তা থেকে শারিরীক। এক সময় আসমার পেটে বাচ্চা এসে যায়। যার জন্য আসমা আত্মহত্যা করেছে। আবার কেউ কেউ বলে নাসিরের সাথে আসমার নয়, রাঙা চাচীর প্রেম এবং শারিরীক সম্পর্ক হয় যা আসমা জেনে ফেলেছিল। এই জন্য নাসির এবং রাঙা চাচী দু’জনে মিলে আসমাকে খুন করে গলাকাট জঙ্গলে ফেলে রেখে আসে। শেষ কথাটা সত্যি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ আসমা মারা যাওয়ার কয়েক দিন পর নাসির রাঙা চাচিকে নিয়ে পালিয়ে যায়। শোনা যায় তারা এখন ঢাকায় একটি গার্মেন্টসে চাকরি করে সুখে শান্তিতে আছে। আর এদিকে তার ছোট ছোট সন্তানগুলি রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করছে। দোরে দোরে মানুষের লাথিগুতা খাচ্ছে।
ঈদ শেষে আমার ঢাকায় ফিরে যাবার দিন চলে এলা। আসমার জন্য মাঝে মধ্যে বুকের মধ্যে কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে। কারা মেরেছে ওকে? কি ভাবে মেরেছে? মরার সময় ও কি খুব কষ্ট পেয়েছে? আচ্ছা মরার সময় ওর কি আমার কথা মনে পরেছিলো একবারও? সবার চোখের আড়ালে মাঝে মধ্যে কাঁদি। ওকে আর কোনদিন দেখতে পারব না একথা মনে উঠলেই যে বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে তা কোনদিন বলে বোঝানো সম্ভব না।
পথঘাট শুকনা বলে লঞ্চঘাট যাওয়ার জন্য আমি রিক্সায় উঠে বসেছি। নীল পলিথিনে ঢাকা আসমার কবরটা দেখা যাচ্ছে। আমি ক্রমাগত চোখ মুচছি। মামা বলল ‘কি মাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না?’ আমি কোন জবাব দিলাম না। আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। আসমা কেমন আছে? ও কি বেহেস্ত পেয়েছে না দোযখ? ওর দোযখ পাওয়ার কথা না। ও নিশ্চই বেহেস্ত পেয়েছে।
এক যুগ পরের কথা…
আজ আমি একজন এমবিবিএস ডাক্তার। বিসিএস দিয়ে সদ্য নিজ থানায় পোস্টিং পেয়েছি। বারো বছর আগে আসমা কি কারণে মারা গিয়েছিল তা খোঁজার জন্য দারস্থ হলাম আমাদের সাথে বিসিএস পাশ করা পুলিশের অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার মুহিনের কাছে। আমি ওকে সব খুলে বললাম। ও আমার কাছে সময় চেয়ে নিলো। বলল ‘যদি ওর পোস্টমর্টেম হয়ে থাকে তবে অবশ্য-ই রির্পোট দেখানো যাবে।’
দিন পনের পরে মুহিন আমাকে ফোন করে থানায় যেতে বলল। দেখলাম আসমার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট। আসমাকে রেপ করা হয়নি। প্রথমে গলায় রশি পেচিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তার পর মুখে বিষ ঢেলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু সে বিষ পাকস্থলিতে পৌঁছায়নি। আমি জানতে চাইলাম ‘আচ্ছা ও কি প্রেনগন্যান্ট ছিলো?’
‘আরে নাহ্!’
আসমার মৃত্যুর পর ওর যারা স্বজন ছিলো যারা ওর খুনের জন্য মামলা করতে পারত তারা ছিলো ওর মা আর ওর দূর সম্পর্কের চাচা নাসির। কিন্তু আমার ধারণা ওই দুইজনই ওর খুনি। তারা কেন কেস করতে যাবে? লেহাজ শরিফ নাকি তখন ফতোয়া দিয়েছে এই মড়া নিয়া ঘাটাঘাটি করলে সবার নানা ক্ষতি হতে পারে। ফলে ভয়েও কেউ আগায়নি।
আমি মুহিনকে বললাম ‘আচ্ছা এই কেসটি এখন নতুন করে ফাইল করা যাবে না?’
‘অবশ্যই করা যাবে, কেন করা যাবে না? কিন্তু কে করবে কেস? এমন হাজারও খুন আছে যার কোন কেসই ফাইল হয় না। এটাও তেমন একটা কেস। কে কেস লড়বে বলুন?’
‘আমি। আমি কেস লড়ব।’
সেদিন আমি আসমার মা অর্থাৎ রাঙা চাচি আর নাসিরকে আসামি করে কেস ফাইল করে তবেই হাসপাতালে ফিরলাম। জানি আমার কষ্ট হয় হবে, নানা ঝামেলা পোহাতে হবে। কিন্তু আমি এই কেসের শেষ দেখতে চাই। এমন চলতে পারে না। খুন করে করে ভূতপ্রেতের নামে চলিয়ে দেয়া আর কত দিন? এ আঁধার দিনের অবসান হওয়া উচিৎ। মানুষ চাঁদে গিয়েছে সেই ১৯৬৯ সালে। এখনও কেন একজন ওঝা সকল রোগের চিকিৎসা করে বেড়াবে? কেন একটা জঙ্গলকে ঘিরে ইবলিশ শয়তানের ঘাড়ে দায় দিয়ে কিছু জানোয়ার খুন রেপ করে বেড়াবে? আমি হাসপাতালে ফিরে একটা এ ফোর সাইজের বের করে পল্লিবিদ্যুতায়ন বোর্ডে দরখাস্ত লিখতে বসলাম। আগে বিদ্যুৎ আসুক। দূর হোক আঁধার সবার আগে। নতুন ওঝা লেহাজ শরিফের ছেলে ইসমাইল শরিফের বিষয়টা কদিন পরেই দেখব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।