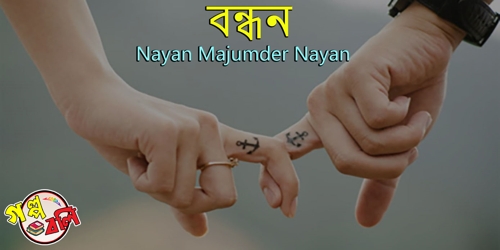মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়ানো জীবনে খুব কম হল না। আসলে খুব ছেলেবেলা থেকেই বাইরের প্রতি আমার ছিল অদম্য টান। একদিকে যেমন ছিলাম বইয়ের নিঃশব্দ পোকা, অন্যদিকে বিস্তৃত মাঠ-ময়দান, নদী-পাহাড়, জল-জঙ্গল, সর্বোপরি বিচিত্র বহুবর্ণ মানুষ আমায় দিত নিশির ডাক বারবার।
স্কুলের শেষদিক থেকেই সে-টানে উধাও হয়ে গিয়েছি এখানে-ওখানে। পড়তাম শ্যামবাজারের টাউন স্কুলে। বাবা ছিলেন ওই স্কুলেরই শিক্ষক। তিনি স্কাউট-দল পরিচালনা করতেন। তাঁর দলের সঙ্গেও বাইরে যাওয়ার সুযোগ ঘটেছে। হয়তো সেখান থেকেই পেয়েছিলাম বাইরের অমোঘ টান।
প্রথম কোথায় অভিভাবকদের বাদ দিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম? যতদূর মনে পড়ে মুর্শিদাবাদ। তখন কিন্তু মুর্শিদাবাদই আমাদের কাছে বেশ দূর ভ্রমণ। মনে আছে, সিরাজদৌলার কী একটা জীবনী পড়ে, একজন বন্ধুর সঙ্গে মাত্র দশ টাকা (তখন থেকেই আমি নিয়মিত টিউশন করি) পকেটে নিয়ে দিয়েছিলাম ভোঁ-দৌড়। বাড়িতে বলেছিলাম বারাসতে এক বন্ধুর মামাবাড়ি যাচ্ছি। সেই প্রথম নিজে ট্রেনে টিকিট কাটা। তখনও ভালো করে গোঁফ ওঠেনি, তবু গম্ভীরভাবে হোটেলের ঘরভাড়া করেছিলাম বহরমপুরে। মনে আছে, ভাড়া ছিল চারটাকা প্রতিদিন। বহরমপুর থেকে বাসে চেপে মুর্শিদাবাদ, আর নৌকোয় চেপে গঙ্গার ওপারে খোসবাগ। সেখানে রয়েছে, নবাবদের সমাধি। আলিবর্দি খাঁর কবরটা ফাটা, কেউ একজন বলেছিল, সিরাজ যখন পলাশির যুদ্ধের সময় মিরজাফরকে বিশ্বাস করে ভুল করেন, সেই সময় আলিবর্দি কবর থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন! সে এক রোমাঞ্চকর ভ্রমণ।
এভাবেই শুরু। প্রথম মেলা দেখি শ্যামবাজার-বাগবাজার অঞ্চলে রথের মেলা। নাগরদোলা, পাঁপড়ভাজা, তালপাতার বাঁশি আর অজস্র মানুষ। পুরো দিন দশেকের মেলা। আমরা বন্ধুরা মিলে যেতাম সেখানে। ধনী বাড়ির ছেলেরা আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে লাঠিলজেন্স চুষত, পাঁপড় খেত, ভেঁপু বাজাত। আমরা শূন্য পকেটেই ঘুরে বেড়াতাম।
সম্ভবত ১৯৮৪-৪৯ সালে কলকাতার ইডেন-গার্ডেন-এ দেখেছিলাম একটি একেবারে অন্য ধরনের মেলা। নাম তার ‘স্বদেশি মেলা।’ ভারতীয় ইতিহাসের নানা চিহ্ন দেখানো হয়েছিল সেখানে। রাণা প্রতাপের বর্ম আর শিরস্ত্রাণ দেখে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল, বেশ মনে আছে। দেখেছিলাম বিদ্যাসাগরের খড়ম। এরকম আরও অনেক কিছু। সে-মেলার একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে হেঁটে যেতেই অনেকক্ষণ লাগে। অতবড় মেলা কলকাতায় আর হয়েছে কি? ছোটবেলার স্মৃতিতে সব কিছুই বড় বড় মনে হয়। কলকাতা ময়দানে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন হত, তাও কম বড় নয়। এখনকার বইমেলা তো প্রকাণ্ড।
আমার জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। তা হলেও স্থায়ীভাবে থাকিনি সেখানে। বাবা কলকাতায় চাকরি করতেন। কলকাতাতেই তাই আমাদের সব শেকড়-বাকড়। দুর্ভিক্ষের বছরে বাবা আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দেশের বাড়িতে। যা হোক দুমুঠো খেতে পাব–এই ভরসায়। কিন্তু পাইনি। তাই বলা বাহুল্য, বাংলাদেশে ছেলেবেলায় কোনও মেলা-টেলা দেখার সুযোগ আদপেই আসেনি।
এখনও মনে পড়ে, ভারী সুন্দর একটা মেলা দেখেছিলাম দেওঘরে। পাহাড়তলিতে সে এক অনুপম আদিবাসী মেলা। পাহাড়-অরণ্যের দূর পথ ধরে দল বেঁধে হেঁটে আসছে অসংখ্য আদিবাসী–পুরুষ-রমণী, কচি-কাঁচা, বুড়ো-বুড়ি আদিবাসীদের কোনও দেবতার পুজো উপলক্ষেই বসেছিল সেই মেলা। আমরা কয়েকজন হঠাৎই পৌঁছে গিয়েছিলেন সেখানে। মুগ্ধ চোখে দেখেছিলাম মানুষের, প্রকৃতির আদিম সৌন্দর্য। শাল-পিয়ালের বন, সুঠাম স্বাস্থ্যের স্ত্রী পুরুষ, মাদলের বোল, সাঁওতালি নাচ-গান, একেবারে আক্ষরিক অর্থে মুগ্ধ করেছিল। নাচেও যোগ দিয়েছি তাদের সঙ্গে। কাঁচা শালপাতার ঠোঙায় হাঁড়িয়া পান সেই মেলার প্রধান আকর্ষণ। এরকম আদিবাসীদের মেলায় আরও গিয়েছি কয়েকবার। বিহারে, উড়িষ্যায় মধ্যপ্রদেশে। মধ্যপ্রদেশের বাস্তার জেলার দুর্গম অঞ্চলে দেখেছিলাম এক মেলা, যেখানে অনেক নারীপুরুষই প্রায় উলঙ্গ। অধিকাংশই খুব গরিব, সেইজন্যই জিনিসপত্রও অবিশ্বাস্য রকমের শস্তা, বেগুনের সের (তখনও কিলো হয়নি) মাত্র দশ পয়সা। হিসেব করে দেখলাম, একটি মেয়ে তার সব বেগুন বিক্রি করে মোট এক টাকা উপার্জন করবে। সেই একটা টাকাও সে মুরগি-লড়াইয়ের জুয়ায় বাজি খেলে হেরে গেল। তারপরেও তার মুখে সে কী খিলখিল হাসি। সর্বস্ব খুইয়েও যে মানুষ অমনভাবে হাসতে পারে, তা আর কোথাও দেখিনি।
কলেজজীবনে পৌষমেলায় গিয়েছি শান্তিনিকেতনে। তখনকার পৌষমেলা কিন্তু এখনকার মতো এত শহুরে সাজানো গোছানো হয়ে ওঠেনি। তখন সেখানে বীরভূমের লোকসংস্কৃতির স্পর্শ বেশ অনুভব করা যেত। আশ্রমিক সঙ্রে ব্রাহ্মসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত যেমন হত, তেমনই তার সঙ্গে সাঁওতালদের নাচ-গান, আউল-বাউলদের অনুষ্ঠানও ছিল জনপ্রিয়। পৌষমেলায় পরেও গিয়েছি অনেকবার। কিন্তু প্রথমবারের কথাই বেশি মনে পড়ে। ৯ পৌষ, মেলার শেষদিন, আধিবাসীদের জন্য বরাদ্দ, রাত্তিরবেলা মশালের আলোয় নাচ হত।
পৌষমেলায় দেখেছিলাম পূর্ণ দাস বাউলের পিতা নবনী দাস বাউলকে। একটা লম্বা আলখাল্লা পরে সারা মেলা প্রাঙ্গণে দাপটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পরিচিত-অপরিচিত যাঁর সঙ্গেই দেখা হচ্ছে, তাকেই তিনি ডেকে ডেকে দেখাচ্ছেন সে আলখাল্লা, ‘ওরে দ্যাখ-দ্যাখ, গুরুদেব দিয়ে গেছেন।’ খুব মজা লেগেছিল। এখন মনে হয়, সত্যি সেটা ছিল কত বড় পুরস্কার। তাঁর কণ্ঠে গান শুনেছিলাম ‘মন তুই পড় গা ইস্কুলে।’ মনে পড়ে, খুব মনে পড়ে।
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তো বাউলদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বাউল গানের তিনি ছিলেন পরম অনুরাগী। নবনী দাসের কাছে শোনা নানা গানের স্পষ্ট প্রভাব আছে তাঁর বাউলাঙ্গের গানে। লালন ফকিরের গানের খাতা রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করে নিজের সঙ্গে রেখেছিলেন, এমন একটা কথাও প্রচলিত আছে।
কলাভবনের ছেলেমেয়েদের অনুষ্ঠানও আমার সামনে সেই প্রথম রবীন্দ্রসংগীতের দরজাটি হাট করে খুলে দিয়েছিল। মধ্যরাতে কোপাই নদীর পাড়ে, বা রনরনে রোদ্দুরে খোয়াইয়ের সামনে বসে আমরাও হেঁড়ে গলায় গাইতাম, ‘আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।’ পৌষমেলাতেই শুরু হত অনেকের প্রথম প্রেমপর্ব। আলাপ হত অনেক নতুন মানুষের সঙ্গে। একবার নাগরদোলায় একটি অচেনা যুবতী বসেছিল আমার পাশে। সেটা যখন খুব জোরে ঘুরছিল, সে ভয় পেয়ে চেপে ধরেছিল আমার হাত। আমরা পরস্পরের নামও জানি না, অথচ হাত ধরাধরি করেছি। এরপরেই তার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল খুব। মেয়েটির গায়ের রং কালো, তার মুখ ও শরীরের গড়ন অপূর্ব, যেন কষ্টিপাথরের ভাস্কর্য। নামও কৃষ্ণা। কলকাতায় ফিরে যোগাযোগ করার জন্য সে তার ঠিকানা ও ফোন নাম্বার লিখে দিয়েছিল এক টুকরো কাগজে। আমার ফোন ছিল না, তাই কিছু দিইনি। সেই কাগজটি খুঁজে পাইনি। কী কষ্ট হয়েছিল সেজন্য! অনেক ছোটগল্প এরকম হয়। কিন্তু আমার গল্পটি অন্যরকম। প্রায় পাঁচবছর পর সেই ঠিকানা লেখা কাগজটা আমি খুঁজে পাই একটা বইয়ের ভাঁজে। তখন হাসি পেয়েছিল। এতদিন পর ফোন করার কোনও মানেই হয় না।
বীরভূমের কেঁদুলি-মেলায় গিয়েছি বারবার। ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেবের বাসস্থান কেন্দ্রবিন্দ্ব বা কেঁদুলি। এখন যার ডাকনাম, ভালোনাম জয়দেব কেঁদুলি। কিংবদন্তী যে, পৌষ-সংক্রান্তিতে গঙ্গা স্নান করলে পুণ্য হয়। কবি জয়দেব প্রতিদিন ভোরবেলায় বহুদূর পথ পায়ে হেঁটে গঙ্গাস্নানে যেতেন। সেবার পৌষ-সংক্রান্তির আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। খুব মনোকষ্ট তাঁর। এবার আর মকরস্নান করা হবে না। তখন রাতে স্বয়ং গঙ্গা তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, ‘এবার আমিই যাব তোর কাছে, অজয় নদের কদম্বখণ্ডীর ঘাটে। সেখানে স্নান করলেই গঙ্গাস্নানের পুণ্যি পাবি তুই।’
জয়দেব ভক্তকবি। তিনি সেবার অজয়েই মকরস্নান সারলেন। সেই থেকে অজয় পেয়ে গেল ধর্মীয় মহিমা। শুরু হল প্রতি বছর পৌষ-সংক্রান্তির দিন অজয় স্নানযাত্রা। বসল মেলা। গানের আসর।
কবির মৃত্যুর পর থেকে তাঁর বাসস্থান কেঁদুলি গ্রামে বসছে বিরাট মেলা। পৌষ সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু করে তিন দিনের এই মেলা সাধারণভাবে ‘জয়দেব-মেলা’ নামেই খ্যাত। বাংলাদেশের প্রাচীনতম মেলাগুলির মধ্যে অন্যতম। অবশ্য জয়দেবের জন্ম হয়েছিল ওড়িশায়, এমন একটি দাবিও আছে। জয়দেব শুধু সংস্কৃতই লিখেছেন, সুতরাং তিনি বাঙালি না ওড়িয়া, এ তর্ক অবান্তর।
পৌষ মাস বাঙালির কাছে বিশেষত গ্রামের বাঙালির কাছে এক বিরাট আনন্দের সময়। পৌষে কৃষকের ঘর ভরে যায় ফসলের হিল্লোলে। শ্রমের পর শ্রমের সাফল্য উপভোগের সময়
এই পৌষ মাস। এ-সময়েই বাংলাদেশের গাঁয়ে গঞ্জে শুরু হয় নানা মেলা ও উৎসব। ধর্মীয় অনুষঙ্গ থাকলেও এসবের মূল আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য এটাই। মানুষের হাতে থাকে অল্পবিস্তর পয়সাকড়ি। কেনা-বেচারও বড় সুসময় এই পৌষ মাস।
বীরভূমের কেঁদুলি মেলাও বস্তুত তারই উজ্জ্বল প্রকাশ। কেঁদুলির মানুষের কাছে তো বটেই, সারা বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, ২৪ পরগণা, হাওড়া হুগলি, এমনকী কলকাতার মানুষের কাছেও জয়দেব মেলা এক অমূল্য আকর্ষণের ব্যাপার। ধর্ম এবং আনন্দ এখানে ওতপ্রোত হয়ে যায়। তাই নানা জেলা থেকে, ভিনপ্রদেশ থেকেও আসেন অসংখ্য ভক্ত বৈষ্ণবের দল, আউল বাউল, সুফি-সহজিয়া, চাষি-মজুর, বাবু-বিবি বা অসংখ্য সাধু-সন্ন্যাসীর দল। নতুন শাড়ি জামা পরে কাঁধে বাচ্চা নিয়ে আসে মঙলির মা, লাঙলের ফলা বা জালের সুতো কাঠি কিনতে পরান মাঝি, নাগরদোলা বা ভানুমতির খেল দেখতে ঝলমলে ঝিমলি, সুবল বা বাবুলাল। আগে সার্কাস কোম্পানি, মিঠাই-মণ্ডা, চুলের ফিতে, কাঁচের চুড়ি, পুঁতির মালা, লোহার ড্রাম, কড়ি-বরগা, জানালা-কপাট, বাসনকোসন, হাঁড়িকুড়ি, ধামা কুলো-হাঁসমুরগি, নামাবলি, তাসের আসর, বহুরূপী কলার কাঁদি।
এইসব সাত সতেরো জিনিসপত্র নিয়ে মাইলখানেক জায়গায় এই মেলার বিস্তার। দূর মাঠের আলপথ দিয়ে সকাল থেকেই লোক আসছে অবিরাম। বাসগুলো ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসছে একেবারে মেলার বুকের ওপর। শীতে শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে গেছে ভাঙন-ধরা অজয় নদ। শীর্ণ নদী গরুর গাড়িতে পার হয়ে ওপার থেকে আসছে বর্ধমানের যাত্রীরা। আসছে খড় বোঝাই গরুর গাড়িও। মেলায় খড়ের চাহিদা। খড়ের বিছানাতেই তো রাত কাটাতে হয় মেলাযাত্রীদের। কাকভোর থেকে পুণ্যার্থীরা ঝুপ ঝাঁপ ডুব মারছে অজয়ের হাঁটু জলে। উত্তরে বাতাসে কনকনে ঠান্ডা, তবুও। তাল, তমাল আর শালবনের নীচে লুকিয়ে আছে লাল ধুলোর মেঠো পথ, অ্যাসফল্ট -এর কালো রাস্তা। দুপাশে বীরভূমের রুক্ষ বিষণ্ণ ফসলহীন মাঠ বিছিয়ে রয়েছে। আমরা কখনও বোলপুর, কখনও দুবরাজপুর, কখনও বর্ধমান হয়ে গিয়েছি জয়দেব মেলায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায় একসময় যেতেন ফি বছর।
মেলায় বাউলদের আকর্ষণটাই ছিল আমাদের কাছে মুখ্য ব্যাপার। বাউলরা আখড়া বানাতেন। এক-একটা আখড়ায় এক-এক বাউল এবং তাঁর সম্প্রদায়। প্রাণের গান গাইতেন তাঁরা গলা ছেড়ে। আমরা ঘুরে-ফিরে সব আখড়াতেই যেতাম, গান শুনতাম, খেতাম, শুতাম। আমাদের সঙ্গে দারুণ ভাব জমে গিয়েছিল তাঁদের। তখন মাইকের উৎপাত ছিল না। শহুরে মানুষরাও খুব কম যেতেন। তাই পরিবেশটা ছিল একেবারেই অন্যরকম–আদিম, গ্রামীণ। সেই পরিবেশে তিন দিনের জন্য আমরা একেবারে হারিয়ে যেতাম, ডুবে যেতাম। ভুলে থাকতাম আমাদের নাগরিক প্রেক্ষাপট। নদীতে স্নান করতাম, কোনও আখড়ায় ভাত খেতাম (এখনকার মতো ভাতের এত হোটেল তখনও হয়নি), রাতে ওই আখড়াতেই ঘুমোতাম, কিংবা জেগে থাকতাম। যেন তিনদিন আমরাও বাউলের সঙ্গে মিলে বাউলই হয়ে যেতাম। ওঁরাও কী করে যেন জেনে গিয়েছিল আমাদের কবি পরিচয়। আমাদের ‘বাউলবাবু’ বলতেন। কনকনে ঠান্ডায়, রাতভর আসরে-আসরে ঘুরে গান শোনা, গানের সঙ্গে গলা মেলানো বা উদ্দাম নাচ এখনও স্মৃতিতে হানা দেয়। এই কেঁদুলির মেলাতেই আমাদের গাঁজা টানার দীক্ষা হয়। তখনও সাহেব মেমরা বাউলদের নিয়ে মাতামাতি শুরু করেনি, আমাদের মতন কলকাতার ছেলে-ছোঁকরারাও বাউলদের সঙ্গে তেমন অন্তরঙ্গভাবে মিশত না। আমরা কৃত্তিবাস পত্রিকার দলবল, আমরা বাউলদের জীবন দর্শনে আকৃষ্ট হয়েছিলাম ওদের সঙ্গে একাত্ম হতে গেলে ওদের পাশে বসে পোড়া রুটি খেতে হবে, কেউ গাঁজার কলকে বাড়িয়ে দিলে প্রত্যাখ্যান করা চলবে না। তা গাঁজা টেনে বেশ মজাই পেয়েছি। এখন দেখি অনেকে ড্রাগের পাল্লায় পড়ে জীবন নষ্ট করে ফেলে। আমরা কয়েকজন অনেকরকম নেশার দ্রব্য পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু কখনও পাকাঁপাকি ধরা পড়িনি।
একবার ধলভূমগড় থেকে ট্রাকে চেপে জঙ্গলের গভীরে ৪-৫ ঘণ্টা যাওয়ার পর হঠাৎ দেখি পাহাড়ের কোলে বসেছে আদিবাসীদের এক রঙিন মেলা। তৎক্ষণাৎ নেমে পড়ি সেখানেই। ট্রাকের ড্রাইভার আমাদের সেখানে নামতে বারণ করেছিল। কেন না, মাত্র কয়েকদিন আগেই নামি সেখানে হানা দিয়েছিল বুনো হাতির পাল। তারা তছনছ করে দিয়ে গেছে সারা গ্রাম। নেকড়েরা নাকি জঙ্গল থেকে ইচ্ছে হলেই যখন তখন বেড়াতে চলে আসে এদিকে। আমরা শুনিনি। নেমে পড়েছিলাম। গাছে-গাছে মহুয়ার ফুল। গন্ধে ম-ম করছে পৃথিবী। পাহাড় থেকে নেমে আসছে একটি ছোট্ট ঝরনা। পাহাড়ের পায়ের কাছে আদিবাসীদের কোনও পুজোপার্বণ উপলক্ষেই বসেছিল সে-মেলা। অল্প কিছু দোকানপাট। গুড়, চিঁড়ে-বাতাসা, মেয়েদের রূপটান, চুলের ফিতে আর তাগড়াই চেহারার মোরগ মুরগি–এইসব। একটা জিনিস খুব অবাক করেছিল। সেখানে কোনও জিনিসের দরদাম করা চলবে না। আমরা অবিশ্বাস্য কম দামে ক’টা মুরগি কিনেছিলাম।
দেখেছিলাম দূরের পাহাড়ি পথ ধরে দল বেঁধে মেলায় আসছে আদিবাসীরা। মেয়েরা খুব রঙচঙে পোশাকে,আর পুরুষরা কাঁধে তিরধনুক ঝুলিয়ে। প্রতি দলের সঙ্গে আছে নেকড়ের মতো বড় বড় শিকারি কুকুর। কুকুরগুলিও খোশমেজাজে মেলায় ঘুরছে-ফিরছে, জুলজুল চোখে দেখছে সবকিছু। একবার আমার দিকে তাকিয়েছিল সন্দেহের চোখে একটা কুকুর। বুক শুকিয়ে গিয়েছিল। সেখানেই অনেক জায়গায় চলছিল মুরগির লড়াই। দুটো বড়বড় মোরগের পায়ে ছোট ছুরি বেঁধে দিয়ে দুটোকে লড়িয়ে দিয়ে মজা দেখত কয়েকশো মানুষ। যার মোরগ জিতবে সে পাবে অন্য মোরগটি। ওই পাহাড়ি মেলায় এটাই ছিল একমাত্র আকর্ষণ।
সেখানে আমরাই ছিলাম একমাত্র প্যান্ট-শার্ট পরা শহুরে মানুষ, মূর্তিমান বেমানান। কিন্তু ওরা আমাদের দেখে যেমন আহ্লাদিত হয়নি, তেমনি বিরূপও হয়নি কিছু। অদ্ভুত শান্ত, স্থির চরিত্র তাদের। মেয়েদের মাথায় লাল ফুল, পুরুষদের পিঠে তীরধনুক। মাথার ওপর টকটকে নীল আকাশ। সবুজ পাহাড়, সাদা ঝরনা। সেখান দিয়ে কোনও বাস চলে না। যানবাহন কিছু নেই। এসেছিলাম একটা ট্রাকে চেপে, ফিরব কী করে? ঝুপ ঝুপ করে নেমে এল রাত। মেলা ফেরত একট দলের পিছু পিছু গিয়ে পৌঁছলাম একটা গ্রামে। সেটা সাঁওতাল ওঁরাওদের গ্রাম। এক বাড়িতে মহুয়া ও হাঁড়িয়া বিক্রি হচ্ছিল, বসে গেলাম সেখানে। রাত্তিরে শোওয়ার জন্য সে-বাড়ির লোকেরা উঠোনে খাঁটিয়া পেতে দিল। মুরগির ঝোল আর রুটি খাওয়াল। তার জন্য কিছুতেই পয়সা নেবে না। এমন আতিথেয়তা ক’জন পায়? কোনও বাড়াবাড়ি নেই, উচ্ছ্বাস নেই, যেন এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।
বারো বছর আগে এলাহবাদে দেখেছিলাম কুম্ভমেলা। প্রতি চারবছর অন্তর কোন আদিকাল থেকে এই মেলা হয়ে আসছে। সারা ভারতবর্ষের মানুষ প্রয়াগের তীর্থ-সঙ্গমে স্নান করে পুণ্যার্জন করতে আসেন। বলা যায়, প্রয়াগে তখন সারা ভারতবর্ষের উজ্জ্বল উপস্থিতি। নাগা সন্ন্যাসীরাই এ মেলার মুখ্য আকর্ষণ। সারা গায়ে ছাই মেখে হাতে একটি লোহার চিমটে নিয়ে রক্তচোখে দাপটে ঘুরে বেড়ায় তারা। আমি যে বছর যাই, তার আগের বার কুম্ভে নাগা-সন্ন্যাসীরা কোনও কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে অঘটন ঘটিয়েছিল মেলায়। পায়ের চাপে পিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছিল বহু মানুষ। সেবারও
নাগাদের ক্ষিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু হয়নি। আমার একটা ব্যাপার খুব মজার লেগেছিল। নাগা-সন্ন্যাসীরাও শীতে কাঁপছে হি হি করে। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, নাগা সন্ন্যাসীর সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। কিন্তু কুম্ভমেলায় নাগাদের প্রধান দাপট, তাদের মিছিল দেখার জন্যই বড় বড় ক্যামরা নিয়ে আসে বিদেশিরা। তাই, স্থানীয় কিছু লোকজন ভাড়া করে নাগা সন্ন্যাসী সাজানো হয়। রিক্সাওয়ালা, মুটে কিংবা ভিখিরিরা পয়সার লোভে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে মিছিলে যোগ দেয়। খাঁটি নাগা সন্ন্যাসীদের শীত সহ্য করা অভ্যাস আছে, ভাড়া করা নাগারা তা পারবে কেন? সেইজন্য কিছু কিছু নাগা অত শীতেও গায়ে ছাই মেখে সটান হেঁটে যাচ্ছে, আর কিছু নাগা এমন লাফাচ্ছে, যেন তাদের গায়ে বিছুটি লেগেছে। না, অত অসংখ্য মানুষ একসঙ্গে স্নান করছে দেখে প্রয়াগে আমার স্নানের ইচ্ছে হয়নি। আমার পুণ্যের লোভও নেই।
প্রথম সেই মুর্শিদাবাদ-ভ্রমণের পর থেকে ঘুরলাম তো কম না। পৃথিবীর প্রায় সব বড়লোক দেশেও গিয়েছি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মেলা ‘বিশ্বমেলা’, যা চার বছর অন্তর ঘুরেফিরে নানা দেশে হয়, অনেকটা অলিম্পিকের মতে, দেখেছি তাও একবার, নিউইয়র্ক-এ। সে এক বিশাল, অবর্ণনীয় রাজকীয় মেলা। প্রতি দেশের বিরাট-বিরাট মণ্ডপ–দেশজ সংস্কৃতির কোনও-না কোনও প্রতিরূপ। নিউইয়র্কের সেই বিশ্বমেলায় ঘুরছিলাম কবি অ্যালেন গিনসবার্গের সঙ্গে। শিল্প প্রদর্শনীর সঙ্গে রয়েছে খাবারের দোকান। পৃথিবীর সব দেশের খাবার সেখানে চেখে দেখা যায়। সেখানে খেয়েছিলাম কেনিয়ার জেব্রার মাংসের আচার, জাপানের কাঁচা মাছ, ক্যানাডার কুমিরের পেটের মাংস, ভাজা, যা অনেকটা ফিস ফিঙ্গারের মতন স্বাদ। পাকিস্তানি প্যাভেলিয়নে ঢুকে গিয়ে একজন লোকের মুখে বাংলা কথা শুনে চমকে উঠেছিলাম। তখনও বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়নি। ভারতীয় প্যাভেলিয়নে একজনও বাঙালি ছিল না।
সেই বিশ্বমেলার মার্কিন প্যাভিলিয়নে বিজ্ঞান প্রদর্শনী কক্ষে, মানুষকে রকেটে চাপিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে দেওয়ার একটা খেলা ছিল। সেই রকেটে চেপে অ্যালেন জিগ্যেস করেছিল, সুনীল আমরা কি সত্যি সত্যি পরের শতাব্দী দেখে যেতে পারব? অ্যালেন পারেনি, সে চলে গেছে তিন বছর আগে। আমি তো পেরে গেলাম দেখছি।
বিশ্ব-বইমেলা দেখেছি ফ্রাঙ্কফুর্ট-এ। ফ্রাঙ্কফুট-এ আছে স্থায়ী মেলা ভবন ও মেলা প্রাঙ্গণ। ভবন মানে অনেকগুলি বহুতল বাড়ি আর প্রাঙ্গণ মানে বিশাল ব্যাপার, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে হয় গাড়িতে চেপে। নিয়মিত গাড়ি চালায় মেলা কর্তৃপক্ষ, ভাড়া লাগে না। নিজেরা করেছি ‘মুক্তমেলা’। পার্ক স্ট্রিট-এর কাছে মনোহর দাস তড়াগের গায়ে প্রতি শনিবার বসত শিল্পসাহিত্যের সে এক অনুপম মেলা। যে যার কবিতা-গল্প পড়ছে, নাটক করছে, গান গাইছে, ছবি দেখাচ্ছে। দর্শকের, শ্রোতার সম্পূর্ণ অধিকার দেখার, শোনার বা প্রত্যাখানের। প্রয়াত কবি তুষার রায় তাঁর সব প্রাণশক্তি ঢেলে দিয়ে কবিতা পড়তেন সেখানে। বিকেলের ওই খেয়ালখুশির মেলায় সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েছিলেন তিনি। তুষার কবিতা পড়লে আমাদের কারও আর শ্রোতা জুটত না। কলকাতা বইমেলায় তো প্রতি বছরই যাই। বইমেলা তো এখন জড়িয়ে গেছে বাঙালির রক্তে। সারা বছর সবাই অপেক্ষায় থাকি এই বই পার্বণের জন্যে। ফ্রাঙ্কফুর্ট বা দিল্লির বইমেলা কলকাতার প্রাণপ্রাচুর্যের কাছে কিছুটা বিবর্ণ মনে হয় আমার।
ঘুরছি অনেক। অনেকেই বলেন, আমার নাকি পায়ের তলায় সরষে। পৃথিবীটাকে আমার কখনও কখনও খুব ছোট্ট মনে হয়। কিন্তু সেই যে ধলভূমগড়ের কাছে নাম-না-জানা পাহাড়ি মেলা, সেখানকার মহুয়া ফুল, মাদল, মানুষজন, সেসব আজও আমায় নির্জনে ডাক দিয়ে যায়। বুক মুচড়ে ওঠে। যদি যাওয়া যেত আর-একবার।