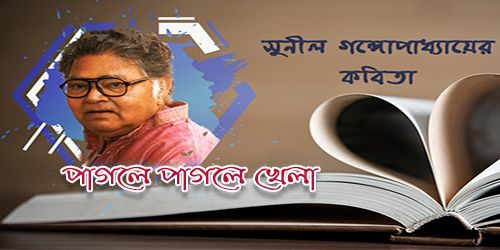বন্ধুর বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, ঘড়ি দেখলে মনে হয় রাত হয়ে গেছে, অথচ বাইরে ফটফটে দিনের আলো, এখানে পৌনে নটার আগে অন্ধকার নামে না। আগে এরকম বিলম্বিত বিকেল দেখেছি কাশ্মীরে, লেনিনগ্রাদে, তখন ওই নামই ছিল, এখন সেন্ট পিটার্সবার্গ। সেখানে রাত এগারটা পর্যন্ত বিকেল ছিল। বাংলা বাক্য হিসেবে এটা অদ্ভুত শোনালেও আর কীভাবেই বা বলা যায়!
এই অঞ্চলটির নাম এজাক্স, টরন্টো শহরের অদূরে। কাল বেশ শীত ছিল, আজ আর গায়ে সোয়েটার লাগছে না। গাড়িতে ওঠার আগে খানিকটা হেঁটে আসার প্রস্তাব দিলেন বন্ধুটি। প্রায় সবই একরকম বাড়ি, রাস্তার দুপাশে সবুজ মখমল, কোনও কোনও বাড়ির সামনে বড়-বড় পিউনি ফুল ফুটে লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে, এ এক এমনই ফুল যে নিজের ভার নিজে বইতে পারে না।
দৃশ্য হিসেবে এমন কিছু বৈচিত্র্য নেই, কিন্তু রাস্তায় একবার বাঁক নিতেই চোখে লাগল বিস্ময়ের ঘোর। সামনেই অকূল জলরাশি, এ দেশের হ্রদগুলি সমুদ্রেরই মতন, পরপর দেখা যায় না, জাহাজ চলে। যেন নীল আকাশ উল্টো হয়ে শুয়ে আছে, এই উপমাটা আমার বারবার ব্যবহার করতে ইচ্ছে হয়। যে অজস্র সাদা রঙের পাখি উড়ছে, সেগুলিকে প্রথম দৃষ্টিতে বক মনে হলেও বক নয়, এ দেশে বক দেখিনি, ওগুলি সিন্ধুসারস বা সিগাল। নীলের পটভূমিকায় ওরা অনবরত নতুন নতুন রেখাচিত্র রচনা করে যাচ্ছে।
পুকুর, নদী, হ্রদ বা সমুদ্র উপভোগ করার শ্রেষ্ঠ উপায় অবগাহন। বন্ধুকে জিগ্যেস করলাম, আপনার বাড়ির এত কাছে, গরম কালে এখানে এসে সাঁতার কাটেন?
কান্তি হোর বললেন, ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। কাছেই পারমাণবিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, তাই বিপজ্জনক বলে এখানে জলে নামাই নিষিদ্ধ।
এখানে কেউ মাছ ধরে না?
ওই একই কারণে এখানে মাছ ধরাও বেআইনি।
সামনে এতখানি সুদৃশ্য জল, অথচ সেখানে স্নান করাও যায় না, মাছ ধরাও যায় না জেনে আমার পূর্ববঙ্গীয় মানসিকতায় একটা জোর ধাক্কা লাগে। অন্টারিও হ্রদের রূপ অনেকটা ম্লান হয়ে যায়।
তবু যা হোক সিন্ধুসারসগুলির ওড়াউড়ির রেখাচিত্র মনে থেকে যাবে।
০২.
বাহাউদ্দিন সাহেবের জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়, বহুকাল প্রবাসী। কিন্তু তিনি তার বাংলা ভাষায় ইচ্ছে করেই জন্মস্থানের বিশেষ উচ্চারণ বজায় রেখে দিয়েছেন। এবং মৎস্য প্রীতি। অনেক বছর কাটিয়েছেন আরব দেশে, সেখানে আশা মেটেনি। উত্তর আমেরিকায় প্রচুর মাছ পাওয়া যায়, আগে স্যাড মাছ খেয়ে ইলিশের সাধ মিটত, এখন আসল পদ্মার ইলিশের ছড়াছড়ি বাংলাদেশি দোকানগুলিতে।
বাহাউদ্দিন সাহেব গ্রামের জীবনের মতন কানাড়াতেও নিজে মাছ ধরেন। মাছ ধরার নির্দিষ্ট এলাকা আছে, ছিপ ফেলতে হলে লাইসেন্স নিতে হয়। বাহাউদ্দিন খুব সফল মৎস্যশিকারি, মাঝে মাঝেই নানারকমের ছিপ ও হাত-জাল নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়েন এবং প্রচুর মাছ ধরে আনেন। একরকমের ছোট মাছ তার খুব প্রিয়, এখানে তার নাম সান ফিস। গ্রাম বাংলার পুকুরে সূর্য পোনা নামে এক ধরনের মাছ থাকে, সেগুলি খুবই ছোট ও অখাদ্য, এই সান ফিস বেশ সুস্বাদু, অনেকটা কই মাছ ও তেলাপিয়ার মাঝামাঝি আকৃতি, একদিন বাহাউদ্দিন আমাদের সেই মাছ খাওয়ালেনও, বলাই বাহুল্য আরও অনেকরকম আহার্য ছিল, আমি সূর্য মাছই বেশি খেলাম।
সূর্য মাছ ধরা খুব মজার খেলা। এতই অজস্র মাছ যে, বাংলার অনেক গ্রামের পুকুরের পুঁটি মাছের মতন, ছিপ ফেললেই পটাপট ওঠে, তা দেখে বাহাউদ্দিনের স্ত্রী, যিনি নিজে কখনও ছিপ হাতে নেননি, তিনিও ছিপ ফেলা শুরু করলেন এবং সার্থকতার সীমা নেই। দুজনে মিলে ঝুড়িঝুড়ি মাছ ধরে এনে ডিপ ফ্রিজে রেখে দেন, তিন-চার মাস চলে যায়, প্রায় বিনা পয়সার মাছ। মাঝে মাঝে বঁড়শিতে দু-একটা অন্য জাতের বড় মাছও গেঁথে যায়। একবার সেরকম একটি বিশেষ ধরনের লোভনীয় চেহারার বড় মাছ টেনে তুলতেই কাছাকাছি অন্য চিপধারীরা শশব্যস্ত সাবধান করে দিল, ওটা রাখবেন না, রাখবেন না, জলে ছেড়ে দিন!
ও মাছ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে যদি পুলিসের নজরে পড়ে, তা হলে অন্তত দুশো ডলার জরিমানা! কারণ, ওই বিশেষ প্রজাতির মাছেরা গ্রীষ্মের তিন মাস ডিম প্রসব করে। তাদের বংশরক্ষার জন্যই ওই সময়কালে মানুষের লোভ সংবরণ করাই সংগত নীতি।
আমাদের ছেলেবেলায় পূর্ববঙ্গের গ্রামে রীতি ছিল, দুর্গাপুজোর বিজয়া দশমীর পর আর ইলিশ মাছ খেতে নেই। আবার সেই সরস্বতী পুজোর দিন জোড়া ইলিশ এনে সেই মৎস্যশ্রেষ্ঠকে বাড়িতে স্বাগত জানাতে হয়। মাঝখানের কয়েকটি মাস ইলিশের ক্রেতা থাকত না বলে জেলেরাও অন্য কাজে মন দিত। আইনের প্রয়োজন ছিল না, পুলিস পাহারারও প্রশ্ন নেই, এটা সামাজিক প্রথা, সেই সময়ে ইলিশের ঝাক নির্বিঘ্নে ডিম ভাসিয়ে দিত নদীর স্রোতে।
এখন সে সামাজিক প্রথা উঠে গেছে, অনেকে জানেই না, ইলিশ সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির কথা কেউ চিন্তা করে না, নদীগুলি রুগ্ন ও কলুষিত, পদ্মা-গঙ্গা-আড়িয়েল খাঁ-র বিখ্যাত ইলিশের সংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছে, স্বাদও আর তেমন নেই।
মাদারিপুর শহরের পাশে আড়িয়েল খাঁ নদীতে ইলিশ মাছ ধরা দেখতে যেতাম আমরা বর্ষাকালে। অনেক নৌকো ভাসছে, মাঝে মাঝে তোলা হচ্ছে জাল, টুকরো-টুকরো বিদ্যুতের মতন তাতে লাফাচ্ছে রুপোলি ইলিশ। খুব সম্ভবত বুদ্ধদেব বসুই একমাত্র বাঙালি কবি, যিনি ইলিশ বিষয়ে লিখেছেন একটি সম্পূর্ণ কবিতা। ইলিশের বিশেষণ দিয়েছিলেন, ‘জলের উজ্জ্বল শস্য’।
আমাদের ছেলেবেলায় ইলিশের ওজনদর ছিল না, আকার-আকৃতি অনুযায়ী দাম। আমার কাকা একদিন সাত পয়সা দিয়ে একটি অপূর্ব সুন্দর ইলিশ কিনেছিলেন, যার ওজন হবে অন্তত আড়াই কিলো। আমার তখন মাত্র সাত বছর বয়েস, বিস্ময়ে ভরা চোখ নিয়ে সব দেখছি, একটি জেলে আমার হাতের সাইজের একটি ইলিশ আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল, এইটা দা ঠাউরের জন্যি ফাউ! (দা ঠাউর, অর্থাৎ দাদাঠাকুর, বাচ্চাদের প্রতি এরকম সম্বোধন তখন প্রচলিত ছিল।) সেই দৃশ্যটি এখনও ফ্রেমে বাঁধানো ছবি হয়ে আছে স্মৃতিতে।
ইলিশ বিষয়ে একটি মজার অনুমান কাহিনী লিখে গেছেন সৈয়দ মুজতবা আলি। ভারতের ইতিহাসে মুহম্মদ বিন তুঘলক একজন খেয়ালি ও পাগলা ধরনের সম্রাট হিসেবেই পরিচিত, যদিও তার অনেক গুণ ছিল এবং স্বভাবে ছিলেন বেপরোয়া। এক সময় তিনি বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য গুজরাটের উপকূল অঞ্চলে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করছিলেন, নৌকো করেও ঘুরেছেন। একদিন তার নৌকোতে হঠাৎ একটি অতি সুদৃশ্য রুপোলি রঙের মাছ উঠে পড়ে। মাছটি দেখে সম্রাট এমনই মুগ্ধ হলেন যে হুকুম দিলেন, তখুনি রান্না করে দেওয়া হোক, তিনি মাছটির স্বাদ নেবেন। তখন রোজার মাস, সারাদিন তার কিছুই আহার করার কথা নয়, তার ওপর এটা অচেনা মাছ, বিষাক্ত কি না কে জানে, সাঙ্গোপাঙ্গরা ইতস্তত করতে লাগল, কিন্তু সম্রাটের জেদের ওপর আর কথা চলে না। মুহম্মদ বিন তুঘলক মাছটি এমনই পছন্দ করলেন যে খেয়ে ফেললেন অনেকখানি, তারপর তার সাংঘাতিক পেটের পীড়া হল এবং সেই রোগেই তার মৃত্যু হল অচিরে। মুজতবা আলির অনুমান, মুহম্মদ বিন তুঘলক যে মাছটি খেয়েছিলেন, সেটি নিশ্চিত ইলিশ (গুজরাটেও ইলিশ পাওয়া যায়, স্থানীয় নাম পাল্লা) এবং ইলিশ ভক্ষণ করে তার মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি নিশ্চিত বেহেস্তে গেছেন।
এখন আর এরকমভাবে কেউ ইলিশ-বন্দনা করে না। আমি নিজেও আর তেমন ইলিশভক্ত নই, আগেকার মতন স্বাদ পাই না।
বাহাউদ্দিন সাহেব আপসোস করে বললেন, অত বড় মাছটাকে ধরেও ছেড়ে দিতে হল, আপনাকে খাওয়াতে পারছিলাম না, সে মাছের স্বাদ আরও চমৎকার!
ধরা-পড়া মাছের চেয়ে পালিয়ে যাওয়া মাছ তো সব সময়ই বেশি ভালো হয়।
০৩.
জীবনের বছরগুলি হাঁটতে-হাঁটতে অনেক মানুষের অনেকরকম ট্রাজেডির কথা জানতেই হয়। কিন্তু এই মানুষটির ট্রাজেডি একেবারে অন্যরকম। নামটা বদল করা দরকার। ধরা যাক, এঁর নাম ওয়াহিদ করিম, পরিচিত মণ্ডলীতে সবাই ডাকে করিম ভাই। হৃষ্টপুষ্ট, হাসিখুশি প্রৌঢ় মানুষটিকে সকলেই পছন্দ করে। পঞ্চাশের দশকে দেশ ছেড়ে এসে অন্তত সাত-আটটি দেশে নানারকম চাকরি করেছেন, এখন স্থায়ী আস্তানা গেড়েছেন কানাডায় চারটি ছেলেমেয়ে, স্ত্রীও রর্তমান, দুটি ছেলে উত্তম চাকরি পেয়েও অলাদা বাসায় উঠে যায়নি, করিম সাহেবের নিজেরও কিছু জমানো টাকা আছে, সুখের সংসার।
করিম সাহেব অবসর নিয়েছেন, ঘুরে-ঘুরে বাংলা ভাষাভাষী বিভিন্ন পরিবারে দেখাসাক্ষাৎ করতে যান, যে-কোনও আড্ডায় তিনি স্বাগত, কারণ তার গল্পের স্টক অফুরন্ত। কথায় কথায় উচ্চহাস্য করে তিনি আসর মাতিয়ে দেন।
দিব্যি সময় কাটছিল, হঠাৎ সব গোলমাল করে দিল করিম ভাইয়ের ছোট ছেলে পিন্টু ওরফে আসরাফ। সে বিয়ে করে ফেলল এক হিন্দু মেয়েকে। এটা অসরাফের মা নীলোফারের একেবারেই পছন্দ নয়। আসরাফ শুধু যে হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছে তাই-ই নয়, সে আপাতত বেকার, বেঙ্গলি ক্লাবে নাটকের অভিনয় করার ব্যাপারে তার যত উৎসাহ, চাকরি খোঁজার উৎসাহ তেমন নেই, এ সময় বিয়ে করে ফেলাটা অসমীচীনই বলতে হবে। তার স্ত্রীর নাম বিউটি, এ দেশেই বর্ধিত, তার আচারে-ব্যবহারে হিন্দুত্ব বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু তার প্রকৃত নাম আরতি সেনগুপ্ত। নাটকের মহলার সময়ই পিন্টুর সঙ্গে বিউটির পরিচয় ও প্রণয় এবং দ্রুত গোপন বিবাহ, সেই জন্য নীলোফার বেগম থিয়েটার ব্যাপারটাই দু-চক্ষে সহ্য করতে পারেন না। কোন কুক্ষণে আসরাফ বেঙ্গলি ক্লাবে থিয়েটার করতে গিয়েছিল।
এ বিষয়ে করিম ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর মতভেদ বিস্তর। করিম ভাই থিয়েটার-গান বাজনা পছন্দ করেন খুব, ছেলে তার মনের মতন মেয়েকে বিয়ে করেছে, তা নিয়ে আপত্তি জানাবার তিনি কারণ খুঁজে পান না। হিন্দু মেয়ে বলে তো আর এ বাড়িতে পুজো-আচ্চা শুরু করেনি, খাওয়াদাওয়ার বাছবিচার নেই, থাকুক না ওরা ওদের মতন। এর চেয়ে কোনও সাদা মেয়েকে বিয়ে করলে কি ভালো হত? ইংরেজি বলতে হত সর্বক্ষণ, তার সামনে লুঙ্গি পরে আসা যেত না। কিংবা ইহুদি মেয়ে?
পিন্টু এখন চাকরি করে না বটে, তবে পেয়ে যাবেই। পিন্টুর বউ ব্যাংকে চাকরি করে, সকাল সকাল বেরিয়ে যায়, ফেরে সন্ধের সময়, তারপরেও এক-একদিন ক্লাবে যায়, তাতে সংসারের তো কিছু বিঘ্ন হচ্ছে না।
নীলোফার বেগম এসব কিছুই জানেন না। তিনি আসরাফের বউকে অবিলম্বে ধর্মান্তরিত করে নাম দিতে চেয়েছিলেন আয়েষা, কিন্তু বিউটি তাতে রাজি নয়, সে মেয়েও খুব তেজি। আসরাফের সঙ্গে তার আগেই কথা হয়ে আছে, তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হলে সে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।
প্রায় প্রতিদিনই খিটিমিটি লেগে রইল। করিম ভাই সব সময় কথা বলেন ছোট ছেলে আর তার বউয়ের পক্ষ নিয়ে। নীলোফার বেগমের মেজাজ এক-এক সময় খুব উগ্র হয়ে ওঠে। ছেলের (য়েও স্বামীর ওপরেই তাঁর রাগ হয় বেশি। এক সন্ধ্যায় পিন্টু আর বিউটি তাদের ঘরে বসে, পরা বন্ধ করে থিয়েটারের পার্ট রিহার্সাল দিচ্ছে, বেশ শোনা যাচ্ছে বাইরে থেকে, নীলোফার বেগমের গায়ে নাটকের সংলাপগুলি শূলের মতন বিঁধছে। বাড়িতে এ অনাচার তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না। এক সময় তিনি অতিষ্ঠ অস্থির হয়ে বলে উঠলেন, আজ রাতেই তিনি ও মেয়েকে বেরিয়ে যেতে বলবেন, তাতে ছেলেও যদি ভেডুয়ার মতন বউয়ের সঙ্গে-সঙ্গে যায় তো যাক। তিনি ওদের ঘরের দিকে ধেয়ে যেতেই বাধা দিলেন করিম ভাই। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে স্ত্রীকে শান্ত করতে গেলেন, কিন্তু তা হল না, বরং শুরু হয়ে গেল ধস্তাধস্তি, এক সময় আকস্মিকভাবে করিম ভাইয়ের ধাক্কায় নীলোফার বেগম পড়ে গেলেন খাওয়ার টেবিলের ওপর, কোনায় লেগে তার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে লাগল। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে নীলোফার বেগম টেলিফোনে ঘোরালেন নশো নম্বর।
অবিলম্বে এসে গেল পুলিশ।
এসব ব্যাপারে পুলিশের বিধান তাৎক্ষণিক। করিম ভাই তাঁর স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছেন, গ্রপাত হয়েছে, সুতরাং এ বাড়িতে তার থাকার আর অধিকার নেই। এক্ষুনি বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে। এবং যতদিন না অন্য ব্যবস্থা হয়, ততদিন তিনি এ বাড়ির হাজার গজের মধ্যে আসতে পারবেন না। জোর করে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করলে তার শাস্তি হবে কঠিনতর।
করিম ভাই অনেকভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, ছেলেরাও এসে বলল, এটা তুচ্ছ পারিবারিক ব্যাপার, কিন্তু পুলিস তাতে কর্ণপাত করতে রাজি নয়। রক্তপাত হয়েছে। করিম ভাইকে পুলিশ বলল, আমরা থাকতে থাকতে তোমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও!
এইরকম সময়েই করিম সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয়।
প্রথমে তিনি একটা মোটেলে গিয়ে উঠেছিলেন। পরিচিতরা জানতে পেরে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে এসেছে। একদিন এ বাড়ি, একদিন অন্য বাড়ি। আড্ডায় সময় তিনি একটি কথাও বলেন না। কী অসহায়, বিষণ্ণ তার মুখ।
একদিন কয়েকজনের সঙ্গে গাড়ি করে যাচ্ছি, একজন বলল, আরে ওখানে করিম ভাই না?
একটা পার্কের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন করিম ভাই। এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন দুরের দিকে। পার্কের ও পাশেই তার বাড়ি, মাঝখানের দূরত্ব হাজার গজের বেশিই হবে।
জোর করে তাকে তুলে নেওয়া হল গাড়িতে।
করিম ভাই ম্লান গলায় বললেন, আমার মাথার বালিশটা নিয়ে আসিনি। অন্যের বাড়িতে, অন্য বালিশে আমার ঘুমই আসে না।
০৪.
পোল্যান্ড থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর শোর্পা ইউরোপের যেখানেই গেছেন, তার সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন একটি ছোট ভাণ্ডে খানিকটা মাটি, পোল্যান্ডের মাটি, তার জন্মভূমির সঙ্গে এইভাবে রেখেছিলেন যোগাযোগ।
কথাটা মনে পড়ল বাংলাদেশিদের এক পার্টিতে।
অতি সুদৃশ্য অ্যাপার্টমেন্ট সাতাশ তলার ওপরে, নানারকম খেলনা দিয়ে সজ্জিত, জানলা দিয়ে আলো ঝলমল নিউ ইয়র্ক নগরের অনেকখানি দেখা যায়। একটা বেশ চওড়া বারান্দাও আছে।
অল্প শীত থাকলেও আমাকে মাঝে মাঝে সেই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়। এখন আর ঘরের মধ্যে সিগারেট টানা চলে না। এক-একটা আসরে দেখা যায়, আমিই একমাত্র অপরাধী।
বারান্দায় অনেকগুলি ফুল গাছের টব। নানা রঙের ফুল, অনেকগুলিরই নাম জানি না। একটি ফুল গাছের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। জবা! এ দেশে জবা আগে দেখিনি, তিনটি ফুল ফুটে আছে।
গৃহস্বামী আলতাফ আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।
তাকে জিগ্যেস করলাম, জবা কোথায় পেলে? দেশ থেকে নিয়ে এসেছ নাকি?
সে বলল, না, জবা গাছ এখানে পাওয়া যায়। তিরিশ ডলার দাম, একটা ডাল একটু ভাঙা বলে কুড়ি ডলারে পেয়েছি।
তারপর সে বলল, তবে, এই টবের মাটি আমি এনেছি বাংলাদেশ থেকে তিনবার অ্যাপার্টমেন্ট বদলেছি, এই মাটি সব জায়গায় সঙ্গে নিয়ে গেছি। এক-এক সময় যখন দেশের জন্য খুব মন কেমন করে, আমি এই মাটি একটু ছুঁই।
তুলনাটা ঠিক হল না। অসাধারণ পিয়ানোবাদক ও সুরস্রষ্টা সোপা হয়েছিলেন নির্বাসিত, আমরা তো তা নয়, আমরা যখন ইচ্ছে দেশে ফিরে যেতে পারি। তবু এত আবেগ বা হা-হুতাশ কেন?
আলতাফ বলল, বাধা নেই বলছেন? তা ঠিক, তবু অনেকরকম বাধা আছে, নিজেদের তৈরি করা।
ঘরের মধ্যে ফিরে এসে এটাই হল প্রধান আলোচ্য বিষয়। ফেরা, না-ফেরা। আমি কোনও পক্ষেই নেই, তাই নীরব শ্রোতা।
উপস্থিত আমন্ত্রিতদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশেরই মত এই যে, দেশ ছেড়ে এসে তারা ঠিক কাজই করেছে, দেশ তাদের চাকরি দিতে পারে না, সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে না, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা অতি নীচু স্তরের, জীবনের নিরাপত্তা নেই…দূরে থেকে তারা বরং দেশের উপকারই করছে, ডলার পাঠায়, কেউ গ্রামের স্কুলের উন্নতির জন্য টাকা দিয়েছে, কেউ ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছে বাবা-মায়ের জন্য…
এদের গলার জোরই বেশি।
অন্য পক্ষ খানিকটা মিনমিন করে বলল, আরে মশাই, ভালো গাড়ি চড়া, ভালো বাড়ি, ইচ্ছেমতন যে-কোনও খাবার, এমনকি সাদা বান্ধবী, এ সবই কয়েক বছর পর একঘেয়ে হয়ে যায়, এখন বুঝতে পারি, মনটা পড়ে আছে নিজের দেশে… মনটা সেখানে আর শরীরটা এখানে। এ এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা… এক-একদিন সন্ধেবেলা হঠাৎ মনে হয়, দূর ছাই, সামনের মাসেই দেশে ফিরে যাব, পাকাঁপাকি লুক স্টক অ্যান্ড ব্যারেল… কিন্তু পরদিন সকালে আবার মনে পড়ে কত পিছুটান।
অন্য পক্ষ থেকে একজন বলল, দাদা, যে-রাতে বেশি মাল খান সে রাতেই দেশের জন্য মনটা বেশি উতলা হয়, তাই না?
একজন আমাকে জিগ্যেস করল, এ বিষয়ে আপনার কী মত?
আমি বললাম, আমি তো এ দেশে থাকতে আসিনি। তাই আমার এ বিষয়ে কোনও মতামত থাকতে পারে না। তবে আমেরিকা-কানাডায় ঘোরাঘুরি করতে-করতে যখন দেখি হাজার-হাজার মাইল জমি খালি পড়ে আছে, মানুষ কত কম, তখন মনে হয়, আমাদের দেশ থেকে কয়েক কোটি লোককে এনে এখানে ছেড়ে দেওয়া উচিত…
এ উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে সে সরাসরি প্রশ্ন করল, আপনি যদি সুযোগ পান, আপনি এ দেশে থেকে যেতে রাজি হবেন?
একজনের গেলাস উল্টে গেল। তাতে মনোযোগ সেদিকে চলে যাওয়ায় তার সুযোগ নিয়ে আমি উত্তর এড়িয়ে সিগারেট টানতে চলে গেলাম বারান্দায়।
আজ্ঞায় একটা কোনও বিশেষ প্রসঙ্গ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। এর মধ্যেই ঘুরে গেছে অন্য দিকে। এখন আলোচনার নায়ক একটি সাতাশ বছরের যুবক, সে অবশ্য এখানে অনুপস্থিত।
ছেলেটির নাম লতিফ, তার মতন মেধাবী ছাত্র ভারতীয় বা বাংলাদেশিদের মধ্যে ইদানীংকালে আর দেখা যায়নি। আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে সে পূর্ণ স্কলারশিপ নিয়ে পড়েছে। অতি কম বয়সে এম এস করার পর সে চাকরি নিল, কয়েক বছর বাদে পি এইচ ডি করবে এই ইচ্ছে নিয়ে।
সেই লতিফ এখন মনোরোগী। চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, কারোর সঙ্গে কথা বলে না, খেতে চায় না, দরজা-জানলা বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকে। এ জন্য তার বাবা দারুণ উদ্বিগ্ন, মা। প্রায় ভেঙে পড়েছেন।
লতিফের কেন এরকম অবস্থা হল? না, প্রেমের ব্যর্থতাজনিত নয়। কলেজ জীবনে সে টের পায়নি, চাকরিতে ঢোকার পরই সে প্রথম বুঝতে পারল, তার গায়ের চামড়ার রঙের জন্য সে তার শেতাঙ্গ বন্ধুদের সমান হতে পারবে না। একই চাকরিতে ঢুকেছে তার এক সহপাঠী, কিন্তু সাদা চামড়া বলেই তার মাইনে ও সুযোগ-সুবিধে বেশি। চাকরি বদলাল, সেখানেই ওই একই ব্যাপার। এটা সে মেনে নিতে পারেনি, প্রতিবাদ করতে গিয়ে লাভ হয়নি। তার ফলেই এসেছে দারুণ মানসিক অবসাদ। ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম, অথচ কিছুতেই সে ডাক্তারের কাছেও যাবে না।
অমন একটি ভালো ছেলের এরকম পরিণতির কথা শুনে সবাই দুঃখিত।
একজন বলল, ছেলেটি লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট হতে পারে, কিন্তু তার বাস্তব বুদ্ধি বড় কম। শুধু লেখাপড়া করলে এইরকমই হয়। এ দেশে যে এরকম ডিসক্রিমিনেশন আছে, তা সে আগে বোঝেনি কেন? আমরা সবাই তা জানি, প্রত্যেকেই কখনও না কখনও ভুগেছি, তবু মেনে নিতে হয়, মেনে না নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আরে বাবা, আমরা বাইরে থেকে এখানে টাকা রোজগার করতে এসেছি, একটু-আধটু লাথি-ঝাটা তো খেতেই হবে। যে গরু দুধ দেয়, সে গরু চাঁট মারে না?
আমাদের দীপ্তেন্দু চক্রবর্তী বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলল, বাজে কথা! শুধু এ দেশে কেন, ডিসক্রিমিনেশন কোন দেশে নেই, আমাদের নিজেদের দেশে নেই? আরও বেশি আছে। ফিফটি পার্সেন্ট গরিবদের তুলনায় মধ্যবিত্তরা সব ব্যাপারে বেশি সুযোগ-সুবিধে পায় না। গ্রামের তুলনায় শহরের লোক কী পায়? এমনকি গায়ের রঙ… খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে বেরয় ফরসা পাত্রী চাই… বরং এ দেশেই ওরকম বিজ্ঞাপন বেরলে জেল হয়ে যেত! কালো মেয়েদের বিয়েই হয় না। প্রতিভা থাকলে এ দেশেও যে সাদা চামড়াদের থেকে ওপরে ওঠা যায়, তার আমি অনেক উদাহরণ দিতে পারি… ওই ছোকরাটাকে কোনও মেয়ের সঙ্গে ভিড়িয়ে দাও, ও সব ডিপ্রেশানফিপ্রেশান হাওয়া হয়ে যাবে!
এরপর যে তর্ক শুরু হল, তাতে যুক্তির চেয়ে চেঁচামেচিই বেশি। এরকম সময়ে অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়াই ভালো।
লতিফকে আমি দেখিনি। তবু যেন দেখতে পেলাম, একটা অন্ধকার ঘরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে একটি সাতাশ বছরের যুবক। কত যত্ন ও পরিশ্রমে সে লেখাপড়া শিখেছে, অথচ কী বিমর্ষ তার মুখখানি। সে নিজের দেশেও ফিরে যেতে পারবে না।
০৫.
মন্ট্রিয়েল নগরটি ভারী রূপবান। কোনও কোনও অঞ্চলে পায়ে হেঁটে ঘুরলেও চক্ষের আরাম হয়।
বাংলায় নগর ও নগরী দুটোই চলে। নদীরা যেমন পুং লিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ। এ দেশের বৃহৎ অট্টালিকাবহুল শহরগুলি দেখলে আমার পুরুই মনে হয়, নগরী বলা যায় না।
মন্ট্রিয়েলে একটা ব্যাপার মিলিয়ে দেখার জন্য আমার কৌতূহল ছিল।
কানাডায় কুইবেক রাজ্যটি ফরাসি প্রধান। মাঝে-মাঝে এরা কানাডা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হতে চায়। একবার শার্ল দ্য গল এসে সেই মনোভাব উস্কে দিয়ে গিয়েছিলেন।
মন্ট্রিয়েলের ফরাসি নাগরিকরা উগ্ৰ ভাষাবাদী। আগেই শুনেছিলাম, এই শহরের সমস্ত বিল বোর্ড, সাইন বোর্ড, পোস্টারে ফরাসি ভাষা রাখতেই হবে। এ জন্য ভাষা-পুলিশ আছে, তারা ঘুরে ঘুরে দেখে, কোথাও কোনও সাইন বোর্ডে শুধু ইংরেজি থাকলে তারা টেনে নামিয়ে দেয়।
যা শুনেছি, তা সত্যি। মন্ট্রিয়েলের যে-কোনও রাস্তায় চোখ ঘোরালেই বোঝা যায়, সেটা ফরাসিদের শহর। ঢাকায় যেমন বোঝা যায়, সে শহরটা বাঙালিদের। দুঃখের বিষয়, কলকাতায় তা বোঝা যায় না। কলকাতাতে ভাষা-পুলিশ তৈরি করতে হবে।
মন্ট্রিয়েলে আমি সবচেয়ে বেশি চমকৃত হয়েছি কয়েকটি ঘোড়ার গাড়ি দেখে!
আমার এক ডাক্তার বন্ধু বলেছিলেন, আমাদের দেশে পঞ্চাশ ভাগ লোক খালি পায়ে হাঁটে। দেশসুদ্ধ সবাইকে যদি জুতো পরানো যেত, তা হলে সবাই স্বাস্থ্যবান হয়ে যেত!
জুতো পরার সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক আছে অবশ্যই।
গ্রামেগঞ্জে, এমনকি শহরের বস্তিতেও শৌচাগার নেই। অধিকাংশ মানুষ গাড়ু কিংবা মগে পানি কিংবা জল ভরে মাঠে-ঘাটে মল-মূত্র ত্যাগ করতে যায়। খোল পড়ে থাকা পূরীষে জন্মায় হক ওয়ার্ম, অতি সূক্ষ্ম সেই বীজাণু খালি পায়ে হাঁটা মানুষের পায়ের তলা দিয়ে ঢুকে যায় শরীরে। তার ফলে সারা জীবন তারা পেটের ব্যায়োতে ভোগে। গ্রামের বহু মানুষের এ জন্য রোগা ডিগডিগে চেহারা।
কিছু কিছু জন্তু-জানোয়ারের পুরীষ আরও মারাত্মক। বিশেষত ঘোড়ার। কলকাতা শহরে এক সময় ঘোড়ার গাড়ি চলত অনেক, এখনও কিছু কিছু আছে। ঘোড়ার পুরীষ থেকে ছড়ায় টিটেনাস। শহরের রাস্তায় আছাড় খেয়ে হাত-পা ছুঁড়ে গেলেই অ্যান্টি-টিটেনাস ইঞ্জেকশন নিতে হয়। আমি নিজেই নিয়েছি তিনবার।
মন্ট্রিয়েলের ঘোড়ার গাড়িগুলি প্রধান যানবাহন নয়, নিছক শখের ভ্রমণবিলাসীদের জন্য। যেমন অনেক বড় শহরেই হোটেলগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে থেকে পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে চায়। এখানকার জুড়ি গাড়িগুলি ভারী সুন্দরভাবে রঙ করা, ঘোড়াগুলিও তেজি। প্রত্যেকটা ঘোড়র পেছন দিকে একটা থলি বাঁধা আছে। প্রথমে অদ্ভুত লেগেছিল, দু-তিনবার দেখার পরেই সেই থলি-রহস্য প্রাঞ্জল হয়ে গেল। ঘোড়ারা চলন্ত অবস্থায় যখন-তখন অপকর্ম করে। তাদের পূরীষে যাতে রাস্তাঘাট দুষিত না হয়, সেই জন্য এরকম থলি বেঁধে রাখার ব্যবস্থা।
আমাদের দেশে ঘোড়ার ব্যবহার হচ্ছে হাজার-হাজার বছর। কিন্তু রাস্তাঘাট ঘোড়ার পূরীষমুক্ত রাখার এত সহজ ব্যবস্থাটা কালোর মাথায় আসেনি? আমরা টিটেনাস রোগ পুষে রেখেছি।
০৬.
এ দেশটা যৌবনের। বুড়ো-বুড়িরা টিকে থাকে কোনওক্রমে সমাজের প্রান্তসীমায়। ছেলেমেয়েরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে নানা জায়গায়, বছরে একবার তাদের মুখ দেখা গেলেই যথেষ্ট। অনেকে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেই কবরখানার জমি কেনার জন্য টাকা জমায়।
অবশ্য যাদের অপরিমেয় অর্থবল থাকে তারা ব্যতিক্রম। বার্ধক্যে শিথিল পেশিতে কিছুটা শক্তি জোগাতে পারে টাকাপয়সা। অর্থ থাকলে হুকুম দেওয়ার অধিকারও থাকে।
প্রবাসী পুত্রকন্যাদের কাছে দেশ থেকে যে-সব বাবা-মা কিছুদিনের জন্য থাকতে আসে, তাদের নানা করুণ কাহিনি প্রচলিত আছে। অল্প দিনের জন্য বেড়িয়ে যাওয়া ভালো, বেশিদিন থাকলেই বন্দিদশা। গাড়ি-নির্ভর দেশ, দেশ থেকে বুড়ো-বুড়িরা এসে গাড়ি চালাতে পারে না। শনি-রবিবার ছাড়া অন্যদিন তাদের কে গাড়িতে চড়াবে? অতি ভক্তিমান-ভক্তিমতী পুত্র-কন্যার পক্ষেও সম্ভব নয়। ফলে দিনের পর দিন বাড়ি থেকে তারা এক পা-ও বেরতে পারে না।
মাঝে মাঝেই আমার মনে হয়, আমি নিজেই যেন আমার আগেকার লেখা কোনও গল্পের চরিত্র হয়ে গেছি। আমি আর স্বাতী কিছুদিনের জন্য থাকতে এসেছি আমাদের পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে। তবে নিজেদের এখনও বুড়ো ভাবতে কিছুতেই রাজি হতে পারি না, বড় জোর প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত টেনে নেওয়া যায়। আর একটা তফাতও আছে, যেহেতু এ দেশটা আমার যথেষ্ট পূর্বপরিচিত, রীতিগীতি জানি, তাই গাড়ি ছাড়াও রাস্তায় বেরতে কিংবা বাসে-ট্রামে চড়তে আমার অসুবিধে হয় না। £ বাড়িটার কাছেই অনেক দোকানপাট আছে, সিনেমা হল, লাইব্রেরি আছে। সুতরাং বন্দিদশার প্রশ্ন নেই।
পুপলু আর চান্দ্রেয়ী কাজে বেরিয়ে যায় সকাল সাতটার মধ্যে। ওদের সঙ্গে দেখা ও গল্পটল্প হয় শুধু সন্ধেবেলা। অবশ্য দুপুরে, কাজের ফাঁকে ওরা দুজনেই টেলিফোন করে।
সকালে ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর আমরা চা-টা খাই। তারপর স্বাতী এটা-সেটা করে, কখনও রান্না করে, কখনও টিভির সামনে, কখনও বই হাতে। আর আমি বাধ্য ছাত্রের মতন লেখাপড়ায় বসে যাই। কলকাতার মতন তো এখানে যখন-তখন লোকেরা দেখা করতে আসে না। আর অত বেশি টেলিফোনও বাজে না, তাই নিরুপদ্রবে কাজকর্ম করা যায়।
এক-এক বিকেলে স্বাতী ও আমি বেরিয়ে পড়ি। একদিন গেলাম সিনেমা দেখতে। ভি সি আর-এ বহু ফিল্ম দেখা যায় বটে, কিন্তু টাটকা, নতুন ছবি দেখতে হলে হলে যেতেই হয়। তা ছাড়া, বড় পর্দায় ছবি দেখার স্বাদই আলাদা। পত্রপত্রিকায় একটি স্প্যানিশ ছবির সমালোচনায় বেশ সুখ্যাতি পড়েছি, সেটাই চলছে পায়ে-হাঁটা দূরত্বে একটা মুভি হাউসে।
প্রথম চমক লাগল টিকিট কাটতে গিয়ে।
লেখা আছে, টিকিটের দাম আট ডলার, সেই অনুযায়ী যোলো ডলার দিতে কাউন্টারের বৃদ্ধা মহিলাটি বললেন, মঙ্গলবার সন্ধেয় দাম কম থাকে, দশ ডলারই যথেষ্ট।
মঙ্গলবারের কী এমন বৈশিষ্ট্য যে শুধু সেদিনই টিকিটের দাম সস্তা, তা আমার বোধগম্য হল না।
সেই মহিলাই কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এসে ভেতরের দরজা খুলে দিলেন।
সওয়া পাঁচটায় ছবি আরম্ভ হওয়ার কথা, আমরা একটু আগে এসে পড়েছি! এখনও পর্যন্ত আর কোনও দর্শক নেই। শুধু আমরা দুজন।
আমি বললাম, এ দেশে সিনেমা হল খুব ভালো প্রেম করার জায়গা।
স্বাতী বলল, যাঃ, আশপাশে লোকজন থাকে।
আমি বললাম, এ দেশে প্রেম করার জায়গার অভাব নেই। গাড়ি আছে, কত ফাঁকা জায়গা, কত জনশূন্য পার্ক, কিংবা অ্যাপার্টমেন্ট তো আছেই। তবু সিনেমা হলের মধ্যে প্রেম করায় অল্পবয়সীরা বিশেষ মজা পায়। মোরাভিয়া উপন্যাসে পড়েছি, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা আগে আগে এসে একেবারে পেছনের সারিতে বসে পড়ে। তারপর আলো নিভলে তারা কিছুই করতে বাকি রাখে না। অর্থাৎ সিনেমা দেখা ছাড়া তারা আর সব কিছুই করে।
আমি স্বাতীর কাঁধে হাত রাখতেই সে বলল, এই যাঃ, কেউ এসে পড়বে।
যথা সময়ে ছবি শুরু হয়ে গেল। এবং আর কোনও দর্শক এল না। একজনও না। এ যেন অলীক, অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এত বড় একটা হলে শুধু দুজনের জন্য একটা ফিল্ম চালানো হচ্ছে? মাত্র দশ ডলার পেয়েছে, এদের খরচ হবে কত? আমাদের দেশে কি শুধু দুজনের জন্য ছবি দেখানো হত? নিশ্চয়ই টিকিটের দাম ফেরত দিয়ে বলত, অন্যদিন আসবেন।
শেষ পর্যন্ত আর একজনও এল না। ঝড়-বৃষ্টি নেই, টিকিটের দাম সস্তা, ভালো ছবি, তবু মঙ্গলবার বিকেলে কেউ আসে না? আমরা যে প্রৌঢ়ত্ব ছাড়াতে চলেছি, তার প্রমাণ, আমার হাতখানা স্বাতীর কাধেই শুধু রইল, আর কোনও ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হল না।
শেষ হওয়ার পর বেরিয়ে আসতেই সেই বৃদ্ধা মহিলা মিষ্টি হেসে জিগ্যেস করলেন, কী, উপভোগ করেছ তো?
মাথা ঝুঁকিয়ে বললাম, অবশ্যই।
এরকমভাবে সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম। এবং এই প্রথম আপসোস হল বয়স বাড়ার জন্য।