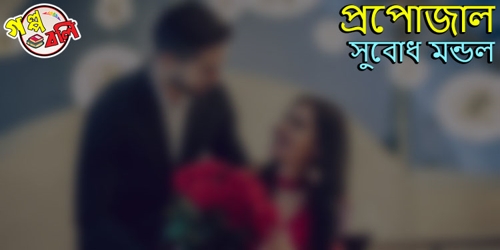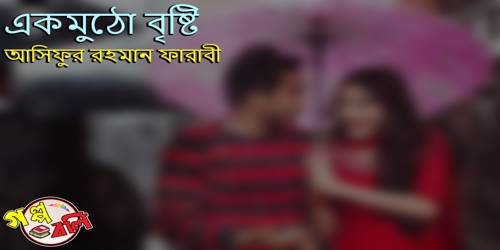একজন খুনিকে দেখতে যাচ্ছি মোহনপুর। আমি বটু দারোগা। গোমোহনী নদীর গা-লাগা যে বোবাডিহির বিল, তার ওপারে লগড়াজলি গাঁয়ে শয়তানটা এসেছে। ধ্রুবপুর আর মোহনপুরের পাশের গাঁ। তারা সরকারের বৈঠকের সামনের ঘোড়ানিম গাছে ঘোড়া বাঁধব, উনি তো মোহনপুরের একপ্রকার জমিদার গোছের মুরুব্বি, অত্যন্ত সজ্জন। ওঁর ছেলে ব্রজলাল ওরফে বিজু ছিল আমার স্কুলের সহপাঠী, বন্ধু। ওদের ওখানে ঘোড়া বেঁধে দফাদার মহেশ রুইদাসকে দিয়ে তলব নেব শয়তানটার।
ঘোড়ায় যাচ্ছি শুনে আমার ছোট ভাগ্নি মিনু একেবারে নেচে উঠল, সে-ও যাবে সঙ্গে।
আমার নিজের সংসার বলতে কিছু নেই। থাকবে কোত্থেকে! বয়েস চল্লিশ ছুঁয়েছে। বিয়েশাদি করা হয়ে উঠল না। বিয়ের আর ইচ্ছেও নেই। বিধবা দিদির ছোট সংসারটা আমার কাঁধে এসে পড়েছে।
যা হোক। একটা টাট্টু করে চড়বড় করে ছুটব।
মিনু সিকদার আদুরে গলায় বলল, ‘নিয়া চলো মামু!’
দিদি বলল, ‘ওই দেখো! তান ধরলে মেয়ে! তুই কী করে যাবি মুখপুড়ি!?’
— ‘দেখব!’
— ‘দেখব মানে?’ দিদি রেগে ওঠে।
— ‘ননা গুণ্ডাকে দেখব!’ জেদের গলায় বলে ওঠে ভাগ্নিটা।
— ‘ওটা গুণ্ডা নয় মিনি! ওটা খুনি। তার চেয়েও খারাপ!’ বললাম আমি।
— ‘হোক। তা-ই দেখব!’ গলায় জেদের তরঙ্গ খেলিয়ে বলল মিনু সিকদার।
মাত্র বছর এগারো বয়েস। বড্ড পাকা। ক্লাস সিক্সের ছাত্রী। প্রায় সব ব্যাপারে নিজের মতামত দেওয়ার স্বাভাবিক শক্তি নিয়েই যেন সে জন্মেছে; হতে পারে বয়েসের তুলনায় ওর কাণ্ডজ্ঞান ও ভাববার ক্ষমতা কিছু বেশি। কিন্তু ননা যে আসলে কী, তা ওকে বলি কী করে? ননা যে আমার কতবড় দুশমন মিনুকে কেউ কি বুঝিয়ে বলেছে?
আমি বটেশ্বর মিত্র। উচ্চশিক্ষিত। কিন্তু চাকরির আকাল বলে পুলিশে চাকরি নিয়ে জীবন কাটালাম। আমিই থানার বড়বাবু।
শ্বেতপদ্মের মতো স্নিগ্ধ সাদা ঘোড়ার রং। ওর নাম নটু, পুরো নাম নোটন মিত্র। ও নটু আর আমি বটু—এই হচ্ছে আদিকথা। নটু আবার মিনিকে বড্ড ভালোবাসে। মিনি কিংবা মিনু—যখন যেমন আসে ডাকি। মিনু নটুকে বটো-বটো বললেই বসে গিয়ে পিঠ পেতে দেয়।
বর্ষাকালে নোটনকে ছাড়া আমার চলে না। বর্ষার পরও মাসখানেক ওর পিঠে চড়ে গ্রাম-শাসন করতে বার হই। কারণ তখন পর্যন্ত কিছু কিছু জায়গা এবং খালবিল জলে ডুবে থাকে—রাস্তার কাদা শুকায় না। কিন্তু শরত্-ই সবচেয়ে স্নিগ্ধ ঋতু; আকাশে তখন মেঘের নানান ছবি ফুটে ওঠে, মেঘে জল তেমন থাকে না, সাদা জলশূন্য মেঘ চিত্র রচনা করে; আকাশে স্বর্ণরথ ভেসে ওঠে।
কত বড় আকাশের তলায় এসে দাঁড়ালাম। মিনিকে নটুর পিঠে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি লাগাম ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। কদমতলা হয়ে ছোট নদীর পাড় ধরে এগোব। কামারপাড়া-ঘোষপাড়া হয়ে ঘোষপাড়ার সাঁকো পেরোব; তারপর ফরাজি পাড়া পড়বে। ফরাজি পাড়া শেষ হলে কোদালকাটির দাঁড়া। দাঁড়া বলতে, এখানে রয়েছে স্লুইস গেট। নদী এখানে বোবাডিহির বিলের সঙ্গে ওই গেটের ভিতর দিয়ে মিশেছে।
আগে ছিলাম দূরের থানায়। এখন এসেছি নিজের গঞ্জের থানায়। এই গ্রাম আমার, আমারই গ্রাম। চারদিকের বাইশটা গ্রাম, আমারই অঞ্চল। ভালো লাগে এ কথা ভেবে যে, আমি আমারই অঞ্চলে পুলিশের ডিউটি করে গ্রামগুলোকে শাসনে রেখেছি। প্রতিটি লোকে আমাকে চেনে। সকলে কপালে হাত ঠেকিয়ে সালাম ঠোকে। কেউ কেউ হাত জোড় করে নমস্কার দেয়। মুর্শিদাবাদের মুসলিমপ্রধান অঞ্চল, হিন্দুর সংখ্যা নিতান্ত কম। কিন্তু মুসলিমরা আমাকে তাদেরই সন্তান মনে করে। কথাটা কাউকে তুষ্ট করার জন্য বলছি না; এই যে সন্তান মনে করাটা, এটা ষোলআনা খাঁটি।
ফরাজি পাড়ায় এসেই ফরাজির বাগানের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ি। ছোট-ছোট কাঁঠালগাছ আশ্চর্য সবুজ, যেন পাতার গায়ে তেল মাখানো হয়েছে এমনই ভেজা-ভেজা লাবণ্য। এ বাগানের মালিক তবা ফরাজি। নানান গাছপালা। বিচিত্র উদ্ভিদময় এই ভূখণ্ড। নদীর কোলে।
যখনকার কথা লিখছি, তখনকার দিনে সারা তল্লাট ঢুঁড়ে দেখলে একটি-দুটির বেশি ম্যাট্রিকুলেশন পাস লোক পাওয়া যেত না। তবে দু-চারটি বা দু-পাঁচটি ‘নন-ম্যাট্রিক’ পাওয়া যেত। অর্থাত্ ম্যাট্রিকুলেশন ফেল মিলত। নন-ম্যাট্রিকেরও তখন বেশ সম্মান ছিল। লোকে গুরুত্ব বুঝাতে বলত, উনি কিন্তু নন-ম্যাট্রিক, পেটে কালির আঁচড় যথেষ্টই আছে।
তবা নন-ম্যাট্রিক চাষি। ওর অনেক গুণ। নানান হাতের কাজ জানে। মাছ ধরার জাল। বাঁশের খিল দিয়ে বোনা একধরনের মাছ ধরার খাঁচা, যাকে মুর্শিদাবাদী লব্জে বলা হতো ‘বিত্তি’। এই রকম আরো অনেক কাজ জানে। তবে ওর সবচেয়ে নামডাক আছে ঘোড়াকে তাঁবে এনে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারে।
নটু তবারই ট্রেনিং পেয়েছে। শুধু তা-ই নয়, একে নগর (গ্রামের নাম) থেকে কিনে এনেছিল তবাই। আমার পছন্দ হওয়াতে কেনা দামে নোটনকে বেচে দেয় সে। সে কারণে ওর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বেশ উপাদেয়। এ পথে এলে তবার সঙ্গে আমার কথা হয়—এই জায়গাটা আশ্চর্য সুন্দর। নদীর ঢালে বিঘা বাইশ জমিতে তার হাতে গড়া বাগান; শস্য-ফল-সবজির ফলন আর নানান পাখির মেলা, দেখবার মতন ব্যাপার বটে।
তবাকে দেখলেই নোটন (নটু) চিনতে পারে—ওর হাতেই তো ও মানুষ হয়েছে। দেখবামাত্রই লেজ নাচিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। মুখ বাড়িয়ে তবার কাছে আদর চায়।
আজও ঠিক একই আচরণ শুরু করল নটু। আমি হাঁক দিতেই নদীর কিনারা থেকে উঠে এল তবা।
— ‘মোহনপুর-লগড়াজলি যাচ্ছেন বড়বাবু!’ বলতে বলতে এবং ঘাড়ের গামছায় হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে এল তবারক।
নটু ওর দিকে মুখ বাড়িয়ে দিলো। নটুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো তবা এবং মিনিকে বলল, ‘তুমি তো আম্মা একটি মরিচ গুড়গুড়ি, ওই পাখি সাত-আটটি ইখানে চরে। দেখবা আম্মা?’
আমি বললাম, ‘শয়তানটা লগড়াজলিতে এসেছে যখন, এখন কী করি?’
তবা যে আমার সোর্স, এ কথা সংসার টের পায়নি কখনো। কারণ, তবা কাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়, আমিও জানি না।
তবা কী যেন বলতে যাচ্ছিল, হঠাত্ হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ‘দাঁড়াও তবারক, এ দিকে এসো, অন্য একটা কথা আছে।’
এই বলে ঢালে নেমে যেতে থাকি। গাছপালার ভিতর দিয়ে। নটু মিনিকে পিঠে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। নদীর কিনারা অবধি চলে আসি আমরা।
— ‘ননা নন্দিনীকে ধর্ষণ করার পর খুন করেছিল; অবশ্য সংশয় আছে—খুন করেছিল নাকি করে নাই! নন্দিনী তখন মাত্র চৌদ্দ; ক্লাস এইট। শিশাডিহির মাঠে একলা পেয়ে সর্বনাশ করে; শিশাডিহি ঢোকার মুখে এসে মাধবপুরের পাপড়ি খাতুনের সঙ্গে আলাদা হয়ে একা শিশাডিহি পার হচ্ছিল নন্দিনী। ননা তখন এক সন্তানের বাপ। বয়েস মাত্র সতেরো। বউ তেরো বছর। ওই বয়েসেই বউয়ের গর্ভসঞ্চার করে ননা। নন্দিনীকে ধর্ষণ করার পর মাঠে মৃত ভেবে ফেলে রেখে পূর্ব-পাকিস্তান পালিয়ে যায়। ওখানে দ্বিতীয় দফা নিকাহ্ করে। কত বছর বাদে লগড়াজলি ফিরেছে। এখানে এসে দেখল ওর প্রথম বউটা অন্যের বউ হয়ে সংসার করছে। ওর প্রথম সন্তানটা জলে ডুবে মারা গেছে বোবা বিলে। ডোঙায় করে ভেসে গিয়ে মরেছে। সাঁতার জানত না। বাচ্চাটার নাম ছিল মাধব শেখ।
— ‘সব জানি বড়বাবু!’
— ‘ননার প্রথম বউ, মাধবের মা সোনাভান দেখেছে। লগড়াজলির উঁচু সড়কের নিচে গা-লাগা বোবা বিল, ওই বিলে নাকি জ্যোত্স্নারাতে ওই ডোঙাটা মাধবকে নিয়ে আজও ভেসে বেড়ায়; যখন বেশুমার জোনাকি ওড়ে, তখন অন্ধকার রাতে ডোঙাটা ভাসে, মাধবের গায়ে-চোখেমুখে ঝাঁক ঝাঁক জোনাকি বসে থাকে। লোকে এই দৃশ্যও দেখে ফেলে হঠাত্-হঠাত্। সত্য?’
— ‘সত্য বইকি বড়বাবু!’
— ‘কিন্তু এই গল্প মিনিকে শুনিয়ে ঠিক করিনি।’
— ‘কেন?’
—‘মিনি বলছে, সে ডোঙাটা দেখবে।’
— ‘বেশ তো!’
‘বেশ তো’ শুনে আমি অবাক হলাম; কিছুটা চমকে উঠলাম।
বললাম, ‘বেশ তো মানে কী? দেখো তবারক, মিনিকে আমি কিছুতেই মোহনপুর-লগড়াজলি নিয়ে যাব না। ধ্রুবপুর নিয়ে যাব না। ও ননাকে দেখতে চাইছে, কী সাংঘাতিক কথা! ওই রকম মহাপাপী ধর্ষক; ওকে কেন দেখতে চাইবে মিনি? না, এ ঠিক নয়। আমি নিজে দেখব, সে এক আলাদা কথা!’
কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তবা ফরাজি। কী যেন চিন্তা করতে করতে নদীর ওপারে কাছারিপাড়ার ঘাটের দিকে চেয়ে রইল। নদীতে এখন ফিরতি স্রোত। গোমোহনীর জল বড় নদী ভৈরবে ফিরে যাচ্ছে। স্রোত আমাদের দিকেই বয়ে আসছে। এদিকে নদীর জলের ওপর দিয়ে স্রোতের উল্টো দিকে বয়ে যাচ্ছে মাঝারি বেগের এক উল্টাপাল্টা হাওয়া। কাছারিপাড়ার নেতাইয়ের ঘাটে জল-খুঁটায় বাঁধা রয়েছে একখানি ডিঙি নৌকো। আর একখানি তালকাঠের ডোঙা। দুটিই ছটফট করে দুলছে। ডিঙিতে ছোট আকারের পাল খাটানো।
তবা হঠাত্ বলে উঠল, ‘লগড়াজলিতে ননা বলতে কি কোনো জায়গাই পেল না। মাফ করবেন বড়োবাবু, আমি মসজিদের ইমামকে দিয়ে যা বলার এবং যে কথা লোকের কানে তোলার দরকার সবই করেছি। ইমাম সাহেবের উদ্যোগে ননাকে আরবি পানিশমেন্ট দেওয়া হয়েছে বাবু।’
এই বলে হঠাত্-ই গলা তুলে মিষ্টি করে একটা হাঁক দেয় তবারক, ‘আয় নোটন মিত্তির চলে আয়!’
আবার আমি চমকে উঠি। পিছনে ফিরে তাকাই। একটু বাদে নোটনকে ঢালে নেমে আসতে দেখা যায় বাগানের ছায়ারোদের ভিতর দিয়ে।
— ‘ইট-পাথর বর্ষণ হলো খুব। বুঝলেন বড়ো বাবু! তার আগে ইমাম ননাকে একখানা মাথাল উপহার দিয়ে বলল, নাও পরে থাকো। তা নইলে মাথা বাঁচবে না ননা।’
এই বলে কাছারিপাড়ার ঘাটের দিকে চেয়ে রইল তবা ফরাজি।
আমাদের পিছনে এসে দাঁড়াল নোটন মিত্র। ওর পিঠে রানির মতো বসে রয়েছে মিনি। নটুকে ওর ছেলেবেলায় ডাকা হতো নোটন (নটু) ফরাজি নামে।
— ‘মহাপাপীকে ঝাঁক-ঝাঁক পাথর মারছে বাচ্চারা। ননা ইয়ে… যাকে বলে মহাপাতক, জবর গুন্থেগার (পাপী); বড়ো পাপ করেছে নলা। পাথর ছুড়ে ছুড়ে ননাকে গাঁ-ছাড়া করার যাকে বলে মচ্ছব চলছে আম্মা।
এই বলে বিরাম নেওয়ার জন্য থামল তবারক।
মিনিকেই সে ‘আম্মা’ বলে সম্বোধন করেছে; আবার করল। নদীর ধারে ধারে মরিচ গুড়গুড়ি পাখিরা কী যেন খুঁটে নিতে ব্যস্ত। একটি মোহনচূড়া তার ঝুঁটি নিয়ে খেলা করছে।
— ‘তারপর কী হলো বলো! শুদুমুদু আম্মা আম্মা করছ!’ বলে উঠল মিনি।
তা-ই শুনে হাহা করে হেসে উঠল তবারক।
তারপর হাসি থামিয়ে বলল, ‘তা-ই তো আম্মা। সবই কেবল শুদুমুদু। কিন্তু নন্দিনীকে যা করা হয় তা তো শুদুমুদু ছিল না!’
সূর্য এখন পশ্চিম আকাশে। নদীর ওপর সামান্য ঢলেছে। রোদের রং গলিত সোনার মতো নরম ঝলকে চারদিককে ভরিয়ে তুলেছে।
— ‘লোকটা যেমন ঘায়েল হলো, তেমনই জেরবার। সোনাভান রাস্তার পাশে আমগাছ তলায় দাঁড়িয়ে নির্বিকার মনে দেখে গেল সমস্ত। একটা কথাও বলল না। সোনাভান এখন অন্যের বিবি হয়েছে কিনা! যা হোক। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। লোকটা, মানে ননা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে বোবা বিলের ধারে দাঁড়িয়ে ছেলের নাম ধরে ডেকে ওঠে, ‘… মাধব, মাধব। আমারে বাঁচাও আব্বা।’ ওই আর্ত চিত্কার লগড়াজলির অনেকে শুনেছে! তখন সন্ধ্যার আকাশে গোল চাঁদ ভাসছে আম্মা!’
— ‘মাধব এল?’
— ‘কোথা থেকে আসবে মিনু, মাধব তো বেঁচে নেই। ওই একটা ডোঙা করে ভেসে গিয়েছিল। সাঁতার জানত না। বাঁচেনি। স্রোত টানছিল কোদালকাটির স্লুইস গেটের দিকে। ভয়াবহ সেই জলের গোত্তা-জড়ানো টান। কোঁ কোঁ করে ডেকে ওঠে গোত্তা! ওই টানে পড়লে যে সাঁতার জানে সেও বাঁচে না আম্মা!’
— ‘স্লুইস গেট দেখব মামু! দেখাও! একবারটি দেখাও, আর দেখাও ডোঙাটা!’ বলে উঠল মিনি।
— ‘দেখ মিনি, সব একসঙ্গে দেখা যায় না। আজ শুধু ডোঙাটা। আমরা মোহনপুর যাচ্ছি না।’ বলে উঠি আমি।
— ‘তা হলে পাশের গাঁয়ে চলো!’
— ‘মানে!’
— ‘তুমি বলেছ, ধ্রুবপুরে রাতে ধ্রুবতারা স্পষ্ট করে দেখা যায়, বলেছ, ওই ধ্রুবতারার নিচের গ্রামটা ধ্রুবপুর। বলনি?’
— ‘তাতে কী?’
— ‘কী আবার। ধ্রুবপুরে গিয়ে নটুর পিঠে বসে তারাটা দেখব, হাত দিয়ে ছোঁয়া যাবে মামু?’
— ‘এই তা হলে প্ল্যান? শুনে রাখ মিনি, হাত বাড়ালেই সব হয় না। বলি কি তবা, এবারের মতো তুমিই সামলাও।’
তবা ফরাজি বলে উঠল, ‘সামলাব কী! ওই দেখুন না ক্যানে! খোয়াজা খিজির, যা করবার করতে লেগে পড়েছে! ডোঙা আর ডিঙিতে তাল দিচ্ছে জুলকার নাইন। দেখো, দেখো আম্মা!’
মিনি অবাক হলো। খাজা খিজির! কে সে? ওই জুলকার নাইনই বা কে?
— ‘বুঝলে না আম্মা? খাজা খিজির হলো পানির ফরিস্তা। খিজির আর জুলকার নাইন মিলেমিশে একটা গল্প যা দাঁড়ায়, তা হলো এই দুই মিলে পানির পির আছেন একজনা। শুনেছি, জুলকার আসলে আলেকজান্ডার, মস্ত একজন বীর। যা হোক, তিনিই খিজির। পানির ফরিস্তা। এখন জলের উপর ডোঙা আর ডিঙি নাচাচ্ছেন। বোঝো আম্মা!’ বলে উঠে কাছারিপাড়ার ঘাটের দিকে পরম ঔত্সুক্যে চেয়ে রইল তবা ফরাজি।
আর এরকম গল্প পেলে মিনির তো আহ্লাদের সীমা থাকে না।
তবা খাজা খিজির না বলে খোয়াজা খিজির বলছে। জ-এর উচ্চারণ করছে ইংরেজি জেড অক্ষরের মতো ধ্বনি দিয়ে। আর তাইতেই তাক লেগে যাচ্ছে মিনির।
— ‘শোনা যায়, চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙা যখন ডুবে গেল, তারপর সেই সোনাদানা ভর্তি ডিঙা এই খিজিরই কাঁধে করে পানির উপর ঠেলে তুলেছিল। পাতাল থেকে। বোঝো!’
বলে উঠল তবারক ফরাজি। এ এক আশ্চর্য মানুষ। কোথায় আলেকজান্ডার আর কোথায় পানির পির বা ফরিস্তা একসঙ্গে মিলে গিয়ে এক বিচিত্র গল্প তয়ের করে চাঁদ সওদাগরকে তার মধ্যে সাঁধ করিয়ে নিলে!
তবার নিজেরও কিছু অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড আছে বলে শোনা যায়। তবে আমি নিজে কখনো তেমন কাণ্ড কিছু প্রত্যক্ষ করিনি।
এই জায়গাটা বড্ড রহস্যময়। নদীর বিস্তীর্ণ পাড়ের বাগান ও শস্যক্ষেত্র; ওই দিকের কাছারিপাড়ার নেতার ঘাট—এই নদীও ঠিক জাগতিক নয় যেন—অনেকটা স্বর্গের নদীর মতো অলৌকিক। এখানকার বাতাস অত্যন্ত সজীব-স্বাস্থ্যকর; বাতাসে ফরিস্তার পবিত্র নিঃশ্বাস মাখানো।
নদীর জল-ঘেঁষে একটি গাবগাছ—হঠাত্ চোখ পড়ে, গাছের একটা ডালে ঝুলে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা মধুচক্র—মৌমাছিগুলো পাহাড়ি, খুদে মৌমাছি নয়, মোটামোটা আকৃতি। চক্রটি ঝুলে রয়েছে নদীর স্রোতের ওপর, জল ছোঁব-ছোঁব করছে। গাবগাছটাকে ঘিরে উড়ছে একদল কমলা বাদুড়। দেখে মনে হচ্ছে অদ্ভুত ধরনের পাখি ওগুলো। ওদের বুকটা কমলা রঙের।
— ‘ওরা কি মধু খাবে?’ আনমনা ভাবে কথাগুলো আমার মুখ থেকে ফসকে বার হলো।
— ‘কারা মধু খাবে মামা?’
অমনি জানতে চাইল মিনি। কথা পড়তে দেয় না।
— ‘ওগুলো কী পাখি তবা? বাদুড়?’ জানতে চাইলাম।
তবারক বলল, ‘ঠিকই ধরেছেন বাবু। কমলা বাদুড়। চেষ্টায় আছে।’
বাতাসে হালকা হিমের ছোঁয়া। এই জায়গাটায় বাংলার নিজস্ব পাখি যারা, তাদের অধিকাংশেরই দেখা মেলে। সাতটা ঝুঁটি ভরত গান গাইছে। আর বেশ ক’টা বেনে বউ পিলো-পিলো করছে আর হঠাত্ থেমে গিয়ে কর্কশ গলায় চিয়াহ্-চিয়াহ্ করছে—এ কেমন স্বভাব বাপু! গাও তো ভালো করে গাও, নইলে ছেড়ে দাও। বরং ঝুঁটি ভরতগুলো, যা পারছে করুক।
— ‘তবে হ্যাঁ, মধুখোর পাখি হচ্ছে ইষ্টিকুটুম পাখিগুলো, মানে এই বেনে বউ পাখিরা। এরাই খোকা হোক, খোকা হোক করে ঘরের বউদের লোভায়। বুঝলে আম্মা!’ বলে উঠল তবা ফরাজি।
আর এই সময়ই কাছারিপাড়ার নেতাইয়ের ঘাটের ডোঙাটা খুলে গেল বাতাস আর স্রোতের ধাক্কায়—খুলে গেল মানে যে-জলখুঁটায় ওটা বাঁধা ছিল সরু দড়িতে, সেই বাঁধন খুলে গেল। দড়ি নয়, ডোঙা বাঁধা ছিল মুগার পিছল হলুদ সুতোয়। কোনো জল-ফরিস্তায় হয়তো বাঁধন খুলেছে।
এ সংসার ফরিস্তাময়। তবা তো সেই রকমই বলে। যারা গভীর ধার্মিক, তারা তো করেই, যারা মোটামুটি বিশ্বাসী, তারাও খাজা খিজির বিশ্বাস করে।
খিজিরই মুগা সুতোর বাঁধন খুলে দিলো ডোঙাটার। আমি যা ভাবছি, তা ঠিক কি না যাচিয়ে নিতে হলে তবাকেই জিজ্ঞেস করতে হয়। কিন্তু আমি নিশ্চিত পানির পির তার খেলা শুরু করে দিয়েছে। ডোঙাটা ধীরে ধীরে ফিরতি জলের স্রোত ধরে এদিকে ভেসে আসতে লাগল।
ঘোড়ার পিঠে বসে ডোঙাটা ওইভাবে জলে ভেসে চলে আসতে দেখে মিনির তো বিস্ময়ের সীমা রইল না।
— ‘এই ডোঙায় করে ভেসে গিয়েছিল মাধব?’
জানতে চেয়ে বলে উঠল মিনি।
— ‘ওমা! নৌকোটাও খুলে গেল তবা কাকা? দেখো, দেখো!’
মিনিই গলা তুলে বলে উঠল হঠাত্।
খিজির পুরোদস্তুর খেলা খেলছে। নেতার ঘাট থেকে ভেসে আসছে খিজিরের নৌকা—অনেকখানিই ভেলার মতো দেখতে।
সোনালি হলুদ রঙের পাখিগুলো, কাশ্মিরি ইষ্টিকুটুম, যার আর একটা নাম কৃষ্ণ গোকুল, তারা বাংলার ‘খোকা হোক’ নয়, কাশ্মিরি হলুদ পাখিরা পুরোপুরি হলুদ; বাংলার বেনেবউদের মাথা-গলা এবং বুকের ওপরের দিকটা তেল চকচকে গাঢ় কালো আর কাশ্মিরিগুলোর মাথাসুদ্দো সর্বাঙ্গ সোনালি হলুদ। বাতাসে ঈষত্ হিম জড়ালেই ওদের, ওই কাশ্মিরি বা হিমালয়া বেনেবউদের এই ফরাজি ভূখণ্ডে দেখা যায়। এরাও বাংলায় এসে ‘খোকা হোক’ বলতে শিখে যায়।
ওরা বাংলার বেনেবউদের সঙ্গে নিয়ে চিয়াহ্ চিয়াহ্ করতে করতে ডোঙার দিকে উড়ে গেল। তারপর ডোঙার কানায় বসে গেল সবাই। ওদের দেখে ঝুঁটি ভরতের সাত জনা ডোঙার দিকে উড়ে গিয়ে জায়গা না পেয়ে ডোঙাটার ওপর এক মানুষ উচ্চতায় ভেসে উড়ে খেলে যেতে লাগল। এরা গান গাইছে বটে, কিন্তু পুরোপুরি সুরে লাগছে না। বসন্তে এদের মজলিস হবে।
— ‘ওই দেখো। নৌকোটাও ছেড়ে দিয়েছে খোয়াজা বাবা। আস্তে আস্তে বাইচ লাগবে।’
বলে উঠল তবা।
তীই-উর, তীই-উর ডাকছে সাতটি ঝুঁটি ভরত। বেশ মিষ্টি শোনাচ্ছে। চিয়াহ্ চিয়াহ্ করছে বেনেবউয়ের দল।
তবা ফরাজি হঠাত্ হাহাকার করে ওঠে, ‘হায় রসুল-আল্লাহ, উল্টা-হাওয়া দিলে গোমানির ফরিস্তা, ডোঙা-নৌকা নেতার ঘাটে ফিরে যাচ্ছে আম্মা! আজ আর হলো না বোধহয়।’
কাছারিপাড়ার নেতাইয়ের ঘাটে ফিরে গেল নৌকা। ডোঙাও ফিরে গেল। এখান থেকে ঘাট দূরে। কিন্তু সুদূর তো নয়। দৃশ্য চোখে পড়ে। ঘাটে জলসিঁড়ি আছে। পাড়ে ঘাস-বিস্তৃত সরু-সাদা সিঁথিপথ—ওই পথ ধরে নেমে এল একটি আধা-ঘোমটা টানা বউ। নদীর পাড়ে ছ’ঘরা বসতি। ঘোষ-মুনশি-মির-ওঝা-মন্ডল। ওই বসতির বউ ওটি। পাড়ের কিনারে ভিড়েছে নৌকা আর ডোঙা। বউ ডোঙা নৌকা বেঁধে দেয় জল-খুঁটায়। হাওয়ার দমকায় ঘোমটা নেমে যায় কাঁধে। বেরিরে আসে নন্দিনীর মতো একটা পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত মুখ। কিশোরী নয়। যুবতী। এ কেমন করে হয়! কে ওটা? তবা বলল, ‘হিয়া মির।’
দুই
পূর্ণ যুবতী তো বটেই। বোধ হয় এ নারী মধ্য যৌবনের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তবার বারবার মনে হচ্ছে, যেন এ নন্দিনী চক্রবর্তীই যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে যৌবনেরও প্রায় মধ্যভাগে পৌঁছে গেছে। কিন্তু এর নামটা তো অন্যরকম শোনাল। ঠিক বুঝলাম না।
— ‘তুমি নামটা যেন কী বললে তবা?’
— ‘বললাম, হিয়া মির।’
— ‘কী আমির?’
— ‘হিয়া মির।’ আমির নয় বড়ো বাবু। হিয়া মির। হিয়া মুনশি নয়। ও হলো মির।’
— ‘একসঙ্গে জড়িয়ে এমন করে বলছ! হিয়ামির। হিয়া শুনছি ‘ইয়া’। ফলে শুনছি ইয়া আমির! যা হোক। ভালোই হলো তবা।’
— ‘জি, বড়ো বাবু!’
— ‘কিন্তু সমস্যাও তো হলো তবা। বুকের ভিতরটা কেমন ছ্যাঁত্ করে উঠল।’
— ‘জি, বড়ো বাবু।’
— ‘চেহারায় এত মিল!’
— ‘আপনারও মনে হচ্ছে যে নন্দিনী বেঁচে থাকলে…!’
— ‘ঠিক তা-ই। কিন্তু এ রকমও হতে পারে!’
— ‘পারে বইকি বড়ো বাবু!’
— ‘কী করে পারে!’
এক আশ্চর্য পিপাসা যেন আমার গলায় কথা বলে উঠল। এই ঘটনা সবটা বুঝে উঠতে না পারলেও মিনু কী যেন একটা ঠাহর করেছে!
— ‘ওটা বউ! মামা, কার বউ মামা!’
বলে উঠল মিনি।
— ‘তুই বুঝবি না মিনি!’ বলে উঠি আমি।
— ‘তুমিই তা হলে বলো, কাকাবাবু!’ বলল মিনি।
এই পাকা মেয়েটাকে নিয়ে আর পারা যায় না! কিন্তু মিনিও কি চিনে নিতে পেরেছে নন্দিনীকে? মিনি তো কিশোরী নন্দিনীকে ফটোয় দেখেছে! ওই কিশোরীই যে এই মধ্য যৌবনের বউটা, কোথাও তো তেমন আভাস রয়েছেই, ওই বউটার চেহারায়।
নন্দিনীর ছোট মামার একটা ফটো তোলার দোকান ছিল গঞ্জে—ওই গঞ্জেই ছিল হাইস্কুল। আমি ওল্ড হায়ার সেকেন্ডারির ছাত্র ছিলাম। নন্দিনীও সেই আমলের ছাত্রী ছিল। যখন আমি ইলেভেন, তখন নন্দিনী চক্রবর্তী এইট। সেকালে রাস্তাঘাট ছিল কাঁচা মাটির পথ, যানবাহন বলতে ঘোড়া আর গরুর গাড়ি। লোকে দু-চার ক্রোশ পায়ে হেঁটেই পার করত। এখনো পথ কাঁচাই; দু-এক জায়গায় মোরাস পড়েছে।
স্কুলে দেড়টা থেকে দুটো—দুপুরের এই আধঘণ্টা ছিল টিফিন পিরিয়ড। অর্থাত্ বিরতি। চাত্রছাত্রীর ৯৯ শতাংশ ছিল গরিব। ফলে টিফিনে টিফিন খাওয়ার ব্যাপার ছিল না। কেউ-কেউ অবশ্য সাদা ন্যাকড়ায় বেঁধে চালভাজা আনত।
শুধু একটা ঘটনা প্রায় হামেশাই ঘটত। টিফিনে নন্দিনী আমাকে ওর মামার দোকানে টেনে নিয়ে যেত। মামা শালপাতার ঠোঙায় করে আমাদের দুজনকে সদরঘাটের মেঠাইয়ের দোকান থেকে আনিয়ে নিয়ে মেঠাই দিত খেতে। আর মাঝে মাঝেই আমাদের দুজনের ছবি তুলত। আমি গরিব হলেও আমার চোখেমুখে নাকি আভিজাত্যের ছাপ ছিল। ছোট মামা বীরু চক্রবর্তী বলত, আমাদের দুজনেরই নাকি ফটোজেনিক ফেস; ছবি ভালো আসে। বীরু আসলে বীরেন্দ্রনারায়ণ। ওঁর এক খাস নাম ছিল গুলাল চক্রবর্তী।
কিছু নায়িক-নায়িকার ছবির সঙ্গে আমাদের ছবি দিয়েও স্টুডিও সাজিয়েছিলেন বীরু মামা। সেই ছবির দিকে চেয়ে দেখে আমার বেশ গর্ব হতো, আবার বেশ সংকোচও হতো। কিন্তু নন্দিনী তেমন কোনো লজ্জা পাচ্ছে বলে মনে হতো না।
ওর আমার একসঙ্গে একখানা আর ওর একলা একখানা ছবি আমার বেজায় পছন্দ হয়েছিল। বীরু মামা একদিন বলল, যা ওই দুইখানা ফটোগ্রাফ যখন এত মনে ধরেছে, তখন ছোট সাইজ; না বড়ো সাইজই দিচ্ছি তোকে। ঘরে রাখবি। এই নে। ফটোর পিছনে গুলাল স্টুডিওর ‘সিল’ মেরে দিলাম।
এই ভাবে আমার কাছে রয়ে গেল নন্দিনীর কৈশোর।
কিন্তু স্টুডিও থেকে নেমে গেল নন্দিনী ও আমার ছবি। কারণ নন্দিনীকে ধর্ষণ করে মাঠের মধ্যে মৃত অবস্থায় ফেলে রেখে পূর্ব পাকিস্তান পালাল ননা।
কিন্তু যদি এমন হয়, মৃত অবস্থায় শিশাডিহির মাঠে যে নন্দিনী পড়ে রইল, সে আসলে বেঁচে ছিল, সে মরেনি এবং ওই হিয়া মির আর নন্দিনী একই নারী, যে ছিল চৌদ্দ-পনের, এখন সে ৩৫-৩৬। কিন্তু এ গল্প কীভাবে সম্ভব?
— ‘ওই বউটাকে আমি চিনি মামু। ওটা বউ না!’
সহসা বলে উঠল মিনি। আমি আর তবারক বেশ অবাকই হলাম।
— ‘ওটা বউ নয় তো কী?’
আমি জানতে চাই।
মিনি বলল, ‘নন্দিনী’।
শুনেছি বাচ্চারাই বেশি মানুষ চিনতে পারে। মানুষের বাইরেরটা এবং ভেতরেরটা, সমদৃষ্টিতে চেনে। অবশ্য নন্দিনীর ছবিটা মিনির মুখস্থ। সে কী করে বুঝে গেছে, ওই ছবির কিশোরীই আমার সর্বস্ব। আমার প্রেম, আমার হূদয়, আমার জীবন।
— ‘ওই বউটার নাম হিয়া। ও কেন নন্দিনী হতে যাবে আম্মা’?
বলে উঠল কেমন একটা সুর করে তবারক।
— ‘না, ওটা বউ না! ও নন্দিনী!’
গলায় আরও নিশ্চিন্ততা মিনির।
এই অবস্থায় আমার বুকের মধ্যে এক আশ্চর্য কষ্ট বেজে উঠল, বেশ একটা দুর্বোধ্য কষ্ট।
আমার এই জীবনটাকে নিয়ে খাজা খিজিরের কী ইচ্ছে, তা তো মোটে জানি না। জলের বিধাতা কী ভাবছে কে জানে!
এদিকে আকাশ থেকে সোনা গলছে, সাদা মেঘের মিনার ছুঁয়ে, রথ রাঙিয়ে, ঘাটের কিনারে জলের ওপর ঝুঁকে থাকা আশ্চর্য ধবল টগরে সে আলো পড়ে জীবনের কী স্পৃহা যে জাগিয়ে তোলে বুঝে পাই না।
হিয়া নৌকো এবং ডোঙাটা আটকাল। কোমরের পেতলের ঘড়া নৌকোর ওপর রাখল। তারপর নৌকোয় চড়ে বসল নিতান্ত সাবধানে। হঠাত্ হাওয়া পড়ে গেল। তারপর কিছুক্ষণ বাদে উল্টো দিক থেকে হাওয়া ছাড়ল।
তবা চুপ করে রয়েছে। কথা বলছে না। মনে হচ্ছিল কিছু বলবে। বলছে না।
— ‘তবা, তুমি তো আমার সোর্স; কিছু বল!’
তবা তার কাঁধের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা মিনিকে স্পষ্ট করে একবার দেখে নিয়ে চোখ নামিয়ে মাথা নিচু করে রইল। ওর মাথায় একখানা গোল সাদা টুপি, গায়ে বেনিয়ান, কাঁধে ঝোলানো রঙিন গামছা। ওর সারাটা মুখ উত্তম কুমারের মতো করে কামানো। থুতনিতে চাট্টি দাড়ি রেখে তবা মুসলমান সাজার চেষ্টা কখনো করেনি। মাথার গোল টুপিটা সব সময় মাথায় থাকে এমনও নয়। অনেক সময় সুন্দর করে সামনে পরে বাগানে ও শস্য খেতে কাজ করে।
কী করে রটেছে জানি না, তবা নাকি জিন তাঁবে করেছে শোনা যায়, নিজেই প্রবল জ্যোত্স্না রাতে সাদা অশ্ব হয়ে নানা স্থানে ছুটে বেড়ায়।
আসলে ও নিজেই এসব প্রচার করে কি না বলতে পারব না। তবে এ কথা ঠিক, ও এক বিচিত্র রহস্যময় মানুষ। আমার চেয়ে বয়েসে বছর পনেরো বড় হবে। অথচ আমি ওকে ‘তুমি’ করে বলি। ও আমাকে ‘আপনি-আজ্ঞে’ করে। কারণ আমি থানার বড় বাবু।
— ‘কই, বললে না?’
— ‘খবর নিই ভালো করে। তারপর বলব।’
— ‘ওর নাম হিয়া। জানলে কী করে?’
— ‘ও-ই বলেছে। নৌকা করে বেশ কাছে এসে গিয়েছিল একদিন। শুধালাম, কে গো তুমি? বললে, আমি হিয়া। মির বাড়ির বউমা। শুধালাম, আগে কখনো দেখিনি তোমাকে। বললে, জি। এই বলে চলে গেল ভেসে। নৌকোটাকে হাওয়া টেনে নিয়ে চলে গেল।’
— ‘তারপর?’
চুপ করে রইল তবারক ফরাজি। নেতার ঘাটের দিকে চেয়ে রইল। সহসা ঠাণ্ডা গলায় বলল, ‘গল্প কিন্তু সহজ হবে না বড় বাবু।’
— ‘নন্দিনীকে ডাকো মামু!
বলে উঠল মিনি।
এবার আমি নিজেই কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠি।
ঈষত্ ধমকের সুরে বলে উঠি, ‘তুই থামবি মিনি! ওটা নন্দিনী নয়, ডাকলেই সে আসবে কেন? তুই ডোঙা দেখতে চেয়েছিলি, দেখা হয়েছে। এবার আমাদের ফিরতে হবে।’
মিনি অল্প করে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, ‘না।’
‘না’ বলবার সময় সে গা নাড়া দিল শরীরী ভাষার না-বাচকতায়। আমার মনে মনে রাগই হচ্ছিল; একজন মুসলিম গৃহবধূকে মিনি নন্দিনী মনে করেছে! অবশ্য বাচ্চারা হিন্দু-মুসলমান বোঝেই না। মিনির বিশ্বাসের জগত্টাই তো আলাদা। জলের দেবতা কিংবা পানির ফরিস্তা তার কাছে জলেরই মতো সহজ বিশ্বাসের ব্যাপার বই তো না!
উল্টো দিকে হাওয়া দিয়েছে। অর্থাত্ হাওয়া আবার আমাদের দিকে, আমাদের এই বাগানের দিকে বয়ে আসছে। তবে হাওয়াটা আগের মতো দমকা-দেওয়া বেগবান নয়—এ হাওয়া ঝিরঝিরে পাতলা। নৌকোটা এদিকে এগিয়ে আসছে অত্যন্ত ধীরে।
নৌকোর পিছু পিছু আসছে ডোঙাটা।
মাধব শেখের ডোঙা।
— ‘ডোঙা আর নৌকো ওইভাবে এক জায়গায় জল-খুঁটায় বাঁধা থাকে! ঠিক বলছি তো তবারক?’ বললাম আমি।
তবা বলল, ‘ঠিক তা নয় বড়ো বাবু। ডোঙাটা তো বোবাডিহির বিল থেকে কোদালকাটির স্লুইস গেটের জল-কপাট তোলা হলে ওই বিল থেকে জলের তোড়ের তাড়ায় ভেসে নদীর স্রোতে এসে পড়ে, চলে আসে নেতা ধোপানির ঘাটে। কবে আসে, ঠিক যে ভেসে এল, কখন স্লুইচ গেট পেরোলো, কেই বা দেখেছে, কেউ-কেউ বলে দেখেছে, আমি আজ অবদি দেখিনি। কিন্তু চলে তো আসে বটে! অদ্ভুত ব্যাপার!’
বলে থামল তবারক ফরাজি।
— ‘বিচিত্র ব্যাপার!’
— ‘হ্যাঁ বড়ো বাবু। সন্দেহ নাই।’
— ‘আগে কখনো বলোনি তো তবা!’
— ‘কথা উঠে নাই, কথা হয় নাই। এই নদীতে কতক কাণ্ড আলিফ লায়লা গোছের, মানে কিনা অ্যারাবিয়ান নাইটস ধাঁচে ঘটে! সব জিনিসের হেতু পাওয়া না।’
— ‘আচ্ছা বলো, নৌকোটার সঙ্গে ডোঙাটার কী সম্পর্ক?’
— ‘নৌকোটা কাছে এলে দেখবেন, ওটার গায়ে পাকা রং দিয়ে হাতের অক্ষরে লেখা আছে, “মধুকর ডিঙা, মির সায়র, বাঁকিপুর, পো: ঝাঁঝির সিথান, থানা—খুনে পুকুর, মাঝি—আজব মির।” ইত্যাদি।’
— ‘তার মানে এ নৌকো মির সায়র বাঁকিপুর থেকে এসেছে!’
— ‘আজ্ঞে। বটেই তো।’
— ‘কোন মাস নাগাদ আজব মিরের নৌকো এল কাছারিপাড়ার নেতার ঘাটে?’
— ‘নদী ভৈরবে যখন বর্ষার নতুন জল পড়ল, আষাঢ়ের গোড়ায় এ বছর বান ডাকল, ভৈরব উপচে শাখানদীগুলোয় জল ঢুকল, তখন জল উজানে বয়ে এল নানান বিলে-খালে-তড়াগে। পালতোলা নৌকা দেখা দিল বড়ো নদী হয়ে ছোট নদীর জিম্মায়—সেই সময় বাঁকিপুর থেকে এল এই নৌকা।’
—‘নৌকায় প্যাসেঞ্জার কয় জন ছিল?’
— ‘যদ্দুর সম্ভব দুজন।’
— ‘আন্দাজে বলছ?’
— ‘কারণ আন্দাজ ছাড়া উপায় নাই।’
— ‘কেন?’
— ‘ছয়ঘরায় যে মির বাড়ি, সেটা তো দীর্ঘকাল তালাবন্ধ; সেখানে হঠাত্ লোক দেখা দিল। ১০৩ বত্সরের রসুল মির তার বউমাকে সঙ্গে করে এসেছে। রসুল মির আড়াই বাঁকির ব্যবসায়ী। তেনার নানান ব্যবসা।’
— ‘আচ্ছা দাঁড়াও। রসুল মিরের কথা দু’লবেজা মনে করি। ইনিই কি ভুলু পণ্ডিতের মহাজন? মানে নন্দিনীর বড়ো মামা ভুলু পণ্ডিতের আড়তে আসতেন যে মহাজন, তিনিই কি রসুল মার্চেন্ট? মির আর মার্চেন্ট একই লোক কি না?’
তবারক তার ডান হাতের মুঠোয় থুতনি হালকা করে চেপে ধরে নেতার ঘাটের দিকে চেয়ে থেকে কী যেন ভেবে নিয়ে আমার কথা সমর্থন করে বলল, ‘মার্চেন্ট আর মির একই লোক। পণ্ডিতের আড়তে সেকেন্ড হ্যান্ড মিলিটারি জিপে করে আসতেন এই মির মহাজন। জিপটা নাকি নিলামে কেনা। মিলিটারি-নিলাম থেকে দর হেঁকে কিনেছিলেন রসুল। যা হোক গল্পটা তো সেখানে নয় বড়ো বাবু!’
আমি বললাম, ‘পণ্ডিতের আড়ত ভুলু পণ্ডিত চালাতেন না, ভুলুর ভাই দুলু চালাতেন—ওঁরা ছিলেন তিন ভাই। ভুলু-দুলু-গুলু। ভুলু হচ্ছে ভূলাল। দুলু হচ্ছে দুলাল। গুলু গুলাল। তিন চক্রবর্তী ভাই। ভুলুর তোলা-নাম হচ্ছে ভূপেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী। দুলু দুলেন্দ্রনারায়ণ। তৃতীয় ভাই বীরেন্দ্রনারায়ণ ওরফে গুলাল চক্রবর্তী। উনিই বীরু মামা। তিন ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে কম গোঁড়া।’
বাতাস আবার ঘুরে গেল। অনেকখানি এগিয়ে এসেছিল আজবের নৌকো। থমকে গেল। তারপর নেতার ঘাটের দিকে ফিরে যেতে লাগল। ডোঙাও ফিরে যেতে থাকল।
— ‘ওমা! নন্দিনী ফিরে যাচ্ছে মামু! দেখো, দেখো! হায় ভগবান, ফিরে যাচ্ছে কেন! হে খিজির বাবা, নন্দিনীকে এনে দে বাবা!’
বলে উঠল মিনি।
তবা মিনির চোখের দিকে কিছুটা অবাক হয়ে তাকাল। তারপর কিছুক্ষণ অপলক চেয়ে রইল।
— ‘পানির ফরিস্তাকে বাবা বলে ডাকছে আম্মা! খুব বুদ্ধি!’
বলে ওঠে তবারক।
এমনি সময়ে নেতার ঘাটে ঝাঁকড়াচুলের একজন আধবুড়ো লোককে পাড়ের ঢাল ধরে সরুপথে নেমে আসতে দেখা যায়। পরনে খাটো ধুতি এবং গায়ে ধবধবে সাদা গেঞ্জি। কাঁধে লাল টকটকে গামছা। রোগা গড়ন, বেঁটে খাটো মানুষ।
— ‘হায় খোয়াজ! কামরু ওঝা কী করতে এল এই বেলা! ওই ডোঙা করে, কাউকে সাপে কাটলে, ওই ওঝা বিষ ঝাড়তে যায়। মরা মানুষ বাঁচাতে পারে!’
ঘিয়ে রঙের এক খণ্ড মেঘ অস্তাচলের সূর্যের মুখে এসে লেগেছে, ঠিক তার পাশেই টগরফুলের কোমল সাদায় অতিরিক্ত উজ্জ্বল আরেক খণ্ড মেঘ, তার বুকটা হঠাত্ ফেটে গিয়ে জবার গাঢ় লালে এক মহাবিস্ময় রচনা করে তুলল। সেই রং এসে পড়েছে নেতা ধোপানির ঘাটে। খয়েরি রঙের নৌকোটা বেশি লাল দেখাচ্ছে এখন! ডোঙাটা কিন্তু কালো।
— ‘লোকটা মাটি শুঁকে বলতে পারে, কোথায় সাপে বাস্তু নিয়েছে। লোকটার গলাটা বড্ড মিঠা। বড়ো বাবু, আপনার কি কামরু ওঝার কথা মনে আছে?’
— ‘আছে।’
— ‘আসুক, কথা বলে দেখুন।’
— ‘ওর আসল নাম শঙ্কর। শঙ্কর গারুড়ী। ধর্মত্যাগ করে মুসলমান হয়, কিন্তু ওঝাগিরি ত্যাগ করে না। লোকটা সাঁওতাল পরগনা থেকে ছেলেবেলায় পরিবারের সঙ্গে খাল-বিল-নদী-ঘেরা মুর্শিদাবাদী ‘ভড়’ এলাকায় আসে। রাজাপুরে জব্বর পিরের কাছে শিষ্যত্ব নেয়। আসলে ও মুসলমান ঠিকই, তবে শিয়াপন্থি, বেশরা। সব জানি।’
— ‘আজ্ঞে। এটাই ‘হিস্ট্রি’। নমাজ পড়ে। ফের শিবের পুজোও করে। এদিকে ওঝা। ওর মাথায় অল্প করে জটের ঝুরি আছে। ও শুনেছি, মানুষের দিগভুলকি (দিগভ্রান্তি) করতে পারে। একে ভুলু পণ্ডিত সহ্য করতে পারত না মুসলমান হয়েছে বলে। আবার পাটের যাতে দর ওঠে, তার জন্য সে ‘দোয়া’ চাইত, তা নিয়ে একখানা ‘গপ্প’ আছে বড়ো বাবু!’
— ‘তা-ই নাকি!’
— ‘আসুক, শুনতে পাবেন।’
— ‘তুমিই বলো তবারক।’
এ কথা বলার পরই মনে পড়ে গেল ঘটনাটি। লাট-পাটের এই এলাকায় এমন ঘটনা মানুষকে বিমূঢ় করে দিলেও, মানুষই আবার মনে করে বিচিত্র কী যে এমন ঘটনা ঘটেছে!
সম্পর্কিত পোষ্ট => কত দূর যেতে হয় জানি না
পাট চাষিকে যেমন দুঃখ দেয়, আড়তদারকেও দেয়। পাটের ব্যবসায় লোকসানের ভয় খুব। যে-দরে পাট আড়তে জমা করল আড়তদার-ব্যবসায়ী, সেই দরে নাফা করা যায় না, যদি কলকাতার মহাজন দর না তোলে। কলকাতায় পাটের চাহিদা কম থাকলে, দর পড়ে যায়। দরের ওঠা-পড়ার ব্যাপারটি চাষি এবং কতকাংশে আড়তদারের কাছেও দুর্জ্ঞেয়। চাষি তো ভালো দর পাওয়াকে ভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করে। এ ব্যাপারে মারোয়াড়ি আড়তদার-ব্যবসায়ী যত অভিজ্ঞ এবং চালাক; বাঙালি তা নয়।
পণ্ডিতের আড়ত বছর-বছর লোকসান টানছিল। মারোয়াড়ি শিবপূজনের সঙ্গে ব্যবসার পাল্লায় পেরে উঠছিল না পণ্ডিতের আড়ত। দুলু চক্রবর্তী বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।
একদিন ভুলু পণ্ডিত ভাইয়ের বিষাদ দেখে মনে বড্ড কষ্ট পাচ্ছিলেন। গঞ্জে আড়ত ছাড়াও জুতো, জামাকাপড়, মনোহারির ব্যবসা আছে, ঔষধের দোকান আছে চক্রবর্তী ভাইদের। ছোট ভাই শৌখিন লোক, ফটোর দোকান দিয়েছে। গুলাল স্টুডিও।
ভুলু পণ্ডিত ব্যবসার পরামর্শদাতা, হাইস্কুলের সংস্কৃতের পণ্ডিত এবং পুজো-আচ্চায় ব্যস্ত থাকেন। বার কয় নির্দল প্রার্থী হিসেবে এবং একবার কী-এক মহাসভার সমর্থনে বিধানসভায় ভোটে দাঁড়িয়ে ‘ফেল’ করেছেন।
সেদিন আড়তের গদিতে বসে ছিলেন ভূলাল পণ্ডিত। রাস্তা দিয়ে ওঝা যাচ্ছিল। তাকে হাঁক দিয়ে ডাকলেন ভুলু। শঙ্কর ওঝা বলে, ‘আমারে ডাকেন নাকি পণ্ডিত মশায়?’ ভুলু বললেন, ‘হ্যাঁ ডাকি। আসো।’
— ‘কী কথা ঠাকুর বাবা?’
— ‘শুনি, তোর দোয়া-দরুদের খুব দম। শুনলাম নতুন ধর্ম নিয়েছিস! তারপর থেকে পিরের দোয়া তোর প্রার্থনায় জাগর হয়। কথা সত্য?’
— ‘আল্লা চাইলে সত্য হয় বটে।’
— ‘তুই মরা মানুষ বাঁচাতে পারিস মন্ত্র আর আয়ুর্বেদে। কথা সত্য?
— ‘দেবী মনসার কৃপা ঠাকুর বাবা।’
— ‘তা হলে পাটের দর তুলে দে কামরু। নইলে দুলেন্দ্রনারায়ণ বাঁচে না যে!’
ভুলু পণ্ডিতের কথায় প্রথমে কী বলবে বুঝে পায় না ওঝা।
— ‘দেখুন ঠাকুর বাবা, আমি বিষ নামাই। মানুষ বাঁচে। ব্যস।’
— ‘তোর দোয়াদরুদে ফজিলত আছে; তুই রাজাপুরের জব্বর পিরের মুরিদ।’
— ‘আজ্ঞে।’
— ‘তোর দোয়ায় মদনপুরে এক বাঁজি সন্তান বিইয়েছে শুনলাম।’
— ‘মনসা চাইলে হয়।’
— ‘জব্বর চাইলেও হয় কামরু। আজ তুই আড়তে থাক। খাওয়া-পরার ভালো বন্দোবস্ত দিব।’
এইভাবে আটক হয়ে যায় কামরু ওঝা। ওকে খাইয়ে-দাইয়ে আড়তে পাট-গাঁটরির ভেতরে সারারাত ‘জেকের’ করার জায়গা দেওয়া হয়। যেমন পারবে দোয়াদরুদ করবে।
পাটের গন্ধ যে কী বিষ, যারা জানে তারাই জানে। ওঝার দোয়ায় পাটের দর উঠবে, কারণ কামরু তো ফকিরও বটে। ভূপেন্দ্রনারায়ণের মনোজগত্ আমাদের পক্ষে ব্যাখ্যার অতীত। জেকের করতে করতে আড়তের ভেতরে পাটের গন্ধে দমবন্ধ হয়ে মারা যায় কামরু। ভোরবেলা ওঝার মৃতদেহ ভৈরব নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়।
কিন্তু কাণ্ড তো সামান্য নয়।
একদিন গঞ্জের পথের ওপর কামরুকে সাপের মরা কোলে করে সাপ খেলাতে দেখা গেল।
— ‘তুমি মর নাই কামরু?’
— ‘লখাইয়ের মতন কামরুও বাঁচে গুলাল।’
গুলাল চক্রবর্তী অবাক হয়ে গেল।
জগত্ বিস্ময়ে থ হয়ে গেল।
সেই কামরু এখন মাধবের ডোঙা করে ফরাজি বাগানের দিকে এগিয়ে আসছে।
তার পিছনে আজব মিরের নৌকায় হিয়া মির বসে রয়েছে। নৌকাও আসছে এদিকে।
তিন
— ‘বড়ো বাবু ভালো আাাছো?’
— ‘আমাকে চিনতে পারছ শঙ্কর?’
— ‘আজ্ঞে।’
— ‘এই ডোঙাটা তো মাধবের? শুনলাম, তুমি এটায় করে সাপে কাটা রোগীর বিষ নামাতে নদী-খালে-বিলে চরে বেড়াও। তোমার পিছনে নৌকায় ওটা কে?’
— ‘বউমা।’
— ‘তোমার বউ মা?’
— ‘আমি তো শাদিসুদা নই, বউমাটি তাই নিজের না। এটি আজব মিরের কিন্তু বউমা।’
— ‘ঠিক বলছ না শঙ্কর। ওটা রসুল মিরের বউমা।’
— ‘একই কথা বড়ো বাবু। যেমন কিনা গারুড়ী আর ওঝা একই লোকের দুইটা পদবি। আমিই শঙ্কর, আমিই কামরু। আমিই মোহনচূড়া, আমিই হুদহুদ। আমিই হিন্দু, আমিই মুসলমান। সবাই আমরা মানুষ হিসাবে কিচির মিচির। পাখির কোটরে সাপ উঠছে বাবা।’
— ‘তোমার ভাষাটি সন্ধ্যা।’
— ‘আজ্ঞা ভাষার কী দোষ! সবই ভাবের দোষ বাবু মশাই!’
— ‘কথায় তোমার অনেক ভাঁজ!’
— ‘নইলে জীব বাঁচে না যে!’
আমরা একেবারে নদীর ধারে গাবগাছটার কাছে এসে দাঁড়ালাম। নরম উজ্জ্বল সোনালি আলোয় নদীর স্রোত ঝিলমিল করছে এবং একটা সান্ধ্য ছায়াও জড়িয়ে রয়েছে রৌদ্রের নম্রতাকে—কখনো কখনো মেঘ ছায়াকে নদীর ওপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে ফিরছে—এই নরম আলোয় কমলা বাদুড় দেখা দিয়েছে।
গাবগাছ নিতান্ত বেঁটে গাছ। তার ডালে ঝুলে রয়েছে মধুচক্র এবং নদীর স্রোতকে ছোঁব-ছোঁব করছে।
মৌচাকটা মধুতে টসটস করছে। জাম ফলের মতো বড় বড় মৌমাছি—এরা খুদে মৌমাছি নয়, এরা পাহাড়ি— চাকটাকে পাহাড়ি চাক বলে লোকে—ভাবছিলাম, এভাবে নদীর স্রোতের ওপর ঝুলে থাকার মানে কী! তবে গাবগাছের ঝাঁকড়া ডালপাতা নদীর জলের ওপর ঝুঁকে এসে চাকটাকে ঢেকেও রেখেছে, যদিও বড্ড লম্বা হওয়াতে ডালপাতা ছাপিয়ে স্রোতের ওপর খসে পড়ার ভঙ্গিমা করে রয়েছে। এতে বাদুড়ে ছোঁ মারবে কিংবা মধুপায়ী পাখিরা হামলা করবে—নাকি এই রকম ঝুলে থাকটাই মধুর সঞ্চয়কে সুরক্ষিত করেছে মনে করে মৌমাছিরা!
এই জায়গাটারই কাছে এল ডোঙা। ডিঙিটাকে হাল ঠেলে এদিকে এনে জলের ওপর চক্রাকারে ঘুরে বেড়াতে লাগল হিয়া। সে চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখছিল, তারপর লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিচ্ছিল!
এ তো নন্দিনীই।
— ‘তুমি নন্দিনী, তুমি আমার মামী হও!’
হঠাত্ ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা মিনি বলে উঠল। ঘোড়াও নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। নন্দিনীর কোলে কালো ওড়নার মতো কী একখানা বসন পড়ে আছে বলে মনে হচ্ছিল।
নন্দিনী কিংবা হিয়া, যেই হও, তুমি খুব সুন্দর দেখতে; সুন্দরীই বটে। মনে মনে বলে উঠি এবং তখন ডিঙিটা আরও খানিক দূরে চলে গেল। হিয়ার মুখটা নেতা ধোপানির ঘাটের দিকে ঘুরে গেছে। পিছন থেকে মনে হচ্ছিল বউটি হাসছে! শব্দ করে হাসতে পারছে না। হাসি চাপতে চাপতে হাসছে।
হাসতে হাসতে কোলের বসনটা খুলে ফেলে মাথা গলিয়ে পরে নেয় বউটি। ওটা বোরখা। কালো বোরখা।
তবা নন্দিনীকে বোরখা পরতে দেখে পাশে আমার দিকে মুখ ফেরাল চাপা বিস্ময়ে।
ওঝা এই সময় ডোঙার খোলে শুইয়ে রাখা জলখুঁটা হাতে নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পাড়ে এসে পড়ে মুগার সুতো বাঁ হাতের আঙুলে জড়িয়ে ডান হাতে জলখুঁটা ডাঙার লাগোয়া জলে পুঁতে দেয়।
ওঝাকে বললাম, ‘তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে শঙ্কর কাকা।’
— ‘আজ্ঞে!’
— ‘তবার সঙ্গে কালই একবার যদি আসো!’
— ‘মা মনসার কৃপা হলে যাব। যদি তেনার চেনা কারুকে দংশায়, না হলে পারব না।’
— ‘ঠিক আছে। আচ্ছা, এখনই কিছু কথা তো বলা যায়!’
— ‘যায় বইকি, তবে আগে কানির চেলার ব্যবস্থা করি, ভুঁসিঘরে ফোঁসাচ্ছে তবা ভাই। চলো। দাঁড়াও, সরাটা সঙ্গে নিয়ে যাই। গহমা খরিস বাস্তু নিয়েছে, হায় আল্লা!’
এই বলে ফের জলের কাছে নেমে গেল শঙ্কর।
ডোঙায় রাখা খান চার সরা তুলে নিয়ে কোলে করে এগিয়ে এল।
এত বিস্ময়াবিষ্ট জীবনে কমই হয়েছি। তবারকের ভুঁসিঘরে সাপ বাস্তু করেছে। গহমা খরিস। এই খরিস সাধারণত গহমার ভুঁইয়ে থাকে। গহমা গরুর খাবার। দেখতে কতকটা আখের মতো। কিন্তু আসলে এ জিনিস একধরনের উদ্ভিদ যা গরুর প্রিয় খাদ্য, ঘাসের সঙ্গে মিশিয়ে সঙ্গে কিছু খইল দিলে গরুরা বেশ সোয়াদ করে খায়।
গহমার জমিতে থাকে বলে ওই খরিসের নাম গহমা খরিস। হজরত মুহম্মদ (স.)-এর পায়ের খড়মের ছাপ রয়েছে ওর মাথায়। যা হোক। ওই জীব ফরাজির ভুসিঘরে রয়েছে, তার মানে ভুসিঘরের মাটির তলায় ভয়ানক বিষধর সাপ রয়েছে।
সূর্য এখন নদীর জলের ওপর মাত্র মানুষপ্রমাণ উঁচুতে টলটল করছে। সোনারোদ এসে লাগছে ডিঙির বোরখা-জড়ানো নারীমূর্তির গায়ে। ওই নারীমূর্তি বৃত্তাকারে ঘুরে এদিকে এগিয়ে এল।
মৌচাকটার কাছে এসে বলল, ‘আমি তোমার মামী? অ্যাই মেয়ে, নাম কী তোমার? বলো, বলো! কী তোমার নাম?’
মিনি এবার ভয় পেয়েছে। তার মামী বোরখার ভেতরে কেন? কী-একটা দুর্বোধ্য কষ্টে সে কেঁদে ফেলল। ভয়েই দু’হাতে চোখ ঢেকে ফেলল। স্বল্প ফুঁপিয়ে উঠল।
বোরখাটি যদি রঙিন হতো, কালো না হতো, তাহলে মিনি হয়তো এভাবে ভয়ে কেঁদে ফেলত না। একবার নসু মিঞার বিবির মুখে নকাব সে ভারি আনন্দ পেয়েছিল—ওই নকাব নাকের ওপর দিয়ে নেবার জন্য ওর মায়ের কাছে কতদিন আবদার করেছে। কিন্তু কালো বোরখায় সে এই মুহূর্তে বিচলিত হয়ে পড়েছে; শিশুর মনটাকে আমাদের বুঝতে হবে—এইভাবে কালো বোরখা দেখতে সে বিশষ অভ্যস্তও নয়। সে তো থাকে হিন্দুপ্রধান গঞ্জে—সেখানে বোরখা-পরিহিতাকে খুব কমই গোচর করা যায়।
যা হোক। তার এই অবস্থা দেখে সরাগুলো কাঁখে নিয়ে ফের লাফিয়ে পড়ে কামরু ওঝা চকিত স্বরে বলে উঠল, ‘আহা! কাঁদে না মা! বোরখায় ভয় করতে নাই। এই বালিকা হলো গে বউমা, এই বড়ো বাবুর ভাগিনী। তোমার নামটি শোনাও তো মা! লক্ষ্মী মা আমার!’
কামরুর কথায় আশ্চর্য প্রকারে কাজ হলো।
চোখের ওপর দু’হাত সরিয়ে আমার ভাগ্নিটা বলল, ‘আমার নাম মিনি সিকদার। মামুর নাম বটেশ্বর মিত্র। ঘোড়ার নাম নোটন মিত্র। আগে ছিল নোটন ফরাজি। কাকার নাম তবারক ফরাজি। আর শুনবে বউমা!’
বলে থামল মিনি।
বোরখা কোনো সাড়া দিচ্ছে না। ডিঙি ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। নদীর স্রোত এতই মন্থর যে, বাতাস পালে লাগলে স্রোতের উল্টো দিকে ডিঙি ফিরে যায় ঘাটে। উল্টা বাতাসে আজব ডিঙি ফিরে যাওয়ার উপক্রম করছে। ওই ডিঙির সঙ্গে ডোঙা মুগার সুতো দিয়ে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় এবং জলখুঁটায় বেঁধে দেওয়া হয়। জুড়ে রাখলে বাতাসের টানে সহজে কোথাও ভেসে চলে যেতে পারে না।
লক্ষ করলাম জল-খুঁটায় ডোঙাটা বাঁধবার আগে সুতোয় বাঁধা আঁকশিটা খুলে মুগার সুতো ডিঙির দিকে ছুড়ে দিল ওঝা। বুঝতে পারলাম ডোঙা আর ডিঙি একই সুতোয় বাঁধা। এবং এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।
বোবাডিহির বিলে বাতাসের ধাক্কায় বা দূরবর্তী স্রোতের টানে ডোঙা ভেসে যাওয়ার ঘটনা আছে। কথা হলো এই যে, ডোঙাটা ভেসে চলে গেলে ওঝার কারবার বন্ধ হয়ে যাবে; শঙ্কর তো সাপ নিয়ে খেলাও দেখায়। সাপ ধরে চালান দেয়। নাফা ভালো।
যা হোক। গারুড়ীর মতো রহস্যময় মানুষ আমি সংসারে দেখিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভুলু পণ্ডিতের মতো জটিল হূদয়ই বা কোথায় দেখেছি! এই লোকটির কথা গারুড়ীর কাছে পাওয়া যেতে পারে।
কিন্তু হঠাত্ পালে উল্টো হাওয়া গেলেছে।
আজবের ছোট ডিঙিটাকে মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিল, ওটা একটা খেলনা ডিঙি। এই নদীটাও ছোট। এর ডাক নাম ছোট নদী। ভৈরব বড় নদী। বড় নদীতে এখন পালতোলা নৌকোর শোভাযাত্রা চলেছে। ছোট নদীতে দু-চারটি নানারঙা পালতোলা নৌকো ঘুরে বেড়ায়। নদীর দেশ বলে এ অঞ্চলে নৌকো করে বিয়েশাদির বরযাত্রা ও কনে-আনার ঘটনা ঘটে। সেই বিয়ের নৌকায় সন্ধ্যা-হেমন্ত-মান্না-প্রতিমা-শ্যামল প্রমুখ গায়ক-গায়িকার গান বাজিয়ে নদীকে পুলকিত করে তোলা হয়। নূর মিঞার মাইক মাইক্রোফোন ভাড়ায় খাটে। ‘মধুমালতি ডাকে আয়’ বাজিয়ে মনসুর মাস্টারের বিয়ে হলো ক’দিন আগে। বেহুলা-লখিন্দরের গান বাজিয়ে আরেকটা বিয়ে যাচ্ছিল ভৈরবে, সেটা নশিপুর প্রাইমারির হেডমাস্টার গুজুদা বন্ধ করে দেন নৌকোর দিকে হাত নেড়ে, বলেন, ‘ওই গান বাজিয়ে কেউ বিয়ে করতে যায়!’ বরযাত্রীরা প্রচণ্ড ধমক খেয়েছে।
ভাষা এবং সাহিত্য নিয়েই তো আমি এমএ পাস করেছি। তাই মনসা ব্যাপারে আমার চিন্তাভাবনা আছে। শুধু ওঝাদের নিয়েই বিশেষ কৌতূহল রয়েছে।
ছেলেবেলা থেকেই ভেবেছি, ওঝারাই মনসার আসল লোক। এর প্রকৃত প্রচারক। এরাই জ্যান্ত বিধাতা। এদের মানুষ শ্রদ্ধা করে যতটা, ঘৃণাও করে ততটা।
সাপে-কাটা রোগী বাঁচলে শ্রদ্ধা-অন্তহীন-কৃতজ্ঞতা।
না, বাঁচলে ঘৃণা, অবজ্ঞা, অনন্ত-অশ্রদ্ধা।
রোগী মারা গেলে অর্থাত্ না বাঁচাতে পেরে একলা ওঝা মাঠ ভেঙে পালাচ্ছে—এমন দৃশ্য কতবার দেখেছি।
বোরখার মূর্তিটিতে নিয়ে আজব-ডিঙিটা ফিরে যাচ্ছে, হঠাত্ ফুঁপিয়ে উঠল মূর্তিটা—এক আশ্চর্য অবরোধের ভিতর ডুকরে উঠল সে।
সহসা শঙ্কর একটা অসহায় বাঁকা হাসি মোটা গুছি-গোঁফের তলায় হেসে বলল, ‘কাঁদুক, আর কী করবে! চলো তবা, সাঁঝলতা দুই-চাট্টে সরায় তুলি। হ্যাঁ বাবু, কথা আমারও আছে চলুন।’
আমি বোধহয় মাটিতেই পুঁতে গেছি। থ হয়ে গেছি। বুকের ভেতর আশ্চর্য কষ্ট। ডাঙায় ফুঁপিয়ে উঠেছে একটি শিশুকন্যা, নদীতে কাঁদছে নারী—এদের কান্নার মধ্যে কোথাও কি কোনো ঐক্য আছে? আশ্চর্যের এই যে, এই দুজনের এই প্রথম দেখা হলো—ওরা কাঁদল, এ কেমন ঘটনা!
বেরিয়েছিলাম ননাকে দেখতে, তাকে পাকড়াও করে থানায় মারধর করব কি না বুঝে পাচ্ছিলাম না! ননা পূর্ববঙ্গে চলে যাওয়ার বছরকতক বাদে লগড়াজলি এসে দেখে, তার বউ অন্যের বউ হয়ে গেছে, তার প্রথম সন্তান মাধব ডোঙায় ভেসে গেছে; মাধবের জল-কবর হয়েছে। ধর্ষণ হলো এই মর্ত্যলোকে পুরুষের প্রথম পাপ।
ধর্ষকের কি কোনো হূদয় থাকে?
কিসের টানে দ্বিতীয়বার ননা লগড়াজলি এসেছিল? এত বছর বাদেও লোকটাকে লগড়াজলি পাথর ছুড়েছিল। তারপর সে তৃতীয়বার এসেছে মাকে দেখতে।
— ‘আচ্ছা শঙ্করকাকা… না থাক। চল নটু, এবার যাওয়া যাক। চল মিনি, গহমা খরিস দেখে আমরা…’
বলে কথার মাঝাখানে থেমে যাই।
তবা বলল, ‘ডোঙা তুমি দেখেছ আম্মা। কামরু বলুক, এটাই মাধবের ডোঙা কি না! কী হে, আম্মাকে বল, ডোঙাটা বোবা বিল থেকে এসেছে কি না!’
নদীর কিনারা ছেড়ে আমরা পাড়ের ঢাল ধরে রাস্তার দিকে উঠছি। রাস্তায় গিয়ে ফরাজির আম-কাঁঠাল বাগান দিয়ে সাজানো বাড়ির দিকে যাব, যা এই বাগান-শস্যখেত থেকে অল্প কিছু দূরে।
আমরা পথের দিকে উঠছি। সবার আগে মিনিকে পিঠে নিয়ে নটু মিত্তির। নটুর পিছনে আমি। একটু পিছিয়ে, তবু আমারই প্রায় কাঁধঘেঁষে তবা। সবার পিছনে বেঁটে-খাটো শঙ্কর গারুড়ী, ওর কাঁখে সরার ওপর সরা। এক কাঁধে ঝোলানো একটি কাপড়ের থলে, তার মধ্যে শক্ত কী একটা যেন রয়েছে। ওই কাঁধেই থলের ফিতের তলায় রঙিন গামছা—ওঝার গোঁফ দেখে বাচ্চারা ভয় এবং আনন্দ, একই সঙ্গে পেয়ে থাকে। গোঁফের তলায় এক অনাবিল প্রসন্নতা উঁকি দিয়ে ওঠে ওঝার কথায়-কথায়।
ঘোড়ার পিঠে বসে পিছনে চেয়ে আছে মিনি। ও শুনতে চায় ডোঙাটা মাধবের কি না!
তবা বলল, ‘কী হে! আম্মাকে বলো, ডোঙাটা কোথা থেকে তোমার কাছে এল।’
শঙ্কর নদীর জলে সূর্য দেখল। পিছনে ফিরে দেখতে দেখতে এগোতে থাকল। সূর্য নদীর স্রোত ছোঁব-ছোঁব করছে।
শঙ্কর বলল, ‘মরা নিয়েই তো ওঝার কারবার। যে মরে গেছে, সে-ও তো বাঁচে তবা ভাই। আমি তো নিজেই ‘মরা’ আম্মা। গাঁটের পাটের গন্ধে মরে গিয়েও বেঁচে রয়েছি। মাধবের ডোঙা আমার কাছে না এসে যাবে কোথায়! এই যে আজব মিরের বউমা হিয়া, এই মেয়ে লোকটি বাঁচা-না-মরা একবার ভাবুন তো বড়ো বাবু!’
আমি চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।
তবা এসে একেবারে আমার কাঁধের পাশে দাঁড়াল।
নটু মিত্তির এগিয়ে গেল।
সূর্য গোমোহনীর জলে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। বাগানে পাখির কলরব বেড়ে গেছে। সূর্যের অস্তরাগের ভিতর পশ্চিম আকাশে গোল একটা চাঁদ এক আশ্চর্য উজ্জ্বল বিষণ্নতায় টইটই করছে।
বাঁ পাশে তবা। ডান পাশে এসে দাঁড়াল কামরু ওঝা।
— ‘বোবা বিলে ডোঙা বারবার হারিয়ে যায় বড়ো বাবু। আর হারিয়ে গেলে সে তো মাধবের ডোঙা হয়ে ভেসে বেড়ায়। সন্দেহ নাই, ওটা মাধবের জিনিস।’
এই বলে কামরু ওঝা এগিয়ে গেল।
পা বাড়িয়ে থেমে শঙ্কর কপালে একটা হাত ঠেকিয়ে ‘জয় মা জাঙ্গুলী’ বলে এগিয়ে গেল।
ওঝা এগিয়ে যেতে যেতে বলে উঠল, ‘জয় মা জাঙ্গুলীতারা।’
এই মুর্শিদাবাদ এক বিচিত্র দেশ; এটি বৃহত্ ভারতের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। এখানে বিষ্ণু আর বুদ্ধে মিলন ঘটে; মুটির তলা থেকে খুঁড়ে হয়েছে বৌদ্ধবিষ্ণু মূর্তি। কর্ণসুবর্ণে ঐতিহাসিকভাবেই বৌদ্ধ প্রভাব টের পাওয়া যায়। এখানে বৌদ্ধ বেশি ছিল বলেই মুসলমানও বেশি হয়েছে, কারণ বৌদ্ধরাই ব্যাপকভাবে মুসলমান হয়েছে।
এই ‘জাঙ্গুলীতারা’ তো মহাযান বৌদ্ধদের প্রাচীন দেবী—এই দেবীর সঙ্গে দেবী বিষহরির বেশ মিল আছে বা মিলেমিশে গেছে দুই দেবী; জাঙ্গলিকয়া তো সাপুড়েও বটে।
আমি সহসা দ্রুত পায়ে এগিয়ে জাঙ্গুলীতারার উপাসককে ধরলাম।
বললাম, ‘মাধবের ডোঙা কতদূর যায় শঙ্কর কাকা?’
— ‘যেখানে সাপে কাটে, দূর যতই হোক, পানিপথ পেলে ডোঙা নিয়ে চলে যাই।’
— ‘আচ্ছা শঙ্কর কাকা, তোমাকে ‘তুমি’ করেই বলি। তুমিও আমাকে ছেলেবেলায় যেমন ‘তুমি’ করে বলতে, তা-ই বলো।’
— ‘আসলে তুমি কী জানতে চাও বটেশ্বর?’
— ‘প্রশ্ন অনেক। আপাতত বলো, এই ডোঙা আড়াই বাঁকি গেছে কখনো?’
— ‘গেছে কতকটা পথ।’
— ‘তুমি নিয়ে গেছ? তুমিই?’
— ‘হ্যাঁ।’
— ‘যখন বাঁকিপুরের মির সায়র গেলে, তখন তোমার বয়েস কত?’
কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ওঝা।
তারপর বলল, ‘বয়েস তখন ৩২-৩৩ হবেটবে।’
— ‘ভুলু পণ্ডিত যখন তোমাকে আড়তে আটকে রেখে পাটের দর বাড়াতে দোয়া করিয়ে নেয় এবং…’
— ‘এবং আমার মরণ হয়। তখন তো মোটামুটি বুড়ো হয়েছে গারুড়ী। কিন্তু আমার বয়েসের হিসেব চাইছ কেন বড়ো বাবু?’
— ‘তখন তুমি গারুড়ী নও, তখন তুমি পিরের মুরিদ হয়ে কামরু ওঝা। তা-ই না?’
— ‘হ্যাঁ।’
— ‘মনে হচ্ছে জীবন গিয়েছে চলে কুড়ি কুড়ি বছরের পার।’
— ‘কুড়ি-কুড়ি। তা হবে বইকি বটেশ্বর। কিন্তু ঠিক কী জানতে চাইছ বলো তো!’
— ‘তুমি ডোঙায় করে কার মৃতদেহ নিয়ে গিয়েছিলে বাঁকিপুর?’
— ‘যে রাতে আশ্বিনের আঁধি হবে, সেই রাতে তোমার সঙ্গে কথা হবে বড়ো বাবু। আজ এই পর্যন্ত। সাপ কয়টাকে ধরতে দাও এখন।’
আমি এবার মাথা নিচু করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। সামনে বেশ কিছুটা দূরে নটু মিত্তির মিনিকে পিঠে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমার পিছনে অনেকটা দূরে বাগানের ঢালের সরুপথ ধরে উঠে আসছে তবারক ফরাজি।
আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি এবং ওঝা সম্মুখে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে দেখে পিছন থেকে কাছে এসে তবা বলল—‘কী হলো দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন বড়ো বাবু?’
— ‘আচ্ছা তবারক, ওঝার সঙ্গে ভুলু পণ্ডিতের সম্বন্ধ আসলে এত কেন জটিল, আমাদের বুঝতে হবে।’
— ‘এই ওঝার পরিবারকে বসতের জন্য জমি দিয়েছিলেন ভুলু পণ্ডিতের বাবা।
— ‘তা-ই নাকি?’
— ‘আজ্ঞে।’
— ‘আর?’
— ‘গাঁয়ের একেবারে শেষে, যেখানে ফসলের মাঠ আরম্ভ হচ্ছে, সেখানে ওঝা ফ্যামিলি ঘর তুলল। আপনার জানার কথা।’
— ‘না। জানতাম না।’
— ‘কিছু তো জানতেন বড়ো বাবু!’
— ‘সাপুড়ে ওঝারা আমার চোখে বরাবর রহস্যময় চরিত্র। ওদের ভেতরে ঢোকা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। মনসার মতো জটিল-কুটিলা সংসারে আর কোথায় পাই বলো তো তবারক। বাংলার ঘরে ঘরে এই দেবীটি তেনার নিজের জন্যে পূজা-ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে আর মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলছে; মৃত্যু হলো এই যোগিনী দেবীর কী বলব হাতসাফাইয়ের খেলা। কাকে কখন মারবে, কার বদলে কাকে এবং কাকে বাঁচাবে কেউ জানে না।’
— ‘কথাটা সহি।’
— ‘এমনকি মনসা নিজেও জানে না কাকে রাখবে, কাকে মারবে। কারণ…’
— ‘কারণ, এই কানির মনটা এমনই পিচ্ছিল যে নিজের মনকে সে নিজেই চেনে না।’
— ‘এই জন্যেই তো ওই কানিকে এত গালাগাল খেতে হয় বাবু! বিষহরির যে বিষঝাড়ার গান, তাতে পর্যন্ত খেউড় করে লোকে। এই দেবীর ডেকে আনা মৃত্যুর মধ্যে একটা তো বেইমানি আছে।’
— ‘একদম ঠিক কথাটি বলেছ তবারক। চলো। তোমার ভুঁসিঘরে শাবল মারবে কামরু। দেখতে হবে তো!’
— ‘শাবল এমনই গা বাঁচিয়ে মারবে, দেখবেন একটা সাপও কাটা পড়ছে না।’
— ‘আরে তা-ই তো! ঠিকই দেখেছ তুমি।’
— ‘কোনো সাপ অপঘাতে মরলে শঙ্কর কাঁদে। ও দেবীকে কানি ডাকে সোহাগ করে।’
— ‘বটে।’
— ‘হ্যাঁ বাবু।’
— ‘আচ্ছা তবারক, এ বছর আশ্বিনের আঁধি হবে বলে মনে হয়?’
— ‘কেন বড়ো বাবু!’
— ‘এ বছর একটা আঁধি খুব দরকার।’
— ‘কামরু কিছু বলল?’
— ‘হ্যাঁ, আঁধির রাতে জানতে পারব নন্দিনীর কী হয়েছিল। আচ্ছা, তুমি বলবে ওঝা-পরিবার চক্রবর্তীদের জমিতে বসত করবার জায়গা পেয়েছিল। তা-ই তো? আচ্ছা চলো। সাপ দেখে মিনি কী করে কে জানে? চলো, চলো…
চার
আঁধি-পীড়িত রাত্রি। বাড়ির বাইরে ঘোর অন্ধকারে বাতাস আর বৃষ্টির এমনই মাতলামি এবং বজ বিদ্যুতের যথেচ্ছাচার যে মনে হচ্ছিল পৃথিবী লোপ পাবে—এমনই প্রলয় চলেছে; এমনই কেয়ামত শুরু হয়েছে। তবার এমনি আসার কথা। রাত দশটা বাজল। গারুড়ী কি আসবে তাহলে?
ঝড়বাদলায় ‘পাওয়ার’ থাকে না। এমনিতেই লোডশেডিং লেগে থাকে। ফলে বাড়িতে লণ্ঠন এবং মোমবাতির ব্যবস্থা রাখতে হয়। বারান্দায় লণ্ঠন এবং ঘরের ভেতরে মোমবাতি জ্বলছে।
চৌকাঠের কাছে দিদি হরিমতী লণ্ঠনের আলোয় প্রভাবতী দেবীর উপন্যাস পড়ছেন। উপন্যাসের নাম ‘ফুলশয্যার রাতে’। মলাটে মাঝে মাঝে আমার চোখ যাচ্ছে। তাতেই বুঝতে পারছি উপন্যাসটির নাম ওই রকম।
মাঝে মাঝে বন্ধ জানালা একটুখানি ফাঁক করে বাইরেটা দেখে নিচ্ছি। আকাশের বিদ্যুত্ চমকে রাস্তার কিছু অংশ, ওইদিকের দিগন্ত চকিতে ভেসে ভেসে উঠছে।
হঠাত্ সাদা ঘোড়াটা চকিতে চকিতে চমকে চমকে উঠল। এদিকেই ছুটে আসছে। ঘোড়ার পিঠের আরোহীকে দেখা যাচ্ছে না কেন? মনে হচ্ছে উবু হয়ে ঝুঁকে আছে তবা। কিন্তু এত অস্পষ্ট যে, পলকা সাদা কালি দিয়ে আঁকা বলে মনে হলো। ঠিক দেখলাম তো?
জানলা ঠেলে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। ফের খুললাম। এবার মনে হলো তবাই আসছে। এই বাদলায় ঘোড়ায় কেউ ওইভাবে আসে? জানলা বন্ধ করে দিলাম। দিদির বাড়িতে আপাতত ঘোড়া রাখার ব্যবস্থা নেই। টিনের চালাটা উড়ে গেল। ঘোড়াটাকে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজতে হবে। আমার ঘোড়াটাকে যখন (অর্থাত্ নটুকে) তবার কাছে পাঠাই তখন আকাশে মেঘ ছিল না। আঁধিতে প্রত্যেক বছর টিন উড়ে যায়। এবারও গেল। নটু একা বেরিয়ে যাওয়ার পরই মেঘ জমল এবং কড়াত্ করে বজ্রের শব্দ হলো। যদি এই আঁধি মাথায় করে নটু তবাকে নিয়ে আসে তাহলে মজুমদারদের আস্তাবলে গিয়ে ওকে থাকতে হবে।
দশ-পনেরো মিনিট চলে গেল। কেউ এল না।
হঠাত্ একটা গলা শোনা গেল, ‘হরি! ওগো হরিমতী!’
ঠিক শুনছি তো?
বাদলা ও বজ্রের শব্দের ফাঁকেই ফের গলাটা, ‘হরি! ওগো হরিমতী! শুনতে পাও?’
মনে হলো, ঠিক এই জানলার ওপারেই কেউ দাঁড়িয়ে ডাকছে। দিদি বই বন্ধ করে বলল, ‘দরজা খুলে ডেকে নে বটু। ওঝা এসেছে।’
পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে চকিতে দরজা খুলে দিতে চলে গেছে মিনি।
— ‘আম্মা! তোমার নামটাই যেন আম্মা সিকদার!’ এমনই করে বলে তবারক। ‘তবা আসেনি?’ বলতে বলতে ঢুকে পড়ল ওঝা।
প্রকাণ্ড মানপাতা মাথায় নিয়ে এসেছে কামরু। অবশ্য সাদা বর্ষাতির ওপর মানপাতার ব্যবস্থা।
বর্ষাতি পরে আছে বলে ওঝাকে বিশেষ রহস্যময় দেখাচ্ছে। বর্ষাতি খুলে বারান্দার তারে ঝুলিয়ে দিয়ে আমার এই পড়াশোনার ঘরটায় ঢুকে এল সাপুড়ে। সেদিন ওর কাঁধের ব্যাগে নাগিন বাঁশি ছিল, দেখেছি। আজও সেটা সঙ্গে। সেদিন যে চার-চারটে গহমা খরিস ধরে—সাপগুলোর সেকি ফোঁসানি—যেন মনসা ক্রোধে ফুঁসছিল! মিনি চোখ বড় বড় করে পুরো দৃশ্যটি উপভোগ করেছিল।
মেঝেয় বসে পড়ল ওঝা। ওকে কিছুতেই চেয়ারে বসানো গেল না।
কিন্তু তবা কোথায়? নটু কোথায়? বাদলা-প্রমত্ত রাস্তা বিদ্যুতের চমকানির ভিতর সাদা ঘোড়া দেখলাম—সে কোথায় গেল? কাউকে এ কথা বলতেও পারছি না। কী ভাববে কে জানে!
‘তোমাকে এক কাপ গরম চা দিই শঙ্কর, সঙ্গে পাঁপড় ভেজে দিচ্ছি। দিই?’ বলল দিদি।
ওজা বলল, ‘দাও। তুমি ভালো আছো হরিমতী?’
দিদি নিঃশব্দে মিটে হেসে ঘাড় কাত করল। তারপর চা করতে চলে গেল। কীযে হলো, জানালাটা আবার একটু ফাঁক করে বাইরে চাইলাম, সাদা ঘোড়াটা দূর দিগন্তের দিকে ছুটে যাচ্ছে, ওর পিঠে কোনো আরোহী নেই।
— ‘কী দেখছ, অমন করে বড়ো বাবু?’
— ‘কী যে দেখছি, তাই তো ভালো করে ঠাহর হচ্ছে না কাকা! তবা কি এরমধ্যে তোমার কাছে গিয়েছিল?’
— ‘পরশু গিয়েছিল। শুধু শুধালে, এ বচ্ছর কি আঁধিটাঁধি হবে নাকি কামরু, কোনো আন্দাজ করতে পার? তারপর শুধালে, আঁধির মধ্যে কখনো ডিঙা নিয়া গিয়েছ কোথাও মনসার ডাকে? বিচিত্র সওয়াল বড়ো বাবু! বললাম, না-ই যদি গেলাম, তাহলে আর ওঝা কিসের ভাই!’
এই বলে আপন মনে শরীর নাচিয়ে মেঝেয় দুই চোখ নত করে খিক খিক করে বিচিত্র আমোদে হাসতে লাগল ওঝা।
বাইরে রাস্তায় বিদ্যুতের ঝলকে সাদা ঘোড়া আবার দেখা গেল। দিগন্তের দিক থেকে শূন্যের ওপর ঝাঁপ দিয়ে ছুটে আসছে। যেন কোনো দক্ষ চিত্রকরের আঁকা ঘোড়া লীলাময় গতিতে উদ্দাম হয়েছে ওই বিদ্যুত্-চমকিত বাদল-উল্লাসে—এ ঠিক বাস্তব অশ্ব নয়, ওটা নটু নয়।
‘আহা তুমি এখনো কী দেখছ অমন করে বাবু!’ বলে উঠল ওঝা
বললাম, ‘আমারই ঘোড়া আমার কাছে ফিরতে পারছে না শঙ্কর কাকা!’
‘ফিরবে, ফিরবে। চিন্তা করো না। সব ফিরে আসবে। মানুষ তো সোনার চাঁদ বড়ো বাবু।’ বলে উঠল মনসার চেলা জাদুকর শঙ্কর গারুড়ী।
আমি আনন্দে মহাবিস্ময়ে বলে উঠলাম, ‘সেকি! তুমি বলছ, মানুষ সোনার চাঁদ!’
— ‘হ্যাঁ বাবু, মানুষ আসলে সোনার চাঁদ। সোনার চাঁদ মানুষ। সে ফিরে পায়।’
— ‘বলছ?’
— ‘পায় না বলছ! তাহলে ঠিক বলছ না। এটি তিন দিনের আঁধি বটেশ্বর। এক আঁধিতে সে গিয়েছিল; আরেক আঁধিতে সে ফিরছে।’
এই জীবন কী অবিশ্বাস্য রূপে সুন্দর। বাইরে জিন রূপে ঘোড়া হয়ে আঁধির সঙ্গে খেলা করে চলেছে তবারক ফরাজি, এদিকে ঘরের মধ্যে আরেক আঁধির কথা বয়ান করতে চলেছে মনসার প্রচারক এবং বিশিষ্ট চেলা শঙ্কর গারুড়ী ওরফে কামরু ওঝা।
বললাম, ‘তুমি আগে বলো, ধর্ষিত হয়ে নন্দিনী খুন হয়, নাকি হয় না?’
— ‘হয় না।’
— ‘বেঁচে থাকে?’
— ‘বেঁচে থাকে।’
— ‘তারপর?’
— ‘ধর্ষিতার সংসারে জায়গা কোথায়? নন্দিনী তো এমনিতে বাপ-মা-মরা, যাকে বলে অনাথিনী, মামাবাড়ির আশ্রয়ে থেকে মানুষ হচ্ছিল। কিন্তু ননা তো সব শেষ করে দিল।’
এই বলে মাথা নিচু করল শঙ্কর। তারপর দু’হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। পড়ার ঘর থেকে এ ঘরে এসে চকিতে ঘুরে গেল মিনি। ওর মা ওকে ডেঁটে রেখেছে; আমাদের কথা শোনার ওর অনুমতি নেই। তাই সে ঘুরে গেল মাত্র, দাঁড়িয়ে পর্যন্ত থাকতে পারল না।
— ‘তুমি কি কাঁদছ কাকা?’
— ‘মনসার চেলা কাটে, কাঁদে না তো!’
— ‘প্রাণও তো দাও শঙ্কর কাকা!’
— ‘আমি কিন্তু…’
— ‘হ্যাঁ, বলো।’
মুখের ওপর থেকে দু’হাত সরিরে ওঝা বলল, আমি কিন্তু তোমার নন্দিনীকে কাটিনি বটেশ্বর। মনসার কিরা, কাটিনি।’
— ‘তুমি কাটবে কেন কাকা?’
— ‘আমার ওপর সেই রকমই হুকুম এল যে!
— ‘মানে!’
আবার দু’হাতে মুখ ঢেকেছে ওঝা! মনে হয়, কাঁদছে।
জানতে চাইলাম, ‘তোমার ওপর কী হুকুম হলো? কে দিলো হুকুম? কেন?’
বজ্র বিদ্যুত্ বৃষ্টি—কোনো বিরাম নেই। আকাশে রোজকেয়ামতের যেন বিলয় চলেছে। আজ যেন বা লয় পাবে পৃথিবী।
মোমবাতির কাঁপা-কাঁপা আলোয় দেখা গেল মুখের ওপর থেকে হাত সরালে, ওঝার গাল বেয়ে চোখের জলের ধারা নামছে।
— ‘আকাশে ঘোলা মেঘ পাক খেয়ে-খেয়ে গেল। বোঝা গেল, আঁধি শুরু হবে। আশ্বিনের গোড়ায় ঘটনা। তারপরই তো, পরের দিন থেকে স্কুলের পুজোর ছুটি শুরু হবে। কিন্তু কে জানত, নন্দিনী আর স্কুলে যাবে না, ওর ধ্রুবপুরেও জায়গা হবে না, ওর জীবনে কেয়ামত এসে গিয়েছে, কানি ওকে দংশাবে বলে ঠিক হলো। ধর্ষিতা মেয়েকে কামড়াবে কানি। আমাকে ডাক দিলো ভুলু পণ্ডিত। বলল, শোনো শঙ্কর, ননা আমার ভাগ্নিটাকে ‘রেপ’ করে দিয়েছে; চিরকালের মতো নষ্ট, এঁটোঝুটা করে দিয়েছে; নন্দিনীকে গহমা খরিস দিয়ে কাটো গারুড়ী, তারপর গোমানীর জলে ফেলে দাও। কাজটা গোপনে করতে হবে, যদি ব্যবস্থা না হয়, তাহলে তুমি ভিটে থেকে উচ্ছেদ হবে গারুড়ীর বাচ্চা, ভেবে দেখো!’
এই বলে আবার দু’হাতে মুখ ঢাকল ওঝা।
শুনতে শুনতে শিরদাঁড়ায় একধরনের ঘৃণিত ঘামের স্রোত নামছিল। আমি হতবাক হয়ে গেলাম।
মনসার নাটক খুব চড়ায় ওঠে, সহজ-স্বাভাবিক যা, তার দিকে এই একচোখ কানা নিয়তি-দেবীর কোনো আগ্রহ নেই।
আমার পায়ের তালু কেমন শিরশির করছে। কপালেও ঘামের দানা দেখা দিয়েছে।
কিছুক্ষণ বাদে চা আর পাঁপড় নিয়ে ঘরে ঢুকল দিদি।
— ‘তুমি ওভাবে দু’হাতে চোখ ঢেকে কী করছ শঙ্কর! নাও, চা খাও।’
বলে থালায়-প্লেটে-ট্রে-তে সাজানো পাঁপড়-চা ওঝার পায়ের কাছে রাখল দিদি।
আমার পড়াশোনার টেবিলের ওপর দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা নন্দিনীর সেই ছবি। হাসিমাখা কিশোরীর নিষ্পাপ মুখখানি আশ্চর্য সৌন্দর্যে ভরে আছে। তুমি মেয়ে হয়ে জন্মেছ নন্দিনী, তুমি ধর্ষিত হলে এদেশে তোমাকে সাপে দংশানো হতে পারে, এভাবেও তোমার মরণ আসে এখানে। তুমি ধর্ষিত হয়েছ, এ যে তোমারই অপরাধ!
নন্দিনীর ছবির কাছে মোমবাতি এবং ধূপকাঠি জ্বলছে। আমি আর নন্দিনীর চোখের দিকে চেয়ে থাকতে পারলাম না। জানলা অল্প ফাঁক করে বাইরে চাইলাম। সাদা ঘোড়াটা এখনো আঁধির সঙ্গে খেলা করে চলেছে।
ওঝা পাঁপড় আর চা খাচ্ছে এখন।
— ‘তুমি কী করলে শঙ্কর কাকা?’
পাঁপড় ঠোঁটে ধরে ভেঙে নিয়ে খেতে খেতে, তার সঙ্গে চায়ে চুমুক দিয়ে কামরু বলল, ‘বলছি বড়ো বাবু!’
বলে দিদির চোখের দিকে একঝলক দেখে নেয়, তাতে করে মনে হলো, দিদির সামনে পাপের কথাটা আর বলতে চাইছে না ওঝা।
দিদিও বুঝতে পেরে সরে চলে গেল। অন্য ঘরে গেল বা মিনির কাছে গেল।
রান্নাঘরে ভাত ফুটছে। আঁধিতে কাজের মেয়েটি আসতে পারেনি। হারু ডাঙার ইলিশ পাওয়া গেছে এই বেলা। ঘণ্টাখানেক বাদে সঙ্গে ওঝাকেও ভাত-মাছ খেতে দেবে দিদি।
— ‘ঘণ্টাখানেক বাদে মাছ-ভাত পাচ্ছ শঙ্কর। হারুডাঙার ইলিশ পেয়েছি মনসাতলার হাটে। খেয়ে নিয়ে বাকি কথা চলবে। আঁধি না থামলে যেও না।’ এই বলে দিদি এ ঘরে ছেড়ে গেল।
দিদি বেরিয়ে যেতেই ওঝা বলল, ‘গহমা খরিস ছাড়লাম নন্দিনী যে-ঘরে রয়েছে তার টালি ফাঁক করে, ওকে ঘেন্নায় খাপরার ঘরে শুতে দেওয়া হয়েছিল। তখন অল্প-অল্প আঁধি শুরু হয়েছে। আমিই এই অবস্থায় সাপ হয়ে দংশোবো, ওঝা হয়ে ঝাড়ব। আমিই ওই সাপ, বললাম, যা গারুড়ী ওই বালিকাকে কেটে আয়! মানুষের চেয়ে পিছল গহমা খরিস তো আর নাই!’
চক্রবর্তীরা ধ্রুবপুরের একপ্রকার জমিদার। গঞ্জে নানান ব্যবসা। প্রচণ্ড ব্রাহ্মণ্যবাদী, বিচিত্র গোঁড়ামি আছে ভুলু পণ্ডিতের।
সাপে কাটা ভাগ্নির মৃতদেহ শঙ্কর গারুড়ীর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে ভুলু বললেন, ‘নিয়ে যা শঙ্কর, নদীতে ফেলে দে। লোককে বলবি, ভাগ্নিটা সাপের কামড়ে মরেছে, আর যদি নন্দিনীকে তুই বাঁচিয়ে তুলিস, তুই কিন্তু পার পাবি না গারুড়ী। তোকে আমি দম বন্ধ করে মারবো। তোর শ্বাসরোধ হয়ে যাবে কানির বাচ্চা। যা, আঁধি শুরু হয়ে গেছে।’
— ‘তারপর?’
ওঝা বলল, ‘এমনই ভয়ংকর সেই আঁধি। কাঁধে নিয়ে চলেছি ধর্ষিতা ও মৃতা এক কিশোরীকে। সাধু ভাষায় বললে এ রকমই দাঁড়াচ্ছে বাপ!’
— ‘তারপর?’
— ‘নেতা ধোপানির ঘাটে বাঁধা ছিল ডোঙা। বড়ো ডোঙা। ওর মাথার দিকে খোলের কাছে কন্যেকে বসিয়ে গালে থাপড় দিয়ে ডাকি, নন্দিনী ও নন্দিনী! চোখ খোলো মা!’
— ‘সেকি!’
— ‘হ্যাঁ বড়ো বাবু! বললাম, তুমি জাগো, তুমি মর নাই নন্দিনী। তোমাকে আমি শঙ্কর গারুড়ী ডাকছি। সুতরাং তুমি চোখ মেলে চাও। মা, আমিই সর্প আমিই ওঝা!’
— ‘চোখ মেলল নন্দিনী!’
— ‘মরা কি অত সহজে চোখ মেলে বাপ! ধর্ষিতা তো মৃত্যুর পরও ধর্ষিতা! তার কি লজ্জা করে না!’
ওঝার এই কথায় আমার কেমন কান্না পেয়ে গেল! ধর্ষিতা মৃত্যুর পরেও চোখ মেলতেও লজ্জা পায়! আঁধির মধ্যে জীবন পাচ্ছে বাংলার এ কিশোরী—ভারতবর্ষের এক নন্দিনী।
— ‘তুমি আবার ডাকলে নন্দিনীর নাম ধরে?’
— ‘তখন হঠাত্ বৃষ্টিটা ঝিরঝিরে হয়েছে, আঁধারের মধ্যে আঁধির গোঙ্গানি কিছু কমেছে। যদিও আবার আসবে প্রচণ্ড তেজে! ওই বৃষ্টির আঁধারে কী-একটা চিল জাতীয় প্রকাণ্ড পাখি মাথার ওপর কেঁদে কেঁদে উড়ছিল। সেটা যে কী পাখি আজও জানি না।’
সম্পর্কিত পোষ্ট => বিকেলের বেহাগ
— ‘আশ্চর্য বটে কাকা!’
— ‘তা বইকি বটেশ্বর!’
এই বলে টেবিলে রাখা গুলাল স্টুডিওর তোলা কিশোরী নন্দিনীর ছবিটার দিকে বিষাদ-বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কামরু ওঝা।
নন্দিনীর দিক থেকে চোখ টেনে নিয়ে ফের মাথা নিচু করল ওঝা। দু’চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল শঙ্কর—যেন সে কিছু একটা ধ্যান করছে।
আমি ধ্যানস্থ শঙ্করের দিকে সকৃতজ্ঞ চেয়ে থাকি। মনে মনে ভাবি, এই সামান্য ওঝা নন্দিনীকে বাঁচিয়েছে—ও নিশ্চয়ই মনসারই খাঁটি চেলা। বাঁচা-মরার ম্যাজিক জানে কামরু।
— ‘নন্দিনী চোখ মেলল কখন?’
—‘নন্দিনী ভেবেছিল, ও মরে গেছে। কিন্তু এটি অদ্ভুত মনসা-মঙ্গল বাবু! কানির চেলা খাপরার ফাঁক গলে পড়ল বটে মেঝেয়। কিন্তু খাটে উঠলই না। ঘরের জল বার হওয়ার ‘সুরি’ গলে বার হয়ে বনে চলে যাওয়ার আগে মেঝেয় কিছুক্ষণ ফোঁস ফোঁস করে ঘুরে বেড়ালো। সেই শব্দে ঘুম ভেঙে গেল নন্দিনীর। সে মাথার কাছে জানলার ফ্লাবে রাখা বাতি কমানো হ্যারিকেনের অল্প আলোয় সুরির মুখটায় জীবটাকে দেখে চিত্কার করে উঠল আর ইংলিশ খাট থেকে ভয়ে পড়ে গেল মেঝেয়। ভয় পেল সাপটাও এবং মেঝেয় পড়ে যাওয়া নন্দিনীর পায়ে দংশন করেই সুড়ুত্ করে সুরির ভিতর দিয়ে বাইরে বেরোল; আমি জানতাম, এই আঁধিতে ওকে আমি আর পাব না। ও ধ্রুবপুরের বাবুর বাগানেই আছে। ওর বিষদাঁত ভেঙে দিয়ে, তবে ওকে খেলতে দিয়েছিলাম বড়ো বাবু!’
— ‘তাই বলো কাকা!’
— ‘বলব কী বটেশ্বর! এমন ছলনা ছাড়া জীবন তো বাঁচত না। কিন্তু ওই আঁধির মধ্যে ডোঙা ছাড়ল শঙ্কর। ঘাট থেকে কালো জলের মধ্যে ঢুকল সে অচৈতন্য নন্দিনীকে নিয়ে আর বলতে থাকল, ‘তুমি মর নাই নন্দিনী, মর নাই, জাগো…’
এক নয়া মনসা-মঙ্গল শুনছি। গহমা খরিসের বিষদাঁত ভাঙা ছিল। বিষদাঁত ভেঙে তাকে এক কুমারী দংশনে খাপরার চালের ফোঁকর গলিয়ে ফেলে দেয় ওঝা। কুমারী ছিল ধর্ষিতা। ধর্ষিত হলে সমাজে সেই নারীর জায়গা হয় না—এমনই এক সমাজের গল্প এটি।
ডোঙা চলেছে। সাদা পাতলা ত্রিপল দিয়ে ঢাকা এই জলযান। সদ্য আঁধি শুরু হয়েছে। পুরো ফাঁপি (আঁধি) লাগেনি এখনো। তার আগে যদুর ঘাটে পৌঁছাতে হবে। সেখানে চমত্কার একখানি নৌকো আছে ছইতোলা। সেটির ব্যবস্থা করেছে আর এক ওঝা ওমর; শঙ্করের চেলা। ওর কাছ থেকেই গহমা খরিসটা চেয়ে নিয়েছিল শঙ্কর গারুড়ী। মাইল দুই জলপথে দ্রুত ভেসে এল ডোঙাটা।
বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শুধু মেঘ ডাকছে আর বিদ্যুত্ চমকাচ্ছে। আকাশে তারা নেই। চাঁদ নেই। ভাগ্য ভালো, আঁধি পুরো লাগলে বাতাস এলোমেলো ঝাপটা দিতে পারে বা গম্ভীর হয়ে বাতাস থেমে গিয়ে অঝোর ঢালতে পারে আকাশ।
হঠাত্ ফোঁপানি শোনা গেল একটা বিদঘুটে গলায়। তারপর গলা ফুটল।
— ‘মা! আমি কোথায় মা! কিসের মধ্যে রয়েছি মা! ওগো! আমি বেঁচে আছি! হা ভগবান!’
ওঝা বলল, ‘তুমি সত্যিই বেঁচে আছো খুকি।’
— ‘কে তুমি? কে গো!’
— ‘আমি শঙ্কর ওঝা। তুমি-আমি ডোঙায় করে যাচ্ছি।’
— ‘কোথায় যাচ্ছি?’
— ‘এখনকার মতন যদুর ঘাট। সেখানে নৌকা পাব মা!’
— ‘কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে!’
— ‘মনসা যেখানে ব্যবস্থা দেন, আমরা সেখানে যাব নন্দিনী।’
— ‘আমি কেন মরলাম না, হে ঠাকুর!’ বলে কাঁদতে থাকে নন্দিনী।
ডোঙা চলতে থাকে।
যদুর ঘাটে পৌঁছাই আমরা।
নৌকা ছাড়ে। ওমর আমাদের সঙ্গে যাবে। বৈঠা টানবে। আমি হাল ধরব। কখনো বৈঠায় বসব আমি—ও হাল ধরে থাকবে।
— ‘আমায় বাঁচালে কেন গারুড়ী কাকা!’
নৌকা ছাড়লে প্রথম এই কথা বলে উঠল নন্দিনী।
এ কথার জবাব দেয় ওমর।
বলল, ‘দোষ শঙ্করদার নাই বুবু!’
— ‘বুবু!’ বলে ডেকে ওঠে ওমর। নন্দিনী নিতান্ত অবাক হয়ে ওঠে। ওমরের বয়েস কম। কিন্তু যুবক তো বটে। কিশোরীকে ‘বুবু’ সম্বোধন করল কেন, তা ওমর নিজেই ব্যক্ত করে, ‘তুমি আমার সফুরা বুবুর মতো দেখতে, তাই ‘বুবু’ ডাকলাম, কিছু মনে করিও না।’ তারপর ওমর বলল, ‘যা হোক। আসল কথা শোনো বুবু! আমারই দেওয়া সাপে তোমাকে কেটেছে, ওটার বিষদাঁত আমিই ভেঙে দিই! ওটা খেলা দেখানোর সাপ, বিষ নাই। শোনো বুবু। তোমাকে বাঁচিয়ে আমার উস্তাদ নিজের বিপদ নিজেই ডেকে নিয়েছে। যদি তোমার বড় মামু এই ঘটনা জানতে পারে, গারুড়ীর সর্বনাশ হয়ে যাবে বুবু। যদি গারুড়ীকে বাঁচাতে হয়, যা বলব করতে হবে।’
—‘কী করতে হবে?’ অবাক হয়ে অসহায় গলায় জানতে চাইল নন্দিনী।
—‘আগে এই বোরখাটা পরে ফেলো। এই আঁধির মধ্যে মা মনসা তোমার নতুন জীবন দিল। এই নতুন জীবনে ভুলু পণ্ডিত তোমার কেউ না। রসুল মার্চেন্ট তোমার নতুন নাম দিয়েছে। হিয়া। হিয়া মির। অর্থাত্ হিয়া মির্জা।’
— ‘আমাকে তোমরা মুসলমান করতে চাইছ?’ বলে ওঠে নন্দিনী।
ওমর বলল, ‘আমি মনসার চেলা। নিজেই কী জাত ঠিক নাই বুুবু। তুমি অন্তরে নন্দিনী চক্রবর্তী। বাইরে হিয়া মির। শোন বুবু, আমি আসলে ওমর চিত্রকর, হিন্দু বা মুসলমান, কোথাও জায়গা পাই নাই। নাও বোরখা পরো হিয়া। আমাদেরও বাঁচতে দাও।’
বোরখা পরতে পরতে নন্দিনী বলল, ‘আমি বটুদাকে এ জীবনে কখানো আর পাব না! হা মনসা, এ তুমি কী করলে!’
পাঁচ
একটি বোরখার মধ্যে সাঁধ করিয়ে রেখে দেওয়া হলো চৌদ্দ বছরের এক কিশোরীকে। এটাই হলো এক ধর্ষিতার জীবনের দস্তুর। মনসা এর বেশি পারল না। এই দেবী এই ধরনের নিতান্ত সাধারণ মানের ‘জাদু’ ছাড়া পারে না। তবে গহমা খরিসের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া কম কথা নয়।
— ‘তারপর কী হলো শঙ্কর কাকা?’
— ‘কী আর হবে বাবা, বোরখার মধ্যেই বাড়তে থাকল নন্দিনী। একটা প্রকৃত ধার্মিক এবং রক্ষণশীল মার্চেন্ট ফ্যামিলি, মির নয়, মির্জা ফ্যামিলিতে আমরা নিয়ে এলাম নন্দিনীকে।
— ‘নন্দিনী আর আপত্তি করেনি কোনো?’
— ‘যে মরে বেঁচেছে, তার তো নিজের মতো জীবন বেছে নেওয়ার সুযোগ নেই বটেশ্বর!’
হঠাত্ মনে হলো বাজের ডাক কমেছে, বিদ্যুতের চমকানিও কম হয়েছে, কিন্তু বৃষ্টি বেড়ে গেছে বলে শাঁই-শাঁই শব্দের মধ্যে কে যেন কাঁদছে—কোনো নারীকণ্ঠের কান্না!
— ‘কেউ কাঁদে শঙ্কর কাকা!’
— ‘হ্যাঁ বড়ো বাবু!’
— ‘মনে হচ্ছে, কাছেই। জানলার কাছটায় এসেছে কেউ।’
— ‘আচ্ছা, বোরখা পরে তোমার খুব কাছাকাছি এসে চলে গেল, এমন হয়েছে, তুমি মনে করতে পার?’
— ‘দাঁড়াও, একি বলছ তুমি কাকা! তার মানে নন্দিনী আমার কাছে নানাভাবে এসেছে!’
— ‘ঠিক সেই রকমই তো গল্পটা বাবু!’
শুনে আমি শিউরে উঠলাম।
আর হঠাত্ মনে হলো, কান্নাটা নন্দিনীর! কেউ না, এ নন্দিনীই। আমি জানালাটা একটু বড় করে ফাঁক করলাম। আর আশ্চর্য! এক বোরখাপরা নারীমূর্তিকে দেওয়াল ছেড়ে বৃষ্টির মধ্যে চলে যেতে দেখা গেল। আমি দ্রুত বর্ষাতি শরীরে গলিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলাম। বিদ্যুত্-চমক ফের বেড়েছে; সেই আলোর বোরখামূর্তি এগিয়ে যাচ্ছে দেখি।
দিগন্তে খেলা করছে সাদা ঘোড়া। কিন্তু আমার সামনে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বোরখা-মূর্তি নারী।
পিছন থেকে ডেকে উঠলাম, ‘নন্দিনী?’
বোরখার নারী সাড়া দিল না। এগিয়ে যেতে থাকল।
আবার ডেকে উঠি, ‘নন্দিনী! তুমি সাড়া দিচ্ছ না কেন?’
নন্দিনী সাড়া দেয় না। পিছনে ফিরে তাকায় না পর্যন্ত। আশ্চর্য রহস্যময় এই কালো বোরখা-আবৃত নারী।
ডেকে উঠি, ‘হিয়া!’
সাড়া দেয় না তবু। এগিয়ে যায়।
— ‘তুমি কেন এসেছিলে! তুমি নিশ্চয়ই হিয়া। আমি জেনে গেছি তুমিই নন্দিনী! দাঁড়াও। কথা বলো!’
দাঁড়ায় না বোরখা-পরিহিতা। এগিয়ে যায়।
কাহারপাড়া হয়ে কদমতলার দিকে যায়, তারপর বালুমাটি যাওয়ার সরুপথটা যেখানে নদীর ধারে শুরু হয়েছে এবং কাহারপাড়ার পথ গিয়ে নদীর ধারেই পড়েছে, সেখানে চলে গিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নেয়, তার সামনে সাদা ঘোড়া ঘাড় বাঁকিয়ে হ্রেষা দিয়ে ছুটছে—বাতাস খেপামির চূড়ান্ত করছে; তারই ভিতর দিয়ে রহস্যময়ী এই নারী চলে যাচ্ছে; আমার কথা শুনছে না।
বললাম, ‘আমার কী করার ছিল! ভুলু পণ্ডিতের বিরুদ্ধে কথা বলবার সাধ্য তো গুলাল মামারও নাই। ভুলুর চোখে তুমি মৃতা, মনসা কানি তোমাকে ধ্রুবপুর থেকে মুছে নিয়ে গেছে, নন্দিনী! তুমি নষ্টা, তুমি ভ্রষ্টা, তোমার জাত গেছে নন্দিনী। তুমি কথা বলো। তুমি মর নাই, বল আমাকে।’
ঘোষপাড়া পেরিয়ে ফরাজি পাড়ায় চলে গেল নন্দিনী। তারপর তবার বাগান হয়ে গাবগাছের কাছে বেঁধে রাখা আজবের নৌকায় গিয়ে বসল। অবাক কাণ্ড! ওখানে মধুচক্রটা নেই। আঁধিতে শেষ হয়ে গেছে। একটা আশ্চর্য শূন্যতার অনুভূতি হলো। তার সঙ্গে মিশে আঁধির হাহাকার। নৌকো নিয়ে নদীতে চলে গেল নারীমূর্তি। নেতার ঘাটের দিকে গেল। আমি তবার খোঁজ করে দেখি, সে বাগানের কুটিরে চৌকির ওপর মুখ হাঁ করে ঘুমিয়ে রয়েছে। ওকে আর ডাকলাম না। দেখি, ওই চালার বাইরের টিনের চালায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে নটু মিত্তির, আমার সেই ঘোড়া, যাকে আমি তবাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলাম।
তাহলে সেই সাদা ঘোড়াটা কোথায় গেল?
—‘চল নটু!’
কী মনে করে রাস্তায় চলে এসে টিনের চালার কাছে ফিরে গেলাম। তারপর নটুকে বাড়ি ফিরতে বললাম। ও সাড়া দিলো না। তার মানে তবার জন্য সে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। আসলে নটু তো তবার কাছে সময় কাটাতে ভালোবাসে।
তাহলে ওই সাদা ঘোড়াটা কে? ও যেমন সত্য নয়, এই বোরখা-মূর্তিও সত্য নয়। আমি সুতরাং কী-সব অলীক দৃশ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি!
রাস্তায় এলাম।
এমন সময় পিছন থেকে হাঁক ভেসে এল।
— ‘দাঁড়ান, বড়োবাবু! আমিও যাব।’
তবার গলা। তবা আর নটু এল রাস্তায়।
আমরা হেঁটে চলেছি তিন জনে।
— ‘এত ঘুম তোমার!’ তবাকে বলি।
তবা লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলে বলল, ‘অকাট্য ঘুম বড়ো বাবু!’
— ‘শঙ্কর গারুড়ী কখন এসছে! কথাও হলো। আরও কথা বাকি।’ বললাম তাবাকে।
তবা বলল, ‘ওমর চিত্রকরের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে বাবু! চলুন, কামরু আরো ভালো বলবে। আপনি কি জানেন বড়ো বাবু, বাজ পড়ে বর্ষার গোড়াতেই মরেছেন ভুলু পণ্ডিত। ওমর বলল, এইটে কানির খেলা তবা চাচা।’ আশ্চর্যের ব্যাপার! এত বড় ঘটনা, আমার কাছে খবর নাই!
পুলিশে চাকরি করলেও আমি আদতে সাহিত্যের ছাত্র। মনসা যে নানান খেলায় লিপ্ত তা বিশ্বাস করতেই ভালো লাগে। এই আঁধি মনসা রয়েছে ভাবলে মন্দ কী? তারই ভিতর রহস্যময়ী বোরখা-নারী আমাকে এভাবে টেনে আনলে, আমি আর কী করতে পারতাম। হে নিয়তি! এখনই যে খেলা চলল, সে কথা তবাকে বললাম না।
ভুলু পণ্ডিতের মৃত্যু কেন যেন আমাকে সুখকর এক স্বস্তি এনে দিচ্ছিল মনের ভেতরে আর ভাবছিলাম, মনসারই খেলা এই সব!
তবা বর্ষাতি নিয়েছে, নটুকেও দিয়েছে।
আমরা তিন জন হেঁটে চলেছি।
‘হরিমতী নিবাস’ আমাদের গন্তব্য, বলা বাহুল্য। দিদির বাড়িই আমার থাকবার জায়গা। যদিও থানায় থাকবার জন্য আমার নামে সাজানো ঘর আছে। থানাটা বড় আমবাগানের মধ্যে। বলতে ভুলে গেছি, গঞ্জ থেকে এই ছোট নদী গোমোহনী দুই মাইল পথ। দিদির বাড়ি থেকে এই নদী দেড় মাইলের কিছু কমই হবে। প্রায় দেড় মাইল পথ আমি আঁধির মধ্যে নন্দিনীর পিছু পিছু এসে গিয়েছিলাম, খেয়ালই করিনি। মনে হচ্ছিল, এসেছি মাত্র আধ মাইল। ঘোরে থাকলে সময় টের পাওয়া যায় না।
হরিমতী নিবাসে ফিরলাম আমরা। নটু থানার শেডে চলে গেল। দিদির রান্না হয়ে গিয়েছিল। আমরা মেঝেয় পাত পেড়ে বলে খেয়ে নিলাম রাত্রির খাবার।
মুখে চাট্টি মুখশুদ্ধি ফেলে আমাদের কথা শুরু হলো। মিনি খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দিদির একমাত্র সন্তান এই মিনি। আমাদের কথা শুরু হলে দিদি এসে চৌকাঠের কাছে আগেরই মতো বসে গেল।
তবা বলল, ‘মাঝখান থেকেই শুনি কামরু। আমার অসুবিধা হবে না। কতক প্রধান-প্রধান কথা ওমরের কাছে শোনা হয়েছে বাবা।’
অভিজ্ঞ মানুষকে বা জ্ঞানীকে ‘বাবা’ ডাকবার নিয়ম আছে। সেই হিসেবে শঙ্কর গারুড়ীকে ‘বাবা’ সম্বোধন করল তবারক ফরাজি।
— ‘রসুল মির নয়, ও হলো রসুল মির্জা। মুর্শিদাবাদের নবাবদের বংশধর।’
—‘হ্যাঁ বাপ, তবারক। ওটি হিয়া মির নয়। ওর খাতায় নাম হিয়া মির্জা। ও সুন্নি নয়, ও শিয়া। ওকে ধর্মের কোনো ধরনের সুন্নি গোঁড়ামি “গ্রিফতার” করেনি। কথা কয়টি বুঝে নাও বটেশ্বর। এমনকি ওর কাছ থেকে ওর পিতৃদত্ত ধর্মও কেড়ে নেওয়া হয়নি—হিন্দু কালচারকে ওই রসুল মার্চেন্ট নিজের কালচার মনে করে। এঁরই পূর্বপুরুষ নবাবরা, যারা নবাবী তখতে বসতেন, শিবের পাদোদক খেয়ে সেই নবাবদের সিংহাসনে অভিষেক হতো। এটা গালগল্প নয়, এটা মুর্শিদাবাদের নবাবী কালচার। সেখানে কানি মনসা নন্দিনীকে নিয়ে গেল বাবা।’
— ‘তুমি তো শিক্ষিত মানুষের মতো করে গল্পটা বলছ শঙ্কর কাকা।’
— ‘আমিও তো তবার মতন নন-ম্যাট্রিক বাবা!’
— ‘তা-ই বলো!’
— ‘তবা তোমাকে কখনো বলেনি বটেশ্বর। বলেনি এই জন্যে যে ওর খুব গুমোর।’
এই বলে হাহা করে গলা খুলে হাসতে লাগল শঙ্কর গারুড়ী।
তবা বলল, ‘তুমি জেনে রাখো, তোমার মনসা থাকলে, আমারও আছে খোয়াজা খিজির। ভক্তি করে ডাকলে জিন-ফরিস্তাও কাছে আসে। কিন্তু নমস্কার তোমাকে বাবা। কত বড়ো ঝুঁকি নিয়ে নন্দিনীকে আঁধির ওপারে নিয়ে গেলে বাবা হে!’
এই পর্যন্ত শুনে আগের মতো মাথা নিচু করল শঙ্কর গারুড়ী। তারই কাছাকাছি মেঝেয় বসেছে তবারক।
আমি অত্যন্ত নিচু ইজি চেয়ারে আধশোয়া।
— ‘তুমি তাকে ধরতে পারনি, ছুটে তো গেলে অমন করে! আসলে নন্দিনীর বড্ড অভিমান বটেশ্বর। তাছাড়া ভাবো, কী কথাই বা বলবে সে তোমার সঙ্গে! তা-ই না! যাক গে। সে গেল আল্লাহ রসুলে না গিয়ে আলি মওলায় বাবা!’
‘কথাটা কী? শুধু হজরত রসুলে হবে না বাবু। আল্লা ছাড়া অন্য কোনো আল্লা নাই। কথাটি সহি বাবা হে! ফের রসুল মুহম্মদ (স.) ছাড়া আরও রসুল থাকলেও আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় নবি ওই হজরত মুহম্মদ (স.)। তিনিই আল্লার সেরা প্রতিনিধি। কিন্তু তারপরেও কথা আছে বাবা। হজরতের পরেও একজন আছেন। তিনি হজরত আলি। আলির অনুসারীরাই শিয়া। আমরা বলছি, শিয়া নবাবদের কথা, যারা আজ গরিব নবাব হয়ে দিন গুজরান করছেন। এই নবাবরা তাদের পূর্বপুরুষদের কালচার মেনে হিন্দুদের প্রতি সহিষ্ণু এবং শ্রদ্ধাশীল। এই গরিব নবাবদের মধ্যে রসুল মির্জা একজন বড় ব্যবসায়ী, তার ব্যবসার পার্টনার শ্যাম জৈন। আজিমগঞ্জের লোক।’
রসুল ব্যবসা বোঝেন, লেখাপড়া তত বোঝেন না। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, তিনি বিদ্বানকে শ্রদ্ধা করতে জানেন না। তার ছেলেমেয়েরা কেউ উচ্চ শিক্ষা নিতে পারেনি। বিদ্বানকে সমীহ করলেও পড়াশোনায় কেমন যেন এলানো এবং ভোঁতা।
হঠাত্ আমি বলে উঠি, ‘এই সব কথার সঙ্গে নন্দিনীর কী যোগ কাকা?’
— ‘আছে বইকি বটেশ্বর। খুব যোগ আছে। খুবই যোগ। তাছাড়া রসুল যদি সুন্নি হতো, হয়তো গল্প অন্যরকম হতো। রসুল যদি নবাবের বংশধর না হতো, তাহলেও গল্পটা যেরকম বলছি, সেরকম হতো না।’
— ‘আচ্ছা!’
— ‘হ্যাঁ, বটেশ্বর।’
এই বলে দম নেয় কামরু ওঝা।
বললাম, ‘একটু জল খাবে শঙ্কর কাকা?’
দিদি চট করে উঠে গিয়ে গ্লাসে জল এনে দেয়।
ওর জল খাওয়া দেখি আমি আর তবা।
গ্লাস খালি করে জল খেয়ে দিদিকে গ্লাস ফেরত দেয় শঙ্কর। একটা আরাম বোধ করে।
তারপর বলে, ‘কথাও আজকাল ভুলে যাই। কী যেন বলছিলাম!’
বললাম, ‘নবাবদের ধর্ম ব্যাপারে বলছিলে কাকা!’
—‘সবাই জানে। শিবের পাদোদক খেয়ে নবাবের সিংহাসনে বসাটা ছিল রেওয়াজ। বোঝো। শুধু এইটুকু বোঝো তো বটেশ্বর।’ বলে ওঠে কামরু ওঝা।
তবা হঠাত্ বলল, ‘নবাবরা শিয়া বলে এ রকম, নাকি নবাব তাই ওই রকম?’
আমি বললাম, ‘এই তর্কটা থাক তবারক। ঔরঙ্গজেব ছিলেন গোঁড়া আর তার দাদা দারাশিকো ছিলেন উদার। এইটুকু বুঝি। নবাবরা ছিলেন অত্যন্ত উদার। আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি শঙ্কর কাকা ।’
— ‘হ্যাঁ বটেশ্বর। রসুল মির্জা নন্দিনীর জন্য ঘরের এক কোণে ঠাকুর পুজোর বন্দোবস্ত দিয়ে বলেছেন, তুমি মা চক্রবর্তী ঠাকুর, তোমার জন্য এইটুকু ব্যবস্থা তো করতেই হয়। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার মনে এক লোভ জন্মেছে খুকি! যদি সুযোগ হয়, একদিন বলব সে কথা!’
— ‘লোভ!’
— ‘হ্যাঁ বটেশ্বর, লোভ!’
— ‘কী লোভ?’
তবা বলল, ব্যবসায়ী মানুষ লোভ বলেছেন না লাভের বাসনা হলো বলেছেন, ভেবে দেখো!’
— ‘নন্দিনী অনাথ! তাকে দিয়ে নাফা কতটুকু হয় হে তবারক? তাছাড়া, মনসার ফেরে পড়ে নবাব ফ্যামিলিতে আশ্রয় চাইছে। একটা বাচ্চা মেয়ে। কী লাভ আজব মির্জার!’
বলে মাথা নিচু করল শঙ্কর।
তবা বলল, ‘তোমাকে খেপিয়ে দিয়ে কথা শুনতে ভালো লাগে বাবা হে!’
‘লোভ’ কথাটায় আমি খুব শঙ্কিত হয়ে পড়ি।
আমার মনোভাব ধরতে পেরে মুখ তুলল কামরু ওঝা।
বলল, ‘ননার লোভ আর রসুল মির্জার লোভ তো এক বস্তু হতে পারে না বড়োবাবু। তবু ওইটুকুনই ধর্ষিতা সমাজ থেকে বার করে দেওয়া সাপে কাটা বালিকা “লোভ” কথাটায় ভয় পেল। তা-ও টের পেয়ে হা হা করে হেসে ফেলে রসুল বলল, ভয় পেও না খুকি, এইটে হলো আজব কথা, মনে হলো আমি আজব মির্জা আজব কথা বলে ফেলে নিজেই লজ্জা পাই। আর কিছু না। ব্যস!’
—‘লোভটা কী, বলে ফেলো কাকা, আমি সইতে পারব।’ বলে উঠি।
— ‘কিন্তু কথাটা বলে ফেলে নিজেই কথাটা গিলে ফেলল আজব মির্জা আর সে কথা বলতে গিয়ে কতবার যে আটকে গেল এই ত্রই বছরে। আজব ভেবেছিল সুন্দরী নন্দিনীকে ছোট ছেলে নৈনিহালের ‘বউ’ করবে, কিন্তু সমস্যা কঠিন।’
বলে আবার মাথা নিচু করল শঙ্কর গারুড়ী। আমার মুখটা কেমন শুকিয়ে উঠল। তবা আমার ভাবান্তর লক্ষ করছিল।
আজব বলল, ‘হায়ার সেকেন্ডারি (ওল্ড) যখন পাস করল নন্দিনী, তখনো একদিন হঠাত্ আজব বলল, তোকে দেখে আমার যে বেশ লোভ হচ্ছে রে মা! কিন্তু কথা হচ্ছে, নৈনিহাল পরীক্ষায় তিনখানা ব্যাক পেয়েছিল খুকি। তুমি তো ফার্স্ব ডিভিশনে পাস করলে! আজবের সংসারে একি আজব ব্যাপার ঘটাচ্ছেন খোদা! নৈনিহালই মির্জা ফ্যামিলির গ্রাজুয়েট, দু-দফা গ্রেস পেয়ে বিএ পাস করেছে। করবে তো ব্যবসা। যথেষ্টই হয়েছে। নৈনিহাল দেখতে সুন্দর, সুপুরুষ, দয়াবান। পছন্দ হয়?’
— ‘কী বলল নন্দিনী?’
— ‘বলল…।’ বলে মাথা নিচু করে চুপ করে রইল শঙ্কর। কথা যেন আটকে গেল গলায়।
চুপ করেই রইল শঙ্কর।
তারপর হঠাত্ বলে উঠল, ‘নৈনিহাল নন্দিনীর পছন্দ, নাকি নয়, যে কথার জবাবই দিলো না হিয়া মির্জা। বলল, তুমি আমাকে এই বোরখা আর বিশাল বাড়ির মধ্যে বন্দি করেছ বাবা, কারণ তুমি তো লুকিয়ে রেখেছ। আমাকে মুক্তি দিতে পার না? আজব বলেছে, তুমি যে বেঁচে আছো, এ কথা ভুলু পণ্ডিত জানলে শঙ্কর গারুড়ীর বিপদ হবে মা! আর বোরখায় থাকতে থাকতে অভ্যাস হয়ে গেলে আর কষ্ট হবে না হিয়া। ঘরের মধ্যে বোরখা তো লাগে না। এটাই তো মুক্তি আম্মা। তুমি অন্তরে হিন্দু, কিন্তু বাইরে শিয়া, এই সিদ্দাগাটা রাখো, ঠাকুরের ছবির কাছে রাখবে, যাতে করে মনে থাকবে এ কথা যে, তুমি মির্জা বাড়ির নবাবের নন্দিনী, অন্তর সত্য, কিন্তু বাহিরটা মিথ্যা নয়, নন্দিনী গারুড়ী। এই সম্বোধনে চমকে উঠল নন্দিনী। সে চক্রবর্তী রূপে ঠাকুরের পূজা করে নাকি আসলে যে গারুড়ী ওঝা, মনসা তার দেবী! এই দ্বন্দ্ব দেখা দিল একদিন। আশ্চর্য অদ্ভুত এই গল্পটা বটেশ্বর!’
এবার আমি নিজে দু’হাতে মুখ ঢাকলাম। আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছিল। ওঝার মুখে এই সব শুনতে শুনতে দিদি অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছিল। তা ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। তবারক কেমন বোকা বোকা ভাবে সব শুনছিল।
সহসা মুখের ওপর থেকে নিজের দু’হাত সরিয়ে তবার চোখে চোখ রেখে একটা খবর দেওয়ার সুরে বললাম, —‘একটা সিদ্দাগা আমার কাছে আছে তবারক। এটা আমায় দিয়েছিল কলেজের সহপাঠী নৈনিহাল মির্জা, যার কথা এতক্ষণ বলে যাচ্ছে শঙ্কর কাকা। নৈনিহাল অসম্ভব সুন্দর নীল চোখের ইরানি—এই বলে মনে করতাম আমরা। ঠিকই নবাবরা তো গোড়ায় ইরানেরই লোক। কথা হচ্ছে, শুধু ওর রূপ দেখেই তো কোনো নন্দিনী ওর প্রেমে পড়তে পারে তবারক—কী বল?’
শঙ্কর বলল, ‘কিন্তু সব নন্দিনী তো এক নয় বটেশ্বর! ওকে আমি বলেছিলাম, যা-ই কর মা, এমএ পাস হওয়া চাই, এই ফ্যামিলিতে কেউ চাইবে না, কিন্তু তুমি এমন করে চাইবে যাতে করে আজব বাধ্য হয় পড়াতে—কলকাতার পার্ক সার্কাসে আজবের বাড়ি আছে। এমএ পড়ার সুবিধা।’
তবারক বলে ওঠে, ‘আজবের বউমা এমএ পাস, বল কী কামরু!’
কামরু বলল, ‘আমার শেখানো কথাই নন্দিনী বলেছিল আজব মির্জাকে।’
আমি শঙ্কিত স্বরে বলে উঠি, ‘কী বলেছিল নন্দিনী?’
ফের মাথা নিচু করে কী যেন চিন্তা করে নেয় শঙ্কর গারুড়ী।
— ‘আমাকে মনসা স্বপ্নে যেমন বলেছে, তার সঙ্গে বুদ্ধি খাটিয়ে হিয়া মির্জার গল্পটা আমি ঝুঁকি নিয়ে তয়ের করেছি। মানুষই মানুষের গল্প বিধাতার মতো কেতায় তয়ের করে বটেশ্বর মিত্র। শোনো হরিমতী, গল্পটা আমারই বুদ্ধির কৌশলে আলিফ লায়লা হয়েছে। বাংলার মুসলমানকে আমি অত্যন্ত খুঁটিয়ে চিনি; আজবকে চিনি পুরা। তুমি বলো নন্দিনী যে, আমাকে এমএ পাস করতে দাও। পাস করলে পর নৈনিহালকে নিকাহ করব। কথা দিলাম। কথা দিলাম আব্বা। হ্যাঁ, ইরানি মুসলমান যদি শিয়া নবাব বা নিতান্ত গরিব কিংবা মার্চেন্ট হয়, এরা ভয় পায় বিদ্যাকে। মরুভূমির কানা জিনের চেয়ে বিদ্যা তার কাছে ভয়াবহ।’
তবারক বলে, ‘গল্পটা কি কঠিন হয়ে উঠছে কামরু?’
জীবনকে তাড়িয়ে বেড়ায়, তা কবে সহজ হয়েছে তবারক? ওমর যদি বিষদাঁত ভাঙা গহমা খরিসটা গছিয়ে না দেয়, তাহলে গল্পটাই তো ধ্রুবপুরে মরে শেষ হয়ে যায় হরিমতী।’
বলে হরিমতীর চোখের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকতে থাকতে শঙ্কর বলল, ‘সিদ্দাগাটা কি চাঁদ-তারা ছাপ অলা একটা সোনার মুদ্রা?’
আমি চমকে উঠে বললাম, ‘হ্যাঁ শঙ্কর কাকা, ঠিক তা-ই।’
— ‘ওটাই চিহ্ন, এ জিনিস নন্দিনীকে তার পুজোর থালায় রেখে ঠাকুর প্রণাম দিতে বলেছিল আজব। জিনিসটা দেখাও আমাকে। কথাটা আসলে হলো ‘সিজদাগাহ’—মানে সিজদা দেবার ‘গাহ’ অর্থাত্ জায়গা। যেমন ‘ঈদগাহ’ সেরকম। ওই মুদ্রার মতো দেখতে বস্তুটাকে সামনে রেখে তার ওপর সিজদা দেয় শিয়ারা। নাও, দেখাও।’
আমি বললাম, ‘আজ্ঞে কাকা! দিই।’
ছয়
শঙ্কর গারুড়ী এক আশ্চর্য চরিত্র। ওঝা, নন-ম্যাট্রিক, কিন্তু আধুনিক এবং একই সঙ্গে আলৌকিক এক জগতের মানুষ।
মুদ্রাবত্ দেখতে সিদ্দাগাটি, যা একপ্রকার টোটেম পুজোরই সামিল হয়ে বিদ্যমান, এটি আমাকে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছে নৈনিহাল, সঙ্গে ছিল বোরখা-পরা এক স্ত্রীলোক; জানতে চেয়েছি, ‘তোমার বউ? বোরখার দিকে সস্নেহে দৃষ্টি ক্ষেপ করে নৈনিহাল বলেছে, ‘হবু’
লাল টুকটুকে মোটর বাইকে করে পিছনে হবু বউকে সঙ্গে নিয়ে রসুল মার্চেন্টের ব্যবসার খোঁজ নিতে আসত নৈনিহাল। রসুল মহাজনের শাখা-ব্যবসাও ছিল গঞ্জে; স্থানীয় লোক সেই ব্যবসা চালাত। ভুলু পণ্ডিতের পাটের আড়তদারি ব্যবসারও মহাজন ছিলেন রসুল। ওই আড়তেও আসত নৈনিহাল। কী আশ্চর্য! বোরখার ভেতরে আটক স্ত্রীলোক যে নন্দিনী, কোনো ইঙ্গিত ছিল না—সে আমার মুখের দিকে চেয়ে বোরখার আড়ালে হয়তো নীরব অশ্রুপাত করেছে, কোনো ফরিস্তাও আমাকে সেই কষ্টের কথা বলেনি।
তবা বড্ড অবাক হয়ে কামরুর হাত থেকে সিদ্দাগা নামক মুদ্রাটি নেয়। এক পৃষ্ঠে চাঁদ-তারা, আরেক পৃষ্ঠে মক্কা-শরিফ—এই হচ্ছে স্বর্ণমণ্ডিত সিদ্দাগা—বোঝাই যাচ্ছে, এটি বিশেষ পরিকল্পনায় গড়া হয়েছে। কাঠের বা পাথরের সিদ্দাগা হয়। এটি টোটেম।
ধর্ম-তাড়িত মানুষ স্বভাবত মূর্তি উপাসক বা টোটেম পূজক, ধর্ম-তাত্ত্বিকরা বলে থাকেন।
কিন্তু পুজোর থালায় সিদ্দাগা ভারি আশ্চর্যই বটে!
সিদ্দাগা আমার হাতে ফিরিয়ে দেয় তবারক।
— ‘তোমার তয়ের করা আলিফ লায়লা শেষ করো কামরু।’
বলে উঠল তবা ফরাজি।
— ‘কেন, তোমার কি ঘুম পাচ্ছে?’ ঈষত্ ব্যাঙ্গের সুরে বলল শঙ্কর গারুড়ী।
নয় দিন চলল আঁধি। সব গল্প শেষ করল শঙ্কর গারুড়ী ওরফে কামরু ওঝা। গল্প তারই তয়ের করা বলে বললেও গল্পটি আপন খেয়ালে বুনে গেছে নিয়তি। কখনো সেই নিয়তি স্মৃতি-পুরাণ আর্যত্ব-ব্রাক্ষণ্যত্ব ধরে এসেছে, কখনো এসেছে ইসলামের ছদ্মবেশে, কখনো অনার্য মনসাকে ধরে, কখনো গল্প নেতা ধোপানির জন্ম-মৃত্যুর খেলায় আজব-তরী বেয়ে নদনদী খাল-বিল ঘুরে বেড়িয়েছে।
ওঝা বলল, ‘হিয়া যা বলত, তাইই করত নৈনিহাল। বাপের লোভ তার মধ্যে বোধহয় ডেরা বাঁধে।’
— ‘আজ্ঞে কাকা।’
— ‘হিয়া তো সরস্বতী ঠাকুরের মতো সুন্দরী আর তেজি মেয়ে, বুদ্ধি আর জ্ঞানের শিখা।’
— ‘আজ্ঞে শঙ্কর কাকা।’
— ‘এই দেবীকে তার বাবা নিশ্চয়ই পাইয়ে দেবে, বাবা এই বিদ্যাবতীকে ঘরে বোরখার বাইরে রাখলেও, বাইরে বোরখার ভেতরে রেখে পুষেছে, অতএব হিয়া তারই, এমনি করেই কি ভাবত না নৈনিহাল? যা হোক। আমাকে, এই গারুড়ীকে ভয় করত নৈনিহাল। গল্পটা আমার তয়ের করা, এ কথাও জানত। কিছু মনে কোরো না তবারক, এই নৈনিহালই ভুলু পণ্ডিতকে হিয়াকাণ্ড বলে দিয়েছিল। আমি কী করে কী করেছি সব ফাঁস করে দেয়!’
— ‘হা ভগবান!’
ভাগবানকে ডেকে উঠলাম।
— ‘একদিন ভুলু আমাকে রাস্তায় ধরে বললেন, দোয়া করো ফকির পাটের যাতে দর ওঠে। বললাম, দোয়া করি দাদা! তখন ভুলু বললেন, আর দোয়া করো কামরু, নবাবের পালিতা কন্যা যেন আড়াই বাঁকির মির্জা সায়র থেকে স্বগৃহে ফিরে আসে। নবাব নন্দিনীর যেন ধ্রুবপুরেই কবর হয়। কবরের জায়গা আমিই দেব গারুড়ী। শুনলাম, তুমি জব্বর পিরের মুরিদ হয়েছ। বুঝলাম, আমার ঘোর বিপদ, হয়তো প্রাণে বাঁচব না। একদিন আড়তে পাটের গাঁটরির ভেতর রসা দিয়ে বেঁধে রাখল ভুলু পণ্ডিত।’
তবারক বলল, ‘এই যে পাটের গন্ধে তোমার মৃত্যু হলো। তোমার মরাদেহ ভৈরবের পানিতে ফেলে দেওয়া হলো, সব ঘটনা সংসারে রটে যায়। তারপর তুমি বেঁচে উঠলে এবং গঞ্জের বটতলায় লোকে তোমাকে সাপ খেলাতে দেখে কেমন অবাক হয়ে গেল, সব ব্যাপার রাষ্ট্র হলো বাবা হে!’
ওঝা বলল, ‘এ কথা নন্দিনীরও কানে গিয়ে পৌঁছাল তবারক।’
আমি বললাম, ‘তোমার কথা শুনছি আর আমি ভাবছি, এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে আমি কোথায়? এমনকি আমারই চোখের সামনে এক বোরখা-পরা স্ত্রীলোককে দেখছি, তাতেও আমি যেন একটা অবান্তর প্রাণী, কারও কেউ না!’
— ‘তুমি সব বটেশ্বর। যা ঘটছে সব তোমার জন্য। তুমিই কারণ। নন্দিনী তো নেতার ঘাটেই ফিরতে চেয়েছে নতুন জন্মে, যাতে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। নন্দিনী তো বটুদাকেই চেয়েছে আর ভেবেছে, বটুদা আমাকে নেবে কেন! তবু আমি একবার অন্তত ছয় ঘরায় আসব এই জীবনে।’
এবার হরিমতী কথা বলে উঠল, ‘তা কী করে হয় গারুড়ী, ওই মেয়ে কি আর সমাজের যোগ্য আছে মনে কর? হলোই বা এমএ পাস!’
এ কথায় প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেল শঙ্কর গারুড়ী। তারপর স্লান হেসে বলল, ‘এই জন্যই তো আঁধির মধ্যে একা কেঁদে ফিরছে নন্দিনী! কিন্তু ভাবনাটা অন্য জায়গায় তবারক। আজবের বয়েস ১০৩ বত্সর। ও মরবে বলে ছয়ঘরা এসেছে। কারণ ভারতে ওর আর কেউ নেই। সবাই বিনিময় করে পূর্ববঙ্গ মানে পূর্ব পাকিস্তান চলে গেছে।’
বলে আবার মাথা নিচু করল ওঝা।
দিদির কথায় আশ্চর্য রকমের বিমূঢ় হয়ে গেলাম আমি। দিদির মনটাই তো এদেশের বহু পুরাতন সামাজিক মন। ধর্ষিতা সম্পর্কে কোনো সহানুভূতি এ সমাজের নেই। ধর্ষিতাকে সমাজের বাইরে ঠেলে ফেলে দেওয়ার নজির নানান পথে তয়ের করে এই সমাজ। কিন্তু এই অবস্থায় আমার কী কাজ? মনে হলো, বাইরে আবার সে এসেছে। হঠাত্ আমি আরাম কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।
তবারক ত্বরিতে বলে উঠল, ‘কী হলো বড়ো বাবু!’
বললাম, ‘আবার কেউ কাঁদছে তবারক, চলো দেখি!’
দিদি বলে উঠল, ‘কেউ কাঁদছে না বটু। সব তোমার মনের ভুল!’
— ‘না, কোনো ভুলটুল নয়! এটা নারী-পুরুষের আদি গল্প! “আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী”। আমরা ধর্ষণ করি এবং ঘৃণা করি! আজ আসল সময়ে নিজেকেই চিনতে পারছি না। চলো তবা। বর্ষাতি নাও।’
বলে বর্ষাতি নিজে গলিয়ে নিই।
ক্ষিপ্র বেগে বাইরে বেরিয়ে চলে আসি।
— ‘দাঁড়ান বড়ো বাবু। টর্চটা সঙ্গে নিই। একটু দাঁড়ান। এলাম বলে।’
এই বলে টর্চ আনতে ছুটে বাড়ির ভেতরে গেল তবারক।
ছুটে এল টর্চ নিয়ে বাইরে।
— ‘ওই তো! ওই তো বোরখা-পরা স্ত্রীলোক। দেখতে পাচ্ছ তবারক?’
— ‘না, বড়ো বাবু, কোথাও কিছু দেখছি না তো!’
— ‘ভালো করে দেখো, ওটা হিয়া মির্জা। ও শ্বশুরের সঙ্গে ছয়ঘরা এসেছে।’
— ‘না, বাবু! কেউ নেই।’
অতি ভয়ংকর হয়ে উঠেছে আঁধি। ফলে এভাবে আঁধির ভেতর দিয়ে কোনো রহস্যময় আলৌকিক নারীর খোঁজে যেতে দিতে চাইছে না তবারক। আমার সে রকমই মনে হলো।
বললাম, ‘তুমি দেখেও দেখছ না তবারক। ওই তো…’
এই বলে একাই এগোতে থাকি। অগত্যা তবা আমার পিছু পিছু আসতে থাকে।
আমি ছয়ঘরার দিকে যেতে থাকি।
— ‘বড়োবাবু, আপনি কোথায় যেতে চাইছেন? ছয়ঘরা? মির বাড়ি?’ একেবারে ঘাড়ের কাছে প্রায় ছুটে এসে জানতে চাইল তবারক।
বললাম, ‘তুমি আমার সোর্স। কিন্তু খবরই তো আনলে না তবা।’
— ‘খবর কিছু জোগাড় হয়েছে বড়ো বাবু। ওঝা কথা বলছিল বলে আমি সেসব খবরাখবরের ব্যাপারে কথা বলিনি। ওঝার সঙ্গে ওমরের কথা মিলিয়ে নেবারও তো দরকার। আমি মির বাড়ি গিয়ে আজবের সঙ্গে কথাও বলেছি দু-চারটি। হিয়া মির্জার সঙ্গে একটি-দুটি কথাও হয়েছে।’
— ‘কই বলোনি তো?’
— ‘আর একটু গুছিয়ে নিয়ে সবিস্তারে বলতাম! ওই দেখুন! ডিহির উপর নিমতলায় মনি ডাক্তার। আজবকে এই আঁধির মধ্যেও দেখতে এসেছিলেন। আজব খুবই বুড়ো হয়েছে। ১০৩ বয়েস। কম কথা। তার বেঁচে থাকাটা আশ্চর্যের। ওর আর গুনাগুনতি দিন। মাথাটা একটু ঘেঁটে গেছে।’
— ‘আমি কথা বলতে চাই তবারক।’
— ‘এখন?’
— ‘শুনুন বড়ো বাবু, আপনি নারী-কান্না শুনলেন। যদি এ কান্না নন্দিনীর হয়, তাহলে, মনি ডাক্তারকে রেখে সে বার হয়েছিল বলতে হয়। এক হতে পারে, ডাক্তার এল, কিন্তু আজব বাঁচল না, তাই সে সুর ধরে কেঁদেছে। কিন্তু সেই কান্না দিদি হরিমতীর বাড়ি পৌঁছায় কী করে!’
— ‘দাঁড়াও। মনি ডাক্তারের সঙ্গে আমি কথা বলব। উনি ডিহি থেকে নেমে আসছেন। সঙ্গে কমপাউন্ডার নাগ মশাই। যদি আজব মারা গিয়ে থাকেন, জানতে পারব না তার লোভ কী বিচিত্র বস্তু! তাঁর সিদ্দাগা কি নন্দিনীর কাছে পুজো চেয়েছে? তিনি পূর্ব পাকিস্তান গেলেন না কেন? এখানে তার সত্যি করে কাজ কী? নৈনিহাল আর নন্দিনীর সম্পর্ক কী?’
মনি ডাক্তার নেমে এসে আমাকে নমস্কার জানালেন। আমি প্রতি নমস্কার দিই।
— ‘এখানে কী করছেন বড়ো বাবু?’
জানতে চাইলেন ডাক্তার বাবু।
আমি বললাম, ‘আপনাকে দেখেই দাঁড়াতে হলো। আজব মির্জার অবস্থা কী?’
— ‘আছে। তবে থাকবে না।’
— ‘কী এমন হলো, আজবের পুরো পরিবার পাকিস্তান চলে গেল, ফের উনি গেলেন না!’
— ‘দাঙ্গা যুদ্ধ এসব হয়তো ব্যাপার! কিন্তু ব্যবসাটা হঠাত্ পড়ে যায় রসুল মির্জার। শ্যাম জৈনের সঙ্গে পার্টনারশিপ আর থাকে না। ভাগ্যের একটা বিপর্যয় এই ষাটের দশকের মাঝামাঝি ঘটল নবাবের জীবনে। তাছাড়া পাকিস্তানের দিকে বরাবর একটা ঝোঁক এই নবাবের ছিলই। ছিল বটে, ফের নিজেই তিনি গেলেন না! মনের এই গতির কথা ব্যাখ্যা করা কঠিন, বড়ো বাবু।’
— ‘সঙ্গের ওই মেয়েটি ওনার কে?’
— ‘সে ভারি রহস্য বড়ো বাবু। আজব লোককে বলছে, ওটা ওর বউমা, ফের বলছে, বউমার বিয়ে দেবে বলে ছয়ঘরায় পড়ে আছে সে। আমার এই কমপাউন্ডার নাগ মশাই বলছে, ওটা নাকি ভুলু পণ্ডিতের ভাগ্নি! যদি ওটা আজবের বউমা হয়, তাহলে স্বামীটি কোথায়? একদিন শুধালাম, হ্যাঁ গো মামণি, আপনার স্বামী কোথায়? জবাবে বউমায়ের কথা কেড়ে নিয়ে ওই আজব বলল, নৈনিহাল সিরাজে আছে। মরে নাই। তবে সাত বছর হয়ে গেল। ফলে বউ তালাক হয়ে গিয়েছে। সাত বছর স্বামী-স্ত্রী’র দেখা-সাক্ষাত্-সহবাস না হলে আপনা-আপনি তালাক হয়ে যায় ডাক্তার বাবু। এখন তাই নতুন করে নিকাহ বসাতে হবে। সে গল্পও অদ্ভুত! আচ্ছা চলি!’
সম্পর্কিত পোষ্ট => আমার প্রথম পাপ
— ‘দাঁড়ান ডাক্তার বাবু, ওই অদ্ভুত গল্পটা আমাকে বলে যান।’
— ‘আঁধি থামলে বলব।’
এই বলে বেশ কিছু পথ চলে গিয়ে চিত্কার করে ডেকে ওঠেন মনি ডাক্তার।
— ‘শুনুন, বড়ো বাবু! শুনুন কথাটা!’
— ‘হ্যাঁ, বলুন ডক্তার বাবু!’
ডাক্তার বাবু এগিয়ে আসেন আমার দিকে। আমি এগিয়ে যাব ডাক্তার বাবুর দিকে। তবারক খানিক দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। একেবারে বুকের কাছে ঘেঁষে এসে ডাক্তার বাবু বললেন, ‘ছোট ছেলে নৈনিহালকে নিয়ে বড্ড কষ্ট এই বৃদ্ধের। মাথাটারও ঠিক নেই, ছেলে ইরানের সিরাজে চলে গেছে আর ফেরেনি। কেন গেল, সব সমাচার স্পষ্ট হচ্ছে না। আমার সন্দেহ, ওটি রসুলের বউমা নয়। এটা ওদের ছদ্মবেশ। আপনি থানার বড়ো বাবু, দেখুন যদি রহস্যের কিনারা করতে পারেন! এটা কি অদ্ভুত গল্প নয়? নৈনিহাল নাকি এদিকে কোথায় একজন হিন্দু বন্ধুর হাতে সিদ্দাগা দিয়ে গেছে, সেই বন্ধুটাকে রসুলের চাই। শুনে তো বিশেষ অবাক হলাম। সিদ্দাগা, যদ্দুর জানি, সিজদার টোটেম, সেটা দিয়ে গেল বন্ধু, যে-কিনা হিন্দু। ওই বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে চাইছে এই বুড়ো। একি অদ্ভুত গল্প নয়? বাকি কথা আঁধি থামলে হবে। পারলে ওই বন্ধু সহপাঠীকে খুঁজে বার করুন, বৃদ্ধ বাপের মনে শান্তি আসবে।’
আমি থ হয়ে দাঁড়িয়ে ডাক্তার বাবুর চলে যাওয়া দেখি। আমার সামনে মনি ডাক্তার বাবুর চলে যাওয়া, ডাক্তার বাবুর পিছনে ডাক্তারি ব্যাগ হাতে কমপাউন্ডার সতীশ নাগ যাচ্ছেন; বাতাস ঝেঁটিয়ে নিয়ে বৃষ্টিকে ওপরে তুলছে আর নিচে নামাচ্ছে।
আমার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা কাকা এগিয়ে এল।
হঠাত্ দেখি ডাক্তার বাবু আর নাগ মশাই দাঁড়িয়ে পড়লেন। আবার কী হলো? দেখি, সতীশ নাগ এগিয়ে আসছেন।
তবা বলল, ‘ডাক্তার বাবুই নাগকে পাঠাচ্ছেন, বুঝলেন না বড়ো বাবু!’
— ‘আবার কী কথা?’
— ‘আছে কিছু।’
সতীশ ডাক্তার বাবুর মতোই নাগ মশাই আমার একেবারে বুকের কাছে ঘেঁষে এসে বললেন, ‘ডাক্তার বাবু আপনাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছেন বড়ো বাবু!’
— ‘কী?’
— ‘আপনি নন্দিনীকে বিয়ে করুন। ব্যস।’
এই বলে চলে গেলেন সতীশ নাগ।
স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ডিহির নিচে সরু পথটার ওপর। ডিহির ওপরই ছয়ঘরার পাড়াটা। মির্জা পরিবারকে ভুল করে লোকে মিরবাড়ি কেন বলে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। রসুল ওরফে আজব মার্চেন্ট তো মির নয়, ওরা মির্জা; শিয়া নবাব, ওদের পূর্বপুরুষ ইরানি—এখনো ইরানের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি।
এদের আত্মীয়দের অনেকেই পূর্ব পাকিস্তান চলে গেছে। মনে রাখতে হবে, এরা ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানে চলে যাওয়ার কথা হামেশা ভাবে, দাঙ্গা হলে, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে এরা ভয় পায় নিতান্ত বেশি, যে-ভয় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমানের মধ্যে নিতান্ত কম। ফের এ কথাও সত্য, এই নবাবদেরই পূর্বপুরুষ শিবের পাদোদক পান করে সিংহাসনে অভিষিক্ত হতেন। মিলন-সংস্কৃতির এক মহা ইবাদত করেছেন নবাবরাই।
সেই নবাবদেরই এক বিশেষ অনুসারী নবাবকেই দেখা করা এই মনসামঙ্গল আঁধির মধ্যে।
— ‘তবারক চলো তা হলে যাই!’
— ‘ডিহিতে উঠবেন?’
— ‘হ্যাঁ।’
এগোতে থাকি।
— ‘পাশে এসো তবারক।’
— ‘আজ্ঞে।’ বলে এগিয়ে এসে তবা ফরাজি আমার পাশে পাশে চলতে থাকে। হঠাত্ আকাশ থেকে মানে মেঘ থেকে ঝরঝর করে কী উড়ন্ত সাপ ঝরে পড়ল। টর্চের আলোয় দেখলাম। মনে হলো, সাপগুলোর রং সবুজ— অনেকাংশে লাউডগা ধরনের লতানো। এরা কী করতে চাইছে। এভাবে কি সর্পবৃষ্টি (পুষ্পবৃষ্টির বদলে) হলো?
— ‘এত সাপ! তবারক! বড্ড আনন্দ পেয়েছে, মনে হচ্ছে!’
— ‘কিন্তু ডিহির উপর, ওটা কে?’
— ‘তাই তো! শঙ্কর কাকা কখন এল!’
শঙ্কর গারুড়ীই যেন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
কে কাঁদে অমন করে, চলো দেখবে, চলো বড়ো বাবু! আজবকে কথাই শুধু নানান ছলে বলে গেছে নন্দিনী, আর তা হচ্ছে…।’
এই বলে সম্মুখে, নিতান্ত কাছে, দাঁড়িয়ে পড়ল কামরু ওঝা।
— ‘কোন কথাটা কাকা?’ বলে উঠি।
— ‘বটুদার কাছেই আমাকে ফিরিয়ে দিও আব্বা। এই আব্বা ডাকটা বড়োই বিশ্বাসী আর খুবই আপনার অমন করে ক’টা বালিকাই বা ডাকতে পারে! চলো, চলো!’
বলে এগোতে থাকে কাকা।
— ‘আচ্ছা, অন্য একটি কথা বলছি, তবাকে বলছি।’ বলল শঙ্কর।
তবা বলল, ‘বলো শুনছি।’
গাবগাছটায় যে মধুর চাকটা ছিল, সেটা আঁধিতে মুছে গেছে, এই আঁধিতে। দেখেছ?’ প্রশ্ন করে শঙ্কর।
তবা বলে ওঠে, ‘আবার হবে।’
— ‘ঠিক।’ তত্ক্ষণাত্ সমর্থন করে দাঁড়িয়ে পড়ে পিছনে ঘুরে দাঁড়াল ওঝা।
— ‘তুমি কী বলো বটেশ্বর?’, শুধাল কামরু ওঝা।
আমিও বলি, ‘আবার হবে কাকা।’
— ‘জীবন এই রকমই, মুছে যায়, আবার হয়।’ বলল শঙ্কর গারুড়ী।
আবার এগোচ্ছে শঙ্কর। আমরাও এগোচ্ছি।
নেতা ধোপানির ঘাটের পাড়ে দোতলা বাড়ি ‘মির্জা মঞ্জিল’। যেন এই মঞ্জিল ঘাটের জলের ওপর ঝুলে আছে, পাড়টা এমনই নদীর জলের দিকে ঠেলে বেড়ে গিয়েছে।
দরজা বন্ধ। ভেতর থেকে খিল আঁটা। বাইরে দরজায় পেতলের দুটি বালা ঝুলছে। গারুড়ী বালা দুটি ধরে নাড়া দেয়।
থেমে থেমে বার তিনেক কড়ায় নাড়া দিতেই দরজা খুল দেয় নন্দিনী। বাইরের ঝলসিত বিদ্যুত্ নন্দিনীর চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।
সে বলে ওঠে, ‘কারা আপনারা?’
ওঝা কালো বর্ষাতি গায়ে নেওয়ায় তাকে চিনে নেওয়া নন্দিনীর পক্ষে আরও দুঃসাধ্য হয়েছে।
শঙ্কর বলল, ‘আমি তোমার কামরু কাকা। আর এরা কে কে, ঘরে ভালো করে আলো দাও, চিনতে পারবে। যত মোমবাতি আছে জ্বেলে দে মা।’
— ‘জি আসুন ভেতরে আসুন।’
এই বলে দরজা ছেড়ে ভেতরে চলে গেল নন্দিনী ।
তারপর সে সারাঘরময় যেন বা অগুনতি মোমবাতি জ্বেলে দিতে থাকে। একটার পর একটা জ্বালতে থাকে। দেখতে দেখতে ওঝা কথা বলল। ‘তুমি কি বুঝতে পারছে কে এসেছে তোমার আব্বার সঙ্গে দেখা করতে? একবার চেয়ে দেখো এদিকে। বর্ষাতি খুলে ফেলো বটেশ্বর। তুমিও বর্ষাতি খুলে রাখো তবা।’ বলল ওঝা।
নন্দিনী কিন্তু এখনো আমার দিকে চোখ তুলে দেখল না। মন দিয়ে মোমের শিখা জ্বালিয়ে বিভিন্ন স্থানে পুঁতে পুঁতে দিতে থাকল এবং বর্ষাতি খুলে রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছি।
আলো দিতে দিতে আলোর শিখায় চোখ রেখে নন্দিনী বলল, ‘ওদের মোড়ায় বসতে বলো, তুমিও বসো।’
ওঝা বলল, ‘মোড়ায় বসো তোমরা। আমিও বসি। আর তুমি মা, আব্বাকে কানে কানে বলো আমরা এসেছি। কানের কাছে চেঁচিয়ে বললে উনি শুনতে পান। আর সমস্যা হচ্ছে, আজব ভাই দৃষ্টি হারিয়েছে, পুরো অন্ধ। তা হোক। তোমার পকেটে যে-সিদ্দাগাটা বার করে হিয়াকে দাও। ও আব্বার হাতে দিয়ে যা বলার বলবে।’
আমি সোনার সিজদাগাহ পকেট থেকে বার করলাম আর অপূর্ব সুন্দরী নন্দিনীর রূপের হুরি সৌন্দর্যে চেয়ে রইলাম।
সাত
আশ্চর্য রাত্রি। বাইরে আঁধি। ভেতরে মোমালোকে উজ্জ্বল ধবল পবিত্র উদ্ভাসিত—সারা ঘরটা যেন একটি স্বর্গের কক্ষ রূপে মায়াবী, রহস্যময়। নারীটি হুরিই বটে। যেন পার্থিব জীবনের কোনো মালিন্য, কোনো গ্লানি ওকে কখনো ছুঁতে পারবে না। ও আমার দিকে চেয়েও দেখছে না। এ কেমন আচরণ!
আজবের ডান হাতের তালুতে সিদ্দাগা রেখে হাত মুঠো করে দিয়ে কানের খুব কাছে মুখ নিয়ে গেল নন্দিনী। আজব শুয়ে আছেন। গায়ের ওপর লাল টুকটুকে নিতান্ত হালকা বালাপোশে শরীর কোমর অবধি ঢাকা। কান পেতে তৈরি অন্ধ মানুষটি। বোঝাই যাচ্ছে তাঁর কানের কাছে নন্দিনীর নিঃশ্বাস পড়লেই তিনি শোনার জন্য ভীষণই উত্সুক হয়ে ওঠেন।
— ‘বাবা! আব্বা! নৈনিহালের দেওয়া আমার সেই সিদ্দাগা বাপু! তুমি আমাকে পুজোর থালায় এটি রেখে বলেছিলে… মনে পড়ে কী বলেছিলে?’ এই বলে থামল নন্দিনী। বাপ মেয়ের এ বড়ই অবাক ঘন সম্পর্ক! এরা তো শ্বশুর-বউমা নয়।
মুখ তুলে এই প্রথম আমার চোখে চোখ রাখল নন্দিনী। তারপর দ্রুত সেই চোখ টেনে নিয়ে আজবের ওপর ফের ঝুঁকল; কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল।
— ‘সিদ্দাগা নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে বটেশ্বর!’
— ‘কে? বলে জোর গলায় জানতে চাইলেন রসুল মির্জা।’
নন্দিনী পুনরাবৃত্তি করল, ‘বটেশ্বর, আব্বা।’
— ‘অ্যাঁ।’
— ‘বটেশ্বর মিত্র!’
— ‘ওহ! বটেশ্বর!’
— ‘হ্যাঁ বাবা। বটেশ্বর মিত্র। থানার বড়ো বাবু!’
— ‘তোমার বটুদা!’
আবার চোখ তুলে তির্যকভাবে আমাকে দেখতে দেখতে নন্দিনী বলল, ‘হ্যাঁ।’
এই ‘হ্যাঁ’ বলার মধ্যে অকারণ একটা অভিমান অল্প করে ছলকালো।
নাটকের নামী অভিনেতাদের মতো রসুল মির্জার গলার স্বরটা বেশ গম্ভীর এবং গমগমে; সেই স্বরে তার ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে; তার চোখের তারা নীল। এত বয়সেও ঠোঁটে জড়ানো হাসির প্রসন্নতা।
— ‘বড়ো বাবুকে কাছে ডাকো নন্দিনী!’ বলে ওঠেন রসুল মার্চেন্ট।
— ‘নন্দিনী! তুমি আমাকে নন্দিনী বলে ডাকলে আব্বা!’
— ‘হ্যাঁ, মা! আজ তো ভুলু পণ্ডিত বেঁচে নেই, তোমার ভয় কী! তোমাকে আর বোরখাও পরতে হবে না। ডাকো। বড়ো বাবুকে ডাকো! আর শোনো, কামরু ওঝাকে তাড়িয়ে দাও! আচ্ছা, ঠিক আছে! ওটাও থাক। আচ্ছা বড়ো বাবুর আগে, গারুড়ীই আসুক! অ্যাই শঙ্কর, ই দিকে আসো!’
বলে নাটকীয় হাঁক দিলেন রসুল মির্জা।
মোড়া হাতে তুলে নিয়ে ক্ষিপ্র বেগে শঙ্কর এগিয়ে গেল রসুলের খাটের কাছে। খাট ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে কচলাতে অল্প ঝুঁকে বলে উঠল, ‘জি নবাবজাদা, যা বলার বড়ো বাবুর সামনেই বলুন!’
নবাব বললেন, ‘হাত লাগাও গারুড়ী, খাড়া করে বসিয়ে দাও। তুমি মোটে ধরবে না মা। যা করার কামরুকে করতে দাও।’
— ‘জি আব্বা!’
তবা বড্ড অবাক হয়ে আমার চোখে চোখ রাখল; আমার চোখে বিদ্যুত্-বিস্ময় খেলে গেল।
খাটের ওপর নবাবকে বসিয়ে দিলো শঙ্কর ওঝা।
নবাব বলল, ‘শুকরিয়া গারুড়ী।’
— ‘আপনার কষ্ট আমি বুঝি নবাবজাদা!’
— নাহ ঝুট্। ঝুটি বাত বলছ শঙ্কর! তুমি আমার কী করেছ, কতবড় নুকসান করেছ এক জরা মাহসুস করতে পার না। তুমি আঁধির মধ্যে যে লড়কিকে নিয়ে গিয়ে বললে, একে লুকিয়ে রাখো নবাব। ওমর সঙ্গে ছিল, বলল, জি হুজুর, মেয়েটিকে বাঁচান। খেয়াল হ্যায়?’
— ‘জি নবাব, হয় বইকি।’
— ‘একজন ইমানদার মুসলমান, হজরত আলির চেলা কী করতে পারে, একটি নারীকে আব্রুর মধ্যে লুকিয়ে ফেলতে পারে, এভাবে ছুপানো ছাড়া…’।
— ‘জি নবাব, এ ছাড়া ভালো ব্যবস্থা আর কী হয়!’
— ‘হমনে দো লবেজাকে অন্দর নন্দিনীকো ছুপায়া থা। এক, বুরখা, দুসরা হলো নাম। ম্যায় নে দিয়া থা উসকা নাম হায়া। হায়া মির্জা। স্কুলের ক্লার্ক পুলিন বাবু করে দিলে হিয়া মির্জা। আমি চটে গেলে পুলিন ঠাকুর বোলা, হিয়াকা মতলব সমঝো দাদা, হিয়াকা মতলব “দিল” (হূদয়)। তো, আচ্ছা হুয়া মেরি নন্দিনী দিলারা বনগয়ি, “দিল”-সে আচ্ছা কিয়া হ্যায় ইস দুনিয়ামে? কিন্তু তুমি বললে, লেখাপড়া শিখে হিয়া যেন দেবী সরস্বতী হয়। তুমি নন্দিনীর কানে কানে লাগাতার কী বলে গেছ, ঠিক বুঝে গেছি আমি।’
— ‘জি।’
— ‘আমার ফ্যামিলিতে প্রথম বিএ পাস নৈনিহাল। হায়ার সেকেন্ডারি (ওল্ড)-মেঁ তিনোঁ সাবজেক্ট পর নৈনিহালকো ব্যাক মিলা। বিএ পাস করনেকে লিয়ে উসকো পার্ট ওয়ান আউর পার্ট -টু-মেঁ দো-দোবার “গ্রেস” লেনা পড়া। উসকো সাথ সরস্বতী কা নিকাহ্ ক্যাসে হোনা থা গারুড়ী। হায়া মির্জা এমএ ফার্স্ট-ক্লাস। নিকাহ্ করনেকে লিয়ে কৌন নৈনিহালকো গ্রেস দেনেকো তৈয়ার থা? ম্যায়? হায়া দেতী? নৈনিহাল বোলা ইয়ে নিকাহ্ নহি হোগা আব্বা। মাথা নিচু করে বললে মেরা বেটা নৈনিহাল। বোলা মুঝে ডর লগতা ইস শাদিমেঁ আব্বাজান। এ বিয়ে ক্যানসেল কর দো। কিন্তু কী বোকামি দেখো গারুড়ী! আমি লোভে পড়ে হায়াকো ‘বহু-বহু’ (বউমা-বউমা) বলে ডাকতে শুরু করেছিলাম। এই কাহানি তোমাকে কেন শোনাচ্ছি কামরু?’
— ‘আমি কিছু বলব না নবাব। আপনি এখনো কষ্ট পাচ্ছেন হুজুর। কিন্তু আমি তো পাটের গাঁটুরির মধ্যে দম বন্ধ হয়ে মরেই গিয়েছিলাম বাবা হে!’
— ‘আমার ছেলেকে আরবি-ফার্সি ওস্তাদ রেখে আমি শিক্ষা দিয়েছিলাম; নৈনিহাল কোরান তেলাওয়াত (সুর করে পড়া) করতে পারত? গলা মিঠা ছিল কামরু।’
— ‘জি।’
১০৩ বছরের বৃদ্ধ এবার চুপ করে গেলেন। তার অন্ধ চোখ থেকে নিঃশব্দে জল গড়াতে লাগল।
— ‘বাবা! আমি নিকাহ্ করব না, একথা কখনো বলিনি। নৈনিহাল নিজেই তো হঠাত্ শেষে বেঁকে বসল আব্বা!’
— ‘হ্যাঁ তাই তো বসল মা! ও তোমার বিরাট শিক্ষাকে ভয় পেয়ে গেল তো। আর এটাই চেয়েছিল গারুড়ী!’
এবার মোড়ার ওপর কপালে হাত রেখে বসে পড়ল শঙ্কর কাকা।
আমি মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।
— ‘তুমি কি চলে যাবে বটুদা!’ বলে উঠল নন্দিনী।
আমি বললাম, ‘এখানে আমার কাজ কী নন্দিনী! ভাববে আমি নৈনিহালকে ঈর্ষা করছি। মোটে তা নয়। নবাব নৈনিহালকে তোমার নিকাহ্ করা উচিত ছিল।’
— ‘শোনো বটুদা, বেশি লেখাপড়া শিখলে মুসলমান সমাজে মেয়েটির বিয়ের সমস্যা হয়। নবাব ফ্যামিলিতে আরও হয়। এমনকি এ সমস্যা, হিন্দু ফ্যামিলিতেও হতে পারে। এ সমাজে মেয়েরা বেশি বাড়লে সর্বত্র সমস্যা হয় বড়ো বাবু! কিন্তু জানি, তোমার সমস্যা আরও দুরূহ বটুদা! আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি আসতে পার! বাবা, বড়ো বাবু, চলে যাচ্ছে। শুনছ? বটেশ্বর চলে যাচ্ছে, যেতে বলি?’
বলে উঠল নন্দিনী।
— ‘কেন? চলে যাবে কেন! বটেশ্বর তো কাছেই এল। ডাকো। আসল কথাটা বলি।’
বললেন রসুল মির্জা।
মোড়া হাতে তুলে নিয়ে আমি নবাবের দিকে এগিয়ে গেলাম। খাটের গা-ঘেঁষে মোড়া রেখে শঙ্কর কাকার কাছাকাছি বসে পড়লাম।
শঙ্কর গারুড়ীকে বললাম, ‘তুমি লজ্জা পেয়ো না শঙ্কর কাকা। তুমি কোনো অন্যায় করনি। নৈনিহালের ‘কমপ্লেক্স’ নিয়ে কার কী করার ছিল কাকাবাবু! আচ্ছা, ঠিক আছে।’
এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে ‘বলুন নবাব’ নবাবের কানে মুখ রেখে বললাম, আসল কথাটা গলার স্বর আরও চড়িয়ে বললাম। ‘বলুন নবাব, কী বলবেন!’
— ‘অ্যাঁ?’
— ‘বলুন’? (গলা আরও চড়ল)।
— ‘কথা হলো! নৈনিহাল পাকিস্তানে গিয়ে মামাত বোন নাজকে বিয়ে করবে ঠিক হলো। বিনিময় করে তামাম ফ্যামিলি চলি গয়ি বটেশ্বর!’
— ‘আজ্ঞে!’
— ‘এবার শোনো!’
— ‘মন দিয়ে শুনবে।’
— ‘আজ্ঞে!’
— ‘সবাই যাচ্ছে, তৈরি সবাই। আমি বসলাম বেঁকে। বললাম, ম্যায় নহি জাউঙ্গা নৈন্হাল। নৈনিহাল যাচ্ছেতাই ‘ড্রামা’ করল বাবা। কান্নাকাটি করল খুব।’
— ‘জি।’
— ‘শেষে মস্ত একটা মতলব আঁটল! হায়াকে বলল, তুই তো যাচ্ছিস হায়া। চল। ভালো বর জোগাড় করে দেবো তোকে। বটু-র চেয়ে সামান্য মোটু হবে, কিন্তু খাসা হবে। আর ওই বটু তোকে নেবে তার কী গ্যারান্টি! দেখো আব্বু, হায়া মির্জা গেলে তোমার আপত্তি নেই তো! ভেবে বলবে আব্বাজান। ও যাচ্ছে! এখানে ওর আছে কী? সমাজের চোখে ও তো বেঁচেই নেই আজব মির্জা! হা-হা-হা!’
— ‘আপনি হাসছেন?’
— ‘কী বললে বটেশ্বর?’
— ‘হ্যাঁ, বলুন।’
একটা ঢোক গিলে অন্ধ নবাব বললেন, ‘আমাকে নিয়ে যাবে পাকিস্তানে। তার জন্য নৈনিহাল একটা সেন্টিমেন্টলি ড্রামা করল। কিন্তু সব শুনেটুনে মাথা হেঁট করে চুপ করে রইল নন্দিনী চক্রবর্তী। ইসকে বাদ শির উঠাকর হায়া নে বোলি ম্যায় নহি জাউঙ্গি নৈনিহাল, কিঁউকি পাকিস্তানমেঁ ননা হ্যায়। ওখানে ননা আছে। এই ড্রামাটা ভাবতে পার বটেশ্বর! তুমি বলবে, ননা কোথায় নেই! ঠিক কথা। কিন্তু ড্রামাটা ভাবো পুত্র!’
আমি ধীরে ধীরে মোড়ার ওপর বসে পড়লাম। তারপর দু’হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলাম।
তবা বলল, ‘নবাব ওঁর কথা বোধহয় শেষ করলেন। তাই কি নন্দিনী?’
— ‘আর কী বলবেন, আমি বলতে পারব না তবা কাকা!’ বলল, নন্দিনী চক্রবর্তী।
তবা বলল, ‘আমি একটা পষ্টাপষ্টি কথা বলতে চাই, তোমাকে শুনতে হবে হিয়া।’
— ‘বলুন।’
— ‘মনি ডাক্তারবাবু তোমার বটুদাকে একটা প্রস্তাব দিলেন। আমি সেই প্রস্তাব সমর্থন করি। নবাব এখানে তোমাকে নিয়ে এসেছেন বিয়ে দেবেন বলে। যে-কথা এখনো উনি বলতে পারলেন না। পারাও তো যায় না, নাকি কামরু? কী বলবে তুমি?’ বলে হিয়ার দিকে চাইল।
কামরু ওঝা বলল, ‘আমি কিন্তু বিষম সমস্যায় রয়েছি।’
— ‘তোমার আবার কী সমস্যা!’ তবা ঈষত্ বাঁকা সুরে বলে ওঠে।
ওঝা বলল, ‘এই গল্প তো মনসার সৃষ্টি বাবা হে। ভাবছি তিনিই শেষ করবেন!’
আমি চমকে উঠে বলি, ‘মানে! কী বলতে চাইছ শঙ্কর কাকা?’
— ‘বলছি। তবারক হরিমতী দিদিকে একবার ডেকে আনুক। গল্পটা তো ওকে বাদ দিয়ে হয় না। আনো, ডেকে আনো। হরিমতী আসুক। তারপর বলছি। বলে মাথা নিচু করল এবং চুপ করে গেল শঙ্কর গারুড়ী।
আমি বলে উঠি, ‘আচ্ছা বেশ। আমিই যাচ্ছি তাহলে দিদিকে ডেকে আনতে। কারণ দিদিকে বুঝিয়ে আনতে হবে!’
— ‘আরে না না। একেবারে না। তুমি যেমন আছো থাকো। একেবারে যাবে না বটেশ্বর। বাইরে তুমি কেন যাবে! তবারক যাক। যা বলছি। এ বাড়িতে সাপ ঢুকেছে। তোমার চিন্তা নাই তবা। যাও, দিদিকে ডেকে আনো! যাও হে, যাও!’
বলে তাড়া লাগায় শঙ্কর গারুড়ী। আমরা শঙ্কায় কেঁপে উঠি।
‘সাপ’ শুনে সবচেয়ে ভয় পেল নন্দিনী। যে-সাপ তাকে কামড়াতে পারত, কামড়ায়ানি, সে এবার কিসের জন্য ঢুকল? আর কোন জীবন-আঁধি সৃষ্টি করবে এই আঁধিবিজড়িত (আঁধিই মনসার পরিচয় দিচ্ছে) সাপ? কাকে নিতে ঢুকেছে? আমাকে? বেশ, আমাকেই নে কানি, আয়!
মনে মনে বলে ওঠে নন্দিনী। কিন্তু ওঝার কথায় অন্য ইঙ্গিত। তার সঙ্গে কত আগ্রহ নিয়ে দেখা করতে এসেছে তার বটুদা! আজও এই মানুষটি বিয়ে করেনি। কেন করেনি? ভালো কি বাসে? তার নন্দিনীকে নিয়ে আজ সে কী করতে চাইছে? আর আঁধিবিজড়িত সাপ কি বটুদাকেই অনুসরণ করছে? সাপের দংশনে মৃত্যুর চেয়ে বিপন্ন-করুণ মৃত্যু আর কিসে আছে! আমার কাছে আসাই কি বটুদার কাল হল? এমনিটাই ভাবছে নন্দিনী?
হা মনসা, হা দেবী, আমি চক্রবর্তী-নন্দিনী মা, আমার শিব (বটেশ্বর)-কে রক্ষা করো, হা দেবী জটিলা-কুটিলা! নন্দিনী কিছুটা বিড়বিড় করে ওঠে। এই ভাবে, এমন ভাবনায় কী বিড়বিড় করছে সে?
আমি বলি, ‘ভালোই তো!’
— ‘কী ভালো? প্রায় যেন ধমক দিয়েই ওঠে নন্দিনী।’
এবং এভাবে শাসিয়ে ওঠা ঠিক হয়নি ভেবে নিজেকে সামলে নিতে মুহূর্তে সুর নরম করে নন্দিনী বলে উঠল, ‘কী ভালো বটুদা?’
— ‘মির্জা-মঞ্জিলে এসে ভালোই করেছি নন্দিনী! সাপ একটা আশ্চর্য-অদ্ভুত আধিদৈবিক বাসনা-প্রসূত জীব, একটুখানি সাহিত্যিক ভাষায় বলা যাচ্ছে কথাটা। সাপের সঙ্গে সামনা-সামনি যুদ্ধ করা যায় না। এই জীবটা যখন যায়, দেখে ভাবি, কী খুঁজছে জীবটা? এর সন্ধান অলক্ষ্যগোচর। এর আকৃতি ও প্রকৃতির কোনো মিল নেই অন্য কোনো জীবের সঙ্গে। এ কাকে খুঁজছে, এবং অন্য কাকে শেষ করবে, কেউ জানে না—ও নিজেও জানে না। ও ত্বক দিয়ে শোনে এবং ত্বক দিয়েই ক্ষিপ্ত বেগে ছুটে যায় এবং খোলস ত্যাগ করে বারবার নবজীবন লাভ করে—এর চেয়ে ক্রূর-বিস্ময় খোদা আর কী সৃষ্টি করেছেন! শুনেছি দম বন্ধ করে এ জীব নিরাহারে গর্তের মধ্যে এক-একটা ঋতু পার করে দেয়; এই জীবই কি নন্দিনীকে অদংশনে রক্ষা করেছে, হা শঙ্কর কাকা, কথা সত্য কি-না!’
শঙ্কর গারুড়ী তার বাঁ কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটায় বাঁ হাত সন্তর্পণে ঢুকিয়ে কী যেন হাতড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে, চাকা মতন কী-যেন একটা জিনিস ওই ব্যাগে রয়েছে এবং বড় শঙ্খের মতো কিছু।
শঙ্কর আমার কথা শুনে বলল, ‘সর্প তা-ই দেখে, যা আসলে অলক্ষ, তাই জন্যে এটাই নিয়তি বাবা হে! ত্বক দিয়ে সন্ধান কি কম কথা হা দেবী। “ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিক্ষগাঃ খগাঃ।” এই জিক্ষগ কিন্তু নিষ্ঠুর, এ নির্বিষ না। আমার থলেয় একটি তুরানি সর্প আছে বটেশ্বর; ভারি সুদর্শন, বাউটির মতো সরু আর থাকে গেঁড়ে পাকিয়ে, এটা ছুঁলে মানুষ পচে যায়। আমি এখন সেইটের পুজো করব। যাও তবা, দিদিকে ডেকে আনো। তুমি আর কথা বোলো না বটেশ্বর।’
আমি বললাম, ‘কথাটা তো শেষ করতেই হবে শঙ্কর কাকা। দাঁড়াও তবারক, শুনে যাও। পারলে দিদিকে বলবে, যা এখন বলতে যাচ্ছি। আমার একটা ভাবনা আছে মেয়েদের ব্যাপারে। এটাকে ঋষিবাক্য বলতে পার, যা আমি নিজের করে নিয়ে বেঁচে আছি।’
মোড়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠা তবারক বলল, ‘বলুন বড়ো বাবু, আমি শুনছি।’
বললাম, ‘মেয়েরা হচ্ছে গাভীর মতন পবিত্র; একে কোনো উপায়েই অশুচি করা যায় না। বুঝলে তবা? আর তুমি, কথাটা কি নবাবকে শোনাতে পার নন্দিনী!’ বলে মাথা নিচু করলাম।
— ‘ননা তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, তা নিয়ে আমার কষ্টের সীমা নেই, কিন্তু যাইই ননা করে থাক, তাতে তুমি অপবিত্র হওনি নন্দিনী। কিন্তু এ কথা তোমাকে বলার সুযোগই তো দেয়নি চেংমুড় দেবী। ভাগ্য তোমাকে আমার থেকে লুকিয়ে বোরখার মধ্যে রেখে দিয়েছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, শঙ্কর কাকা, তুরানি সাপে স্বাহা-স্বাহা বলে পুজো দেবে বোধহয়।’ মাথা নিচু করেই কথাগুলো বলে গেলাম।
— ‘সমস্তদুগ্ধা বৃক্ষ সহকারে জিক্ষগার পুজো দেবো, হরিমতী আসুক। যা হোক। জীবিত সর্পের পূজাই তো আসল নাগপঞ্চমী বাবা হে!’ বলল শঙ্কর।
দ্রুত দিদিকে আনতে ছুটে গেল তবারক ফরাজি।
দিদিও পাগলের মতো ছুটে এল। এসে কান্নায় ভেঙে পড়ল। তারপর কাঁদতে কাঁদতে শঙ্করের দুটি হাত জড়িয়ে ধরে বলল, ‘আমার ভাইটিকে বাঁচাও গারুড়ী। ভালো করে পূজা দাও। আমাকে কী করতে হবে বলো।’
কামরু ওঝা ওরফে শঙ্কর গারুড়ী বলল, ‘আগে সাঁঝলতাটিকে দু’ চোখ ভরে দেখো হরিমতী। এই জিনিসে ননাকে মাধবের ডোঙায় চেটে দেয়—দেখো, দেখো! অ্যাই নাও সাপের সরার ঢাকনা খুলে দিচ্ছি। এই যে সাপ যাকে বাংলার লোকে সন্ধ্যার পর সাপ না বলে ভয়ে সংস্কার বশে সন্ধ্যালতা ডাকে, সেটি আসলে সরু-লতিকা তুরানি জীব। পণ্ডিতরা কেউ কেউ বলে, তুরান থেকেই সন্ধ্যালতা ভারতে ঢুকেছিল। গরমের জায়গায় এর বিষ তেজি হয় হরিমতী—এমন সরুলতা ননাকে চেটে দেয়। ভাবো!’
গলার বাউটির মতো এই সাপ ঠাণ্ডা হয়ে গেলে মতন গেড়ে নিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে বলে মনে হলো। কিন্তু প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলেন হরিমতী।
— ‘এই সাপে পুজো দিচ্ছি কেন শঙ্কর?’
ধূপধুনোয় ভরে গেছে ঘর। এবার নাগিন বাঁশি বাজিয়ে নাগকে জাগাবে শঙ্কর। শঙ্কর নিত্য-স্নানের যে-তর্পণ হয়, তার যে মন্ত্রটি সেটি বারংবার আউড়ে নিচ্ছে। সেখানেই তো ‘ক্রূরাঃ সর্পাঃ’ কথাটি আছে। যেখানে গন্ধর্ব, কিন্নর যক্ষ ইত্যাদিকে নাগ বলা হয়েছে; সাপকে এই তিনের থেকে আলাদা করে তার খল-চরিত্রের নিষ্ঠুরতার কথা বলা হয়েছে। ধর্ষকের ধর্ষকাম পুরুষ-প্রবৃত্তি একধরনের সর্প বিশেষ—তাকে ধ্বংস করতে হলে এই সরুলতা দিয়ে ছোঁ দিতে হয় বা চাটাতে হয় তখন অতি কামুক পুরুষ পচে যেতে থাকে—ধর্ষক সাপের মতোই শহরে গ্রামে চলাচল করে—সেই সাপের মাথা ও ফনায় খাজা খিজিরের খড়মের ছাপ আছে। খিজির সাপ (যেমন গহমা খরিস)-কে খড়ম চেপে মেরে দিতে চেয়েছিল, পরে কী মনে করে ছেড়ে দেয়—বোধহয় ভাবে, পুরুষের বীর্যেই তো মহাপুরুষ জন্মে। তুরানি এই সাপে চেটেছিল ননাকে।
নিত্যস্নানের তর্পণ-মন্ত্রটি এ রকম—
‘দেবা যক্ষাস্ততা নাগা গন্ধর্বাপ্সরসোহসুবাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিক্ষগাঃ খাগাঃ
বিদ্যাধরাজলাধারাস্ত থৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহাবাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্মে বতাশ্চ যে
তেষামাপ্যায়নয়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া
দিদির পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে মিনি। ওঝার উচ্চারিত মন্ত্রের গমকে, ধূপধুনা-সাপে, মৃত্যুবোধে এতটুকু শিশুর মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে। ও জেনে গেছে, তার মামুকে সাঁঝলতায় দংশাতে পারে; এই আঁধির মধ্যে তার মামুর মৃত্যু হতে পারে। মৃত্যুর পর সেই মামুকে বাঁচিয়ে তুলবে এমন বেহুলা কি সংসারে আছে?
দিদি আমার চেয়ে বছর দুইয়ের বড়। স্বামী তাকে ছেড়ে গেছে। তারক সিকদার ছিল প্রাইমারি শিক্ষার এসআই (স্কুল পরিদর্শক)। একটি নিতান্ত কমবয়সী রাজকন্যাকে বিয়ে করার মানসে দিদিকে ত্যাগ করে; এখনো খোরপোষ টানে, দিদির বাড়িটাও তারকের করা—দিদিকে দিয়ে চলে গেছে। দিদির অনেকখানি বয়স হলে মিলি জন্মায়। মেয়ে এবং আমিই দিদির সর্বস্ব।
মেঝেয় আসন পেতে সর্পপূজা চলছে।
দিদি উবু হয়ে ওঝার নিতান্ত কাছে ঝুঁকে রয়েছে। তার পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে মিনি। বেশ খানিকটা তফাতে নবাবের খাট। খাটে নবাবের মাথার দিকে প্রান্তঘেঁষে বসে রয়েছে স্থির বসে থাকা নবাবের আড়ালে নন্দিনী, যদিও সেই আড়াল থেকেই ও আমাকে দেখছে। আমি রয়েছি খাটের গা-ঘেঁষে উঁচু মোড়ায়। নবাবের পায়ের দিকে খাটের প্রান্তে তবারক ফের বসেছে এসে। তবা ওঝাকে প্রশ্ন করল, ‘আরবি পানিশমেন্ট দেওয়া হয় ননাকে বাইশি সভা করে, জানো তো কামরু?’
— ‘কেন জানব না বাবা হে! মাধবের ডোঙার মাথাটা নিয়ে, ওটা দামি কাঠের, পানিতে নুন ধরে না অর্থাত্ পানির নুনে নষ্ট হয় না এমন কাঠ দিয়ে তয়রি—সেই মাথাটা নিয়ে ডোঙার নতুন বডিতে জোড়া হয়। তাইতে করে টিকে যায় মাধবের ডোঙা। পুরনো হেড, নতুন বডি।
আট
— ‘তো!’ বলে প্রশ্ন করল তবারক।
ওঝা বলল, ‘আমি যে ডোঙা করে জলে-জলে ঘুরে গায়ে গায়ে বিষ নামাতে যাই, সেটা সুতরাং মাধবেরই ডোঙা। সেই ডোঙার মাথার খোলে তুরানি এই সাপটা ছিল। যখন পাথরের বর্ষণ মাথায় করে পলাবার চেষ্টায় বোবা বিলের কিনারে এসে ছেলের নাম ধরে বাঁচাও মাধব বলে কেঁদেকেটে ডাকলে, অনেক ডাকাডাকির পর এই ডোঙাটা ভেসে এসে কিনারে ঠেকল। এই ঘটনায় পরনকথা জন্মে, মাধব বাপকে বাঁচতে সাহায্য করতে ডোঙা নিয়ে ভেসে এসেছিল।’
— ‘তা হলে সাপটা?’
— ‘মাধব তুরানি সাপের ছদ্মবেশে ডোঙার মধ্যে ছিল। বাপকে চেটে দেয়।’ বলে আগুনে ধূপ ছোড়ে ওঝা।
মিনি নিতান্ত ভয় পেয়ে আমার কোলের কাছে ডুকরে কেঁদে ওঠে, ‘বাঁচাও মামু’ বলে ছুটে আসে। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে বলি, ‘ভয় কি মিনি, আমি তো আছি, আমি মরব না। ঠিক বেঁচে থাকব দেখে নে।’
ওঝা এবার স্মিত হেসে বলল, থাকবে বইকি বটেশ্বর। নন্দিনীর সঙ্গে বিবাহ হলে তুমি বেঁচে থাকবে। প্রত্যেক বাঙালি নারীর মধ্যে একজন করে বেহুলা থাকে কিনা! জানই তো, গহমা খরিস ওই নন্দিনীকে দংশায় নাই। আচ্ছা দেখছি তোমাকে, মনসা গাছ মানে সমস্তদুগ্ধা গাছ মানে সিজ গাছের শেকড় কাঁসার বাটিতে রেখে সেই বাটি সামান্য চালান করে দেখলাম, হা বিষহরি! এ যে তোমার ভাইয়ের দিকেই যাচ্ছে, ভয়ে আর বাটি চালান করিনি হরিমতী। তবে হ্যাঁ এটাও ঠিক, যদি বাটি বেঁকে যায়, যেতে যেতে বাঁক নিয়ে বেঁকে যায়, তবেই রক্ষে!’
শঙ্কাতুরা হরিমতী কান্নামেশা গলায় বলে ওঠেন, ‘যাবে?’
‘দেখা যাক।’ বলে বাটি চালানোর আয়োজন শুরু করে ওঝা।
আশ্চর্য অলৌকিক মনসা-মঙ্গল শুরু হয়।
— ‘ওঁ বিষহরায়ে নমঃ’—এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে কাঁসার বাটি চালনা শুরু করে ওঝা। সেই বাটির মধ্যে একটি সিজমনসার শিকড় রেখেছে কামরু। ধূপচিতে ধূপের গুঁড়ো ফেলে হোম দেওয়ার কায়দায় দশাক্ষর মন্ত্র বলে গেছে শঙ্কর। ‘ওঁ মনসাদেব্যৈ নমঃ স্বাহা’ বলে গেছে সে। তিলজলপূর্ণ তামার বাটি কাছে রেখে ‘ওঁ তদবিষ্ণু’—এই মন্ত্রে বিষ্ণুকে স্মরণ করেছে শঙ্কর।—এই সব ব্যবস্থা ওর ব্যাগের মধ্যেই থাকে। কিন্তু এই বাটি চালান এক আশ্চর্য তুক।
তাতেই অতি আশ্চর্য কাজ হলো।
বাটিটা আমার পায়ের দিকে মসৃণ মেঝেয় এগিয়ে এসে অন্য একদিকে ঘুরে গেল।
বার তিন চেষ্টা করল শঙ্কর।
তিনবারই একই দৃশ্য রচনা করল বাটিটা।
দিদির মুখটা হাসিতে আনন্দে ভরে গেল।
— ‘ভাইটা আমার বেঁচে গেল শঙ্কর!’ বলে উঠল দিদি।
নন্দিনীর আনন্দের সীমা নেই। সে মিনিকে কাছে পাবার জন্য পাগলের মতো আকুলতায় দু’হাত সামনে বাড়িয়ে দেয়। মিনি অতি তত্পরতায় আমাকে ছেড়ে খাটে বুক বেয়ে উঠে পড়ে হামা দিয়ে নবাবের পাশ দিয়ে চলে যায় নন্দিনীর কাছে।
শঙ্কর তখন রহস্য ভেদ করবার জন্য বলে, ‘কার গুণে, কার কপালে তোমার ভাই এযাত্রা বেঁচে গেল শুনবে হরিমতী?’
— ‘হ্যাঁ নিশ্চয়ই। বলো, বলো!’
— ‘যা-ই মনে করো হরিমতী! ওই যে খাটে বসে আছে নন্দিনী, দেখো দেখো, ওরই গুণে তোমার ভাই বেঁচে গেল। ভাইকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে চাও, ওই হায়া মির্জার সঙ্গে বিবাহ দাও!’
ওঝার নাটুকে গলা নবাবের হয়তো কানে গিয়ে থাকবে, নবাব বলে উঠলেন, ‘আমি আজব মির্জা। আমি নবাব। এটি আমার নন্দিনী হায়া মির্জা—বটেশ্বর একে নিকাহ্ করুক, এই খোয়ায়েশ নিয়া নেতার ঘাটে এসেছি হরিমতী। না কোরো না। শঙ্কর, গান দাও ভাই!’
নন্দিনীকে ছবির কিশোরী নন্দিনী অপেক্ষা অধিক সুন্দর দেখাচ্ছে। বিস্ময়াবিস্ট হয়ে সেই রূপ প্রায় অপলক কিছুক্ষণ দেখতে থাকে হরিমতী। সহসা তার মুখ থেকে বার হয়, ‘এ ঠিক দেবী সরস্বতী শঙ্কর!’
— ‘রূপ একটা মস্ত গুণ হরিমতী। আসলে বিষহরি তো সরস্বতীও বটে। আমি প্রণাম জানাচ্ছি তোমার এই সরস্বতীকে হরিমতী। একে ঘরে রাখো, তোমার ভাই বাঁচবে। এদের বিয়ে দাও। বাংলার প্রত্যেক কুমারীর মধ্যে একজন করে বেহুলা থাকে। আর আমাদের গল্পে বেহুলাকেই সাপে কাটে হরিমতী। পুরুষের ধর্ষণ-প্রবৃত্তি গহমা খরিস। তার বিষদাঁত ভেঙে দিলে আধুনিক মনসা মঙ্গল শুরু হয়। তাই কি-না ভেবে দেখো। যা হোক, কী বলছ তুমি?’
বলে দিদির মুখের দিকে চেয়ে রইল ওঝা।
দিদি তবারকের চোখে চোখ রেখে বলল, ‘হায়া মির্জা তাহলে ঘরে আসুক তবারক, ব্যবস্থা করো।’
মিনিকে বুকের মধ্যে নিবিড় করে চেপে ধরল নন্দিনী। হঠাত্ তবারক শঙ্কর ওঝাকে প্রশ্ন করে, ‘তুমি কিন্তু একটা জায়গায় খটকা রাখলে কামরু?’
— ‘কিসের খটকা বাবা হে?’
— ‘তুরানি সাপে চেটে দেয় ননাকে। সে পচে গলে গেছে?’
— ‘হ্যাঁ গেছে।’
— ‘তাহলে সে তৃতীয় দফা লগড়াজলি এল কী করে? তার বুড়া মাকে দেখতে এসেছে, আমার সোর্স বলছে।’
— ‘ওটা একটা অলীক পরনকথা তবারক। এই বর্ষায় সাপের উপদ্রব বাড়লে গল্পটা লোকে ছড়াতে থাকে। কেউ কেউ তাকে দেখতেও পায়। কিন্তু ডোঙার খোলে তুরানি সাপের ছদ্মবেশে মাধব অপেক্ষা করছিল। ধর্ষক বাপকে কাটবে বলে। এটাই বিষহরির অন্য গল্প তবারক। সন্তান বাপকে দংশন করে, হায় মা জাঙ্গুলী।’ বলে ধ্যানের ভঙ্গিমায় দু’চোখ বন্ধ করল ওঝা।
আঁধি শেষ হয়ে শরতের নতুন আলো ফুটল। নদীর কোলের ফরাজি বাগানে পাখিরা নতুন করে গান ধরল। হরিমতী আর নবাবে মিলে আমাদের নন্দিনী আর আমার বিয়ে দিলেন। তবা আর শঙ্কর কত আনন্দ যে করল তার ইয়ত্তা হয় না। মিনির সুখ আর ধরে না।
নবাব যে এবার বিদায় নেবেন তা আমরা ভাবিনি।
তবারককে ডাকলেন নবাব।
তারপর বললেন, ‘তুমি আরবি পড়তে পার?’
তবা বলল, ‘পারি বইকি নবাব।’
— ‘পড়ো। এই চিঠিতে নৈনিহালের খবর আছে। ভেবেছিলাম, হায়ার বিয়ে দেওয়ার পর এখানে থেকে মরব। কিন্তু হলো আর কই! নৈনিহাল পাকিস্তান থেকে ইরান চলে যায়। সিরাজে আমাদের বংশের লোক থাকে। ঘরবাড়ি ব্যবসা সব আছে। ছেলে সেখানে গেল। তারপর কী হলো, দেখো।’
চিঠিটা পড়ল তবারক। তারপর কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেল। ওর ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে থাকল।
নবাব বললেন, ‘এই অবস্থায় আমি কী করি বলো! আমাকে সিরাজ যেতে হবে তবারক। তারপর আমি খুঁজব, যদ্দিন না পাই। কী বলো?’
‘জি’ বলে মাথা নিচু করল তবারক ফরাজি।
ওমরকে খবর দেওয়া হয়েছিল। সে এসে পৌঁছাল। আজবের নৌকো আজবকে নিয়ে ছেড়ে গেল। সেই চলে যাওয়া দৃশ্যের দিকে চেয়ে রইলাম আমরা। নৌকা যাচ্ছে দেখি, গাবগাছটায় নতুন করে মধুচক্র দেখা দিয়েছে। আকাশে মেঘের রথ স্থির হয়ে সোনায় আলোর ঝলমল করছে। আমাদের আনন্দের শেষ নেই।
প্রশ্ন করি, ‘চিঠিতে কী ছিল তবারক?’
তবারক বলল, ‘নৈনিহাল মরুভূমির বুকে হারিয়ে গেছে বড়ো বাবু! ১০৩ বছরের বুড়া বাপ সেই সন্তান দিকহারা মরুভূমিতে খুঁজে ফিরবে।
— ‘যদ্দিন না নবাবের মৃত্যু, তদ্দিন তিনি ছেলেকে খুঁজবেন—এ কেমন আলিফ লায়লা!’