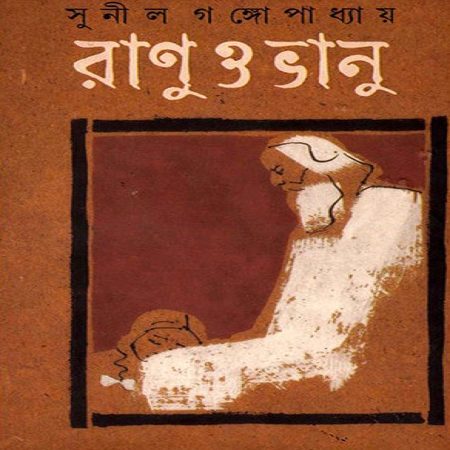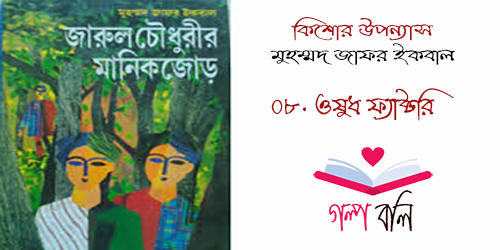প্রিয় রবিবাবু :
আমি আপনার গল্পগুচ্ছের সব গল্পগুলো পড়েছি, আর বুঝতে পেরেছি। কেবল ক্ষুধিত পাষাণটা বুঝতে পারিনি। আচ্ছা সেই বুড়োটা যে ইরানি বাদির কথা বলছিল, সেই বাঁদির গল্পটা বলল না কেন? শুনতে ভারী ইচ্ছে করে। আপনি লিখে দেবেন। হ্যাঁ।
আচ্ছা জয় পরাজয় গল্পটার শেষে শেখরের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হল। না? কিন্তু আমার দিদিরা বলে শেখর মরে গেল। আপনি লিখে দেবেন যে, শেখর বেঁচে গেল আর রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হল। কেমন? সত্যি যদি শেখর মরে গিয়ে থাকে, তবে আমার বড় দুঃখ হবে।
আমার আপনাকে দেখতে খু উ উ উ উ উ উব ইচ্ছে করে। একবার নিশ্চয় আমাদের বাড়িতে আসবেন। নিশ্চয় আসবেন কিন্তু, না এলে আপনার সঙ্গে আড়ি। আপনি যদি আসেন তবে আপনাকে আমাদের শোবার ঘরে শুতে দেব। আমাদের পুতুলও দেখাব।
ইতি রাণু
সকালবেলার ডাকে অনেকগুলি চিঠি ও পত্রপত্রিকা এসেছে। টাটকা টাটকা চিঠিগুলো পড়ে ফেলাই কবির অভ্যেস। এক একটা চিঠির উত্তরও লিখতে বসেন সঙ্গে সঙ্গে।
এই চিঠিটি পড়ে কবি কিছুক্ষণ বিস্মিত ভাবে তাকিয়ে রইলেন জানলার দিকে।
তিনতলার এ ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় অনেকখানি আকাশ। কিছু চিন্তা করার সময় আকাশের দিকে কবির চোখ চলে যায়। চার দেয়ালের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ পরিসরে ছুটে যায় মন, যেন শূন্যে ফুটে ওঠে অনেক লেখা বা রেখাচিত্র।
আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা।
কাল সারারাত শুধু যে খুব গরম ছিল তাই-ইনয়, একেবারে নিবাত নিষ্কম্প, প্রকৃতির সব কিছুই স্তব্ধ। গরমে কবির একটুও কষ্ট হয় না, গরম টেরই পান না, পিঠ বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরে গেলেও অস্বস্তি বোধ করেন না।
এই শ্রাবণ মাসে বেশি গুমোট হলেই বোঝা যায়, বৃষ্টি আসবে। ঠিকই ঘনিয়েছে মেঘ। কবি বৃষ্টি এত ভালবাসেন যে তৃষ্ণার্ত চাতকের মতন ঘন ঘন তাকান মেঘের দিকে। সব কটি ঋতুর মধ্যে বর্ষাই তার সবচেয়ে প্রিয়।
চিঠিখানি তিনি দু’বার পড়লেন। পত্রলেখিকা পদবি দেননি, শুধু লিখেছেন নাম। ঠিকানা আছে অবশ্য, বেনারসের।
এই রাণু কে? কত বয়েস? চিঠির ভাষায় অল্প বয়েসিনীই মনে হয়, কিন্তু গম্ভীর ভাবে সমোধন করেছে, ‘প্রিয় রবিবাবু’! অগ্রে বা অন্তে শ্রদ্ধা বা প্রণাম জানাবার কোনও বালাই নেই। আপনাকে আমাদের শোবার ঘরে শুতে দেব’ এই অংশটি পড়ে কবির মুখের দাড়ি-গোঁফের আড়াল থেকে ঝলসে উঠল কৌতুক হাস্য। এটা বেশি খাতির? এখনও পর্যন্ত তিনি কারওর বৈঠকখানায় কিংবা বারান্দায় শোওয়ার আমন্ত্রণ পাননি!
রাণু? এই নামে কবির নিজেরই এক কন্যাসন্তান ছিল। সে আর নেই। বুক ভরা অভিমান নিয়ে সে চলে গেছে পৃথিবী ছেড়ে।
গুরু গুরু মেঘগর্জন শুরু হয়েছে। যেন ডঙ্কা বাজিয়ে রথে চেপে আসছে বর্ষা। হঠাৎ বাতাস হয়েছে প্রবল। কবি এসে দাঁড়ালেন ঝুল বারান্দায়। প্রথম বর্ষণকে বরণ করলেন মাথা পেতে।
তারপরই ডাক এল নীচ থেকে।
চিঠিগুলির উত্তর আর এখন লেখা হল না।
শান্তিনিকেতন থেকে গুরুতর খবর এসেছে। চারজন ছাত্র খুবই অসুস্থ। ইনফ্লুয়েঞ্জা! অতি পাজি রোগ। এই মহাযুদ্ধের সময় থেকেই শুরু হয়েছে বলে কবি এই অসুখের নাম দিয়েছেন যুদ্ধ জ্বর। যুদ্ধে যেমন সৈন্যরা অনেকে আহত, অনেকে নিহত হয়, সেই রকম এই রোগেও অনেকে ভুগে ভুগে কাহিল হচ্ছে, কেউ কেউ মারাও যাচ্ছে।
শান্তিনিকেতনে পাঠাতে হবে ওষুধপত্র ও একজন ভাল চিকিৎসক। এখন আর তিনি কবি নন, তিনি গুরুদেব, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সব ভার তার ওপর। তার ওপর ভরসা করেই অভিভাবকরা ছেলেদের পাঠান।
ওখানকার ছাত্রদের আবাস ভবনটির ছাদ থেকে বর্ষার জল পড়ছে, মেরামত করা দরকার। একজন কলা-শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। টাকা?
পর পর কয়েকটি দিন গেল নানা রকম ব্যস্ততায়। তারপর তিনি নিজেই জ্বরে পড়লেন। এখন জ্বর হলেই ভয়ের কথা। প্রথম দিন তিনি জ্বর গায়ে নিয়েই গেলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে। ওঁর ছেলে মলু শান্তিনিকেতনের ছাত্র। বিকেলবেলা কালিদাস আর সুকুমার এল নতুন গান শিখে নিতে। জ্বরের কথা কারওকে বললেন না, গান গাইবার সময় তিনি নিজেই ভুলে গেলেন।
কালিদাস ইতিহাসের পণ্ডিত, আর সুকুমার সন্দেশ পত্রিকায় কবিতা-গল্প-নাটক লিখে শুধু ছেলেদের নয়, বড়দেরও মাতিয়ে রেখেছে। এই দুজনেরই গানে খুব উৎসাহ।
সুকুমার সব সময়েই যেন কৌতুকে ভরপুর, সে দু হাত ছড়িয়ে মাথা নেড়ে গান গায়। তুলনায় কালিদাস একটু গভীর প্রকৃতির হলেও সুকুমারের সব কিছুতে সে তাল দিয়ে যায়।
‘এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না/ মন উড়েছে উড়ুক-না রে মেলে দিয়ে গানের পাখনা…’ এই গানটি সুকুমারের খুব প্রিয়। এর অন্তরাটা এখনও গলায় ঠিক ওঠেনি। টধরণী আজ মেলেছে তার হৃদয় খানি।…’
কালিদাস কবির কাছে শুনতে চায় নতুন গান। কবি খাতার পাতা ওল্টাতে লাগলেন। তাঁর সদ্য রচিত গানটি গম্ভীর ধরনের, দেশাত্মবোধক। ‘দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী/আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি…’। গাইতে গাইতে কবির কণ্ঠস্বর এক সময় গম্ভীর ভাবে গমগম করতে লাগল। ‘প্রেরণ করা ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে—’
সুকুমার আর কালিদাস সে গান শুনতে শুনতে বুঝতেই পারল না যে কবির শরীর সুস্থ নেই।
পরদিন টের পেয়ে গেল প্রতিমা। ব্যস্ত হয়ে গেল রথী। এ রকম জ্বর কিছুতেই অবহেলা করা চলে না। বিধান রায় নামে একজন তরুণ ডাক্তার বেশ নাম করেছে, ডাকা হল তাকে। এরই মধ্যে তাঁর ভিজিট ষোলো টাকা এবং গাড়ি ভাড়া দিতে হয়।
চিকিৎসকটি নির্দেশ দিয়ে গেলেন সম্পূর্ণ বিশ্রামের।
বিশ্রাম মানে শুয়ে থাকা। কিন্তু শুয়ে শুয়েও তো লেখা যায়। সঙ্গীত বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য বারবার তাড়া দিচ্ছে প্রমথ। সে প্রবন্ধটি লিখতে লিখতে কবির মনে পড়ল অনেকগুলি চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি।
তিনি সব চিঠিরই উত্তর দেন। কেউ একজন কষ্ট করে চিঠি লিখল, অথচ উত্তর পেল না, এটা তার মতে পত্র প্রাপকের অসভ্যতা।
রাণু নামী মেয়েটিকেও তিনি চিঠি লিখে দিলেন। তার পরিচয় ও বয়েস বুঝতে না পেরে খানিকটা আলগা আলগা ভাবে।
মন টানছে শান্তিনিকেতন। জ্বরের জন্য যাওয়া হচ্ছে না। বর্ষার শান্তিনিকেতন অপরূপ।
নিজের অসুখের চেয়েও চারজন ছাত্রের অসুস্থতার জন্য তার উদ্বেগ বেশি। ডাক্তার পাঠানো হয়েছে। কয়েকদিন পর ছাত্রদের অবস্থার উন্নতির খবর পেয়ে কবিও সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন।
শরীর কাহিল, কিন্তু জ্বর ছেড়েছে। কবির ইচ্ছে করল, আর একবার বৃষ্টিতে ভিজতে। মনে এসে গেল একটা নতুন গান : ব্যাকুল বকুলের ফুলে ভ্রমর মরে পথ ভুলে। আকাশে কী গোপন বাণী বাতাসে করে কানাকানি, বনের অঞ্চলখানি পুলকে ওঠে দুলে দুলে…।
সে গানের সুর গুনগুনোতে তালটাও নতুন রকমের হয়ে গেল।
অসুস্থতা ছাড়াও সুখ বিঘ্নিত হবার অনেক রকম কারণ থাকে। কবি জড়িয়ে পড়লেন রাজনীতির ঝঞ্ঝাটে।
সরকার নতুন ভাবে শুরু করেছে দমননীতি। বাল গঙ্গাধর তিলকের পত্রিকা বন্ধ করতে বলা হয়েছে। অ্যানি বেসান্তের ওপর জারি করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা, তিনি বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে প্রবেশ করতে পারবেন না। শুধু তাই নয়, অ্যানি বেসান্তকে অন্তরীন করা হল মাদ্রাজে।
তার প্রতিবাদে সারা দেশ উত্তাল। সরকারকে উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য মাদ্রাজের তেজস্বী প্রাক্তন বিচারক স্যার সুব্রহ্মণ্যম আইয়ার ইংরেজ শাসকদের দেওয়া তার স্যার ও দেওয়ান বাহাদুর খেতাব বর্জন করলেন এবং প্রস্তাব দিলেন, এবারের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে অ্যানি বেসান্তকেই সভাপতি করা হোক!
বিভিন্ন রাজ্য কংগ্রেসের কমিটি এ প্রস্তাব মেনে নিল সাগ্রহে, শুধু গণ্ডগোল বাঁধল বাংলায়। বাংলার কংগ্রেসে দলাদলি তো লেগেই আছে, অ্যানি বেসান্তকে সভাপতি করার প্রসঙ্গে মতভেদ হল তীব্র, দুই পক্ষের তর্কাতর্কি ও হুড়োহুড়িতে পণ্ড হয়ে যায় সভা।
সুরেন বাঁড়ুজ্যের মতন কংগ্রেসের এক শ্রেণীর নরমপন্থী নেতাদের ধারণা, এই বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজরা ভারত থেকে প্রচুর সৈন্য ও সম্পদ নিতে বাধ্য হয়েছে, তার বিনিময়ে যুদ্ধশেষে সরকার ভারতে স্বায়ত্তশাসন দিতে বাধ্য হবে। ভারত সচিব তো সম্প্রতি বিলেতের পার্লামেন্টে সেই আশ্বাসই দিয়েছেন। সুতরাং এখন সরকারকে না চটিয়ে সহযোগিতার পথ নেওয়াই ভাল। অপরপক্ষে চিত্তরঞ্জন দাশের মতন চরমপন্থী নেতাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সরকার মোটেই অত সহজে স্বায়ত্তশাসন দেবে না। ভারত সচিবের ওই আশ্বাস নিছক ধাপ্পা বা স্তোকবাক্য।
রাজ্য কংগ্রেসের ভোটাভুটি বানচাল হয়ে যাচ্ছে দেখে চরমপন্থীরা ঠিক করলেন, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদে স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মনোনীত করা হোক, তা হলে সাধারণ সদস্যরা তার সমর্থনে ভোট দেবে। অ্যানি বেসান্তকে জাতীয় অধিবেশনের সভাপতি করার প্রস্তাবও গ্রহণ করা সহজ হবে। এক সকালে দল বেঁধে চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, ফজলুল হক ও আরও অনেকে দেখা করতে এলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে।
রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা করেন অ্যানি বেসান্তকে। এই মহীয়সী ইংরেজ রমণী ভারতে ইংরেজ সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। তাকে সমর্থন করা অবশ্যই উচিত। সরকার তাকে অন্তরীন করে অপমান করতে চাইছে, এখনই তো ভারতবাসীর কর্তব্য কংগ্রেস সভাপতি পদে তাকে বরণ করে সম্মান জানানো।
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনও প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে রাজনীতির সঙ্গে জড়াননি। সেই প্রায় এক যুগ আগে, বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের সময় তিনি রাস্তায় নেমে মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন, সেটা ঠিক রাজনীতি নয়, নেমেছিলেন প্রাণের টানে, তারপর রাজনৈতিক নেতারা এসে হম্বিতম্বি শুরু করতেই সরে এসেছিলেন তিনি। একজন কবির পক্ষে রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকাই তো ভাল।
কিন্তু এরকম সঙ্কটের সময়, তার নাম ব্যবহার করলে যদি একটা মহৎ কাজ হয়, তখনও কি প্রত্যাখ্যান করা যায়? কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি রাজি হয়ে গেলেন এ প্রস্তাবে, তার সম্মতিপত্র ছাপা হল প্রত্যেক সংবাদপত্রে।
অমনি গালাগালিও শুরু হয়ে গেল। নরমপন্থীদের হাতে অনেক কাগজ। তারা তাকে আখ্যা দিল, হঠকারী, অব্যবস্থিত চিত্ত। নীতিহীন কিছু রাজনৈতিক নেতার পাল্লায় পড়ে শেষ বয়েসে কবি অধঃপাতের দিকে যাচ্ছেন। কবিতা লেখা ছেড়ে এখন তার ক্ষমতা দখলের লোভ হয়েছে? অথচ রাজনীতিতে তিনি একেবারেই অনভিজ্ঞ!
চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিন পাল প্রমুখ কয়েকজন অন্য সময়ে রবীন্দ্রনাথের ঘোর বিরুদ্ধপন্থী, কোনও সুযোগ পেলেই তাঁর লেখার অপব্যাখ্যা করে গালাগালি দিতে ছাড়েন না। এখন রবীন্দ্রনাথ তাদের সঙ্গেই হাত মিলিয়েছেন বলে অন্যরা বিদ্রুপ করতেই বা ছাড়বে কেন?
কিন্তু তিনি ওঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছেন কি ক্ষমতার লোভে? এর মধ্যেই স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে পরে আর কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও সংস্রব রাখবেন না। রাজনীতিতে যাবেনই না কোনও পক্ষে।
ওই সব নিন্দা কটুক্তিগুলি যেন এক একটি ধারালো তির, বড় লাগে, বড় জ্বালা হয়। কবি বেশিক্ষণ সহ্যই করতে পারেন না। এক এক সময় ভাবেন, ওসব পত্র পত্রিকা পড়বেনই না। তবু কেউ না কেউ ঠিক সামনে এনে দেয়, বিশেষ বিশেষ খারাপ জায়গাগুলি দাগিয়ে রাখে। কখনও ভাবেন, ওসব তুচ্ছ মনে করবেন, অগ্রাহ্য করবেন। তবু পারা যায় না। কণ্টক যত ক্ষুদ্রই হোক, তারও বিদ্ধ করার ক্ষমতা থাকে।
এ রকম সময়ে মনে কবিতা আসে না, গান আসে না।
কোথাও পালাতে ইচ্ছে করে।
অথচ পালাবারও উপায় নেই, অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব। জমিদারির আয় খুব কমে গেছে। পর পর কয়েক বছর খরার জন্য শিলাইদহের প্রজারা খাজনা দিতে পারছে না ঠিক মতন। প্রমথ চৌধুরীকে দুশো টাকা মাইনেয় জমিদারির কাজ দেখাশুনো করার জন্য ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়েছে, সেও সুবিধে করতে পারছে না বিশেষ।
শিলাইদহে একবার নিজের যাওয়া উচিত, তার সময় নেই।
এরকম অস্থিরতা ও ব্যস্ততার মধ্যেও এক ঝলক স্নিগ্ধ বাতাসের মতন বেনারস থেকে এল আর একটি চিঠি।
প্রিয় রবিবাবু :
আপনি এতদিন আমাকে চিঠি দেননি বলে খুব রাগ হয়েছিল, কিন্তু আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। আমার ভাল নাম কী জানেন? প্রীতি। বেশ সুন্দর নাম না? ইস্কুলে সবাই আমাকে প্রীতি বলে ডাকে। কিন্তু আপনি আমাকে রাণু, রাণু বলেই ডাকবেন। আমার ও নামটা সুন্দর লাগে কি না তাই বলছি। আমার আরও নাম আছে, শুনবেন? রানি, রাজা, বাবা। সব নামগুলোই বেশ। না? আপনি যে কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম বলে একটা সুন্দর লেকচার দিয়েছিলেন না, সেটা ভারতী আর প্রবাসীতে বেরিয়েছিল। মা, বাবজা, বাবু, আশারা সেটা পড়ে বললেন যে খুব সুন্দর হয়েছে। আমিও তাই পড়তে গেলাম। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। বোধহয় সেটা খুব শক্ত। কিছুদিন আগে আমার খুব অসুখ করেছিল। এখন ভাল আছি। আপনি নিশ্চয় একদিন আমাদের বাড়ি আসবেন। আমরা এ বাড়ি ছেড়ে যাব না। এ বাড়ি আমাদের নিজের বাড়ি। ভাড়ার বাড়ি নয়। আপনি আসবার সময় আমাদের জানাবেন। আমি ইস্কুলের ছুটি নিয়ে আপনাকে ইস্টিশানে আনতে যাব। এ চিঠির উত্তর শিগগির দেবেন যেন, হারিয়ে ফেলবেন যেন। আমি কেমন সুন্দর ফুল আঁকা কাগজে চিঠি লিখেছি।
রাণু
আমাদের বাড়ির ঠিকানা আবার লিখে দিচ্ছি।
235 August Kund
Benares City
আপনি আর গল্প লেখেন না কেন?
কবি চিঠিখানা পড়ার পর উলটেপালটে দেখলেন। গোটা গোটা স্পষ্ট হাতের লেখা, বানান ভুল নেই। ভাষা এমন, যেন মুখের ভাষা, লেখা নয়, কথা বলছে সামনাসামনি। এবারেও সম্বোধনে শুধু গম্ভীরভাবে ‘প্রিয় রবিবাবু’, শ্রদ্ধা-ভক্তি জানাবার কোনও পাট নেই, শেষে শুধু নাম, যেন সমবয়েসী।
কে এই মেয়েটি?
ঠিকানাটা দেখে কবির খটকা লাগল।
অগস্ত্য কুণ্ড? চেনা চেনা লাগছে। কাশীতে একবার অগস্ত্য কুণ্ডের একটা বাড়িতে গিয়েছিলেন না?
হ্যাঁ। মনে পড়ল, সংস্কৃতের অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারীর বাড়ি। সে বাড়ির কেউ? ফণিভূষণের স্ত্রীর নাম সরযূবালা, সে এক সময় কয়েকখানা চিঠি লিখেছিল, সে চিঠি অন্য রকম। এ মেয়েটি ইস্কুলে পড়ার কথা লিখেছে।
ফণিভূষণের বেশ কয়েকটি ছেলে-মেয়ে। তার মধ্যে একজনের কথাই একটু একটু মনে আছে। প্রথমে অদ্ভুত লেগেছিল। মেয়েটির সাজসজ্জা একেবারে ছেলেদের মতন। তাকে ডাকাও হয় নন্দদুলাল নামে। পরে জেনেছিলেন, ওঁদের পরপর দুটি পুত্রসন্তান বাঁচেনি, তাই তৃতীয় সন্তানটি মেয়ে হলেও তাকে ছেলে সাজিয়ে রাখা হয়। ওর আসল নাম আশা। শুনেছিলেন, সে মেয়েটি পড়াশুনোয় খুব ভাল, উপনিষদ থেকে নির্ভুল মুখস্থ বলে।
রাণু বা প্রীতি সেই আশারই পরের বোন? আশার বয়েসই এখন বড় জোর তেরো-চোদ্দো হবে, তা হলে এর বয়েস কত? কোন ক্লাসে পড়ে, তাও লেখেনি। এর বয়েস এগারো বাবোর বেশি হতেই পারে না! এর মধ্যেই সে তার এত লেখা পড়ে ফেলেছে? এমনকী প্রবন্ধ পড়ারও চেষ্টা করে?
আপনি আর গল্প লেখেন না কেন?
হ্যাঁ, অনেকদিন গল্প মাথায় আসেনি।
কবি ভাবলেন, আমি মানুষটি খেজুর গাছের মতন। কেউ খোঁচা না দিলে রস বেরোয় না। কেউ তাড়া না দিলে মাথায় আসে না নতুন লেখা। এখন শুধু প্রবন্ধ লেখার তাগিদ। এ মেয়েটির জন্য একটি গল্প লিখতে হবে।
রাণুর পরের চিঠিটি পেয়ে কবি একা একা হাসলেন অনেকক্ষণ।
এই সাতান্ন বছরের জীবনে চিঠি তিনি কম পাননি, নিজেও লিখেছেন কয়েক সহস্র, কিন্তু এমন ছেলেমানুষি ভরা নির্মল রসের চিঠি যেন আগে কখনও উপভোগ করেননি।
সে লিখেছে : আমি এতদিন চিঠি দিইনি বলে রাগ করবেন না। আমার খুব অসুখ হয়েছিল। কিন্তু এখন ভাল আছি। লক্ষ্মীটি রাগ করবেন না। আজকে থেকে আমাদের পুজোর ছুটি শুরু হয়েছে। 31st October-এ খুলবে। আচ্ছা, আপনার চিঠি লেখা ছাড়া আর কী কাজ! আর কই গল্পও লেখেন না। ইস্কুলেও যান না। আমার আপনার চাইতে ঢের বেশি কাজ। সকালে নটা পর্যন্ত মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ি। বিকেলে চারটে পর্যন্ত ইস্কুলে থাকি। ইস্কুল থেকে এসে এক পণ্ডিতজীর কাছে হিন্দী পড়ি। আর রাত্রে লেখা, টাস্ক করি। আপনাকে দেখে বিশ্রী বলব না। ছবিতে তো আপনাকে সুন্দর করে আঁকে। আপনি নিশ্চয় ছবির চেয়ে বেশি সুন্দর। আমার বেশ একটি সুন্দর বন্ধু। না? আপনার বোধহয় কোনও সুন্দর বন্ধু নেই, আপনাকে দেখে আমার খুব ভাল লাগবে। আপনাকে এসে কিন্তু আমাদের বাড়িতে থাকতে হবে। আর কোথাও থাকতে পাবেন না। আচ্ছা, আপনি পদ্মার উপর নদীতে নৌকোয় থাকতেন না নদীর ধারে বাড়িতে থাকতেন। আমার সেখানে যেতে ইচ্ছে করে…
মেয়েটি বার বার তাকে দেখতে চায় বলে কবি লিখেছিলেন, আমায় দেখলে তুমি ভয় পেয়ে যাবে, আমার দাড়ি-গোঁফওয়ালা ভয়ংকর চেহারা, আমার অনেক বয়েস। সাতান্ন।
তার উত্তরে রাণু লিখেছে, আপনার মোটেই অত বয়েস নয়। কবিদের আবার বয়েস বাড়ে নাকি?
আপনার বয়েস সাতাশ। আমার কাছে আপনি তাই। ওর থেকে আর আপনার বয়েস বাড়বে না।
শান্তিনিকেতনে বেশি দিন থাকা হল না। ফিরতে হল অনেক কাজ অসমাপ্ত রেখে। বেলার অসুখ বেড়েছে।
বেলার কথা ভাবলেই কবির মন বিষণ্ণ হয়ে যায়। শুধু তার অসুখের জন্যই নয়। বেলাকে ক্ষয় রোগে ধরেছে। তাকে বাঁচানো যাবে না, এ রোগের চিকিৎসা নেই। কিন্তু শেষের দিনগুলিতে তার শ্বশুরবাড়ির পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কটা বিষিয়ে গেল!
বেলা, মাধুরীলতা, কবির সবচেয়ে প্রিয় সন্তান। যেমন তার রূপ, তেমনই তার হৃদয়ের সৌন্দর্য। কবি নিজে বেলাকে নতুন নতুন বই পড়িয়েছেন, সাহিত্য রচনা করতে শিখিয়েছেন। কত সাধ করে বেলার বিয়ে দিয়েছেন তার এককালের প্রিয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর সুযোগ্য পুত্র শরৎকুমারের সঙ্গে।
ভুল হয়েছিল। খুবই ভুল হয়েছিল। কন্যাদের বিবাহ ব্যাপারে কবি বার বার অবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। তখন ঝোঁক চেপেছিল, আর একটি কবির পরিবারের সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপন করবেন। বেলা নিছক গৃহবধূ হবে না, সে পরিবারে সাহিত্যের আবহাওয়ায় তার সৃষ্টি প্রতিভা বিকশিত হবে।
কোথায় সাহিত্যের আবহাওয়া? শরৎকুমার কাব্যকলার ধার ধারে না। বিবাহের প্রস্তাব তোলার পর যখন পাত্রপক্ষ থেকে কুড়ি হাজার টাকা পণ চাওয়া হয়, তখন কবি প্রথম ধাক্কা পেয়েছিলেন। তবু চৈতন্যোদয় হয়নি, ঠাকুর পরিবার পণপ্রথার ঘোর বিরোধী, তবু তিনি প্রকারান্তরে সেই দাবি মেনে নিলেন। বেলার সুখের অলীক কল্পনায় কিছুটা মূল্যবোধ বিসর্জন দিতেও রাজি ছিলেন কবি।
সেই শরৎকুমার এখন শ্বশুরকে গ্রাহ্যই করে না। টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে সিগারেট ফোঁকে, কবিকে দেখলেও পা নামায় না, কথা বলে না, মুখ ফিরিয়ে থাকে অন্যদিকে।
কোন অভিমানে বেলারও ভাবান্তর হয়েছে কে জানে, সে এখন রথী বা প্রতিমার সঙ্গেও দেখা করতে চায় না। তার অসুখের অবস্থায় কোনও রকম খবরাখবরই দেওয়া হয় না জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। কবি তবু নিজে নিয়মিত খবর নেন, নিজে দেখা করতে যান।
পাঁচ বছর আগে সারা এশিয়া মহাদেশ থেকে যিনি প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, সারা বিশ্ব থেকে যার আমন্ত্রণ আসে, কত মানুষ যাঁর দেখা পেলে ধন্য হয়, সেই কবিকে তাঁর কন্যার শ্বশুরবাড়ির দরজায় উপস্থিত হলেই সহ্য করতে হয় কত রকম অপমান। তবু কবি তাঁর প্রিয়তমা কন্যার শেষ সময়ে দূরে থাকতে পারেন না, বারবার ছুটে ছুটে আসেন।
কবিকে ঠিক বাধা দেওয়া হয় না। সে বাড়ির কেউ অভ্যর্থনাও জানায় না তাঁকে। সবাই যেন সরে যায় আড়ালে। বৈঠকখানায় শরকুমারকে দেখতে পান, সে উত্তর দেবে না জেনেও কবি মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, শরৎ ভাল আছ?
সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান দোতলায়। মেয়ের নোগশয্যার পাশে গিয়ে বসেন।
রূপ ঝরে গেছে মাধুরীলতার। দু চোখে আলো নেই। এককালের মাখনের মতন মসৃণ ত্বক এখন খড়ি-ওঠা। কার হাড় প্রকট। ঢলঢলে হয়ে গেছে সেমিজ, মুখখানি ছাইবর্ণ।
কবি প্রতিবারই এক গুচ্ছ টাটকা ফুল ও নানা ধরনের আতর নিয়ে আসেন। বিছানার পাশে ফুল নামিয়ে রেখে তিনি জিজ্ঞেস করেন, আজও জ্বর বেশি নাকি রে, বেলি?
বেলা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।
কিশোরী বয়েসে সে কোনও কথা না বললেও সব সময় তাকে মনে হত বাত্ময়। এখন তার ওষ্ঠাধর শুকনো। যেন সব কথা ফুরিয়ে আসছে।
কবি তবু কথা বলে যান। গল্প শোনান। কবিতা শোনান। বেলা সাড়াশব্দ করে না।
কখনও কবি একটুখানি গান গেয়ে ওঠেন। বলেন, এই গানটা তোর মনে আছে, তুই খুব পছন্দ করতি। আমার কঠিন হৃদয়টারে ফেলে দিলেম পথের ধারে/ তোমার চরণ দেবে তারে মধুর পরশ পাষাণ ঢালা…
বেলার চোখ তখন একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে অস্ফুট কণ্ঠে বলে, বাবা আর একটু গাও।
কবি খুব নিচু গলায় গাইতে থাকেন : আমার অভিমানের বদলে আজ নেব তোমার মালা/ আজ নিশিশেষে শেষ করে দিই চোখের জলের পালা—
বেলার একটি শীর্ণ হাত তিনি ধরে থাকেন মুঠো করে। বিন্দু বিন্দু জল গড়িয়ে পড়ে তার গাল বেয়ে।
কেউ এক পেয়ালা চা বা এক গেলাস সরবত পাঠায় না কবির জন্য। গান শুনতে শুনতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে বেলা।
কবি মাথা নিচু করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসেন।
দুঃখের বহিঃপ্রকাশে যেন দুঃখের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। কবির সব দুঃখ থাকে তার বুকের মধ্যে চাপা। নির্জনে সেই দুঃখ মুক্তি পায় শব্দ সমাহারে কিংবা সুরে।
বেলার বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর তিনি আবার শত কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু কারওর সঙ্গেই কন্যার অসুখ বিষয়ে আলোচনা করেন না।
তিলক ও অ্যানি বেসান্তের হোমরুল দাবি কবি সমর্থন করেন, সে কথা প্রকাশ্যে জানাবার জন্য প্রবন্ধও লিখেছেন। কিন্তু তার মতে, ইংরেজদের কাছ থেকে শাসন-অধিকার আদায়ের আগে এ দেশবাসীকেও যে তার যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। ভারতীয়রা যে এখনও ধর্মতন্ত্রের কাছে বিবেক বাঁধা রেখেছে। তার থেকে মুক্ত হতে
পারলে সমাজে কিছুতেই ঐক্য আসবে না।
রামমোহন লাইব্রেরিতে তিনি সেই প্রবন্ধটি পাঠ করবেন, কেউ কেউ উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, ভারত প্রতিরক্ষা আইন চালু আছে। এই সময় সরকার বিরোধী বক্তৃতা দিলে তিনিও অন্যান্য নেতাদের মতন গ্রেফতার হতে পারেন। সে সম্ভাবনা কবিও অস্বীকার করলেন না, কিন্তু এখন জেলখানায় যেতে তার আপত্তি নেই।
আজ আর বাড়ি ফেরা হবে না বলেই তিনি বেরুলেন। যথা সময়ে বক্তৃতাও হল, পুলিশ আশেপাশে ঘোরাঘুরি করলেও ধরল না আঁকে। শুধু তো কবি নন, তিনি একজন নাইট খেতাব পাওয়া ভারতীয়, তার গায়ে হাত ছোঁয়াতে গেলে অনেক ওপরওয়ালার অনুমতি নিতে হয়।
এর মধ্যে চলছে ‘ডাকঘর’ নাটকের অভিনয়ের তোড়জোড়। গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র, সমরেন্দ্র এই তিন ভাইয়ের খুব উৎসাহ। অসিত হালদার আর মুকুল দে নামে দুই তরুণ শিল্পীও খুব খাটাখাটনি করছে। অসিতের খুব দুঃখ, সে কোনও পার্ট পায়নি। রিহার্সাল চলতে চলতেই নাট্যকার তার জন্য বখা পাঁচু নামে একটা চরিত্র জুড়ে দিলেন। আশামুকুল নামে এক বালক চমৎকার অভিনয় করছে অমলের ভূমিকায়।
বিচিত্রায় মূল অভিনয়ের দিনে নাটকের মাঝখানেই হল একটি ছোট্ট নাটক।
আগেই কবি অনুভব করেছিলেন যে ডাকঘর নাটকটিতে গানের অভাব রয়ে গেছে। এক সময় আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসি—এই পংক্তি দিয়ে শুরু করে লিখেছিলেন একটি কবিতা। এর ভাবের সঙ্গে ‘ডাকঘর’-এর বিষয়বস্তুর মিল আছে। তাই এই কবিতায় সুরারোপ করে ইন্দিরাকে আড়াল থেকে গাইতে বলেছিলেন, ইন্দিরা একা গাইতে রাজি না হয়ে ডাক্তার নীলরতন সরকারের মেয়ে অরুন্ধতী ও আরও কয়েকটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে নিল।
পেছনের রাস্তা দিয়ে একজোড়া বোষ্টম-বোষ্টমী গাইতে গাইতে যাবে। হ্যাদে গো নন্দরানী, আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।’ এ পর্যন্ত হবার পর বিরতির ড্রপ সিন।
কবি অন্য কোনও ভূমিকা নেননি, শুধু গায়কের ভূমিকা। মাথায় মাত্র একটা গেরুয়া রঙের পাগড়ি পরে বাউল সেজে একবার মাধব দত্তের ঘরের পাশ দিয়ে নাচতে নাচতে গেয়ে গেলেন, গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে। আর একবার অন্তরাল থেকেও তার গান, ‘বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে। তবু, বিরতির সময় তার মনে হল, বিষয় অনুযায়ী আর একটা গান দরকার।
গ্রিনরুমের একটা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে তিনি অতি দ্রুত রচনা করতে লাগলেন একটা গান। সময় একেবারে নেই, তিনি লিখছেন ঝড়ের বেগে, সঙ্গে সঙ্গে গুনগুনোচ্ছেন সুর, যেন কোনও দৈবশক্তি ভর করেছে তার ওপর, বাণী ও সুর একসঙ্গে বেরিয়ে আসছে। নন্দলাল বসুকে বললেন, তিনি ইঙ্গিত না দিলে যেন পর্দা না ভোলা হয়, আশামুকুলকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বললেন, এই গানটা চটপট তুলে নে, তোকে গাইতে হবে।
ভয়ে আশামুকুলের মুখ শুকিয়ে গেল। একবার মাত্র শুনে পুরোটা গান মুখস্থ করে সঠিক সুরে সে গাইতে পারবে না। সে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, গুরুদেব, আমাকে মাপ করুন।
গুরুদেব বললেন, পর্দা তুলে দাও!
তার পর নিজেই আড়াল থেকে গাইলেন, ‘ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে’।
অভিনয়ের শেষে এই সদ্যরচিত গানটির জন্য সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল, শুধু একজন বলল, গুরুদেব গানটি চমৎকার হয়েছে ঠিকই। বাউল গানের সুরটিও ভাল মানিয়েছে। কিন্তু তাড়াহুড়োতে একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছেন। কী বলুন তো?
কবি তখনও ঠিক বুঝতে পারলেন না।
সেই ব্যক্তিটি আবার বলল, চাবি ভাঙলে কি ঘর খোলা যায়? তবে তো আরও সর্বনাশ। ঘর খুলতে গেলে তালা ভাঙতে হয়!
কবি স্মিত হাস্যে বললেন, ঠিকই ধরেছিস তো!
ঘরের চাবির সঙ্গে নিয়ে যাবি বেশ সাবলীল মিল। ঘরের তালা লিখলে অন্য মিল খুঁজতে হত। বন্দিশালা? যাওয়ার পালা? ঠিক জুতসই হচ্ছে না। কবি আর বদলালেন না। ধরা যাক, এটা আর্যপ্রয়োগ!
কবি অবশ্য আর্ষপ্রয়োগ’ শব্দটা নিজে উচ্চারণ করলেন না। তা হলে তো নিজেকে ঋষি বলে জাহির করতে হয়!
নিপাতনে সিদ্ধও বলা যেতে পারে।
মজার ব্যাপার এই, কবি এর পর অনেকবার লক্ষ করেছেন, অনেকেই এ গানটা শুনে তালা ভাঙা আর চাবি ভাঙার তফাতটা বুঝতে পারেন না।
কিছু কিছু মানুষ সব কিছুই ঠিকঠাক বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চায, যেন কল্পনা বা দুর্বোধ্যতার স্থান নেই তাদের জীবনে।
কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের পর আবার ডাকঘরের অভিনয় হল বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য। দেখতে এলেন গান্ধীজি, তিলক, মদনমোহন মালব্য, অ্যানি বেসান্ত প্রমুখ।
এই সবের মাঝে মাঝে কবির নিজেরও শরীর খারাপ হচ্ছে, আবার বেলাকেও দেখতে যাচ্ছেন।
আমন্ত্রণ এসেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে হবে।
গান্ধীজি প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, হোমরুল আন্দোলনের জন্য তিনি জনসাধারণের কাছ থেকে যে দান গ্রহণ করেছেন, তার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা তিনি রবীন্দ্রনাথকে দিতে চান। সেই টাকায় রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় ঘুরে ঘুরে ভারতের আন্দোলনের কথা প্রচার করুন, বিশ্ব জনমত গড়ে তুলুন।
প্রথম আমন্ত্রণ বিষয়ে বিবেচনা করার সময় নিলেও গান্ধীজির প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন সবিনয়ে। জনসাধারণ দান করেছেন রাজনৈতিক আন্দোলন চালাবার জন্য, সে টাকা গ্রহণ করা কবির পক্ষে সম্ভব নয়। বিদেশে রাজনৈতিক প্রচারকের ভূমিকা নিতেও তিনি অপারগ।
দুপুরবেলা একা একা চলে যান অসুস্থ মেয়ের কাছে। তাকে শোনান ডাকঘর’ অভিনয়ের গল্প। মালব্যজি কেঁদে ফেলেছিলেন, তিলক কবির দু’হাত জড়িয়ে ধরে কপালে চুঁইয়েছিলেন, অ্যানি বেসান্ত উচ্ছসিত, গান্ধীজি মুখে কিছু না বললেও তাঁর পত্রিকায় লিখেছেন দীর্ঘ প্রশংসা।
উঠে আসবার আগে গাইলেন নতুন গান, ‘মাতৃমন্দির পুণ্য-অঙ্গন কর মহোজ্জল আজ হে’। জগদীশচন্দ্র বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই উপলক্ষে লেখা।
হঠাৎ বেলার অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হল। সে উঠে বসে, হাঁটা চলা করে। খাওয়াতে অরুচি অনেকটা কমেছে, মুখের রং-ও যেন কিছুটা ফিরেছে মনে হয়। কবি খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আমেরিকায় যাত্রার ব্যবস্থা করতে লাগলেন, গান্ধীজির প্রস্তাব মতো নয়, নিজেরই
উদ্যোগে।
এর মধ্যে সি এফ অ্যান্ড্রুজ এক দুঃসংবাদ নিয়ে এলেন।
অ্যান্ড্রুজ রবীন্দ্রনাথেরও ভক্ত, গান্ধীজিরও ভক্ত। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে তিনি পড়াবারও দায়িত্ব নিয়েছিলেন, কিন্তু বেশি সময় পান না, প্রায়ই নানা দিকে ছুটোছুটি করতে হয়। যেখানেই ভারতীয়দের ওপর কোনও অবিচার ও অত্যাচার হচ্ছে, সেখানেই তিনি চলে যান প্রকৃত সত্য যাচাই করতে। এমনকী দক্ষিণ আফ্রিকাতেও যান বারবার।
অ্যান্ড্রুজ কয়েকটি বিদেশি পত্রপত্রিকার কর্তিকা পেয়েছেন, যাতে ছাপা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এক বিশ্রী, অসত্য, অলীক অপবাদ। দিল্লি থেকে ছুটে এসে অ্যান্ড্রুজ সেগুলি দেখালেন কবিকে।
ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে কয়েকজন ভারতীয়কে গ্রেফতার করা হয় আমেরিকায়, তাদের নামে মামলা চলে সানফ্রান্সিস্কোতে। সেই মামলার অন্যতম আসামি এক বাঙালি, তাঁর নাম ডঃ চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী। আমেরিকায় বসে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী দল সংগঠন করার জন্য তিনি নাকি অর্থসাহায্য পেতেন জার্মানি থেকে। ইংরেজদের সঙ্গে এখন জার্মানির ঘোর যুদ্ধ চলছে, তাই জার্মানি ভারতীয় বিপ্লবীদের সহায়তা করতে উৎসাহী, যেমন রুশ সরকারকে বিপর্যস্ত করার জন্য জার্মানি লেনিনকেও সাহায্য করেছে।
উক্ত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী জানালেন যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল, আগেরবার রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় এসে তাঁদের কার্যক্রম সমর্থন করেছেন, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এ ব্যাপারে সাহায্য পাবার জন্য। আমেরিকা থেকে তাঁর সুইডেনেও যাবার কথা ছিল, কিন্তু সেখানে গ্রেফতার হতে পারেন এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে হয়। বিপ্লবীদের তহবিল থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হয়েছে বারো হাজার ডলার!
সর্বৈব মিথ্যা যাকে বলে।
শুধু আমেরিকা নয়, জাপানি পত্রপত্রিকাতেও এই অভিযোগের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, তার অনেকগুলিতেই বিদ্রুপের সুর। সে সব পড়ে কবি কিছুক্ষণ বসে রইলেন হতবাক হয়ে।
কিন্তু এর প্রতিকার তো করতেই হবে। অ্যান্ড্রুজ তৎপর হয়ে যোগাযোগ করলেন বাংলা সরকার ও ভারত সরকারের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ এক দীর্ঘ চিঠি পাঠালেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনকে। চিঠি পৌছতে যদি দেরি হয়, তাই পাঠানো হল একটি টেলিগ্রাম।
সানফ্রান্সিস্কোতে মামলার শুনানির সময় আমেরিকান সরকারের পক্ষের অ্যাটর্নি যখন রবীন্দ্রনাথের নামে অভিযোগ সম্বলিত দলিল আদালতে পেশ করেন, তখন আসামিপক্ষের উঁকিল জিজ্ঞেস করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কি তাহলে একজন আসামি? অ্যাটর্নি সাহেব উত্তর দিলেন, না, তা নয় বটে, আমরা তাড়াতাড়িতে ওঁর নামটা জুড়ে দিতে ভুলে গেছি।
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রবীন্দ্রনাথের চিঠি ও তারবার্তা পাবার পর খোঁজখবর শুরু হয়। তখন সেই অ্যাটর্নি সাহেব জানান যে, না, সত্যিই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিযুক্ত নন, তিনি আসামিপক্ষের উঁকিলের প্রশ্নের উত্তরটি দিয়েছিলেন রসিকতা করে। কাগজওয়ালারা সেই বাক্যটি তুলে দিয়েছে, তারা রসিকতাও বোঝে না! ভারত সরকারের পক্ষ থেকেও মন্তব্য করা হল যে স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে ওই সব
অভিযোগের কোনও প্রমাণ নেই, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।
এই মামলার সময় জানা গেল আরও রোমহর্ষক ঘটনা, ঘটে গেল সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড।
আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে কবিকে নিয়ে তীব্র মতভেদ ছিল। একদল মনে করত, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাদের পক্ষে আনা দরকার, তাকে প্রচারের কাজে ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যাবে অনেক।
অন্য দলের মতে, এই কবি বিভিন্ন বক্তৃতায় পূর্ব-পশ্চিমের আদানপ্রদান বিষয়ে যেসব কথা বলছেন, তা ভারতীয় জাতীয়তাবোধের বিরোধী। তিনি ইংরেজদের অপশাসন বিষয়ে কিছু বলেন না।
এই মতভেদ এমনই তীব্র যে দ্বিতীয় দলের কারুর কারুর মনে হল, কবির কথা বলা একেবারে বন্ধ করে দিতে পারলেই কম ক্ষতি হবে। কবি যখন সানফ্রান্সিস্কোর একটি হোটেলে অবস্থান করছিলেন, তখন একজন বিপ্লবী গেল তাঁকে খুন করতে, অন্য দলের একজন ছুটে গেল সেই আততায়ীকে বাধা দিতে। হোটেলের লবিতে দু’জনের তর্ক বেধে গেল, দু’জনকেই সরে যেতে হল।
মামলার সময় সেই প্রসঙ্গ আসার উপক্রম হতেই আসামিপক্ষের একজন ফস করে একটা পিস্তল বার করে গুলি করল তার এক সহযাত্রীকে। সঙ্গে সঙ্গে আদালতের মার্শালও গুলি চালিয়ে শেষ করে দিল দ্বিতীয় জনকে। দুই নিহত বিপ্লবীর নিস্তব্ধ শরীরে গুপ্ত রয়ে গেল প্রকৃত সত্য।
একবার গুজব যখন রটেছে, তা সম্পূর্ণ প্রশমিত হবার আগে আমেরিকায় যাবার আর প্রশ্নই ওঠে না। কবি যাত্রার সব আয়োজন বাতিল করে দিলেন।
এরই মধ্যে আর একটি দুঃসংবাদ এল, জাপান থেকে ভারতে ফেরার পথে কবির আর একজন প্রিয় ইংরেজ বন্ধু পিয়ার্সন গ্রেফতার হয়েছেন পিকিঙে। শান্ত, নির্বিরোধী, মধুর স্বভাবের মানুষ পিয়ার্সন, এখানকার ছাত্রদের ভালবেসে শান্তিনিকেতনকেই করে নিয়েছেন নিজের বাসস্থান। তাঁর মুক্তির জন্যও উদ্যোগ নিতে হল কবিকে।
মানুষের প্রাণের সঙ্গে প্রদীপের তুলনা কোনওদিন পুরনো হয় না।
কয়েকদিন যাবৎ মনে হচ্ছিল বেলা বুঝি সত্যি ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ আরোগ্যের পথে যাচ্ছে। হঠাৎ তার অবস্থার আবার খুবই অবনতি হয়েছে দু’দিন আগে।
।কবি সাধারণত দুপুরবেলা নিরিবিলিতে দেখতে যান মেয়েকে। কাল বিকেল পর্যন্ত ছিলেন। আজ সকাল থেকেই তাঁর মন উতলা হয়ে আছে। লেখালেখি কিংবা বিষয় কর্মে মন বসছে না কিছুতেই। একসময় তিনি বেরিয়ে পড়লেন।
বেলার বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে, কয়েক পা এগিয়েই থমকে গেলেন কবি।
সদর দরজা হাট করে খোলা। বৈঠকখানায় ও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কিছু মানুষ, সকলেই কথা বলছে খুব নিম্ন স্বরে। কবিকে দেখে সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেল।
কবির পা মাটিতে গেঁথে গেল, স্থির মূর্তিবৎ তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন একটুক্ষণ। তিনি বুঝে গেছেন, বেলা আর নেই।
শোকের বাড়ির কোনও চিহ্ন লাগে না, বাতাসে গন্ধ পাওয়া যায়। হয়তো ফুলের গন্ধ, তবু সে গন্ধ অন্যরকম। অন্যদিনও হয়তো এ সময় দরজা খোলা থাকে, আজকের দরজা বড় বেশি ভোলা। হয়তো অন্যদিনও এই মানুষেরা আসে, কিন্তু আজ তারা অন্য মানুষ।
কবি আর ওপরে উঠলেন না। মৃত কন্যার মুখ দেখতে চান না তিনি। এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। বেলা চলে গেছে, এখন এ পরিবারের লোকেরা কবিকে হয়তো আরও অপ্রিয় কথা শোনাতে দ্বিধা করবে না।।
হাতে করে ফুল এনেছিলেন, বেলার প্রিয় চাঁপা ফুল, সেই ফুলের গুচ্ছ দোরের কাছে রেখে ফিরে গেলেন দ্রুতপদে।
তাঁর চোখে এক বিন্দু অশ্রু নেই। বুকের মধ্যে কিছু যেন চাপ বেঁধে আছে, তিনি মনকে নির্দেশ দিলেন শান্ত হতে। মৃত্যুর কাছে তিনি কিছুতেই পরাভূত হবেন না। মৃত্যু তো অনন্ত জীবন প্রবাহেরই অঙ্গ।
বেলাকে যে আর বেশি দিন ধরে রাখা যাবে না, সে জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন আগে থেকেই। তাঁর অন্য মেয়ে রাণু আর রাণুর মায়ের ওপরেও মৃত্যুর ছায়া পড়েছিল ধীরে ধীরে। শুধু তাঁর আদরের ছেলে শমী, সবাই বলত শমী যেন তার বাবারই ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি, সেই শমী চলে গেল আচম্বিতে, সেই আঘাত সামলানো সহজ ছিল না।
জোড়াসাঁকোয় এসে তিনি উদ্বিগ্ন রথী আর প্রতিমাদের খবরটি জানালেন অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে। ঠিক কখন, কী ভাবে এসেছে বেলার শেষ মুহূর্ত কিংবা কী ভাবে সম্পন্ন হবে শেষকৃত্য, তা নিয়ে একটি কথাও বললেন না, উঠে গেলেন তিনতলার ঘরে।
রথী জানে তার বাবার মনের গড়ন। নিজে তো শোকের কোনও চিহ্ন দেখাবেনই না, অন্য কেউ তাঁর সামনে শোকের উচ্ছ্বাস দেখালে বিরক্ত হবেন। মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করার একমাত্র উপায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকা। বাবা এখন অন্যদিনেরই মতো লেখাপড়া নিয়ে বসবেন। এমনকী অন্য কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে এমনই স্বাভাবিক ভাবে কথা বলবেন, অন্যরা বুঝতেই পারবে না আজ কী ঘটে গেছে।
বিকেল পর্যন্ত কবি রইলেন নিজের ঘরে।
তারপর হঠাৎ একসময় ব্যস্তসমস্ত ভাবে বাইরে বেরোবার পোশাকে সজ্জিত হয়ে নামতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে।
রথী সর্বক্ষণ আড়াল থেকে নজর রাখছিল। সে প্রথমে ভাবল, তবে কি নীচে কোনও দর্শনার্থী এসেছে? না, কেউ এলে আগে তো তাকেই জানাবার নির্দেশ সে দিয়েছে ভৃত্যদের।
সে জিজ্ঞেস করল, বাবা, আপনি কোথাও বেরোচ্ছেন?
বাবা বললেন, হ্যাঁ, একটু ঘুরে আসি।
রথী আবার বলল, আমি যাব আপনার সঙ্গে?
বাবা বললেন, তার দরকার নেই, সন্ধের আগেই ফিরে আসব।
রথী বারান্দা থেকে দেখল, বাবামশাই বাড়ির গাড়ি নিলেন না, হেঁটেই যাচ্ছেন।
হয়তো যাচ্ছেন গঙ্গার ধারে। খানিকক্ষণের জন্য নদীর টাটকা বাতাস গায়ে মেখে এলে ভালই হবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গুমোট গরমের দিন। বাইরে কিছু ভাব দেখাবেন না, কিন্তু বাবামশাই যে কী কঠিন সংযমের পরীক্ষা দিচ্ছেন, তা কি রথী বোঝে না? মাধুরীলতা আর নেই! রথী নিজে সারা দুপুর নিঃশব্দে কেঁদেছে।
কবি খানিকটা হেঁটে চিৎপুরের রাস্তায় এসে একটা ভাড়ার ঘোড়ার গাড়ি ডাকলেন। তাতে উঠে বসে নির্দেশ দিলেন ভবানীপুরের দিকে যেতে।
সেখানে পৌঁছে তিনি ল্যান্সডাউন রোডে একটি নম্বর খুঁজতে লাগলেন। একটু পরে থামলেন একটা বাড়ির সামনে। এই তো পঁয়ত্রিশ নম্বর।
সদর দরজা বন্ধ। তিনি মুখ তুলে জোরে জোরে ডাকলেন, রাণু! রাণু!
ওপরের জানলা দিয়ে কে যেন মুখ বাড়াল।
কবি ঘোরলাগা মানুষের মতো বললেন, রাণু কোথায়? আমি রাণুকে দেখতে এসেছি।
ঘটাং করে দরজা খুলে গেল। প্রথম দৃষ্টিপাতে কবির মনে হল, তিনি কোনও অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছেন।
সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে, একটি পরী, না অপ্সরা? নাকি তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম?
আপাতত মনে হয়, একটি দশ-এগারো বছরের বালিকা, দুধেআলতা গায়ের রং, সরল হরিণী চোখ, মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, তার অঙ্গে একটি সুতোও নেই, সে সম্পূর্ণ নগ্নিকা।
এই বয়েসের মেয়েরা নগ্ন থাকে না। কবি যে সমাজে বিচরণ করেন, সেখানে দু’তিন বছরের বালিকারাও পোশাক না পরে বাইরের লোকের কাছে আসে না, কবি সেরকম দেখতেই অভ্যস্ত। তাই তাঁর মনে হল, অবশ্যই পরী কিংবা অপ্সরা, তাদের পোশাকের প্রশ্ন নেই। প্রির্যাফেলাইট চিত্রকলায় যে সব উড়ন্ত পরীদের দেখা যায়, তারা তো এই রকমই।
কবির মনে হল, এ বালিকা টাকা-পয়সা গুনতে শেখেনি, ঘড়ি দেখতে জানে না, কারণ স্বর্গে টাকাপয়সা কিংবা ঘড়ি নেই।
এ বালিকা জন্ম মৃত্যুর অতীত, কালের চিহ্ন ওকে স্পর্শ করে না।
আজকের দিনটিতেই এ বালিকা সরাসরি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে তাঁর হৃদয় জুড়িয়ে দিতে।
রাণু তার আয়ত চক্ষুদুটি মেলে তাকিয়ে রইল কবির দিকে।
কবির দীর্ঘকায় সুঠাম শরীরে এখনও বয়েসের স্পর্শ লাগেনি। মাথার চুলে সদ্য পাক ধরেছে, দাড়িও সাদায়কালোয় মেশামেশি, কিন্তু চক্ষুদুটি যৌবনবন্ত।
তাঁর বিষণ্ণতা এখন ঢেকে দিয়েছে বিস্ময়।
রাণু প্রথম দেখেই চিনেছে।
কিন্তু সে কোনও কথা বলে একটা হাত ধরল কবির।
কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই দুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন রাণুর মা, এক পিসি, এক মামা।
মামাটি বিস্মিতভাবে বলে উঠলেন, আরেঃ, রবিবাবু।
কবি এক দৃষ্টিতে নগ্নিকা বালিকাটির দিকে চেয়ে বললেন, তুমিই রাণু?
রাণু বলল, আপনি রবিবাবু, কথা রেখেছেন তাহলে। এসেছেন!
রাণুর মা বললেন, ছি ছি ছি, রাণু, তুই এই ভাবে … যা, শিগগির যা!
রাণু কিছুই বুঝতে না পেরে বলল, কেন, কী হয়েছে? উনি তো আমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছেন।
মা বললেন, হতচ্ছাড়ি, যা ইজের পরে আয়। জামা পরে আয়!
রাণু বলল, বড্ড গরম, ঘেমে যাচ্ছি যে!
কবি বাস্তবে ফিরে এসে ঈষৎ লজ্জাবোধ করলেন।
গত আট নমাস ধরে রাণু তাঁকে কত না চিঠি লিখেছে, তিনিও উত্তর দিয়েছেন সমানে। এতদিন চোখের দেখা হয়নি। শেষ চিঠিতে রাণু মাথার দিব্যি দিয়েছিল, সে কলকাতায় আসছে, এবার দেখা করতেই হবে। ঠিকানা দিয়েছিল এ বাড়ির।
কিন্তু কবি তো রাণুর বাবা-মায়ের সঙ্গেও পরিচিত। মামাটিকেও চেনেন। তবু বয়স্ক ব্যক্তিদের আগে সম্বোধন না করে, ঝোঁকের মাথায় শুধু রাণুর নাম ধরেই ডেকেছেন।
কবিকে এনে বসানো হল দোতলার প্রশস্ত বসবার ঘরের আরামকেদারায়।
সবাই ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করল কবির পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে, শুধু রাণু ছাড়া।
সে এর মধ্যে একটা গোলাপি রঙের শাড়ি আলুথালু ভাবে গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে, মিটিমিটি হাসছে।
লাঠিতে ভর দিয়ে এলেন শীর্ণকায় ফণিভূষণ অধিকারী।
তিনি একটানা রোগে ভুগছেন, কাশিটা কিছুতেই সারছে না, তাই হাওয়া বদল ও চিকিৎসার জন্য সপরিবারে এসেছেন কলকাতায়।
এখন বয়স্কদের সঙ্গেই কবি কথা বলতে লাগলেন। বাইরে থেকে একজন অতিথি এসে শুধু বাড়ির একটি বালিকার সঙ্গেই কথা বলবেন, এ তো শোভা পায় না। যদিও কবি এসেছেন রাণুরই টানে।
তিনি মাঝে মাঝেই দেখছেন রাণুকে।
সে যেন ঠিক এই বয়েসের মাধুরীলতা। রাণুর শরীর বেলার তুলনায় খানিকটা বড়সড়, তবু তাকে যতবার দেখছেন, বেলার সঙ্গেই মিল খুঁজে পাচ্ছেন।
বেলা তার বাবার দিকে যে ভাবে তাকাত, তার চেয়ে রাণুর চাহনি ভিন্ন।
খানিকটা যেন রাগ রাগ ভাব। যেন, কবি কেন তাকে ছেড়ে অন্যদের সঙ্গে কথা বলছেন, সেটা তার পছন্দ হচ্ছে না।
রাণুর মামা কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বেশ বাক্যবাগীশ মানুষ। একএকটা গল্প শুরু করলে থামতে চান না। কথা বলেন বাংলা-হিন্দি মিশিয়ে, শুনতে বেশ লাগে। একবার তিনি শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের কাছে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার শিরোনামটি ছিল চমকপ্রদ। ‘কো বাং চো চাং’! অর্থাৎ ‘কোমর বাঁধো, চোখ চাও!’ সে উপদেশাত্মক বক্তৃতা শুনে ছাত্ররা শিক্ষা গ্রহণের বদলে হেসে গড়াগড়ি দিয়েছিল।
কবি এবার উঠে পড়বেন। সবাই অনুরোধ করল, আরও কিছুক্ষণ থাকার জন্য। কবি কি একটা-দুটো নতুন কবিতা শোনাবেন না? কিংবা গান?
যারা অনুরোধ করছে, তারা জানে না যে আজ সকালেই কবির কন্যা-বিয়োগ হয়েছে। তবে রাণুকে যতবার দেখছেন, ততবার যে তাঁর বুকের ব্যথা একটু একটু করে কমে যাচ্ছে, সে কথাও ঠিক।
উঠে দাঁড়িয়ে তিনি ফণিভূষণকে বললেন, অধিকারী মশাই, আপনি স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে চান, সবাই মিলে শান্তিনিকেতনে চলে আসুন। শান্তিনিকেতনের জল-হাওয়া খুব ভাল, অনেকে তো বলে, ওখানকার জলে পাথর পর্যন্ত হজম হয়ে যায়। অবশ্য আপনাদের পাথর খেতে দেব না। আপনাদের কোনও অসুবিধে হবে না, সব ভার আমার ওপর!
কবিতা আসছে না একেবারেই। বাংলার বদলে কবি এখন বেশি লিখছেন ইংরেজি। কখনও নিজের রচনার অনুবাদ, আর বিদেশি বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকদের চিঠিপত্র। গীতাঞ্জলি পুরস্কার পাবার পর তাঁর বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজিতে। ভালই বিক্রি হয়, তার রয়ালটির টাকায় কিছুটা নির্বাহ হয় শান্তিনিকেতনের ক্রমবর্ধমান ব্যয়। আরও ইংরেজি গ্রন্থের চাহিদা আছে।
বিদেশযাত্রা আপাতত স্থগিত। বিশ্বযুদ্ধের এখন ঘোর অবস্থা। রাশিয়া ও রুমানিয়া এর মধ্যে সন্ধি করেছে জার্মানির সঙ্গে। পূর্ব রণাঙ্গন থেকে সৈন্য সরিয়ে এনে জার্মানরা এখন সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়েছে ফ্রান্সের দিকে। প্যারিস নগরীর পতন বুঝি আসন্ন।
কবি বেশি সময় কাটাচ্ছেন শান্তিনিকেতনে। ছাত্রদের ক্লাস নিচ্ছেন নিয়মিত। সেসব ক্লাসে দশ-বারো বছরের ছাত্ররাও যেমন থাকে, তেমনই যোগ দেন অধ্যাপকেরা, হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়েন অ্যান্ড্রুজ, আবার সীতা, শান্তার মতো তরুণীরাও বসে পড়ে এক ধারে।
ফণিভূষণ অধিকারীকে সপরিবারে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে মহর্ষি ভবনে। তাঁর চিকিৎসার ত্রুটি নেই, যদিও উন্নতি হচ্ছে না বিশেষ। কবি প্রতিদিন তাঁকে দেখতে যান।
রাণু বনবালার মতো সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। কখনও সে সকলের উপাসনাগৃহে উঁকি মারে, কখনও ক্লাস নেবার সময় একপাশে দাঁড়ায়, আবার এক একসময় সে আম্রকুঞ্জের কোনও গাছে চড়ে বসে।
এখানে একটি পোষা হরিণ আছে, সেটি তার খেলার সঙ্গী। তাকে সে ঘাস খাওয়ায়, ছোলা খাওয়ায়। হঠাৎ হরিণটি খোয়াইয়ের দিকে ছুটতে শুরু করলে রাণুও তার সঙ্গে ছোটে। রাণুর আগেই অবশ্য হরিণটা ফিরে আসে নিজের জায়গায়।
দূর থেকে তাই দেখে কবি হাসেন। একদিন বললেন, ভাবছি এবার থেকে তোমাকে শকুন্তলা বলে ডাকব।
রাণুর তাতে ঘোর আপত্তি। অন্য কোনও নামের চেয়ে রাণু নামটাই তার বেশি পছন্দ। সে বরং শকুন্তলার গল্পটা শুনতে চায়।
কবি অন্য কাজ সরিয়ে রেখে গল্প বলতে শুরু করেন।
কিশোরী শকুন্তলার রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে যেন কবির সামনের এই মেয়েটির চেহারার সঙ্গেই মিলে যায়। রাণু কিন্তু তা বুঝতে পারে না।
সে এখনও সচেতন হয়নি নিজের সম্পর্কে। তাই তো গরম লাগলেই সে জামা খুলে ফেলে। এখানে অবশ্য তার মা তাকে প্রায় সব সময় চোখে চোখে রেখেছেন, নিজে রাণুকে শাড়ি পরিয়ে বাইরে পাঠান।
ছোটাছুটি করতে গিয়ে রাণুর শাড়ির আঁচল মাটিতে লুটোয়। কখনও শাড়িতে পা জড়িয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে মাটিতে। আবার সামলে নেয়।
গল্পের মাঝখানে রাণু জিজ্ঞেস করল, শকুন্তলা কি শাড়ি পরত?
কবি স্মিতহাসে একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আশ্রমের ঋষিরা পরতেন বঙ্কুলের পোশাক, সেকালে ধুতি-শাড়ির চলনই ছিল না। ছবিতে অবশ্য অন্যরকম আঁকে।
তিনি বললেন, গাছের পাতা সেলাই করে কী সুন্দর পোশাক বানানো হত তখন। শাড়ির চেয়েও অনেক ভালো।
গাছের পাতার পোশাক কেমন হবে, কল্পনা করার চেষ্টা করল রাণু।
শকুন্তলার গল্পটা অবশ্য শেষ হল না, মাঝখানে অন্য লোক আসায় ছেদ পড়ে গেল।
অন্য তোক দেখলে রাণুও আর এখানে থাকতে চায় না।
দুপুরবেলা কবি যখন লিখতে বসেন, তখন কেউ তাঁর ঘরে আসে। আশ্রমের সবাই এটা জানে। কিন্তু রাণুকে কে আটকাবে? দমকা বাতাস কিংবা আকাশের অশনিকে কেউ বাধা দিতে পারে।
বহু প্রত্যাশিত বর্ষা সবে এসে পড়েছে। আর ক’দিন পরেই পয়লা আষাঢ়ের উৎসব হবে, আজও বৃষ্টি পড়ছে ঝেপে ঝেপে। কবি ইংরিজি চিঠি লিখছেন এক বিদেশিনীকে।
হঠাৎ একটুকরো ঝড়ের মতো দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল রাণু।
বৃষ্টিতে তার মাথার চুল ভেজা, তার মুখখানিও কমল-কোরকের মতো জলে ধোওয়া। একটা কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরেছে সে, আঁচলটা গাছ-কোমর করে বাঁধা।
চক্ষুদুটি বিস্ফারিত করে বলল, জানেন, জানেন, হরিণটাকে কাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
কবি সে সংবাদ আগেই জেনেছিলেন। লেখা থেকে সহজে মন ফেরানো যায় না। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, হুঁ।
রাণু কাছে এসে তাঁর হাত থেকে কলম কেড়ে নিয়ে ধমক দিয়ে বলল, এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, আর আপনি এখনও লিখচেন? কী এত লেখেন সারাদিন? মোটেই এত লিখতে হবে না। কাল থেকে সবাই মিলে কত খোঁজাখুজি করছে, আমিও খুঁজতে গিয়েছিলাম—
কবি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় খুঁজতে গিয়েছিলে?
রাণু বলল, অনেক দূরে, খোয়াইয়ের ও পাশে যে জঙ্গল আছে,…তারপর লালবাঁধে।
কবি এবার লেখার সরঞ্জাম সরিয়ে রেখে বললেন, বনের হরিণ, ও যে একদিন চলেই যাবে তা জানতুম। এবারের বসন্তে, যখন শালগাছগুলো মঞ্জরীতে ভরে গেল, বাতাস ভরে গেল সুগন্ধে, তখনই ওকে উন্মনা দেখেছি। আমার হাত থেকে আর খাবার নিতে চাইত না। তখনই বুঝেছি, অরণ্য ওকে টানছে, মানুষের কাছে আর থাকতে চায় না। তুমি যে ফিরে এসেছ, জঙ্গলে হারিয়ে যাওনি, তাই-ই যথেষ্ট।
রাণু বলল, আমি কেন হারিয়ে যাব? আমার জঙ্গল ভাল লাগে না, আমার কাশী ভাল লাগে।
কবি জিজ্ঞেস করলেন, শান্তিনিকেতন ভাল লাগছে না?
রাণু বলল, হ্যাঁ, ভাল লাগছে। আপনি আছেন বলেই বেশি ভাল লাগছে। আচ্ছা, হরিণটাকে আর পাওয়াই যাবে না? আমার কষ্ট হচ্ছে।
কবি সুর করে বললেন, সে কোন বনের হরিণ ছিল আমার মনে/কে তারে বাঁধল অকারণে…
রাণু ভুরু দুটি তুলে বলল, ওটা কী, গান? এই মাত্র বানালেন?
কবি বললেন, না। কাল রাতেই মনে এসেছিল। বনের হরিণকে ঘরের পাশে বেঁধে না রেখে মনের মধ্যে রেখে দেওয়াই তো ভাল।
রাণু বলল, বাকিটা শুনি শুনি–
কবি আবার সুর ধরলেন,…সে কোন বনের হরিণ ছিল আমার মনে/কে তারে বাঁধল অকারণে।।/গতিরাগের সে ছিল গান, আলো ছায়ার সে ছিল প্রাণ/আকাশকে সে চমকে দিত…
হঠাৎ গান থামিয়ে কবি বললেন, এবারে অন্য দুটি প্রাণী পুষব ঠিক করেছি। বলো তো, কোন প্রাণীর শরীরের চেয়ে তার ল্যাজটা বেশি লম্বা?
রাণু কয়েক মুহূর্ত মাত্র চিন্তা করে বলল, জানি। হনুমান!
কবি সহাস্যে বললেন, ছি ছি, আমি হনুমান পুষব? তুমি ভাবলে, আমার সঙ্গে মিল আছে? আমার লাঙ্গুলটি প্রকাশ্য নয় বটে, কিন্তু আমিও মাঝে মাঝে এক লম্ফে সমুদ্র পাড়ি দিই!
রাণু কোপের ভঙ্গি করে বলল, মোটেই আমি সে কথা ভেবে বলিনি। আপনি জানেন না, আপনি কত সুন্দর? আপনি সকলের চেয়ে সুন্দর।
কবি বললেন, শুনে আশ্বস্ত হলেম। আমি মনে করেছিলাম, আমি ছ’ফুট লম্বা মানুষ, এত বড় গোঁফ দাড়িওয়ালা কিম্ভুত কিমাকার লোক, প্রথম দেখে তুমি হয়তো নারদমুনির মতন মনে করে ভয় পাবে, তোমার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে যাবে। তা যে হল না সেদিন, তুমি যখন এসে আমার হাত ধরলে, তখন তোমার হাত একটুও কাঁপল না, এ কী কাও বলো দেখি!
রাণু কবির গা ঘেঁষে এসে বলল, মনে মনে যেমন ভেবে রেখেছিলাম, আপনি তার চেয়েও বেশি সুন্দর। এবারে কী পুষবেন বলুন না?
কবি বললেন, ময়ূর। রথীকে এক জোড়া ময়ুর আনতে বলেছি। এক জোড়া না হলে ওদের মানায় না!
রাণু তার বেদানা রঙের ওষ্ঠ উলটে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, ওঃ ময়ুর! আমাদের কাশীতে কত ময়ূর আছে, পুষতে হয় না। এবারে রেলে চড়ে আসবার সময় দু পাশের মাঠে অনেক ময়ূর দেখেছি!
কবি বললেন, তা ঠিক। কিন্তু এখানে তো ময়ুরেরা নিজে নিজে আসে না। এই বর্ষায় ময়ূরের পেখম মেলা নৃত্য দেখবার জন্য পুষতেই হবে অগত্যা। হ্যাঁ, ভাল কথা, আর সবাই আমাকে প্রণাম করে, তুমি করো না কেন?
রাণু বলল, আর সবাই আপনাকে গুরুদেব বলে। আমি তো বলি। কেমন যেন দূর দূর মনে হয়।
কবি বললেন, ও তাই! আমি মনে করেছিলুম, তোমারও বুঝি জাতের গুমোর আছে। তোমার বাবা প্রথম যখন এখানে আসেন, আমাকে প্রণাম করতে চাননি। শুনেছিলুম, তোমরা তো উঁচু জাতের বামুন, আর আমরা পিরিলির বামুন, পতিত, তাই আমার পায়ে তোমাদের হাত ছোঁয়াতে নেই।
রাণু বলল, মোটেই না। আমার বাবা, মা সবাই আপনাকে প্রণাম করে দেখেছি।
কবি বললেন, এখন করেন। তবু তুমি করো না কেন?
রাণু বলল, অত ভক্তি-শ্রদ্ধা আমার আসে না। আমি যে আপনাকে ভালবাসি!
কবি রাণুর নবনীত কোমল একটি হাত ধরে বললেন, এত স্পষ্টাস্পষ্টি ভালবাসার কথা কতকাল যে কেউ আমাকে বলেনি। রাণু, তুমি আমার মাধুরীলতার শূন্যস্থান যেন পূর্ণ করে দিতে এসেছ! তোমাকে যতবার রাণু বলে ডাকি, ততবার আমার আর এক মেয়ে রেণুর কথাও মনে পড়ে। কখনও কখনও তাকে রাণু বলেও ডাকতাম। কিন্তু, তুমি যদি আমায় ভালবাসো, তবে সব চিঠিতে গম্ভীর ভাবে প্রিয় রবিবাবু লেখো কেন? এ যেন একেবারে ফর্মাল সম্বোধন! তা হলে যে আমাকেও রাণু দেবী বলে লিখতে হয়!
রাণু বলল, আমি আপনাকে যখন প্রথম চিঠি লিখেছিলাম, তখনও আপনি আমার কাছে নিতান্ত রবিবাবুই ছিলেন। তখনও আমি আপনাকে ভালবাসতাম। কিন্তু তখনকার চাইতে এখন বেশি ভালবাসি। আমি আপনাকে তো ইংরিজি কায়দায় প্রিয় লিখিনি। প্রিয়র বাংলা মানে যা হয় তাই লিখেছি। আমি আর কাউকে প্রিয় লিখিও না। আপনি তো কবিতায় অনেক প্রিয় লেখেন, আমি লিখলেই বুঝি যত দোষ! আমি প্রিয় যে চিঠি লেখবার পাঠ তা জানিও না। আপনাকে প্রিয় লাগে বলেই লিখি। আপনি ঠাকুরকে যেমন বলেন, আমিও আপনাকে তেমনি প্রিয় বলি।
কবি সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, বোঝা গেল, বোঝা গেল। তোমার যুক্তির কাছে হার মানছি! অধ্যাপকের মেয়ে না যেন পাকা উঁকিলের মেয়ে। কিন্তু রবিবাবু কেন? অন্তত রবিদাদাও তো লিখতে পারো!
রাণু বলল, ও নামেও অনেকে আপনাকে ডাকে। আমি এমন একটা নাম চাই, যে নামে আর কেউ ডাকবে না।
কবি বললেন, সে রকম নাম খুঁজে বার করতে হবে।
রাণু জিজ্ঞেস করল, আপনার মেয়ে মাধুরীলতা কখনও আপনার কোলে বসত?
কবি বললেন, তোমার বয়েসে? নিশ্চয়ই। যখন তখন এসে ঝুপ করে আমার কোলে বসে গলা জড়িয়ে ধরত।
রাণু বলল, তা হলে আমিও বসি?
রাণুর চেয়ে একটু বড়, প্রায় পিঠোপিঠি বোন ভক্তি, সেও বড় সুন্দর, কিন্তু রাণুর মতন তার সৌন্দর্যে তেমন জ্যোতি নেই। ওদের বাবা এই দুই কন্যার অন্য নাম দিয়েছেন, ছায়া ও কায়া। ভক্তি সত্যিই ছায়ার মতন, নির্বাক ও সুস্থির, সে রাণুর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, কিন্তু রাণুর কখনও হরিণীর গতি, শান্তি হাঁটে ধীর লয়ে। রাণু যে কোনও মানুষের সঙ্গে অকপটে আলাপ করে নিতে পারে, ভক্তি তখন আড়ালে চলে যায়।
রাণু সময়ে-অসময়ে কবির কাছে চলে যায়, ভক্তি লজ্জায় কবির সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতে পারে না।
রথী আর প্রতিমার সঙ্গেও রাণু বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছে। আশ্রমের সকলেই এখন রাণুকে চেনে, কবি যে এই বালিকাটিকে বিশেষ পছন্দ করেন, তাও সবাই জানে। মাধুরীলতার বিয়োগ বেদনা কবির মন থেকে অনেকটা ভুলিয়ে দিয়েছে এই মেয়েটি, সে জন্য সকলেই তাকে অবাধ প্রশ্রয় দেয়।
কবির সেবার ভার পুত্রবধু প্রতিমার ওপর। খাওয়ার ব্যাপারে কবির খুঁতখুঁতুনি আছে, তাই ঠাকুর-চাকরদের ওপর নির্ভর না করে প্রতিমা নিজে তাঁর আহার্য প্রস্তুত করে, নিজেই কবির কাছে নিয়ে যায়।
রাণু রান্নাঘরে এসে প্রতিমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয় মাঝে মাঝে।
একটা পাথরের গেলাসে ভরা হয়েছে গরম দুধ, একটা রুপোর রেকাবিতে দুটি সন্দেশ ও ছাড়ানো বেদানা।
রাণু জিজ্ঞেস করল, এগুলো আমি নিয়ে যাব প্রতিমাদিদি?
প্রতিমা ভুরু তুলে বলল, ওমা, দিদি বলছিস কী রে? তোর থেকে আমি কত বড়!
রাণু জিজ্ঞেস করল, তা হলে কী বলে ডাকব? বউদিদি?
কাল তুই আমার বরকে কী বলে ডাকছিলি? রথীকাকা না? কাকার বউ বুঝি বউদিদি হয়?
দু’জনেই হাসতে লাগল মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে।
তারপর প্রতিমা বলল, তুই বাবামশাইকে রবিবাবু বলিস? কী পাকা মেয়ে!
রাণু বলল, চিঠিতে লিখেছিলাম। মুখে তো বলি না।
তা হলে কী বলে ডাকিস এখন? কথা বলার সময়?
কিছুই বলি না। এখনও নামটা ঠিক হয়নি।
আমরা বাবামশাই বলি, তুই দাদামশাই বলে ডাকতে পারিস?
রাণু দু দিকে মাথা দোলায়। এ সম্বোধন তার পছন্দ হয় না।
তারপর হাত বাড়িয়ে বলল, আজ আমি ওঁর খাবার নিয়ে যেতে পারি?
প্রতিমা বলল, তুমি নেবে? ঠিক আছে নিয়ে যাও! ওঁর একটা দোষ আছে, উনি কিছুতেই পুরোটা দুধ শেষ করেন না। সন্দেশও আধখানা কামড়ে ফেলে রাখেন। দ্যাখো, তুমি যদি সবটা খাওয়াতে পারো।
রাণু খুব সাবধানে হাঁটি হাঁটি পা পা করে পাথরের গেলাস ও রেকাবি দু হাতে ধরে উপস্থিত হল কবির কাছে।
ঘরের মধ্যে দুজন ব্যক্তি কবির সঙ্গে আশ্রম-বিদ্যালয় বিষয়ে আলোচনা করছে।
কবি অন্য লোকের সামনে কিছু খান না, তা রাণু জেনে গেছে এর মধ্যেই। সে গেলাস ও রেকাবি টেবিলের ওপর রাখল।
কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল, ব্যক্তি দুটির নাম কালীমোহন ও সন্তোষ। কবি মাঝে মাঝে সুরুল, খামার, কৃষি, গোপালন এই সব বলছেন। কবির মুখে এই ধরনের নীরস কথা রাণুর একেবারে পছন্দ হচ্ছে না। দুধ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে!
ব্যক্তিদ্বয় অবশ্য একটু পরেই নিষ্ক্রান্ত হলেন।
রাণু দুধের গেলাস কবির মুখের কাছে নিয়ে এল।
কবি যথারীতি একটি চুমুক দিয়েই বললেন, বাঃ বেশ।
রাণু বলল, উহু, ওটুকু খেলে চলবে না। আরও খান!
কবি বললেন, প্রতিমা বুঝি হাল ছেড়ে দিয়ে তোমাকে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন? ঠিক আছে, তোমার সম্মানে আর এক চুমুক দিচ্ছি।
রাণু বলল, সবটা খেতে হবে।
কবি বললেন, তুমি কি আমাকে দুগ্ধপোষ্য শিশু বানাতে চাও নাকি? বাধ্য হয়ে কিছুটা খাই, গো বৎসদের সম্পূর্ণ বঞ্চিত করতে চাই না।
রাণু বলল, বাছুরে আর এ দুধ খাবে কী করে, দোওয়ানো হয়ে। গেছে।
আবার তিনজন দর্শনার্থী উপস্থিত। রাণু সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিয়ে গেল দুধের গেলাস।
কথা শুরু হল ছাপাখানা বিষয়ে।
আমেরিকার লিংকন শহরের অধিবাসীরা কবিকে একটি ছাপাখানা উপহার দিয়েছিল। অনেক রকম টাইপ ও যন্ত্রপাতিও পৌঁছে গেছে জাহাজযোগে। শান্তিনিকেতনে সেই ছাপাখানাটি এখনও ঠিক মতন চালু হয়নি।
এবারেও কবি আগন্তুকদের সঙ্গে নীরস কথাবার্তা চালাতে লাগলেন, মাঝে মাঝে ইংরিজি শব্দ।
লোক তিনটির মুখ রাণুর চেনা। গতকালই ১লা আষাঢ় উপলক্ষে বর্ষা উৎসব হল, তাতে অনেক সংস্কৃত শ্লোক পাঠ আর গান শুনেছিল সে। কবি ভাষণ দিয়েছিলেন, গান গেয়েছিলেন, মজা হয়েছিল বেশ। এঁদের মধ্যে চশমা পরা ভদ্রলোকটিও গান গেয়েছিলেন।
হঠাৎ কথা থামিয়ে কবি বললেন, এই দ্যাখো, তোমাদের সঙ্গে এই অধীরা বালিকাটির পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। এর নাম রাণু। চারু, তোমাকে তো এই মেয়েটির কথা লিখেছিলুম, বলতে পারো এ এখন আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী। রাণু, এঁরা হলেন, চারুচন্দ্র, সুকুমার আর অজিত।
তারপর চশমা পরা ব্যক্তিটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, তুমি সুকুমারকে চেন না বুঝি? ইনি সুকুমার রায়, ছাপাখানার মস্ত বিশেষজ্ঞ, আর তোমাদের বয়েসীদের জন্য কত চমৎকার সব লেখা লিখেছেন!
রাণু চোখ বড় বড় করে বলল, সুকুমার রায়, মানে সন্দেশ? আমি পড়েছি, পাগলা দাশু, পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা, আর…গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা, আওয়াজ খানা দিচ্ছে হানা দিল্লি থেকে বর্মা…।
অজিত বললেন, বাঃ বেশ মুখস্ত আছে দেখছি!
রাণু কবির বাহু ছুঁয়ে সুকুমারকে বলল, আমি কিন্তু আপনাকে ভালবাসি না। শুধু এঁকে ভালবাসি।
তার সরল উক্তি শুনে সবাই হেসে উঠলেন এক সঙ্গে।
কবি বললেন, এ বালিকা ভালবাসা ভাগাভাগি করতে জানে না।
সুকুমার বললেন, ও বস্তুটি ভাগাভাগি করলে তেমন স্বাদ থাকে না। আমি একজন পাঠিকা পেয়েছি, এই যথেষ্ট।
চারুচন্দ্র বললেন, ছাপাখানার বিষয়টা এখন বাকি থাক। গুরুদেবকে তো তৈরি হয়ে নিতে হবে। সন্ধেবেলা সভা আছে।
ওঁরা বেরিয়ে যেতেই রাণু আবার দুধ ও সন্দেশ শেষ করার জন্য চেপে ধরল কবিকে।
কবি বললেন, আর যে খেতে পারছি নে। এরপর লেকচার দিতে হবে। যে-মানুষ বেশি কথা বলে, তাকে লঘু ভোজন করতে হয়।
রাণু বলল, আপনি অত লেকচার দেন কেন? গল্প লেখার নাম নেই, কবিতা লেখা নেই, খালি লেকচার। মোটেই ভাল নয়। এ সব আপনাকে খেতেই হবে!
কবি একটি সন্দেশ মুখে পুরে বললেন, এরপর দেরি হয়ে যাবে। এবার উঠি।
রাণু বলল, আপনি এই ভাবে সভা করতে যাবেন? চুল আঁচড়াননি। কবিদের বুঝি চুল আঁচড়াতে নেই?
কবি বললেন, বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময় খুব সাজগোজ করতেন, তুমি তা দেখোনি। এখন আর… সময় মতন কিছুই খুঁজে পাই না, চিরুনি যে কোথায় লুকোয়।।
দেরাজ টেনে খুলে রাণু বলল, এই তো চিরুনি! চুপটি করে বসুন, আমি চুল আঁচড়ে দিচ্ছি।
মা যেমন শিশু সন্তানের গাল টিপে ধরে চুল আঁচড়ে দেন, সেই রকমই ভঙ্গিতে একটি বালিকা চুল আঁচড়ে দিচ্ছে একজন প্রবীণ মানুষের।
কবি সস্নেহে রাণুর পিঠে হাত রেখে বললেন, আমি বুঝি তোমার একটা খেলনা?
রাণু বলল, নড়বেন না। মাথায় কী সুন্দর চুল। দাড়িও ঠিক করে দিচ্ছি।
কবি বললেন, রাণু, তুমি চলে গেলে কে আমার চুল আঁচড়ে দেবে, কে আমায় জোর করে খাওয়াবে?
রাণুদের ফেরার সময় ঘনিয়ে এল।
ফণিভূষণের স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হয়েছে, ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছেন আরও কিছুদিন থেকে যাবার জন্য, কিন্তু তাঁকে তো কাজে যোগ দিতে হবে। কত আর ছুটি পাওয়া যাবে।
রাণু এখানেই থেকে যেতে চায়, সে এখানকার স্কুলে পড়বে। সেই জেদ ধরে সে এমন কান্নাকাটি শুরু করল যে তার বাবা-মা শেষ দিনটিতে তাকে ঘর থেকে বেরুতেই দিলেন না।
কবি নিজে এই পরিবারটিকে ট্রেনে তুলে দেবার জন্য এলেন বোলপুরে। ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে তাঁর মনে হল, না আসাই উচিত ছিল।
রাণু কিছুতেই ট্রেনে উঠবে না। সে ছটফটিয়ে মামার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে আর কাঁদছে। আর আকুল ভাবে কবির দিকে তাকিয়ে বলছে, আমি আপনার কাছে থাকব, আমার বাবাকে বলুন না—
কবিরও বুক মোচড়াচ্ছে, তিনি জোর করে মুখ ফিরিয়ে রইলেন।
প্রায় টেনে-হিঁচড়ে কামরায় তোলা হল রাণুকে। হুইল দিয়ে ছেড়ে দিল ট্রেন।
চলন্ত গাড়িতেও রাণুর কান্না কিছুতেই থামে না।
তার দুই দিদি কত ভাবে মন ভোলাবার চেষ্টা করল তার, রাণু কিছুতেই দেখবে না বাইরের দৃশ্য। এক একটা স্টেশনে ট্রেন থামছে, খাবার কেনা হচ্ছে, সে খেতেও চায় না।
মা এক সময় বললেন, বাবারে বাবাঃ, পারা যায় না এই জেদি মেয়েকে নিয়ে। গুরুদেব আমাদের আবার আসতে বলেছেন, আবার তো আসবি! এত কান্নার কী আছে?
রাণু ফোঁপানি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, আবার কবে আসব?
মা বললেন, আসব শিগগিরি… দেখা যাক যদি পুজোর ছুটিতে সম্ভব হয়।
ট্রেন বর্ধমান ছাড়াবার পর রাণু চিঠি লিখতে বসল।
…এখন গাড়ি চলছে। আমি খুব কাঁদছি। আপনার জন্য মন কেমন করছে। আপনার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে। আপনার নাওয়া হয়ে গেছে, কে চুল আঁচড়ে দেবে আপনাকে? …রোজ বিশ্রাম করবেন। আমার সন্ধেবেলা ভাল লাগবে না। আপনারও বোধহয় ভাল লাগবে না। …যদি কিছু সভা হয় তো বেশি জোরে লেকচার দেবেন না। আজ সন্ধেবেলা তো আমি আসব না, আপনি বোধহয় সভা করবেন। এবার যেদিন ছাতে বসবেন সেদিন নিশ্চয় আপনার আমার জন্য মন কেমন করবে। আপনি একলাটি চুপ করে বসে থাকবেন। খানিকক্ষণ আগে আমরা সব জলখাবার খেয়েছি। আপনিও বেশি করে দুধ খাবেন। …সন্ধে হয়ে এসেছে। এখন শান্তিনিকেতনের কথা মনে আসছে। এ সময়ই তো আমার সবচেয়ে বেশি আপনার জন্য মন কেমন করবে। কাশীতে গিয়েও করবে। …আমার গাড়িতে একটুও ভাল লাগছে না। আপনার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে।
কবিও বিষণ্ণ হয়ে রইলেন কয়েকটি দিন। এই এক মাস ধরে সরল সুন্দর বালিকাটি তাঁর মন লাবণ্যে ভরিয়ে দিয়েছিল। মাধুরীলতা চলে যাবার পরেই ওর সঙ্গে দেখা, এ এক আশ্চর্য যোগাযোগ। মাঝে মাঝেই মাধুরীলতা আর রাণু মিলেমিশে গেছে। রথী আর প্রতিমাও মেয়েটিকে ভালবেসে ফেলেছিল।
রাণুর চিঠি পাওয়া মাত্র কবি উত্তর লিখতে বসলেন।
রেলের পথে তোমার যে মন খারাপ হয়েছিল সেই পড়ে আমার বড় কষ্ট হল। তুমি মনে করো না আমি বুঝতে পারিনি। সেই বুধবারের দিন যখন তোমার গাড়ি চলছিল, আর আমি যখন চুপটি করে আমার কোণে, এবং সন্ধেবেলা ছাদে বসে ছিলুম তখন তোমার কষ্ট আমাকে বাজছিল। আমি মনে মনে কেবল এই কামনা করছিলুম যে, বাদলের ওপর যেমন ইন্দ্রধনু তৈরি হয়, তেমনি করে তোমার অশ্রুভরা কোমল হৃদয়ের উপরে স্বর্গের পবিত্র আলো পড়ক, সৌন্দর্যের ছটায় তোমার জীবনের এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্ত পূর্ণ হয়ে উঠুক।
আমি আমার জীবনকে তাঁরই কাছে উৎসর্গ করেছি–সেই উৎসর্গকে যে তিনি গ্রহণ করেছেন তাই মাঝে মাঝে তিনি আমাকে নানা ইশারায় জানিয়ে দেন—হঠাৎ তুমি তাঁরই দূত হয়ে আমার কাছে এসেছ। তোমার উপর আমার গভীর স্নেহ তাঁর সেই ইশারা। এই আমার পুরস্কার। এতে আমার কাজের দ্বিগুণ উৎসাহ হয়, আমার ক্লান্তি দূর হয়ে যায়, আমার মনের আকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।
নদীয়া জেলার টুঙ্গি গ্রামের এক টুলো পণ্ডিত ছিলেন বেণীমাধব অধিকারী। ছাত্র পড়ানো ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র চর্চা করে তিনি সময় কাটাতেন। পণ্ডিতের অন্তরালবর্তিনী স্ত্রীর ভূমিকা সারাদিন ধরে রান্নাবান্না করা ও নিয়মিত সন্তান প্রসব। সাতটি পুত্র কন্যার জন্ম দিয়ে পণ্ডিতজায়া একদিন নিঃশব্দে বিগত হলেন।
গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। গৃহিণী বিগত আর গৃহ রেখে লাভ কী, পণ্ডিত গ্রাম ছেড়ে বিবাগী হয়ে গেলেন। দণ্ড ধারণ করে হলেন সন্ন্যাসী, নতুন নাম নিলেন স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী।
সারা ভারত পর্যটন করে যোগানন্দ সরস্বতী এবসময় স্থিত হলেন কাশীতে। ততদিনে তাঁর কিছু ভক্ত ও শিষ্য জুটেছে, এক ধনী ভক্ত তাঁকে একটি বাড়ি ও সংলগ্ন জমি দান করে, সেখানে গড়ে ওঠে আশ্রম। ব্রহ্মকুণ্ডের সেই আশ্রমে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা ও শিব মূর্তির পূজা ও নিয়মিত সাধন ভজন হয়।
সন্ন্যাসী হলেও যোগানন্দ সরস্বতী পূর্ব জীবনের স্মৃতি একেবারে মুছে ফেলেনি। মাঝে মাঝে সন্তানদের খোঁজ খবর নেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে একজন খুবই কৃতবিদ্য হয়েছে, সংস্কৃত ও দর্শনের খ্যাতনামা অধ্যাপক, ক্রমে তিনি দিল্লির হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ হন।
একেবারে শেষ বয়েসে যোগানন্দ কোনও একজন সন্তানকে কাছে পাবার জন্য উতলা হয়ে ওঠেন। দিল্লি থেকে ডেকে পাঠান ফণিভূষণকে। পিতার অনুরোধ অমান্য করতে পারলেন না ফণিভূষণ, দিল্লির চাকরি ছেড়ে সপরিবারে চলে এলেন কাশীতে, কিন্তু আশ্রমে উঠলেন না। পাশেই একটা নতুন বাড়ি বানালেন। কাশী শহর বিদ্যা চর্চার একটি বৃহৎ কেন্দ্র, সেখানে অধ্যাপনার কাজ পেতে তাঁর কোনও অসুবিধে হল না।
ফণিভূষণের নিজের পরিবারটিও বেশ বড়। পাঁচটি ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, আশ্রিত আত্মীয়-পরিজন, দাস-দাসী, জমজমাট সংসার। এ পরিবারে গান বাজনার খুব চর্চা হয়, যদিও ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর ব্যাপারে অধ্যাপক মশাই কড়া নজর রাখতেন।
দুই পুত্র সন্তানের মৃত্যুর পর প্রথম কন্যা আশা, তাকে বেশ কিছুদিন ছেলে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, সবাই ডাকত নন্দদুলাল বলে, রজঃস্বলা হবার পর আশা ওই নাম শুনলেই রেগে যায়, ছেলেদের মতন জামা টামা ছুড়ে ফেলে দিয়েছে, এখন শাড়ি ছাড়া কিছু পরে না। পড়াশুনোয় দারুণ মেধাবিনী, এই বয়েসেই সে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকেছে। প্রায়ই সে বিরলে বসে ধ্যান করে।
দ্বিতীয় বোন শান্তি মুখচোরা, লাজুক, বাড়িতে তার অস্তিত্ব যেন টেরই পাওয়া যায় না। তার পরের বোন প্রীতির ডাক নাম রাণু, স্বভাবে সে আগের দুই বোনের সম্পূর্ণ বিপরীত, বাড়ির মধ্যে সে-ই সবচেয়ে দুরন্ত। সব সময় সে প্রাণচাঞ্চল্যে অস্থির, বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না, সে যেন সর্বক্ষণ বাড়ির সর্বত্র পরিদৃশ্যমান।
লক্ষ্মী মেয়ে ও সুবোধ বালকদের খুব প্রশংসা হয় বটে, কিন্তু দুরন্ত সন্তানটিকেই বয়স্করা বেশি পছন্দ করেন। তিন-চার বছর বয়েস থেকেই রাণু পাশের আশ্রমে গিয়েও হুটোপাটি করে, যোগানন্দ সরস্বতী এই নাতনিটির দিকে প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তাকে কোলে বসিয়ে আদর করতে চান। কিন্তু চুপ করে বসে থাকার পাত্রীই নয় রাণু, সে ছটফটিয়ে উঠে যায়। যোগানন্দ ছড়া কেটে বলেন, রাণু আমার মানিক। নাড়বও না, চাড়বও না, দেখব খানিক খানিক।
তান্য বোনদের সঙ্গে রাণু ইস্কুলে যায় বটে, কিন্তু ইস্কুলের পড়ার দিকে রাণুর মন নেই। সে পড়ে যত রাজ্যের গল্পের বই, বড়দের হোক, ছোটদের হোক, বাছ-বিচার নেই কিছু। এ বাড়িতে বই প্রচুর, কলকাতা থেকেও পত্র-পত্রিকা আসে। ছেলেমেয়েরা জন্ম থেকেই আছে দিল্লি ও বারাণুসীতে, স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম হিন্দি, তবু সবাই খুব ভাল বাংলা শিখেছে। মা সরযূবালা চন্দননগরের মেয়ে, হাতেখড়ির সময় থেকেই তিনি প্রতিটি সন্তানকে বাংলা ভাষায় দীক্ষা দিয়েছেন। প্রথমে তিনি ওদের রামায়ণ-মহাভারত আর রূপকথার গল্প পড়ে শোনান, তারপর বই ধরিয়ে দেন।
সাত বছর বয়েস থেকেই রাণুর গল্পের বই পড়ার নেশা। অনেক বই। পড়তে পড়তে সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে একজন লেখকের লেখাই বেশি পছন্দ করে ফেলল। যা পড়ে তাই-ই ভাল লাগে, তাঁর অনেক পদ্য সে মুখস্ত করে ফেলেছে, কিছু কিছু লেখা সবটা বুঝতে পারে না, তবু পড়তে ছাড়ে না। দশ বছর বয়েসেই সে এই রবিঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত।
রবিবাবু গানও লেখেন। মা রবিবাবুর বেশ কয়েকটা গান গাইতে পারেন, সেই সব গান শোনার সময় রাণুর দুরন্তপনা ঘুচে যায়, চুপটি করে শোনে। রাণু নিজে অবশ্য গাইতে পারে না, তার গানের গলা নেই। সেজন্য তার খুব দুঃখ হয়।
স্কুলের পড়ার বই বিশেষ ছোঁয় না রাণু, শুধু পরীক্ষার আগে তার রাত জেগে পড়াশুনো করার ধুম পড়ে যায়। একবার তার পরীক্ষার ফলাফল দেখে সবাই হতবাক। স্কুল থেকে প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়ি চলে এল রাণু। তার এক মামা কালীপ্রসন্ন প্রায়ই এসে থাকেন এখানে, তিনি ভাল বাংলাই বলতে পারেন না, কথা বলেন অনেক হিন্দি শব্দ মিশিয়ে। তার সামনে এসে রাণু রেজাল্টের কাগজটা নিয়ে লাফাতে লাফাতে বলতে লাগল, আমি হিন্দিতে ফাস্ট হয়েছি, আমি হিন্দিতে ফার্স্ট হয়েছি।
শুধু নিজের ইস্কুলে নয়, সারা উত্তর প্রদেশে হিন্দি পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে এই বাঙালি বালিকাটি।
কালীপ্রসন্ন খুশি হলেন অবশ্যই, তবু কৌতুক-ছলে হাত বাড়িয়ে বললেন, দেখি, দেখি, আউর সব সাবজেক্টমে গাড়ু মিলা, না কেয়া?
আশ্চর্যের ওপর আশ্চর্য, রাণু সব বিষয়েই ক্লাসে প্রথম হয়েছে। এ কি জাদুর ভেকি নাকি?
এরপর থেকে অভিভাবকরা ঠিক করেছেন, রাণুর ইস্কুলের পড়া নিয়ে আর খবরদারি করা হবে না। ও ওর নিজের নিয়মেই পড়ুক!
এই ক্ষুদ্র জীবনে রাণু তার প্রথম চিঠি লিখেছিল প্রিয় লেখক রবিবাবুকে। তিনি একবার উত্তর দিতেই শুরু হয়ে গেছে নিয়মিত পত্র বিনিময়। রাণু আর কারুকেই চিঠি লেখে না।
চিঠিতে এখন চলেছে নাম নির্বাচন নিয়ে বোঝাপড়া। সবই ওঁকে বলে গুরুদেব কিংবা রবিবাবু। গুরুদেব সম্বোধন রাণুর একেবারে পছন্দ হয় না, শুনলেই মনে হয় যেন ঠাকুর্দার মতন গেরুয়া পরা, মাথায় জটাওয়ালা বুড়ো। উনি তো সন্ন্যাসী নন, কবি। তাই রাণু এতদিন রবিবাবুই সম্বোধন করেছে, সেটা কবির পছন্দ নয়। উনি লিখেছেন, রবিবাবুর বদলে রবিদাদা কেমন?
ওই নামেও দু’একজনকে ডাকতে শুনেছে রাণু। এমন নাম চাই, যা হবে রাণুর নিজস্ব, ওই নামে আর কেউ ডাকবে না।
কিন্তু রবি নামটা যে কবির খুব পছন্দ। এক যে ছিল রবি, সে শুধু এক কবি। বদলাতে হলেও এমন নাম দিতে হবে, যার অর্থ হবে রবিই।
রবি মানে তো সূর্য। সূর্যদাদা? এ নামে ডাকলেই একদম অচেনা হয়ে যাবেন মানুষটি। মার্তণ্ড? ধুৎ! শুনলেই মনে হয় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। দিবাকর? ওই নামে কাশীতে একজন চেনা মানুষ আছে, মোটেই সুবিধের লোক নয়।।
কবি নিজেই আর একটা নামের প্রস্তাব দিলেন। খুব কম বয়েসে তিনি ভানু সিংহ ছদ্ম নামে কিছু কবিতা ও গান লিখেছিলেন, তারপর আর অনেকদিন সে নাম কেউ মনে রাখেনি। ভানুদাদা কেমন হয়, ও নামে আর কেউ ডাকবে না।
রাণুর খুব পছন্দ হয়ে গেল।
ভানুর সঙ্গে রাণু নামটারও চমৎকার মিল। অন্য কেউ ডাকতে চাইলেও বলা হবে, তোমাদের নামের সঙ্গে মেলাও আগে। কাদম্বিনী কিংবা জগদম্বারা পারবে? এমনকী সীতা, শান্তার সঙ্গেও মিলবে না।
ভানুদাদা শুধু একলা রাণুর।
আর যিনি গুরুদেব, কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি অন্য সকলের হোন গে যান!
সেবারে কলকাতায় গিয়ে প্রথম দেখা হল, তারপর এক মাস শান্তিনিকেতনে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। তারপর থেকেই রাণুর মনে হয়, পৃথিবীতে তার এত আপন মানুষ আর কেউ নেই।
কী অপরূপ সুন্দর সেই মানুষটি। দীর্ঘকায়, শক্তিমান পুরুষ, অথচ চক্ষু দুটি ভারী কোমল, মাথায় অনেক চুল, মুখ ভর্তি কাঁচা পাকা দাড়ি, অথচ যখন হাসেন তখন মনে হয়, ওঁর শরীরে বয়েসের কোনও ছাপই পড়েনি। ভরাট, সুরেলা কণ্ঠস্বর, সব সময় মজা করে কথা বলেন। এ মানুষটার শরীরে বুঝি একটুও রাগ নেই।
অবশ্য উনি যখন অন্য মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন, রাণু তো অনেকবার পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছে ও শুনেছে। তখন উনি গম্ভীর হতে পারেন, শক্ত কথা বলেন, অন্যদের বকুনিও দেন। আবার শুধু রাণুর সামনে একেবারে বদলে যান। যেন একেবারে মনের মানুষ। রাণু ওঁর লেখা থামিয়ে দিলেও বিরক্ত হন না। একদিন বলেছিলেন, তোমাকে দেখেই তো আমার নতুন গান মনে আসছে।
আহা রে, ওঁর মেয়ে মাধুরীলতা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল! রাণু তাকে দেখতে পেল না। এক একসময় কবি রাণুর হাত ধরে বলতেন মাধুরীলতার কথা। তখনও তাঁর চোখ ছলছল করেনি, শুধু দৃষ্টি যেন চলে যেত অনেক দূরে।
শান্তিনিকেতন ছেড়ে আসতে রাণুর খুবই কষ্ট হয়েছিল। এখন অনেকটা সহ্য হয়ে এসেছে, মা-বাবার কথাও তো মানতে হবে। মা বলেছেন, আবার শান্তিনিকেতনে যাওয়া হবে শিগগিরই।
দিন যায়, দিন যায়। সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধে আর রাত্রি নিয়ে এক একটা লম্বা লম্বা দিন। সানাইয়ের সুরে ভোর হয়। সেতারে ভৈরবী ও আশাবরী রাগিণীর মতন গড়িয়ে যায় সকাল, তবলার বোলের মতন দুপুর, বেহালার ছড়ে পূরবীতে বিকেলের শেষে সূর্যাস্ত হয় গঙ্গায়, তারপর অন্ধকারে স্বল্প আলোকিত এক একটা বজরায় শোনা যায় নূপুরধ্বনি আর গান, সিন্ধু বারোয়াঁর উদাস সুরের মতন নেমে আসে ঘুম।
বর্ষা কাল পেরিয়ে শরৎ এল। পুজোর ছুটিতেও শান্তিনিকেতনে যাওয়া হল না, বাবা খানিকটা সুস্থ হয়ে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। রাণুর অভিমান হয়। আগে কাশী তার এত ভাল লাগত, এখন শান্তিনিকেতনই সর্বক্ষণ মন টানে।
একদিন আশ্রম বাড়ির ইদারার কাছে কোথা থেকে একটা ময়ুর উড়ে এসে বসেছে। খবর পেয়েই সকালবেলা পড়ার বই ফেলে রাণু এক ছুটে গেল দেখতে। সারা শরীরে অজস্র রঙের বাহার নিয়ে ময়ূরটি মাথা তুলে বসে আছে দৃপ্ত ভঙ্গিতে।
অত সুন্দর দেখতে হলেই বা, ছোট ছেলেমেয়েদের ময়ূরের কাছে যেতে দেওয়া হয় না। ওরা নাকি চোখ খুবলে নেয়। রাণুর ভয় ডর নেই, কে তাকে বাধা দেবে! সে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়।
তার মনে পড়ল, শান্তিনিকেতনে দুটো ময়ূর আসার কথা ছিল। এতদিনে কি এসে গেছে? কবি কি নিজের হাতে তাদের খাওয়ান?
কথা নেই বার্তা নেই, ময়ূরটা যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনই হঠাৎ আবাব উড়ান দিয়ে চলে গেল।
যেখানে ময়ূরটি বসে ছিল, এখন আর সেখানে নেই, তবু যেন আছে। দেখতে পাচ্ছে রাণু। সে একদৃষ্টিতে সেই শূন্যতার মধ্যে একটি ময়ূর সৃষ্টি করে তাকিয়ে রইল সেদিকে।
আর এক সন্ধেবেলা রাণু পড়তে বসেছে দিদিদের সঙ্গে। সবে বইতে শুরু করেছে শীতের বাতাস। মাঝে মাঝেই রাণুর মন উতলা হয়ে যায়। সে ভাববার চেষ্টা করে, শীতকালে শান্তিনিকেতন কেমন দেখায়? তখন কি পাতা ঝরে যায় সব গাছের? জল থাকে কোপাই নদীতে? ছাত্ররা কি শীত কাটাবার জন্য সন্ধের সময় আগুন জ্বালে?
কে যেন কড়া নাড়ছে সদর দরজায়।
সন্ধের সময় ফণিভূষণের সঙ্গে কাশীর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দেখা করতে আসেন। বৈঠকখানা ঘরে উচ্চাঙ্গের কথাবার্তা হয়। এক একদিন গান বাজনার আসর বসে পেছন দিকের দালানে।
আজকের আগন্তুকটি অপরিচিত। ফণিভূষণ তার সঙ্গে কথা বলছেন। পাশের ঘর থেকে একটু একটু শুনতে পাচ্ছে রাণু।
অপরিচিত ব্যক্তিটির নাম ভীমরাও শাস্ত্রী। তিনি মহারাষ্ট্রের লোক, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছেন। নিজস্ব একটি কাজে এসেছেন বারাণুসীতে, আসবার সময় গুরুদেব এই ঠিকানা দিয়ে তাঁকে বলেছেন, রাণু নামে একটি এ বাড়ির মেয়ে কেমন আছে, একবার খবর নিয়ে আসতে।
শান্তিনিকেতন শব্দটি কানে যাওয়া মাত্র দৌড়ে চলে এল রাণু।
ফণিভূষণ মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে সহাস্যে বললেন, এই আমার মেয়ে রাণু। রবিবাবুকে বলবেন, সে দিব্যি আছে, তরতরিয়ে বড় হচ্ছে। রবিবাবুর নামে একেবারে পাগল!
ভীমরাও শাস্ত্রীকে খাতির করে ভেতরে বসানো হল। শান্তিনিকেতনে গুরুদেব এই পরিবারটিকে কত যত্ন করেছেন, এখন তাঁর দৃতকে আপ্যায়ন না করে ছাড়া হবে কেন? তাঁকে দেওয়া হল মালাই, জিলিপি, নিমকি, গজা। ভীমরাও ভোজনরসিক, এ সবে তাঁর আপত্তি নেই।
তিনি একজন গায়ক, গান শোনাবেন না?
বসে গেল গানের আসর। ভীমরাও খেয়াল-তরানায় বিশেষজ্ঞ। তবে শান্তিনিকেতনে দিনুবাবুর কাছ থেকে তিনি কিছু কিছু গুরুদেবের গানও কণ্ঠে তুলেছেন, শোনালেন সেগুলিও। রাণুকে বললেন, এইটা গুরুদেবের নতুন গান : ওহে সুন্দর, মরি-মরি–
তিন চারদিনের গানের আসরে শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া যেন অনেকটা বইতে লাগল ব্ৰহ্মকুণ্ডে।
শেষদিনে রাণু ভীমরাওকে বলল, আপনার হাত দুটো দেখি।
বিস্মিত ভীমরাও-এর বাড়ানো দু হাত জড়িয়ে ধরে রাণু জিজ্ঞেস করল, শান্তিনিকেতনে গিয়ে আপনি কবিকে প্রণাম করবেন তো?
ভীমরাও বলল, জরুর। গুরুদেবের চরণ স্পর্শ করনে সে মেরা তনুমন পবিত্র হো যাতা!
রাণু বলল, এই যে আমি আপনার হাত ধরলাম, তারপর আপনি এই হাতে কবিকে ছোঁবেন, তাতে আমারও একটু ছোঁয়া হবে। রেলে যাবার সময় কিন্তু আপনি আর কারুকে ছোঁবেন না, শান্তিনিকেতনে পৌঁছেও না, প্রথমেই কবিকে–
সরবালা হাসতে হাসতে বললেন, দেখেছেন তো, এ মেয়েটা সত্যিই পাগল!
‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকার সম্পাদক জলধর সেন এক সাহিত্যিক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন শান্তিনিকেতনে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকার লেখক নন, তিনি ‘প্রবাসী’র ও ‘সবুজপত্রে’র। জলধর সেন তাঁর কাছে লেখা চাইতে আসেননি, এসেছেন অন্য কারণে। জলধর সেনের আদি নিবাস নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে, সেই অঞ্চলটি ঠাকুরদের জমিদারির অন্তর্গত। জলধর সেন ঠাকুরদের প্রজা, কয়েক বছরের খাজনা বাকি পড়েছে, তিনি এসেছেন জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে কিছুটা খাজনা মকুব করে দেবার আবেদন জানাবার জন্য।
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট সময়ের আগে জলধর সেন সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেখছেন বন্ধুটির সঙ্গে।
সকালের প্রার্থনা সভা সেরে রথী আসছে এদিকে, জলধর সেনকে দেখে চিনতে পেরে কথাবার্তা বলতে লাগল। কথার মাঝখানে জলধর তার পাশের শ্যামলা রঙের, মধ্যম আকৃতি, সাদামাটা চেহারার ব্যক্তিটিকে দেখিয়ে বললেন, এঁকে চেনেন? ইনি নভেলিস্ট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই।
রথী চমকিত হয়ে বলল, বিলক্ষণ! ওঁর নাম কে না শুনেছে। উনি সুবিখ্যাত লেখক।
নমস্কার বিনিময়ের পর রথী জিজ্ঞেস করল, আপনি এখানে এই প্রথম এলেন? কেমন লাগছে?
শরৎচন্দ্র বললেন, বেশ মনোরম পরিবেশ। তবে শুনেছিলাম, এখানে একটা ইস্কুল আছে। সেটা তো কোথাও দেখতে পেলাম না।
রথী মৃদু হাস্যে চারপাশের গাছগুলির দিকে হাত দেখিয়ে বলল, এই তো ইস্কুল।
শরৎচন্দ্র ঠিক বুঝতে না পেরে ভুরু কুঞ্চিত করলেন।
রথী আবার বলল, এইসব গাছতলাতেই ইস্কুল বসে। আমিও এখানে পড়েছি। বাবামশাই এখানেই ক্লাস নেন।
জলধর জিজ্ঞেস করলেন, বৃষ্টির সময় কী করে ক্লাস হয়?
রথীর বদলে শরৎচন্দ্রই উত্তর দিলেন, রেইনি ডে, ছুটি হয়ে যায়। বাল্যকালে এরকম ইস্কুল পেলে আমিও পড়তাম!
রথী বলল, আপনার বয়েসী অনেকেই কিন্তু বাবামশাইয়ের ক্লাসে এসে বসেন।
শরৎচন্দ্র বললেন, সে ভাগ্য কি আর আমার হবে।
রথী ওঁদের দুজনকে নিয়ে গেল পিতৃ সন্নিধানে।
কবি ভোর থেকেই খুব ব্যস্ত। উপাসনার সময় বক্তৃতা ও গান গাইতে হয়েছে। তারপর প্রাতরাশ সারার আগেই ঘিরে বসেছে অনেকজন, চলছে নানা রকম কাজের কথা।
শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর হাস্য পরিহাসেরও সময় নেই। কুশল বিনিময়ের পর তিনি জলধর সেনকে বেশি কথার সুযোগ দিলেন না। বিষয়টি শোনা মাত্র তিনি শুধু আংশিক খাজনা নয়, পুরো খাজনাই মকুব করে দিলেন। তারপর রথীকে বললেন, তুই এঁদের দেখাশুনো কর, যেন আতিথ্যের কোনও ত্রুটি না হয়। শরৎ, কিছু মনে কোরো না, আমি নিজে বেশি সময় দিতে পারছি না–
শরৎচন্দ্র আজ্ঞে না না বলে প্রণাম করে উঠে গেলেন।
কবির বিশেষ ব্যস্ততার কারণ, ৭ই পৌষের মেলা শুরু হয়ে গেছে, আগামিকাল আছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। তার ব্যবস্থাদি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।
প্রাচীন আর্যদের আদলে তিনি এই শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেছিলেন যৌবনকালে। তারপর এতগুলি বছরের মধ্যে তার চিন্তা ও আদর্শের অনেক ব্যাপ্তি ঘটেছে। শুধু বাংলার নয়, শুধু ভারতের নয়, সমস্ত বিশ্বের জ্ঞান বিনিময়ের কেন্দ্র গড়ে তুলতে চান এখানে। যে-জ্ঞান সব রকম ধর্মবিশ্বাসেরও উর্ধ্বে। সেই জন্য আগামিকাল যে প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন হবে, তার নাম দিয়েছেন বিশ্বভারতী।
শুধু তাই-ই নয়। উন্নত ধরনের কৃষি, গোপালন ইত্যাদি শিক্ষা দেবার জন্যও আর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার কথা চিন্তা করছেন। গ্রাম বাংলায় চাষবাস ও পশু পালনের উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি হবে কী করে?
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেই তো হল না, সেসব চালাবার মতন রসদও চাই। এত টাকা আসবে কোথা থেকে? দক্ষিণ ভারত থেকে আমন্ত্রণ এসেছে, চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন, সভা ও কলেজে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে হবে। দলবল সমেত রাহা খরচ ও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের জন্য বেশ কিছু আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে, সুতরাং যাওয়া দরকার। তদুপরি অসুস্থ শরীর নিয়েও এই কবির ভ্রমণে ক্লান্তি নেই।
আমন্ত্রণকারীদের মধ্যে আছেন স্বয়ং মহীশূরের রাজা, তাঁর বসন্ত মহলে সংবর্ধনা ও আতিথ্য দিতে চেয়েছেন। বেশি উদ্যোগ নিয়েছেন মহারাজের রাজস্ব সচিব জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ নামে একজন অধ্যাপক কবির বিশেষ ভক্ত, তিনিও খুব আগ্রহী, এত সব আহ্বান উপেক্ষা করা যায় না।
প্রায় সওয়া দুমাস ধরে তিনি পরিভ্রমণ করলেন দাক্ষিণাত্যের বহু স্থানে, মাঝখানে ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেও বক্তৃতায় কসুর হল না। কলকাতায় যখন ফিরলেন, রীতিমতন গরম পড়ে গেছে, এখানেও সভা-সমিতির বিরাম নেই। তার মধ্যেই মাঝে মাঝে মনটা অস্থির হয়ে ওঠে। একটা অভাববোধ, একটা শূন্যতা কিছুতেই মেটে। বিখ্যাত ও অতি ব্যস্ত মানুষটির মনের মধ্যে যে একটি স্নেহকাতর, কাঙাল রয়েছে, সে আর কে বুঝবে? শুধু কাজ আর কাজ, এতে যে কাব্য স্রোতও শুকিয়ে যাবার উপক্রম।
রাণুরা এ বছর আর এল না।
ওকে দেখার জন্য কবি মাঝেমাঝে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন খুবই। কেন? ওই সরলা বালিকাটির সঙ্গে সময় কাটাতে গিয়ে তিনি নিজের বয়েস ভুলে যেতে পারেন। হালকা কৌতুকে মন পরিশ্রুত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথকে সবাই ভক্তি শ্রদ্ধা করে, ভানুর কথা এখন আর কেউ মনে রাখেনি। এই মেয়েটির সান্নিধ্যে, এমনকী চিঠিপত্রেও তিনি ভানুকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন। রাণু যখন তখন ঝুপ করে কোলে বসে পড়ে। গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে, চুল আঁচড়াওনি কেন বলে বকুনি দেয়, এমনটি তো আর কেউ নেই।
অনেককাল আগে ইন্দিরা ছিল এমনই, নিয়মিত দেখা না করলে কিংবা চিঠি লিখতে দেরি করলে সে কত অভিমান করত। তার জন্য একবার বিলেত থেকেও ফিরে এসেছিলেন তাড়াতাড়ি। ইন্দিরার সঙ্গে সে সম্পর্ক আর নেই, দেখা হয় অবশ্য, কিন্তু কথার সুর বদলে গেছে।
রাণু নিজে আসতে পারেনি, তাই কবিকে কাশীতে যাবার জন্য প্রতি চিঠিতে অনুরোধ করে। সে মনে করে, কবির কাজগুলির তেমন গুরুত্ব নেই, কাজ থেকে ছুটি নেওয়াটাই আসল। হয়তো তার মনে করাটাই ঠিক।
শুধু একটি বালিকা ডাক পাঠিয়েছে বলেই তো কাশী যাওয়া যায়, একটা উপলক্ষ চাই। এমনি এমনি যেতে গেলে অনেককে কৈফিয়ত দিতে হবে।
বারাণুসী থেকে আমন্ত্রণ এসে গেল, বক্তৃতা দিতে হবে সেখানকার সাহিত্য পরিষদে।
সদ্য দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরেছেন ক্লান্ত হয়ে, ইনফ্লুয়েঞ্জার জের এখনও চলছে, এর মধ্যেই আবার কাশী যাওয়া কি ঠিক হবে? রথী, প্রতিমা এবং আরও অনেকের একেবারেই ইচ্ছে নয়। সাহিত্য পরিষদের বক্তৃতা তো কয়েক মাস পরেও হতে পারে। কিন্তু কবি যাবেনই যাবেন। কেন তার এত আগ্রহ তা আর কেউ বুঝবে না।।
সবাই নানা রকম কাজ নিয়ে ঘুমিয়ে আছে।
শান্তিনিকেতন নিয়ে নিত্য নতুন সমস্যা। কোন শিক্ষা ঠিক এখানকার আদর্শ মেনে চলছেন না, কোন বিষয়ের জন্য নিয়োগ করতে হবে নতুন শিক্ষক, তা সবই দেখতে হয় কবিকে।
ছাত্রাবাসের ছাদ থেকে বৃষ্টির জল পড়লেও কবির কাছেই নালিশ আসে, তাঁকেই সুরাহা করতে হয়। প্রতিটি ছাত্র ভর্তির ব্যাপারেও তাঁর মতামত লাগে।
ওদিকে প্রমথ প্রায়ই আসে জমিদারির আদায় পত্তর নিয়ে আলোচনা করতে। অনেক দলিল-দস্তাবেজে কবির স্বাক্ষর দরকার।
কবি সে সব কাজ সেরে নিচ্ছেন দ্রুত, মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যেন দেখতে পাচ্ছেন কাশীর গঙ্গার দৃশ্য। অপরাহের স্তিমিত আলোয় নদীর ওপর দুলছে বজরাগুলো…ব্রহ্মকুণ্ডের গলির মধ্যে একটা বাড়ি, সে বাড়িতে থাকবার জন্য একটি বালিকা কতবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছে, তার বাবা-মাও খুশি হবেন… সেখানে কোনও কাজের কথা নয়, শুধু বিশ্রম্ভালাপ, শুধু কৌতুক। এ রকম কিছু লঘু সময় এখন কবির বিশেষ প্রয়োজন।
অনেক কাজ অসমাপ্ত রেখে কবি ট্রেনে চেপে বসলেন।
আগে থেকেই খবর রটে গিয়েছিল, বারাণুসী স্টেশন একেবারে লোকে লোকারণ্য। কবিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য অনেকে মালা ও পুষ্পস্তবক এনেছে। প্ল্যাটফর্ম প্রায় সবটাই বাঙালি মুখে ভর্তি, শোনা যাচ্ছে ওই ভাষায় জোরে কথাবার্তা। কলরব মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গন একেই বলে। ট্রেনের দরজার কাছে কবি কয়েক মুহূর্ত থমকে দাড়িয়ে রইলেন।
ফুল বর্ষণ ও প্রণামের ধুম পড়ে গেল। কর্তা ব্যক্তিগোছের কয়েকজন কবিকে ঘিরে রেখে ভিড় ঠেলে এগোবার চেষ্টা করলেন, কবি ব্যাকুল ভাবে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুঁজতে লাগলেন একজনকে। কথা ছিল, রাণু এসে তাকে নিয়ে যাবে স্টেশন থেকে। কোথায় রাণু? এত জনতার মধ্যে একটি ছোট মেয়েকে খুঁজে বার করা অসম্ভব।
স্টেশনের বাইরে এনে কবিকে বসানো হল একটি মোটর গাড়িতে। কর্তাব্যক্তিরা জানালেন, তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে কাশী নরেশের অতিথিভবন নদের প্যালেসে। কিন্তু ব্ৰহ্মকুণ্ডের গলির এক বাড়িতে এক বালিকা তার জন্য আসন পেতে রেখেছে, কবি যে সেখানেই থাকবেন ভেবে এসেছেন! সে কথা আর বলাই হল না। রাজ-আবাস প্রত্যাখ্যান করার যুক্তি তিনি কী দেখাবেন?
বিশাল প্রাসাদ, সুন্দর বাগান, এর মধ্যেই অজস্র দর্শনার্থী সেখানে অপেক্ষা করে বসে আছে।
কর্তাব্যক্তিরা জানালেন, কোথায় কোথায় তাঁর সংবর্ধনা ও বক্তৃতা সভার কর্মসূচি নির্ধারিত হয়েছে। পরপর কয়েকদিন একটু সময়েরও ফাঁক নেই।
বাঙালিদের আয়োজিত সংবর্ধনা সভাগুলিকে কবি বেশ ভয় পান। প্রশস্তি জানাবার ছলে বেশ কয়েকজন হোমরা-চোমরা লম্বা লম্বা বক্তৃতা ফেঁদে বসে, তাতে আশ কথা পাশ কথা, স্থানীয় সমস্যা, এমনকী পয়ঃপ্রণালীর জল নিষ্কাশনের অব্যবস্থার কথাও বাদ যায় না। কয়েকজন দীর্ঘ কবিতা শোনায়। এমনকী এই উপলক্ষে দু’একজন গানও লিখে ফেলে, স্বসুরারোপিত সেই গান যেন থামতেই চায় না। লঙ্গরখানার খিচুড়িতে যেমন চাল ও ডাল পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখে, এই গানেও সেরকম কথা ও সুরের মধ্যে অনেকখানি দূরত্ব।
সাহিত্য পরিষদের সভায় ঠিক সেই রকমই হল। কবি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে, হাসি হাসি মুখে সব শুনে গেলেন। বাল্যকাল থেকে এরকমই সহবতের শিক্ষা পেয়েছেন, নিজের অপছন্দের কথা কিছুতেই বলতে পারেন না মুখ ফুটে।
রাণুরা দেখা করতে আসবে না?
পরদিন বিকেলে কবি আর একটি সভায় যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন, নদেশ্বর প্যালেসের সামনে একটি ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল। রাণুরা চার বোন, এক পিসি এসেছে মা বাবার সঙ্গে।
কর্মকর্তারা কবিকে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা কবছেন, এখন কথা বলার সময় কোথায়?
রাণু যেন এর মধ্যে আর একটু লম্বা হয়েছে, একটু রোগা দেখাচ্ছে, তার মুখমণ্ডলের মধ্যে প্রধান তার দুটি আয়ত চক্ষু, সেই চক্ষু ভরা অভিমান।
ফণিভূষণ ও সরযূবালার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কবি এবার জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ, রাণু?
রাণু কোনও শব্দ না করে শুধু ঘাড় হেলাল।
সভার সময় বয়ে যাচ্ছে, আর দেরি করা যায় না, কবি ফণিভূষণকে বললেন, আপনারা কাল আর একবার আসুন। কোনও গল্পই হল না। কাল বিকেলে আমি কোথাও যাব না।
ফণিভূষণ বললেন, আমাদের বাড়ি এখান থেকে অনেকটা দূর। ভেবেছিলাম আপনাকে নিয়ে যাব, আমাদের সকলেরই খুব ইচ্ছে, আপনি যদি একবার আমাদের গৃহে পায়ের ধুলো দেন।
কবি বললেন, সেটা তো এখন সম্ভব হচ্ছে না। কাল বিকেলে আপনারা সবাই আবার আসুন, অবশ্যই আসবেন।
পরদিন ফণিভূষণ ও সরযূবালা আসতে পারলেন না, পিসিমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন চার বোনকে।
আজ কবি বাতিল করে দিয়েছেন একটি সভা, অন্য দর্শনার্থীদের বিদায় করে দিয়েছেন সংক্ষেপে। এদের জন্য তিনি আনিয়ে রেখেছেন কফি-আইসক্রিম। বেনারসের লোকেরা যখন তখন মালাই রাবড়ি খায়, কিন্তু এই বস্তুটি অভিনব।
অন্য বোনেরা তবু দু’একটা কথা বলছে, রাণু একেবারে নীরব।
পিসিমা জিজ্ঞেস করলেন, গুরুদেব রাজবাড়িতে অনেক ভাল ভাল রান্না হয় জানি। কিন্তু এখানে কি আপনাকে ভাত খেতে দেয়?
কবি বললেন, না। তবে আমি রুটিও বেশ পছন্দ করি।
পিসিমা বললেন, একদিন আমাদের বাড়িতে গিয়ে আমার হাতের রান্না খাবেন না?
কবি বললেন, খুবই তো ইচ্ছে আছে।
রাণু সেখান থেকে উঠে গিয়ে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়াল।
কবিও একটু পরে সেখানে গিয়ে মৃদু স্বরে বললেন, তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ, না!
রাণু সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে বলল, করবই তো! আপনি কথা রাখেননি। আপনি আমাদের বাড়ি গিয়ে থাকলেন না। আমাদের ছোট বাড়ি, এই রাজপ্রাসাদই আপনার বেশি পছন্দ।
কবি বললেন, তা মোটেই না। রাজবাড়িতে আমি স্বস্তি বোধ করি। দেখোনি, শান্তিনিকেতনে আমি মাটির বাড়িতে থাকি। রাজাদের নিয়ে মুশকিল এই, তারা যখন তখন কবিদের ধরে আনতে চায়। সেই বিক্রমাদিত্যের আমল থেকে এটা শুরু হয়েছে। তাছাড়া উদ্যোক্তারা বললেন, কয়েকটি জায়গায় বক্তৃতা দিতে হবে। এখান থেকেই যাওয়া আসার সুবিধে।
রাণু ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, আপনি অত বক্তৃতা দেন কেন? না দিলেই বা ক্ষতি কী?
কবি ছদ্ম বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, সে কী! আমি তো বক্তৃতা দিচ্ছি তোমাকেই খুশি করার জন্য। গলায় জরির চাদর ঝুলিয়ে, সেজে গুজে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাঙা গলা আরও ভেঙে বক্তৃতা শক্তির চমৎকারিত্বে কাশীবাসীদের মুগ্ধ করে দিলেন, সবাই এটুকু অন্তত বুঝল যে লোকটি নিতান্ত হেলাফেলার নয়, মুখচোরা নয়, এতে ভানুদাদার রাণু খুশি হবে না? রাণু মুখ তুলে শুধু বলল, ভানুদাদা।
নিরিবিলিতে কথা বলার কি উপায় আছে। এর মধ্যে কারা যেন কিছু জরুরি বার্তা নিয়ে উপস্থিত হল।
তাদের একটু অপেক্ষা করতে বলে কবি পাশের ঘর থেকে একটি অতি সুদৃশ্য, রুপোর কাজ করা, হাতির দাত বাঁধানো এসরাজ এনে বললেন, এটা তোমার জন্য।
রাণু নিতে ইতস্তত করছে দেখে তিনি বললেন, তোমার অন্য বোনদের জন্যও কিছু কিছু উপহার এনেছি। আমার খুব ইচ্ছে, তুমি এসরাজ বাজানো শিখবে, তারপর আমার গানের সঙ্গে বাজাবে।
রাণু এবারে এসরাজটি নিয়ে গালে ছোঁয়াল।
সে আগে থেকেই এসরাজ বাজানো শিখেছে। লেখাপড়া শেখবার সঙ্গে সঙ্গে ফণিভূষণ মেয়েদের গান-বাজনা শেখাবারও ব্যবস্থা করেছেন। দু’জন মুসলমান ওস্তাদ নিয়মিত তালিম দিয়ে যান। বড় বোন সেতার বাজায়, অন্য দু’বোন গানের গলা সাধে, রাণুর গানের সুর ঠিক হয় না, কিন্তু এসরাজে সে এর মধ্যেই বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছে।
কবি তো তা জানতেন না, তবু কেন এসরাজই আনলেন রাণুর জন্য?
যে জার্মানিকে মনে করা হয়েছিল দুর্জয় শক্তিমান, সেই জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ, ফরাসি, ইতালিয়ান, বেলজিয়ান ও আমেরিকান বাহিনী একতাবদ্ধ হয়ে আক্রমণ চালালে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়ে গেল। এর মধ্যে জার্মানদের খাদ্য ও রসদে টান পড়েছে, শুরু হল পশ্চাৎ অপসরণ। কিছু দিনের মধ্যেই জার্মান সম্রাট কাইজার দেশ ছেড়ে পালিয়ে আশ্রয় নিলেন হল্যান্ডে।
রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের পর রাজতন্ত্র মুছে গেছে, জাররা নিহত হয়েছেন সবংশে, লেনিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গৃহযুদ্ধ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ট্রটস্কি গড়ে তুলেছেন লাল ফৌজ। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যও তছনছ হয়ে গেছে। গণ-অভ্যুত্থানে অষ্ট্রিয়ার সম্রাটকে বিদায় নিতে হয়, হাঙ্গেরি টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যেরও আর অস্তিত্ব রইল না, মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক গড়ে তুললেন প্রজাতন্ত্র। নিরপেক্ষ দেশ সুইজারল্যান্ডের জেনিভায় প্রতিষ্ঠিত হল রাষ্ট্রসঙ্ঘ।
প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর সারা পৃথিবী জুড়ে এরকম অভূতপূর্ব অদল বদল ঘটছে, কিন্তু পরাধীন ভারতের রাজশক্তির কোনও লয়-ক্ষয় নেই।
যুদ্ধ চলাকালীন ভারতের সম্পদ ও সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নেবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল ইংরেজদের, তাই বারবার দেশীয় নেতাদের মিথ্যে আশ্বাসবাক্য ও টোপ ছুড়ে দিয়েছে তারা। যুদ্ধের পর সেই শাসকবর্গের নখ ও দাত আরও ধারালো হয়ে দেখা দিল।
যুদ্ধের সময় এক লক্ষ একট্টি হাজারের কিছু বেশি ভারতীয়কে নিযুক্ত করা হয়েছিল সেনাবাহিনীতে, তাদের মধ্যে এক লক্ষ সাড়ে একুশ হাজার সৈন্যকে পাঠানো হয় বিদেশের রণাঙ্গনে এবং এক লক্ষেরও বেশি ভারতীয় সৈন্য আর ফিরে আসেনি। আর ভারতের কত সম্পদ ব্যয়িত হয়েছে তার কোনও হিসেব নেই।
এই রক্তদান ও সম্পদের বিনিময়ে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া তো দূরের কথা, বরং দমন নিপীড়ন আরও কঠোর হল, নাগরিক অধিকার খর্ব করে পাশ হয়ে গেল রাওলাট আইন। ভারতের সর্বমান্য নেতা সশস্ত্র বিপ্লবপন্থী লেনিনের মতন কেউ নন, অহিংসপন্থী মোহনদাস গান্ধী।
যুদ্ধের সময় ইংরেজদের বিব্রত করতে না চেয়ে তাদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি নিয়েছিলেন গান্ধীজি, এবার বাধ্য হলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলন ঘোষণা করতে। ধর্মঘটের ডাক দিয়ে গান্ধীজি দেশবাসীর কাছে আবেদন জানালেন যে এই আন্দোলন যেন অহিংস ও শান্তিপূর্ণ হয়।
কিন্তু তা হল না। বিভিন্ন জায়গায় খণ্ড যুদ্ধ হল জনসাধারণ ও পুলিশের মধ্যে। শুধু গুজরাটেই জনতার আক্রমণে দুজন পুলিশ নিহত হলে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় আঠাশ জনের। জনতা ট্রেন অবরোধ, সরকারি সম্পত্তি আক্রমণ কিংবা টেলিগ্রাফের তার কেটে দিলে সরকারের পক্ষ থেকে গ্রামে গ্রামে মেশিনগানের গুলি ও বিমান থেকে বোমাবর্ষণও হতে লাগল।
এইসব হিংসাত্মক ঘটনায় খুবই ব্যথিত হলেন গান্ধীজি। দেশের মানুষ তাঁর নির্দেশ মানেনি বলে অনশনে বসলেন তিনদিনের জন্য।
জনসাধারণ সত্যাগ্রহের প্রকৃত মর্ম বোঝেনি। তাদের সঠিক শিক্ষাও দেওয়া হয়নি। তার আগেই আন্দোলন শুরু করা ভুল হয়েছে। বিভিন্ন জনসভায় তিনি বলতে লাগলেন, আপাতত আন্দোলন বন্ধ, কিন্তু দেশের মানুষ যদি নিষ্ঠার সঙ্গে, দৃঢ় চিত্তে, অহিংসার পথে সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত হয়, তবে তিনি আবার শুরু করবেন তিন মাস পরে।
এই সময় বম্বের গভর্নর ডেকে পাঠালেন গান্ধীজিকে। স্বয়ং বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের নির্দেশ তিনি জানিয়ে দিলেন চাঁচাছোলা ভাষায়। মিঃ গান্ধী যদি আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন, তা হলে এবারে দমন করা হবে আরও কঠোরভাবে। সামরিক আইন জারি করা হবে, দেশে রক্ত গঙ্গা বয়ে যাবে।
এর পরেও ঝুঁকি নিতে গান্ধীজির বিবেক সায় দিল না। কিছু সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে সারা দেশ থেকে সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে নিলেন সত্যাগ্রহ।
এর মধ্যে একটি সাঙ্ঘাতিক অকল্পনীয়, নিষ্ঠুর কাণ্ড ঘটে গেছে।
সংবাদপত্রের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, অনেক খবরই প্রকাশিত হয় না। দেশের কোথায় কী ঘটছে, তা জানার উপায় নেই। পঞ্জাবে সামরিক শাসন জারি আছে। সেখানকার একটি বীভৎস ঘটনার একটু একটু উড়ো খবর কানে আসছে। অ্যান্ড্রুজ সাহেব চরকি বাজির মতন সারা ভারত ঘুরে বেড়ান, তিনিও কিছু জেনে এসেছেন। বানোয়ারিলাল চৌধুরী নামে একজন শান্তিনিকেতনে এসে কবিকে শোনালেন জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক সংবাদ।
পঞ্জাবিরা যোচূজাতি। মহাযুদ্ধের সময় পঞ্জাবের গভর্নর মাইকেল ও ডায়ার এই রাজ্য থেকেই জোর জবরদস্তি করে বেশির ভাগ সৈন্য সংগ্রহ করেছে। তার মধ্যে অনেকেই প্রাণ দিয়েছে। সেই প্রাণদান কীসের জন্য? যুদ্ধ থেকে যারা ফিরে এসেছে, তারাও অবরুদ্ধ ক্রোধে ফুঁসছে, অসহযোগ আন্দোলন শুরু হতেই পঞ্জাবে নানা জায়গায় সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। যত প্রতিবাদ, তত অত্যাচার। সরকার মিলিটারি ডেকে অমৃতসর শহরের ভার দিয়েছে জেনারাল ডায়ার-এর হাতে। ডায়ার নিষিদ্ধ করেছে সবরকম সভা-সমিতি।
প্রতি বছরই তিরিশে চৈত্র অমৃতসর শহরে খুব বড় আকারের বৈশাখী উৎসব হয়। কাছাকাছি গ্রাম থেকে হাজার হাজার মানুষ আসে। এ বছরেও সে রকম গ্রামবাসীরা এসেছে উৎসবে যোগ দিতে, তারা নিষেধাজ্ঞার কথা জানেই না। প্রায় হাজার দশেক মানুষ সমবেত হয়েছে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামে একটি পার্কে, সেটি চতুর্দিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা, একটি মাত্র প্রবেশের রাস্তা। জেনারাল ডায়ার তার সেনাবাহিনী নিয়ে এসে সেই প্রবেশপথ আটকে দিল। সাধারণ মানুষকে ছত্রভঙ্গ হতে বলা হল না, কোনও সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হল না, জেনারাল ডায়ার বীরদর্পে হুকুম দিল গুলি চালাতে। অস্ত্রহীন, শান্ত, নিরীহ মানুষের দল, তাদের মধ্যে নারী-শিশু বৃদ্ধও আছে, গুলি খেয়ে মরতে লাগল পোকা-মাকড়ের মতন। শত শত নিহত ও আহতের আর্তনাদও ছাপিয়ে গেল গুলির শব্দ। রাস্তাটা সরু বলে মেশিনগান আনা যায়নি, বন্দুকের টোটা একসময় ফুরিয়ে গেল বলেই সকলকেই শেষ করা গেল না।
রবীন্দ্রনাথ হিংসাত্মক প্রতিরোধ পন্থা সমর্থন করেন না। গান্ধীজি যখন আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথকে একটি বিবৃতি দেবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাবধান করে লিখেছিলেন, এই ধরনের আন্দোলন হঠাৎ লাগামছাড়া হয়ে আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে, তাতে ক্ষতিই হবে বেশি।
তা বলে এত বড় অত্যাচার, এরকম একটা কুৎসিত ঘটনার প্রতিবাদ হবেনা? ইংরেজের এই বর্বরতার খবর বিশ্ববাসী জানবে না? গান্ধীজি নীরব কেন? কংগ্রেসের কোনও নেতাই বলছেন না কিছু।
রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত। কিছু একটা অবশ্যই করা দরকার। অ্যান্ড্রুজকে তিনি দিল্লিতে গান্ধীজির কাছে পাঠালেন একটা প্রস্তাব দিয়ে। গান্ধীজি রাজি থাকলে তিনিও দিল্লি চলে যাবেন। তারপর ওঁরা দুজনে একসঙ্গে পঞ্জাবে প্রবেশ করার চেষ্টা করবেন। পঞ্জাবে বাইরের লোকের প্রবেশ এখন নিষিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজিকে নিশ্চিত গ্রেফতার করা হবে, সে সংবাদ গোপন রাখা যাবে না, প্রচারিত হবে বিশ্বের সর্বত্র। এটাই হবে প্রতিবাদ।
অ্যান্ড্রুজ দিল্লি গিয়ে তখনই ফিরলেন না। খবরও পাঠাচ্ছেন না কিছু। কবি মনমরা হয়ে শুয়ে থাকেন, লিখতে ইচ্ছে করে না কিছু। প্রশান্ত মহলানবীশ কিংবা কালিদাস নাগ এলেই জিজ্ঞেস করেন, অ্যান্ড্রুজ বা গান্ধীজির কোনও খবর পেলে?
অ্যান্ড্রুজ ফিরলেন বেশ কয়েকদিন পর, ভগ্নদূতের মতন। তাঁর তখন এ কুল রাখি না ও কুল রাখি অবস্থা। রবীন্দ্রনাথকে তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতন মনে করেন, আবার তিনি গান্ধীজিরও বিশেষ অনুরাগী। আমতা আমতা করে জানালেন, গান্ধীজি কবির প্রস্তাবে রাজি হননি। সরকারের সঙ্গে এখন তিনি প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে যেতে চান না, এটা উপযুক্ত সময় নয়।
কবি অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। গান্ধীজি সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করলেন না। কবিকে শান্ত, নিঃশব্দ, সমাহিতের মতন এক এক সময় বসে থাকতে দেখেছে অনেকে, কিন্তু এ যেন নিস্তব্ধতার মধ্যেও রয়েছে চরম অস্থিরতা।
বিকেলের দিকে তিনি রথীকে বললেন, একটা ঠিকে গাড়ি ডাক তো!
কারুকে সঙ্গে নিলেন না। একাই চলে গেলেন ভবানীপুরে চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়িতে।
চিত্তরঞ্জন আপ্যায়ন করে বসালেন বটে, কিন্তু কথাবার্তা বললেন না বেশিক্ষণ। কবি প্রথমেই সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, পঞ্জাবের ঘটনায় বাঙালিরা কেউ প্রতিবাদ করবে না? তোমাদের মতন কংগ্রেসের নেতারাও মৌনী হয়ে থাকবে? একটা সভা ডাকো, আমি নিজে তার সভাপতি হতে রাজি আছি।
চিত্তরঞ্জন বললেন, নিশ্চয়ই ডাকব। আপনি সভাপতি হলে তো কোনও কথাই নেই। সবাই যোগ দেবে। আর কাকে বক্তা হিসেবে রাখা উচিত?
কবি বললেন, তা তোমরাই ঠিক করো।
চিত্তরঞ্জন বললেন, অবশ্য আপনি যখন বক্তৃতা দেবেন, তখন আর অন্য বক্তা রেখে কাজ কী? কাকেই বা ধরতে যাব। আপনিই আমাদের সবার হয়ে বলবেন।
কবি বললেন, বেশ তাই-ই হবে। কবে সভা ডাকবে, কোথায়, এখনি ঠিক করো। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে।
চিত্তরঞ্জন ইতস্তত করতে লাগলেন। অন্যান্য নেতাদের সঙ্গেও পরামর্শ করা দরকার। কে কী মতামত দেবে ঠিক নেই। সুরেন বাঁড়ুজ্যে নিশ্চিত বাগড়া দেবেন। বিপিন পাল, ফজলুল হক এঁরাও…। হুট করে কি মিটিং ডাকা যায়?
তিনি কবিকে বললেন, আপনিই সভাপতি ও একমাত্র বক্তা যখন, তখন মিটিংটা আপনার নামেই ডাকলে হয় না?
কবি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, একদৃষ্টিতে চিত্তরঞ্জনের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। চিত্তরঞ্জনও দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইছেন। কীসের ভয়? কিংবা এরই নাম রাজনীতি! অন্য সময় চরমপন্থী, এখন রক্ষণশীল।
আর বাক্যব্যয় না করে ফিরে এলেন জোড়াসাঁকোয়।
সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে বৈঠকখানা ঘরে প্রশান্তচন্দ্র আর কালিদাসদের দেখে বললেন, তোমরা এখন যাও। আজ আর আমাকে পাবে না।
কালিদাস বলল, কয়েকখানা নতুন গান লেখাবেন বলেছিলেন। কাল।
কবি নীরস গলায় বললেন, বললুম তো, আজ আর কিছু হবে না। এখন যেন কেউ আমাকে বিরক্ত না করে।
কালিদাস আর প্রশান্তচন্দ্র মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। কবি এমন ভাবে তো কথা বলেন না তাদের সঙ্গে। তারা গুটিগুটি প্রস্থান করল বাড়ির দিকে।
কিছুদিন ধরে কবির শরীর খারাপ চলছে, মাঝে মাঝেই জ্বর হয়। ডাক্তার নীলরতন সরকার এসে দেখে গেছেন। অসুস্থ হলেও কবি তো দিনের পর দিন বিষণ্ণ হয়ে থাকেন না। কিছু না কিছু লেখেন, গান শেখাতেও ক্লান্তি নেই। আজ হঠাৎ এ রকম রুক্ষ স্বরে কথা বললেন কেন? এই সব ভেবে ভেবে প্রশান্তচন্দ্রের সারা রাত ঘুমই এল না। বিছানায় ছটফট করে, ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। রাস্তায় টিমটিম করছে গ্যাসের আলো, এমনকী দুধের গোয়ালারাও এখনও বেরোয়নি।
জোড়াসাঁকোর বিশাল বাড়িটি ঊষালগ্নে অস্পষ্ট হয়ে আছে।
খাটিয়া পেতে দারোয়ানরা ঘুমোচ্ছে সামনের প্রাঙ্গণে। প্রশান্তচন্দ্র দেখল, দোতলায় একটি ঘরে শুধু আলো জ্বলছে। দারোয়ানদের জাগিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল, আলো-জ্বলা ঘরটির দরজা খোলা, সেদিকে পেছন ফিরে টেবিলে বসে লিখছেন কবি। প্রশান্তচন্দ্র দাঁড়িয়ে রইল নিঃশব্দে।
একটু পরে মুখ ফিরিয়ে প্রশান্তচন্দ্রকে দেখে কবি অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, এসেছ? বসো।
আবার লিখতে লাগলেন। লেখার সময় অন্য কারুর উপস্থিতি তিনি পছন্দ করেন না, প্রশান্তচন্দ্রের এখন কী করা উচিত বুঝতে পারছে না, অন্য ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করাই হয়তো উচিত, কিন্তু কবি যে বসতে বললেন!
খানিক পরেই কবি বলে উঠলেন, থাক, এই যথেষ্ট হয়েছে। নাও, প্রশান্ত পড়ে দেখো!
প্রশান্তচন্দ্র কাগজগুলি হাতে নিয়ে দেখল। সেটা একটা ইংরেজিতে লেখা চিঠি, ভারতের বড়লাটকে সম্বোধন করে লেখা।
ক্লান্ত ভাবে চেয়ারে মাথা হেলান দিলেন কবি। দু’চোখের কোণে কালি, কিন্তু ওষ্ঠে তৃপ্তির রেখা।
তিনি বললেন, সারা রাত বিছানায় যাইনি। সারা গা জ্বলছিল। পঞ্জাবের ঘটনার কেউ কোনও প্রতিবাদ করবে না, এ আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। গান্ধী আমার প্রস্তাবে রাজি হলেন না, চিত্তকে গিয়ে বললাম, কিছু একটা করো, সেও দেখি গা বাঁচিয়ে থাকতে চায়। আমাকেই যদি সব দায়িত্ব নিতে হয়, তা হলে আর সভা ডেকে লোক জড়ো করার দরকার কী, নিজের কথা লিখেই জানাব। ইংরেজ সরকার আমাকে খাতির করে নাইটহুড দিয়েছিল। যে-সরকার আমার দেশের মানুষের ওপর এমন নৃশংস অত্যাচার করে, সেই সরকারের দেওয়া খেতাবে আমার দরকার নেই। জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদে আমি নাইটহুড ফিরিয়ে দিচ্ছি।
এর মধ্যে ভোরের আলো পুরোপুরি ফুটেছে, নিভিয়ে দিতে হল ঘরের আলো।
স্বয়ং ব্রিটিশ সম্রাট প্রদত্ত খেতাব পরিত্যাগ করা রাজদ্রোহের প্রায় সমতুল্য। এ চিঠি প্রচারিত হলে সম্রাটকেই অপমান করা হবে। প্রশান্তচন্দ্র কম্পিত বক্ষে চিঠিখানি পড়তে লাগল। অনেক কাটাকুটি করে লেখা হয়েছে, কী জ্বলন্ত ভাষা, The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous content of humiliation, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of my country-men…
তখুনি ডেকে পাঠানো হল অ্যান্ড্রুজকে।
কবি বললেন, দেখো সাহেব, ঠিক আছে কি না।
অ্যান্ড্রুজ পড়তে পড়তে বললেন, হ্যাঁ, প্রতিবাদ হিসেবে এটা উচিত কাজই হয়েছে, কিন্তু, কিন্তু, গুরুদেব, ভাষা একটু নরম করে দিলে হয় না?
কবি এর উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে রইলেন অ্যান্ড্রুজের দিকে।
প্রায় কেঁপে উঠলেন অ্যান্ড্রুজ। কবির এমন হিমশীতল দৃষ্টি তিনি আগে কখনও দেখেননি। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, না, না, ঠিক আছে, এ ভাষা বদল করার দরকার নেই।
অ্যান্ড্রুজকে দায়িত্ব দেওয়া হল, চিঠিখানি বড়লাটকে তারবার্তা হিসেবে পাঠানোর। প্রশান্তচন্দ্র কয়েকখানা অনুলিপি করতে লাগল, রামানন্দবাবুকে ও অন্যান্য সংবাদপত্রে পাঠাতে হবে।
কবি উঠে গেলেন তিনতলায়। এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। এখন বিছানায় শুলেও বিগত রাত্রির ঘুম না-হওয়া পূরণ করা যাবে না, দিনের বেলা তিনি কিছুতেই ঘুমোতে পারেন না।
প্রকৃত বিশ্রাম হতে পারে বিশ্রম্ভালাপে। এখন ওইসব গুরুতর চিন্তা মন থেকে একেবারে সরিয়ে ফেলে যদি কৌতুক হাস্য-পরিহাস করা যেত! যদি কেউ তাঁর উত্তপ্ত মস্তিষ্কে হাত বুলিয়ে দিত।
সে রকম কেউ কাছে নেই।
চোখের সামনে ভেসে উঠল লাবণ্যময়ী এক কিশোরীর মুখ। রাণুর বাবা শান্তিনিকেতনে আসেননি, সপরিবারে বেড়াতে গেছেন আলমোড়া পাহাড়ে। এই সময়ে রাণুর সঙ্গে কথা বলতে পারলে তাঁর মন পরিশুদ্ধ হতে পারত।
বেশ কয়েকদিন চিঠি লেখা হয়নি রাণুকে। চিঠি লেখাও তো এক রকম কথা বলা। রাণুর দুটো চিঠি জমে গেছে, তাঁর পাহাড়ের ভ্রমণ বিবরণে ভরা!
কবি স্নান-প্রাতরাশের কথা ভুলে চিঠি লিখতে বসলেন:
তোমার চিঠিতে যে-রকম ঠাণ্ডা এবং মেঘলা দিনের বর্ণনা করেছ, তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তুমি তোমার ভানুদাদার এলাকার অনেক তফাতে চলে গেছ। বেশি না হোক, অন্তত দুতিন ডিগ্রির মতোও ঠাণ্ডা যদি ডাকযোগে এখানে পাঠাতে পারে তা হলে তোমাদেরও আরাম, আমাদেরও আরাম।…এখানে গরমের ঝাঁজে আকাশ ঝাপসা হয়ে আছে—কেমন যেন ঘোলা নীল—ঠিক যেন মূৰ্ছিত মানুষের ঘোলা চোখটার মতো।…যাই হোক, আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম করে সইতে পারি, কিন্তু মর্তের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পঞ্জাবে আছ, পঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধহয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজরা পুড়িয়ে দিলে। ভারতবর্ষে অনেক পাপ জমেছিল, তাই অনেক মার খেতে হচ্ছে। মানুষের অপমান ভারতবর্ষে অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। তাই কত শত বৎসর ধরে মানুষের কাছ থেকে ভারতবর্ষ এত অপমান সইছে, কিন্তু আজও শিক্ষা শেষ হয়নি। আমাদের অনেক ভাল হতে হবে, আমাদের প্রেম পৃথিবীর সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে, তবে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হবে।
চিঠিখানা সঙ্গে সঙ্গে লেফাফায় ভরে, ঠিকানা লিখে তক্ষুনি ভৃত্যকে ডেকে ডাকবাক্সে ফেলতে পাঠিয়ে দিলেন।
কিন্তু তৃপ্তি হল না। এ চিঠি যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, রাণুর ভানুদাদার নয়। শেষের দিকে বক্তৃতার ভাব এসে গেছে, রাণুর সঙ্গে কথা বলা তো হয়নি।
আবার একটা চিঠি লিখতে বসলেন:
মাঝে তোমার একটা চিঠির জবাব দিতে পারিনি। কলকাতায় এসেছি। কেন এসেছি হয়তো খবরের কাগজ থেকে ইতিমধ্যে কতকটা জানতে পারবে। তবু একটু খোলসা করে বলি। তোমার লেফাফায় তুমি যখন আমার ঠিকানা লেখ—তখন বরাবরই আমার সার পদবি বাদ দিয়ে লেখ! আমি ভাবলুম, ওই পদবিটা তোমার পছন্দ নয়। তাই কলকাতায় এসে বড়লাটকে চিঠি লিখেছি যে, আমার ওই ছার পদবিটা ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু চিঠিতে আসল কারণটা লিখিনি, বানিয়ে বানিয়ে অন্য কথা লিখেছি। আমি বলেছি, বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জমে উঠেছিল, তারই ভার আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে—সেই ভারের ওপরে আমার ওই উপাধির ভার আর বহন করতে পারছি নে, তাই ওটা মাথার ওপর থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। যাক এ সব কথা আর বলতে ইচ্ছে করে না—অথচ অন্য কথাও ভাবতে পারি নে। এত লোক এত অন্যায় দুঃখ পাচ্ছে যে, দূরে বসে বসে আরামে থাকতে লজ্জা হয়–তাদের দুঃখের অংশ যদি আমি নিতে পারি তা হলেও দুঃখ অনেকটা লাঘব হয়। ওই দেখ, আবার ফের ঘুরে ফিরে সেই একই কথা!
চিঠি শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। রেলগাড়ি চেপে এই চিঠি যাবে আলমোড়ায়, এক গাড়িতে তো হবে না, বদল করতে হবে, পোঁছোতে কদিন লাগবে কে জানে? তারপর ডাকপিওন যখন বিলি করতে ওদের দরজায় যাবে, তখন চিঠিখানা পড়ে রাণুর মুখের অবস্থা কী রকম হবে? বিশ্ব জানবে, কেন তিনি নাইটহুড পরিত্যাগ করেছেন। আর রাণু জানবে, শুধু তার জন্যই তার ভানুদাদা স্যার পদবিটা ছার করে দিয়েছেন।
সেই কিশোরীর আনন্দটুকু তাঁর নিজের গায়ে মেখে নিতে ইচ্ছে হল।
আর ক্লান্তিবোধ নেই।
রাণু বারবার অনুযোগ করে, তিনি কেন আর গল্প লিখছেন না। এবারে রাণু এলে আর তাকে বিমুখ করা যাবে না। একটা কিছু লিখতেই হবে রাণুর জন্য।
তিনি আবার লিখতে বসে গেলেন।
শান্তিনিকেতনে যাওয়া একেবারে ঠিকঠাক, তবু বাতিল হয়ে গেল শেষ মুহূর্তে। ফণিভূষণ বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির দর্শন ও সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন, থাকতে হবে সেই ক্যামপাসে, বাড়ি বদলের ঝক্কি ঝামেলা কি কম!
রাণুর খুবই মন খারাপ, আবার নতুন বাড়িতে যাবার কিছুটা উত্তেজনাও আছে। নতুন করে জিনিসপত্র গুছোনো, বাড়ি সাজানো। ব্ৰহ্মকুণ্ডের গলির তুলনায় এখানে অনেকটা খোলামেলা আকাশ। গাছপালাও প্রচুর, কিছুটা যেন শান্তিনিকেতনের কথা মনে পড়ে যায়।
এর মধ্যেই গরম পড়ে গেছে বেশ, কিন্তু রাণু আর খালি গায়ে থাকে না। মা বকে বকে তার স্বভাব শুধরেছেন। তার অবশ্য এখনও লজ্জার নম্রতার বদলে চাঞ্চল্যই বেশি। শরীরে যৌবন আসি আসি করছে, কিন্তু রাণু তা টের পায়নি। সে সিঁড়ি দিয়ে দুদ্দাড় করে নামে, রাস্তায় কোনও ফেরিওয়ালাকে ডাকার জন্য খালি পায়ে দৌড়ে যায়।
বড় দুই দিদিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে হস্টেলে, রাণু ভর্তি হয়েছে কাছাকাছি ইস্কুলে। পড়াশুনোর চেয়ে সে এস্রাজ নিয়েই সময় কাটায় বেশি। তার গান গাইতেও ইচ্ছে করে, মাঝে মাঝে সে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে আপনমনে গান গেয়ে যায়, জলের কল খোলা থাকলে বাইরে থেকে শোনা যায় না।
হঠাৎ একদিন অ্যান্ড্রুজ সাহেব এই নতুন বাড়িতে এসে উপস্থিত। এই সাহেবটিকে রাণুর বেশ মজার লাগে। কথা বলার সময় মুণ্ডুটা এদিক ওদিক নাড়েন আর দাড়িতে হাত বুলোন। বাংলা উচ্চারণ একেবারে পারেন না, তবু মাঝে মাঝে বাংলা বলা চাই। গুরুদেবকে বলেন গুঢুডেব!
অ্যান্ড্রুজ যে প্রস্তাব দিলেন, তা শুনে রাণু আনন্দে নেচে উঠল।
এই গ্রীষ্মে এদের সবারই শান্তিনিকেতন যাবার কথা ছিল, তাই গুরুদেব ঠিক করে রেখেছিলেন যে রাণুকে দিয়ে তাঁর একটি নাটকে অভিনয় করাবেন। অধিকারী মশাই নতুন চাকরিতে যোগ দিয়েছেন, যেতে পারছেন না, গুরুদেব তা জেনেছেন ও বুঝেছেন যে এখনই আপনাদের পক্ষে যাওয়া অসুবিধেজনক। তবে অধিকারী মশাই যদি রাজি থাকেন, তা হলে শুধু রাণুকে অ্যান্ড্রুজ শান্তিনিকেতন নিয়ে যেতে পারেন, আবার কেউ ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। অ্যাজ শুধু এই জন্যই। কাশীতে আসেননি, লক্ষ্ণৌতে তাঁর অন্য কাজ ছিল, গুরুদেব বলে দিয়েছিলেন, ফেরার পথে কাশীতে নেমে এই কথাটা জানাতে।
রাণুর বাবা রাজি হলেন না। এর আগে রাণু কখনও বাড়ি ছেড়ে একা কোথাও থাকেনি, তাকে অতদূরে পাঠাতে তাঁর মত নেই। কন্যাসন্তান একটু বড় হয়ে উঠলে তার ওপর বিশেষ নজর তো রাখতেই হয়।
রাণু গিয়ে কেঁদে পড়ল তার মায়ের কাছে।
সরযুবালার আপত্তি নেই। একবার শান্তিনিকেতন দেখার পর তাঁর নিজেরই বারবার সেখানে যেতে ইচ্ছে করে। গুরুদেবের সান্নিধ্য পাওয়াই তো বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। কত নতুন নতুন গান শোনা যায়। সন্ধেবেলা ছাদের ওপর সাহিত্য বাসর হয়। এখানে তো সে সব কিছুই নেই।
স্বামীর আশঙ্কা উড়িয়ে দেবার জন্য সরযূবালা বললেন, গুরুদেব রাণুকে এত স্নেহ করেন, রাণু তাঁর কাছে থাকবে, এতে চিন্তার কী আছে?
ফণিভূষণ বললেন, গুরুদেব রাণুকে বিশেষ স্নেহ করেন, তা জানি। কিন্তু তিনি ব্যস্ত মানুষ, তিনি কি সর্বক্ষণ এই দুরন্ত মেয়েকে সামলে রাখতে পারবেন? ওখানে আরও মানুষজন নেই?
সরযূবালা বললেন, শান্তিনিকেতনের সবাই কাশীর লোকদের চেয়ে অনেক ভাল! এখানে কি মেয়েদের একা রাস্তায় বেরোবার উপায় আছে? প্রায়ই তো গুণ্ডাদের উপদ্রবের কথা শোনা যায়। শান্তিনিকেতনে তিনি মহিলাদের সন্ধের পরেও নিঃশঙ্ক চিত্তে ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন।
তা ছাড়া গুরুদেব নিজে অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন, তা কি প্রত্যাখ্যান করা সমীচীন?
এর পর আর কথা নেই। ফণিভূষণকে সম্মতি জানাতেই হল।
ট্রেনে অ্যান্ড্রুজ সাহেব একগাদা কাগজপত্র ছড়িয়ে সেগুলি পড়াশুনোতেই ব্যস্ত রইলেন। কথাবার্তা বিশেষ বলেন না। রাণুও ‘গল্পগুচ্ছ’ আর ‘বউ ঠাকুরানির হাট’ নিয়ে এসেছে, আগে পড়া গল্পগুলিই আবার পড়ে, বারবার পড়তে তার ভাল লাগে, এক এক সময় বই থেকে চোখ তুলে তলিয়ে থাকে চলন্ত প্রকৃতির দিকে। হ্যাঁ, মনে হয় ট্রেনটা থেমে আছে আর বাইরের মানুষজন, এমনকী গাছপালাগুলোও ছুটছে উলটো দিকে।
টিফিন কেরিয়ার ভর্তি খাবার সঙ্গে দিয়েছেন মা। লুচি, আলুর দম, বোঁদে, গাজা, মালাই। কবির জন্য আলাদা সন্দেশের বাক্স। অ্যাজ সাহেব এ সব কিছুই খাবেন না, রাণু দিতে গেলে তিনি যেন ভয় পেয়ে গিয়ে বলে ওঠেন, ওইসব বস্তু খাইলে পেটের ব্যায়াম হয়।
লুচি খেলে পেটের অসুখ হবে, রাণু এমন কখনও শোনেনি।
ট্রেনের চাকার যে আওয়াজ, তার যেন একটা ভাষা আছে। সমস্ত রেলগাড়িটা যেন ছুটতে ছুটতে বলছে, আর কত দূর, আর কত দূর! রাণুর মনও যেন বলছে সেই কথা, আর কত দূর, আর কত দেরি হবে, কখন দেখা হবে ভানুদাদার সঙ্গে?
একসময় অ্যাজ পড়া থামিয়ে বললেন, শোনো বালিকা, তোমাকে একটা কথা বলা উচিত মনে করি। তুমি গুরুদেবের কাছে যাইতেছ, কিন্তু তাঁহাকে বেশি বিরক্ত করিও না। তাঁহার সময় নষ্ট করিও না। তিনি কত বড় মানুষ, তুমি জানো?
রাণু বলল, হ্যাঁ জানি। পৃথিবীর সব মানুষের চেয়ে তিনি বড়।
রাণুর কথার কৌতুকের সুরটি তিনি ধরতে পারলেন না। তিনি কৌতুকের ধার ধারেন না। গম্ভীর মুখে বললেন, হাঁ, তা বলিতেও পারো। তিনি অতিশয় ব্যস্ত। আমি যখনই তাঁহার নিকটে যাই, দেখি যে তুমি তাঁহার পাশে বসিয়া আছ। তাঁহার সহিত কথা বলিতেছ।
রাণু বলল, তাতে আপনার হিংসে হয় বুঝি?
অ্যান্ড্রুজ বললেন, আমার অনেক কাজের কথা থাকে। সে সব হয় না। তুমি কথা বলিয়া সময় নষ্ট করো।
রাণু বলল, বেশ করব। আমি আমার কবির সঙ্গে কথা বলব।
অ্যান্ড্রুজ চোখ বড় বড় করে তাকাতেই রাণু খিল খিল করে হেসে উঠল।
কামরার অন্য লোকেরা অবাক ভাবে তাকিয়ে থাকে। এক সাহেবের সঙ্গে চলেছে একটি ফুটফুটে কিশোরী মেয়ে। সাহেব দেখলে অনেকেরই সভয় সম্ভ্রম হয়, মেয়েটি কিন্তু মাঝে মাঝেই মজা করছে সাহেবটিকে নিয়ে।
উত্তর প্রদেশ ছাড়িয়ে বিহার, তারপর বাংলায় প্রবেশ করল ট্রেন। এত পুকুর, নদী, খাল বিল দেখলেই বাংলাদেশ চেনা যায়। স্টেশনের নামও বাংলায় লেখা। মুমফালি এখন বাদাম হয়ে গেছে, সীতাফল হয়ে গেছে আতা।
হাওড়া স্টেশনে নেমে অ্যান্ড্রুজ বললেন, গুরুদেব এখন শান্তিনিকেতনে রহিয়াছেন। কিন্তু আমার কিছু কার্য আছে, তাই দুই দিন কলিকাতায় থাকিয়া তারপর সেখানে যাইব।
রাণু বলল, কবি শান্তিনিকেতনে? তা হলে আমার একদিনও কলকাতায় থাকার ইচ্ছে নেই।
অ্যান্ড্রুজ বললেন, বলিলাম যে আমার কিছু প্রয়োজন সারিতে হইবে।
রাণু বলল, আপনার প্রয়োজন আপনি সারুন গে। আমাকে রেল গাড়িতে চাপিয়ে দিন, আমি একাই যেতে পারব।
তা তো আর হয় না। অগত্যা অ্যান্ড্রুজকেও কাজ ফেলে চেপে বসতে হল পরের ট্রেনে।
বোলপুর থেকে ঘোড়ার গাড়িতে শান্তিনিকেতন। সন্ধে হয়ে এসেছে, পশ্চিম আকাশে শেষ সূর্যের রক্তিম ছটা। সঙ্গীত ভবনে ছাত্ররা গান ধরেছে সমস্বরে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা ফিরে আসছে। নিজেদের কুলায়।
গাড়িটা প্রার্থনা ভবনের সামনে থামতেই রাণু লাফিয়ে নেমে পড়ল, তারপর ছুট লাগাল মাঠের মধ্য দিয়ে।
একদিকে একটা বেশ বড় বাড়ি তৈরি হচ্ছে, এখন অর্ধসমাপ্ত অবস্থা। প্রথমেই একটা ব্যাপার নতুন লাগল, বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে! আগে সন্ধের সময় ঘরে ঘরে লণ্ঠন জ্বলতে দেখে গেছে রাণু।
সাধুচরণের কাছে জেনে নিল, কোথায় আছেন কবি। তিনি ঘন ঘন বাসস্থান বদল করেন।
একটি একতলা বাড়ির ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে রাণু। দেখল, একটা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কবি, গান গাইছেন নিচু গলায়, সম্ভবত সুর দিচ্ছেন নতুন গানে।
রাণু নিঃশব্দে এগিয়ে পেছন থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, কে বলুন তো?
গান থামিয়ে কবি বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভেবে বলছি।
রাণুর হাত দুটি ধরে বললেন, এমন শুভ্র কমলকলিকার মতো দুটি মুঠি কার হতে পারে? নিভৃত ঝর্নার মতো কণ্ঠস্বর যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। পারিজাত ফুলের সুগন্ধ পাচ্ছি, ঘরের বাতাসও বদলে গেছে, এ যেন বারাণুসীর জাহ্নবীর বাতাস …
ঘুরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে তিনি বললেন, এ কী, এর মধ্যে এত বড় হয়ে গেছ?
ফুলকাটা ঘটিহাতা ব্লাউজ পরেছে রাণু, চম্পক বর্ণের শাড়ি, এর মধ্যে যথেষ্ট দীঘল হয়েছে তার বরতনু, মাথার চুল পিঠ ছাড়িয়ে গেছে। দীর্ঘ ট্রেনযাত্রার ক্লান্তির সামান্যতম চিহ্নও নেই মুখে, প্রসাধনও নেই কিছু, যেন সদ্য বৃষ্টি-ধোওয়া প্রকৃতি।
রাণু বলল, বাঃ, বড় হব না?
কবি অস্ফুট স্বরে বললেন, ওহে সুন্দর মরি মরি, তোমায় কী দিয়ে বরণ করি—
রাণু বলল, ও গানটা আমি শুনেছি। এখন কী গান গাইছিলেন, সেটা করুন।
কবি সুর ছাড়াই বলতে লাগলেন, আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে/ ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে।
রাণু তার করমচা রঙের হাতের পাঞ্জা কবির মুখে চাপা দিয়ে বলল, না, এটা শুনব না। জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় আবার কী? না, না, এরকম বলা চলবে না।
কবি হেসে বললেন, বাকিটা শোনো! তাই তো আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে/ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন-বায়ে,/নতুন সুরে গান উড়ে যায় আকাশ-পারে,/নতুন রঙে ফুল ফুটে তাই ভারে ভারে—
রাণুর কাঁধে স্নেহময় হাত রেখে তিনি আবার বললেন, ওগো আমার নিত্যনূতন, দাঁড়াও হেসে।/ চলব তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে–
রাণু বলল, আপনার কিন্তু এর মধ্যে একটুও বয়েস বাড়েনি।
কবি বললেন, বাড়েনি কী বলছ, বরং যেন কমছে। কাল কী হল শুনবে? কাল আমার পঞ্চম বর্গের ছেলেরা দুপুরবেলা এসে ধরল, তাদের খাওয়াতে হবে। সমরেশ সিংহ নামে একটি ছেলে ওদের সর্দার। সে-ই আমার কাছে এসে দরখাস্ত করলে। আমি বল্লম, আচ্ছা বেশ। তাই সন্ধেবেলা আমার ও বাড়ির নীচের দক্ষিণের বারান্দায় বসে ওদের ভোজ হয়ে গেছে। ওদের ফরমাশ ছিল লুচির। লুচি ডাল ধোকা চাটনি যেমনি পাতে পড়া অমনি কোথায় যে অদৃশ্য হতে লাগল তার ঠিকানা পাওয়া গেল না। তার ওপর আম ছিল, রসগোল্লা ছিল—
রাণু বলল, শুনেই আমার জিভে জল আসছে!
কবি বললেন, তারপর কী হল, ভাগ্যিস বৃষ্টি এসে পড়ল হঠাৎ, নইলে ওদের খাওয়া ফুরোত না, অথচ আমার খাবার ফুরিয়ে যেত। এই লোভী বাঁদরগুলোকে আমি খুব ভালবাসি। ওরা ক্লাসে কী রকম চেঁচায় দেখেছ তো, এখনও সেইরকম চেঁচামেচি করে, সমস্ত শান্তিনিকেতন অশান্ত হয়ে ওঠে—আমার ক্লাসে ওরা মনে করে খেলা—এ তো পড়া নয়, আমি যেন ওদের খেলার সর্দার। সত্যিই আমি তাই—মনের ভিতর দিকে আমার আর বয়েস হল না–তুমি সাতাশ বলেছ, আমি যেন সাতাশের চেয়েও কম—আমি জানি, তাই তোমার ইচ্ছে করে আমাকে ছোট ছেলের মতন সাজাতে, এবং যত্ন করতে, আদর করতে।
রাণু চোখ পাকিয়ে বলল, ভানুদাদা, আপনি আজও চুল আঁচড়াননি।
কবি বললেন, আমার চিরুনি রানিটি যে কোথায় পলাতকা হয়ে যায়। সে বুঝি শুধু তোমার হাতে ধরা দেবে বলেই লুকিয়ে বসে থাকে।
চিরুনি ঠিক খুঁজে বার করল রাণু।
রাণু যে গাল টিপে ধরে চুল আঁচড়ে দেয়, এই ভঙ্গিটা খুব উপভোগ করেন কবি।
তিনি মৃদু সুর করে বললেন:
বঁধুয়া, হিয়া ‘পর আও রে,
মিঠি মিঠি হাসয়ি, মৃদু মৃদু ভাষয়ি,
হমার মুখ পর চাও রে!
রাণু একটু চমকে উঠেই বলল, এ আবার কী? হিন্দি নাকি? এ আবার কী ছাই হিন্দি? এর চেয়ে আমি হিন্দি অনেক ভালো জানি।
কবি বললেন, হিন্দি আমিও খারাপ জানি না। এক সময় মেজদাদা আর মেজ বউঠানের সঙ্গে উত্তর ভারতের মতো জায়গায় গিয়ে থেকেছি। কিন্তু এটা হিন্দি নয়। এটা বাংলাও নয়। এটা নতুন ভাষা, ভানু সিংহের ভাষা। এখন থেকে আমি মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলব।
রাণু বলল, আর একটু বলুন! আর একটু!
কবি বললেন:
সজনি সজনি রাধিকা লে
দেখ অবহুঁ চাহিয়া
মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া
একটু থেমে, কপালটা চেপে ধরে কবি বলতে লাগলেন, তারপর, তারপর…মনে আসছে না, মনে আসছে না, কতকাল আগেকার লেখা…তবে শেষটা শোনো
মল্লিকা চামেলী বেলী
কুসুম তুলহ বালিকা,
গাঁথ বৃথি, গাঁথ জাতি
গাঁথ বকুল মালিকা।
তৃষিত নয়ন ভানুসিংহ
কুঞ্জপথম চাহিয়া
মৃদুল গান শ্যাম-আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া।
রাণু বলল, আবার করুন তো, আবার করুন তো! আমি মুখস্ত করে নেব।
কবি বললেন, পর পর কি গাওয়া যায়। পরে আবার হবে।
রাণু জিজ্ঞেস করল, এটা কবে লিখেছিলেন?
কবি বললেন, তা প্রায় তোমার বয়েসে!
পরদিন ‘বিসর্জন’ নাটকের রিহার্সালের সময় রাণু দেখল, কবির বয়েসের ব্যাপারটা বাইরের দিক থেকেও কত সত্য।
আগে ঠিক ছিল, ‘বিসর্জন’ নাটকে কবি সাজবেন রঘুপতি। হঠাৎ নিজেই তা বদলে দিলেন, রাণু হবে অপর্ণা, আর তিনি জয়সিংহ। যুবক জয়সিংহের ভূমিকায় তাঁর কী সাবলীল পদক্ষেপ, অভিমানের কী দৃপ্ত ভঙ্গি, কে বলবে তাঁর বয়েস সাতাশের বেশি!
প্রথম কয়েকদিন পার্ট শেখাতে গিয়ে হিমসিম খেতে হল কবিকে।
অন্য সময় রাণু কত চঞ্চল, কত স্বাভাবিক, কিন্তু নাটকের মুখস্ত করা পার্ট বলতে গিয়ে সে দারুণ আড়ষ্ট হয়ে যায়। অপর্ণা হিসেবে তাকে মানিয়েছে চমৎকার, কিন্তু ঠিক ঠিক কথাগুলো বলতে হবে তো!
কবি অবশ্য হাল ছাড়লেন না। তবে, বিসর্জনের মঞ্চস্থ হবার তারিখটি পিছিয়ে গেল অনেক। কারণ, কবিকে এর মধ্যে গুজরাত যেতে হবে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে।
নাটকের রিহার্সাল ও গান রচনা বন্ধ করে কবি বক্তৃতা লিখতে বসলেন।
রাণুর তা পছন্দ নয়। কেন কবিকে এত বক্তৃতা দিতে হয়?
রাণু বলল, আমি অতদূর থেকে এলাম, আর আপনি গুজরাতে চলে যাবেন?
কবি বললেন, তা কি কখনও সম্ভব? হয় তুমিও আমার সঙ্গে গুজরাতে যাবে, কিংবা যতদিন তুমি এখানে থাকবে, ততদিন আমি গুজরাত কেন অমরাবতী, অলকাতেও যাব না।
তারপর তিনি বুঝিয়ে বললেন যে, শান্তিনিকেতনের কর্মকাণ্ড চালাবার জন্য তাঁকে অনবরত অর্থচিন্তা করতে হয়। ভিক্ষাপাত্র নিয়ে যেতে হয় দেশে দেশে। অনেকে এমনি এমনি ভিক্ষে দিতে চায় না, তাই বক্তৃতা দিতে হয়। যে কোনও কারণেই হোক, সম্প্রতি বেশ কিছু গুজরাতি ছাত্র এখানে এসে ভর্তি হয়েছে। গুজরাতের বড় বড় ব্যবসায়ীরা টাকা তুলে দেবার আশ্বাস দিয়ে আয়োজন করেছে কয়েকটি বক্তৃতাসভার।
রাণু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আপনাকে বক্তৃতা দিতে হবে না, আমি আপনাকে টাকা দেব!
কবি সকৌতুকে বললেন, তোমার বুঝি অনেক টাকা আছে? অধ্যাপক কন্যা সন্ধান পেয়েছে কোনও গুপ্তধনের? কিংবা যক্ষ অধিপতি স্বয়ং কুবের তোমার ভক্ত হয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন মণিমাণিক্য?
রাণু কাঁধের ছোট্ট ঝোলা ব্যাগটি খুলতে খুলতে বলল, আমি পরীক্ষায় ফাস্ট হয়ে তিরিশ টাকা জলপানি পেয়েছি। এই সব টাকা আপনার।
কবি বললেন, শুধু পরীক্ষায় কেন, তুমি অনেক বিষয়েই ফাস্ট। কিন্তু জলপানির সব টাকা দিয়ে দেবে?
রাণু বলল, আমি টাকা নিয়ে কী করব? আপনাকে দেব বলেই তো এনেছি।
কবি বেশ কয়েক মুহূর্ত অপলক ভাবে তাকিয়ে রইলেন কিশোরীটির দিকে।
তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আমি অনেক রাজা-মহারাজের কাছ থেকেও দান পেয়েছি, কিন্তু তোমার এই দানের তুলনা হয় না। দাতাদের মধ্যে তুমি সর্বকনিষ্ঠ শুধু নও, তোমার মতো আর কেউ সর্বস্ব দান করেনি! দাও, আমি মাথা পেতে নিচ্ছি।
টাকাটা হাতে নিয়ে তিনি আবার বললেন, অনেক দিন ধরেই ভাবছি, শান্তিনিকেতনে একটা ঘন্টাঘর বানাতে হবে। তোমার টাকাতেই শুরু হবে সেই কাজ। দাঁড়াও, এখুনি সুরেনকে ডেকে বলছি। এর পর যখন তুমি আসবে, দেখতে পাবে ঘণ্টা তৈরি হয়ে গেছে। যখনই সেই ঘণ্টা বাজবে, আর কেউ না শুনুক, আমি ঠিক শুনতে পাব, তাতে ধ্বনিত হচ্ছে রাণুর নাম। রাণু, রাণু, রাণু, রাণু, ঢং ঢং ঢং ঢং।
তিনদিন পরেই সরযূবালার আগ্রহাতিশয্যে ফণিভূষণ অন্য মেয়েদের নিয়ে পৌঁছলেন শান্তিনিকেতনে। তাঁদের জন্য দেওয়া হল একটি পৃথক বাড়ি, কবির গুজরাট সফরের তারিখ পিছিয়ে গেল।
রাণু অধিকাংশ সময় কবির সঙ্গেই কাটাবে। এটা সবাই ধরে নিয়েছে, তাতে কবির মন ভাল থাকে। তাঁর নতুন করে লেখারও জোয়ার এসেছে।
রাণু কবির কাছে নতুন গল্পের জন্য আবদার করেছিল। কবি তাকে একটি নতুন লেখা শোনালেন, সেটা ঠিক গল্পও নয়, কবিতাও নয়। কিংবা সেটা গল্পও হতে পারে। কবিতাও হতে পারে। সব গল্পেই যে জমজমাট কাহিনী থাকতে হবে, তার কোনও মানে নেই। আবার অনেক কবিতাতেও কাহিনীর আভাস থাকে। ইংরেজ-ফরাসিরা তো ছন্দ-মিল ছাড়াও কবিতা লিখছে।
কবি শোনাতে লাগলেন : এখানে নামলো সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন দেশে কোন সমুদ্র পারে তোমার প্রভাত হল!
অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিত নববধূর মতো; কোত্থানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা।
জাগল কে। নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায়-জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সেউতির মালা।
এখানে একে একে দরজায় আগল পড়ল, সেখানে জানলা খুলে গেল। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া…
সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ওই প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক।
শুনতে শুনতে আবিষ্ট হয়ে গিয়ে রাণু জিজ্ঞেস করল, এটা কবে লিখেছেন?
কবি বললেন, তোমাকে একদিন চিঠি লিখতে লিখতেই এই লেখাটা মনে এসে গেল। কিংবা বলতে পারো, লেখাটাই যেন আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিল।
রাণু জিজ্ঞেস করল, এই লেখাটার নাম কী?
কবি বললেন, এটার নাম ‘সন্ধ্যা ও প্রভাত’। এরকম আরও লিখছি, সব মিলিয়ে নাম দেব ভেবেছি ‘লিপিকা’।
রাণু বলল, আমাকে সবগুলোই শোনাতে হবে কিন্তু।
শান্তিনিকেতনের বারোয়ারি রান্না ফণিভূষণের সহ্য হয় না, তিনি আলাদা রাঁধুনি নিযুক্ত করেছেন। সে জন্য রাণু যেখানেই থাকুক, সন্ধের পর এসে বাবা-মায়েদের সঙ্গে খেতে বসতে হয়। এখানে সবাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে, রাণুর ঘুম আসে না। এক একদিন খাওয়ার পরেও সে আবার চলে যায় কবির কাছে। কিংবা কবিই ডেকে পাঠান তাকে।
কবির পাশটিতে ঘেঁষে বসে, কখনও শিশুর মতন গলা জড়িয়ে ধরে সে লিপিকার লেখাগুলি শোনে। কখনও কখনও দু’বার করে শুনতে চায়। শব্দগুলির ঝংকারে সে শিহরন বোধ করে। এরই মধ্যে কোনও কাজের কথা নিয়ে উপস্থিত হন অ্যান্ড্রুজ। রাণুকে দেখে তিনি স্পষ্ট বিরক্ত হন, তারপর দুজনের মধ্যে যেন নিঃশব্দ প্রতিযোগিতা চলে, কে বেশি আকৃষ্ট করতে পারবে কবির মনোযোগঅধিকাংশ দিনই অ্যান্ড্রুজকেই আগে প্রস্থান করতে হয়।
একদিন বেশি বেশি রাত হয়ে গেল। কবি ও রাণু কথায় কথায়, গল্পে গল্পে এমন বিভোর হয়ে ছিলেন যে সময় টের পাননি। গোটা শান্তিনিকেতন এখন ঘুমন্ত, শুধু জেগে আছে সারমেয়কুল। মাঝে মাঝে তাদের ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। মেঘমুক্ত আকাশ ভেসে যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়, গাছগুলি সেই জ্যোৎস্নার আদর খাচ্ছে।
কবি নিজে রাণুকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।
রাণু কারুকে না জানিয়ে, পা টিপে টিপে এসে শুয়ে পড়ল বোনদের পাশে।
পাশের ঘরে ফণিভূষণ এখনও জেগে আছেন। রাণুর ফিরে আসা টের পেয়ে তিনি টর্চ জ্বেলে ঘড়ি দেখলেন, কিছু বললেন না।
পরদিন প্রাতরাশের সময় রাণু বলল, বাবা, আমার শান্তিনিকেতন থেকে চলে যেতে ইচ্ছে করে না। আমি এখানেই পড়তে পারি না?
ফণিভূষণ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না।
সরযূবালা বললেন, কথাটা তো ও মন্দ বলেনি। ওর যখন শান্তিনিকেতন এত ভাল লাগে, ও এখানেই পড়াশুনো করুক না। গুরুদেব ওঁকে এত স্নেহ করেন, তাঁর কাছে থাকলে ও কতকিছু শিখবে। এরকম সৌভাগ্য ক’জনের হয়!
ফণিভূষণ বললেন, গুরুদেবের কাছে বেশি প্রশ্রয় পেয়ে ওর মাথা বিগড়ে যেতে পারে। এখানে থাকলে ওর পড়াশুনো হবে না।
সরযুবালা বললেন, যদি অন্যদের মতন হস্টেলে থাকে? এখানে তো মেয়েদেরও হস্টেল হচ্ছে শুনছি।
ফণিভূষণ বললেন, হস্টেলের খাওয়া তোমার মেয়ের সহ্য হবে?
রাণু বলল, হ্যাঁ বাবা, আমার কোনও অসুবিধে হবে না। আমি ঠিক পারব। আরও তো মেয়েরা থাকবে।
ফণিভূষণ কঠোরভাবে বললেন, রাণু আমি না বলে দিয়েছি, তুমি আমাদের সঙ্গে কাশী ফিরে যাবে। আর কোনও কথা নয়।
কয়েকদিন বাদে বিদায় নেবার সময় স্বয়ং কবি ফণিভূষণকে অনুরোধ করলেন, রাণুকে তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে শান্তিনিকেতনে পড়াতে চান।
ফণিভূষণ আগেই মনস্থির করে ফেলেছেন। তিনি রাজি হলেন না।
গুজরাতের আমন্ত্রণ আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না, কবিকে বেরিয়ে পড়তেই হল সদলবলে। অনেকগুলি সভা-সমিতিতে যোগ দিতে হবে, তবে প্রধান আমন্ত্রক গুজরাত সাহিত্য পরিষদ। কবি আসছেন জেনে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা দেবার জন্য আগে থেকেই প্রচার চালাতে লাগলেন গান্ধীজি।
আমেদাবাদ পৌঁছোবার আগেই প্রতি রেল স্টেশানে জনতা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য উপস্থিত। বহুকালের মধ্যে কোনও রাজকীয় অতিথিও এত সমাদর পায়নি।
গান্ধীজির সঙ্গে কবির রাজনীতি বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ তো আছেই, সাহিত্য বিষয়েও মতের মিল নেই। গান্ধীজি মনে করেন, জনসাধারণের উন্নতিই সাহিত্যিকদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁদের রচনা যেন সাধারণ মানুষের ঈশ্বর উপলব্ধির সহায়ক হয়, যে কারণে বাণভট্টের কাদম্বরীর চেয়েও তুলসীদাসের রামায়ণ অনুসরণযোগ্য। গান্ধী রসের ব্যাপারটা বিশেষ বোঝেন না।
সবরমতী আশ্রমে এক রাত কাটিয়ে কবি রওনা দিলেন ভাবনগর রাজ্যের দিকে। তারপর কাঠিয়াবাড়। ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যের রাজারা বিশ্বভারতীর বিভিন্ন কাজের জন্য অর্থ সাহায্য করছেন, তাই বক্তৃতাও দিতে হচ্ছে অনবরত।
সারাজীবনে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন অনেক, কখনও লিখিতভাবে, কখনও সরাসরি ভাষণ। এখন তিনি এমনই অভ্যস্ত যে অনর্গল সুললিত বাক্য বেরিয়ে আসে। সহজে ক্লান্তও হন না।
তবু এক একটা সভার মধ্য পথে তাঁর মনে হয়, বক্তৃতা দেওয়াই কি তাঁর কাজ? একটি কিশোরী মেয়ে তাঁকে বার বার বলে, আপনি এত বক্তৃতা দেন কেন? সত্যিই তো, এইসব কথা শুনে কার কী লাভ হয়? কেউ কি মনে রাখে? একটা সভায় সে কথা বলেও ফেললেন।
এখানে তাঁকে ইংরেজিতেই ভাষণ দিতে হয়। গান্ধীজি একদিন বললেন, ইংরেজি তো অনেকেই বোঝে না, আপনি হিন্দিতেই বলুন না। যতটুকু পারেন, যেমন করে পারেন।
কবি শুরু করলেন এইভাবে : আপকি সেবামে খড়া হোকর বিদেশীয় ভাষা ক য়হ হম চাহতে নহী। পর জিস প্রান্তমেঁ মেরা ঘর হৈ বহাঁ সভামে কহনে লায়েক হিন্দিকা ব্যবহার হৈ নহী।
মহাত্মা গাঁধী মহারাজকী ভী আজ্ঞা হৈ হিন্দিমে কহনেকে লিয়ে। যদি হম সমর্থ তব ইসসে বড়া আনন্দ ঔর কুছ হোতা নহী। অসমর্থ হোনে পর ভি আপকি সেবামে মৈ দো চার বাত হিন্দিমে বলুংগা।…
কিছুক্ষণ হিন্দিতে বলার চেষ্টা করে তিনি বাংলায় বলতে লাগলেন, আমি কবি মাত্র—বাক্য আমার কণ্ঠে নেই, আছে হৃদয়ে। আমার বাণী এরকম সভায় বেরোতে চায় না, সে থাকে ছন্দের অন্দরমহলে।… সমাদর করে আমাকে আজ মঞ্চে তুলে দেওয়া হয়েছে, কবির কাছে চাওয়া হচ্ছে বক্তৃতা–বাঁশিকে লাগানো হচ্ছে লাঠির কাজে। …সভায় দাঁড়িয়ে আনন্দ দেওয়া, উপদেশ দেওয়া, কিছু কাজের কথা বলার শক্তি আমার নেই। জনসাধারণ আমার প্রতি যে দাক্ষিণ্য প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিদান দিতে না পেরে আমি হার মানছি…এই প্রীতি ও সমাদর ঈশ্বরেরই অযাচিত দান—সেই দানের যোগ্য হবার সাধনা করাই আমার কাজ। সেই সাধনা কবির সাধনা।
গুজরাতের অনেকগুলি জায়গা সফর করে তিনি এলেন বোম্বাই। সেখানে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের দিনটির স্মরণ সভার আয়োজন চলছে। সভাধিপতি বিশিষ্ট ব্যারিস্টার ও কংগ্রেসের নেতা জনাব মহম্মদ আলি জিন্না। তিনি চান জালিয়ানওয়ালাবাগের জমিটি কিনে সেখানে একটা স্মৃতিস্তম্ভ গড়া হোক। জিন্না এসে কবিকে ধরলেন, এই প্রস্তাবের সমর্থনে একটা ভাষণ লিখে দিতে। কবি অবশ্য সেই বীভৎস দিনের স্মৃতি স্থায়ী করার সমর্থক নন।
গুজরাত থেকে কিছু অর্থ পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়। শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর সব খরচ চালাবার দায়িত্ব কবির নিজের। এদিকে জমিদারির আয় খুবই কমে এসেছে, প্রমথ বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না। এতদিন মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কবির জমিদারি ছিল যৌথভাবে, এবার ভাগাভাগি না করে উপায় নেই। কারণ, মেজদাদার ছেলে সুরেন জমি কেনা-বেচার ফাটকা ব্যবসা করতে গিয়ে দারুণ ঋণগ্রস্ত, সে তার অংশ বিক্রি করে দিতে চায়। এর মধ্যেই বালিগঞ্জে ঠাকুরদের জমি কিনে নিয়েছে বিড়লা নামে এক ব্যবসায়ী, কুড়ি বিঘে জমি বিক্রি হয়েছে মাত্র চার লাখ টাকায়। সুরেনের বোন ইন্দিরাও তার মায়ের কাছ থেকে যৌতুক হিসেবে পাওয়া ব্রাইট স্ট্রিটের কমলালয়’ নামে সুদৃশ্য বাড়িটি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে।
টাকা চাই, আরও টাকা চাই। টাকার খনি এখন আমেরিকা। ইওরোপ এখন যুদ্ধবিধ্বস্ত, কিন্তু আমেরিকার গায়ে একটি আঁচড়ও লাগেনি। সে দেশে বক্তৃতা নিয়েও ব্যবসা হয়। কোনও কোনও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যেসব ব্যক্তিদের নামের চাহিদা আছে, তাঁদের দিয়ে বিভিন্ন শহরে বক্তৃতার ব্যবস্থা করে, টিকিটের লভ্যাংশের কিছুটা বক্তাকে দিয়ে সিংহভাগ নিজেরা নেয়। একবার চুক্তি হলে তার অন্যথা হবার উপায় নেই। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন একবার এরকম চুক্তিতে বাধ্য হয়ে বক্তৃতা দিতে দিতে ক্লান্ত হয়েও নিষ্কৃতি পাননি। নোবেল পুরস্কার পাবার পর কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একবার বক্তৃতা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে এনেছিলেন।
কবি ঠিক করলেন, যতই পরিশ্রম হোক, আবার যাবেন আমেরিকায়। এর মধ্যে একবার যাত্রার উদ্যোগ নিয়েও স্থগিত রাখতে হয়েছিল। কিন্তু এবারে কবির এজেন্ট মেজর পল্ড আর উৎসাহ দেখাচ্ছে না। সে জানাল যে আমেরিকায় এখন ভারতীয় নামের বাজার মন্দা। যুদ্ধ ফেরত সৈন্যদের সংবর্ধনা জানাতেই সাধারণ মানুষ বেশি উৎসাহী। ইওরোপীয় উদ্বাস্তুদের জন্য চাঁদা তোলা হচ্ছে চতুর্দিকে, ভারত সম্পর্কে কেউ মাথা ঘামাতে চায় না। কবির ইংরিজি বইগুলির বিক্রিও কমে আসছে হুহু করে।
তবু কবি ঠিক করলেন, তিনি নিজের উদ্যোগেই যাবেন। একবার গিয়ে পৌঁছেলে বহু মানুষ অবশ্যই শুনতে চাইবে তাঁর কথা। তাঁর মুখে বিশ্বমৈত্রী ও ভারতীয় মহান ঐতিহ্যের বাণী।
প্রথমে থামলেন লন্ডনে। সেখানে তাঁর বন্ধু ও অনুরাগীর সংখ্যা ইংরেজদের মধ্যেও অনেক। সকলকেই খবর দেওয়া হল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সাক্ষাৎ করতে এলেন না, রোদেনস্টাইন-এর মতন যে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হল, তাঁদেরও কথাবার্তা কেমন যেন আলগা আলগা। শুষ্ক ভদ্রতার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব প্রকট।
কবির একান্ত অনুগত উইলি পিয়ার্সন যুদ্ধের সময় নজরবন্দি ছিলেন, এখন তিনি হলেন কবির সফর-সচিব। কবি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার বলল তো? বন্ধুরা আমাকে হঠাৎ পরিত্যাগ করল কেন?
পিয়ার্সন বুঝেছেন কারণটি কী। কবির নাইটহুড প্রত্যাহার অনেকেই ভালভাবে নিতে পারেনি। বিশেষত যুদ্ধের সংকটের মধ্যে ইংরেজ সরকারকে অপদস্থ করাটা মেনে নিতে পারেনি অনেকেই।
কিন্তু ভারতীয়দের ওপর যে নৃশংস অত্যাচার করা হয়েছে, তা কি এখানকার বুদ্ধিজীবীরা জানে না?
না, অনেকেই জানে না, পত্র পত্রিকায় সঠিক খবর প্রকাশিত হয়নি। তা ছাড়া, ইংরেজ জাতির স্বভাবই এই, যুদ্ধের সময় সরকারের কোনও কাজেরই সমালোচনা করে না। সবাই সমর্থনে এককাট্টা। এখানে কিছু জানাবার উপায় নেই, কোনও কাগজ ছাপবে না।
ইংল্যান্ড ছেড়ে ফ্রান্সে এসে বরং কিছুটা সমাদর পেলেন কবি। দেখা হল অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিত ও মনীষীর সঙ্গে। ইওরোপের আরও কয়েকটি দেশ ঘুরে কবি পাড়ি দিলেন আমেরিকার পথে।
নিউইয়র্কে এসে হোটেলে উঠলেন নিজের খরচে। সবকিছুর কী সাংঘাতিক দাম। ইওরোপের প্রায় সাতগুণ। এর আগে সম্পন্ন ব্যক্তিদের বাড়িতে তাঁকে আতিথ্য দেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। এবারে কেউ এল না, দিনের পর দিন বসে রইলেন হোটেলের কক্ষে। সংবাদপত্রে তাঁকে নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য নেই। কয়েকটি ছোটখাটো সভার আয়োজন হল বটে, তা মোটেই অর্থকরী নয়। এবং শ্রোতাদের আগ্রহেরও বেশ অভাব।
কবি আগে ধারণাই করতে পারেননি যে ইংরেজদের মতন, তাঁর নাইটহুড প্রত্যাহার নিয়ে মার্কিনিরাও বিরাগ পোষণ করবে। যুদ্ধের শেষ দিকে মার্কিনিরা ইংরেজদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাই ইংরেজ সরকারের নিন্দে তারাও বরদাস্ত করতে পারে না। তাছাড়া ব্রিটিশ গোয়েন্দারা এর মধ্যে তলে তলে এ দেশে কবির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছে।
আমেরিকায় অর্থ সংগ্রহের আশা নেই দেখে কবি যখন অবিলম্বে ফিরে যাবার কথা চিন্তা করছেন, তখন মেজর পড় এসে জানাল যে, টেক্সাস রাজ্যে কবির গোটা পনেরো বক্তৃতা সভার আয়োজন করা যেতে পারে।
তাতেই রাজি হয়ে গেলেন কবি। তাতে পরিশ্রম হল প্রচুর, কিন্তু প্রায় পাঁচ মাস ঘোরাঘুরি করলেন, তবু তাঁর প্রত্যাশা মোটেই পূর্ণ হল না। বিশ্বভারতী গড়ার জন্য সাহায্য চাইতে এসেছেন, অনেকের কাছে। তা শোনাচ্ছে ভিক্ষে প্রার্থনার মতন। অনেক সময় তাঁর আয়ের চেয়ে ব্যয় হতে লাগল বেশি। আমেরিকার মানুষদের ওপর ইংরেজদের প্রচারের প্রভাব যে এতখানি হতে পারে, তা তিনি বুঝতেই পারেননি। তিনি ভারতে ইংরেজ সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করছেন, ইংরেজরা তার প্রতিশোধ নিচ্ছে অতি গোপনে এবং সূক্ষ্মভাবে তাঁর জনপ্রিয়তায় বাধা দিয়ে। এক মার্কিনি ধনবতী মহিলা বিশ্বভারতীর জন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার দিতে প্রায় রাজি হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁকেও এক ইংরেজ অফিসার বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিবৃত্ত করে।
এক জায়গায় কবিকে সত্যিই ভিক্ষে নিতে হল। ঘটনাটিকে একটি তিক্ত রসিকতা বলা যেতে পারে।
নিউ ইয়র্ক শহরের উত্তরে ক্যাটস্কিল মাউনটেন্সে এক বিলাসবহুল গৃহে কবি আমন্ত্রণ পেলেন। সেখানে প্রচুর ধনী ব্যক্তির সমাগম হয়। যেমন বিরাট ফাউন্টেনপেন কম্পানির মালিক মিঃ ওয়াটারম্যান, সাবান কম্পানির মালিক মিস্টার কলগেট, কোডাক নামে ফিল্ম কম্পানির মালিক মিস্টার ইস্টম্যান। পার্টিতে প্রচুর লোকজন। তার মধ্যে দু’জন রাশিয়ান শিল্পী কবির ছবি আঁকতে চেয়ে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। এই সময় ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন ধনকুবের জে ডি রকেফেলার, গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে করতে তিনি মুখ মোছর জন্য পকেট থেকে রুমাল বার করলেন, টুং করে একটা দশ পয়সা মাটিতে পড়ল। রকেফেলারের মতন ধনীরা পকেটে পয়সা রাখেন না, কী করে যেন ওই দশ পয়সাটা রুমালের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। তিনি এদিক ওদিক তাকিয়ে সেই পয়সাটা কবির হাতে গুঁজে দিয়ে গাড়িতে উঠে গেলেন।
কবি প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতেই পারলেন না। তিনিও রকেফেলারকে চেনেন না। বিস্মিতভাবে তিনি অন্য লোকদের বলতে লাগলেন, এটা অদ্ভুত না, এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আমার হাতে এই পয়সাটা দিয়ে গেলেন, আমাকে কি দেখে ভবঘুরে মনে হয়? ক্রমে কথাটা গৃহস্বামীরও কানে গেল, তিনি লজ্জা পেয়ে গোপনে খোঁজ করতে লাগলেন জনে জনে। রকেফেলারকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে, এক বুড়ো নিগ্রোকে আমি একটা ডাইম ভিক্ষে দিয়েছি!
শুধু ভারতীয় ভক্ত ও অনুরাগিণীদের চোখেই নয়, ইওরোপের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও যে কবিকে মনে করেন অতি সুদর্শন ও অভিজাত চেহারা, কেউ কেউ তাঁকে তুলনা করেছেন যীশুর সঙ্গে, সেই কবিই এক ধনী আমেরিকানের চোখে ‘বুড়ো নিগ্রো’।
এরকম পরিবেশে কবির নিজস্ব সচিব, অতিভক্ত, শান্ত, নিরীহ পিয়ার্সনের সঙ্গেও একদিন মন কষাকষি হয়ে গেল। কবি যথোচিত সম্মান পাচ্ছেন না দেখে পিয়ার্সন ভক্তির বাড়াবাড়ি শুরু করে দিলেন, যেন শ্বেতাঙ্গদের প্রতিভূ হিসেবে সব দোষ স্খলনের ভার তাঁর ওপর। তিনি লোকজনের সামনে কবির পায় হাত দিয়ে প্রণাম করেন বারবার। সবসময় গুরুদেব গুরুদেব করেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণামের ব্যাপারে এখানে অনেকেই হতচকিত হয়ে যায়। গুরুদেব শব্দটির মানে শুনেও তাদের ভুরু কুঁচকে ওঠে।
একদিন বিরক্ত হয়ে কবি তাঁকে বললেন, তুমি সবসময় কেন আমাকে গুরুদেব বলে ডাকো? কেন আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করো? এ অভ্যেস ছাড়ো! আমি জানি, তুমি এটা মন থেকে করো না, করতে পারো না। আর সেইজন্যই এটা সত্যিকারের অসৌজন্য। তুমি জানো, আমি কখনওই অবতার কিংবা গুরু হতে চাই না। আমার নিকটজনদের কাছ থেকে আমি শ্রদ্ধাভক্তিও দাবি করি না। আমি শুধু চাই ভালবাসা আর সহানুভুতি। আমি শুধুমাত্র একজন কবি, আর কিছু না।
বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে কবি আমেরিকা থেকে ফেরার পথে থামলেন লন্ডনে। এখানেও কয়েকদিন থেকে তিনি বুঝলেন ভুল করেছেন, পুরোনো বন্ধুদের আন্তরিকতাহীন ব্যবহারই তাঁকে বেশি আঘাত দেয়। ঠিক করলেন ফ্রান্সে চলে যাবেন। এলেন বিমানে। এই প্রথম তাঁর আকাশপথে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হল। দেখা হল আঁদ্রে জিদ ও রোম্যাঁ রোলার সঙ্গে। খাতির যত্ন পেয়ে তাঁর হৃদয় খানিকটা জুড়োলো।
আমেরিকায় পাঁচটি মাস নষ্ট হয়েছে, ইওরোপের বিভিন্ন দেশে কাটালেন প্রায় আড়াইমাস। সুইডেনে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিতে পারেননি, আট বছর পর সেখানে যেতে হল আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা দিতে। অন্যান্য দেশের তাঁর অনুবাদক ও প্রকাশকরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, তাও উপেক্ষা করা যায় না। হুয়ান র্যামোন হিমেনেথ তাঁর সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেছেন স্পেনে, এঁর অনুবাদে কবির বেশ কয়েকটি বই জনপ্রিয় হয়েছে। সংবর্ধনার সময় কবির একটি নাটক মঞ্চস্থ হবার কথা, তাতে দু’জন তরুণের অভিনয় সম্পর্কে আগে থেকেই প্রশংসা শোনা যাচ্ছে। তরুণ দুটির নাম ফেডেরিকো গার্থিয়া লোরকা আর লুই বুনুয়েল, তারা কবির খুবই অনুরাগী।
এবারেও খুব অভ্যর্থনা পেলেন জার্মানিতে।
তাতে তিনি মুগ্ধ, অভিভূত হয়ে থাকলেও দুটি ব্যাপার বুঝতে তাঁর ভুল হল। তিনি ভেবেছিলেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত জার্মানিতে তরুণ সমাজ আর যুদ্ধ চায় না, এখন শান্তির বাণী শুনতে চায়। প্রকৃতপক্ষে তা নয়, পরাজিত ও অপমানিত জার্মানরা ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে। দিন দিন বাড়ছে জঙ্গি মনোভাব, তৈরি হচ্ছে নাৎসি দল। জার্মান লেখকবুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও কমে আসছে তাঁর প্রভাব। বেল্ট ব্রেখট, হারমান হেস, স্টিফেন জোয়াইগ, কাউন্ট হারমান কাইজারলিং প্রমুখ তাঁর সুখ্যাতি করলেও অনেকে রইলেন বিমুখ। যেমন রাইনার মারিয়া রিলকে, টমাস মান, অসওয়াল্ড স্পেঙলার, ফ্রানৎস কাফকা প্রমুখেরা রইলেন উদাসীন, কেউ কেউ আড়ালে আবডালে নিলে করতেও ছাড়লেন না। আঁদ্রে জিদের অনুবাদ করা গীতাঞ্জলি পড়েছিলেন রিলকে, তাঁকে ওই বইটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল, রিকে রাজি হননি।
জার্মানিতে বেশ কিছু অর্থ প্রাপ্তি হয়েছিল কবির, কিন্তু অন্যায্য ভার্সাই চুক্তির ফলে জার্মান মুদ্রার এমনই দাম পড়ে গেল যে টাকাগুলো হয়ে গেল নিছক কাগজ!
আর মন টিকছে না, কবিকে হাতছানি দিচ্ছে তাঁর স্বদেশ, বারংবার মনে পড়ছে শান্তিনিকেতনের কথা। তিনি জাতীয়তার সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক হতে চান, কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্রই জাতীয়তাবাদের গোঁড়ামি আরও দৃঢ় হচ্ছে। তবু তিনি জেদ ধরে আছেন, অর্থ সাহায্য পাওয়া যাক বা না যাক, বিশ্বভারতীতে তিনি পূর্ব পশ্চিমের মিলন ঘটাবেনই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে জ্ঞান ও আদর্শের বিনিময়েই সভ্যতার প্রকৃত অগ্রগতি হতে পারে। সিলভ্যাঁ লেভির মতন বিদগ্ধ ব্যক্তি শান্তিনিকেতনে এসে পড়াতে রাজি হয়েছেন এটাও তো একটা দারুণ প্রাপ্তি। এই ভাবেই শুরু হবে কবির আদর্শের বাস্তবায়ন।
দীর্ঘকালীন প্রবাসেও কবি মাঝে মাঝে খবর পান দেশের ঘটনাবলির। গান্ধীজি আবার শুরু করেছেন অসহযোগ আন্দোলন। ছেলেরা ইস্কুল কলেজ ছেড়ে দিচ্ছে, সরকারের সঙ্গে পদে পদে অসহযোগিতার নামে ইতস্তত ঘটছে সংঘর্ষ। এর পরিণাম কী হবে, তা কি গান্ধীজি ভাবছেন না?
মার্সেই থেকে কবি ফেরার জাহাজে চেপেছেন। সহযাত্রী একটি বাঙালি তরুণ একদিন এসে তাঁকে প্রণাম করল, চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়েসী এই ছেলেটির নাম সুভাষচন্দ্র বসু, তার মুখমণ্ডলে রয়েছে। প্রতিভার দীপ্তি। সে কেমব্রিজ থেকে ফিরছে, মেধাবী ছাত্র, আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও সে পদত্যাগ করেছে, ইংরেজ সরকারের অধীনে সে চাকরি করতে চায় না, দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়াই তার অভিপ্রায়। কবির বেশ পছন্দ হল ছেলেটিকে।
সন্ধেবেলা কবি দাঁড়িয়ে থাকেন জাহাজের ডেকে। তাকিয়ে থাকেন বর্ণাঢ্য সূর্যাস্তের দিকে। এক দেশে যখন সূর্যাস্ত, আর এক দেশে তখন প্রভাত। যেমন জীবনের একদিকে বার্ধক্য, অন্যদিকে শৈশব। জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা, খ্যাতি, সম্মান, অর্থ এই সব কিছু ভুলে কবির ফিরে যেতে ইচ্ছে করে কৈশোর-যৌবনে। কিছুক্ষণের জন্য তিনি হয়ে ওঠেন ভানুসিংহ, চোখের সামনে দুলতে থাকে এক প্রাণচঞ্চলা কিশোরীর মুখ।
তিনি আপন মনে বলতে লাগলেন, যৌবনবেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি, হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি, হে ভোলা সন্ন্যাসী। চঞ্চল চৈত্রের রাতে কিংশুক মঞ্জরী সাথে শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি। আশ্বিনের বৃষ্টি হারা শীর্ণ শুভ্র মেঘের ভেলায়, গেল বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়, নির্মম হেলায়?
বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় দুলে দুলে উঠছে জাহাজ। আকাশে যেন নতুন নতুন নক্ষত্র জমা হচ্ছে পুরাতনদের পাশে। আকাশও যেন দুলছে। জীবন যেন চলেছে লক্ষ্যহীন পথে।
কবি ওপরের দিকে চেয়ে ধ্রুবতারাটিকে খুঁজতে লাগলেন।
সমুদ্রে দিকভ্রষ্ট নাবিকদের এই নক্ষত্রই তো পথ দেখায়।
কবির মনে পড়ল, জীবনে প্রথমবার সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইংল্যান্ড গমনের সময় তিনি একটি গান বেঁধে ছিলেন। তখনও তার মন এক জনের বিচ্ছেদ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়েছিল। বিলেত যাওয়ার আকর্ষণের চেয়েও সেই বিশেষ একজনের জন্য পিছুটান ছিল অনেক বেশি।
অনেকদিন পর কবি সেই গানটি গুনগুন করতে লাগলেন : তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথ হারা। যেথা আমি যাই নাকো তুমি প্রকাশিত থাকো, আকুল নয়নজলে ঢালো গো কিরণ ধারা। তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সংগোপনে, তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূল কিনারা। কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি, অমনি ও মুখ হেরি শরমে সে হয় হারা।
সেইদিন আর এখনকার মধ্যে কত দীর্ঘ দূরত্ব, তা শুধু সময় দিয়ে মাপা যায় না। সময়ের ব্যবধান অনেক কিছু ভুলিয়ে দেয়, আবার দুটি একটি ব্যাপার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে ওঠে। প্রথম যৌবনের পরিচিত কত মুখ অস্পষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু নতুন বউঠানের মুখখানি চির উজ্জ্বল।
কিশোরী রাণুই যেন নতুন বউঠানের স্মৃতি বেশি করে ফিরিয়ে আনছে। অথচ দু’ জনের কত অমিল। কবিও সেই আমি আর এই আমি এক নেই। তখন ছিলেন সদ্য যৌবনে, আজ তিনি প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায়। বয়েসের হিসেবে প্রৌঢ়ত্ব, শরীরে নয়। শরীর এখনও এই পৃথিবীর রূপরস-গন্ধ উপভোগ করার জন্য উন্মুখ। আর তার মনের অবস্থান যে কোথায়, তা ক’জন জানতে পারে? অন্য সকলে সব সময় তাকে একটা উঁচু বেদীর ওপর বসিয়ে রাখতে চায়, শুধু এই একটি কিশোরীই তাঁকে সেখান থেকে টেনে নামিয়ে খেলার সাথী হতে ডাকে। বড় মধুর সে খেলা। বয়েস কমাবার খেলা।
কতকাল দেখা হয়নি, কেমন আছে সে?
একবার একা আসবার অনুমতি পাবার পর, যে কোনও ছুটিতে রাণুর কলকাতা কিংবা শান্তিনিকেতনে চলে আসতে অসুবিধে হয় না। মাঝে মাঝে কবির কাছ থেকেও ডাক আসে, তখন আর আপত্তি করেন না রাণুর বাবা। কারুকে না কারুকে সঙ্গী পাওয়াই যায়।
এবারে বিসর্জনের মহড়া শুরু হয়েছে পুরোদমে, শান্তিনিকেতনেনয়, জোড়াসাঁকোয়। এর মধ্যে অনেকটা তৈরি হয়ে নিয়েছে রাণু। পার্ট সব মুখস্থ, অভিব্যক্তির তালিম দেন কবি নিজে। শিক্ষক হিসেবে তিনি কড়া, বকুনি দিতেও ছাড়েন না। রাণুর সবচেয়ে মুশকিল, সে ভেবে পায় না কী করবে হাত দুটো নিয়ে। কেমন যেন শক্ত হয়ে পাশে ঝুলে থাকে। কবি তার হাত ধরে বুঝিয়ে দেন, কি জয়সিংহ— কোথা জয়সিংহ—কেহ–কেহ নাই এ সংসারে বলতে বলতে ডান হাত ছুড়তে হবে জোরের সঙ্গে। বাঁ হাতে ধরিয়ে দিলেন একটা ফুলের সাজি।
জয়সিংহ ও অপর্ণার একটি দৃশ্যের মহড়া যে কতবার হল তার ইয়ত্তা নেই।
কবি : কেবলি একেলা! দক্ষিণ বাতাস যদি
বন্ধ হয়ে যায়, ফুলের সৌরভ যদি
নাহি আসে, দশদিক জেগে ওঠে যদি
দশটি সন্দেহ সম, তখন কোথায়
সুখ? কোথা পথ? জানো কি একেলা কারে
বলে?
রাণু : জানি। বসে আছি ভরা মনে
দিতে চাই, নিতে কেহ নাই।
কবি : সৃজনের
আগে দেবতা যেমন একা। তাই বটে!
তাই বটে! মনে হয় এ জীবন বড়ো
বেশি আছে- যত বড় তত শূন্য, তত
আবশ্যকহীন
রাণু : জয় সিংহ, তুমি তুমি
একা! তাই দেখিয়াছি, কাঙাল যে-জন
তাহারো কাঙাল তুমি! যে তোমার সব
নিতে পারে, তারে তুমি খুঁজিতেছ যেন…
কবি : আয় সখী
চিরদিন চলে যাই দুই জনে মিলে
সংসারের পথ দিয়ে, শূন্য নভস্তলে
দুই লঘু মেঘখণ্ড সম…
এ বাড়িতে সব সময় জনসমাগম, তাই রিহার্সাল হয় পাশের বাড়িতে। কবির খুড়তুতো ভাইরা ব্রাহ্ম হননি, গগন, অবন, সমর তিনজনেই ভাল শিল্পী, রবিকাকার যে কোনও কাজে তারা যোগ দেন, নাটকের ব্যাপারে খুবই উৎসাহ। রাণু রিহার্সালের ফাঁকে ফাঁকে আইসক্রিম কিনে খাবার জন্য পালিয়ে যায়। তা নিয়ে খুব মজা করেন তিন ভাই! এক একজন হঠাৎ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেন, অপর্ণা কোথায়, অপর্ণা পালিয়েছে! অপর্ণা উধাও।
তখন তাকে খুঁজে আনবার জন্য কয়েকজনকে পাঠাতে হয়।
বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে আসেন মহড়া দেখতে। সকলেরই বেশ দৃষ্টি পড়ে থির বিজুরির মতন অপরূপ রূপ লাবণ্যবতী এই কিশোরীটির দিকে। জগদীশচন্দ্র বসু ডেকে জিজ্ঞেস করেন তার পিতৃপরিচয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাশে বসিয়ে একদিন এমন গল্প করতে লাগলেন রাণুর সঙ্গে যে রাণুর পার্ট এসে গেছে, তাকে ডাকাডাকি করা হচ্ছে, শরৎচন্দ্র তবু তাকে ছাড়ছেন না।
মহড়া শেষ হবার পরেও অনেকক্ষণ গল্পগুজব ও পানাহার চলে। কিন্তু কবি আর সেখানে নিজে থাকেন না, রাণুকেও থাকতে দেন না।
তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসেন নিজের ঘরে।
সে রকম ফেরার পথে কবি একদিন বললেন, এবারে তোমার কী যেন একটা পরিবর্তন দেখছি রাণু। তোমাকে যেন অন্যরকম দেখাচ্ছে।
রাণু বলল, আমাকে আবার অন্যরকম দেখাচ্ছে কী করে? আমি তো সেই একই রকম আছি।
কবি বললেন, তোমাকে দেখে অনায়াসে বলা যায়, ওগো, তুমি পঞ্চদশী, পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে।
রাণু বলল, আমি বুঝি চাঁদ? আগে কেউ আমার চাঁদপানা মুখ বললেই আমার রাগ হত।
কবি বললেন, না, তুমি চাঁদ নও। তুমি তুমিই।
মৃদুস্মিত স্বপ্নের আভাস তব বিহ্বল রাতে। কচিৎ জাগরিত বিহঙ্গ কাকলি তব নব যৌবনে উঠিছে আকুলি ক্ষণে ক্ষণে। রাণু, শুধু যেন তাই-ই নয়। তোমাকে আরও অন্যরকম লাগছে।
রাণু বলল, ভানুদাদা, আমি সারাজীবনে তোমার কাছে একটুও বদলাব না। একই রকম থাকব।
মূল অভিনয়ের দু’দিন আগে হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে গেল রাণুর। বাড়াবাড়ি রকমের রিহার্সালে কাবু হয়ে পড়ল, কবি বললেন, আজ রিহার্সাল না দিলেও চলবে। তুমি চুপটি করে শুয়ে থাকো, খবর্দার উঠবে না একবারও।
জোড়াসাঁকোর বাড়ির তিনতলায় একটি ঘরে শুইয়ে রাখা হল রাণুকে। কেউ তাকে ডাকবে না, বিরক্তও করবে না।
রক্তপদ্ম রঙের শাড়ি পরে আছে রাণু, শুয়ে আছে পাশ ফিরে, এক রাশ চুল বিছানার ওপর মেলা। বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ঘরের মধ্যে আধো-অন্ধকার। একজন নাপতেনি হেঁটে আসছে দালান দিয়ে, জানলার ফাঁকে সেই ঘরের মধ্যে চোখ পড়তেই সে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ওমা, ওমা!
অন্য একজন দাসী তাই শুনে কাছে আসতেই সে কাপতে কাঁপতে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই দ্যাখো দ্যাখো,নতুন বউঠান!নতুন বউঠান এসে শুয়ে আছেন।
আরও কয়েকজন এসে উঁকিঝুঁকি মারল। তারাও বলল, হ্যাঁ আচমকা দেখে নতুন বউঠান মতনই মনে হয় বটে। ভয় পাবারই কথা।
কোলাহলে ঘুম ভেঙে গেল রাণুর, সে কিছুই বুঝতে পারল না।
রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই পল্লবিত হয়ে কবির কানে ঘটনাটি পৌঁছোল।
তিনি এসে দেখলেন, রাণু আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ একজন বিজলি বাতি জ্বেলে দিয়েছে। নিশীথ কুসুমের মতন তার মুখখানি স্বপ্ন মাখা।।
কবি তার শিয়রের কাছে বসলেন।
একই রকম মাথার চুল। সে রকমই ললাট। ভুরু ও চোখ দুটিও যেন অবিকল। নাক…তবে ঠোঁটের তলা থেকে অন্যরকম। রাণুর চিবুক আর নতুন বউঠানের চিবুকে কোনও মিল নেই। সব মেয়েদের শুয়ে থাকার ভঙ্গিই কি একরকম? ঘুম আর জাগরণের সময় মেয়েদের চেহারাও অনেক বদলে যায়। ঘুমন্ত নারী যেন মায়া দিয়ে গড়া।
কবি মনে মনে ফিরে গেলেন তার সদ্য যৌবনের দিনগুলিতে। যে নক্ষত্রের আলো তাকে উদ্দীপিত করেছিল সেই সময়, তা লুপ্ত হয়ে গেছে বহুকাল। তাঁর জীবনের এই সন্ধ্যালগ্নে সেই নক্ষত্রই যেন আবার ফিরে এসেছে।
তিনি নিম্ন স্বরে উচ্চারণ করলেন, এই বুঝি মোর ভোরের তারা এল সাঁঝের তারার বেশে…
রাণু চোখ মেলে দেখল, ভানুদাদা তার একটি হাত ধরে বসে আছেন। মুখখানি বিধুর। যেন ভেতরে ভেতরে কষ্ট পাচ্ছেন খুব।
ধড়মড় করে উঠে বসে সে বলল, কী হয়েছে ভানুদাদা?
কবি বললেন, কিছু হয়নি তো। তোমাকে দেখছি।
রাণু আবার জিজ্ঞেস করল, খানিক আগে জানলার কাছে কয়েকজন কী যেন বলাবলি করছিল। কী হয়েছে, বলুন না?
কবি বললেন, আমার আগে ওরাই ঠিক বুঝে ফেলেছে। আমারও একটু একটু মনে হচ্ছিল। তুমি তো হঠাৎ বেশ বড় হয়ে গেছ, এখন তোমার সঙ্গে নতুন বউঠানের মুখের অনেকখানি আদল।
রাণু জানতে চাইল, নতুন বউঠান কে?
কবি বললেন, আমার এক অতি আপন বউঠান, তুমি আর তার কথা জানবে কী করে? সবাইকে কাঁদিয়ে তিনি চলে গেছেন অনেকদিন আগে। তিনি প্রথম আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন খুব কম বয়েসে, আমিও তখন ছোট, দুজনে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছি। এ বাড়িতে আমার সঙ্গেই ছিল তার সবচেয়ে বেশি বন্ধুত্ব। জ্যোতিদাদা কাজেকর্মে খুব ব্যস্ত থাকতেন, আমরা দুজনে একসঙ্গে সময় কাটাতাম, কত গান, কত কবিতা, কত খেলা। আজ হঠাৎ মনে হল, সেই নতুন বউঠানই যেন তোমার মধ্য দিয়ে ফিরে এসেছেন আমার কাছে।
রাণু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, মোটেই আমি নতুন বউঠানের মতন নই। আমি রাণু, আমি ঠিক আমার মতন!
কবি বললেন, তা ঠিক। তুমি শুধু নতুন নও, তুমি অভিনব!
রাণুর কপালে তিনি হাত রাখলেন। বেশ জ্বর এসেছে তার।
বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে টিকিট বিক্রি করে এম্পায়ার থিয়েটারে বিসর্জনের অভিনয় হবে তিন দিন। ডেঙ্গু জ্বরের জন্য প্রথম দিনটিতে রাণুর অভিনয় করা হল না, অন্য একজনকে দিয়ে কাজ চালিয়ে দেওয়া হল।
দ্বিতীয় দিনে রাণু জেদ ধরল, সে স্টেজে নামবেই। জ্বর গায়েই সে স্নান করল, ভাত খেল। মেকআপম্যান দুজন, নন্দলাল বসু আর সুরেন কর। তাঁরা আগে কবিকে সাজালেন। জাদুবলে যেন সেই ষাট বৎসর বয়স্ক কবি হয়ে উঠলেন নবীন যুবা, একেবারে দেবদুর্লভ কান্তি। সবার সামনে রাণু কবিকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, আমার ভানুদাদাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে! এমনটি আর কেউ নেই!
দিনু ঠাকুর হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, রাণুর ভানু! রবিদাদা, সাবধান! অভিনয়ের সময় এ মেয়ে যেন তোমায় ভানুদাদা বলে ডেকে না ওঠে!
রাণু বলল, মোটেই আমার সে রকম ভুল হবে না।
অবন বললেন, যদি হয়ও, থেমে গিয়ে যেন জিভ কেটে ফেলোনা! গড়গড় করে চালিয়ে যাবে!
কোমরবন্ধ ঠিক করতে করতে কবি নন্দলালকে বললেন, এককালে আমিও ছবি-টবি আঁকতুম। রাণুকে আমি নিজে সাজাব, কেমন হয় তোমরা দেখো!
রাণুকে তিনি নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। তার গালে রঙের পোঁচ দিতে দিতে কবি বললেন, রোজ তুমি আমার চুল আঁচড়ে দাও, আজ আমি তোমার চুল আঁচড়ে কেমন সুন্দর খোঁপা বেঁধে দেব দেখবে।
রাণু বলল, খোঁপা বাঁধতে হবে না, চুল খোলা থাক।
কবি বললেন, এত বড় চুল, খোলা রাখলে তুমি বসবার সময় নিজের চুলের ওপরেই বসে পড়বে। তারপর হঠাৎ উঠতে গিয়ে পড়বে ধড়াম করে!
রাণু বলল, না। আমি সাবধানে থাকব। গ্রামের মেয়েরা তো চুল খোলাই রাখে!
কবি বললেন, তুমি যেন কত গ্রামের মেয়ে দেখেছ!
কবি আবার তার খোঁপা বাঁধলেন, আবার খুলে দিলেন। খোলা চুলেই রাণুকে মানাচ্ছে ভাল।
মুখ ও ওষ্ঠ রঞ্জিত করে, ভুরু এঁকে কবি তাকে বললেন, নাও, এবার শাড়ি পরে নাও। কুঁচি দিও না।
নাটক তো জমজমাট হল বটেই, ঘনঘন করতালি ধ্বনি থামতেই চায় না। টিকিট কেটে বিশিষ্ট দর্শকরা তো শুধু ‘বিসর্জন’ দেখতে আসেনি, অনেকেই এসেছে শুধু কবির অভিনয় দর্শন করতে। কিন্তু অপর্ণাবেশী রাণুও কম হাততালি পেল না, এ মেয়েটি ঢুকলেই যেন মঞ্চ আলোকিত হয়ে যায়। সবাই কানাকানি করে, এই মেয়েটি কে? ঠাকুরবাড়ির কারও কন্যা?
অভিনয় শেষে কৌতূহলীরা ঘিরে ধরলেন রাণুকে। অল্পবয়েসী ছেলেরা তার সঙ্গে কথা বলতে চায়।
কবি তার সময় দিলেন না, রাণুকে নিয়ে থিয়েটার হল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন তাড়াতাড়ি। একটা হুড খোলা হাওয়া গাড়িতে ফিরতে লাগলেন জোড়াসাঁকোয়।
কবি বললেন, সবাই তোমার এত প্রশংসা করেছিল, তাতে খুব গর্ব হচ্ছিল আমার। আজ তোমার পার্ট রিহার্সালের চেয়েও অনেক ভাল হয়েছে।
রাণু বলল, ভাল আবার কী! আপনার এত সুন্দর লেখা সব লাইনগুলো শুনলেই তো লোকের ভাল লাগবে। হ্যাঁ, বলতে পারেন,
পার্ট ভুলে যাইনি!
কবি বললেন, লেখা যেমনই হোক, নাটকে অভিনয় ভাল না হলে, মানুষের মর্ম ছোঁয় না।
রাণু বলল, সবই তো আপনার শেখানো!
কবি বললেন, শেখালেই কি সবাই ঠিকঠাক পারে? নিজস্বতাও থাকা চাই। তোমার যে জ্বর হয়েছিল, বোঝা যায়নি একটুও। মুখখানা জ্বলজ্বল করছিল, কী রকম আপনি আপনি কাঁদলে! তবে, একবার চুলের ওপর বসে পড়েছিলে!
রাণু বলল, আছাড় তো খাইনি।
তারপর সে জিজ্ঞেস করল, আপনি যে নতুন বউঠানের কথা বলছিলেন, তিনি কখনও আমার মতন নাটকে অভিনয় করেছেন আপনার সঙ্গে?
কবি বললেন, হ্যাঁ। একবার অলীকবাবু প্রহসনে আমি সেজেছিলাম অলীকবাবু, আর নতুন বউঠান হেমাঙ্গিনী। আর একবার মানময়ী’ নাম দিয়ে একটা গীতিনাট্য হয়েছিল, তাতে আমি মদন, আর উনি উর্বশী।
রাণু বলল, উর্বশী? খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন বুঝি?
কবি বললেন, তোমারই মতন।
রাণু আবার জিজ্ঞেস করল, তিনি গান গাইতে পারতেন?
কবি বললেন, সেটাও তোমার মতন। গান ভালবাসতেন খুব, তেমন গানের গলা ছিল না।
রাণু কবির চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞেস করল, অভিনয় কেমন করতেন? আমি তাঁর থেকে ভাল করিনি? ভানুদাদা, বলুন, আমি বেশি ভাল করিনি?
কবি হাসতে লাগলেন প্রাণখুলে।
সুদীর্ঘ আমেরিকা সফরে কবি বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে পারেননি বটে, কিন্তু একটি রত্ন লাভ করেছিলেন।
সেক্রেটারি পিয়ার্সনের কাছে তিনি জেনেছিলেন, একটি ইংরেজ যুবক নিউ ইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করছে, তার খুব ইচ্ছে সে ভারতের কোনও গ্রামে গিয়ে গরিব মানুষদের জন্য কিছু কাজ করবে।
কবি যুবকটিকে ডেকে পাঠালেন।
যুবকটির নাম লিওনার্ড এল্মহার্স্ট, ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ারে তার জন্ম, সে ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনো করেছে কেমব্রিজে। মহাযুদ্ধ শুরু হলে তাকেও যথারীতি যুদ্ধে যেতে হয়, সৈনিকরূপে সে প্রেরিত হয় ভারতে।
শাসক সম্প্রদায়ের মানুষ হয়েও সে ভারতের গ্রামগুলির দৈন্যদশা দেখে বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েছিল। কৃষিপ্রধান দেশ, অথচ বিজ্ঞানসম্মত উন্নত প্রথায় চাষবাসের কোনও ব্যবস্থাই নেই, সরকার থেকেও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয় না। চাষিদের জীর্ণশীর্ণ চেহারা, স্বাস্থ্যবিধি জানে না, পশুপালন পদ্ধতিতেও পিছিয়ে আছে কয়েকশো বছর। ইংরেজরা এ দেশ শাসন ও শোষণ করবে, বিনিময়ে কিছু দেবে না?
তখনই সে ঠিক করেছিল, তাদের পক্ষ যদি যুদ্ধে জয়ী হয় এবং সে প্রাণে বাঁচে, তা হলে সে আবার ফিরে আসবে ভারতে। তার জাতির পক্ষ থেকে ভারতের ঋণ সে কিছুটা শোধ করার চেষ্টা করবে, একক, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়।
যুদ্ধে তার প্রাণটি গেল না, জয়ীর বেশেই সে ফিরল স্বদেশে। ভারতের দরিদ্র মানুষদের জন্য কিছু একটা করার সঙ্কল্প সে ভোলেনি। কিন্তু ইতিহাসের জ্ঞান নিয়ে সে আর কতটা সাহায্য করতে পারবে? কৃষি ও ফসল উৎপাদনে আমেরিকা বিশেষ উন্নত, সে বিষয়ে উচ্চশিক্ষারও ব্যবস্থা আছে, তাই সে ইতিহাস-পাঠ ছেড়ে আমেরিকায় এসে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো শুরু কIে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে।
কবির কাছ থেকে আহ্বান পেয়ে সে একদিন উপস্থিত হল হোটেলে।
এল্মহার্স্ট যুদ্ধে যোগদান করার জন্য যখন জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছিল, তখন তার কাছে ছিল ‘গীতাঞ্জলি’র ইংরেজি অনুবাদের এক কপি। মাঝে মাঝেই সেই কবিতাগুলি পড়ে সে এক মহান সভ্যতার স্বাদ পেয়েছে। অনেক কবিতা তার কণ্ঠস্থ। সেই কবির সন্নিধানে সে। এসেছে, তাতেই তার রোমাঞ্চ হয়।
কবি কিন্তু অধ্যাত্মবাদ, শান্তি কিংবা বিশ্ব মৈত্রী নিয়ে কিছু বললেন না, তাকে পরিষ্কার ভাষায় জানালেন, তুমি ভারতের গ্রামে গিয়ে কাজ করতে চাও শুনেছি, আমি বাংলার গ্রামাঞ্চলে শান্তিনিকেতন নামে একটি বিদ্যালয় খুলেছি, সেখানে পড়াশুনোর কাজ ভালই হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, শান্তিনিকেতন আশ্রমটি যেন একটি দ্বীপ, কাছাকাছি গ্রামগুলির সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগই নেই। বীরভূমের গ্রামগুলি দিন দিন যেন ধ্বংসের পথে যাচ্ছে, অনেক মানুষ নিরুপায় হয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে। গ্রামের মানুষ যদি খাদ্যপুষ্টিহীন, ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে নৈরাশ্যে ড়ুবে থাকে, তা হলে আমার বিদ্যালয়ে কিছু ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে কী লাভ? তাতে দেশের উন্নতি হতে পারে না। শান্তিনিকেতনের কাছেই সুরুল গ্রামে আমি কিছু জমি কিনে রেখেছি, আমার খুব ইচ্ছে, সেখানে উন্নত ধরনের কৃষি, পশুপালন, হাতের কাজ শিক্ষার একটা কেন্দ্র গড়ে তুলি। কিন্তু তেমন উপযুক্ত লোকবল নেই। তোমার সাহায্য কি পেতে পারি?
এল্মহার্স্ট বলল, আপনি আমাকে সুযোগ দিতে চান, এতে আমি অবশ্যই ধন্য। আপনার সঙ্গ পাওয়াই আমার দারুণ সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু আমি কৃষি বিষয়ে নিজে ভাল করে না জানলে গ্রামের মানুষদের সাহায্য করব কীভাবে? এখানে তা নিয়েই পড়াশুনো করছি, সম্পূর্ণ করে পরীক্ষাটা দিতে চাই।
কবি বললেন, বেশ তো, পরীক্ষা শেষ হলে আমায় জানিও।
তারপর কবি দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। এল্মহার্স্টও পরীক্ষা শেষ হলে ইংল্যান্ডে এসে কবিকে চিঠি লিখলেন, এখন আসতে পারি?
কবির বদলে উত্তর দিলেন অ্যান্ড্রুজ। না, এসো না। এখানে তোমার কাজ চালাবার মতন অর্থের জোগান দেবার মতন সামর্থ্য আমাদের নেই।
অ্যান্ড্রুজের ওপর শান্তিনিকেতন পরিচালনার অনেকখানি ভার। তিনি নিজের দায়িত্বেই এই সিদ্ধান্ত নিলেন, না কবিও মত বদলেছেন, তা বোঝা গেল না।
এতেও দমবার পাত্র নন এল্মহার্স্ট।
সে আমেরিকায় গিয়ে শুধু চাষবাস নিয়ে পড়াশুনোতেই ড়ুবে থাকেনি, সে রসেবশে থাকার মানুষ, সেখানকার সমাজের নানান স্তরে মিশেছে, আমোদ-ফুর্তিও করেছে, ডরোথি স্ট্রেইট নামে এক বিধবা রমণীর সঙ্গে পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা ও প্রণয়ও হয়ে গেছে এর মধ্যে।
ডরোথির অনেক গুণ, শুধু দোষের মধ্যে এই, সে বড় বেশি ধনী। বিশাল পৈতৃক সম্পত্তি তো আছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মৃত স্বামীর বিশাল ঐশ্বর্য। আমেরিকার উচ্চ সমাজে তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাওয়ার মতন অবস্থা, কিন্তু সে আকৃষ্ট হয়েছে এক সাধারণ ঘরের ইংরেজ যুবকের প্রতি।
এল্মহার্স্ট ইচ্ছে করলেই ডরোথিকে বিবাহ করে বিলাসী জীবন কাটাতে পারে, কিন্তু ভারতের গ্রামে গিয়ে কিছুদিন অন্তত শ্রমদান করতে সে বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ। প্রণয় ও বৈভব লাভের বিনিময়েও সে সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করতে চায় না। আবার ডরোথির পক্ষেও তার সঙ্গিনী হয়ে ভারতের গ্রামের জল-কাদায়, মশা-মাছির মধ্যে দিন কাটানোর প্রশ্নই ওঠে না। একেই বলে উভয় সঙ্কট।
এই ডরোথি স্ট্রেইট নামে ধনবতী মহিলাই কবির আমেরিকা সফরের সময় বিশ্বভারতীয় জন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার সাহায্য করার জন্য উদ্যত হয়েও অন্যের প্ররোচনায় নিরস্ত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইস্কুল সম্পর্কে তার এখনও কোনও আগ্রহ নেই, কিন্তু তার প্রেমিক যদি কোনও শখ মেটাতে চায়, তাতে ডরোথির কার্পণ্য নেই, যাকে বলে গড ফরসেকেন প্লেস, সেরকম কোনও গ্রামে গিয়ে অ্যাডভেঞ্চার করার ইচ্ছে হয়েছে এমহাস্টের, কিছুদিন সে সাধ মিটিয়ে আসুক, সে জন্য ডরোথি এখনই পাচিশ হাজার ডলার দিতে প্রস্তুত।
টাকার কথা জানিয়ে, অবিলম্বে শান্তিনিকেতনে এসে উপস্থিত হল এল্মহার্স্ট।
কবি দুই ইংরেজ তত্ত্বে বিশ্বাসী। এক ধরনের ইংরেজ অস্ত্র উঁচিয়ে অন্য দেশ দখল করতে যায়, সেখানে যথেচ্ছ শোষণ ও অত্যাচার চালায়, জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার মতন বর্বরতা প্রদর্শন করে। আবার সেই ইংরেজ জাতির মধ্যে এমন মানুষও আছে যারা কাব্যসাহিত্যে, দর্শনে-বিজ্ঞানে কত উন্নত, নিষ্ঠাবান মানবতাবাদী। পরদুঃখে কাতর। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজদেরই প্রতিনিধি অ্যান্ড্রুজ, পিয়ার্সন, এল্মহার্স্ট।
অ্যান্ড্রুজ, পিয়ার্সন শান্ত ও প্রৌঢ়, এদের তুলনায় এমহার্স্ট বয়েসে নবীন তো বটেই, দীর্ঘকায়, সুদর্শন ও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। কয়েক দিনেই সে মাতিয়ে তুলল শান্তিনিকেতন। বাংলা শিখতে শুরু করে এগিয়ে যেতে লাগল চমকপ্রদভাবে।
কবির ভাই বোনদের মধ্যে একমাত্র বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ পাকাপাকিভাবে বসতি নিয়েছেন শান্তিনিকেতনে, অন্য কেউ কদাচিৎ আসেন। ওঁর ছেলে দীপেন্দ্রনাথ বা দীপুবাবুও এখানে থাকেন অধিকাংশ সময়, তিনি সাহায্য করেন তদারকিতে। এল্মহার্স্ট এঁদের সঙ্গে আলাপ করে এঁদের অভিজাত অথচ সহজ, সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যায়। দীপুবাবুর স্ত্রী হেমলতা সকলের বড়মা, তিনিই নিয়েছেন এই তরুণ, উৎসাহী ইংরেজ ছাত্রটিকে বাংলা শেখাবার ভার।
গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনকে উপলক্ষ করে কিছুটা অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। গান্ধীজি অসহযোগের ডাক দিয়েছেন, সরকারের সঙ্গে, কোনও ইংরেজের সঙ্গেই দেশের মানুষ সহযোগিতা কিংবা যোগাযোগ রক্ষা করবে না। ছাত্র-ছাত্রীরা ছেড়ে আসবে স্কুল কলেজ, বিলিতি বস্ত্র বর্জন করে সকলে চরকায় সুতো কাটবে। এই উপায়ে এক বৎসরের মধ্যে এসে যাবে স্বরাজ।
কবি এই নীতি ও পথ মানতে পারেননি। জ্ঞান অর্জনের পথ রুদ্ধ করে দেবার তিনি ঘোর বিরোধী। এল্মহার্স্টও তো ইংরেজ, তার নিঃস্বার্থ সহযোগিতা গ্রহণ না করার কী যুক্তি থাকতে পারে? এর মধ্যে কলকাতায় গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি আলোচনা হয়েছে সুদীর্ঘ সময় ধরে। কবিকে দলে টানতে না পেরে তিনি শেষ পর্যন্ত অনুরোধ করেছিলেন, গুরুদেব, আপনি অন্তত চরকা কেটে সুতো বুনতে শুরু করুন, তাতে আপনার দৃষ্টান্তে অনেকে অনুপ্রাণিত হবে। কবি সহাস্যে বলেছিলেন, মহাত্মাজি, আমি শব্দের সঙ্গে শব্দ বয়ন করে গান বা নাটক রচনা করতে পারি, কিন্তু আপনার ওই তুলো থেকে সুতো বুনতে গেলে সেই তুলোরই চরম দুর্গতি হবে।
এই আলোচনার সময় কবির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করবার জন্য একদল লোক জোড়াসাঁকোর প্রাসাদের প্রাঙ্গণে কিছু বিদেশি কাপড়ে আগুন ধরিয়ে বিকট উল্লাসের ধ্বনি তুলেছিলেন। পত্র-পত্রিকাতেও বিদ্রুপ বর্ষিত হচ্ছিল তাঁর নামে। কবি তবু নিজের বিশ্বাসে অটল।
তাঁর অনুপস্থিতিতে শান্তিনিকেতন বিদ্যাশ্রমেও কিছু ছাত্র ও অধ্যাপক মেতে উঠেছে রাজনীতিতে, এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ আসবে এই উন্মাদনায় তারা কবির বদলে গান্ধীজির পথ ধরে চলতে চায়, এর পেছনে আছে অ্যান্ড্রুজের প্রশ্রয়। কবি এ জন্য বেদনা বোধ করছেন, প্রয়োজনে অবাধ্য ছাত্র-শিক্ষকদের আশ্রম থেকে সরিয়ে দিতেও দ্বিধা বোধ করবেন না। এল্মহার্স্টকে বলে দিয়েছেন তার কাজের প্রস্তুতি পূর্ণ উদ্যমে চালিয়ে যেতে।।
বাংলা শিখতে গিয়ে এল্মহার্স্টের সঙ্গে দীপুবাবুর প্রায়ই দেখা হয়। মানুষটি ভোজন ও আচ্ছা, দু’ব্যাপারেই খুব রসিক। এল্মহার্স্টকে দেখলেই গল্প করেন কিছুক্ষণ। একদিন বললেন, জানো সাহেব, একবার আমার খুব পেট খারাপ হয়েছিল। তখন গান্ধীজি এসেছিলেন আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। আমার অসুখের কথা শুনে বললেন, নিশ্চয়ই তোমার ভেতরে কোনও গোপন পাপ আছে। পাপ থাকলেই তা রোগ হয়ে ফুটে বেরোয়। কী অদ্ভুত কথা! আসলে আমি তখন খুব দুধ খেতাম, তা হজম হত না। কিছুদিন আগে শুনলাম, গান্ধীজি খুব আমাশায় ভুগছেন। আমি অমনি টেলিগ্রাম করলাম, এবার আপনার ভেতরে কী পাপ আছে খুঁজুন! হা-হা-হা! উনি তো ছাগলের দুধ খান, বেশি বাড়িয়েছেন বোধহয়। বলল সাহেব, মানুষের পেটে ছাগলের দুধ সহ্য হয়!
গল্প বলতে বলতে নিজেই উচ্চহাস্যে ঘর ফাটান। এল্মহার্স্টও এই সব গল্প উপভোগ করে, এতে তার বাংলা শিক্ষা এগোয়।
ডরোথির টাকায় একটা ট্রাক কেনা হয়েছে, তাতে মালপত্র পাঠানো হচ্ছে সুরুলে। সেখান তার নিজের এবং কর্মীদের জন্য আবাস নির্মাণের কাজও চলেছে। কবির পুত্র রথীকে সে সঙ্গে পেয়েছে, রথীও কৃষি বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে এসেছে আমেরিকা থেকে, এতদিনে তা বিশেষ কাজে লাগায়নি, এ ছাড়া রয়েছে সন্তোষ ও কালীমোহনের মতন কয়েকজন, এখানকার গ্রাম সম্পর্কে যাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। সবাই মিলে তৈরি করা হচ্ছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।
এখানে মাঝে মাঝে এল্মহার্স্ট একটি তরুণী মেয়েকে দেখতে পায়, সে যেন সবার চেয়ে আলাদা।
সে যেন হাঁটে না, বাতাসে ওড়ে। সত্যিই সে যখন ছুটে ছুটে চলে, তার শাড়ির আঁচল ওড়ে পতাকার মতন। সে যখন কোনও গাছতলায় দাঁড়ায়, মনে হয় যেন স্থির চিত্র।
তাকে প্রায় সময় দেখা যায় কবির কক্ষে, আবার কখনও গাছতলার ক্লাসে বসে থাকে, কখনও এমনকী রান্নাঘরে। মাঠের মধ্য দিয়ে যাওয়া আসার সময় কয়েকবার এমহার্স্ট তার মুখোমুখি হয়েছে, কিন্তু কথা বলেনি। এ দেশীয় মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় না হলে কথা বলা যায় কিনা, তা সে জানে না। একবার একেবারে সামনাসামনি চোখাচোখি হতে এল্মহার্স্ট অভ্যেসবশত বলেছিল, হ্যালো। মেয়েটি উত্তর না দিয়ে শুধু তাকিয়েছিল ডাগর চোখে। এল্মহার্স্ট পরে ভেবেছে, হয়তো তার বলা উচিত ছিল, নমস্কার।
মেয়েটির মুখশ্রী অতি অপূর্ব তো বটেই, চমৎকার তার শরীরের গড়ন। মাঝে মাঝে সে উত্তর ভারতীয়দের মতন সালোয়ার কামিজ পরে, তখন বোঝা যায়, তার পা দুটি অনেক ইউরোপীয় রমণীরও ঈর্ষাযোগ্য। সবচেয়ে আকর্ষণীয় অবশ্যই তার দুটি চক্ষু, যেন সব সময় বিস্ময়ে ভরা, যেন সে স্বপ্নরাজ্যের অধিবাসী, এখানকার কেউ নয়।
ঠাকুর পরিবারের ক’জন এখানে থাকেন, তা এল্মহার্স্টের জানা হয়ে গেছে। পরিচয় হয়েছে অধ্যাপকদের সঙ্গে, তাঁদের স্ত্রীদেরও দেখেছে। কবির দু’একজন বন্ধু এখানে আলাদা বাড়ি করেছেন, মাঝে মাঝে এসে থাকেন, এ মেয়েটি কিন্তু তাঁদের কেউ নয়।
একদিন কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে এমহার্স্ট দরজার কাছে। দাঁড়িয়ে দেখল, কিছু একটা পরিহাসের পর সেই মেয়েটি আর কবি খুব হাসছেন। মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে কবির কাঁধ ঘেঁষে।
এ সময় প্রবেশ করা উচিত কিনা ভেবে সে দ্বিধাগ্রস্ত হল। অবশ্য কবিই তাকে তলব করেছেন। সেই মেয়েটিই প্রথম তাকে দেখতে পেয়ে ভেতরে আসার জন্য চোখের ইঙ্গিত করল। কবি মুখ ফিরিয়ে বললেন, এসো লেওনার্ড।
শুরু হল কাজের কথা।
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাঠামো তৈরি হয়ে গেছে। বাকিটা লেওনার্ড ও তার সহকর্মীরাই শেষ করতে পারবে। শান্তিনিকেতনের আটটি ছাত্র ওখানে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু এল্মহার্স্টের একটা শর্ত আছে, ছাত্রদের চব্বিশ ঘণ্টাই ওখানে থাকতে হবে, রাত্রে শান্তিনিকেতন ফেরা চলবে না। কোনও ভৃত্য রাখা হবে না। ঘর পরিষ্কার থেকে রান্নাবান্না সবই প্রত্যেককে করতে হবে নিজের হাতে। কবি কি এতে সম্মত আছেন?
কবি বললেন, অবশ্যই। রাত্রে ফেরার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। যেসব নিয়ম-কানুন ঠিক করে দেওয়া হবে, তা কেউ অমান্য করলে শাস্তি দিতে দ্বিধা কোরো না। তবে রান্নার ব্যাপারটা, আমি জানি না এরা কতখানি পারবে, হয়তো প্রথম প্রথম সাহায্যের দরকার হবে।
একটি ছাত্র সম্পর্কে এল্মহার্স্টের খটকা আছে। তার নাম সুবীর, সে কবির মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথের নাতি, সুরেন ঠাকুরের ছেলে। তার ঠাকুমা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী অতি জাঁদরেল মহিলা, এল্মহার্স্ট এর মধ্যেই লোকমুখে শুনেছে, এবং নাতিটি তাঁর খুব আদরের। সেও কি অন্যদের মতন সুরুলে রাত্রিবাস করবে?
এই প্রশ্ন করতেই কবি বললেন, ঠাকুর পরিবারের ছেলেরা অন্যদের থেকে আলাদা কীসে? আমার ছেলে রথী এখানকার অন্য ছাত্রদের সঙ্গেই মিলেমিশে থেকে লেখাপড়া শিখেছে।
মেয়েটি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়, এল্মহার্স্ট কথাবার্তা শেষ করে চলে যাবার পরেও সে এখানে থাকবে।
কিছুক্ষণ পরে কবির খেয়াল হল।
তিনি বললেন, ও তোমাদের তো ফর্মালি পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। এই বালিকাটির নাম–
রাণু চোখ পাকিয়ে বলল, বালিকা?
কবি সহাস্যে বললেন, তাই তো, কখন যে বড় হয়ে গেছে, মনেই থাকে না। ইয়াং লেডি বলা উচিত। এই ইয়াং লেডির নাম শ্রীমতী রাণু অধিকারী, আর এই তরুণ ইংরেজটি লিওনার্ড এন্মহার্স্ট, রাণু এস্রাজ বাজায় আর আমার লেখায় বিঘ্ন ঘটায়, আর এই সাহেবটি গ্রাম বাংলা সুজলা সুফলা করে দেবে।
রাণু বলল, এঁকে আমি অনেকবার দেখেছি।
এল্মহার্স্ট করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে নিয়েও তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে নিয়ে যুক্তকরে বলল, নমস্কার।
রাণুও নমস্কার করে জিজ্ঞেস করল, আপনি বাংলা জানেন?
এল্মহার্স্ট বলল, একটু একটু।
রাণু বলল, আমিও একটু একটু ইংরিজি জানি।
কবি বললেন, একজন এক ঝুড়ি ভাল আম দিয়ে গেছে। লিওনার্ড, তুমি আম খাও?
তক্ষুনি ঘরে ঢুকলেন অ্যান্ড্রুজ।
কবি বললেন, স্যার চার্লস তো ওসব ছুঁয়েও দেখেন না।
অ্যান্ড্রুজকে কবি মাঝে মাঝে কৌতুক করে স্যার চার্লস বলে সমোধন করেন। উনি পেটরোগা মানুষ, খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে খুব খুতখুতে।
তিনি দু’হাত নাড়লেন।
এমহার্স্ট বলল, আম তো অতি উপাদেয় আর স্বাস্থ্যকর ফল।
রাণু একটা পাকা আম দিল এল্মহার্স্টের হাতে। এল্মহার্স্ট সেটা নিয়ে কী করবে বুঝতে পারল না। ছুরি দিয়ে খোসা না ছাড়িয়ে খাবে কী করে।
রাণু আর একটা আম নিয়ে বলল, এই দেখুন। প্রথমে দু’হাতে আমটাকে একটু পাকিয়ে তুলতুলে করতে হয়। তারপর–
রাণু সেই প্রক্রিয়াটি দেখাতে দেখাতে তার শুভ্র দাঁতে আমটার তলার দিকের খোসা খানিকটা ছিঁড়ে ফেলল। তারপর চুষতে চুষতে এল্মহার্স্টের দিকে চোখের ইঙ্গিতে বলল, এরকম করুন।
এল্মহার্স্ট কবির দিকে তাকিয়ে বললেন, কত কিছু শেখার আছে।
অ্যান্ড্রুজের সব সময় অতি ব্যস্ততার ভঙ্গি। তিনি বললেন, গুরুদেব, আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।
তারপর তিনি অপর দু’জনের দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেন এরা থাকলে সেই গোপন কথা বলা চলবে না।
রাণু ওঁর পেছন থেকে এমন একটা মুখভঙ্গি করল, যা দেখে এল্মহার্স্ট হাসি চাপল অতি কষ্টে।
রাণুই বেরিয়ে গেল আগে।
অ্যান্ড্রুজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কবি একবার জানলা দিয়ে দেখলেন, আম্রকুঞ্জ দিয়ে এল্মহার্স্ট আর রাণু হেঁটে যাচ্ছে পাশাপাশি।
রাণুর সম্প্রতি এক বিশেষ জ্বালা হয়েছে।
সবাই তাকে দেখলেই বলে, তুমি কী সুন্দর, তুমি কী সুন্দর! সমবয়সী থেকে বুড়োরা পর্যন্ত।
রাণু বুঝতেই পারে না, সে কীসের সুন্দর। তার দিদিরা আরও বেশি। সুন্দর। সবাই তো সুন্দর। যে যার মতন।
আর সুন্দর হলেই বা কী, তা সর্বক্ষণ বলতে হবে কেন? এক একটা গাছ, কত ফুল, কত প্রজাপতি সুন্দর। ফাল্গুন মাসের বাতাস সুন্দর, নদীর ওপর বৃষ্টি পড়া সুন্দর, মাটিতে লুটোনো জ্যোৎস্না সুন্দর, পৃথিবীতে কত কিছু সুন্দর আছে, তা বলে কি লোকেরা সব সময় সে সব দেখে সুন্দর সুন্দর বলে লাফাচ্ছে?
কাশীর রাস্তায় আজকাল মাঝে মাঝেই এক একটা ছেলে তার হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিয়ে পালিয়ে যায়। সে চিঠির প্রথম লাইন, বাংলা বা হিন্দিতে হবেই, তুমি কী সুন্দর! বাকিটা আর পড়ে না রাণু, ছিঁড়ে ফেলে দেয়।
শান্তিনিকেতনেও অনেক বয়স্ক ব্যক্তির রাণুকে একলা দেখলেই গলার আওয়াজ বদলে যায়। কেমন যেন গদো গদো ভাব। রাণুর ভাল লাগে না।
এই তো সেদিন তপনদাদা সন্ধেবেলা একটা ছাতিম গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিলেন, রাণুকে দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। প্রথমে কিছুই বললেন না, রাণুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ছাতিম গাছে অনেক ফুল এসেছে। সেই ফুলে কেমন যেন মশলা মশলা গন্ধ, সেই গন্ধে মাদকতা আসে।
রাণুর অস্থিরতা দেখে একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছ রাণু?
এই কথাটা অনেক রকম ভাবে বলা যায়, এক এক রকম উচ্চারণে বদলে যায় অর্থ। আগে থেকে উত্তর জেনেও এরকম প্রশ্ন কেন করে মানুষ?
কাছেই কবির নতুন মাটির বাড়ি। জানলায় জ্বলছে আলো, রাণু আঙুল দিয়ে সেই দিকে দেখাল।।
তপনদাদা বললেন, কী সুন্দর হয়েছ তুমি। তোমাকে দেখে কালিদাসের সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব’র কথা মনে হচ্ছে।
রাণু বলল, ওসব বলবেন না তপনদাদা।
তপনদাদা বললেন, কেন, কেন, কেন? মহান কবির কাব্যে যেমন লেখা হয়েছে, তা যদি চোখের সামনে দেখতে পাই, তখন যে বিস্ময়ের চমক লাগে।
কালিদাস বুঝি আমাকে দেখে লিখেছেন?
কবিদের সুদুর দৃষ্টি থাকে। তিনি এক সময় কল্পনায় যে রূপ দেখেছিলেন, তা তোমার মধ্যে জীবন্ত হয়েছে!
আমি এখন যাই?
আর একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে যাও না। রোজই ভাবি, তোমাকে একটা কথা বলব।
বলুন না।
অমন করে কি ঝট করে বলা যায়? এ তো কাজের কথা নয়, মনের কথা। তুমি এত সুন্দর রাণু, তোমাকে দেখতে দেখতেই–
তা হলে আমি এখন আর দাঁড়াতে পারছি না।
সঙ্গে সঙ্গে রাণু ছুট লাগাল।
তার বলতে ইচ্ছে হল, সুন্দর হয়েছি তো বেশ করেছি, তাতে আপনার কী?
একমাত্র তার ভানুদাদা কখনও তাকে তুমি কি সুন্দর, তুমি কি সুন্দর বলেন না। ভানুদাদা তো তার বন্ধু। বন্ধুর সঙ্গে কখনও খুব ভাব, কখনও আড়িও হয়। কখনও অভিমানে কথা বন্ধ হয়ে যায়, আবার এক ঘণ্টার মধ্যে গলা জড়িয়ে কত কথা। কখনও হাসি, কখনও কান্না। রাণু তত কাঁদেই, সে যেদিন কাশীতে ফিরে যায়, সেদিন ভানুদাদার চোখও চিকচিক করতে দেখেছে।
ভানুদাদার ঘরে বেশি মানুষজনের ভিড় দেখলে রাগ হয় রাণুর। সে তো আর সর্বক্ষণ এখানে থাকে না, ছুটি পেলেই চলে আসে। সেই কটা দিন সে ভানুদাদাকে আপন করে পেতে চায়।
যদিও সে মনে মনে জানে, তা সম্ভব নয়। তোকজন তো আসবেই। ভানুদাদা যে বিরাট মানুষ, তিনি কত রকম কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। এত রকম কাজ করতে ভালও বাসেন, আবার কাজ থেকে যখন তখন ছুটি নিতেও ওঁর মন আনচান করে। বেড়াতে ভালবাসেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরছেন, যে কোনও জায়গা থেকে আমন্ত্রণ এলেই রাজি হয়ে যান, অথচ নিজের ঘরের নিভৃত কোণটিই যেন তাঁর বেশি প্রিয়।
লোকের সামনে ভানুদাদা এক এক সময় মজা করে বলেন, এই রাণু যখন তখন এসে আমার কাজে বিঘ্ন ঘটায়, লেখা থামিয়ে দেয়।
অথচ রাণু যদি একবেলা ওঁর সঙ্গে দেখা না করে, অমনি তিনি অস্থির হয়ে বনমালীকে দিয়ে তাকে ডেকে পাঠান। বকুনির সুরে বলেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?
আবার শিগগিরই তিনি কোন দূর বিদেশে চলে যাবেন।
কবি কিছু লেখায় মগ্ন হয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে আছেন। রাণু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে উঠল : ভানু সিংহ, তুমি বুঝি একা! তাই দেখিয়াছি, কাঙাল যে-জন তাহারো কাঙাল তুমি! যে তোমার সব নিতে পারে, তারে তুমি খুঁজিতেছ যেন…
কবি পেছন ফিরে তাকালেন। লেখা থেকে মন ফিরিয়ে এনে বললেন, আয় সখী, চিরদিন চলে যাই দুই জনে মিলে সংসারের পথ দিয়ে…..তারপর কী যেন?
রাণু হাসতে হাসতে নুয়ে পড়ে বলল, তোমার নিজের লেখা মনে থাকে না?
কবি বললেন, এত মনে রাখা মানুষের পক্ষে সম্ভব? কত রাশি রাশি পৃষ্ঠা ভরিয়েছি। নিজের নাটকের পার্ট ভুলে যাই। কত গানের বাণী মনে করতে পারি না।
একটু থেমে বললেন, রাণু, তুমি যেই নাটকের সংলাপ বললে, শুনতে শুনতেই মনে হল, আর একটা নতুন নাটক লিখতে হবে, তাতে তুমি অভিনয় করবে। মাঝখানে মুক্তধারা হয়ে গেল, তখন তো তোমাকে পাওয়া গেল না। অবশ্য মুক্তধারায় ঠিক তোমার মানানসই কোনও ভূমিকাই ছিল না। অবশ্য ফুলওয়ালি সাজতে পারতে, ছোট পার্ট। নতুন নাটকে তুমিই হবে প্রধান। একটা চরিত্রও মনে এসে গেল।
রাণু কাছে এসে বলল, কী রকম, কী রকম, বলো না!
কবি বললেন, আর একটু দানা বাঁধুক মাথার মধ্যে। আগেই মুখে বলে দিলে অনেকটা আবেগ ক্ষয়ে যায়।
রাণু বলল, ভানুদাদা, তুমি লিখছিলে লেখো। আমি কি তোমার এখানে চুপটি করে বসে থাকতে পারি?
কবি বললেন, তুমি শুধু বসে থাকবে না, তুমি আমার সঙ্গে গল্প করবে। তোমার কথা না শুনলে যে আমার লেখায় ভাব আসে না।
রাণু বলল, এখন তো আর আমি ছোট্টটি নই। এখন মাঝে মাঝে—
কবি সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, খবর্দার, খবুদার, তুমি বেশি বড় হয়ে যেও না।
রাণু বলল, শোনো না, এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি যখন এসে তোমার লেখা থামিয়ে দিই, কত লোক তোমার লেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকে—
কবি বললেন, আমি খুবই ব্যস্ত, কেজো মানুষ। আবার আমি নিঃসঙ্গ, অকর্মার ধাড়ি। আমাকে এই দু’ভাবেই তোমাকে দেখতে হবে। রাণু, যেখানে আমি সকল লোকের, সেখানে আমি সংসারের কাজ করবার ক্ষেত্রে, যেখানে আমাকে যদি না চিনতে পারো, তা হলে আমার কাছে এসেও আমার আসল কাছে আসা হবে না। আবার আমি খুব ছোটও বটে, … তুমি আমাকে দেখবে শুনবে খাওয়াবে পরাবে সাজাবে, আমার সে বয়েসও আছে। তাই সন্ধ্যাবেলায় মোড়ায় বসে তুমি যখন আমার কাছে নানা বিষয়ে গল্প বলে যাও, সে আমার খুব মিষ্টি লাগে—সন্ধ্যা আকাশের তারা ঈশ্বরের খুব বড় সৃষ্টি, কিন্তু সন্ধ্যায় তোমার মুখের কথাগুলি তার চেয়ে কম বড় নয়—ওই তারার আলো যেমন কোটি কোটি যোজন দূরের থেকে আসছে—তেমনই তোমার হাসি গল্প শুনতে শুনতে মনে হয় যেন কত জন্ম-জন্মান্তর থেকে তার ধারা সুধা স্রোতের মতন বয়ে এসে আমার হৃদয়ের মধ্যে এসে জমছে।।
রাণু আচ্ছন্নের মতন হয়ে গিয়ে বলল, ভানুদাদা, আমি এসব ঠিক বুঝতে পারি না।
কবি বললেন, তোমাকে সব বুঝতেও হবে না। তুমি তো তুমিই ওগো, সেই তব ঋণ–।
তারপর তিনি হঠাৎ হেসে উঠে বললেন, সকাল থেকে তোমার আঁচলের আভাসটুকুও দেখা যায়নি। তাই তো আমার চুলেও চিরুনির ছোঁওয়া লাগেনি, তা তোমার নজরেও পড়ছে না?
রাণু ত্ৰস্তে বলল, ওমা, তাই তো। এক্ষুনি আঁচড়ে দিচ্ছি।
সে দেরাজ থেকে চিরুনি বার করে কবির কোলে বসে গলা জড়িয়ে ধরল।
কবি বললেন, এ জায়গাটা বড় বেশি শূন্য ছিল, এখন পূর্ণ হল। এবার তোমার গল্প বলো। সকালে কোথায় গিয়েছিলে?
এল্মহার্স্ট সাহেবের সঙ্গে সুরুলের কাজ দেখতে গিয়েছিলাম।
এল্মহার্স্টের সঙ্গে বুঝি তোমার বেশ ভাব হয়েছে?
হ্যাঁ, আমি ওঁর কাছে ইংরিজি শিখছি।
শুধু ইংরিজি শিখছো? মানুষটাকে ভাল লাগে না?
তাও লাগে। মানুষটা ভারী মজার। সুরুলে যে ইনস্টিটিউট ফর রুরাল রিকস্ট্রাকশান হয়েছে—এটার ইংরিজি নাম কেন? শান্তিনিকেতনের মতন একটা সুন্দর নাম দাওনি কেন?
দেব। ভাবছি। এখন ওই নামেই কাজ চলুক। তোমার গল্পটা বলো।
হ্যাঁ, ওখানে এল্মহার্স্ট সাহেব সব কিছু গড়ে তোলার জন্য তো অসুরের মতন খাটছে, আবার তার মধ্যেই ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল নিয়ে পেটাপেটি করে, ক্রিকেট খেলে, গান গায়। এই সাহেবটা তোমার ওই অ্যান্ড্রুজ সাহেবের মতন গোমড়া মুখো নয়।।
অ্যান্ড্রুজ যে বয়েস কমাবার মন্ত্র জানে না। এমহাস্টের মস্ত সুবিধে, তার বয়েস কমাবার চেষ্টাও করতে হয় না। সে তোমার ভানুদাদার চেয়েও তরুণ।
আহা, আমার ভানুদাদার সঙ্গে বুঝি কারুর তুলনা চলে! তারপর শোনো না, সুরুলে কী সব মজার কাণ্ড হয়েছে।
শুনি শুনি, তোমার মুখ থেকেই রিপোর্ট শোনা যাক।
তোমার মেজ বউদিদির সঙ্গে এল্মহার্স্টের তর্ক হয়েছে। কী যেন তোমার মেজ বউদিদির নাম?
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী।
এল্মহার্স্ট তো ওই নামটা উচ্চারণ করতেই পারে না। বলে গ্যান্ডানান্ডিন!
কিন্তু আমি তো এল্মহার্স্টকে তর্ক করতে বারণ করেছিলাম। আমার মেজো বৌঠানের কথার ওপর পৃথিবীর আর কারুর কথা চলে না। কী তর্ক হল এমহাস্টের সঙ্গে?
ওঁর নাতি সুবীর তো ওখানে হাতের কাজ শিখছে। এল্মহার্স্ট নিয়ম করেছে, ওখানে মেথর রাখা হবে না, চাকর রাখা হবে না, সব ছেলেদেরই বাথরুম পরিষ্কার করতে হবে। ঘর ঝাঁট দিতে হবে। নিজের হাতে সব কাজ শিখতে হবে। রাত্তিরে ওখানেই শুতে হবে সকলের সঙ্গে।
সে তো জানিই।
সুবীর বোধহয় মজা করে তার ঠাকুমাকে বলেছিল যে, একদিন তার হালুয়ায় মাছি পড়েছিল আর সারাদিন সে রোদুরে মধ্যে মাথায় করে তক্তা বয়েছে। তাই শুনে ঠাকুমা চটে আগুন। তিনি সুরুলে নিজে গিয়ে দেখে শুনে এল্মহার্স্টকে বললেন, আমার নাতি কি কুলির কাজ আর মেথরের কাজ করবে? তোমরা ভেবেছটা কী? তাতে এল্মহার্স্ট বললে, সুবীর স্বাবলম্বী হতে শিখছে, তা ওর ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক কাজে লাগবে! সুবীরের ঠাকুমা তা মানতে চাইলেন না।
কবি গম্ভীর হয়ে রইলেন।
তিনি জানেন, মেজবউঠান এই শান্তিনিকেতনের কোনও কিছুই পছন্দ করেন না, তাঁর মতে, এ সবই অকাজের কাজ। কিন্তু সুবীরকে তো জোর করে আনা হয়নি। সুরেন সব সময় তার রবিকাকার সব কাজের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, সে-ই তার ছেলেকে এখানে পাঠিয়েছে।
রাণু বলল, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সুবীরকে জোর করে সন্ধেবেলা নিয়ে এসেছেন। সে সুরুলে কাজ করলেও শান্তিনিকেতনে এসে রাত্রে ঘুমোবে। তার দেখাদেখি আরও দু তিনটি ছেলে শান্তিনিকেতনে বাবা-মায়ের কাছে চলে আসছে।
কবি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, যে-সব ছাত্র শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবে, ঠাকুর বাড়ির হোক বা যে বাড়িরই হোক, তাদের বিদেয় করে দিতে হবে।
তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যাক ও কথা। এলমহার্স্টের সঙ্গে তোমার আর কী কী গল্প হল বলো।
রাণু বলল, আমি সাহেবের কাছে ইংরিজি ঝালিয়ে নিচ্ছি, সেও আমার কাছে টুকটাক বাংলা কথা শিখে নিচ্ছে। তোমার গানও শিখতে চায়। আমাকে বলল, শেখাও। আমি কি আর গান গাইতে পারি। তাই ওকে এস্রাজ বাজিয়ে শোনালাম, তোমারই গান, ওই যে সেই গানটা, ‘ওদের সাথে মেলাও যারা চরায় তোমার ধেনু…’।
কবি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় বসে শোনালে?
রাণু বলল, হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম খোয়াইয়ের ধারে। সেখানে বেশ নিরিবিলি।
কবি বললেন, বাঃ। তা হলে এল্মহার্স্টের সঙ্গে তোমার বেশ ভাব জমেছে বলো!
রাণু মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, হ্যাঁ, হয়েছেই তো। তুমি যদি এরপর আবার অ্যান্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গম্ভীর গম্ভীর কথা বলল, আমার দিকে না তাকাও, তা হলে আমি এহাস্টের কাছে চলে যাব।
কবি ছদ্মাত্রাসে বললেন, তা হলে তো আমার পক্ষে খুব বিপদের কথা। অ্যাজকে সংযত করতেই হবে, এল্মহার্স্টের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামলে কি আমি পারব? শোনো রাণু, তুমি আমার সঙ্গে শিলং পাহাড়ে যাবে?
রাণু বলল, শিলং পাহাড়? সে তো খুব সুন্দর জায়গা। বাবা কি আমাকে যেতে দেবেন?
কবি বললেন, আমি তোমার বাবাকে লিখব। ওঁরাও সকলে মিলে যেতে পারেন। এখান থেকে বড় দল যাবে, কোনও অসুবিধে হবে না।
রাণু জোর দিয়ে বলল, যাবো, যাবো, আমি যাবো। আমাকে নিতেই হবে।
এই যে লম্বা লম্বা গাছগুলি এখানে অনেক দেখি, এর নাম আমি জানি পালমিরা পাম, বাংলায় কী বলে? তাল গাছ? তাল গাছ। ঠিক আছে, আর এই যে ছোট ঘোট বেতের স্টুল? মোড়া? আর এই যে ফসল রাখার স্টোরেজ টাওয়ার? ধানের গোলা?
এমহা গ্রামে গ্রামে ঘুরে সব কিছু বুঝতে ও জানতে চায়। সঙ্গে থাকে সন্তোষ মজুমদার অথবা কালীমোহন ঘোষ। আতাবুদ্দি নামে এক বর্ধিষ্ণু চাষির বাড়ির উঠোনে সে একটা মোড়ায় বসে। আতাবুদ্দি বেশ বর্ধিষ্ণু চাষি, তার তিনটে ধানের গোলা। একটু দূরে বসে তার স্ত্রী এক টুকরো বাঁশ ছুলে ছুলে একটা ধামা বানাচ্ছে। কী নিপুণ ভাবে ছুরি চালিয়ে বাঁশ দুলছে সে। এক পাশে একটা খড়ের ঘরের মধ্যে টেকি পাড় দিয়ে ধান ভানা হচ্ছে। এলমহা মন দিয়ে দেখে সেই প্রক্রিয়াটি।
আতাবুদ্দির জমিতে বর্ষার সময় প্রথম ফসল ভাল হয়, দ্বিতীয়বার জলের সমস্যা, পোকার আক্রমণের সমস্যা। তার হাল-লাঙল এখনও মান্ধাতার আমলের। সাহেব দেখে সে বিস্মিত বা অভিভূত হয়নি, কারণ সে এবং এখানকার গ্রামের মানুষ পিয়ার্সন সাহেবকে দেখেছে। অতি ধীর, স্থির, বিনীত পিয়ার্সনকে সবাই ভক্তি করে।
গ্রামের মানুষদের মধ্যে কতরকম জাতিভেদ ও শ্রেণীভেদ, তাও এল্মহার্স্ট বুঝতে পারে। আছে ব্রাহ্মণ, যারা এককালে অন্যদের চেয়ে নিজেদের অনেক উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী মনে করত, তারা আজ অনেক নীচে নেমে এসেছে, বেশ করুণ অবস্থা। ভুবনডাঙায় আগে নাকি একশো পরিবার চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়রা ছিল, এখন তাদের সংখ্যা মাত্র তিরিশটি পরিবার। মহিলারা অধিকাংশ বিধবা। মুসলমানরা তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে, তাদের মহিলারা পর্দানশিন। এছাড়া আছে সাঁওতাল গোষ্ঠী, ডোম, মুচি। দারিদ্র ও অস্পৃশ্যতা। সব গোষ্ঠীর আলাদা আলাদা বৃত্ত, অথচ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল।
একদিন এক মুচিদের গ্রামে গিয়ে দেখলেন, কিছু লোক দৌড়ে পালাচ্ছে। কারণ কী? কাবুলিরা আসছে, গরিব গ্রামবাসীরা তাদের কাছে ঋণী, ঋণ শোধ করতে পারবে না, কাবুলিরা তাদের মারধোর করবে, ঘরে ঢুকে ঘটিবাটি যা পায় তা কেড়ে নেবে। কাবুলিদেরও দেখা গেল দুরে। তিনজন দীর্ঘকায় পুরুষ, ঢোলা পাতলুন ও লম্বা কুর্তা পরা, মাথায় মস্ত বড় পাগড়ি, হাতে প্রকাণ্ড লাঠি। এদের দেখে রোগা রোগা বাঙালিদের ভয় পাবারই কথা।
কাবুলিরা একজন সাহেবকে দেখে থমকে গেছে। কালীমোহন তাদের ডেকে আনলেন, এক মুচি বাড়ির প্রাঙ্গণে মোড়ায় বসে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে লাগল। কাবুলিরা সেলাম জানিয়ে মাটিতে বসল উবু হয়ে। ফিরে এল পলাতক গ্রামবাসীরা। মেয়েদের মুখে যসি, তারা ধরে নিয়েছে সাহেব তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেবে।
মুচিরা নিজেদের দোষ স্বীকার করল বেশ সরলভাবে। তারা ঘর থেকে এনে দেখাল কিছু শস্তা ধরনের কিন্তু চকচকে, রঙিন জামাকাপড়। আগের বছর কাবুলিরা এসে বলেছে, যে-কেউ এগুলি কিনতে পারে, পয়সা দিতে হবে না তক্ষুনি, পরের বছর দিলেই হবে। মুচিদের কারুরই পয়সা নেই। কিন্তু পয়সা না দিয়েও যদি এমন লোভনীয় জিনিস পাওয়া যায়, তা হলে লোভ সামলানো যায় কী করে? পরের বছরের কথা পরের বছর দেখা যাবে, তার মধ্যে কিছুই হয় না। কাবুলিরা ফিরে আসে, যে জিনিসের দাম তারা চার টাকা বলেছিল, এখন সুদ সমেত তার জন্য বারো টাকা চায়। সে মূল্য দিতে না পারলে মার তো খেতেই হবে।
কাবুলিদেরও নিজস্ব যুক্তি আছে। সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে তারা আসে ব্যবসা করতে। তারা অর্থ বিনিয়োেগ করে, পরিশ্রম করে। তার বিনিময়ে মুনাফা চাইবে না? জিনিসের দাম তারা অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়, কারণ এই সব গ্রামের কিছু লোক এমনই ধড়িবাজ যে তারা দূর থেকে কাবুলিদের দেখলেই বনে-জঙ্গলে লুকোয়, তাদের ঘরে যেসব জিনিস থাকে তার কানাকড়িও মূল্য নেই। সুতরাং একটা গ্রামে যাদের হাতের কাছে পায়, তাদের কাছ থেকেই পুরোপুরি বিনিয়োগ ও মুনাফা তুলে নিতে হয়।
এল্মহার্স্ট বোঝে, এখানে সালিসি করেও পুরোপুরি সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা তার নেই। কাবুলিরা আজ ফিরে গেলেও আবার আসবে। কালীমোহনের দিকে ফিরে সে বলে, আসলে এসব গ্রামে স্কুল খোলা দরকার। এই মুচিরা চামড়ার কাজ জানে। আধুনিক উন্নত পদ্ধতিতে ট্যানিং শেখালে তারা চামড়ার দ্রব্য বেশি দামে বিক্রি করতে পারে। তাতেই এদের অবস্থা ফিরবে।
আবার অন্য কোনও গ্রামে চাষিদের দেওয়া মুড়ি ও শশা খেতে খেতে আলু চাষে পোকা লাগা ও তার প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করে এল্মহার্স্ট। সব কিছুর জন্যই শিক্ষা দরকার, চিরাচরিত প্রথা থেকে সরে এসে যে যুগোপযোগী হতে হবে, এটাই বোঝানো দরকার সব জায়গায়।
গ্রামের মানুষদের, এমনকী অনেক শিক্ষিত ভদ্ৰশ্রেণীর মানুষদেরও স্বাস্থ্যনীতি জ্ঞানের চরম অভাব দেখেই সে বেশি বিস্মিত হয়। প্রায় সকলেই সারা বছর কিছু না কিছু রোগে ভোগে। পায়খানা বলে কোনও জিনিসই নেই। গ্রামের মানুষ, ছাত্ররা, অধ্যাপকরাও সকালবেলা এক লোটা জল নিয়ে মাঠের মধ্যে গিয়ে বসে। অনেকে আড়ালও খোঁজে না। তাদের পুরীষের ওপর যে-সব মাছি বসে, সেই সব মাছিই উড়ে আসে রান্নাঘরে। পেটের পীড়া হবে না?
সেইজন্য সুরুলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এল্মহার্স্ট প্রথমেই জোর দিয়েছেন পূরীষ পরিষ্কার প্রকল্পে। ট্রেঞ্চ খুঁড়ে সেখানে পূরীষ ফেলে চাপা দিতে হবে, এবং সে কাজ করতে হবে ছাত্রদের নিজেদেরই। তা নিয়ে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররা, ব্রাহ্মণেরা পূরীষ ছোঁবে? এমহার্স্ট একাই সে কাজ শুরু করল। একজন খাঁটি ইংরেজ কি ব্রাহ্মণের চেয়ে কিছু কম? কয়েকদিন পর একজন ব্রাহ্মণ ছাত্র হাত লাগাতেই অন্যরা মেনে নিয়েছে।
গ্রামের মানুষদের সঙ্গে মত বিনিময় তবু সহজ, শিক্ষিত ভদ্ৰশ্রেণীর মধ্যে একটা অবিশ্বাসের দূরত্ব থেকেই যায়। সে একজন ইংরেজ হয়েও গ্রামে এসে কেন খেটে মরছে, তা অনেকে বুঝতে পারছে না। অ্যান্ড্রুজ আর পিয়ার্সন সম্পর্কে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই, এরা দু’জনেই ব্রিটিশ সরকার বিরোধী, এঁরা পুলিশের কাছে নির্যাতিত হয়েছেন, এঁরা ইংরেজ হয়েও ভারতীয় স্বাধীনতাকামীদের পক্ষে।
এল্মহার্স্ট রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত দিতে চায় না। সে বলে, আমি চাষা, চাষের কাজ নিয়েই থাকতে চাই। যদিও সে সব খবরাখবর রাখে, তার দৃঢ় ধারণা, অচিরকালের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার ধাপে ধাপে ভারতে স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হবে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সে রকম আলোচনাই চলছে। বড় জোর পাঁচ-দশ বছর লাগবে। এটাই ইতিহাসের গতি। এর মধ্যে ভারতীয় জনগণ যদি আন্দোলনের মাধ্যমে সেই স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করতে চায়, সেটাও স্বাভাবিক।
কিন্তু গান্ধীজি যে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেবার আশ্বাস দিয়েছেন, তা কবির মতন, এল্মহার্স্টও মনে করে অবাস্তব। গান্ধীজি বলেছেন, এই অসহযোগ আন্দোলন হবে অহিংস। কিন্তু বছর প্রায় শেষ হতে চলেছে, এরই মধ্যে বিভিন্ন দিকে দেখা যাচ্ছে হিংসার স্ফুরণ।
স্বাধীনতা পাবার আগে ভারতবাসীকে শিক্ষায় ও আধুনিক প্রযুক্তিতেও অগ্রসর হতে হবে। কবির এই ভাবনার সঙ্গেও এল্মহার্স্ট একমত। কবিকে সে কাছাকাছি থেকে যত দেখছে, ততই তার শ্রদ্ধা বাড়ছে। কবি শুধু ভাব-জগতে থাকেন না, তিনি দেশের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গেও নিজেকে জড়িতে রাখতে চান। অন্যদের দেখাদেখি সে এখন কবির পা ছুঁয়ে প্রণাম করে এবং সম্বোধন করে গুরুদেব বলে।
ডরোথিকে সে চিঠি লেখে নিয়মিত, সব কিছু জানায়। এই প্রণাম ও গুরুদেব সম্বোধনের ব্যাপারে ডরোথি রীতিমতন ক্ষুব্ধ। ভারতীয়দের এই পদস্পর্শ করে প্রণামের রীতিটির মর্ম পাশ্চাত্যের মানুষদের পক্ষে বোঝা সত্যিই কঠিন। ক্রিশ্চানরা যীশুর মূর্তির পা ছোঁয়, কোনও জীবিত মানুষের পা ছোঁয়ার কথা ভাবতেই পারে না। বাংলার এই কবিটি নিজেকে কি অবতার মনে করেন? গুরুদেব শব্দটির অর্থ বুঝেও বিভ্রান্তি ঘোচে না। কীসের গুরুদেব? ইনি কি কবি, না ধর্মপ্রচারক?
কিছুদিন পরই অবশ্য ডরেথির চিঠির সুর বদলে গেল। এল্মহার্স্ট তো নির্বোধ সংস্কারগ্রস্ত নয়, সে জেনেশুনে যা করছে, নিশ্চিত তার যুক্তি আছে।
সুরুলের ছাত্রদের নিয়ে হঠাৎ একটা গণ্ডগোল শুরু হল।
শান্তিনিকেতন থেকে যে ক’জন ছাত্র সুরুলে প্রশিক্ষণ নিতে এসেছে, তাদের মধ্যে একজনের নাম সত্যেন বসু। সে ঠিক শান্তিনিকেতনের ছাত্র নয়, তাকে ঢুকিয়েছেন অ্যান্ড্রুজ। সে আসলে একজন রাজনৈতিক কর্মী। ছেলেটি এমনিতে বেশ গুণসম্পন্ন, কিন্তু সে মনে করে, গান্ধীজির আদর্শে আপাতত এইসব শিক্ষাটিক্ষা বন্ধ রেখে অসহযোগ আন্দোলন জোরদার করাই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সরকারের সঙ্গে কোনওরকম সহযোগিতা বা আদান প্রদানের বিরোধী গান্ধীজি। কিন্তু এল্মহার্স্ট সরকারের কৃষি বিভাগ থেকে সাহায্য নিতে অরাজি নয়। সুরুলের ভাঙাচোরা রাস্তা সারিয়ে দেবার জন্য জেলা বোের্ডকে অনুরোধ করা হবে না কেন? সাধারণ মানুষ যে সব কর ও খাজনা দেয়, তার থেকেই তো এসব কাজ হয়।
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাজ বেশ ভালভাবেই চলছে, আর সত্যেন তলে তলে করে যাচ্ছে রাজনৈতিক প্রচার। ছাত্রদের মধ্যে সৃষ্টি করতে চায় অসন্তোষ। এখন সবরকম শিক্ষা ব্যবস্থা ভণ্ডুল করে দিতে পারলেই রাজনৈতিক আন্দোলন জোরদার হবে।
ঠাকুমার আদেশে সুবীর যখন সন্ধের পর সুরুল ছেড়ে শান্তিনিকেতন যাওয়া শুরু করল, তখন সত্যেন আরও কয়েকটি ছাত্রকে উস্কানি দিতে লাগল, তোরাও মশার কামড় খেয়ে এখানে রাত্তিরে থাকবি কেন, শান্তিনিকেতনে গিয়ে ঘুমোবি।
ছাত্রদের কয়েকবার সাবধান করে দেবার পর এমহার্স্ট বুঝলেন, জ্ঞানদানন্দিনী চান, তাঁর নাতিকে এখান থেকে বিতাড়িত করা হোক। তা হলে তিনি সুবীরকে নিয়ে কলকাতায় চলে যেতে পারবেন। তিনি জোর করে ফেরৎ নিয়ে গেছেন, তা আর কেউ বলতে পারবে না। ঠিক আছে, তবে তাই হোক।
এখন থেকেই কঠোর শাস্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে না পারলে পরে আর ছাত্রদের বাগ মানানো যাবে না।
এক সকালে এল্মহার্স্ট সুবীর এবং আর একটি ছাত্রকে বলল, তোমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও, কাল সকালের ট্রেনে তোমাদের তুলে দেওয়া হবে। এখানে আর তোমাদের স্থান হবে না।
বিকেলে সমস্ত ছাত্র এবং শিক্ষককর্মীদের ডেকে এল্মহার্স্ট সব ব্যাপার বুঝিয়ে দিয়ে বললো, এখানে শৃঙ্খলাভঙ্গ সহ্য করা হবে না। তাই ছাত্র দুটিকে বহিষ্কার করা হচ্ছে।
সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন লাফিয়ে উঠে বলল, তা হলে আমিও আর এখানে থাকতে চাই না। আমিও চলে যাব।
আরও দুটি ছাত্র হাত তুলে বলল, আমরাও চলে যেতে চাই।
অবিচল মুখে তাদের দিকে তাকিয়ে এল্মহার্স্ট জিজ্ঞেস করল, আর কেউ? হাত ভোলো।
আর কেউ হাত তুলল না দেখে এমহার্স্ট বলল, সকাল সাতটায় গাড়ি তৈরি থাকবে। তোমাদের স্টেশনে পৌঁছে দেবে।
সত্যেন উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, আপনি ভেবেছেন কী। আপনি যা বলবেন, তাই-ই হবে? আমরা ইংরেজের হুকুম সহ্য করব? কাল স্ট্রাইক হবে এখানে। স্ট্রাইক, স্ট্রাইক, আমি সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি।
এল্মহার্স্ট আর কোনও মন্তব্য করল না।
কিন্তু পরদিন সকালে স্ট্রাইকে যোগ দিল না কেউ।
আল নামে ড্রাইভারটি ট্রাক নিয়ে প্রস্তুত ঠিক সাতটার সময়। এল্মহার্স্ট এবং কালীমোহনও পোশাক পরে প্রস্তুত।
সুরুলের প্রতিষ্ঠানটির নাম এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে শ্রীনিকেতন, সেখানকার দশজন ছাত্রের মধ্যে চারজনকে ভোলা হল ট্রাকে। সত্যেনকেও।
সত্যেন ঠিক করে রেখেছিল, গাড়িটা যখন শান্তিনিকেতনের মধ্য দিয়ে যাবে, তখন সে লাফিয়ে নেমে পড়ে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবে। সেখানে ছাত্র-অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকেই অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থক। সবাই মিলে পথ অবরোধ করা যেতে পারে।
কিন্তু গাড়িটা শান্তিনিকেতনের দিকে না গিয়ে অন্য একটা গর্তবহুল পথ দিয়ে পৌঁছোলো বোলপুর স্টেশনে। সত্যেনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। স্টেশনেও নেমে সে চ্যাঁচামেচি করতে লাগল, তারা কিছুতেই উঠবে না ট্রেনে।
তাদের চিৎকারে কর্ণপাত না করে এল্মহার্স্ট সুবীরকে বলল, তোমার বাবাকে টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে, তিনি হাওড়া স্টেশনে অপেক্ষা করবেন, তুমি উঠে পড়ো।
সকালবেলা স্টেশনে অনেক লোক জড়ো হয়েছে, তারা মজা দেখছে ভিড় করে।
সত্যেন মেঠো বক্তৃতার ঢঙে তাদের উদ্দেশে বলতে লাগল, ভাই সব, আপনারা এগিয়ে আসুন। গান্ধীজির মহান আদর্শে আমরা সবাই এক হয়ে স্বরাজ অর্জন করতে চলেছি। সাহেবদের কোনও হুকুম আমরা মানব না। এই সাহেবটি জোর করে আমাদের…
জনতা নির্বাক। গান্ধীজির ডাক তাদের অনেকেরই এখনও মর্মে পৌঁছয়নি। এই সাহেবটিকে তারা প্রায়ই দেখে, কোনওদিন কারুর ওপর অত্যাচার করেছে বলে শোনা যায়নি। রবি ঠাকুরের আশ্রমে মাঝে মাঝেই অন্য সাহেবরা আসে, তারা কেউ পুলিশ সাহেবদের মতন নয়।
সত্যেন চায় যে-কোনও উপায়ে সুবীরকে এখানেই রাখতে।
এল্মহার্স্ট শক্ত করে ধরে আছে সুবীরের হাত। সত্যেনের উস্কানিতেও কেউ তাকে কেড়ে নেবার জন্য এগিয়ে এল না। সুবীর অবশ্য দাঁড়িয়ে আছে মাথা নিচু করে।
ট্রেনের কামরায় সুবীরকে তুলে দিল এল্মহার্স্ট। ট্রেন ছাড়ার মুহুর্ত পর্যন্ত দরজার কাছে পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে ও কালীমোহন। সত্যেনের চ্যাঁচামেচি ও অভিযোগের কোনও উত্তর দেওয়া হল না।
এল্মহার্স্ট শান্তভাবে সিগারেট টানতে লাগল, যেন সে সত্যেনের কোনও কথাই শুনতে পাচ্ছে না।
তারপরই সে গাড়ি নিয়ে শান্তিনিকেতনে এসে কবিকে জানাল সব বৃত্তান্ত। শ্রীনিকেতনের অধিনায়ক হিসেবে এসব সিদ্ধান্ত তার নিজের। কবি তাকে সে অধিকার দিয়েছেন।
কবি আর সেই মুহুর্তে নিছক কবি রইলেন না, হয়ে উঠলেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা। নিজের রক্ত জল করা পরিশ্রমে এবং নিজের উপার্জন ও সংগৃহীত অর্থ নিঃশেষ করে তিল তিল করে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তিনি কিছুতেই এতে আঘাত লাগতে দেবেন না।
উত্তেজিত হয়ে তিনি তক্ষুনি ডেকে পাঠালেন অ্যান্ড্রুজকে।
তাঁকে কঠোরভাবে বললেন, এসব তোমারই অবিবেচনার কুফল। তুমিই সত্যেনকে প্রশ্রয় দিয়েছ। ওরা বোলপুর থেকে হেঁটে আসছে এদিকে। আমি কিছুতেই ওদের শান্তিনিকেতনে আর আসতে দিতে চাই না। এখানে এলেই হাঙ্গামা বাধবে। ওদের মাঝপথে আটকাও, যেমন করে হোক পরের ট্রেনে কলকাতায় ফেরত পাঠাও। ওদের অভিভাবকদের জানিয়ে দাও, কেন আমরা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।
এল্মহার্স্টের সঙ্গে চোখাচোখি হল অ্যাভুজের। এল্মহার্স্টের ঠোঁটে মৃদু মৃদু হাসি।
এই ঘটনার পর শ্রীনিকেতনে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে লাগলো, কাজ চলতে লাগল সুষ্ঠুভাবে।
অ্যান্ড্রুজের সঙ্গে ঠিক বনিবনা না হলেও পিয়ার্সনের সঙ্গে এলমহাশেঁর বেশ সৌহার্দ্য। পিয়ার্সন একটা গরু পুষেছেন, এল্মহার্স্ট গল্প করতে এলে তাকে টাটকা, খাঁটি দুধ খেতে দেন। সিলভ্যাঁ লেভি নামে এক ফরাসি পণ্ডিত সস্ত্রীক এসে রয়েছেন এখানে, তাঁদের কুটিরে হানা দিলে পাওয়া যায় মাদাম লেভির তৈরি করা ছোট-হাজরি। নানারকম সসেজ ও চিজ আছে তাঁর সংগ্রহে। এল্মহার্স্ট সবরকম দেশি খাবারই চেখে দেখে, মাঝে মাঝে ইওরোপিয় আহার্যের স্বাদ নিতেও ইচ্ছে হয়। শান্তিনিকেতনের সব বাড়িতেই তার জন্য অবারিত দ্বার।
এল্মহার্স্টের ধূমপানের নেশা আছে। তবে এখানে আর সিগারেট বা সিগার নয়। সে হুঁকো, গড়গড়া টানতেও শিখে ফেলেছে। তাকে গড়গড়ায় দীক্ষা দিয়েছেন দীপুবাবু। গড়গড়া টানাও শিখতে হয়, প্রথম প্রথম মুখে জল চলে আসে, এর জন্যে বিশেষ দম লাগে।
এল্মহার্স্টের একটা ব্যাপারে আশ্চর্য লাগে। ঠাকুর পরিবারের প্রায় সকলেরই নানারকম নেশা আছে, একমাত্র কবিই শুধু সুরা পান করেন না। ধূমপান করেন না, এমনকী পানও খান না।
হুঁকো-গড়গড়া ব্যবহারকে আর্টের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন জোড়াসাঁকোর অন্য তিন ঠাকুর।
এল্মহার্স্টকে কাজের জন্য মাঝে মাঝেই কলকাতায় যেতে হয়। কবির নির্দেশ আছে, তিনি থাকুন বা না থাকুন, এল্মহার্স্ট তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই উঠবে। চিৎপুর থেকে গলি দিয়ে এসে সামনের প্রাঙ্গণে পা দিয়েই একবার পাশের বাড়িটির বারান্দার দিকে চোখ চলে যায়, তাকে দেখলেই কেউ না কেউ সেই বারান্দা থেকে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।
দক্ষিণদিকের এই প্রশস্ত বারান্দাটি বড় অপূর্ব, যেমন সুরুচিসম্মতভাবে সজ্জিত, তেমনই আনন্দময় পরিবেশ। গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র ও সমরেন্দ্র এই তিন ভাই সেখানে বসে ছবি আঁকেন। অন্যদের সঙ্গে গল্প ও রঙ্গরসিকতা করেন। এমন একইরকম প্রসন্নমনা ও পরিহাসপ্রিয় তিন ভ্রাতাকে এল্মহার্স্ট আর কোথাও দেখেনি।
এঁরা শান্তিনিকেতনে বিশেষ যান না, এমন অলস মেজাজ যে বাড়ি থেকেই কখনও বেরোন না বলে মনে হয়। কিন্তু এল্মহার্স্টকে দেখলেই খোঁজখবর নেন। প্রবল প্রতাপান্বিতা জ্ঞানদানন্দিনীর সঙ্গে এল্মহার্স্টের সঙ্ঘর্ষের খবরও এঁদের কানে এসেছে। শুনতে চান তার বিস্তারিত বিবরণ। সত্যেন ঠাকুরের নাতিকে শান্তিনিকেতন থেকে তাড়িয়ে ছাড়ল, এ সাহেবটির তো জেদ কম নয়।
বারান্দার এক পাশে নানান আকারের ও প্রকারের মূল্যবান সব হুঁকো ও গড়গড়া সাজানো থাকে। এমহারে হাতে একটি নল ধরিয়ে দেওয়া হল। এ বাড়ির তামাক নিশ্চিত বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করানো, এমন সুগন্ধ আর কোথাও পাওয়া যায় না।
গল্পের মাঝখানে হঠাৎ মাথাটা ঝুকিয়ে এনে গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে ফিসফিস করে গগনেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, হাঁগো সাহেব, রবিকাকার কী হয়েছে বলে তো?
এল্মহার্স্ট প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারে না।
অবনীন্দ্র মুচকি হেসে বললেন, হঠাৎ যেন রবিকাকার নবযৌবন এসেছে। অনেকদিন কবিতাই লিখছিলেন না। এখন একেবারে প্রেমের কবিতার বান ডেকেছে। এর পেছনে প্রেরণাদাত্রীটি কে?
সমরেন্দ্র বললেন, প্রেরণা ছাড়া প্রেমের কবিতা কি আর আসে?
এবার এল্মহার্স্ট বুঝেও না বোঝার ভান করে।
গগনেন্দ্র বললেন, বলো না, বলো না, তুমি নিশ্চয়ই জানো। তার নামের প্রথম অক্ষরটা কী?
এল্মহার্স্ট হাসি হাসি মুখ করে থাকে, তবু কিছু বলে না।
গগনেন্দ্র বললেন, অবন, তুমি যেন সেদিন কী কবিতার লাইনগুলো বলছিলে!
অবনীন্দ্র বলতে লাগলেন, মনে আছে সে কি সব কাজ সখী, ভুলায়েছ বারেবারে। বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার কঙ্কন ঝঙ্কারে। ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে, ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে, কখনও আমের নবমুকুলের বেশে, কভু নব মেঘ ভারে। চকিতে চকিতে চল চাহনিতে ভুলায়েছ বারেবারে।
গগনেন্দ্র আর সমরেন্দ্র একসঙ্গে বললেন, অপূর্ব, অপূর্ব!
অবনীন্দ্র বললেন, এমন শব্দ ঝংকার, একবার দু’বার পড়লেই কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। রবিকাকা অনেকদিন এমন ভাল কবিতা লেখেননি। এল্মহার্স্ট, তোমার সঙ্গে সে মেয়েটির বেশ ভাব হয়েছে, তাও আমরা জানি।
গগনেন্দ্র বললেন, দেখো সাহেব, তুমি যেন সেই ব্রাহ্মণ কন্যাটিকে হরণ করে নিয়ে যেও না। তা হলে বাংলা সাহিত্যের বড় ক্ষতি হবে। আমরা চাই রবিকাকা আরও ভাল কবিতা লিখুন।
এবার এমহার্স্ট সশব্দে হেসে উঠল।
রাণুর সঙ্গে কবির নাম জড়িয়ে কিছু কিছু ফিসফিসানি শান্তিনিকেতনেও এহাস্টের কানে এসেছে। কিন্তু তাকে ঠিক স্ক্যান্ডাল মঙ্গারিং বলা চলে না। যেন সকৌতুক প্রশ্রয়ের ভাব আছে। সবচেয়ে বেশি প্রশ্রয় কবির পুত্র ও পুত্রবধূর। রাণু যখন কবির ঘরে গিয়ে অনেকক্ষণ গল্প করে, তখন রথী ও প্রতিমা পারতপক্ষে অন্যদের সেখানে যেতে দেয় না। বাঙালিদের এমনই সাহিত্য প্রীতি, কবি যে নতুন উৎসাহে আবার কবিতা লিখছেন, সেটাই বড় কথা, এর মধ্যে নৈতিকতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ইংল্যান্ড হলে এতদিনে সংবাদপত্রে রসালো গল্প বেরিয়ে যেত।
প্রাচ্য ও পশ্চিমদেশীয় মানুষদের চিন্তাধারার কোথায় কোথায় তফাত, তা এল্মহার্স্ট এখন কিছুটা কিছুটা বুঝতে পারে।
কবি তাকে এক এক সময় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথাও শুনিয়েছেন।
কৈশোর-যৌবনে এক বউদির সঙ্গে কবির বিশেষ ভাব ছিল। জ্যোতিদাদার স্ত্রী কাদম্বরী দেবী ছিলেন কবিরই প্রায় সমবয়সী। জ্যোতিদাদা নানান কাজে খুব ব্যস্ত থাকতেন, বাড়িতে অনুপস্থিত থাকতেন প্রায়ই, তখন কবি ও সেই বউদিদি একসঙ্গে সময় কাটাতেন, গল্প করতেন, গান গাইতেন। সেই রমণী কবির অনেক রচনার প্রেরণাদাত্রী। আবার কখনও কখনও সন্ধের সময় কোনও বাগানবাড়িতে দাদা-বউদির সঙ্গে তরুণ কবিটি মেতে উঠতেন সাহিত্যচর্চা ও গানবাজনায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বড় বড় বনেদি যৌথ পরিবারে এরকম সম্পর্ক অস্বাভাবিক ছিল না। ইওরোপেও এমন হত।।
কবির বিয়ের পর কিছুদিনের মধ্যেই সেই তরুণী বউদিটি আত্মহত্যা করেন। কেন তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন, তা অবশ্য কবি কখনও খুলে বলেননি এল্মহার্স্টকে। কবির স্ত্রীও বাঁচেননি বেশিদিন। তারপর অনেকগুলি বছর ধরে কবি লেখাপড়া ও কাজের মধ্যে ড়ুবে রয়েছেন। নারীসঙ্গ বঞ্চিত জীবন কি কোনও কবির পক্ষে, শিল্পীর পক্ষে, কোনও সৃষ্টিশীল মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক? অনেকেই বলছে, মাঝখানে যেন এই কবির কাব্যরসের ধারাটি প্রায় শুকিয়ে আসছিল, এতদিন পর রাণু নামের এই মেয়েটির সংস্পর্শে এসে তাঁর রচনায় নতুন জোয়ার এসেছে। এ মেয়েটির রূপ ও সারল্য অতুলনীয়। পড়াশুনোও করে, সাহিত্যরুচি আছে, এর সঙ্গে কথা বলেও আনন্দ পাওয়া যায়।
রাণু এমহাষ্টকেও বেশ পছন্দ করে। সে এল্মহার্স্টের সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বললে, কিংবা কোথাও বেড়াতে যেতে চাইলে কবি অমনি রাণুকে ডেকে পাঠান। কবির ঈর্ষা হয় নাকি? এ কথা ভেবেই কৌতুক বোধ হয় এল্মহার্স্টের। অবশ্য ঈর্ষা জিনিসটা ভালোবাসারই আশে পাশে ঘুরঘুর করে।
কবির বয়েস ষাট পেরিয়েছে, কিন্তু শরীর বেশ মজবুত। মাথাভর্তি চুল, চলাফেরা যুবকের মতন। কণ্ঠস্বরে আছে দৃঢ়তা। কবি নিজেই একদিন বলছিলেন, এ দেশে অনেকে মনে করে, মেয়েরা সন্তানবতী হলেই প্রৌঢ়া আর পুরুষরা চল্লিশেই বুড়ো। অল্প বয়েসে সবাই বাবাখুড়োদের বুড়োদের দলে ফেলে দেয়, কিন্তু নিজে স্বাটে পৌঁছেও দেখছি, বার্ধক্যের ছোঁয়া তো লাগেনি এখনও। মনেও না, শরীরেও না।
শরীরের যৌবন থাকাটা কল্পনাশক্তির পক্ষে জরুরি। ষাটের পরেও অনেক বছর মানুষের যৌন ক্ষমতা থাকতে পারে। এ দেশে অবশ্য যৌন শব্দটি অনুচ্চাৰ্য। ইওরোপে ভালোবাসার সম্পর্ক হলে শারীরিক সম্পর্ক অবধারিত, বয়েসের তফাত থাকলেও এ দেশে বাল্যকাল থেকেই শেখানো হয় সংযম। সংযমে অনেকে গৌরব বোধ করে। ইওরোপে সন্ন্যাসীরা ছাড়া গৃহী মানুষেরা সংযমে বিশ্বাস করে না। এদেশে শারীরিক সম্পর্ক ছাড়াও গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক হতে পারে। অবশ্য ইওরোপেও একসময় এরকম ছিল, এবাদুরদের গানে কি তার পরিচয় নেই? ব্ৰিস্তানের সঙ্গে ইসলডের কি শারীরিক মিলন হয়েছিল কখনও? প্রাচ্যে যেন সেই ধারাটাই এখনও রয়ে গেছে। এলমহার্টকে অনেকে বলেছে, গুরুদেবের কবিতায়, গানে শরীরের কথা নেই, ভাবের মিলনই প্রধান।
এইসব ভাবতে ভাবতে পাশের বাড়িতে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে গিয়ে এল্মহার্স্ট দেখল, ওপর থেকে একটা রঙের ঝড় তুলে তরতরিয়ে নেমে আসছে রাণু।
রাণু এখন এখানে? সেইজন্যেই ওদিকের বারান্দায় এত কৌতূহল। রাণু এল্মহার্স্টকে বলল, তুমি ওপরে যাও, আমি একটু পরে আসছি।
এল্মহার্স্ট জিজ্ঞেস করল, তুমি পুজোর ছুটিতে আসোনি। এই গ্রীষ্মের ছুটিতে শান্তিনিকেতনে আসছ তো?
রাণু বলল, না, আমরা তো কালই যাচ্ছি শিলং পাহাড়ে। তোমার সঙ্গে আবার অনেকদিন দেখা হবে না।
এলমহার্ট বলল, তুমি দেখা করতে চাও না?
রাণু বলল, বারে, আমি কি একসঙ্গে দু’জায়গায় থাকতে পারি নাকি?
এল্মহার্স্ট দুষ্টুমির সুরে বলল, বুঝেছি, আমার সঙ্গে যাতে তোমার দেখা না হয়, সেইজন্যই কবি তোমাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।
রাণু বলল, আহা কী বুদ্ধি। তুমি ছাই বুঝেছ।
এবারেও কবি লোক পাঠিয়ে রাণুকে আনিয়েছেন কাশী থেকে। তার বাড়ির আর কেউ আসেনি।
রথী ও প্রতিমা তো যাবেই, কন্যা মীরাকেও সঙ্গে নিলেন কবি। জামাইটি মীরাকে কষ্ট দিচ্ছে। কোনও জামাইয়ের কাছ থেকেই জীবনে শান্তি পেলেন না কবি।।
রথী ও প্রতিমার এতদিন সন্তানাদি হয়নি বলে তারা একটি গুজরাতি শিশু কন্যাকে দত্তক নিয়েছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে পুপে। মীরার মেয়ে বুড়িও সঙ্গে আছে এবং একজন ম্যানেজার। তাই গৌহাটি থেকে নেওয়া হল দুটো গাড়ি।
কবির গাড়িতে রাণুর স্থান সব সময় কবির পাশে।
সমতল ছাড়িয়ে গিরিপথের দুধারের শোভা বড় মনোরম। ভল্লুক বর্ণ মেঘ খেলা করছে ছোট ছোট পাহাড় শিখরে। কখনও রৌদ্র, কখনও ছায়ায় গাছগুলি বিভিন্ন রকমের সবুজ। পার্বত্য মানুষদের পোশাকে অনেক রকম রং, বাঙালিদের মতন সাদামাটা নয়। ফুটফুটে চেহারার কিশোর-কিশোরীরা মধু ভরা কলসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিক্রির আশায়।
রাণু হঠাৎ বলে উঠল, ওই দেখো না গিরির শিরে, মেঘ করেছে। গগন ঘিরে— আর করো না দেরি–
কবি বললেন, তোমার এটা মনে পড়ল? আমার যেটা মনে পড়ছে, তার সঙ্গে এখানকার প্রাকৃতিক কোনও যোগ নেই। কাজ থেকে ছুটি পেয়েছি, মানুষের ভিড় থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছি, তাই হঠাৎ মনে পড়ছে পুরনো একটা কবিতা। তুমি এটা পড়েছ? কর্ম যখন দেস্তা হয়ে জুড়ে বসে পূজার বেদি, মন্দিরে তার পাষাণ-প্রাচীর অভ্রভেদী চতুর্দিকেই থাকে ঘিরে; তারই মধ্যে জীবন যখন শুকিয়ে আসে ধীরে ধীরে, পায় না আলো, পায় না বাতাস, পাব না ফাঁকা, পায় না কোনো রস, কেবল টাকা, কেবল সে পায় যশ… তারপর কী যেন, ঠিক মনে পড়ছে না। একটু পরে আছে, সংগোপনে বহন করে কর্মরথে, সমারোহে চলতেছিলেম নিষ্ফলতার মরুপথে। তিনটে চারটে সভা ছিল জুড়ে আমার কাঁধ; দৈনিকে আর সাপ্তাহিকে ছাড়তে হতো নকল সিংহনাদ…
রাণু খিলখিল করে হেসে ফেলে বলল, তুমি নিজেকে নিয়ে খুব মজা করো ভানুদাদা! নকলসিংহনাদ! তারপর কী?
কবি বললেন, মিটিং হলে আমি হতেম বক্তা; রিপোর্ট লিখতে হত তক্তা তক্তা–
রাণু আরও হেসে গড়িয়ে পড়ল কবির কাঁধে।
কবি বললেন, মাথায় একটা নতুন লেখা গজগজ করছে। এখানে মিটিং নেই, আর কোনও কাজ নেই, মানুষজনের ভিড় নেই, শুধু লিখব আর গান গাইব।
রাণু বলল, আর?
কবি বললেন, আর হ্যাঁ, শ্ৰীমতী রাণু দেবীর সঙ্গে গল্প করব। অনেক গল্প।
তা অবশ্য হয় না। খ্যাতিমান মানুষদের পক্ষে নির্জনতা অতি দুর্লভ! কবি শিলং এসেছেন, সে খবর রটে গেলে মানুষ ভিড় করে দেখতে আসবে না? সভা সমিতি হবে না?
রথী খুব কঠোরভাবে নিয়ম করে দিয়েছে, সকাল, দুপুর আর সন্ধের পর কবির কাছে কোনও দর্শনার্থী আসতে দেওয়া হবে না, শুধু বিকেলের দু’ঘণ্টা তাদের জন্য বরাদ্দ।
নৈশ ভোজের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা হবেনা, চা-পানের জন্য কোথাও কোথাও যাওয়া যেতে পারে।
বাড়িটিতে ঘরগুলি আকারে বেশ বড় বড়, কিন্তু ঘরের সংখ্যা বেশি নয়। অনেকগুলি চওড়া বারান্দা। দোতলায় সবচেয়ে প্রশস্ত কক্ষটি সাজানো হয়েছে কবির জন্য, পাশেরটি বৈঠকখানা। রাণু আর সকন্যা মীরা বারান্দার এক ধারের ঘরে, অন্য ধারের ঘরটিতে রথী ও প্রতিমা। বাচ্চাদুটি যাতে বারান্দায় হুটোপুটি না করে, সেই জন্য তাদের সবসময় সামলায় আয়া, একতলায় সরকারবাবু ও পাচক-ভৃত্যেরা।
কবির ঘরের একদিকে চওড়া পালঙ্ক, অন্যদিকে, জানলার কাছে লেখার টেবিল। সঙ্গে একটি ঝুল বারান্দা, সেখানে দাঁড়ালে দেখা যায় বাগান। এ বাড়ির চারদিকেই বাগান, আর সে বাগান পাইন গাছ দিয়ে ঘেরা। পাইন গাছগুলির ওপর দিয়ে একটু একটু পাহাড় দেখা যায়। বাগানে ফুলের অন্ত নেই।
রাণু বাগানে ঘুরে বেড়ায় আর অন্য সময় কবির ঘরেই থাকে। কবি যখন লেখায় নিমগ্ন হয়ে থাকেন, কথা বলেন না, রাণু তখন শুয়ে থাকে পালঙ্কে। কবি বাইরে কোথাও গেলেও এই ঘরটিতে থাকতেই তার ভাল লাগে।
রথী ও প্রতিমা এরকম দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু মীরার চোখে লাগে।
এক দুপুরে কবি গেছেন পাশের বাড়িটিতে, সেখানে থাকেন ময়ূরভঞ্জের মহারানি সুচারু দেবী। কেশব সেনের এই কন্যাটি কবির পূর্ব পরিচিত। রাণু যায়নি, সে শুয়ে আছে কবির খাটে।
মীরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, ও কী রাণু, কী করছিস?
মীরার কণ্ঠে ভসনার সুর, কিন্তু রাণু কী দোষ করেছে বুঝতে পারল না।
মীরা বললেন, বড় হচ্ছিস, সেটা বুঝি খেয়াল থাকে না?
বড় হওয়াটাই কি তবে দোষের কিংবা সেটা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে?
সে উঠে বসে সরল ভাবে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে মীরাপিসি?
মীরা এবার রীতিমতো বিরক্ত ভাবে বলল, পুরুষ মানুষের বিছানায় ওভাবে শুতে হয়!
পুরুষ মানুষ? কবি পুরুষ মানুষ? পৃথিবীর সব মানুষ একদিকে, আর কবি অন্য দিকে। তিনি তো ভানুদাদা। কখনও ভানুদাদা এই খাটে শুয়ে থাকলেও রাণু তার পাশে শুয়ে কত কথা বলে যায়।
মীরা বলল, বাবামশাই লেখার সময় কাছাকাছি কেউ থাকুক, তা পছন্দ করেন না। উঠে আয়, ওখান থেকে উঠে আয়।
বড়দের কথার অবাধ্য হতে শেখেনি রাণু। সে উঠে চলে এল অন্য ঘরে। মুখ গোঁজ করে বসে রইল। তার কান্না এসে যাচ্ছে, মীরাপিসি তা দেখতে পেলে যদি আরও রাগ করে, তাই সে একখানা বই তুলে আড়াল করল মুখ।।
খানিক বাদে সিঁড়িতে পদশব্দ শুনে বোঝা গেল কবি ফিরেছেন।
আরও কিছুক্ষণ পর কবির উদাত্ত গলায় ডাক শোনা গেল, রাণু। রাণু কোথায় গেলে?
সে ডাক শুনে রাণু তাকাল মীরার দিকে।
মীরা অপলক ভাবে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বলল, যা—।
রাণুকে দেখে কবি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় ছিলে?
কারুর নামে নালিশ করতে নেই, তাই রাণু বলল, এই, এখানেই …
কবি বললেন, এই লেখাটা আমাকে এমন পেয়ে বসেছে, ফিরেই লিখতে বসে গেছি। হঠাৎ একসময় মনে হল, ঘরটা যেন বেশি ফাঁকা লাগছে, কী যেন নেই, গন্ধটাও অন্যরকম …
কবির চেয়ারের পেছনে এসে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে রাণু জিজ্ঞেস করল, তুমি এখন কী লিখছ ভানুদাদা?
কবি কলমটা নামিয়ে রেখে রাণুর দিকে ফিরে বললেন, অনেক অনেকদিন আগে, যখন তোমার এই ভানুদাদা ছিল ভানু সিংহ, তখন কিছু লিখতে বসলে কখনও কখনও নতুন বউঠান আমার পেছনটিতে এসে দাঁড়িয়ে ঠিক এইরকম ভাবে জিজ্ঞেস করতেন। এখন কী লিখছ তুমি? সেই দিনগুলি কি ফিরে এল? রাণু, এই লেখাটার জন্য তোমার কাছাকাছি থাকা যেন বেশি বেশি দরকার। এক একবার তোমার মুখখানা দেখি, আর অনেক কিছু মনে পড়ে যায়। এটা একটা নাটক।
রাণু বলল, নাটক? সেই যেটা লিখবে বলেছিলে? কী নাম দিয়েছ?
কবি বললেন, যক্ষপুরী, পরে হয়তো বদলেও যেতে পারে।
রাণু বলল, আমায় যে পার্টটা দেবে, সেটা বড় করে লিখবে কিন্তু!
কবি সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, তুমিই তো এই নাটকের প্রাণ। তুমি হিরোইন। তোমাকে নিয়েই লিখছি।
রাণু ভুরু তুলে বলল, আমাকে নিয়ে? জ্যান্ত মানুষদের নিয়ে বুঝি কিছু লেখা যায়?
কবি বললেন, লেখার মানুষগুলো যেমন জ্যান্ত হয়ে পড়ে, তেমনি জ্যান্ত মানুষেরাও লেখার মধ্যে চিরকালীন হয়ে যায়।
রাণু বলল, আমায় একটু পড়ে শোনাবে?
কবি বললেন, শোনাব। আরও কয়েক পৃষ্ঠা লেখা হোক। তোমার নাম দিয়েছি নন্দিনী। কেমন, পছন্দ?
রাণু ঘাড় কাত করে বলল, হ্যাঁ, এ নামটাও সুন্দর। সে কি কোনও রাজার নন্দিনী?
কবি বললেন, না, সে আকাশের। সে আলোর। সে মুক্ত বাতাসের। এই পৃথিবীতে যত কিছু সুন্দর, সে সব কিছুর নন্দিনী।
রাণু বলল, একদিন তোমার এই লেখা সারা পৃথিবীর মানুষ পড়বে। সবার আগে আমি তোমাকে সেই লেখাটা লিখতে দেখছি, আমার কী ভাল যে লাগছে!
কবি বললেন, তোমার সেই ভাল লাগাটা আমাকে স্পর্শ করে দাও!
বিকেল হলে দীনেশ সেনের বাড়ির ছেলেমেয়েরা রাণুকে ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য ডেকে নিয়ে যায়।
বাগান থেকে নানারকম ফুল তুলে নিয়ে রাণু কবিকে এনে দেখায়। রাণু অনেক ফুলের নাম জানে না, কবি সব ফুল চেনেন। জীবনে কত ফুল নিয়ে যে গান ও কবিতা লিখেছেন!
সেদিন সন্ধেবেলা রাণুর হাতে হলুদ রঙের এক জাতীয় ফুল দেখে তিনি বললেন, এটা কী ফুল বলো! ড্যাফোডিল, এ ফুল নিয়ে একটি বিখ্যাত ইংরিজি কবিতা আছে, জানো?
রাণু শুধু বাংলা নয়, ইংরিজি কবিতা পড়ে। সে বলল, ড্যাফোডিল এই ফুল বুঝি? কবিতাটা জানি, ওয়ার্ডসওয়ার্থের :
I wandered lonely as a cloud
That floats on high o’er vales and hills
When all at once I saw a crowd
A host, of golden daffodils…
শুনতে শুনতেই কবির মধ্যে শিক্ষক সত্তাটি জেগে উঠল। তিনি যে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের ইংরিজি কাব্য পড়ান।
তিনি বললেন, কবিতাটির কী বৈশিষ্ট্য বল তো? ওয়ার্ডসওয়ার্থ, যিনি প্রকৃতির কবি হিসেবেই বিদিত, তিনি প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে অনিলেন অভিনবত্ব, প্রকৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন নিজেকে, I wondered lonely as a cloud… অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক ভাবে দেখা নয়, কবি দাঁড়িয়ে আছেন প্রকৃতির মধ্যে। এবং শেষ ছত্রগুলি আরও বিস্ময়কর। এই প্রথম একজন কবি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, প্রকৃতির মধ্যে থাকলেই প্রকৃতিকে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তা দেখতে হয় কল্পনার চোখ দিয়ে। শেষের লাইনগুলি ঠিক মনে পড়ছে, সেই যে কবি যখন একটা চেয়ারে বসে আছেন, কিছুদিন পরের কথা–
রাণু বলল, আমার মনে আছে :
For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude
And then my heart with pleasure fills
And dances with the daffodils.
কবি বললেন, বাঃ, বেশ মুখস্থ করেছ তো। ওই যে বললেন, ইনওয়ার্ড আই, ভেতরের চোখ, ওই চোখ দিয়েই সত্য রূপ দেখা যায়।
রাণু বলল, ভানুদাদা, তুমি যখন শান্তিনিকেতনে পড়াও, আমি কখনও তোমার ক্লাসে বেশিক্ষণ বসিনি, অন্যদের সঙ্গে বসতে আমার ভাল লাগে না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, কী ভুল করেছি। তুমি কত সহজ করে বোঝাও, কত কী শিখতে পারতাম।
কবি বললেন, তোমাকে একা পড়াতেও আমার ভাল লাগবে। রসো, আগে এই নাটকটি শেষ করে নিই।
পরের দিন রাণু নিয়ে এল আর একরকম ফুল।
কবি রীতিমতো চমকে উঠে বললেন, এ কী, এ যে রক্তকরবী।
রাণু বলল, হ্যাঁ, একজন বলল। অনেক ফুটেছে। এই ফুল নিয়ে কোনও কবিতা নেই?
কবি বললেন, ইংরেজিতে কিছু আছে কি না জানি না। বাংলা কোনও লেখায় একসময় হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে।
রাণু বলল, ভাবছি, এই ফুলগুলো দিয়ে একটা মালা গাঁথব।
কবি বললেন, হ্যাঁ, মালা গেঁথে রেখে দাও। যাকে তাকে দিও না, রঞ্জনকে দিতে হবে।
রাণু বুঝতে না পেরে বলল, রঞ্জন? রঞ্জন কে?
কবি বললেন, সে আসবে, তার জন্য প্রতীক্ষায় থাকতে হয়।
কয়েকদিন পর মাঝ রাতেও রাণুর ঘুম এল না।
এক এক রাতে এমন হয়, ঘুম যেন নিরুদ্দেশে চলে যায়।
পাশের খাটে মীরা তার মেয়েকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ আগে, রাণুর চোখ দুটি সম্পূর্ণ খোলা।
এ ঘরে মস্ত একটা দেয়ালঘড়ি আছে। তার পেণ্ডুলামের টিক টিক শব্দ যেন বড় বেশি শব্দ করছে।
ঘড়ির আওয়াজ বড় অদ্ভুত। দিনের অধিকাংশ সময়, এমনকী রাত্তিরেও তার আওয়াজ যেন খেয়ালই করা যায় না। আবার ঘুম না এলে মনে হয়, এই শব্দ আর সব কিছু ছাপিয়ে গেছে।
বেশ কিছুক্ষণ বিছানায় ছটফট করার পর রাণু উঠে পড়ল। দাঁড়াল গিয়ে সামনের দিকের ঝুল বারান্দায়। তার অঙ্গে ঢোলা রাত-পোশাক।
সন্ধের পর খুব একচোট বৃষ্টি হয়েছে। এখন আকাশ নির্মেঘ। জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে বাগান। কোথাও কোনও শব্দ নেই। এ যেন আদিম পৃথিবীর রূপ। পাইন গাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের প্রহরীর মতো। বাগানের ফুলগুলি এখন আলাদা করে চেনা যায় না, শুধু পাওয়া যাচ্ছে একটা মিশ্রিত সুগন্ধ।
রাণু দেখল, কবির ঘরে এখনও বাতি জ্বলছে।
রাত তো কম হল না, দুটো-তিনটে হবেই। কবি এখনও লিখে চলেছেন? এমন করলে মানুষের শরীর টেকে?
পা টিপে টিপে রাণু চলে এল কবির ঘরের দরজার কাছে। ভেজানো দরজা, একটু ঠেলতেই খুলে গেল।
ঘরের দুদিকে জ্বলছে দুটো বাতি। লেখার টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছেন কবি। ঝরনা কলমটা খসে পড়ে গেছে নীচে।
রাণু নিঃশব্দে এসে কলমটা তুলে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকল, ভানুদাদা!
তিনবার ডাকের পরেই কবি সচকিত ভাবে মুখ তুলে বললেন, কে? ও, রাণু, এসো।
রাণু বলল, রাত অনেক হয়েছে, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। এমন ভাবে ঘুমোলে ঘাড় ব্যথা হয়ে যাবে যে। তুমি বিছানায় গিয়ে শোও। ওঠো, ওঠো।
কবি বললেন, ঠিক ঘুমিয়ে পড়িনি। আধা ঘুম আর আধো জাগরণের মধ্যে ছিলাম। এই অবস্থাটা বেশ মজার, অনেক কিছু দেখতে ও শুনতে পাওয়া যায়। আমি নাটকটার অনেক না-লেখা সংলাপ চরিত্রগুলির মুখ দিয়ে শুনতে পাচ্ছিলাম।
রাণু বলল, তা হোক, তবু তুমি এবার শুয়ে পড়ো।
কবি বললেন, হবে, হবে, শোওয়া তো আর পালাচ্ছে না। তুমি একটু বসো তো চুপটি করে। একটা গান শুনবে?
কবির চোখেমুখে ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নেই।
রাণু সম্মতি জানাতেই তিনি গান ধরলেন :
তোমায় গান শোনাব, তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো
ওগো ঘুম ভাঙানিয়া।
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাকো,
ওগো দুখ জাগানিয়া।
এলো আঁধার ঘিরে
পাখি এল নীড়ে
তরী এল তীরে,
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো
ওগো দুখজাগানিয়া…
কবি একটু থামতেই রাণু বলল, দুখজাগানিয়া? শুনতে কেমন যেন লাগছে। দুঃখকে কি কেউ জাগায়?
কবি বললেন, তেমন দুঃখ তো পাওনি! বিশ্ববিধাতা তোমাকে তেমন দুঃখ যেন না দেন … তবু অনেক দুঃখে মানুষ পবিত্র হয়। নন্দিনীও বিশু পাগলকে জিজ্ঞেস করেছে, তুমি আমাকে বলছ দুখজাগানিয়া?
রাণু বলল, বিশুপাগল কে?
কবি বললেন, পরে বলছি। বাকিটা শোনো। তুমি যখন বাগানে খেলছিলে, আমি দেখছিলাম অলিন্দে দাঁড়িয়ে, তখনই মনে এল গানটা :
আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্না হাসির দোলা তুমি থামতে দিলে না যে।
আমার পরশ করে
প্রাণ সুধায় ভরে
তুমি যাও যে সরে
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকো
ওগো দুখ জাগানিয়া
গান শেষ হবার পরে দু’জনেই স্তব্ধ। কেটে যেতে লাগল পল, অনুপল।
তারপর রাণু বলল, ভানুদাদা। তবু আমি দুখজাগানিয়া কথাটার মর্ম বুঝতে পারছি না। আমি যে তোমার তুলনায় কত সামান্য।
কবি বললেন, না রাণু, তুমি সামান্য নও। হয়তো তুমি বুঝতেই পারো না, কতখানি মাধুর্য তুমি আমাকে দাও!
রাণু বলল, আমি আর কী দিই। আমি তো পাই। সাত রাজার ঐশ্বর্যের চেয়েও বেশি। আমি কি বুঝি না যে তুমি কত বড়, কত ব্যস্ত, কত কাজের মানুষ। তবু যে তুমি আমার ছেলেমানুষি সহ্য করো–
কবি রাণুর হাত ধরে বললেন, তুমি যে তুমিই ওগো, সেই তব ঋণ। আর কেউ বুঝবে না। তোমার ভালবাসা আমার কাছে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারের চেয়েও বেশি।
রাণুর ভেতরে যে আচ্ছন্নতার ভাব এসেছিল, সেটা কাটিয়ে দিয়ে সে আবার উচ্ছল গলায় বলল, আ হা হা, এরপর চিন জাপান কিংবা কামস্কাটকা থেকে নেমন্তন্ন এলেই তুমি আবার উধাও হয়ে যাবে। কতদিনের জন্য কে জানে।।
কবি বললেন, তা হয়তো যাব। তবু তুমি থাকবে। তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম। রাণু, তুমি আমাকে নতুন বউঠানের স্মৃতি ফিরিয়ে দিয়েছ। আমি আবার সেই বয়েসের উৎসাহে মেতে উঠেছি।
রাণু বলল, ভানুদাদা, তুমি আমাকে অন্য কারুর সঙ্গে তুলনা করবে। আমি রাণু। তোমার নতুন বউঠানকে আমি চিনি না।
কবি বললেন, তা ঠিক। তুলনা করা উচিত নয়। থাক তবে ওসব কথা। এসো, তোমাকে নাটকটার কিছু অংশ পড়ে শোনাই। এইখান থেকে, নন্দিনী বলছে, বিশু পাগল, তুমি আমাকে বলছ দুখজাগানিয়া?
বিশুপাগল : তুমি আমার সমুদ্রের অগম পারের কি দূতী …
রাণুকে আর তার পিত্রালয়ের গণ্ডির মধ্যে ধরে রাখা যাচ্ছে না। যদিও তার দিদিদের এখনও বিয়ে হয়নি, কিন্তু রাণুর বিয়ে আর না দিলেই নয়। সে প্রায় অরক্ষণীয়া হয়ে উঠেছে।
সেই বিসর্জন নাটকের অভিনয়ের পর থেকেই তার প্রতি বহু পাত্রের পিতামাতাদের নজর পড়ে। পাত্রেরা নিজেরাও কম নজর দেয় না।
এখন রাণুর একা একা চলাফেরা তো নিরাপদ নয় বটেই, কারুর সঙ্গে বেরোলেও মধুলোভী পিঁপড়ের মতো অত্যুৎসাহী যুবকেরা তাকে ঘিরে ধরে।
কবিকেও এখন এই উপদ্রব সহ্য করতে হয়।
তিনি প্রায়শই রাণুকে সঙ্গে নিয়ে কোনও থিয়েটার দেখতে বা সভা-সমিতিতে যান, সেখানে কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে এসে আর জায়গা ছাড়ে না, তাদের আধখানা দৃষ্টি কবির দিকে, আর দেড়খানা চোখ রাণুর প্রতি।
কোনও সভাস্থলে কিংবা রঙ্গালয়ে রাণুকে দেখলেই যেন একটা চাপা ফিসফিসানি শোনা যায়, কে এই মেয়েটি? কে এই বিদ্যুৎবরণী?
কে এই সুকেশিনী, মঞ্জুভাষিণী?
রাণুর বাবা ও মা কবিকে জানিয়েছেন, তাঁরা রাণুর জন্য পাত্র দেখা শুরু করেছেন। অবশ্য কবি নিজে যদি কোনও পাত্র নির্বাচন করে দেন, তার চেয়ে ভাল কিছু আর হতে পারে না।
রাণুর কলেজে পড়া এখনও শেষ হয়নি, এর মধ্যেই অন্যের বাড়ি চলে যাবে? অবশ্য কবির আপত্তি জানাবার কোনও মুখ নেই, কারণ তিনি তাঁর নিজের তিন মেয়েরই বিবাহ দিয়েছেন রাণুর চেয়েও অনেক কম বয়েসে।
রাণুকে তিনি নিজের সঙ্গিনী করে রাখবেন কোন যুক্তিতে?
একবার তিনি রাণুকে একটা চিঠিতে হঠাৎ তাঁর ভেতরের হাহাকারের কথা সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। লিখেছিলেন :
… তোমার জীবনে, রাণু, যদি আমার মধ্যে সেই সদর দরজাটা খুঁজে পেতে, তাহলে খোলা আকাশের স্বাদ পেয়ে হয়তো খুশি হতে। তোমার অন্দরের দরজার অধিকার দাবি আমার তো চলবে না–এমনকি সেখানকার সত্যকার চাবিটি তোমার হাতেও নেই, যার হাতে আছে সে আপনি এসে প্রবেশ করবে, কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমি যা দিতে পারি, তুমি যদি তা চাইতে পারতে, তাহলে বড় দরজাটা খোলা ছিল। কোনও মেয়েই আজ পর্যন্ত সেই সত্যকার আমাকে সত্য করে চায়নি—যদি চাইত তাহলে আমি নিজে ধন্য হতুম। কেননা, মেয়েদের চাওয়া পুরুষদের পক্ষে একটা বড় শক্তি। সেই চাওয়ার বেগেই পুরুষ নিজের গূঢ় সম্পদকে আবিষ্কার করে। … শঙ্কর যখন তপস্যায় থাকেন তখন তাঁর নিজের পূর্ণতা আবৃত হয়ে থাকে। উমার প্রার্থনা তপস্যা রূপে তাঁকে আঘাত করে যখন জাগিয়ে দেয়, তখনই তিনি সুন্দর হয়ে, পূর্ণ হয়ে, চিরনবীন হয়ে বেরিয়ে আসেন। উমার এই তপস্যা না হলে তাঁর তো প্রকাশের ক্ষমতা নেই। কতকাল থেকে উৎসুক হয়ে আমি ইচ্ছা করেছি, কোনও মেয়ে আমার সম্পূর্ণ আমাকে প্রার্থনা করুক, আমার খণ্ডিত আমাকে নয়। আজও তা হল না—সেইজন্যই আমার সম্পূর্ণ উদ্বোধন হয়নি। কী জানি আমার উমা কোন দেশে কোথায় আছে। হয়তো আর জন্মে সেই তপস্বিনীর দেখা পাব।
রাণু এই চিঠি বারবার পড়েছে, আকুল ভাবে কেঁদেছে, কিন্তু কোনও উত্তর দিতে পারেনি। সে ভালবাসতে জানে, ভালবেসেছে কবিকে, কিন্তু ভালবাসার বিনিময়ে কী চাইতে হয়, তা সে জানে না। কবি তো এখানে শুধু কবি নন। নিজেকে বলছেন পুরুষ, আবেদন জানাচ্ছেন এক নারীর কাছে, রাণু যে এভাবে কখনও ভাবেনি। অত বড় একজন মানুষ, তাকে সমগ্র ভাবে চাইবার সাহস তার হবে কী করে? খণ্ডিত মানুষটিই ভানুদাদা, সেই অংশটিই সে আপন করে চেয়েছে।
শিলং পাহাড়ে যাবার কিছুদিন আগে কবি আর একবার গিয়েছিলেন কাশীতে। সেবারই প্রথম রাণুদের বাড়িতে রাত্রি যাপন করলেন। তখন থেকেই শুরু হয়েছে বিয়ের আলোচনা।
কবি বেদনার সঙ্গে মেনে নিয়েছেন, রাণুকে অন্য একজন পুরুষের হাতে সঁপে দিতেই হবে। তা বলে কি চিরবিচ্ছেদ হবে রাণুর সঙ্গে? তাঁর আশঙ্কা, রাণুর বাবা হয়তো তড়িঘড়ি করে এমন কোনও পাত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ করবেন, যে রাণুকে নিয়ে যাবে দূর প্রবাসে। বিয়ে হোক, তবু রাণু থাকুক কাছাকাছি। এমন একটি ভাল বংশের, শিক্ষিত, রুচিবান পাত্র বাছতে হবে, যে রাণুকে ভালবাসবে, তাকে মর্যাদা দেবে, আবার কবির প্রতিও শ্রদ্ধাশীল, যে তাঁর সঙ্গে রাণুর যোগাযোগ রক্ষা করতে বাধা দেবে না।
সে ভার নিতে হবে তাঁকেই। এ কাজটি তাঁর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সম্পূর্ণ মনোযোগ যে দেবেন, তার সময় পান না। কর্তব্যের বোঝ যে সবসময় কাঁধে চেপে আছে। এর মধ্যে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ দেহরক্ষা করলেন। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা উত্তাল। নজরুল ইসলাম নামে একটি অল্পবয়েসী ছেলে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা কবিতায় ঝড় বইয়ে দিয়েছে। এই তেজী তরুণটিকে বেশ পছন্দ করেন কবি। পত্রিকায় একটা উত্তেজক রচনাকে রাজদ্রোহমূলক অভিযোগ এনে পুলিশ তাকে বন্দি করে রেখেছে কারাগারে। প্রতিবাদে নজরুল শুরু করেছে আমরণ অনশন, কারুর কথাই শুনছে না। এভাবে ওর মৃত্যু হলে বাংলা সাহিত্যের নিদারুণ ক্ষতি হয়ে যাবে। তাকে অনশন ভঙ্গ করার জন্য পাঠাতে হল টেলিগ্রাম। কবির সদ্য প্রকাশিত ‘বসন্ত’ নামের গীতিনাট্যটি নজরুলের নামে উৎসর্গ করে তার এক কপি পাঠিয়ে দিলেন জেলখানায়। বসন্ত’ নাটিকাটির অভিনয়েরও ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু কবির মনে সর্বক্ষণ চিন্তা, রাণুর বাবা কোনও পাত্রপক্ষকে কথা দিয়ে ফেলবেন না তো?
বেনারসের কোনও আমন্ত্রণই তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না। সভাসমিতি তো আছেই, এই সুযোগে তিনি ফণিভূষণ ও সরযূকে বারবার বোঝালেন, কিছুদিন দেরি হয় হোক, তাঁকে না জানিয়ে, তাঁর সম্মতি না নিয়ে রাণুর বিবাহ ঠিক করা মোটেই উচিত হবে না।
বিশেষত তিনি সরযূকে একদিন আলাদা করে ডেকে বললেন, শোনো, রাণুর যে যোগ্য হবে, সে যেন রাণুকে ভুল না বোঝে। ওর মধ্যে যে দুর্দমতা আছে, তার সম্বন্ধেও অসহিষ্ণু হবেনা। মুশকিল এই, এটা তো জানোই, রাণুর জীবনের মাঝখানে কেমন করে আমি একটা কেন্দ্র দখল করে বসে আছি, সুতরাং ওর যেখানেই গতি হোক আমাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে চলবে না, তাতে সমস্ত ব্যাপারটাই জটিল হয়ে উঠবে। সেই জট যদি ছাড়ানো সম্ভব হত, তাহলে সবই সোজা হত। কিন্তু ও বেদনা পেতে যেরকম অসাধারণ পটু, তাতে ওকে কাঁদাতে আমার মন সরে না। ওকে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা দেবার পথ আমার হাতে নেই—তবে কিনা আমার অন্তরের স্নেহ পাবার পক্ষে ওর ভবিষ্যতেও যাতে কোনও ব্যাঘাত না হয়, এই সম্ভাবনার কথাই আমি আশা করতে পারি।
সরযু কবির পায়ের কাছে বসে পড়লেন। কবির প্রতি তাঁর এমনই ভক্তি যে কবির সম্মতি ছাড়া রাণুর বিয়ে দেবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।
বারাণুসী থেকে কবির লক্ষৌ যাবার কথা। কাছাকাছি থেকেও রাণুর অদর্শন তাঁর কাছে অসহ, রাণুও তাঁকে ছাড়তে চায় না।
ফণিভূষণ কিছুটা খুঁত খুঁত করছিলেন। বিয়ের কথাবার্তা চলছে, এই সময় রাণুকে বাইরে পাঠানো কি ঠিক হবে? এবারেও সরযূর প্রবল সমর্থনে রাণু শেষ পর্যন্ত অনুমতি পেয়ে গেল।
কথায় বলে রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। রাণু যেন একই অঙ্গে দুই-ই।
লোকজনের মাঝখানে সে সপ্রতিভ। চাঞ্চল্য দমন করে চুপ করে বসে থাকতেও জানে। লক্ষৌ-এর গভর্নর ডিনার পার্টিতে আহ্বান করেছিলেন, সেখানে সে বিলিতি আদবকায়দা শিখে নিল চটপট।
আবার কবি অতুলপ্রসাদ সেনের বাড়ির সান্ধ্য আসরেও সে মধ্যমণি। অতুলপ্রসাদ দিনের বেলা হ্যাট-কোট পরা ব্যারিস্টার, সন্ধেবেলা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা খাঁটি বাঙালি, ঢোল-মৃদঙ্গ বাজিয়ে গান করেন, রাণুও আঁচলটি এমন ভাবে গলায় জড়িয়ে নিল, যেন পল্লিবাংলার লক্ষ্মী মেয়েটি।
অনেকের অনুরোধে সে এস্রাজ বাজিয়েও শোনাল। তখন সে যেন সাক্ষাৎ বীণাবাদিনী সরস্বতী!
একটা উঁচু বেদির ওপর বসানো হয়েছে তাকে, একটা লাল পাড়, সাদা সিল্কের শাড়ি পরা, কপালে একটি টিপ, পিঠের ওপর খোলা চুল, যেন একটা দিব্য আভা ফুটে বেরুচ্ছে তার সর্বাঙ্গ থেকে।
তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কবির বুক টনটন করতে লাগল।
এখানেও রাণুর পাণিপ্রার্থীর সংখ্যা অনেক। একটুক্ষণও চোখের আড়াল করার উপায় নেই।
লক্ষ্ণৌ থেকে কবিকে যেতে হয়েছিল করাচিতে, তিনি তাড়াতাড়ি রাণুকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বেনারসে।
শিলং থেকে ফেরার পর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কবিকে আবার যেতে হল আমেদাবাদের দিকে। এবারে সঙ্গে নিলেন এল্মহার্স্টকে।
নতুন নাটকটির এখনও শেষ অংশ লেখা হয়নি। পরিমার্জনও করছেন বারবার। সফর, বক্তৃতা, ভোজসভা এসব কিছু সেরেও লেখার কাজ চলছে ফাঁকে ফাঁকে।
লিমবিডি নামে একটি ছোট দেশীয় রাজ্যে থাকার সময় এক রাতে তিনি এল্মহার্স্টকে ডেকে বললেন, লেওনার্ড, আজ আমার মনটা বেশ খারাপ হয়ে আছে। কেন জানো? কারণটা শুনলে তুমি অবাক হবে। যে নাটকটা লিখছিলাম এতদিন ধরে, তার শেষ অংশে এসে গেছি, কালই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। আজই শেষ করা যেত, কিন্তু এতদিন যে চরিত্রগুলির সঙ্গে রয়েছি, তাদের ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। অথচ বিদায় দিতে হবেই। শুধু আর একটা দিন বিলম্বিত করা।
এল্মহার্স্ট বলল, নাটকটি পড়তে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। শিগগিরই অনুবাদ হবে নিশ্চিত?
কবি বললেন, তা হবে, সুরেন আগেই জানিয়ে রেখেছে। এ নাটক তো তোমাকে পড়তে হবেই, কারণ এটা তোমাকেই উৎসর্গ করছি।
দারুণ বিস্মিত হয়ে এল্মহার্স্ট বলল, আমাকে? নিজেকে খুবই ধন্য ও সম্মানিত মনে করছি অবশ্যই। কিন্তু জানতে কৌতূহল হচ্ছে, কেন আমাকে উৎসর্গ করছেন?
কবি বললেন, কারণ, তুমিই তো এ নাটকের নায়ক।
আরও বেশি বিস্মিত হয়ে এল্মহার্স্ট বলল, মাই গুডনেস! নায়ক? আমি? আপনার নাটকের? আপনি রসিকতা করছেন আমার সঙ্গে।
কবি বললেন, তুমি রঞ্জন। নাটকের কেন্দ্রে আছে আমাদের রাণু, তার নাম নন্দিনী, সে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে। আর জালের আড়ালে রয়েছে অদৃশ্য রাজা, রঞ্জনের সঙ্গেই তার প্রধান প্রতিযোগিতা। আমি এ নাটকটাকে ঠিক রূপক বলতে চাই না।
এল্মহার্স্ট বললেন, কিন্তু হুবহু বাস্তব চরিত্র নিয়ে কি শিল্প হয়? শিল্পে নিশ্চিত তার অনেক রূপান্তর ঘটে।
কবি বললেন, তা অবশ্যই। তবে আমাদের তিনজনের আদলেই নাটকের মূল কাঠামোটি আমার প্রথম মনে আসে। রাণু জানে না, সে-ই আমাকে দিয়ে এ নাটকটি রচনা করিয়েছে। হয়তো তোমার কথা মাথার মধ্যে ছিল বলেই আমি রঞ্জনের মুখে কোনও সংলাপ বসাইনি।
আপনি বলছেন, রঞ্জনই এ নাটকের নায়ক। অথচ তার কোনও সংলাপ নেই? এরকম নাটক পৃথিবীতে আগে লেখা হয়েছে?
বিশ্বসাহিত্যের সব খবর তো জানি নে। স্বাভাবিক ভাবেই এই আঙ্গিকটি লেখার সময় এসে গেল। অন্য সবাই রঞ্জনের কথা বলছে, সে আসবে, আসবে, এসে পড়বে, কিন্তু শেষ দৃশ্যের আগে তাকে দেখা যাবে না। তখনও তার কথা বলার ক্ষমতা নেই।
আশ্চর্য, ভারী আশ্চর্য! আপনি চাইছেন, আমি নাটকটিতে ওই ভূমিকায় অভিনয় করব। আমার বাংলা উচ্চারণ ঠিক হবে না, তাই কি আপনি রঞ্জনের মুখে কথা বসাননি।
কবি হাসতে হাসতে বললেন, সেটা একটা কারণ হতে পারে। অবশ্যই। তবে, কারণ যাই-ই হোক, তা তো পাঠকদের জানবার কথা নয়। বাংলা নাটকে নায়করা বড্ড বেশি কথা বলে, লম্বা লম্বা লেকচার দেয়, আমার রঞ্জন বোবা নয়, তবু সে সংলাপহীন নায়ক।
আরও কিছুক্ষণ নাটকটি বিষয়ে আলোচনা চলে।
তাবপর একসময় এল্মহার্স্ট বলল, গুরুদেব, আমার একটি নিবেদন আছে। এবার হয়তো শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন থেকে আমার পাট চুকোতে হবে। আপনি ডরোথির কথা জানেন। সে আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়। আমিও এখন তাকে বিয়ে করে সংসার ধর্ম শুরু করতে চাই।
কবি বললেন, এ তো ভারী সুখবর। তোমাকে আমি বেশিদিন ধরে রাখার কথা ভাবিইনি। আমার ছাত্র কর্মীরা তোমার ওপর বরাবরের মতন নির্ভরশীল হয়ে থাকবে, এ কখনও হতে পারে না। তুমি তাদের শুরুর কাজটি ধরিয়ে দেবে, তারপর তারা নিজের পায়ে দাঁড়াবে, এটাই তো ঠিক। আমার তো মনে হয়, সে রকম ভাবেই ওরা তৈরি হয়েছে।
এল্মহার্স্ট বলল, আমার যতদূর সাধ্য করেছি। কৃষি, পশুপালন ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পর্কে একটা চেতনা জাগ্রত হয়েছে, এখন কাজ চলতে থাকবে।
কবি বললেন, তাতেই আমি খুশি।
তারপর নিঃশব্দ হাসিতে মুখ ভরিয়ে, চক্ষু নাচিয়ে বললেন, আমি আরও বেশি খুশি তোমার বিবাহ-সম্ভাবনার কথা শুনে। আমার মন থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেল। বাপ রে, ইদানীং আমি লক্ষ করছিলুম যে তুমি কাশীর কন্যাটির প্রতি এত বেশি বেশি মনোেযোগ দিচ্ছিলে, যাতে সেই কন্যাটিরও মনের গতি যেন আগেকার পথ ছেড়ে তোমার দিকে ধাইছিল। আমার পক্ষে ভয় পাবারই কথা, তাই না?
এল্মহার্স্টও হেসে বলল, আপনার এ আশঙ্কার কোনও কারণই ছিল না। আপনি যে রকম একটি ত্রিভুজ প্রেমের ধারণা দিচ্ছেন, সেটা অলীক। মেয়েটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক খানিকটা ভালো লাগার, আর অনেকটাই কৌতুকের। তবে কিছুদিন ধরে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে, সেটা বলব? হয়তো এ রকম কথা বলার অধিকার আমার নেই।
কবি বললেন, বলো, প্রাণ খুলে বলল। এল্মহার্স্ট বলল, আপনি অনেক বিষয়েই আমার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করেন, তাই বলছি। রাণুর সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা আমি বুঝি। খুবই মধুর, নির্দোষ সম্পর্ক। কিন্তু এখন রাণুর বিয়ের কথাবার্তা চলছে, এখন বোধহয় আস্তে আস্তে আপনাদের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি করাই ভাল। এত বেশি চিঠি লেখা, ঘন ঘন দেখা হওয়া, আপনি বাইরে গেলে ওকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চান, এতে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা আছে।
কবি বলল, তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ। কিন্তু ও যে অবুঝ। কান্নাকাটি করে, বারবার আমার কাছে আসতে চায়। তবু, নিজেকে সরিয়ে নিতেই হবে। লিওনার্ড, তুমি ইওরোেপ চলে গেলেও আর একবার এসো। আমার খুব ইচ্ছে, এই নতুন নাটকটা মঞ্চস্থ করলে, তাতে তুমি, রাণু আর আমি অংশ নেবো। গূঢ় কথাটি আর কেউ বুঝতে পারবে না। তোমাকে দেখা যাবে একেবারে শেষ দৃশ্যে, শুয়ে আছে রঞ্জন, নন্দিনী ঝুকে তোমার চুলে একটা পালক এঁটে দেবে।
পূর্ববঙ্গের এক জমিদারনন্দন কবির জীবন অতিষ্ঠ করে দিচ্ছে একেবারে। জোড়াসাঁকোয় সে প্রতিদিন আসে, শান্তিনিকেতনেও ধাওয়া করে। এই সব ছোটখাটো জমিদারদেরও অনেকে রাজা বলে, যুবকটির রাজপুত্রসুলভ কান্তি, লেখাপড়াও কিছুটা শিখেছে, গান জানে, কবির কাছে বসে তাঁরই গান শোনায়। উদ্দেশ্য একটাই। অনেকেই জেনে গেছে, কাশীর রূপবতী-গুণবতী কন্যাটিকে বধূরূপে পেতে গেলে সর্বাগ্রে কবির সম্মতি আদায় করতে হবে।
কবি ছেলেটিকে মোটামুটি পছন্দ করেও ঠিক যেন মেনে নিতে পারেন না।
ছেলেটির তেমন কিছু ব্যক্তিত্ব নেই, বাধ্য ধরনের, কবির নির্দেশ মেনে চলছে বলেই মনে হয়, কিন্তু ওদের পরিবার রক্ষণশীল। যদি রাণুকে সুদূর মৈমনসিং-এ নিয়ে গিয়ে পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে? সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।
রাণুর সঙ্গে ছেলেটির পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। কবি একদিন জানতে চাইলেন, ওকে তোমার কেমন লাগে?
রাণু ওষ্ঠ উলটে বলল, লাল মুলো!
বৃহৎ ঠাকুর পরিবারেও যুবকের অভাব নেই। তাদের কেউ কেউ এখন নতুন উৎসাহে কবির রচনা কণ্ঠস্থ করে, কবির কাছে তার পরীক্ষাও দিতে চায়।
এ ছাড়াও বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার ও উচ্চ রাজকর্মচারী তরুণেরা কবির কাছে আসা যাওয়া করে, তাদের অভিভাবকেরা চিঠি লেখেন, কবি কিছুতেই মনস্থির করতে পারছেন না। কারুকেই পুরোপুরি মনঃপূত হয় না।
রাণুর বাবা-মা অধীর হয়ে পড়লেও এখনও কিছুই ঠিক হল না। তারা অপেক্ষা করে আছেন কবির নির্দেশের। হয়তো নাটকের শেষ পৃষ্ঠাটি লেখার মতন, রাণুর বিবাহ-পর্বও যতদূর সম্ভব বিলম্বিত করতে চান কবি। চেতনে কিংবা অবচেতনে।
চিঠি লেখা কমাতে পারেননি, রাণু লিখলে উত্তর না দেওয়া কি তাঁর পক্ষে সম্ভব? রাণু তাঁর কাছে আসতে চাইলে তিনি কি নিষেধ করতে পারেন? বরং, এক-দু মাসের ব্যবধান হলেই তাঁর ভেতরে একটা ছটফটানি শুরু হয়। লিখতে লিখতে থেমে যায় কলম।
এ রকম একটা আশঙ্কা তাঁর মনের গহনে রয়ে গেছে, যদি রাণু নিজেই হঠাৎ কারুকে পছন্দ করে ফেলে? অত্যুৎসাহী যুবকেরা যদি বেনারসেও চলে যায়। সেখানে কী ঘটছে, তার সব তো কবি জানতে পারছেন না।
অবশ্য রাণুর মা কথা দিয়েছেন, কবির সম্মতি না নিয়ে কারুকে পাকা কথা দেওয়া হবে না।
শত কাজের মধ্যেও কবি যেন একটা যাই যাই শব্দ শুনতে পান। রাণু চলে যাবেই। খেলার সাথী, বিদায় দ্বার খোলো-এবার বিদায় দাও। গেল যে খেলার বেলা। ডাকিল পথিকে দিকে বিদিকে, ভাঙিল রে সুখমেলা।
চিনদেশ থেকে আমন্ত্রণ এসেছে। অনেকদিন দেখা হবে না, রাণু তাই এসেছে শান্তিনিকেতনে। কিন্তু তার সঙ্গে নিরিবিলিতে বিশ্রম্ভালাপ করার কি জো আছে, যেন অবিরাম স্রোত বয়ে যাচ্ছে মানুষের। শান্তিনিকেতনে কেন হঠাৎ এত মানুষ আসছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন কিছু কিছু বিশিষ্টজন, কবিকে তাঁদের জন্য সময় দিতেই হয়।
রাণু এসে এক একবার উঁকি মারে, ঘর ভরা লোকজন দেখলে চকিতে সরে যায়। কবি দেখতে পান তার বুক ভরা অভিমান তরঙ্গিত হচ্ছে মুখে।
রাণুকে কিছু সময় আটকে রাখার জন্য কবি একটা উপায় বার করেছেন।
চেকোস্লোভাকিয়া থেকে এসেছেন এক বিশিষ্ট শিল্পী। এঁর পোট্রেট আঁকার হাত খুব ভাল। ইনি নিজেই একদিন টগরফুলের মালা গাঁথতে থাকা রাণুকে দেখে তার একটা প্রতিকৃতি আঁকার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন কবির কাছে। কবিরও মনে হয়েছিল, বিয়ের আগে রাণুর একখানা ছবি আঁকিয়ে রাখলে খুব ভাল হয়।
তেল রঙের ছবি, বেশ কয়েকদিন সিটিং দিতে হবে। তিনি রাণুকে রাজি করালেন। বলে দিলেন, বেশি নড়াচড়া করবে না। শিল্পী যেদিকে বলবেন, সেদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হবে।
শিল্পীর নাম নভ্কভ্স্কি, দীর্ঘকায় পুরুষ, কাজ চালানো গোছের ইংরিজি বলতে পারেন। কণ্ঠস্বর গমগমে। তাঁর ঘর ‘শান্তিনিকেতন’ বাড়িটির দোতলায়। সেখানে উত্তরের আলো আসে।
এঁর ছবি আঁকার ধরনটি বিচিত্র। ইজেলে ক্যানভাস লাগানো, কিন্তু প্রথম কয়েকটি দিন তিনি তুলির বদলে রঙিন পেন্সিলে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় রাণুর স্কেচ করতে লাগলেন কাগজে। শুধু বিভিন্ন ভঙ্গিমায় নয়, নানা রকম পোশাকে।
প্রথম দিনই তিনি রাণুকে বললেন, তোমার অনেকগুলো পোশাক নিয়ে এসো। আলাদা আলাদা রঙের।
এক পোশাকে একটা স্কেচ করার পর বললেন, এবার হলুদ কাপড়টা পরে নাও!
রাণু পোশাকগুলো নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, শিল্পী বললেন, কোথায় যাচ্ছ, এখানেই বদলে নাও!
রাণু অবাক চোখে তাকাল। লোকটি বলে কী? অন্য লোকের সামনে মেয়েরা কাপড় বদলাতে পারে?
সে চলে গেল পাশের ঘরে।।
তার ফিরতে দেরি হচ্ছে বলে অস্থির হয়ে উঠছেন শিল্পী।
রাণু ফিরতেই তিনি বললেন, আমি সময় নষ্ট করতে পারি না। এর পরের বার আমি উলটোদিকে ফিরে থাকব, তুমি এখানেই পালটে নিও।
রাণু বলল, না। আমি তা পারব না।
এবার শিল্পীটির অবাক হবার পালা। তিনি যদি না তাকিয়ে থাকেন, তাতেও লজ্জার কী আছে? প্রাচ্য দেশে অনেক কিছুই বোেঝা যায় না।
চারদিন পর রেখাঙ্কন শেষ হল। এবার শিল্পী রাণুকে একটি চেয়ারে বসিয়ে তুলি হাতে নিলেন। ক্যানভাসে তুলি ছোঁয়াবার আগে তিনি রাণুর কাছে এসে গালটি ধরে বললেন, একটু ডানদিকে তাকাও। কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, রিল্যাক্স, রিল্যাক্স।
রাণু কেঁপে উঠল। অচেনা পুরুষ মানুষের স্পর্শ। এ দেশের লোকেরা মেয়েদের গায়ে হাত দেয় না। কিছু কিছু গুরুজন শ্রেণীর প্রৌঢ়দের কথা আলাদা, যারা স্নেহ জানাবার অছিলায় বুকে জড়িয়ে ধরতে চায়। রাণু সেই সব গুরুজনদের কাছাকাছি যায় না দ্বিতীয়বার।
এক এক সময় মনে হয়, ছবি আঁকার ব্যাপারটা যেন শাস্তির মতন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক জায়গায় বসে থাকা যায়? তাও নড়াচড়া করা চলবে না। একটু এদিক ওদিক হলেই শিল্পী কাছে এসে গাল ধরবেন, কাঁধ ধরবেন, বুকের আঁচল ঠিক করে দেবেন। তাতে আরও অস্বস্তি।
ছবির জন্য এসে বসতে হয় দুপুরে, বিকেলের আলো ম্লান হয়ে গেলে রাণুর ছুটি। তখনও কবির ঘরে নোকজন ভর্তি দেখলে সে বলে, আমি সুরুলে চলে যাচ্ছি এল্মহার্স্টের কাছে!
সুরুলে যেতে কোনও অসুবিধে নেই, রাণু সাইকেল চালানো শিখে নিয়েছে।
এল্মহার্স্ট ভারী সুন্দর চা বানায়। যুদ্ধের গল্প বলে। ইংরিজি গান গাইতে পারে বেশ, কিন্তু বাংলা গান কিছুতেই তার গলায় মানায় না।
রাণু জানে, এল্মহার্স্ট এখান থেকে চলে যাবে। কবির সঙ্গে চিন ভ্রমণের লোভে আরও কয়েকটা দিন থেকে যাচ্ছে, ভারত আর চিনের মধ্যে কতখানি মিল বা অমিল তা সে দেখে আসতে চায়। তবে এমহাস্টের কথায় একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর যত দেশই সে ঘুরুক, বাংলাকে সে ভুলবে না, বিশেষত শান্তিনিকেতনকে। তারপর রাণুর দিকে চেয়ে বলে, এবং তোমাকে।
পাশাপাশি অন্য একটা সাইকেলে এল্মহার্স্ট রাণুকে সন্ধের পর আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে যায়।
রাত্রির আহারের পর কবি আর কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। তখনই রাণুর সময়। তখন বারান্দায় বসে দু’জনের গল্প শুরু হয়।
গল্পের চেয়ে গানই বেশি। কবি অনেক গান রচনা করছেন এখন। নতুন-পুরনো অনেক গান শোনান রাণুকে। সেই গানই যেন কথা বলা।
ভেবেছিলেম আসবে ফিরে, তাই ফাগুন শেষে দিলেম বিদায়। তুমি গেলে ভাসি নয়ননীরে, এখন শ্রাবণদিনে মরি দ্বিধায়। এখন বাদল সাঁঝের অন্ধকারে আপনি কাঁদাই আপনারে, একা ঝর ঝর বারিধারে ভাবি কী ডাকে ফিরাব তোমায়। যখন থাকো আঁখির কাছে, তখন দেখি ভিতর বাহির সব ভরে আছে। সেই ভরা দিনের ভরসাতে চাই বিরহের ভয় ঘুচাতে, তবু তোমা হারা বিজন রাতে, কেবল হারাই হারাই বাজে হিয়ায়।
গান শুনতে শুনতে রাণুর চোখে জল আসে। কবির হাতের ওপর হাত রেখে সে বলে, ভানুদাদা, আমি কোথাও যাব না।
তবু যে যেতেই হবে এক সময় তা কবিও জানেন, রাণুও জানে।
এ যেন ট্রেনের কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একজন, আর একজন প্ল্যাটফর্মে। দুজনের হাত মুঠি করে ধরা। ট্রেন নড়েচড়ে উঠতেই সে দুটি হাতে টান পড়ল। কে কাকে টানছে? দুজনেই যেন বলছে, এসো, এসো। তবু মুঠি খুলে যাবে।।
ছবি আঁকা এগিয়েছে অনেকখানি, ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে স্পষ্ট রাণুর আদল। ছবি আঁকার সময় শিল্পীর কথা বলা অভ্যেস। মাঝে মাঝেই বলেন, তোমার মতন এমন নীরব বাত্ময় চোখ আমি আগে আর কোনও নারীর দেখিনি। তোমার কোমরের গড়ন এমন নিখুঁত হল কী করে। তুমি কি কাশীর গঙ্গায় সাঁতার কাটো? তোমার আঙুলগুলি ঠিক চাঁপা ফুলের মতন।
এ সব শুনলে লজ্জারুণ হয়ে যায় রাণু। মুখটা নিচু করলেই শিল্পী দ্রুত কাছে এসে থুতনি ধরে তুলে দেন, তাকিয়ে থাকেন অনেকক্ষণ।
একদিন বিকেল প্রায় শেষ হয়েছে, এবার আঁকা বন্ধ হবে। তুলি রেখে, হাত থেকে রং মুছে শিল্পী রাণুর কাছে এসে তার থুতনিটা ধরলেন। তারপর বললেন, অনেক ছবি এঁকেছি আমি, কিন্তু তুমি আমায় হারিয়ে দিলে। তোমার প্রকৃত রূপ কিছুতেই যেন ফোটাতে পারছি না। আমার সৃষ্টির চেয়েও জীবন্ত তুমি অনেকগুণ সুন্দর। হয়তো আমি যদি তোমায় একবার খুব নিবিড় করে কাছে পাই, একবার জড়িয়ে ধরে একটি চুম্বন করি—
রাণু উঠে দাঁড়িয়ে শিল্পীকে ঠেলে সরিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। ছুটতে ছুটতেই মাঠ পেরিয়ে কবির বাড়িতে চলে এল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দেখল, কবি নেমে আসছেন একা।
রাণু কবির বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, ভানুদাদা, আমি আর ছবি আঁকাবো না, তুমি আমাকে ওখানে আর যেতে বোলো না?
কবি হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, কী হয়েছে?
রাণু বলল, ওই লোকটা আমাকে…ওই লোকটা–
সে আর কিছু বলতে পারল না, শুধু কাঁদতে লাগল।
কবি একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। শরীর জ্বলতে লাগল তাঁর। নিশ্বাস পড়তে লাগল ঘনঘন।
তিনি কঠোর স্বরে বললেন, থাক, তোমাকে আর যেতে হবে না। আমি নভুকভস্কিকে নিষেধ করে দেব। দরকার নেই ছবির।
রাণুর পিঠে তিনি হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তারপর তাকে সামনে ফিরিয়ে দেখলেন তার সজল মুখ।
এই মুখ কি রং তুলিতে ক্যানভাসে ফোটানো সম্ভব? কিংবা শব্দে শব্দে গেঁথে?
সে রাতে কবি রাণুকে আর একটি গান শোনালেন।
আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে, হেরে মাধুরী। নয়ন আমার কাঙাল হয়ে মরে না ঘুরি। চেয়ে চেয়ে বুকের মাঝে গুঞ্জরিত একতারা যে— মনোরথের পথে পথে বাজল বাঁশরি। রূপের কোলে ওই যে দোলে অরূপ মাধুরী। কূলহারা কোন রসের সরোবরে মূলহারা ফুল ভাসে জলের পরে। হাতের ধরা ধরতে গেলে ঢেউ দিয়ে তায় দিই যে ঠেলে—আপন মনে স্থির হয়ে রই, করিনে চুরি। ধরা দেওয়ার ধন সে তো নয়, অরূপ মাধুরী।
পরদিন সকালে বাগানে ফুল তুলতে গেছে রাণু। শরৎ এসেছে, ফুটেছে অজস্র শিউলি ফুল। গাছে যত মাটিতে ঝরে আছে আরও বেশি। আজ শিউলির মালা গেঁথে কবিকে পরাতে হবে।
হঠাৎ সামনে একটা দীর্ঘ ছায়া পড়ল।
চমকে পেছনে তাকিয়ে রাণু দেখল শিল্পী নভ্কভ্স্কি এক দৃষ্টে চেয়ে আছে তার দিকে। রাণুর বুক কেঁপে উঠল। এই রে, শিল্পী কি প্রতিশোধ নিতে এসেছেন নাকি? কাছাকাছি কেউ নেই।
শিল্পী দুঃখী ভাঙা গলায় বললেন, রাণু, তুমি কবিকে বলে দিলে কেন?
রাণু অধোবদনে পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁটতে লাগল।
শিল্পী বললেন, আমি যা চেয়েছিলাম, তুমি রাজি না হলে আমি কি জোর করতাম? আমি কি বর্বর?
রাণু বুঝতে পারল, মানুষটি খুবই আঘাত পেয়েছেন। কিন্তু রাণু কী করবে, কাল যে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল।
শিল্পী বললেন, আজই আমি শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আর কোনওদিন দেখা হবে না।
রাণু কেঁদে উঠে বলল, সে কি, আপনি আজই চলে যাবেন? আপনার সব কাজ হয়ে গেছে?
শিল্পী একটা গাছের গুড়ির গায়ে ঘুষি মেরে বললেন, চুলোয় যাক কাজ!
আপনি আমার ব্যবহারের জন্যই চলে যাবেন? আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।
শিল্পী এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন রাণুর মুখের দিকে।
অস্ফুট স্বরে বললেন, হল না। কিছুই ফোটানো হল না।
তার উল্টোদিকে ফিরে হাঁটতে লাগলেন হন হন করে।
রাণু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার একটা গাছ হয়ে যেতে ইচ্ছে হল।
তারপর দূর থেকে কেউ ডাকল রাণুর নাম ধরে।
রাণুকেও কাশী ফিরে যেতে হবে। শান্তিনিকেতনে ছুটি শুরু হচ্ছে। কবি সদলবলে যাত্রা করলেন চিন দেশের উদ্দেশে।
সেখান থেকে জাপান ঘুরে দেশে ফিরবেন প্রায় পাঁচ মাস পরে।
তার দু’মাস পরে আবার দিলেন বহু দূরপাল্লার পাড়ি। পেরুর স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছেন। দক্ষিণ আমেরিকায় আগে যাওয়া হয়নি, তাঁর অনেক দিনের সাধ, আমন্ত্রণটিও খুব সম্মানের।
রাণুর পত্র নির্বাচন হল না এখনও। কবি মনে মনে জানেন, তিনি যতদিন না ফিরছেন, ততদিন রাণুর পরের ঘরে যাবার কোনও সম্ভাবনা নেই। ততদিন রাণুর একমাত্র মনের মানুষ থাকবে তার ভানুদাদা।
রাণুর জন্য পাত্র নির্বাচন এবং পাকা কথা হয়ে গেল অবশ্য কবির অনুপস্থিতিতেই।
ঘটকালি করলেন লেখিকা অনুরূপা দেবী। এ সম্বন্ধ একেবারে আশাতীত।।
বর্তমানে বাঙালিদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর ব্যবসা ক্ষেত্রে তাঁর মতন সফল আর কেউ নন। ইংরেজ শ্ৰেষ্ঠীদের সঙ্গেও তিনি পাল্লা দিয়ে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছেন, ব্রিটিশ সম্রাট তাঁকে দিয়েছেন নাইটহুড।
স্যার রাজেনের সুযোগ্য পুত্র বীরেন বিলেত থেকে লেখা-পড়া শিখে এসে যোগ দিয়েছে পিতার ব্যবসায়ে। তার জন্য পাত্রী খোঁজা চলছিল, অনুরূপা দেবীর মাধ্যমে কাশীর অধিকারী পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ হতেই আর বেশি কথাবার্তার প্রয়োজন হল না। এক পক্ষ মুগ্ধ হল রূপ দর্শনে, অন্য পক্ষ আকৃষ্ট হল বিত্তে।
মুখোপাধ্যায় পরিবারটি সনাতন হিন্দু রীতি নীতি যেমন মানে, তেমনই বিলিতি চাল চলনেও অভ্যস্ত। খাঁটি ব্রাহ্মণ ঘরের সুলক্ষণা, সুদর্শনা কন্যার ঠিকুজি কুষ্ঠি যেমন মিলিয়ে নেওয়া হল, তেমনই বিয়ের আগে কিছুদিন চলতে লাগল কোর্টশিপ। রাণুকে এনে রাখা হল আলিপুরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়িতে, বীরেন এক একদিন ঘোড়ায় চেপে সেখানে আসে, নানা বিষয়ে আলোচনা হয়, এক একদিন সে ভাবী পত্নীকে নিয়ে হাওয়া খেতে যায় ময়দানে।
কবি এ সব কিছুই জানতে পারলেন না।
হারানামারু জাহাজে চেপে সমদ্র পাড়ি দিতে দিতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, পেরু পোঁছোবার আগেই চিকিৎসকদের নির্দেশে তাঁকে নামিয়ে নেওয়া হল বুয়োনোসআয়ারসে। সেখানকার শহরতলি সান ইসিদ্রোতে এক বাগানবাড়িতে তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন ভিক্টোরিয়া ওকামপো নামে এক ধনবতী মহিলার সেবা ও সান্নিধ্যের উষ্ণতায়।
কবিকে না জানিয়েই সব ঠিক হয়ে গেল, এ জন্য অপরাধবোধ হল রাণুর মায়ের। কবি কোথায় রয়েছেন, তাও জানা নেই। অথচ এমন পাত্র হাতছাড়াও করা যায় না। সমস্ত খবর জানিয়ে একটা চিঠি লিখে বম্বেতে পাঠিয়ে দেওয়া হল, খামের ওপরে লেখা রইল টু অ্যায়েট অ্যারাইভাল। এবং স্থির হল, কবি এসে পৌঁছবার পর হবে আশীর্বাদ। ততদিন কোর্টশিপ চলুক।
শেষ পর্যন্ত পেরু যাওয়া হলই না কবির।
ফেরার পথে ইওরোপ হয়ে বম্বে পৌঁছেই পেলেন সেই চিঠি। পড়েই বুঝলেন, এ সম্বন্ধ অবধারিত। পাত্র সম্পর্কেও আপত্তি জানাবার কারণ নেই। এক অধ্যাপকের কন্যার গলায় বরমাল্য দেবে এক রাজপুত্র। একালের ধনী ব্যবসায়ীরাই তো রাজার স্থান নিয়েছে।
কলকাতায় আসবার আগেই তিনি চিঠিতে জানিয়ে দিলেন তাঁর সম্মতি, শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ।।
দেশে ফেরা মানেই নানান সমস্যায় জড়িয়ে পড়া। রাজনৈতিক ডামাডোল ও পুলিশি ধরপাকড় চলছেই। কবি আর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান না, আর সে জন্যই সমালোচিত ও নিন্দিত হচ্ছেন কিছু কিছু পত্রপত্রিকায়। তিনি গান্ধীজির চরকা-নীতি সমর্থন করতে পারেননি, শান্তিনিকেতনে এসে দেখলেন, সেখানে প্রায় ঘরে ঘরে চরকায় তকলিতে সুতো কাটা চালু হয়ে গেছে, বিধুশেখর শাস্ত্রী ও নন্দলাল বসুর মতন মানুষও তাতে উৎসাহের সঙ্গে মেতেছেন।
কবি অসন্তুষ্ট হলেও তা প্রকাশ করলেন না, ওঁদের নিষেধও করলেন না।
হঠাৎ তাঁর রচনার স্রোতটিও শুষ্ক হয়ে গেল। পুরনো নাটকগুলো মাজা ঘষা করেন, নতুন কিছু মনে আসে না। মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যান।
জার্মানি থেকে বিশিষ্ট বন্ধু কাইসারলিঙ একটি প্রবন্ধ লেখার অনুরোধ পাঠিয়েছেন। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিবাহ প্রথা বিষয়ে একটি সংকলন সম্পাদনা করছেন। তাঁর খুব ইচ্ছে ভারতীয় বিবাহের আদর্শ বিষয়ে রচনাটি কবির লেখা হবে।
ভারতীয় বিবাহের আদর্শ বলে সত্যিই কি কিছু আছে? বিয়ে তো পাত্র-পাত্রীরা করে না। তাদের বাবা-মায়েরা বিয়ে ঘটিয়ে দেয়। এর মধ্যে প্রেমের স্থান কোথায়? প্রেম আছে কাব্যে। সমাজ জীবনে তো শুধু প্রথা ও লোকাচার।
আসন্ন একটি বিবাহের কথা কবির মনের মধ্যে সদা জাগ্রত, তাই তিনি এই বিষয়টি নিয়ে লিখতে রাজি হলেন।
হঠাৎ একটি চিঠি পেয়ে কবির বুকে যেন আচম্বিতে বজ্রাঘাত হল। তিনি কাঁপতে লাগলেন।
চিঠিখানি লিখেছেন রাণুর মা। তাঁর কাছে কয়েকটি উড়ো চিঠি এসেছে, সেই চিঠিগুলোও তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন এই সঙ্গে। এবং জানিয়েছেন, এ রকম চিঠি রাণুর ভাবী শাশুড়ির কাছেও গেছে।
স্বাক্ষরহীন চিঠিগুলি কদর্য ইঙ্গিতে ভরা। কবির সঙ্গে রাণুর সম্পর্কের নানান বর্ণনা লিখে জানানো হয়েছে, এ বিবাহ সুখের হতে পারে না। দু’একটি চিঠিতে লেখা হয়েছে অন্য কথা। কবি নিজে তো রাণুকে বিয়ে করবেন না। তিনি তো গুরুদেব সেজে আছেন, তাই তিনি চান, নিজের অতি বশংবদ, কোনও ছেলের সঙ্গে রাণুর বিয়ে দিয়ে নিজের কাছে রাখতে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি একটি যুবকের সঙ্গে রাণুর পরিচয় করিয়ে দিয়ে, দুজনের এমন অবাধ মেলামেশার প্রশ্রয় দিয়েছেন, যা অবৈধ প্রেমের পর্যায়ে পড়ে। এ কন্যা কীটদ্ৰষ্ট, রাজেন মুখার্জির মতন উচ্চ বংশের যোগ্য হতে পারে না।
এ সব চিঠি পড়ার সময় কবিকে দেখলে কেউ চিনতেই পারবে না। তাঁর এমন পাংশুবর্ণ, বিহ্বল মুখ কেউ কখনও দেখেনি।
বিভিন্ন রচনা ও সামাজিক ভূমিকার জন্য সারাজীবনে তিনি প্রচুর কটুক্তি ও নিন্দাবর্ষণ সহ্য করেছেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র ও নৈতিকতা বিষয়ে কেউ কখনও দোষারোপ করেনি। চৌষট্টি বছর বয়েসে এসে তাঁর নামে এমন কলঙ্ক আরোপের চেষ্টা চলেছে?
এ সব কথা হু-হু করে ছড়ায়। পাত্র পক্ষ এর সামান্য অংশও বিশ্বাসযোগ্য মনে করলে এ বিয়ে ভেঙে যাবে। এতদুর প্রস্তুতির পর বিয়ে ভেঙে গেলে রাণুর সারা জীবনটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
না, না, যেমন করেই হোক, রক্ষা করতে হবে এই সম্বন্ধ।
কবির বুকটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। সেই অবস্থায় তিনি চিঠি লিখতে বসলেন পাত্রের মাকে:
…কোনও এক গুপ্তনামা নিন্দুক রাণুর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া আপনাকে যে পত্র দিয়াছে, রাণুর মা আজ তাহা আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।
বিদেশ হইতে বোম্বাই ফিরিয়া আসিয়াই সংবাদ পাইলাম, আপনাদের ঘরে রাণুর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। শুনিয়া বড় আহ্লাদে রাণুকে আশীর্বাদ করিয়া পত্র পাঠাইলাম। শ্রীমান বীরেনকেও লিখিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় রাণুর মার চিঠি পাইয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি।
রাণুকে তাহার শিশুকাল হইতে জানি এবং একান্ত মনে স্নেহ করি। ইহা জানি, তাহার চরিত্র কলুষিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহার বয়েসে বাঙালির ঘরের মেয়েরা যে সাধারণ অভিজ্ঞতা সহজে লাভ করে, তাহার তাহা একেবারেই ছিল না, সে এমনই শিশুর মতন কাঁচা যে তাহার কথাবার্তা ও আচরণ অনেক সময়ই হাস্যকর মনে হইত। এইরূপ অনভিজ্ঞতাবশত লোক ব্যবহার সম্বন্ধে তাহার কোনও ধারণা ছিল না। এই কারণে রাণুর বিবাহ সম্বন্ধে আমার মনে বিশেষ উদ্বেগ ছিল। আমি তাহার জন্য এমন সৎপাত্র কামনা করিতেছিলাম, যে তাহার একান্ত সরলতার যথার্থ মূল্য বুঝিবে এবং লৌকিকতার ত্রুটি ক্ষমা করিবে।
এক সময় আমার এক বন্ধু পুত্র আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দৈবক্রমে রাণুকে দেখিয়া তাহাকে বিবাহের জন্য উৎসুক হইয়া উঠে। সগোত্রে বিবাহে তাহার পিতার সম্মতি হইবে না আশঙ্কা করিয়া আমি প্রথমে বাধা দিই। তখন তাহার পিতা কলিকাতায় ছিলেন না। সেই ছেলেটি ও তাহার একজন গুরুস্থানীয় আমাকে বারবার আশ্বাস দিলেন যে, আপত্তি গুরুতর হইবে না এবং বিবাহ নিশ্চয়ই ঘটিবে।
ছেলেটি ভাল, তাহার হাতে রাণু কষ্ট পাইবে না নিশ্চয় ভাবিয়া আমি তাহাদের পরিচয়ে বাধা দিই নাই, কিন্তু পরিচয় বলিতে একবার শান্তিনিকেতনে দেখা হইয়াছিল। রাণু তখন আমার কন্যা মীরা ও বউমার সঙ্গে ছিল। ছেলেটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দেখা হওয়া তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল।
আপনি আমার কন্যা বেলাকে জানিতেন। তাহার ছোট ভাই শমী বাঁচিয়া নাই। আমি অনেকবার ভাবিয়াছি যে, সে যদি বাঁচিয়া থাকিত, তবে রাণুর সঙ্গে নিশ্চয় তাহার বিবাহ দিতাম।
সঙ্গে সঙ্গে আর একটি চিঠি লিখলেন সরযুকে :
চিঠি পেয়ে বজ্রাহত হলুম। কিন্তু ভয় পেয়ো না। আমার যা সাধ্য তা আমি করবো। Lady Mukherji কে আজই চিঠি লিখে দিলুম। Sir Mukherji কে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছি। খুব সম্ভব দুজনেই এখানে আসবেন। রাণুকে বোলো, বেশি উদ্বিগ্ন না হয়। সমস্তই ঠিক হয়ে যাবে।
চিঠি লিখছেন, আর কবির হাতে কাঁপছে।
নিন্দুকরা এর মধ্যে আরও কত বিষ ছড়াচ্ছে কে জানে! ওই সব আড়ালের নিন্দুকরা কারা তা জানার উপায় নেই, খুব কাছের মানুষও হতে পারে।
কবি স্নান করলেন না, আহারেও তাঁর রুচি হল না।
কবির শরীর খারাপ মনে করে উদ্বিগ্ন হয়ে প্রতিমা খোঁজ নিতে এল বারংবার। কবি তাকেও কিছু বলতে পারছেন না।
ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থেকেও তাঁর ঘুম এল না। চোখে ভাসতে লাগল রাণুর মুখ। সে ও কি এসব শুনেছে? কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে তার? সে কি কান্নাকাটি করছে খুব।
প্রশান্তর মুখে কবি শুনেছেন, ভাবী স্বামীর সঙ্গেই বেশ ভাব হয়ে গেছে রাণুর। মনে মনে সে একেবারে তৈরি হয়ে রয়েছে এই বিয়ের জন্য। এখন যদি বিয়েটা ভেঙে যায়।
যে-আঘাত সে পাবে, তার পরেও কি সে তার ভানুদাদাকে ভালো বাসতে পারবে?
তিনিই বা রাণুকে সান্ত্বনা দেবেন কোন ভাষায়?
সস্ত্রীক রাজেন মুখার্জি যখন কবির সঙ্গে দেখা করতে এলেন, তখন তাঁর সঙ্গে রয়েছে আরও কয়েকটি কুৎসাপূর্ণ চিঠি।
দু’পক্ষে কয়েকদিন ধরে আলোচনা চলল।
কবি বারবার ব্যাকুল ভাবে বোঝাতে লাগলেন, রাণুদের পরিবারের সকলের সঙ্গে তাঁর অনেকদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, রাণুকে তিনি বিশেষ স্নেহ করেন, কিছু কুলোক তার মন্দ ব্যাখা করতে চাইছে।
শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, বীরেনের মতামত নেওয়া হবে। সে রাজি হলে আর কোনও বাধা থাকবে না।
বীরেন বিলিতি আদব-কায়দায় অভ্যস্ত। সে রাণুকে দেখেছে একাধিক বার, কথা বলেছে, তাকে পছন্দ করেছে। উড়ো চিঠি টিটি সে গ্রাহ্য করে না, তার আপত্তির কোনও প্রশ্নই ওঠে না।
বিয়ের তারিখও ধার্য হয়ে গেল। মেঘ মুক্ত হয়ে কবি বিরাট স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।
রাণু এসব কিছুই জানে না। সে বিয়ের আগের কয়েকটা দিন ভানুদাদার সঙ্গে কাটাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। লিখছে চিঠির পর চিঠি।
কবি এখন সতর্ক হয়ে গেছেন। রাণুর চিঠির উত্তর দিচ্ছেন নির্লিপ্ত ভাষায়। শেষ চিঠিতে লিখলেন :
বিবাহের অধিকদিন আগে তোমার পক্ষে কলকাতা যাওয়া ঠিক হবে না। বিশেষত আমার বাড়িতে থাকলে সর্বদাই নানাদিক থেকে উৎপাতের আশঙ্কা আছে। খুবই ইচ্ছা ছিল, বিবাহের আগে কিছুকাল তোমরা সবাই আমার বাড়িতেই থাকব কিন্তু সেটা ঘটতে দিল না।
শান্তিনিকেতনে ওদের উৎপাত চিঠি ছাড়া আর কোনও আকারে পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং এখানে তোমরা যতদিন খুশি নিরুপদ্রবে থাকতে পারো।
রাণু প্রায় জোর করেই বাবা-মাকে রাজি করিয়ে, সবাইকে নিয়ে চলে এল শান্তিনিকেতন। এবার যেন অন্যরকম। পদে পদে বিধিনিষেধ। সবাই খালি উপদেশ দেয়, দৌড়োবে না, বৃষ্টি ভিজবে না, দুপুর রোদে বেরোলে রং কালো হয়ে যাবে। ঠিক সময় খাবে, ঠিক সময় ঘুমোবে।
এমনকী রাণুর ভানুদাদাও সবার সামনে তাকে অনবরত উপদেশ দেন, শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে কেমনভাবে ব্যবহার করতে হবে সবার সঙ্গে। গুরুজনদের সেবা আর ছোটদের প্রতি স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে হতে হবে আদর্শ স্ত্রী।
রাণু অন্য সব বিধিনিষেধ মানে, শুধু রাত্তিরবেলা সে একবার ভানুদাদার কাছে যাবেই যাবে। তখন ভানুদাদা তার একান্ত আপন। ভানুদাদাও অপেক্ষা করেন তার জন্য। ওপরের বারান্দায় জ্যোৎস্নালোকে বসে দুজনের কত কথা, কত গান।
এখন আর বাবা-মাও তাকে নিষেধ করেন না। আর তো মাত্র কয়েকটি দিন, তারপর মেয়ে চলে যাবে পরের বাড়িতে। সব মাবাবারই মনটা এই সময় নরম হয়ে থাকে। খুব বড়লোকের বাড়ির বউরা বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারে না। বিয়ের পর রাণুর সঙ্গে আর কবে দেখা হবে, তার ঠিক নেই! সেইজন্যই এখন বেশি শাসন করে মেয়ের মনে আঘাত দিতে মন চায় না।
সব বাঙালি মেয়েকেই একটা বয়েস থেকে বিয়ের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। রাণুর এর চেয়ে ভাল বিয়ে তো আশা করা যায় না। তার মনে খুশির ছোঁয়া লেগেছে ঠিকই, আবার যখন তখন কান্নাও পায়। মুক্ত বিহঙ্গকে বন্দি করা হবে খাঁচায়, হোক না সেটা সোনার তৈরি খাঁচা।
ভানুদাদার সঙ্গে হাসি-গল্প করতে করতে হঠাৎ সে কেঁদে ফেলে ঝরঝরিয়ে। কবি বাধা দেন না, চেয়ে থাকেন একদৃষ্টিতে।
এক সময় কান্না থামিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, ভানুদাদা, আমি আর শান্তিনিকেতনে আসব না?
কবি বললেন, না এসে পারবে? তোমার স্বামীকে বুঝিয়ো।
রাণু বলল, কী জানি ভয় করে। শুনেছি, তাঁর খুব কাজের নেশা।
কবি বললেন, কাল হঠাৎ রাতে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল, সকালে উঠে তোমাকে আর দেখতে পাব না। তোমার বাবা কলকাতা ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, বোধহয় তোমাদের সবাইকে নিয়ে চলে গেছেন।
রাণু বলল, তা কখনও সম্ভব? তোমাকে না জানিয়ে চলে যেতে পারি?
কবি বললেন, অসম্ভবের কথাও এক এক সময় মনে আসে। আর ঘুম এল না, একটা গান লিখে ফেললুম। এখনও দিনুকে শেখানো হয়নি।
রাণু বলল, আমি তবে প্রথম শুনব।
কবি গাইতে লাগলেন :
না বলে যায় পাছে সে আঁখি মোর ঘুম না জানে।
কাছে তার রই, তবুও ব্যথা যে রয় পরাণে।
যে পথিক পথের ভুলে এল মোর প্রাণের কূলে
পাছে তার ভুল ভেঙে যায়, চলে যায় কোন্ উজানে।
এল যেই এল আমার আগল টুটে
খোলা দ্বার দিয়ে আবার যাবে ছুটে।
খেয়ালের হাওয়া লেগে যে খ্যাপা ওঠে জেগে
সে কি আর সেই অবেলায় মিনতির বাধা মানে।
এ গান শুনেও কান্নার কী আছে? তবু রাণু কান্নায় ভেঙে পড়ল। সে জানে, কবি কত ব্যথা পাচ্ছেন ভেতরে ভেতরে। সে নিজেও তো কল্পনা করতে পারছে না, এরপর ভানুদাদার সঙ্গে তার দেখাও হয়তো হবে না, তবু তার জীবনটা কাটবে কী ভাবে।
কবি তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, এসো।
আষাঢ় মাস, বর্ষা নেমে গেছে। প্রতিদিন বর্ষা আসছে কেঁপে কেঁপে, এরই মধ্যে চলেছে রাণুর বিয়ের প্রস্তুতি।
কবির আবার ইওরোপ যাবার কথা। ভেবেছিলেন রাণুর বিবাহের দিন থাকতেই পারবেন না, কিন্তু সে যাত্রা পিছিয়ে গেল।
তিনি আশা করেছিলেন, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থেকেই বিয়ে হবে রাণুর, সে জন্য বাড়ি রং করালেন। কিন্তু পাত্র পক্ষ তাতে রাজি নন, এ বিয়েতে ঠাকুর বাড়ির কোনও ভূমিকা তাঁরা চান না।
রাজেন্দ্রনাথ মধ্য কলকাতায় একটি মস্ত বড় বাড়ি ভাড়া করে দিলেন কন্যাপক্ষের জন্য। সে বাড়িতে বাগান আছে, পুকুর পর্যন্ত আছে। অধিকারীদের সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের স্থান সঙ্কুলান হয়ে যাবে সেখানে।
বিয়ের দিন বৃষ্টি পড়ছে সকাল থেকে। দুপুরেই কবি পুত্রবধূ প্রতিমাকে পাঠিয়ে দিলেন, তার মতন এমন সুন্দর করে সাজাতে আর কেউ পারে না।
এক দঙ্গল মেয়ে ঘিরে বসে আছে, তার মধ্যে সাজানো হচ্ছে রাণুকে। যেন একটু একটু করে গড়া হচ্ছে দেবী প্রতিমা। ডাকের সাজের মতন সোনা-রুপোর গয়নার মুড়ে দেওয়া হল সারা শরীর। যত্নে বাঁধা কবরীতে যূথী ফুলের মালা।
সাজ যখন প্রায় শেষ, তখন বীরেনের এক বোন প্রেমলতা এসে বলল, এ সাজ চলবে না। সব খুলে ফেলতে হবে। সে নিজে সাজাবে।
সবাই বিস্মিত। এত সুন্দর সাজ। খুলে ফেলতে হবে কেন?
বীরেনের মা বলে পাঠিয়েছেন, প্রতিমা একবার বিধবা হয়েছিল। রথীর সঙ্গে তার দ্বিতীয়বার বিয়ে হয়েছে। শুভ কাজে এরকম কোনও রমণীর স্পর্শই অকল্যাণকর।
জল এসে গেল প্রতিমার চোখে। সে সেখান থেকে দৌড়ে চলে গেল। রাণুও উঠে যাচ্ছিল তাকে ধরতে, অন্য সবাই তাকে জোর করে বসিয়ে রাখলেন চেয়ারে। সেও কাঁদতে লাগল নিঃশব্দে।
উপস্থিত সকলকে বলে দেওয়া হল, এ কথা কোনওক্রমেই জানানো হবে না কবিকে। পাত্রপক্ষের প্রবল প্রতিপত্তি, তাদের কোনও নির্দেশই উপেক্ষা করার উপায় নেই। তারা যদি বেঁকে বসে, লগ্নের সময় যদি বর না আসে, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, সারাজীবনে রাণুর আর বিয়ে হবে না। পাত্রের অন্য বিয়েতে অবশ্য কোনও নিষেধের কথা লেখা নেই শাস্ত্রে।
আলোর রোশনাইতে রাতকে দিন করা হয়েছে, চতুর্দিকে ফুলের সমারোহ। রোশনচৌকিতে শানাই বাজাচ্ছে বিখ্যাত বাদকের দল। দ্বারের কাছে আমন্ত্রিতদের গায়ে পিচকিরিতে আতর ও গোলাপজল ছড়াচ্ছে কয়েকটি বালক-বালিকা। বিলি হতে লাগল কাগজে ছাপা অনুরূপা দেবীর লেখা বিয়ের পদ্য।
যথা সময়ে পরপর কয়েকটি রোলস রয়েস গাড়িতে চেপে উপস্থিত হল বর ও বরযাত্রীর দল। উলুধ্বনিতে মুখরিত হল অঞ্চল। রাণুর মা গঙ্গাজলে বীরেনের পা ধুইয়ে দিয়ে বরণ করে নামালেন গাড়ি থেকে।
সমস্ত রকম শাস্ত্রীয় আচার মেনে নিষ্পন্ন হল বিবাহ।
শান্তিনিকেতন থেকে গায়ক-গায়িকার দল আনিয়েছেন কবি। শুভদৃষ্টির আগে দণ্ডায়মান বরকে ঘিরে, পিড়িতে বসানো কনেকে যখন সাত পাক ঘোরানো হল, তখন তারা গান ধরল, একটু দুরে বসে সব দেখতে লাগলেন কবি। এক সময় যজ্ঞ শুরু হতেই তিনি উঠে চলে গেলেন।
তারপর বাসর ঘরে নানা রকম গান বাজনা ও রঙ্গ কৌতুক চলল অনেক রাত পর্যন্ত। সেখানে ঠাকুরবাড়ির কেউ উপস্থিত রইলেন না।
পরদিন ভোরে গাড়ি নিয়ে এলেন ভাসুর। এসে গেল বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের মুহূর্ত। এ সময় চেঁচিয়ে কাঁদতে নেই, মুখে আঁচল চাপা দিতে হয়। ঝাপসা চোখে রাণু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, বুঝতেই পারল না, কখন পৌঁছে গেল শ্বশুর বাড়ি।
হ্যারিংটন স্ট্রিটে মুখার্জিদের প্রাসাদটি কলকাতার অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান।
সকালে সেখানে হল হিন্দু মতে কুশণ্ডিকা। সন্ধ্যায় বিলিতি কায়দায় রিসেপশান। বাংলার গর্ভনর, বহু ইংরেজ রাজ-পুরুষ এবং অনেক রাজা-মহারাজ, বিখ্যাত ব্যক্তিদের আগমনে ভরে গেল বিশাল হল ঘর। বাজতে লাগল বিলিতি বাজনা। প্রথমে পরিবেশিত হল চা, তারপর শ্যাম্পেন।
বিবাহের পরের রাতটিকে বলে কালরাত্রি। এ রাতে বর ও বধূর এক সঙ্গে থাকতে নেই। রাণুকে নিয়ে যাওয়া হল তার বড় ননদের ঘরে।
তৃতীয় রাত, ফুলশয্যার রাত্রিটিতেই প্রকৃত পক্ষে বর ও বধূর প্রথম মিলন। তাদের জীবনে এটাই দীর্ঘতম রাত। এ রাতে ঘুম জানলার ঝিল্লিতে অপেক্ষা করে বারবার ফিরে যায়। শেষ রাতে পাকাপাকি আসে। তাই পরদিন রোদুর উঠে গেলেও তাদের কেউ জাগায় না।
কিন্তু পরদিন সকাল হতে না হতেই এই নব দম্পতির দরজায় ঘা দিয়ে ডেকে জাগাতে হল। নববধুর সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে।
এরকম দিনে, এত সকালে কেউ আসে? এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার কেউ কখনও দেখেনি। বাড়ির সকলেরই ভুরু কুঞ্চিত হয়ে গেল।
অন্য কেউ হলে ফিরিয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু আগন্তুকটি যে সে কেউ নয়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্তান, খ্যাতিমান পুরুষ, তাই তাঁকে বসিয়ে রাখা হল বৈঠকখানা ঘরে।
কবি সেখানে বসে রইলেন একা। পরের ট্রেনে তিনি শান্তিনিকেতনে যাবেন, তাই রাণুকে একবার দেখতে এসেছেন। এভাবে, এই সময়ে, আগে থেকে কিছু না জানিয়ে আসাটা যে অসমীচীন, সে কথা তাঁর মনেই আসেনি।
অনাত্মীয় পরপুরুষদের সামনে এ বাড়ির বউদের দেখা করার প্রথা নেই। তবু কর্তারা যখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি দিয়েছেন, নতুন বউকে পুরোপুরি সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠাতে হবে। অনেকটা সময় লাগল।
বেগুনি রঙের ঢাকাই শাড়ি ও অনেক রকম অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে, ননদিনী ও অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে রাণু নেমে এল নীচে। দাঁড়াল ড্রয়িংরুমের দরজার কাছে। তার মাথায় ঘোমটাটানা।
তাকে দেখা মাত্র কবি বুঝতে পারলেন, কী ভুল করেছেন।
এ অন্য রাণু, অন্যের রাণু। এখানে তার সঙ্গে কথা বলতে গেলেও আর সবাই দাঁড়িয়ে থাকবে।
রাণু রাছে এগিয়ে তাঁর পায়ের কাছে বসে প্রণাম করল। এই তার প্রথম প্রণাম। কবি তার মাথায় হাত রেখে অস্ফুট স্বরে আশীর্বাণী উচ্চারণ করে বেরিয়ে গেলেন দ্রুত।
রাণুকে আর চিঠি লেখা কিংবা যোগাযোগ রক্ষা করা উচিত নয়, কবি তা জানেন। তবু এক এক সময় মন মানে না। এক এক সময় এই বিচ্ছেদের শূন্যতা অসহ্য মনে হয়। এক এক সময় যুক্তিহীন হয়ে যান। রাণুকে ডেকে পাঠান।
রাণুর যে এখন বাইরে যাওয়ার অনেক বিধিনিষেধ, তা সে কবিকে কী করে বোঝাবে! বেরোতে হলেই সঙ্গে কেউ থাকে। বিশেষ করে তার ঠাকুরবাড়ি যাওয়া আসা শ্বশুরবাড়ির কেউ পছন্দ করে না। স্পষ্ট আপত্তি জানায় না, কিন্তু অসন্তোষের ভাব স্পষ্ট ফুটে ওঠে। তাই যেতেও চায় না রাণু।
কবি একদিন তোক মারফত চিঠি দিয়ে পাঠালেন। আজ সন্ধেবেলা তিনি একটা থিয়েটার দেখতে যাবেন, সঙ্গে নিয়ে যেতে চান রাণুকে। চিঠির ভাষা যেন আদেশের মতন। তিনি বীরেনকে আসতে বলেননি, শুধু রাণুকে।
শ্বশুর-শাশুড়ির বদলে রাণু অনুমতি চাইল তার স্বামীর কাছে। বীরেন বাংলা গান, কবিতা বা বাংলা সাহিত্যেরই ধার ধারে না। সে ভালবাসে পোলো খেলা। মোটর রেসিং। মাঝে মাঝে স্ত্রীকে নিয়ে লং ড্রাইভে যাওয়া তার অবসর বিনোদন।
বিয়ের আগেকার উড়ো চিঠির প্রসঙ্গ নিয়ে সে কখনও উচ্চবাচ্য করেনি। তবে জোড়াসাঁকোর কবি কিংবা শান্তিনিকেতনের গুরুদেবের প্রতি যে তার তেমন টান নেই, তা সে হাবেভাবে বুঝিয়ে দেয়।
রাণুর অনুরোধ শুনে সে বলল, আজ কী করে যাওয়া হবে? আজ বাড়িতে একটা পার্টি আছে, তুমি না থাকলে অতিথিরা কী মনে করবে?
রাণু তবু মিনতি করে বলল, যদি ঠিক সময়ে চলে আসি? অনেক। দিন থিয়েটার দেখিনি, আমার খুব ইচ্ছে করছে।
বীরেন নিরেশ গুলায় বলল, যদি আটটার মধ্যে ফিরে আসতে পারো তো যাও!
শুধু তো থিয়েটার দেখা নয়, কবির সঙ্গে বসে থিয়েটার দেখা! বাড়ির গাড়ি ও একজন সরকার মশাইকে নিয়ে গেল রাণু। জোড়াসাঁকোয় গিয়ে সে আর ওপরে উঠল না, খবর পাঠাতে কবি নিজেই নেমে এলেন।
রাণুকে দেখে তিনি ছেলেমানুষের মতন খুশি।
রাণুর জমকালো সাজগোেজ দেখে তিনি বললেন, সেই রাণু! মুখখানি কিন্তু ঠিক একই রকম আছে। মনে হয় যেন কত যুগ দেখিনি তোমাকে।
গাড়িতে সরকার মশাই ও ড্রাইভার আছে বলে কথা বলতে অস্বস্তি হচ্ছে রাণুর।
থিয়েটার আরম্ভ হবার কথা সাড়ে পাঁচটায়। সময় রক্ষা করা বাঙালিদের ধাতে নেই। তা ছাড়া নাটকের আগে ছোটখাটো বক্তৃতা, কবিকে দেওয়া হল পুষ্প স্তবক। শুরুতেই এক ঘণ্টা দেরি।
সাধারণ দর্শকদের থেকে আলাদা করে একেবারে সামনে কবি ও রাণুকে বসানো হয়েছে দুটি সিংহাসনের মতন বড় ভেলভেট মোড়া চেয়ারে। কবি পুষ্প স্তবকটি তুলে দিয়েছেন রাণুর হাতে।
কবির নাটক ‘চিরকুমার সভা প্রথম অভিনীত হচ্ছে পেশাদারি মঞ্চে। চমৎকার সেট। নাট্যকার স্বয়ং উপস্থিত বলে অভিনেতা অভিনেত্রীরা অভিনয় করছে প্রাণ ঢেলে, গানগুলিও জমেছে বেশ।
মাঝখানের বিরতির সময়ই বেজে গেল পৌনে আটটা।
মাঝে মাঝে হাতঘড়ি দেখছে, আর ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে রাণু। নাটকটির প্রতি আকর্ষণও অদম্য, তবু পিছু টান।
একটু আসছি বলে সে উঠে গেল।
হলের ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে সে টেলিফোন করল শ্বশুরবাড়িতে। অন্য একজন ধরতে সে চাইল বীরেনের সঙ্গেই কথা বলতে।
অন্য লোকটি কয়েক মুহূর্ত পরে বলল, সাহেব বলছেন, তিনি ব্যস্ত আছেন, আমাকেই বলুন।
রাণু বলল, আমি যে নাটকটি দেখছি, সেটা শেষ হতে খানিকটা দেরি হবে।
রাণু বুঝতে পারল, বীরেন কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, তবু সে ফোন ধরবে না, লোকটি রাণুর কথা বীরেনকে রিলে করে শোনাচ্ছে।
একটু পরে লোকটি জানাল, সাহেব বললেন, অতিথিরা সবাই এসে বসে আছেন। মিসেস মুখার্জিকে বলো, উনি না এলে খাবার পরিবেশন করা যাবে না।
আর কোনও কথা নয়।
রাণু পড়ল বিষম দোটানায়। কথা শুনেই বোঝা গেল, এখুনি না ফিরলে বীরেন বিষম রাগ করবে। আর নাটক না দেখে মধ্য পথে চলে গেলে দুঃখিত হবেন কবি। এ নাটক শেষ হতে আরও অন্তত সওয়া ঘণ্টা।
কয়েক মিনিট দ্বিধায় দুলতে লাগল রাণু। কবির অনুমতি নিতেও তার পা সরল না। মনস্থির করে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে উঠে পড়ল গাড়িতে।
মধ্য পথে কী ভেবে সে জানলা দিয়ে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিল। ফুলের স্তবকটি।
তিনতলার ঘরগুলি বীরেন ও রাণুর। বারান্দা থেকে দেখা যায় সুন্দর কেয়ারি করা বাগান। ভোরবেলা অনেক পাখি এসে বসে।
এ বাড়ির নিয়ম পুরুষরা বেশি দেরি করে ঘুমোলেও বউদের উঠতে হবে সকাল সকাল। তাই বীরেন জাগবার আগেই রাণু নেমে যায় পালঙ্ক থেকে। বারান্দায় গিয়ে একটুখানি দাঁড়ায়, টাটকা বাতাস মুখে চোখে মাখে।
দিনের বেলা সাদা বা ড়ুরে ধনেখালি কিংবা টাঙ্গাইল শাড়ি পরতে হবে। মাথায় কাপড় দিয়ে, আঁচলে বাঁধতে হবে চাবির গোছা। এর পর সারাদিন আর স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে না। সবচেয়ে আপন মানুষটির সঙ্গে যাবতীয় কথা বলা ও অন্য যা কিছু, তা শুধু রাতে।
শ্বশুর রাজেন্দ্রনাথ অবশ্য শয্যাত্যাগ করেন অতি প্রত্যুষে। দোতলার বারান্দায় একটি আরামকেদারায় বসে তিনি আকাশের আলো ফোটা দেখেন। তাঁর জন্য বিভিন্ন ঋতুর ফল ছাড়িয়ে রুপোর রেকাবিতে সাজিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব রাণুর।
মানুষটি কর্মবীর হিসেবে পরিচিত। ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতাতেই তিনি শুধু সফল নন, অন্যভাবেও পাল্লা দেন। সাহেবদের নিজস্ব বেঙ্গল ক্লাবে তাঁকে একবার প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি বলে তিনি তেজের সঙ্গে অন্য কয়েকজনের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ক্যালকাটা ক্লাব, সে ক্লাবের সুনাম দিন দিন বাড়ছে।
সারাদিন রাজেন্দ্রনাথ বহু কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকেন, শুধু সকালবেলা এক দেড় ঘণ্টা সময় তিনি রাখেন পরিবারের মানুষদের জন্য। স্ত্রী বসে থাকেন পাশে, বিবাহিতা মেয়েদের বাড়িতেই রেখেছেন বা কাছাকাছি বাড়ি কিনে দিয়েছেন, তারাও আসে, পুত্রবধূ রাণুর কাছ থেকেও তিনি নানান ছোটখাটো বিষয়ে জানতে চান।
ফলাহারের পর কফি বানিয়ে দেবেন তাঁর পত্নী। মেয়েরা অবশ্য কফি নয়, চা পান করবে।
এর পর সংবাদপত্র খুলতে না খুলতেই এসে যান কেউ না কেউ। কোনও সাহেব-মেম, বা স্যার পি সি মিটার, স্যার নীলরতন সরকার বা বর্ধমানের বিশাল বপু মহারাজ। রাজেন্দ্রনাথ ভৃত্যদের মুখে খবর পেয়ে চলে যান ড্রয়িং রুমে। সেখানে মেয়েদের যেতে নেই।
একটু বেলা হলে মেয়েদের নেমে আসতে হয় একতলায়।
রান্নাঘরে ঢুকে শাশুড়ি দিনের দিন রান্নার নির্দেশ দেবেন, রাণুকে শুধু শুনতে হবে পাশে দাঁড়িয়ে। সে রান্নার র-ও জানে না, মশলাপাতিরও নাম জানে না, তবু শিখতে তো হবে। বিয়ের আগে তার রান্নার পরীক্ষা নেওয়া হয়নি। রন্ধন কার্যে অযোগ্যতার কথা সে অকপটে জানিয়েছিল, তা শুনে খুব এক চোট হেসেছিল বীরেন। বাড়ির বউরা রান্না করলে পাচকদের চাকরি যাবে যে!
ডাইনিং রুমে ব্রেক ফাস্ট খেতে বসবেন রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বড় ছেলে ও বীরেন, এবং এক জামাই। তারপর সবাই বিভিন্ন গাড়িতে অফিসে যাত্রা করবে। বীরেন বড় ছেলে না হলেও তার পিতার প্রিয়, তার ওপরেই অধিকাংশ ব্যবসায়ের ভার, সে যায় রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে এক গাড়িতে।
গাড়িগুলি ছাড়বার সময় বাড়ির মেয়েরা মাথায় কাপড় দিয়ে গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিদায় জানাবে। অনেক দিন ধরে এই প্রথা চলে আসছে। এই সময়টায় রাণু এক ঝলক পথের দৃশ্য দেখতে পায়।
গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে চিনে, জাপানি ও অন্যান্য অনেক ফেরিওয়ালা। বাবুরা বেরিয়ে গেলেই তারা ডাইনিং রুমে এসে বিভিন্ন ধরনের কাপড়, এমব্রয়ডারি সিল্ক লেস বিছিয়ে বসে, প্রায় প্রতিদিনই কিছু কেনাকাটি হয়, বেশ সময় কেটে যায়।
দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর বসতে হবে শাশুড়ির ঘরে। রাণুর পাঁচ ননদ, সকালে যারা আসতে পারে না, তারা দুপুরে আসবেই। পান খেতে খেতে গল্প আর সেলাই বোনা। সেলাইটা যে খুব প্রয়োজনীয় তা নয়, এমনই চলে আসছে। রাণু একেবারেই সেলাই পারে না, আঙুলে সূচ ফুটে রক্ত বেরিয়ে যায়, অন্য কেউ দেখে ফেলার আগেই সে সেই রক্ত চেটে খেয়ে নেয়। তবু কিছুদিনের মধ্যেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেখা হয়ে যায়, একটা ক্রসস্টিচের আসন বুনে সে বাহবাও পেয়ে গেল।
এ বাড়িতে কেউ গান শোনে না। রবীন্দ্রনাথের গান শোনার তো প্রশ্নই নেই। কেউ বাংলা নাটক দেখতে যায় না। কেউ বই পড়ে না। কেউ বৃষ্টিতে ভেজে না, কেউ বাগানে দৌড়োয় না। মেয়েরা সাইকেল চালায়, এ কথা শুনলে তারা আঁতকে ওঠে।
মাঝে মাঝে যে একেবারে বাইরে যাওয়া হয় না তা নয়। শাশুড়ির জন্য সব সময় একটি রোলস রয়েস গাড়ি সাহেব ড্রাইভার সমেত মজুত থাকে। এক একদিন তিনি পুত্রবধূ ও মেয়েদের নিয়ে বেরোন। কোথায়? অবশ্যই বিভিন্ন দোকানে শখের কেনাকাটির জন্য। হল অ্যান্ড অ্যান্ডারসন, আর্মি অ্যান্ড নেভি স্টোরস, হোয়াইট অ্যাওয়ে লেড ল আর হ্যারিসন হ্যাথওয়ে—এই চারটি দোকানের মধ্যেই তাঁদের গতিবিধি সীমাবদ্ধ। কোনও ভারতীয় দোকানে তাঁদের যাওয়া মানায় না, এমনকী নিউ মার্কেটেও, সেখানে যে হেঁজিপেঁজিরাও যায়। নির্দিষ্ট দোকানগুলিতেও দরাদরির প্রশ্নই নেই। পছন্দমতন দ্রব্যটি তুলে নেবে, দামও দেবে না, সে দায়িত্ব পশ্চাৎ অনুবর্তী সরকার বাবুদের।
সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে হয়েও রাণু দ্রুত শিখে নিতে লাগল এই নব্যধনী ও ইংরেজ-অনুসারী পরিবারের আদব কায়দা। যেমন, কারুর সঙ্গেই বেশি বেশি আন্তরিকতা দেখাতে নেই। হাসি হাসি মুখ থাকলেও সব সময় কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখতে হবে অন্যদের সঙ্গে। বাইরের লোকের কথা বেশিক্ষণ মন দিয়ে শুনবে না। একটু পরেই চলে যাবে অন্যদের দিকে। হঠাৎ হঠাৎ উদাসীন হয়ে যাবে। কেউ খুব আর্ত বা বিপন্ন হয়ে কাছে এলে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেবে অবশ্যই, সেই সঙ্গে বুঝিয়ে দেবে, তার জন্য তুমি বেশি সময় দিতে রাজি নও। টাকা পাবে, মনোযোগ পাবে না। আত্মীয়-স্বজনরা এলে বুঝে নিতে হবে, কে কোন পর্যায়ের। যারা সমপর্যায়ের নয়, হাসি মুখে ছোটখাটো অপমান করে তাদের জানিয়ে দিতে হবে, যখন তখন এসো না।
ভানুদাদার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। শান্তিনিকেতনের স্মৃতি হঠাৎ হঠাৎ ঝলসে উঠে অন্য সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। তাঁকে চিঠি লিখি লিখি করেও লেখা হয় না। তাঁর পুরনো চিঠিগুলোই সে বারবার পড়ে।
শ্বশুর-শাশুড়ি যখন বিলেতে কিংবা অন্য কোথাও বেড়াতে যান তখন রাণু কিছুটা স্বাধীনতা পায়। তাও একা বেরুতে পারে না, হুট করে যেতে পারে না বাপের বাড়িতে। স্বামীর সঙ্গেই শুধু থিয়েটার-বাইস্কোপে যেতে পারে। বীরেনের ও সবে রুচি নেই একেবারেই, সময়ও নেই, তবে তরুণী স্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারে না একেবারে।।
কবির সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয় রাণুর, কখনও কোনও উৎসবে, পরিচিতদের বিবাহ বাসরে। সৌজন্যমূলক কথা হয় শুধু, যেন খুব দূরের মানুষ, চোখাচোখি হয়, তার মর্ম অন্য কেউ বোঝে না। রাণু বুঝতে পারে। সেবারে সেই থিয়েটার হল থেকে কবিকে কিছু না জানিয়ে মধ্য পথে চলে আসার জন্য কবি খুব আঘাত পেয়েছেন, এখনও অভিমান করে আছেন। কিন্তু কবিকে সব অবস্থাটা বুঝিয়ে বলার সুযোগই সে পেল না এ পর্যন্ত। সে রকম নিভৃত সান্নিধ্য আর পাবার উপায় নেই।
ক্রমে রাণু মা হল।
প্রথমে একটি কন্যা, তারপর একটি পুত্র।
একটি মেয়ের কুমারী অবস্থা থেকে বিবাহিত অবস্থার মধ্যে অনেক তফাত হয়ে যায় ঠিকই। তার চেয়েও বেশি বদল হয়ে যায় জননী হলে।
প্রকৃতিই তার মনোযোগের অনেকখানি টেনে নেয় সন্তানের দিকে। এ বাড়িতে শিশুদের জন্য মাদ্রাজি আয়া রাখা হয়, আছে গণ্ডা গণ্ডা কাজের লোক, তবু কোনও সন্তানের সামান্য কান্নার আওয়াজ শুনলেই রাণু তিনতলা থেকে ছুটে যায় একতলায়। ওদের সামান্য জ্বর বা সর্দিকাশি হলে দুশ্চিন্তায় রাণুর মুখে অন্ন রোচে না। যতই কলকাতার সবচেয়ে নামকরা ডাক্তারবদ্যি ডাকা হোক, সে সময় বীরেন কলকাতায় না থাকলে রাণু যেন অগাধ জলে পড়ে।
নিজের সাজগোজের দিকে আর মন নেই রাণুর, সে ছেলেমেয়ে দুটিকে অনবরত পুতুলের মতন সাজায়, তবু আশ মেটে না। এ বাড়িতে আসার পর থেকে তার এস্রাজ বাজানোর পাট চুকে গেছে, বই পড়ারও সময় পায় না, ছেলেমেয়েদের ছড়া শেখায়, রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শোনায়।
কিছু কিছু কর্তব্য পালন করে যেতে হয় অবশ্যই, স্বামীর সঙ্গে যেতে হয় পার্টিতে। সে সবচেয়ে ধনী বাঙালি পরিবারের বধূ, তার চালচলনে সামান্য বিচ্যুতি দেখাবার উপায় নেই।
রাণু বেশ ভাল ইংরিজি বলতে পারে, ইংরিজি সাহিত্যও যথেষ্ট পড়েছে জেনে তার শ্বশুরমশাই বাড়িতে ইংরেজ অতিথি এলে পুত্রবধূকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দেন। রাণুর সঙ্গে বাক্যালাপ চালিয়ে যেমন বিস্মিত হন সাহেবমেমরা, তা দেখে তেমনই গর্ববোধ করেন তার শ্বশুর।
দিনের পর দিন চলে যায়, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।
মানুষের স্মৃতি যেন অনেকটা নদীর মতো। কখনও নিস্তরঙ্গ হয়ে থাকে অনেক নীচে, আবার কখনও জোয়ারের মতো ফুলে ফেঁপে উত্তাল হয়ে ওঠে।
হঠাৎ একসময় শান্তিনিকেতনের জন্য তার মন আকুলি বিকুলি করে ওঠে। নিজের ঘরে বসে সে যেন ছাতিম ফুলের গন্ধ পায়, যেন আম্রকুঞ্জের বাতাস এসে তার গায়ে লাগে, শুনতে পায় ছাত্র-ছাত্রীদের বৃন্দগান। চোখে ভাসে, জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাওয়া একটা দোতলার বারান্দা, সেখানে কি কবি একা বসে আছেন?
রাণুর দুই বোন এখন থাকে শান্তিনিকেতনে। বড় বোন আশা বেশি বয়েসে বিয়ে করেছে শান্তিনিকেতনেরই অধ্যাপক আর্যনায়কমকে। ওরা সবসময় কবিকে দেখতে পায়, অথচ রাণুরই সে অধিকার নেই।
বোনেদেরও কতদিন দেখেনি রাণু।
আর একটা কথা ভেবেও তার কষ্ট হয়, তার ছেলেমেয়ে এখনও কবিকে চিনল না, তারা কবির আশীর্বাদ পাবে না?
একদিন সে বীরেনকে বলল, আমরা একবার শান্তিনিকেতনে বেড়াতে যেতে পারি না? তুমি তো শান্তিনিকেতন দেখইনি।
বীরেন বলল, আমি পৃথিবীর বহু বিখ্যাত স্থান এখনও দেখিনি। শান্তিনিকেতনের এমন কী বৈশিষ্ট্য আছে?
রাণু বলল, আহা, শান্তিনিকেতনের সঙ্গে অন্য কোনও জায়গার তুলনাই হয় না।
বীরেন বলল, সেটা কে তুলনা করছে, তার ওপর নির্ভর করে।
রাণু বলল, ওখানে আমার দুই দিদি রয়েছে। সুন্দরী শ্যালিকাদের সঙ্গেও কয়েকটা দিন কাটাতে ইচ্ছে করে না তোমার?
এক একজন পুরুষ কোনও বিষয় অপছন্দ করলেও তা নিয়ে তর্কে যেতে চায় না। তাতে সময় নষ্ট। সোজাসুজি আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করলেও স্ত্রীর মন-খারাপ আটকাতে পারবে না। এ নিয়ে কয়েকদিন অশান্তি চলবে। তার চেয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নেওয়া ভাল।
শ্বশুর ও শাশুড়ি দু’জনেই গত হয়েছেন এর মধ্যে, এখন আর অন্য কারুর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। রাণু নিজেই বন্দোবস্ত করতে লাগল সব কিছুর।
স্বামী, পুত্র-কন্যা, তাদের আয়া, ঠাকুর-চাকর ও বিরাট লটবহর নিয়ে চাপ হল ট্রেনের রিজার্ভ করা একটা কম্পার্টমেন্টে। বোম্বাই দিল্লির ট্রেনের তুলনায় শান্তিনিকেতনের ট্রেন অনেক শ্লথ গতি, কামরাগুলো অপরিচ্ছন্ন, হকারদের চিৎকারে কান পাতা দায়। প্রথম থেকেই সব কিছু বীরেনের অপছন্দ, সে নাক কুঁচকে রইল।
বোলপুর স্টেশনে জল কাদা থিক থিক করছে। বীরেনের মুখ দেখলে মনে হয়, তাকে যেন জোর করে তেতো ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে।
অভ্যর্থনা জানাতে রথী উপস্থিত। অনেকদিন পর রাণু এসেছে, এবারে তার খাতিরই আলাদা। সে এখন ভারতের এক প্রধান শিল্পপতির স্ত্রী। কিছুদিন আগে আর এক ব্যবসায়ী শ্ৰীযুক্ত টাটা এখানে একটি অতিথিনিবাস নির্মাণের জন্য অনেক টাকা দিয়েছেন। রাণু তার স্বামীকেও সঙ্গে এনে বড় ভাল কাজ করেছে, তিনি সব ঘুরে টুরে দেখুন। তাঁর জন্যই সাজিয়ে রাখা হয়েছে একটি আলাদা বাড়ি।
সে বাড়িতে যেমন সর্বক্ষণ লোকজনের আনাগোনা, তেমনই কবির কাছেও যাওয়া হয় সদলবলে। একসঙ্গে চা পান ও কিছু কিছু গল্প হয়। কবি যেন অনেকটা নীরব হয়ে গেছেন, কথা বলতেই চান না। হঠাৎ হঠাৎ উঠে যান অন্য ঘরে।
রাণু লক্ষ করে, কবি চুল আঁচড়াননি। তাঁর দাড়িতেও যেন বেশি পাক ধরেছে। কিন্তু ইচ্ছে করলেও তো সে আর এখন কবির মাথায় চিরুনি চালাতে পারবে না।
বীরেন এখানে সময় কাটাবার একটা উপায় পেয়েছে। সে ব্রিজখেলা পছন্দ করে, রথীরও তাসের নেশা আছে, প্রতি বিকেলবেলা অন্য পার্টনার জুটিয়ে বসে যায় তাসের আসর।
রাণু তখন সেখান থেকে উঠে যায় কবির ঘরে।
সেখানে বসে আছেন নেপাল মজুমদার ও বিধুশেখর শাস্ত্রী। তাঁরা উঠে যেতেই এলেন এক পারস্যদেশীয় অধ্যাপক। আবার অন্য কেউ। মীরা ও প্রতিমাও আসে যখন তখন।
এর মধ্যে আশার বাড়িতেও যেতে হয় রাণুকে।
শান্তিনিকেতনের পুরনো বাসিন্দা, যারা রাণুকে অনেকদিন ধরে দেখছেন, তাঁদের মতে রাণু যেন এখন আরও সুন্দর হয়েছে। এখন সে পূর্ণ যুবতী, কৈশোর বা প্রথম যৌবনের চাঞ্চল্য আর নেই, মুখের লাবণ্য যেন আরও বিকশিত হয়েছে, তার হাসি যেন পূর্ণ চাঁদের কিরণ। সবাই রাণুর সঙ্গে কথা বলতে চায়, সবাইকে তার কিছু কিছু সময় দিতে হয়।
শুধু যাঁর সঙ্গে অনেকদিনের জমে থাকা গল্প বিনিময় করার জন্য ছুটে আসা, তাঁকেই নিরিবিলিতে পাওয়া যায় না।
একদিন বিকেলে রাণু জিজ্ঞেস করল, ভানুদাদা, তোমার নতুন গান শোনাবে না আমাকে?
কবি বললেন, এমন হট্টমেলায় কি গান হয়?
ইঙ্গিতটি স্পষ্ট।
কবির রাত্রির আহারের পর তাঁর কাছে আর কেউ আসে না। সেইরকম সময়েই তো বারান্দায় বসে কবি রাণুকে শুনিয়েছেন গান, শুনেছেন রাণুর এলোমেলো কথা, দেখেছেন তার কান্না। এবারে তো রাণু সে সময় একবারও আসেনি।
দু’জনের দৃষ্টিতে যেন একটা সেতু গড়া হল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর রাণু আলতো ভাবে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল।
কবির জন্য নৈশ আহার এলে রাণুরও ডাক পড়ে বাড়ি ফেরার জন্য।
ছেলেমেয়েদের আগেই খাওয়া হয়ে গেছে। তাদের ঘুম পাড়ানোও হয়ে গেছে, দেখে এসেছে রাণু। এবার ডাইনিং টেবিলে অনেকে মিলে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া। তারপর ড্রয়িং রুমে বসে কিছুক্ষণ গল্প।
একটা নির্দিষ্ট সময় বিজলি বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয় বলে শান্তিনিকেতনে সবাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। একসময় ঘর ফাঁকা হয়ে গেল।
রাণুর সারা শরীরে একটা অস্থিরতার তরঙ্গ বইছে।
এই সময় তার ভানুদার কাছে যাওয়ার কথা।
বীরেন একটা বিলিতি রেডিও এনেছে, সেটার নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে বিশ্বসংবাদ শোনার চেষ্টা করছে। সে একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়বে, রাণু জানে। রাণু টপ করে চলে যেতে পারে ভানুদাদার কাছে।
কিন্তু সে একা যাবে? এখন কি আর তা সম্ভব? তার সাহস হল না।
ভানুদাদা যা চাইছেন, তা দেবার ক্ষমতা আমার নেই, নেই, নেই!
অথচ ভানুদাদা অপেক্ষা করে বসে আছেন। দোতলার বারান্দার অন্ধকারে, একা। তিনি নিশ্চিত ভেবেছেন, রাণু আজ আসবেই। কবিরা কি সারাজীবনই এরকম অবুঝ থাকে? ভালবাসা তাদের বাস্তব জ্ঞান ভুলিয়ে দেয়।
রাণুর মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হচ্ছে সেই শিলং পাহাড়ের বাড়িতে শোনা একটি গান:
তোমায় গান শোনাব, তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো
ওগো ঘুম ভাঙানিয়া
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাকো,
ওগো দুখ জাগানিয়া—
রাণু এখন দুখজাগানিয়ার সঠিক মানে বুঝতে পারে। কত সুখের স্মৃতির মধ্যেও জেগে ওঠে দুঃখ?
শুধু দুখজাগানিয়া তো নয়, কয়েকটি স্মৃতি যেন বুকের মধ্যে ঝড় তুলে দেয়।
ভানুদাদা আর সে, সে আর ভানুদাদা, এই দু’জনের নিভৃতি আর কখনও পাওয়া যাবে না।
রাণু যেতে পারছে না, অথচ কতটুকুই বা দূরত্ব!
সে দৌড়ে গিয়ে বীরেনের গায়ে ধাক্কা মেরে বলল, ওগো, চলো না একবার কবির সঙ্গে দেখা করে আসি।
বীরেন দুটি ভুরু অনেকখানি তুলে বলল, এখন? কেন? এই তো কিছুক্ষণ আগে কথা বলে এলাম।
রাণু বলল, তবু চলো না, আবার এখন একবার যাই।
বীরেন বলল, ফর গডস সেক, টেল মি হোয়াই!
রাণু ব্যাকুল ভাবে বলল, আমরা কাল চলে যাব, একবার শেষ দেখা করে আসব না? বিদায় নেব না?
বীরেন বলল, কাল তো যাব দুপুরবেলা? সারা সকাল পড়ে আছে। তখন দেখা করা যাবে না?
বাণু তবু দীনহীনা হয়ে বীরেনের হাত ধরে ভিক্ষে চাওয়ার মতো বলল, প্লিজ চলো, আমার ইচ্ছে করছে, তুমি আমার সঙ্গে চলো।
স্ত্রীর এই পাগলামির অর্থ বুঝতে পারল না বীরেন। মেয়েদের সব ব্যবহারের মর্ম ক’জন পুরুষই বা বোঝে!
অগত্যা বীরেনকে উঠে, পোশাক বদলে বেরোতেই হল।
এর মধ্যেই নিঝুম হয়ে গেছে শান্তিনিকেতনের পল্লীগুলি। গাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে আলো ছায়ার জাফরি কাটা। বাতাসে রেশমি স্পর্শ। রাণু কিছুই দেখছে না, তার বুক ধক ধক করছে। অতিকষ্টে সে সামলে আছে কান্না।
এর মধ্যে টিপি টিপি বৃষ্টি নামল।
বারান্দায় নয়, কবি বসে আছেন একটি নতুন তৈরি ঘরে। ঘরটি ধোঁয়ায় ভর্তি। একটা বড় ধুনুচিতে শিউলি পাতা পোড়ানো হচ্ছে, মশা তাড়াবার এটা নবতম উপায়।
পায়ের শব্দে কবি ফিরে তাকালেন।
কিছু বলতে গিয়ে থেমে গিয়ে, রাণুর পাশে বীরেনকে দেখতে পেয়ে ফ্যাকাশে গলায় বললেন, তোমরা এসেছ, বসো!
দু’জনে একটু দূরের সোফায় বসল। কেউ কোনও কথা বলছে না।
ধোঁয়ার জন্য মাঝে মাঝে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছেন কবি।
রাণুর মনে হল, সে যেন বিশ্বাসঘাতিনী, ভানুদাদার কাছে কথা রাখেনি। কিন্তু এসময় একা আসা যে এখন আর তার পক্ষে সম্ভব নয়, তা কি ভানুদাদা বুঝবেন না?
বীরেনের এই ধোঁয়া সহ্য হয় না। সে জিজ্ঞেস করল, আমি এই ধুনুচিটা একটু সরিয়ে রাখতে পারি?
কবি বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঘরের ওই কোণটায়…
তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এই সময় এলে, বিশেষ কিছু বলার আছে।
বীরেনের কিছুই বলার নেই, সে তাকাল তার স্ত্রীর দিকে।
রাণু নতমুখী হয়ে বসে আছে। যেন তাকাতেও ভয় পাচ্ছে কবির দিকে।
একটু পরে সে বলল, একটা গান শোনাবেন না?
কবি বললেন, গান…আজ আর হবে না, শরীরটা তেমন ভাল নেই।
কবির যখন শরীর ভাল নেই, তখন তো আর তাঁকে জাগিয়ে রাখা উচিত নয়। বীরেন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, রাণু, তা হলে এখন আমরা যাই?
রাণুও উঠে দাঁড়িয়ে, এই প্রথম কবির দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে কাতর গলায় বলল, যাই?
রাণু আশা করেছিলেন, কবি বলবেন, আর একটু বসো।
আগে যেমন বিদায় নিতে দিতেন না এক কথায়।
এখন তিনি মুখে কিছুই বললেন না। মাথা নোয়ালেন সামান্য।
বীরেন ব্যস্ত ভাবে পা বাড়িয়েছে দরজার দিকে। রাণু বারবার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। প্রতি রোমকূপে সে আকাঙক্ষা করছে, কবি তাকে একবার অন্তত ডাকবেন।
ধোঁয়ার জন্য স্পষ্ট মুখ দেখা যাচ্ছে না কবির।
রাণু নিজেই আবার বললেন, আমরা যাচ্ছি।
কবি কিছুই বললেন না, যেন ধোঁয়ার মধ্যে মিলিয়ে গেলেন একেবারে।
এরপর আর সারা রাত রাণুর ঘুম আসবে কী করে?
নিদ্রিত স্বামীর পাশে সে ছটফট করতে করতে উঠে পড়ল ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে।
কবি এই সময় বাড়ির সমানের প্রাঙ্গণে বসে প্রথম সূর্যের আলো গায়ে মাখেন। এখানেই তাঁকে চা দেওয়া হয়।
রাণু প্রায় ছুটে গিয়ে দেখল, এই সাতসকালেও কবির সামনে বসে আছেন সুধাকান্ত। দু’জনে চা খাচ্ছেন। পটে আর চা নেই, সুধাকান্ত উঠে গেলেন রাণুর জন্য চা আনতে।
সুধাকান্ত যাচ্ছেন, আর দেখা যাচ্ছে দূর থেকে হেঁটে আসছেন বিধুশেখর। মধ্যবর্তী এইটুকু সময়ের মধ্যে রাণুকে তার নিজের কথা বলতেই হবে কবির কাছে।
সে বলল, ভানুদাদা, কাল রাত্তিরে।
কবি হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে।
কবিও কি ঘুমোতে পারেননি কাল রাতে? তাঁর চোখের নীচে ক্লান্তির কালো রেখা। দৃষ্টিতে জ্যোতি নেই। বসে থাকার ভঙ্গিটিও কেমন যেন ভাঙাচুররা।
সময় নেই আর সময় নেই।
যে-কথা অন্যদের সামনে বলা যায় না, সে কথা বলতে দেয় না অন্যরা।
রাণু দু’ দিকে তাকাল। বিধুশেখর হাঁটতে হাঁটতে একবার নিচু হয়ে মাটি থেকে কী যেন তুললেন। সুধাকান্ত এক পরিচারকের হাত থেকে নিল দ্বিতীয় একটি চায়ের পট। দু’জনেই এখানে এসে পড়বে আর এক মিনিটের মধ্যে।
গাঢ় বিষাদ মাখা মুখ কবির। ঊষালয়ের অপরূপ আলোও তা মুছে নিতে পারেনি। তিনি এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন রাণুর মুখের দিকে।
রাণু আবার ব্যাকুলভাবে বললেন, ভানুদাদা, তোমাকে শুনতেই হবে–
কবি তাঁকে থামিয়ে দিলেন আবার।
তিনি ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, রাণু, তুমি আর আমাকে ভানুদাদা বলে ডেকো না। ভানু সিংহ হারিয়ে গেছে চিরকালের মতন। আর তাকে ফেরানো যাবে না। তুমি সুখী হও। তোমার স্বামীর পরিবারের গৌরব বৃদ্ধি করো। তোমার ছেলে ও মেয়েকে আমি আশীর্বাদ করি, তারাও যোগ্য হয়ে উঠে দেশের সেবা করুক।।
রাণু দু’হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। কাঁপছে তার সারা শরীর।
দূরে ঢং ঢং করে করে ঘণ্টা বেজে উঠল। রাণুর বালিকা বয়েসের দানে নির্মিত সেই ঘণ্টা।
কবি চেয়ার ছেড়ে উঠে হাঁটতে লাগলেন।
পিঠের দিকে দৃ’হাত, শরীরটা যেন ঈষৎ বেঁকে গেছে এর মধ্যে। শিথিল হয়ে গেছে চামড়া।
আম্রকুঞ্জের মধ্য দিয়ে কবি আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছেন একা। একটু একটু নড়ছে তাঁর ঠোঁট।
আমার ভুবন তো আজ হলো কাঙাল, কিছু তো নাই বাকি, ওগো নিঠুর দেখতে পেলে তা কি। তার সব ঝরেছে, সব মরেছে, জীর্ণ বসন ওই পড়েছে—প্রেমের দানে নগ্ন প্রাণের লজ্জা দেহো ঢাকি।
কুঞ্জে তাহার গান যা ছিল কোথায় গেল ভাসি। এবার তাহার শূন্য হিয়ায় বাজাও তোমার বাঁশি। তার দীপের আলো কে নিভালো, তারে তুমি আবার জ্বালো–আমার আপন আঁধার আমার আঁখিরে দেয় ফাঁকি।…
যখন ভাঙলো মিলন মেলা ভেবেছিলাম ভুলবো না আর চক্ষের জল ফেলা। দিনে দিনে পথের ধুলায় মালা হতে ফুল ঝরে যায়–জানি নে তো কখন এলো বিস্মরণের বেলা।
দিনে দিনে কঠিন হলো কখন বুকের তল—ভেবেছিলেম ঝরবে না আর আমার চোখের জল। হঠাৎ দেখা পথের মাঝে, কান্না তখন থামে না যে–ভোলার তলে তলে ছিল অশ্রু জলের খেলা।…
আমার এ পথ তোমার পথের থেকে অনেক দূরে গেছে বেঁকে। আমার ফুলে আর কি কবে তোমার মালা গাঁথা হবে, তোমার বাঁশি দূরের হাওয়ায় কেঁদে বাজে কারে ডেকে।
শ্রান্তি লাগে পায়ে পায়ে, বসি পথের তরুছায়ে। সাথী হারার গোপন ব্যথা বলবো যারে সে জন কোথা—পথিকরা যায় আপন মনে, আমারে যায় পিছে রেখে…
তুমি তো সেই যাবেই চলে, কিছু তো না রবে বাকি—আমার ব্যথা দিয়ে গেলে জেগে রবে সেই কথা কি। তুমি পথিক আপন মনে, এলে আমার কুসুম বনে, চরণপাতে যা দাও দলে সে সব আমি দেব ঢাকি।
বেলা যবে আঁধার হবে, একা বসে হৃদয় ভরে, আমার বেদনখানি আমি রেখে দেব মধুর করে। বিদায় বাঁশির করুণ রবে সাঁঝের গগন মগন হবে, চোখের জলে দুখের শোভা নবীন করে দেব রাখি…
॥ সমাপ্ত ॥