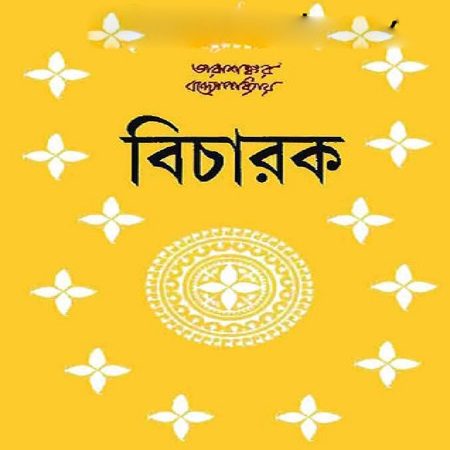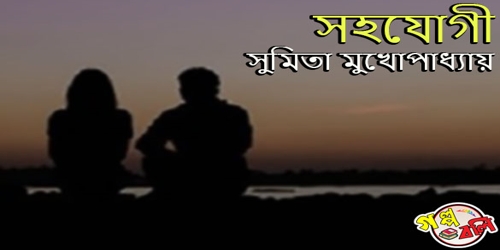আদালতে দায়রা মামলা চলছিল। মামলার সবে প্রারম্ভ।
মফস্বলের দায়রা আদালত। পশ্চিম বাঙলার পশ্চিমদিকের ছোট একটি জেলা। জেলাটি সাধারণত শান্ত! খুনখারাবি দাঙ্গা-হাঙ্গামা সচরাচর বড় একটা হয় না। মধ্যে মধ্যে যে দু-চারটে। দাঙ্গা বা মাথা-ফাটাফাটি হয় সে এই কৃষিপ্রধান অঞ্চলটিতে চাষবাস নিয়ে গণ্ডগোল থেকে পাকিয়ে ওঠে। কখনও কখনও দু-একটি দাঙ্গা বা মারামারি নারীঘটিত আইনের ব্যাপার নিয়েও ঘটে থাকে। অধিকাংশই নিম্ন আদালতের এলাকাতেই শেষ হয়ে যায়, কৃচিৎ দুটি-চারটি আইনের জটিলতার টানে নিম্ন আদালতের বেড়া ডিঙিয়ে দায়রা আদালতের এলাকায় এসে। পড়ে। যেমন সাধারণ চুরি কিন্তু চোর পাঁচ জন—সুতরাং ডাকাতির পর্যায়ে পড়ে জজআদালতের পরিবেশটিকে ঘোরালো করে তোলে। চাষের ব্যাপার সেচের জল নিয়ে মারামারি, আঘাত বড়জোর মাথা-ফাটাফাটি, কিন্তু দু পক্ষের লোকের সংখ্যাধিক্যের জন্য রায়টিং-এর চার্জে দায়রা আদালতে এসে পৌঁছয়। এই কারণে জেলাটি সরকারি দপ্তরে বিশ্রামের জেলা বলে গণ্য করা হয় এবং কর্মভারপীড়িত কর্মচারীদের অনেক সময় বিশ্রামের সুযোগ দেওয়ার জন্য এই জেলাতে পাঠানো হয়। কিন্তু বর্তমান মামলাটি একটি জটিল দায়রা মামলা।
খুনের মকদ্দমা। আদালতে লোকের ভিড় জমেছে। মামলাটি শুধু খুনের নয়, বিচিত্র খুনের মামলা।
অশোক-স্তম্ভখচিত প্রতীকের নিচেই বিচারকের আসনে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। অচঞ্চল, স্থির, নিরাসক্ত মুখ, অপলক চোখের দৃষ্টি। সে-দৃষ্টি সম্মুখের দিকে প্রসারিত কিন্তু কোনো কিছুর উপর নিবন্ধ নয়। সামনেই কোর্টরুমের ডান দিকের প্রশস্ত দরজাটির ওপাশে বারান্দায় মানুষের আনাগোনা। বারান্দার নিচে কোৰ্টকম্পাউন্ডের মধ্যে শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের রিমিঝিমি বর্ষণ বা দেবদারু গাছটির পত্রপল্লবে বর্ষণসিক্ত বাতাসের আলোড়ন, সবকিছু ঘষা কাচের ওপারের ছবির মত অস্পষ্ট হয়ে গেছে। একটা আকার আছে, জীবন স্পন্দনের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু তার আবেদন নেই; বন্ধ জানালার ঘষা কাচের ঠেকায় ওপারেই হারিয়ে গেছে। সরকারি উকিল প্রারম্ভিক বক্তৃতায় ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে মামলাটির আনুপূর্বিক বিবরণ বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর দৃষ্টি মনের পটভূমিতে সেই ঘটনাগুলিকে পরের পর তুলি দিয়ে এঁকে এঁকে চলেছিল। কৃচিৎ কখনও সামনের টেবিলের উপর প্রসারিত তার ডান হাতখানিতে ধরা পেন্সিলটি ঘুরে ঘুরে উঠছিল অথবা অত্যন্ত মৃদু আঘাতে আঘাত করছিল। তাও খুব জোর মিনিটখানেকের জন্য।
প্রবীণ গম্ভীর মানুষ। বয়স ষাটের নিচেই। গৌরবর্ণ সুপুরুষ, সরল কর্মঠ দেহ, কিন্তু মাথার চুলগুলি সব সাদা হয়ে গেছে। পরিচ্ছন্নভাবে কামানো গৌরবর্ণ মুখে নাকের দু-পাশে দুটি এবং চওড়া কপালে সারি সারি কয়েকটি রেখা তাঁর সারা অবয়বে যেন একটি ক্লান্ত বিষণ্ণতার ছায়া। ফেলেছে। লোক, বিশেষ করে উকিলেরা_যাঁরা তাঁর চাকরি জীবনের ইতিহাসের কথা জানেন বলেন, অতিমাত্রায় চিন্তার ফল এ-দুটি। মুনসেফ থেকে জ্ঞানেন্দ্রবাবু আজ জজ হয়েছেন, সে অনেকেই হয়, কিন্তু তাঁর জীবনে লেখা যত রায় আপিলের অগ্নি-পরীক্ষা উত্তীৰ্ণ হয়েছে এত আর কারুর হয়েছে বলে তারা জানেন না। রায় লিখতে এত চিন্তা করার কথা তারা। একালে বিশেষ শোনেন নি। শুধু তাই নয়, তার চিন্তাশক্তির গভীরতা নাকি বিস্ময়কর। প্রমাণ প্রয়োগ সাক্ষ্যসাবুদের গভীরে ড়ুব দিয়ে তার এমন তত্ত্বকে আবিষ্কার করেন যে, সমস্ত কিছুর সাধারণ অর্থ ও তথ্যের সত্য আমূল পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়-অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারে তিনি ক্ষমাহীন। একটি নিজস্ব তুলাদণ্ড হাতে নিয়ে তিনি ক্ষুরের ধারের উপর পদক্ষেপ করে শেষ প্রান্তে এসে তুলদণ্ডের আধারে যে আধেয়টি জমে ওঠে তাই অকম্পিত হাতে তুলে দেন, সে বিষই হোক আর অমৃতই হোক।
খ.
কর্মক্লান্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্রাম নেবার জন্যই এই ছোট এবং শান্ত জেলাটিতে মাসকয়েক আগে এসেছেন। ইতিমধ্যেই উকিল এবং আমলা মহলে নানা গুজবের রটনা হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রনাথের আরদালিটি হাল-আমলের বাঙালির ছেলে। এদিকে ম্যাট্রিক ফেল। কৌতুহলী উকিল এবং আমলারা তাকে নানান প্রশ্ন করে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সাধারণত আদালত এবং নিজের কুঠির মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন। ক্লাবের সভ্য পর্যন্ত হন নি। এ নিয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারীমহলেও গবেষণার অন্ত নেই।
এ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন–জ্ঞানেন্দ্রনাথ নাকি বলেন যে, তাঁর স্ত্রী আর বই এই দুটিই হল তার সর্বোত্তম বন্ধু। আর বন্ধু তিনি কামনা করেন না।
প্রবাদ অনেক রকম তার সম্বন্ধে। কেউ বলে তিনি শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্রাহ্ম। কেউ বলে তিনি পুরো নাস্তিক। কেউ বলে লোকটি জীবনে বোঝে শুধু চাকরি। কেউ বলে ঠিক চাকরি নয়, বোঝে শুধু আইন। পাপ-পুণ্য, সৎ-অসৎ ধৰ্ম-অধৰ্ম, এসব তার কাছে কিছু নেই, আছে শুধু আইনানুমোদিত আর বেআইনি। ইংরেজিতে যাকে বলে—লিগাল আর ইলিগাল।
তাঁর স্ত্রী সুরমা দেবীও জজের মেয়ে। জাস্টিস চ্যাটার্জি নামকরা বিচারক। এখনও লোকে তার নাম করে। ব্যারিস্টার থেকে জজ হয়েছিলেন। সুরমা দেবী শিক্ষিতা মহিলা। অপরূপ সুন্দরী ছিলেন সুরমা দেবী এক সময়। আজও সে-সৌন্দর্য ম্লান হয় নি। নিঃসন্তান সুরমা দেবীকে এখনও পরিণত বয়সের যুবতী বলে ভ্ৰম হয়। এই সুরমা দেবীও যেন তাঁর স্বামীর ঠিক নাগাল পান না।
জজসাহেবের আরদালিটি সাহেবের গল্পে পঞ্চমুখ। সেসব গল্পের অধিকাংশই তার শুনে সংগ্রহ করা। কিছু কিছু নিজের দেখা। সে বলে—মেমসাহেবও হাঁপিয়ে ওঠেন এক এক
সময়।
ঘাড় নেড়ে সে হেসে বলে রাত্রি বারটা তো সাহেবের রাত নটা। বারটা পর্যন্ত রোজ কাজ করেন। নটায় আরদালির ছুটি হয়। মেমসাহেব টেবিলের সামনে বসে থাকেন; সাহেব। নথি ওলটান, ভবেন, আর লেখেন। আশ্চর্য মানুষ, সিগারেট না, মদ না, কফি না; চা দু কাপ দু বেলা—বড়জোর আর এক-আধ বার। চুপচাপ লিখে যান। মধ্যে মধ্যে কাগজ ওলটানোর খসখস শব্দ ওঠে। কখনও হঠাৎ কথা—একটা কি দুটো কথা, বইখানা দাও তো! বলেন। মেমসাহেবকে। আউট হাউস থেকে আরদালি বয়েরা দেখতে পায় শুনতে পায়।
এখানকার দু-চার জন উকিল, উকিলবাবুদের মুহুরি এবং জজ-আদালতের আমলারা এসব। গল্প সংগ্রহ করে আরদালিটির কাছে।
আরদালি বলে–তবে মাসে পাঁচ-সাত দিন আবার রাত দুটো পর্যন্ত। ঘরে ঘুমিয়ে পড়ি। দেড়টা-দুটোর সময় আমার রোজই একবার ঘুম ভাঙে। তেষ্টা পায় আমার। ছেলেবেলা থেকে। ওটা আমার অভ্যেস। উঠে দেখতে পাই সাহেব তখনও জেগে। ঘরে আলো জ্বলছে। প্রথম প্রথম আশ্চর্য হতাম, এখন আর হই না। প্রথম প্রথম সাহেবের ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়েও থমকে দাঁড়াতাম, সাহেব না ডাকলে যাই কী করে? দুই-এক দিন চুপিচুপি ঘরের পিছনে জানালার পাশে দাঁড়াতাম। দেখতাম টেবিলের উপর ঝুঁকে সাহেব তখনও লিখছেন। এক-একদিন শুনতাম শুধু চটির সাড়া উঠছে। বুঝতে পারতাম সাহেব ঘরময় পায়চারি করছেন। এখনও শুনতে পাই। কোনো কোনো দিন বাথরুমের ভেতর আলো জ্বলে, জল পড়ার শব্দ ওঠে, বুঝতে পারি মাথা ধুচ্ছেন সাহেব। ওদিকে সোফার উপর মেমসাহেব ঘুমিয়ে থাকেন। খুটখাট শব্দ উঠলেই জেগে ওঠেন।
বলেন-হল? এক-একদিন মেমসাহেব ঝগড়া করেন। এই তো আমার চাকরির প্রথম বছরেই; বুঝেছেন, আমি ওই উঠে সবে বাইরে এসেছি; দেখি মেমসাহেব দরজা খুলে বাইরে এলেন। খানসামাকে ডাকলেন–শিউনন্দন! ওরে!
ভিতর থেকে সাহেব বললে-না না। ও কি করছ? ডাকছ কেন ওদের?
মেমসাহেব বললেন– ইজিচেয়ারখানা বের করে দিক।
আমি নিজেই নিচ্ছি—ওরা সারাদিন খেটে ঘুমাচ্ছে। ডেকো না। সারাদিন খেটে রাত্রে না-ঘুমালে ওরা পারবে কেন। মানুষ তো!
আরদালি বিস্ময় প্রকাশের অভিনয় করে বলে—দেখি সাহেব নিজেই ইজিচেয়ারখানা টেনে বাইরে নিয়ে আসছেন। আমি যাচ্ছিলাম ছুটে। কিন্তু মেমসাহেব ঝগড়া শুরু করে দিলেন। আর কী করে যাই? চুপ করে দাঁড়িয়ে শুধু শুনলাম। মেমসাহেব নাকি বলেন-আরদালি এবার বলে যায় তার শোনা গল্প, পুরনো আরদালির কাছে শুনেছে সে, সুরমা নাকি আগে প্রায়ই ক্ষুব্ধভাবে বলতেন—দুনিয়ার সবাই মানুষ। রাত্রে ঘুম না-হলে কারুরই চলে না। ফলে শুনেছি এক ভগবানের। তা জানতাম না যে, জজিয়তি আর ভগবানগিরিতে তফাত নেই। তারপর বলেন, তাই-বা কেন? আমার বাবাও জজ ছিলেন।
জ্ঞানেন্দ্রনাথ হাসতেন। হেসে আর-একখানা চেয়ার এনে পেতে দিয়ে বলতেন–বোসো
রায় লেখা তখন শেষ হয়ে যেত। সুরমাও বুঝতে পারতেন। স্বামীর মুখ দেখলেই তিনি তা বুঝতে পারেন। রায় লেখা শেষ না-হলে সুরমা কোনো কথা বলেন না। ওই দুটো-চারটে কথা-চা খাবে? টেবিলফ্যানটা আনতে বলব? এই। বেশি কথা বলবার তখন উপায় থাকে না। বললে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেন, প্লিজ, এখন না, পরে বোলো যা বলবে।
রায় লেখা হয়ে গেলে তখন তিনি কিন্তু আরেক মানুষ। সুরমা বলতেন—মুনসেফ থেকে তো জজ হয়েছ। ছেলে নেই, পুলে নেই। আর কেন? আর কী হবে? হাইকোর্টের জজ, না সুপ্রিমকোর্টের জজ? ওঃ! এখনও আকাঙা গেল না?
জ্ঞানেন্দ্রনাথের একটি অভ্যেস-করা হাসি আছে। সেই হাসি হেসে বলতেন বা বলেন না। আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। ঠিক সময়ে রিটায়ার করব এবং তারপর সেই ফাষ্ট্র বুকের নির্দেশ মেনে চলব। গেট আপ অ্যাট ফাইভ, গো টু বেড অ্যাট নাইন। তা-ই বা কেন—এইট। সকালে উঠে মর্নিং-ওয়াক করব; তারপর থলে নিয়ে বাজার যাব। বিকেলে মার্কেটে গিয়ে তোমার বরাতমত উলসুতো কিনে আনব। এবং বাড়িতে তুমি ক্রমাগত বকবে, আমি শুনব। কিন্তু যতদিন চাকরিতে আছি, ততদিন এ থেকে পরিত্রাণ আমার নেই।
আর একদিন, বুঝেছেন;–আরদালি বলে আর একদিনের গল্প।
সুরমা বলেছিলেন-আচ্ছা বলতে পার, সংসারে এমন মানুষ কেউ আছে যার ভুল হয় না?
জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেছিলেন–না নেই।
সুরমা বলেছিলেন—তবে?
–কী হবে?
–এই যে তুমি ভাব তোমার রায় এমন হবে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেউ পালটাতে পারবে না। হাইকোর্ট না, সুপ্রিমকোর্ট না—এ দম্ভ তোমার কেন?
দম্ভ? জ্ঞানেন্দ্রনাথ হা-হা করে হেসে উঠেছিলেন। আরদালি বলে—সে কী হাসি! বুঝেছেন না। যেন মেমসাহেব নেহাত ছেলেমানুষের মত কথা বলেছেন। মেমসাহেব রেগে গেলেন, বললেন– হাসছ কেন? এত হাসির কী আছে?
সাহেব বললেন–তুমি দম্ভ, হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট, কথাগুলো বললে না, তাই।
মেমসাহেব বললেন–ভুল হয়েছে। ভগবানও পালটাতে পারবেন না বলা উচিত ছিল। আমার।
জ্ঞানেন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন—উঁহুঁ, ওসব কিছুর জন্যেই নয় সুরমা। হাসলাম মেয়েরা চিরকালই মেয়ে থেকে যায় এই ভেবে।
–তার মানে?
—মানে? তুমি তো সে ভাল করে জান সুরমা। এবং সে কথাটা তো আমার নয়, আমার গুরুর, তোমার বাবার। দম্ভ নয়, হাইকোর্টে রায় টিকবে কি না-টিকবে সেও নয়, সে কখনও ভাবি নে। ভাবি আজ নিজে যে রায় দিলাম, সে রায় দু মাস কি ছ মাস কি ছবছর পরে ভুল হয়েছে বলে নিজেই নিজের উপর যেন না স্ট্রিচার দিই। শেষটায় খুব রাগ করে তুমি ভগবানের কথা তুললে–। মধ্যে মধ্যে জজগিরি আর ভগবানগিরির সঙ্গে তুলনাও কর—
সুরমা সেদিন স্বামীর কথার ওপরেই কথা কয়ে উঠেছিলেন, বেশ খোঁচা দিয়ে বলেছিলেন না, তা বলি না কখনও। বলি, আমার বাবাও জজ ছিলেন; তার তো এমন দেখি নি। আরও অনেক জজ আছেন, তাদেরও তো এমন শুনি নে। বলি, তোমার জজিয়তি আর ভগবানগিরিতে তফাত নেই। হ্যাঁ, তা বলিই তো। তোমাকে দেখে অন্তত আমার তাই মনে হয়।
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চোখ দুটি বন্ধ করে প্রশান্তভাবে মিষ্টি হেসে বলেছিলেন—তাই। আমার জজিয়তি আর ভগবানগিরির কথাই হল। আমি অবিশ্যি ভগবানে বিশ্বাস ঠিক করিনে, সে তুমি জান, তবু তুলনা যখন করলে তখন ভগবানগিরির যেসব বর্ণনা তোমরা কর—ভাল ভাল কেতবে আছে—সেইটেকেই সত্য বলে মেনে নিয়ে বলি, আমার জজিয়তি ভগবানগিরির চেয়েও কঠিন। কারণ ভগবান সর্বশক্তিমান, তার উপরে মালিক কেউ নেই, সূক্ষ্ম বিচারক নিশ্চয়ই, কিন্তু তবুও অটোক্র্যাট। অন্তত করুণা করতে তার বাধা নেই। ইচ্ছে করলেই আসামিকে দোষী জেনেও বেকসুর মাফ করে খালাস দিতে পারেন। পাপপুণ্যের ব্যালান্সশিট তৈরি করে পুণ্য বেশি হলে পাপগুলোর চার্জশিট ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে নিক্ষেপ করতে পারেন। মানুষ জজ তা পারে না। আমি তো পারিই না।
বার লাইব্রেরি থেকে আদালতের সামনের বটতলা পর্যন্ত এমনি ধরনের আলাপ-আলোচনার মধ্যে এই মানুষটির সমালোচনা দিনে এক-আধ বার না-হয়ে যায় না। এসব কথা অবশ্য পুরনো কথা। জেলা থেকে জেলায় তাঁর বদলির সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলিও প্রচারিত হয়েছে। এখন জানেন্দ্রনাথ আরও স্বতন্ত্র এবং বিচিত্র। অহরহ চিন্তাশীল প্রায় এক মৌনী মানুষ। মেমসাহেবও তাই। দুজনেই যেন পরস্পরের কাছে ক্ৰমে মৌন মূক হয়ে যাচ্ছেন। এই দুকূল পাথার নদীর বুকে দুখানি নৌকা দুদিকে ভেসে চলেছে।
গ.
সরকারি উকিল অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মামলার ঘটনাগুলির বর্ণনা করে চলেছিলেন। অবিনাশবাবু প্রবীণ এবং বিচক্ষণ উকিল। বক্তা হিসাবে সুনিপুণ এবং আইনজ্ঞ হিসাবে অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী। এই বিচারকটিকে তিনি খুব ভাল করে চেনেন। আরদালির কথা থেকে নয়, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। এবং এই জেলায় আসার পর থেকে নয়, তার অনেক দিন আগে থেকে। এ। জেলায় তখন সরকারি উকিল হন নি তিনি; তার পরের তখন প্রথম আমল। আশপাশের জেলা থেকে তাঁর তখন ডাক পড়তে শুরু হয়েছে। জীবনে প্রতিষ্ঠা যখন প্রথম আসে তখন সে একা আসে না, জলস্রোতের বেগের সঙ্গে কল্লোল-ধ্বনির মত অহঙ্কারও নিয়ে আসে। তখন সেঅহঙ্কারও তার ছিল। একটি দায়রা মামলার আসামির পক্ষ সমর্থন করতে গিয়েছিলেন। সে মামলায় উনি তাকে যে তিরস্কার করেছিলেন তা তিনি আজও ভুলতে পারেন নি। আজও মধ্যে মধ্যে হঠাৎ মনে পড়ে যায়।
সেও বিচিত্ৰ ঘটনা। বাপকে খুন করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিল ছেলে। ষাট বছর। বয়সের বৃদ্ধ বাপ, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের জোয়ান ছেলে, সেও দুই ছেলের বাপ। মামলায় প্রধান সাক্ষী ছিল মা। ছেলেটি কৃতকর্মা পুরুষ। যেমন বলশালী দেহ তেমনি অদম্য সাহস, তেমনি। নিপুণ বিষয়বুদ্ধি। প্রথম যৌবন থেকেই বাপের সঙ্গে পৃথক।
বাপ ছিল বৈষ্ণব, ধর্মভীরু মানুষ। বিঘা সাতেক জমি, ছোট একটি আখড়া ছিল সম্পত্তি। তার সঙ্গে ছিল গ্রামের কয়েকটি বৃত্তি। কার্তিক মাসে টহল, বারমাসে পার্বণে—ঝুলন, রাস, দোল, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসবে নাম-কীর্তন এবং শবযাত্রায় সংকীর্তন গাইত, তার জন্য গ্রাম্য বৃত্তি ছিল। এতেই তার চলে যেত। ছেলে অন্য প্রকৃতির, গোড়া থেকেই সে এ-পথ ছেড়ে বিষয়ের পথ ধরেছিল। চাষের মজুর খাটা থেকে শুরু, ক্ৰমে কৃষণি, তারপর গরু কিনে ভাগচাষ, তারপর জমি কিনে চাষী গৃহস্থ হয়েছিল। তাতে বাপ আপত্তি করে নি; প্রশংসাই করত। কিন্তু তারপর ছেলের বুদ্ধি যেন অসাধারণ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। নিজের জমির পাশের জমির সীমানা কেটে নিতে শুরু করল এবং এমন চাতুর্যের সঙ্গে কেটে নিতে লাগল যে অঙ্গচ্ছেদের বেদনা যখন অনুভূত হল তখন দেখা গেল যে, কখন কতদিন আগে যে অঙ্গটি ছিন্ন হয়ে গেছে, তা যার জমির অঙ্গ ছিন্ন হয়েছে, সেও বলতে পারে না। হঠাৎ প্রয়োজনের সময় অর্থাৎ চাষের সময় দেখা যেত বলাই দাসের ছোট জমি বেড়ে গেছে এবং অন্যের বড় জমি ছোট হয়ে গেছে। এবং তখন ছিন্নাঙ্গ জমির মালিক সীমানা মাপতে এলে বলাই তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিত, জোর করলে লাঠি ধরত; সালিসি মান্য করলে আদালতের ভোলা দরজার দিকে পথ-নির্দেশ করে সালিসি অমান্য করে আসত। বাপ অনেক হিতোপদেশ দিলে, কিন্তু ছেলে শুনলে না; ধর্মের ভয় দেখালে, ছেলে নিৰ্ভয়ে উচ্চ-হেসে উঠে গেল। ওদিকে বাড়ির ভিতরেও তখন শাশুড়ি-পুত্রবধূতে বিরোধ বেধেছে। বৈষ্ণবের সংসারে বধূটি পেঁয়াজ ঢুকিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, মাছ ঢুকিয়েছে এবং ছেলে তাকে সমর্থন করেছে। একদিন মা এবং বউয়ের ঝগড়ার মধ্যে বলাই দাস মাকে গালাগাল দিয়ে স্ত্রীর হাত ধরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, এক অন্নে এক ঘরে সে আর থাকবে না, পোষাবে না। বাড়ির পাশেই সে তখন নূতন ঘর তৈরি করেছে। বাপ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেছিল-জয় মহাপ্রভু, তুমি আমাকে বাঁচালে!
আর বলাই দাসের অবাধ কর্মোদ্যম। তাতে বাপ মাথা হেঁট করে নিজের মৃত্যু কামনা করেছিল। হঠাৎ পুত্রবধূ দুটি ছেলে রেখে মারা গেল। বলাই দাস স্ত্রীর শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব ভোজন অন্তে বন্ধুবান্ধব ভোজন করালে মদ-মাংস-সহযোগে এবং গোপন করার চেষ্টা করলে না, নিজেই মত্ত অবস্থায় পথে পথে স্ত্রীর জন্য কেঁদে বলে বেড়ালে—তার জীবনে কাজ নেই, কোনো কিছুতে সুখ নেই, সংসার ত্যাগ করে সে চলে যাবে। সন্ন্যাসী হবে।
বাপ মহাপ্রভুর দরজায় মাথা কুটলে। এবং ছেলের বাড়িতে গিয়ে তাকে তিরস্কার করে এল। বলাই দাস কোনো উত্তর-প্রত্যুত্তর করলে না, কিন্তু গ্রাহ্য করলে হলেও মনে হল না, উঠে চলে গেল।
দিন তিনেক পর ভোরবেলা উঠে বাপ পথে বেরিয়েই দেখলে বলাই দাসের বাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে আতর বলে একটি স্বৈরিণী, গ্রামেরই অবনত সম্প্রদায়ের মেয়ে। বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে চলে গিয়েছে; ঝুমুর দলে নেচে গেয়ে এবং তার সঙ্গে দেহ ব্যবসায় করে বেড়ায়; মধ্যে মাঝে দু-দশ দিনের জন্য গ্রামে আসে। আতর কয়েকদিন তখন গ্রামেই ছিল।
বাপ ছেলেকে ডেকে তুলে তার পায়ে মাথা কুটেছিল। এ অধৰ্ম করিস নে। সইবে না। ব্যভিচার সবচেয়ে বড় পাপ।
হাত ধরে বলেছিল—তুই আবার বিয়ে কর।
বলাই দাস তখন অন্ধ। হয়ত-বা উন্মত্ত। শুধু আতরই নয়, গ্রামের আরও যে-কটি স্বৈরিণী ছিল তাদের সকলকে নিয়ে সে জীবনে সমারোহ জুড়ে দিলে। অনুরোধ ব্যর্থ হল, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে হল বিরোধ। বিরোধ শেষে চিরদিনের মত বিচ্ছেদের পরিণতির মুখে এসে দাঁড়াল।
বাপ সংকল্প করলে ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করবে। করলেও। নিজের সামান্য সাত বিঘা জমি দেবতার নামে অর্পণ করে ভবিষ্যৎ সেবাইত মহান্ত নিযুক্ত করলে নাতিদের। শর্ত করল যে, মতিভ্ৰষ্ট ব্যভিচারী বলাই দাস তাদের অভিভাবক হতে পারে না। তার অন্তে সেবাইত এবং নাতিদের অভিভাবক হবে তার স্ত্রী। তার স্ত্রীর মৃত্যুকালে যদি নাতিরা নাবালক থাকে, তো, কোনো বৈষ্ণবকে অভিভাবক নিযুক্ত করে দেবেন গ্রামের পঞ্চজন। ছেলে খবর শুনে এসে দাঁড়াল। বাপ পিছন ফিরে বসে বললে—এ-বাড়ি থেকে তুই বেরিয়ে যা। বেরিয়ে যায় বেরিয়ে যা! এ-বাড়ি আমার, কখনও যেন ঢুকিস নি, আমার ধৰ্ম চঞ্চল হবেন। মৃত্যুর সময়েও আমার মুখে জল তুই দিনে, মুখাগ্নিও করতে পাবিনে, শ্ৰাদ্ধও না। ভগবান যদি আজ আমার চোখ দুটি নেন, তবে আমি বাঁচি। তোর মুখ আমাকে আর দেখতে হয় না।
পরের দিন রাত্রে বাপ খুন হল। গরমের সময়, দাওয়ার উপর একদিকে শুয়ে ছিল বৃদ্ধ, অন্যদিকে নাতি দুটিকে নিয়ে শুয়ে ছিল বৃদ্ধা। গভীর রাত্রে কুড়ুল দিয়ে কেউ বৃদ্ধের মাথাটা দু ফাঁক করে দিয়ে গেল। একটা চিৎকার শুনে ধড়মড় করে বৃদ্ধা উঠে বসে হত্যাকারীকে ছুটে উঠোন পার হয়ে যেতে দেখে চিনেছিল যে সে তার ছেলে। মাথায় কোপ একটা নয়, দুটো। একটা কোপ বোধ করি প্রথমটা, পড়েছিল এক পাশে; দ্বিতীয়টা ঠিক মাঝখানে। মা সাক্ষী দিলে, আবছা অন্ধকার তখন, চাঁদ সদ্য ড়ুবেছে, তার মধ্যে পালিয়ে গেল লোকটি, তাকে সে স্পষ্ট দেখেছে। সে তার ছেলে বলাই। বলাই দাস অবিনাশবাবুকে উকিল দিয়েছিল। কতকটা জমি হাজার টাকায় বিক্রির ব্যবস্থা করে, ফৌজদারি মামলায় তার নামডাক শুনে, লোক পাঠিয়ে তাঁকে নিযুক্ত করেছিল। অবিনাশবাবু জেরা করতে বাকি রাখেন নি। মায়ের শুধু এক কথা।–বাবা
সুযোগ পেয়ে অবিনাশবাবু ধমক দিয়ে উঠেছিলেন। বাবা নয়! বাবা-টাবা নয়। বল, হুজুর।
মা বলেছিল–হুজুর, মায়ের কি ছেলে চিনতে ভুল হয়? আমি যে চল্লিশ বছর ওর মা। দুপুরবেলা মাঠ থেকে ফিরে এলে ওর পিঠে আমি রোজ তেল মাখিয়ে দিয়েছি।
অবিনাশবাবু বলেছিলেন—ছেলের সঙ্গে তোমার অনেক দিনের ঝগড়া। আজ বিশ বছর ঝগড়া। ছেলের বিয়ে হওয়া থেকেই ছেলের সঙ্গে তোমার মনোমালিন্য। তোমাদের ঝগড়া হত। বল সত্যি কি না?
মা বলেছিল তা খানিক সত্যি বটে। কিন্তু সে মনোমালিন্য নয় হুজুর। বড় পরিবারপরিবার বাই ছিল,-পরিবারের জন্যেই ও পেঁয়াজ-মাছ খেতে ধরেছিল, তার জন্যেই পেথকান্ন। হয়েছিল, তাই নিয়ে বকাকি হত। সে বকাকিই, আর কিছু নয়।
অবিনাশবাবু বলেছিলেন না। আমি বলছি সেই আক্ৰোশে তুমি বলছ তুমি চিনতে পেরেছ। নইলে আসলে তুমি চিনতে পার নি।
মা বলেছিল—চিনতে আমি পেরেছি হুজুর। আক্রোশও আমার নাই। ও আমার নিজের ছেলে। ধর্মের মুখ তাকিয়ে-মা থেমেছিল এইখানে, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল তার। অবিনাশবাবু তাকে কাঁদতে সুযোগ দেন নি, সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন ধর্মের মুখ তাকিয়ে? আবোল-তাবোল বোকো না। জোর করে কাঁদতে চেষ্টা কোরো না। বল কী বলছ?
মা-মেয়েটি কঠিন মেয়ে, সে আত্মসংবরণ করে নিয়ে বলেছিলনাঃ, কাদব না হুজুর। ধর্মের মুখ তাকিয়ে সত্যি কথাই আমাকে বলতে হবে হুজুর। আমি মিছে কথা বললে ও হয়ত এখানে খালাস পাবে। কিন্তু পরকালে কী হবে ওর? মরতে একদিন হবেই। আমিই-বা কী বলব ওর বাপের কাছে? আমি সত্যিই বলছি। হুজুর বিচার করে খালাস দিলে ভগবান ওকে খালাস দেবেন, সাজা দিলে সেই সাজাতেই ওর পাপের দণ্ড হয়ে যাবে; নরকে ওকে যেতে হবে না।
অবিনাশবাবু এইবার মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন, জেরা করেছিলেন পাপ-পুণ্য তুমি মান?
মা বলেছিল মানি বৈকি হুজুর। কে না মানে বলুন? নইলে দিনরাত হয় কী করে?
ধমক দিয়েছিলেন অবিনাশবাবু থাম, বাজে বোকো না। সঁইত্রিশ বছর আগে, বর্ধমান জেলায়, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে তুমি একবার এজাহার করেছিলে?
বৃদ্ধা ঈষৎ চকিত হয়ে মুখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে অবিনাশবাবুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।
কঠোর স্বরে অবিনাশবাবু বলেছিলেন–বল? উত্তর দাও।
বৃদ্ধা বলেছিল—দিয়েছিলাম।
–কিসের মামলা সেটা?
–আমি বাপের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম আমার এই স্বামীর সঙ্গে। আমার বাবা তাই মামলা করেছিল আমার স্বামীর নামে। সেই মামলায় আমি সাক্ষি দিয়েছিলাম।
—তোমার বাবার নাম ছিল রাখহরি ভটচাজ? তুমি বামুনের মেয়ে ছিলে?
–হ্যাঁ।
–যার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলে সে কোন্ জাত ছিল?
—সদ্গোপ। আমাদের বাড়ির পাশেই ওদের বাড়ি ছিল। ছেলেবেলা থেকে ওর বোনের সঙ্গে খেলা করতাম, ওদের বাড়ি যেতাম। তারপর ভালবাসা হয়। আমি যখন বুঝলাম, ওকে নইলে আমি বাঁচব না, তখন আমি ওর সঙ্গে বেরিয়ে আসি। দুজনে বোষ্ট্রম হয়ে বিয়ে করি। মামলা তখনই হয়েছিল।
–কী বলেছিলে তখন এজাহারে?
–বলেছিলাম-আমি বাপ চাই না, মা চাই না, ধৰ্ম্ম চাই না, আমি ওকে নইলে বাঁচব না, ওই আমার সব–পাপ-পুণ্য সব। এর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে যদি আমাকে নরকে যেতে হয় তো যাব।
মামলার সওয়াল-জবাবের সময় অবিনাশবাবু মায়ের চরিত্রের এই দিকটির ওপরেই বেশি জোর দিয়েছিলেন, নারীচরিত্রের বিচিত্র এক বৈশিষ্ট্যের কথা বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন–এ মেয়েটির অতীত ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ সেই বিচিত্র নারী-প্রকৃতি, যে নারী জীবনের সনাতন পুরুষের জন্য বাপ, মা, জাতি, কুল, ধর্ম অধৰ্ম সবকিছুকে অনায়াসে অবলীলাক্রমে ত্যাগ করতে পারে। এরা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বোধ করি এই লজ্জাকর মোহে মগ্ন এবং অন্ধ হয়ে থাকে। এরা অনায়াসে সন্তান ত্যাগ করে চলে যায় অবৈধ প্ৰণয়ের প্রচণ্ড আকর্ষণে, দেহবাদের। এক রাক্ষসী ক্ষুধার তাড়নায়। এই মেয়েটি যখন আজ ধর্মের কথা বলে তখন বিশ্বসংসার হাসে কিন্তু সে তা বুঝতে পারে না। প্রতিহিংসার তাড়নায় যে ধর্মকে সে মানে না আজ সেই ধর্মের দোহাই দিচ্ছে। আসলে সে হত্যাকারী কে তা চিনতে পারে নি। সেই অতি অল্পক্ষণ সময়, যে সময়ে সে স্বামীর চিৎকারে ঘুম ভেঙে উঠে মশারি ঠেলে বাইরে এসেছিল, যখন হত্যাকারী ঘরের দরজা পার হয়ে পালাচ্ছিল, তার মধ্যে রাত্রির অন্ধকারে কারুর কাউকে চিনতে পারা অসম্ভব। চিনতে সে পারে নি। হয়ত-বা কাউকে দেখেই নি, সে জেগে উঠতে উঠতে হত্যাকারী পালিয়ে গিয়েছিল। সেই উত্তেজিত অবস্থায় সে যা দেখেছিল তা তার চিত্তের কল্পনার অলীক প্রতিফলন। ছেলেকে সে গোড়া থেকেই দেখতে পারত না। তার ওপর ছেলের সঙ্গে স্বামীর বিরোধ হয়েছিল, সুতরাং তার মনে হয়েছিল পুত্রই হত্যাকারী এবং তাকেই সে কল্পনা-নেতে দেখেছিল। এ নারী মা নয়, মাতৃত্বহীনা, বিচিত্রা, পাপিষ্ঠা। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, মা হয়ে পুত্রকে হত্যাকারী বলে ঘোষণা করবার সময় একটি ফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত তার চোখ থেকে নির্গত হয় নি।
জোরালো বক্তৃতা অবিনাশবাবু চিরকালই করেন। ওই কেসে তিনি এই তথ্যটির ওপর ভিত্তি করে প্রাণ ঢেলে বক্তৃতা করেছিলেন। এ ছাড়া আর অন্য কোনো পথই ছিল না। এবং জুরীদের অভিভূত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তারা ওই কথাই বিশ্বাস করেছিলেন স্বামীর প্রতি অত্যধিক আসক্তির বশে এবং পুত্রের বিবাহের পর থেকে পুত্রবধূর প্রতি পুত্রের আকর্ষণের জন্য পুত্রের সঙ্গে তার সনাতন বিদ্বেষের প্রেরণাতেই আপন অজ্ঞাতসারে সে পুত্ৰকেই হত্যাকারী কল্পনা করেছে; এমন ক্ষেত্রে সদ্য ঘুমভাঙার মুহূর্তে অজ্ঞাত হত্যাকারীকে পুত্র বলে ধারণা করাই। সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক। সুতরাং তারা সন্দেহের সুযোগে অর্থাৎ বেনিফিট অফ ডাউটের অধিকারে আসামিকে নির্দোষ বলেছিলেন। কিন্তু এই কঠিন ব্যক্তিটি জুরীদের সঙ্গে ভিন্নমত হয়ে আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। এবং তার রায়ে অবিনাশবাবুর মন্তব্যগুলির তীব্র সমালোচনা করে। ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন।
রায়ে তিনি লিখেছিলেন—এই মায়ের সাক্ষ্য আমি অকৃত্রিম সত্য বলে বিশ্বাস করি। আসামিপক্ষের লার্নেড অ্যাডভোকেট তার চরিত্র যেভাবে মসীময় করে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন তা শুধু বিচার-ভ্রান্তিই নয়—অভিপ্ৰায়মূলক বলে আমার মনে হয়েছে। সাক্ষী এই মাটি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক চরিত্রের নারী। প্রবল দৈহিক আসক্তি, যা ব্যাধির শামিল, তার কোনো অভিব্যক্তিই নাই তার জীবনে। বরং একটি সূক্ষ্ম সুস্থ বিচারবোধ তার জীবনে আমি লক্ষ্য করেছি। সে প্রথম যৌবনে কুমারী জীবনে একজন অসবর্ণের যুবককে ভালবেসেছিল। সে ভালবাসার ভিত্তিতে দেহলালসাকে কোনো দিনই প্রধান বলে স্বীকার করে নি। প্রতিবেশীর পুত্ৰ, বাল্যসখীর ভাই, সুদীর্ঘ পরিচয় এ ভালবাসাকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিল; মনের সঙ্গে মনের অন্তরঙ্গতা ঘটেছিল। আকস্মিকভাবে কোনো সুস্থ সবল ও রূপবান যুবককে দেখে যুবতী মনে যে বিকার জন্মায়, তাকে উন্মত্ত করে তোলে—তা এ নয়। এ উপলব্ধি সম্পূর্ণরূপে মনের উপলব্ধি। সেই উপলব্ধিবশে যে হৃদয়াবেগের নির্দেশে সে গৃহ কুল জাতি ত্যাগ করেছিল তা সমাজববাঁধের বিচারে পাপ হতে পারে কিন্তু মানবিক বিচারে অন্যায় নয়, অধর্ম নয়, অস্বাস্থ্যকর নয়। সামাজিক ও মানবিক বিচার সর্বত্র একমত হতে পারে না বলেই আইন মানবিক বিচারের ভিত্তিতে গঠিত। হয়েছে একালে। যা সমাজের বিচারে পাপ সেই সূত্র অনুযায়ীই তা সর্বক্ষেত্রে আইনের বিচারে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে স্বীকৃত নয়। যাকে তিনি বলেছেন দেহলালসা—আইনের বিচারে আমার। দৃষ্টিতে তা সর্বজয়ী ভালবাসা-প্যাশন অব লাইফ; তার জন্য মর্মান্তিক মূল্য দিয়েও সে অনুতপ্ত নয়, লজ্জিত নয়। এবং পরবর্তী জীবনের আচরণে সে একটি বিবাহিতা সাধ্বী স্ত্রীর সকল কর্তব্য অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে করে এসেছে। এই মা যে বেদনার সঙ্গে ধর্মের মুখ তাকিয়ে পুত্রের বিরুদ্ধে সাক্ষি দিয়েছে তাকে আমি বলি ডিভাইন; স্বর্গীয় রূপে পবিত্র। আশ্চর্যের কথা, সুবিজ্ঞ অ্যাডভোকেট মহাশয় এই হতভাগিনী মায়ের সাক্ষ্য দেওয়ার সময়ের বেদনার্ততা ও ধর্মজ্ঞানের বা সনাতন নীতিজ্ঞানের মর্মান্তিক দ্বন্দ্ব যেন ইচ্ছাপূর্বকই লক্ষ্য করেন নি। বলেছেন—সাক্ষ্য দেওয়ার সময় পুত্রের ফাঁসি হতে পারে জেনেও তার চোখে জল পড়ল না।
হাইকোর্ট জ্ঞানেন্দ্রনাথের বিচারকেই মেনে নিয়েছিলেন।
জ্ঞানেন্দ্রনাথ আসামি অর্থাৎ ওই ছেলেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। এই দণ্ডাদেশ ঘোষণার ইতিহাসও ঠিক সাধারণ পর্যায়ে পড়ে না। অসাধারণই বলতে হবে। অবিনাশবাবু আর একটা কেসে ওখানে গিয়ে সে ইতিহাস শুনেছিলেন। তিন দিন নাকি সে তার অদ্ভুত স্তব্ধ অবস্থা; তিনটি রাত্রি তিনি ঘুমোন নি, সবটাই প্রায় লিখে ফেলে ওই দণ্ডাদেশের কয়েক লাইন অসমাপ্ত রেখে অবিশ্ৰান্ত পদচারণা করেছিলেন। এদিকে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীমহলে একটা উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছিল। জ্ঞানবাবুর এই বিনিদ্র রাত্রিযাপনের কথা তাদের কানে পৌঁছুতে বাকি থাকে নি। সিভিল সার্জেন এসেছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন এসপি। এসডি-ও যিনি, তিনিও এসেছিলেন। নতুন জজসাহেব শেষে কি ফাঁসির হুকুম দেবেন? এঁদের যে উপস্থিত থেকে দণ্ডাদেশকে কাজে পরিণত করতে হবে।
ভোরবেলা, আবছা অন্ধকারের মধ্যে ফাঁসির মঞ্চটাকে দেখে অদ্ভুত মনে হবে। মৃত্যুপুরীর হঠাৎ-খুলে-যাওয়া দরজার মত মনে হবে। মনে হবে, দরজাটার চারপাশের কাঠগুলো থেকে। কপাট-জোড়াটা অদৃশ্য হয়ে গেছে, খোলা দরজাটা হাঁ-হাঁ করছে মৃত্যুর গ্রাসের মত। তারপর দূর থেকে হয়ত হতভাগ্যের কাতর আর্তনাদ উঠবে। হয়ত ঝুলিয়ে তুলে নিয়ে আসবে একটা হাড় আর মাংসের বিহ্বল বোঝাকে। ওঃ! তারপর দণ্ডাদেশ পড়তে হবে। দণ্ডিত হতভাগ্যের মাথায় কালো টুপি পরিয়ে দেবে। ওঃ।
সিভিল সার্জেন বলেছিলেন—এ জেলে আজ তিরিশ বছর ফাঁসি হয় নি। গ্যালোজ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে। শুধু আছে একটা টিবি। সব নতুন করে তৈরি করতে হবে।
ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবও বিচলিত হয়েছিলেন।
পরামর্শ করে ওঁরা এসেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবুর কুঠিতে। ইঙ্গিতে অনুরোধও জানিয়েছিলেন। জ্ঞানবাবু বলেছিলেন–তিন দিন আমি ঘুমুই নি। শুধু ভেবেছি।
ম্যাজিস্ট্রেট বলেছিলেন-আমি শুনেছি। মানুষকে ডেথ সেন্টেন্স দেওয়ার চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক কর্তব্য কিছু হয় না।
জ্ঞানেন্দ্রবাবু বলেছিলেন, আমার স্ত্রীও খুব বিচলিত হয়েছেন। তিনি যেন আমার মুখের দিকে চাইতে পারছেন না। কিন্তু কী করব আমি।
সত্যই সুরমা দেবী অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন, সভয়ে বলেছিলেন—তুমি কি ফাঁসির হুকুম দেবে?
প্রথমটা উত্তর দিতে পারেন নি জ্ঞানেন্দ্রবাবু। অনেকক্ষণ পর বলেছিলেন ওর মা তার সাক্ষ্যে যে কথা বলে গেছে তারপর ওই দণ্ড দেওয়া ছাড়া আমি কী করতে পারি বল?
সুরমা দেবী এরপর আর কোন কথা বলবেন? তবু বলেছি। লনওই মায়ের কথাই ভেবে। দেখ। সে হতভাগিনীর আর কী থাকবে বল?
—ধৰ্ম! জ্ঞানেন্দ্রবাবু বলেছিলেন হিন্দু ধৰ্ম, মুসলমান ধৰ্ম কি ক্রিস্টান ধর্ম নয় সুরমাসত্যধর্ম।
কয়েক মুহূর্ত পরে মুখ তুলে এক বিচিত্ৰ হাসি হেসে বলেছিলেন ওই মেয়েটি আমাকে শিক্ষা দিয়ে গেল। ইতিহাসের বড় মানুষ মহৎ ব্যক্তি এই সত্যকে পালন করে আসেন পড়েছি; একালে মহাত্মা গান্ধীকে দেখেছি, মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু ভেবেছি—ও পারেন শুধু মহৎ যারা তারাই। কিন্তু ওই মেয়েটি বুঝিয়ে দিলেনা, পারে, তার মত মানুষেও পারে। মস্ত বড় আশ্বাস পেলাম। আজ।
বলেই সঙ্গে সঙ্গে বসে গিয়েছিলেন লিখতে। এক নিশ্বাসেই প্রায় লাইন কটি লিখে শেষ করে দিয়েছিলেন। বিচার নিষ্ঠুর নয়, সে সাংসারিক সুখদুঃখের গণ্ডির উর্ধ্বে। জাস্টিস ইজ ডিভাইন।
সেদিন ম্যাজিস্ট্রেট, এসপি, সিভিল সার্জেন এঁদেরও সেই কথাই তিনি বলেছিলেন। আর কোনো দণ্ড এক্ষেত্রে নাই। আমি পারি না! আই কান্ট।
ঘ.
অবিনাশবাবু মামলাটি সযত্নে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। সাজাবার অবশ্য বিশেষ কিছু ছিল না, তবু একটি স্থান ছিল যেটির জন্য গোটা মামলাটি সম্পর্কে প্রথমেই বিরূপ ধারণা হয়ে যেতে পারে। তার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়েই রয়েছেন। তিনি স্থির জানেন যে, বিচারকের আসনে উপবিষ্ট ওই যে লোকটির স্থির দৃষ্টি সামনের খোলা দরজার পথে বাইরের উন্মুক্ত প্রসারিত প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে লক্ষ্যহীনের মত, যা দেখে মনে হচ্ছে এই আদালত-কক্ষের কোনো কিছুর সঙ্গেই তার ক্ষীণতম যোগসূত্রও নেই, দৃষ্টির সঙ্গে কোন দূরে চলে গিয়েছে তার মন উদাসী বৈরাগীর মত, ঘটনার বর্ণনায় কোনো অসঙ্গতি ঘটলে অথবা ঘটনার ঠিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানটিতে মানুষটি সজাগ হয়ে উঠে বলবেন ইয়েস। অথবা চকিত হয়ে ঘুরে তাকাবেন, ভুরুদুটি প্রশ্নের ব্যঞ্জনায় কুঞ্চিত হয়ে উঠবে, এবং জিজ্ঞাসা করবেন—হোয়াট? কী বললেন– মিস্টার মিট্রা? ডিড ইউ সে?
অবিনাশবাবুর অনুমান মিথ্যা হল না; আজও জজসাহেব চকিতভাবে ঘুরে অবিনাশবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, হোয়াট? কী বলছেন মিঃ মিট্রা? আপনি বলছেন ছোটভাই খগেন্দ্র ঘোষ, যে খুন হয়েছে, সে-ই আসামি বড়ভাই নগেনকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল? নগেন, এই আসামি, ডেকে নিয়ে যায় নি?
অবিনাশবাবু খুশি হলেন মনে-মনে, এই প্রশ্নই তিনি চেয়েছিলেন; তিনি সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নেড়ে বললেন– ইয়েস, ইয়োর অনার। তাই প্রকৃত ঘটনা। তাই বলেছি আমি।
জ্ঞানেন্দ্রবাবু বললেন—দ্যাট্স্ অলরাইট। গো-অন প্লিজ।
অবিনাশবাবু বলে গেলেন ইয়েস, ইয়োর অনার, ঘটনার যা পরিণতি তাতে সাধারণ নিয়মে আসামি নগেন এসে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল এই হলেই ঘটনাটি সোজা হত। এবং পূর্বের কথা অনুযায়ী নগেনেরই ডাকতে আসবার কথাও ছিল। কিন্তু সে আসে নি।
অবিনাশবাবু ধীরকণ্ঠে একটি একটি করে তাঁর বক্তব্যগুলি বলতে শুরু করলেন। কোনো আবেগ নাই, কোনো উত্তাপ নাই, শুধু যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণ।-নগেন আসে নি। তারই ডাকবার কথা ছিল, কিন্তু সে এল না, ডাকলে না। ইয়োর অনার, এইটিই হল আসামির সুচিন্তিত পরিকল্পনার অতি সূক্ষ্ম চাতুর্যময় অংশ। অন্যদিকে এই অতিচতুরতাই তার উদ্দেশ্যকে ধরিয়ে দিচ্ছে, অত্যন্ত সহজে ধরিয়ে দিচ্ছে। সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা অত্যন্ত সহজেই এ তথ্য উঘাটিত হবে। অবশ্য আর একটি ব্যাখ্যাও হতে পারে, কিন্তু তাতেও এই একই সত্যে উপনীত হই আমরা। ইয়োর অনার, সমস্ত বিষয়টি যথার্থ পটভূমির উপর উপস্থাপিত করে চিন্তা করে দেখতে হবে। পটভূমিকা কী? পটভূমি হল-বাঙলাদেশের পল্লীগ্রামের একটি স্বল্পবিত্ত চাষীর সংসার। সুবল ঘোষ একজন চাষী। আমাদের দেশের পঞ্চাশ বছর আগের চাষীদের একজন। তখনকার দিনের ধর্মবিশ্বাসে সামাজিক বিশ্বাসে দৃঢ় বিশ্বাসী। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলেটি বাল্যকাল থেকেই বিচিত্র প্রকৃতির। সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, প্রথমটায় এই বালক ছিল অত্যন্ত দুর্দান্ত। বাপ একমাত্র ছেলেকে অনেক আশা পোষণ করে স্কুলে পড়তে দিয়েছিল। সাধ্যের অতিরিক্ত হলেও ছেলেকে মানুষের মত মানুষ, ভদ্র শিক্ষিত মানুষ তৈরি করবার সাধকে। সে খর্ব করে নি। কয়েক মাইল দূরে বর্ধিষ্ণু গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে বোর্ডিঙে রেখেছিল। স্কুলের রেকর্ডে আমরা পাই, ছেলেটি আরও কতকগুলি দুর্দান্ত প্রকৃতির ছেলের সঙ্গে মিশে স্কুলে প্রায় নিত্যশাসনের পাত্র হয়ে ওঠে এবং দু বছর পরেই স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়। তার কারণ কী জানেন? তার কারণ চৌর্যাপরাধ এবং হত্যা; মানুষ নয়—জন্তু। বোর্ডিঙের কাছেই ছিল একজন ছাগল-ভেড়া ব্যবসায়ীর খামার এবং গোয়াল। এই গোয়াল থেকে নিয়মিতভাবে দুচার দিন পর পর ছাগল-ভেড়া অদৃশ্য হত। কোনো চিহ্ন পাওয়া যেত না। রক্তের দাগ না, কোনো রকমের চিৎকার শোনা যেত না, কেনো হিংস্ৰ জানোয়ারেরও কোনো প্রমাণ পাওয়া যেত না। শেষ পর্যন্ত অনেক সতর্ক চেষ্টার পর ধরা পড়ল এই দলের একটি ছোট ছেলে। সে স্বীকার করলে, এ কাজ তাদের। তারা এই ছাগল-ভেড়া চুরি করে গভীর রাত্রে রান্না করে ফিস্ট করত। বিচিত্রভাবে অপহরণ করতে পটু এবং সক্ষম ছিল একটি বালক! এই আসামি নগেন ঘোষ। কয়েকটি গোপন প্রবেশপথ তারা করে রেখেছিল। একটি জানালাকে এমনভাবে খুলে রেখেছিল। যে, কেউ দেখে ধরতে পারত না যে, জানালাটি টানলেই খুলে আসে। সেই পথে রাত্রে প্রবেশ করত এই নগেন এবং ঘরের মধ্যে ঢুকেই যেটিকে সে সামনে পেত, সেইটিকেই মুহূর্তে গলা টিপে ধরত, এবং সঙ্গে সঙ্গে মুচড়ে ঘুরিয়ে দিত। এতে সে প্রায় সিদ্ধহস্ত হয়েছিল। এমনটি আর অন্য কেউই পারত না। এই কারণের জন্যই হেডমাস্টার তাকে স্কুল থেকে বিতাড়িত করেন। বাপ এর জন্য অত্যন্ত মর্মাহত। এবং ছেলেকে কঠিন তিরস্কার করে। তারা বৈষ্ণব, এই অপরাধ তাদের পক্ষে মহাপাপ। এই অপরাধ বাপকে এমনই পীড়া দিয়েছিল যে সে এই পাপের জন্য ছেলেকে প্ৰায়শ্চিত্ত না করিয়ে পারে নি; মাথা কামিয়ে শাস্ত্ৰবিধিমত প্ৰায়শ্চিত্ত! ছেলে সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করে। এবং বার বৎসর নিরুদ্দেশ থাকার পর ফিরে আসে। তখন তার বয়স প্রায় আটাশ-ঊনত্রিশ। ইয়োর অনার, সন্ন্যাসীর বেশে ফিরে আসে। তখন এই যে ক্ষুদ্র শান্ত চাষীর সংসারটি, সে-সংসারে পরিবর্তনশীল কালের স্রোতে অনেক ভাঙন ভেঙেছে এবং অনেক নূতন গঠনও গড়ে উঠেছে। নগেনের মায়ের মৃত্যু হয়েছে, তার ভগ্নী বিধবা হয়েছে, বাপ সুবল ঘোষ বংশলোপের ভয়ে আবার বিবাহ করেছে, এবং একটি শিশুপুত্র রেখে সে-পত্নীটিও পরলোকগমন করেছে। সুবল ঘোষ তখন কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। শিশুপুত্রটিকে মানুষ করছে। সুবলের বিধবা কন্যা, আসামি নগেনের সহোদরা।
সুবল হারানো ছেলেকে পেয়ে আনন্দে অধীর হল এবং তার অঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশ দেখে। কেঁদে আকুল হয়ে উঠল। বললে—তুই এবেশ ছাড়।
নগেন বললে–না।
বাপ বললে–ওরে তুই হবি সন্ন্যাসী, হয়ত নিজে পাবি পরমার্থ, মোক্ষ। কিন্তু এই আমাদের পিতৃপুরুষের ভিটে, এই ঘোষ বংশ? ভেসে যাবে?
নগেন বললে–ওই তো খগেন রয়েছে।
সুবল বললেছ বছরের ছেলে, ও বড় হবে, মানুষ হবে, ততদিনে মানুষ-অভাবে ঘর পড়বে, দোর ছাড়বে; জমিজেরাত খুদকুঁড়ো দশজনে আত্মসাৎ করে পথের ভিখারি করে দেবে। ওই বিধবা ঘোষ বংশের যুবতী মেয়ে, তোর মায়ের পেটের বোন, ওর অবস্থা কী হবে ভাব? মন্দটাই ভাব!
নগেন বললে, বেশ, খগেনকে বড় করে ওর বিয়ে দিয়ে ঘরসংসার পাতিয়ে দেওয়া পর্যন্ত আমি রইলাম। কিন্তু আর কিছু আমাকে বোলো না।
পাবলিক প্রসিকিউটার অবিনাশবাবু তাঁর হাতের কাগজগুলি টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে কোর্টের দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকালেন। পাঁচটার দিকে চলেছে ঘড়ির কাটা। টেবিলের উপর কাগজ-ঢাকা কাচের গ্লাসটি তুলে খানিকটা জল খেয়ে আবার আরম্ভ করলেন, ইয়োর অনার, মানুষের মধ্যেই জীবনশক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। জড়ের মধ্যে যে-শক্তি অন্ধ দুর্বার, জন্তুর মধ্যে যে-শক্তি প্রবৃত্তির আবেগেই পরিচালিত, মানুষের মধ্যে সেই শক্তি মন বুদ্ধি ও হৃদয়ের অধিকারী হয়েছে। জন্তুর প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না; সার্কাসের জানোয়ারকে অনেক শাসন করে অনেক মাদক খাইয়েও তার সামনে চাবুক এবং বন্দুক উদ্যত রাখতে হয়। একমাত্র মানুষেরই পরিবর্তন আছে, তার প্রকৃতি পালটায়। ঘাত-প্রতিঘাতে, শিক্ষা-দীক্ষায়, নানা কার্যকারণে তার প্রকৃতির শুধু পরিবর্তনই হয় না, সেই পরিবর্তনের মধ্যে সে মহত্তর প্রকাশে প্রকাশিত করতে চায় নিজেকে, এইটেই অধিকাংশ ক্ষেত্রের নিয়ম। অবশ্য বিপরীত দিকের গতিও দেখা যায়, কিন্তু সে দেখা যায় স্বল্পক্ষেত্রে।
জ্ঞানবাবুর গম্ভীর মুখে একটি হাসির রেখা ফুটে উঠল। অবিনাশবাবু চতুর ব্যক্তি। অসাধারণ কৌশলী। এইমাত্ৰ যে-কথাগুলি তিনি বললেন, সেগুলি তার অর্থাৎ জ্ঞানবাবুর কথা। কিছুদিন আগে এখানকার লাইব্রেরিতে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এই কথাগুলিই বলেছিলেন।
অবিনাশবাবু বললেন– তৎকালীন আচার-আচরণ কাজকর্ম সম্পর্কে যে প্রমাণ আমরা পাই, তাতে আমি স্বীকার করি যে, আসামি নগেনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছিল এবং সে-পরিবর্তন সৎ ও শুদ্ধ পরিবর্তন। তার বার বৎসরকাল অজ্ঞাতবাসের ইতিবৃত্ত আমরা জানি না কিন্তু পরবর্তীকালের নগেনকে দেখে বলতে হবে, এই অজ্ঞাতকালের সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্পর্শ এবং তীর্থ ইত্যাদি ভ্রমণের ফল নিঃসন্দেহে একটি পবিত্র প্রভাব বিস্তার করেছিল তার উপর। না-হলে, অর্থাৎ সেই বর্বর পাষণ্ডতা তার মধ্যে সক্রিয় থাকলে, সে অনায়াসেই তার বাপের মৃত্যুর পর দু-বছরের বালক খগেনকে সরিয়ে দিয়ে নিষ্কণ্টক হতে পারত। তার পরিবর্তে সে এই সভাইকে ভালবেসে বুকে তুলে নিলে। শুধু তাই নয়, বাপের মৃত্যুর কিছুদিন পর বিধবা বোন মারা যায়। তারপর এই নগেনই একাধারে মা এবং বাপ দুইয়ের স্নেহ দিয়ে তাকে মানুষ করে। ছেলেটি দেখতে ছিল অত্যন্ত সুন্দর। নগেন খগেনকে খগেন বলে ডাকত না, ডাকত গোপাল বলে। টোপরের মত কোকড়া একমাথা চুল, কাঁচা রঙ, বড় বড় চোখ। ছেলেটি সত্যিই দেখতে গোপালের মত ছিল।.
একটু থেমে হেসে অবিনাশবাবু বললেন–এক্সকিউজ মি ইয়োর অনার, আমি এক্ষেত্রে একটু কাব্য করে ফেলেছি। বাট আই অ্যাম নট আউট অব মাই বাউন্ডস, ইয়োর অনার। কারণ–
জ্ঞানবাবু বললেন–একটু সংক্ষেপ করুন।
অবিনাশবাবু বললেন–এই মামলাটি অতি বিচিত্র ধরনের, ইয়োর অনার, আমার মনে হয়, বর্তমান ক্ষেত্রে এমনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এবং তার বিশ্লেষণ ভিন্ন আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হতে পারব না। আমি নিজে স্বীকার করেছে যে, নৌকো উটে নদীর মধ্যে দুজনে জলে ড়ুবে গিয়েছিল। ছোট ভাই সাঁতার ভাল জানত না, সে বড় ভাইকে জড়িয়ে ধরে, বড় ভাই আসামি নগেন সেই অবস্থায় নিজেকে তার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য আত্মরক্ষার জান্তব প্রবৃত্তির তাড়নায় তার গলার নলি টিপে ধরে। এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ছোট ভাইয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভেসে উঠে কোনো রকমে এসে নদীর বাঁকের মুখে চড়ায় ওঠে। পরদিন সকালে ছোট ভাইয়ের দেহ পাওয়া যায় ওই চড়ায় আরও খানিকটা নিচে। মৃত খগেনের শবব্যবচ্ছেদের যে রিপোর্ট আমরা পেয়েছি, তাতেও দেখেছি খগেনের গলায় কণ্ঠনালীর দুইপাশে কয়েকটি ক্ষতচিহ্ন ছিল। ডাক্তার বলেন, নখের দ্বারাই এ ক্ষতচিহ্ন হয়েছে। এবং শবের পাকস্থলীতে জল পাওয়া গেছে অতি অল্প; জলে ড়ুবে মৃত্যু হলে আরও অনেক বেশি পরিমাণে জল পাওয়া যেত। ডাক্তার সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এ মৃত্যু ঘটেছে শ্বাসরোধের ফলে এবং কণ্ঠনালী প্রচণ্ড শক্তিতে টিপে ধরার জন্য, মৃতের শ্বাস রুদ্ধ হয়েছিল। এখন এক্ষেত্রে আমাদের বিচার্য, আসামি নগেন মানসিক কোন অবস্থায় খগেনের গলা টিপে ধরেছিল। সেই মানসিক অবস্থার অভ্রান্ত স্বরূপ নির্ণয়ের উপরই অভ্রান্ত বিচার নির্ভর করছে। সামান্যমাত্র ভ্রান্তিতে বিচারের পবিত্রতা, মহিমা কলঙ্কিত হতে পারে, নষ্ট হতে পারে। আমরা নির্দোষ একটি অতি সাধারণ মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণায় অধীর হয়ে মানবিক জ্ঞান হারিয়ে আত্মরক্ষার জান্তব প্রবৃত্তির অধীন হওয়ার জন্য তাকে ভুল করে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করার ভ্রম করতে পারি। আবার বিপরীত ভুলের বশে অতি-সুচতুর অতিকুটিল ষড়যন্ত্র ভেদ করতে না-পেরে নিষ্ঠুরতম পাপের পাপীকে মুক্তি দিয়ে মানবসমাজের চরমতম অকল্যাণ করতে পারি। ইয়োর অনার, সিংহচর্মাবৃত গর্দভ সংসারে অনেক আছে, কিন্তু মনুষ্যচর্মাবৃত নরঘাতী পশু বা বিষধরের সংখ্যা আরও অনেক বেশি। সিংহচর্মাবৃত গর্দভের সিংহচর্মের আবরণ টেনে খুলে দিলেই সমাজ নিরাপদ হয়, সমাজে কৌতুকের সৃষ্টি হয়; মনুষ্যচর্মাবৃত পশু বা সরীসৃপের মনুষ্যকর্মের আবরণ মুক্ত করলে মানুষের সমাজ আতঙ্কিত হয়; তখন সমাজকে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবার গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে সমাজেরই উপরে। এই কারণেই আমাকে অতীতকাল থেকে এ-পর্যন্ত এই আসামির জীবন ও কৃতকর্মগুলি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করতে হচ্ছে। ধৰ্মাধিকরণে বিচারক মানুষ হয়েও মানুষের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন, স্থূল প্রমাণ-প্রয়োগসম্মত বিচার করার চেয়েও তার বড় দায়িত্ব আছে; স্কুল প্রমাণ-প্রয়োগের আবরণ ছিঁড়ে মর্ম-সত্যকে আবিষ্কার করে তেমনি বিচার করতে হবে, যাকে বলতে পারি ডিভাইন জাস্টিস।
কোর্টের বাইরে কম্পাউন্ডের ওদিক থেকে পেটা ঘড়িতে ঘণ্টা বাজতে লাগল ঢং ঢং। কোর্টরুমের ঘড়িতে তখনও পাঁচটা বাজতে দু মিনিট বাকি।
নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জ্ঞানবাবু বললেন–কাল পর্যন্ত মামলা মুলতুবি রইল।
একবার তাকিয়ে দেখলেন আসামির দিকে। সরল সুস্থদেহ নগেন ঘোষ, স্থির নিম্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। আশ্চর্য স্থির দৃষ্টি, লোকটার মুখ যেন পাথরে গড়া। কোনো অভিব্যক্তি নাই।
লোকটি থানা থেকে এসডিও কোর্ট এবং এখান পর্যন্ত স্বীকার করে একই কথা বলে আসছে। নৌকাতে নদী পার হবার সময় বাতাস একটু জোর ছিল; মাঝনদী পার হয়েই বাতাস আরও জোর হয়ে উঠেছিল, খগেন সাঁতার প্রায় জানত না, সে ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠে, নগেন হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরে তাকে বলে, ভয় কী? খগেন মুহূর্তে নৌকার ওপাশ থেকে এপাশে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে ছোট নৌকাখানা যায় উল্টে। জলের মধ্যে খগেন তাকে সজোরে আঁকড়ে ধরে। দুজনে ড়ুবতে থাকে। প্রথমটা নগেন তার হাত ছাড়াতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যত চেষ্টা করেছে, ততই সে নগেনকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরেছে। নগেনের বুকটা ফেটে যাচ্ছিল, জল খাচ্ছিল সে, হঠাৎ খগেনের গলায় তার হাত পড়ে। সে ওর গলাটা টিপে ধরে। খগেন তাকে ছেড়ে দেয়। সে জানে না, খগেন তাতেই মরেছে কি না। কিনারায় এসে উঠে কিছুক্ষণ সে শুয়ে ছিল সেখানে। তারপর কোনো রকমে উঠে বাড়ি আসে। মাঝরাত্রে তার শরীর সুস্থ হলে মনে হয়, খগেন হয়ত মরে গিয়েছে। হয়ত গলা টিপে ধরাতেই সে মরে গিয়েছে। সকালে উঠে সে থানায় যায়। এজাহার করে। এর সাজা কী সে তা জানে না। ভগবান।
জানেন। যা সাজা হয় জজসাহেব দিন, সে তাই নেবে।
ভগবান জানেন। হায় হতভাগা! নিজে কী করেছে তা নিজে জানে না। ভগবানকে সাক্ষী মানে। কিন্তু ভগবান তো সাক্ষি দেন না। অথচ ডিভাইন জাস্টিস করতে হবে বিচারককে।
ডিভাইন জাস্টিস!
অবিনাশবাবু কথাটা যেন অভিপ্ৰায়মূলকভাবেই ব্যবহার করেছেন।
কথাটা জ্ঞানবাবু নিজেই বোধ করি অন্যের অপেক্ষা বেশি ব্যবহার করেন। স্কুল প্রমাণ প্রয়োগ যেখানে একমাত্র অবলম্বন, মানুষ যতক্ষণ স্বাৰ্থান্ধতায় মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না, ততক্ষণ ডিভাইন জাস্টিস বোধহয় অসম্ভব। সরল সহজ সভ্যতাবঞ্চিত মানুষ মিথ্যা বললে সে-মিথ্যাকে চেনা যায়, কিন্তু সভ্য-শিক্ষিত মানুষ যখন মিথ্যা বলে তখন সে-মিথ্যা সত্যের চেয়ে প্রখর হয়ে ওঠে। পারার প্রলেপ লাগানো কাচ যখন দর্পণ হয়ে ওঠে তখন তাতে প্রতিবিম্বিত সূর্যটা চোখের দৃষ্টিকে সূর্যের মতই বর্ণান্ধ করে দেয়। জজ, জুরী, সকলকেই প্রতারিত হতে হয়। অসহায়ের মত।
জাস্টিস চ্যাটার্জি বলতেন—He is God, God alone, He can do it.—আমরা পারি না। অমোঘ ন্যায়-বিধানের কর্তব্যবোধ এবং ন্যায়ের মহিমাকে স্মরণে রেখে প্ৰমাণ-প্ৰয়োগগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে, বিন্দুমাত্র ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে, আমরা শুধু বিধান অনুযায়ী বিচার করতে পারি।
একটি নারী অপরাধিনীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার সময় বলেছিলেন তিনি। সুরমা তারই মেয়ে; সুরমা কেঁদে ফেলেছিল—একটা মেয়েকে ফঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবে বাবা?
চ্যাটার্জি সাহেব বলেছিলেন—অপরাধের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের কৃতকর্মের গুরুত্ব এক তিল কমবেশি হয় না মা। দণ্ডের ক্ষেত্রেও নারী বা পুরুষ বলে কোনো ভেদ নাই। ঈশ্বরকে স্মরণ করে এক্ষেত্রে আমার এই দণ্ড না দিয়ে উপায় নেই।
তারই কাছে জ্ঞানেন্দ্রনাথ শিখেছিলেন বিচারের ধারাপদ্ধতি। তিনিই ওঁর গুরু। জ্ঞানেন্দ্রবাবু ঈশ্বর মানেন না। ঈশ্বরকে স্মরণ তিনি করেন না। ঈশ্বর, ভগবান নামটি বড় ভাল। কিন্তু শুধুই নাম। তিনি সাক্ষিও দেন না, বিচারও করেন না, কিন্তু ওই নামের মধ্যে একটা আশ্চর্য পবিত্রতা আছে, বিচারের ক্ষেত্রে একটি আদর্শ আছে; সেটিকেই তিনি স্মরণ করেন। তাই ডিভাইন জাস্টিস। ফিরবার পথে গাড়ির মধ্যে বসে বার বার তিনি আপনার মনে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করে। চলেছিলেন–ডিভাইন জাস্টিস ডিভাইন জাস্টিস।
স্থূল প্রমাণ-প্রয়োগের আবরণ ছিঁড়ে মর্ম-সত্যকে আবিষ্কার করে তেমনি বিচার করতে হবে যা অভ্রান্ত, যাকে বলতে পারি ডিভাইন জাস্টিস।
অবিনাশবাবুর কথাগুলি কানের পাশে বাজছে।
ডিভাইন জাস্টিস ডিভাইন জাস্টিস!
স্ত্রী সুরমা দেবী কুঠির হাতার বাগানের মধ্যে বেতের চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে বসে বই পড়ছিলেন। সারা দিনের বাদলার পর ঘণ্টাখানেক আগে মেঘ কেটে আকাশ নির্মল হয়েছে, রোদ উঠেছে। সে-রৌদ্রের শোভার তুলনা নেই। ঝলমল করছে সুস্নাত সুশ্যামল পৃথিবী। সম্মুখে। পশ্চিম দিগন্ত অবারিত। কুঠিটা শহরের পশ্চিম প্রান্তে একটা টিলার উপর। এর ওপাশে পশ্চিমদিকে বসতি নেই, মাইল দুয়েক পর্যন্ত অন্য কোনো গ্রাম বা জঙ্গল কিছুই নেই, লাল কাকুরে প্রান্তরের মধ্যে তিন-চারটে অশ্বত্থ গাছ আর একটা তালগাছ বিক্ষিপ্তভাবে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আর প্রান্তরটার মাঝখান চিরে চলে গেছে একটা পাহাড়িয়া নদী। ভরা বর্ষায় নদীটা এখন কানায় কানায় ভরে উঠে বয়ে যাচ্ছে। তারই ওপাশ অবধি প্রান্তরের দিগন্তের মাথায় সিঁদুরের মত টকটকে রাঙা অস্তগামী সূর্য। রৌদ্রের লালচে আভা ক্রমশ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। গাড়িটা এসে দাঁড়াল। আরদালি নেমে দরজা খুলে দিয়ে সসম্ভ্ৰমে সরে দাঁড়াল। জ্ঞানেন্দ্রবাবু এরই মধ্যে গভীর চিন্তায় ড়ুবে গিয়েছিলেন। স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন গাড়ির মধ্যে। আরদালি মৃদুস্বরে ডাকলে হুজুর!
চমক ভাঙল জ্ঞানেন্দ্রবাবুর। ও! বলে তিনি গাড়ি থেকে নামলেন।
সুরমা দেবী স্বামীকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। বইখানা চায়ের টেবিলের উপর রেখে দিয়ে এগিয়ে এলেন। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে গাঢ় কণ্ঠেই বললেন– কতদিন চলবে সেস?
একটু হেসে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন– বেশিদিন না। সেটা জটিল কিন্তু সাক্ষীর সংখ্যা কম। দিনে বেশি দিন লাগবে না।
বাগানের মধ্যে চায়ের টেবিলটার দিকে তাকিয়ে বললেন– বাগানে চায়ের টেবিল পেতেছ?
সুরমা বললেন–বৃষ্টি আসবে না। দেখছ কেমন রক্তসন্ধ্যা করেছে।
–হ্যাঁ। অপরূপ শোভা হয়েছে। আকাশের দিকে এতক্ষণে তিনি চেয়ে দেখলেন,সুরমা কথাটা বলে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিতে তবে ফিরল সেদিকে। রক্তসন্ধ্যায় রক্তসন্ধ্যার মধ্যে জীবনের একটি স্মৃতি জড়ানো আছে। সুরমার সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা হয়েছিল, সেদিনও রক্তসন্ধ্যা হয়েছিল আকাশে।
সুরমা বললেন–তাড়াতাড়ি এসে একটু।
–Yes, time and tide wait for none;–হাসলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু।
–শুধু তার জন্যই নয়। কবিতা শোনাব।
–এক্ষুনি আসছি।
জ্ঞানেন্দ্রবাবু হাসলেন। গম্ভীর ক্লান্ত মুখখানি ঈষৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি খুশি হয়ে উঠেছেন। দীর্ঘদিন পর সুরমা কবিতা লিখে তাকে শোনাতে চেয়েছে। সুরমা কবিতা লেখে, তার ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা লেখে। তখন লিখত হাসির কবিতা। সেকালে নাম করেছিল। সুরমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর তিনিও কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। কবিতায় সুরমার কবিতার উত্তর দিতেন তিনি। এবং আবিষ্কার করেছিলেন যে তিনিও কবিতা লিখতে পারেন। অন্তত পারতেন। জজিয়তির দপ্তরে তঁর সে-কবিত্ব পাথরচাপা ঘাসের মতই মরে গেছে। কিন্তু সুরমার জীবনে বারমাসে ফুল-ফোটানো গাছের মত কাব্যরুচি এবং কবিকর্ম নিরন্তর ফুটেই চলেছে, ফুটেই চলেছে।
হয়ত অজস্র ফুল ফোটায় সুরমা, কিন্তু সে ফোটে তার দৃষ্টির অন্তরালে তার নিশ্বাসের গণ্ডির বাইরে। কবে থেকে যে এমনটা ঘটেছে তার হিসেব তার মনে নেই, কিন্তু ঘটে গেছে। হঠাৎ একদা আবিষ্কার করেছিলেন যে, সুরমা তাকে আর কবিতা শোনায় না। কিন্তু সে লেখে। প্রশ্ন করেছিলেন সুরমাকে; সুরমা উত্তর দিয়েছিলেন হাসির কবিতা লিখতাম, হাসি ঠাট্টা করেই শোনাতাম। ওসব আর লিখি না। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যা লেখ তাই শোনাও।
সুরমা বলেছিলেন শোনাবার মত যেদিন হবে সেদিন শোনাব। জ্ঞানেন্দ্রনাথ একটু জোর করেছিলেন, কিন্তু সুরমা বলেছিলেন-ও নিয়ে জোর কোরো না। প্লিজ!
জ্ঞানেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ পরই ভুলে গিয়েছিলেন কথাটা। বারমাসে ফুল-ফোটানো সেই গাছের মতই সুরমার জীবন-যাতে শুধু ফুলই ফোটে, ফল ধরে না! সুরমা নিঃসন্তান।
আজ সুরমা কবিতা শোনাতে চেয়েছে। চিন্তা-ভারাক্রান্ত মন খানিকটা হালকা হয়ে উঠল। গুরুভারবাহীর ঘর্মাক্ত শ্ৰান্ত দেহে ঠাণ্ডা হাওয়ার খানিকটা স্পর্শ লাগল ফেন।
একবার ভাল করে সুরমার দিকে তাকালেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। পরিণত-যৌবনা এ সুরমার মধ্যে সেই প্রথম দিনের তরুণী সুরমাকে দেখতে পাচ্ছেন যেন। ঘোষাল সাহেব বাঙলোর মধ্যে চলে গেলেন, একটু ত্বরিত পদেই। সুরমা দেবী দাঁড়িয়েই রইলেন পশ্চিম দিগন্তের দিকে চেয়ে।
সুরমার মনেও সেই স্মৃতি গুঞ্জন করে উঠেছে আজ। অনেকক্ষণ থেকে। সাড়ে চারটের সময় বাইরে বারান্দায় এসে দূরের ওই ভরা নদীটার দিকে চেয়ে বসে ছিলেন তিনি। ধীরে ধীরে নিঃশব্দ আয়োজনের মধ্যে আকাশে রক্তসন্ধ্যা জেগে উঠেছিল। তার দৃষ্টি সেদিকে তখন আকৃষ্ট হয় নি। হঠাৎ রেডিওতে একটি গান বেজে উঠল। সেই গানের প্রথম কলি কানে যেতেই আকাশের রক্তসন্ধ্যা যেন মনের দোরে ডাক দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।
তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর আমার সাধের সাধনা।
শুধু রক্তসন্ধ্যার রর্ণচ্ছটাই নয়, তার সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার স্মৃতিটুকুও বর্ণাঢ্য হয়ে দেখা দিল।
সে কত কালের কথা! বর্ধমানে জজসাহেবের কুঠিতে ছিল তখন তারা। তার বাবা তখন। বর্ধমানে সেসন জজ। উনিশ শো একত্রিশ সাল। আগস্ট মাস। এমনি বর্ষা ছিল সারাদিন। সন্ধ্যার মুখে ক্ষান্তবর্ষণ মেঘে এমনি রক্তসন্ধ্যা জেগে উঠেছিল। বাবা-মা বাড়িতে ছিলেন না, তারা গিয়েছিলেন ইংরেজ পুলিশ সাহেবের কুঠিতে চায়ের নিমন্ত্রণে। নিজে সে তখন কলকাতায় থেকে পড়ত। সেইদিনই সে বাবা-মায়ের কাছে এসেছিল। সেই কারণেই তার নিমন্ত্রণ ছিল না, পুলিশ সাহেব জানতেন না যে সে আসবে। একা বাঙলোর মধ্যে বসে ছিল, হঠাৎ পশ্চিমের জানালার পথে রক্তসন্ধ্যার বর্ণচ্ছটার একটা ঝলক ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিল একখানা রঙিন। উত্তরীয়ের মত। এবং গোটা ঘরখানাকেই যেন রঙিন করে দিয়েছিল। একলা বাঙলোর মধ্যে তার যেন একটা নেশা ধরেছিল মনে প্ৰাণে। সে মুক্তকণ্ঠে ওই গানখানি গেয়ে উঠেছিল—
তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর আমার সাধের সাধনা।
****
মম হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে তব চরণ দিয়েছি রাঙিয়া
অয়ি সন্ধ্যাস্বপনবিহারী
মনের উল্লাসে গাইতে গাইতে সে জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়েই অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল। সামনেই বাঙলোর হাতার মধ্যে সিঁড়ির নিচে বাইসিকল ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। সুন্দর, সুপুরুষ, দীর্ঘ-দেহ, গৌরবর্ণ, স্বাস্থ্যবান জ্ঞানেন্দ্রনাথও তখন পূর্ণ যুবক। বেশভূষায় যাকে স্মার্ট বলে তার চেয়েও কিছু বেশি। গলার টাইটি ছিল গাঢ় লাল রঙের, মনে আছে সুরমার। অপ্ৰতিভ হয়ে গান থামিয়ে সরে গিয়েছিল সে জানালার ধার থেকে। এবং আরদালিকে ডেকে প্রশ্ন করেছিল—কে ও? কী চায়?
আরদালি বলেছিল এখানকার থার্ড মন্সব সাহেব। নতুন এসেছে। সাবকে সেলাম দেনে লিয়ে আয়ে থে।
–কতক্ষণ এসেছে? সাহেব নেই বল নি কেন?
–দো মিনিট সে জেয়াদা নেহি। বোলা সাহেব নেহি, চলা যাতে থে, লেকিন বাইস্কিল পাংচার হো গয়া। ওহি লিয়ে দেরি হয়।
বাইসিক্ল পাংচার হয়েছে? হাসি পেয়েছিল সুরমার। বেচারি মুন্সব সাব, এমন সুন্দর স্যুটটি পরে এখন বাইসিক্ল ঠেলতে ঠেলতে চলবেন। বর্ধমানের রাস্তার লাল ধুলো জলে জলে গলে কাদায় পরিণত হয়েছে। মধ্যে মধ্যে খানাখন্দকের ভিতর লাল মিকশ্চার! সুরকি মিকশ্চার! একান্ত কৌতুকভরে সে আবার একবার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছিল।
আজ রেডিওতে ওই গানখানা শুনে রক্তসন্ধ্যার রূপ অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে সুরমা দেবীর মনে।
খ.
জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাঙলোয় ঢুকেই সামনের দেওয়ালের দিকে তাকালেন। ওখানে টাঙানো রয়েছে। তরুণী সুরমার ব্রোমাইড এনলার্জ করা ছবি।
লাবণ্য-ঢলঢল মুখ, মদিরদৃষ্টি দুটি আয়ত চোখ, গলায় মুক্তোর কলারটি সুরমাকে অপরূপ করে তুলেছে। সে-আমলে এত বহুবিচিত্র রঙিন শাড়ির রেওয়াজ ছিল না, পাওয়া যেত না, সুরমার পরনে সাদা জমিতে অল্প-কাজ-করা একখানি ঢাকাই শাড়ি। আর অন্য কোনো রকম শাড়িতে সুরমাকে বোধ করি বেশি সুন্দর দেখাত না। সেদিন জজসাহেবের কুঠিতে দেখেছিলেন শুধু সুরমার মুখ। সিঁড়ির নিচে থেকে তার বেশি দেখতে পান নি। দেখতে চানও নি। রক্তসন্ধ্যার রঙে ঝলমল-করা সে মুখখানার থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরে নি। দেখবার অবকাশও ছিল না। সুরমা জজসাহেবের মেয়ে; কলেজে পড়েন; প্রগতিশীল সমাজের লোক। জ্ঞানেন্দ্রনাথ তখন মাত্র থার্ড মুনসেফ। গ্রাম্য হিন্দু মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মাত্র। তার সমাজের লোকে মুনসেফি পাওয়ার জন্য রত্ন বলে, ভাগ্যবান বলে। কিন্তু সুরমাদের সমাজের কাছে নিতান্তই ঝুটো পাথর এবং মুনসেফিকেও নিতান্তই সৌভাগ্যের সান্ত্বনা বলে মনে করেন তারা। সুরমাকে ঠিক এই বেশে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন তাঁর নিজের বাসায়, কিছুদিন পরে। বোধহয় মাস দেড়েক কি দু মাস পর। তাঁর বাসা ছিল শহরের উকিল-মোক্তার পল্লীর প্রান্তে। বেশ একটি পরিচ্ছন্ন খড়ো বাঙলো দেখে বাসাটি নিয়েছিলেন। তখনও ইলেকট্রিক লাইট হয় নি। বাসের জন্য গরমের দেশে খড়ড়া বাঙলোর চেয়ে আরামপ্রদ আর কোনো ঘর হয় না। সামনে একটুকরো বাগানও ছিল। সেদিন কোর্ট শেষ করে বাইসিক্লে চেপে বাড়ির একটু আগে একটা মোড় ফিরে, বাইসিক্লে-চাপা অবস্থাতেই তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর বাসার দরায় মোটর দাঁড়িয়ে! কার মোটর? পরমুহূর্তে মোটরখানা চিনে তার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। এ যে সেসন্স্ জজের কার! ওই তো পাশে দাঁড়িয়ে জজসাহেবের আরদালি ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে। বাইসিক্ল থেকে বিস্মিত এবং ব্যস্ত হয়ে নেমে আরদালিকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কে এসেছেন?
আরদালি মুনসেফ সাহেবকে সসম্ভ্ৰমে সেলাম করে বলেছিল-মিস্ সাহেব আমি হ্যায় হুজুর।
মিস্ সাহেব? জজসাহেবের সেই কন্যাটি? সেদিন বাঙলোয় তার গানই শুধু শোনেন নি জ্ঞানেন্দ্রনাথ, তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আহ্বানও শুনেছিলেন-আরদালি!
শুধু তাই নয়। এই কলেজে পড়া, অতি-আধুনিকা, বাপের আদরিণী কন্যাটি সম্পর্কে ইতিমধ্যে আরও অনেক কথা তিনি শুনেছেন। ব্যঙ্গ-কবিতা লেখে। বাক্যবাণে পারদর্শিনী। এখানকার নিলাম-ইস্তাহার-সর্বস্ব সাপ্তাহিকে জজসাহেবের মেয়ের ব্যঙ্গ-কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তাও পড়েছেন। আরও একদিন এই মেয়েটিকে দেখেছেন ইতিমধ্যে। সেদিন বাঙলোয় শুধু মুখ দেখেছিলেন; মধ্যে একদিন সব-জজসাহেবের বাড়িতে তার ছোট ছেলের বিয়ে উপলক্ষে প্রীতি-সম্মেলনে মেয়েটিকে জজসাহেবের পাশে বসে থাকতেও দেখেছেন। দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটিকে ভাল লেগেছিল, তেমনি সমও জেগেছিল তার সংযত গাম্ভীর্য দেখে। সেই মেয়ে এসেছেন তার বাড়িতে? কেন? হয়ত প্রগতিশীল রাজকন্যা কোনো সমিতিটমিতির চাঁদার জন্য বা সুমতিকে তার সভ্য করবার জন্য এসে থাকবেন। সুমতি কি–?
আজ সুমতির নাম স্মৃতিপথে উদয় হতেই প্রৌঢ় জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুরমার ছবি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বাঁ দিকের দেওয়ালের দিকে তাকালেন। দেওয়ালটার মাঝখানে কাপড়ের পরদা–ঢাকা একখানা ছবি ঝুলছে।
সুমতির ছবি। সুমতি তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী।
একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। হতভাগিনী সুমতি! জ্ঞানেন্দ্রবাবুর মুখ দিয়ে দুটি আক্ষেপভরা সকাতর ওঃ-ওঃ শব্দ যেন আপনি বেরিয়ে এল। তিনি দ্রুপদে এঘর অতিক্রম করে পোশাকের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।
সুমতির স্মৃতি মর্মান্তিক।
আঃ বলে একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। মর্মান্তিক মৃত্যু সুমতির। শার্টটা খুলছিলেন তিনি, আঙুলের ডগাটা নিজের পিঠের উপর পড়ল। গেঞ্জিটাও খুলে ফেললেন। পিঠের উপরটার চামড়া অসমতল, বন্ধুর। ঘাড় হেঁট করে বুকের দিকে তাকালেন। বুকের উপরেও একটা ক্ষতচিহ্ন। হাত বুলিয়ে দেখলেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বুকের ক্ষতচিহ্নটার প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। বাঁ হাত দিয়ে পিঠের ক্ষতটা অনুভব করছিলেন। গোড়া পিঠটা জুড়ে রয়েছে। ওঃ! এখনও স্পর্শকাতর হয়ে রয়েছে। বিশ বৎসর হয়ে গেল, তবু সারল না। কোট শার্ট গেঞ্জির নিচে ঢাকা থাকে। অতর্কিতে কোনো রকমে চাপ পড়লেই তিনি চমকে ওঠেন। কনকন করে ওঠে। সুমতিকে শেষটায় চিনবার উপায় ছিল না। তিনি শুনেছেন, তবে কল্পনা করতে পারেন। তিনি তখন অজ্ঞান; বোধ করি একবার যেন দেখেছিলেন। বারেকের জন্য জ্ঞান হয়েছিল তার।
পোশাকের ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুমের ভিতর গিয়ে ঢুকলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। চৌকির উপর বসে হাতে মুখে জল দিলেন। সাবানদানি থেকে সাবানটা তুলে নিলেন।
ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই সারা বাথরুমটা একটা লালচে আলোর আভায় লাল হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল; যেন দপ করে জ্বলে উঠেছে কোথাও প্রদীপ্ত আগুনের ছটা! চমকে উঠলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু, হাত থেকে সাবানখানা পড়ে গেল, মুহূর্তের মধ্যে ফিরে তাকালেন পাশের জানালাটার দিকে। ছটাটা ওই দিক থেকেই এসেছে। জানালাটার ঘষা কাচগুলি আগুনের রক্তচ্ছটায় দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। একটা নিদারুণ আতঙ্কে তার চোখ দুটি বিস্তারিত হয়ে উঠল, চিৎকার করে উঠলেন তিনি। একটা ভয়ার্ত আর্তনাদ। ভাষা নেই; শুধু রব।
****
দপ করে আগুন জ্বলে উঠেছে বটে কিন্তু অগ্নিকাণ্ড যাকে বলে তা নয়।
জানালাটার ঠিক ওধারেই খানিকটা, বোধ করি আট-দশ ফুট খোলা জায়গার পরই কুঠির বাবুর্চিখানায় বাবুর্চি ওমলেট ভাজছিল। ওমলেট ভাজবার পাত্রটা সম্ভবত মাত্রাতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। তার উপর ঘি ঢালতেই সেটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে, এবং বিভ্রান্ত পাঁচকের হাত থেকে ঘিয়ের পাত্রটাও পড়ে গেছে। আগুন একটু বেশিই হয়েছিল। তারই ছটা গিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে ঘষা কাচের জানালায়।
তাই দেখেই জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছেন।
ভয়ার্ত চিৎকার করতে করতে খালি গায়ে, খালি পায়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন। সে কী চিৎকার! শুধু ভয়ার্ত একটা ও-ও-ও-শব্দ শুধু। সুরমা দেবী ছুটে এসে তাকে ধরে উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেনকী হল? কী হল! ওগো! ওগো!
থরথর করে কাঁপছিলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। কিন্তু ধীমান পণ্ডিত ব্যক্তি তিনি, দুরন্ত ভয়ের মধ্যেও তাঁর ধীমত্তা প্ৰাণপণে ঝড়ের সঙ্গে বনস্পতি-শীর্ষের মৃত, লড়াই করে অবনমিত অবস্থা থেকে মাথা তুলে দাঁড়াল। পিছন ফিরে বাঙলোর দিকে তাকালেন তিনি। চোখের ভয়ার্ত দৃষ্টির চেহারা বদলাল, প্রশ্নাতুর হয়ে উঠল। বললেন–আগুন। কিন্তু
অর্থাৎ তিনি খুঁজছিলেন, যে-আগুনকে দাউদাউ শিখায় জ্বলে উঠতে দেখলেন তিনি এক মিনিট আগে—সে আগুন কই? কী হল!
সুরমা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—আগুন? কোথায়?
আত্মগতভাবেই জ্ঞানেন্দ্রবাবু প্রশ্ন করলেন-কী হল? অগ্নির সে লেলিহান ছটা যে তিনি দেখেছেন, চোখ যে তার বেঁধে গিয়েছে। পরক্ষণেই ডাকলেনবয়।
বয় এসে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করে বললে—একটুক্ষণ জ্বলেছিল, তারপরই নিতে গিয়েছে।
জ্ঞানবাবু বললেন–এমন অসাবধান কেন? ঘরে আগুন লাগতে পারত!
বয় সবিনয়ে বললে—টিনের চাল–!
–লোকটার নিজের কাপড়চোপড়ে লাগতে পারত। স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন–ওকে জবাব দিয়ে দাও! বলেই হনহন করে বাঙলোর ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। সুরমা দেবী কোনো উত্তর দিলেন না। স্বামীর পিঠজোড়া ক্ষতচিহ্নের দিকে চেয়ে রইলেন। দীর্ঘদিন পূর্বের কথা তাঁর মনে পড়ল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ এবং সুমতি ঘরে আগুন লেগে জ্বলন্ত চাল চাপা পড়েছিলেন। খবর পেয়ে জজসাহেব এবং সুরমা ছুটে গিয়েছিলেন। ঘরে আগুন লেগেছিল রাত্রে। মফঃস্বল শহরের খড়া বাঙলোবাড়ি, শীতকাল, দরজা-জানালা শক্ত করে বন্ধ ছিল। খড়ের চালের আগুন প্রথম খানিকটা বোধহয় বেশ উত্তাপের আরাম দিয়েছিল। যখন ঘুম ভেঙেছিল সুমতি ও জ্ঞানেন্দ্রনাথের, তখন চারিদিক ধরে উঠেছে। দরজা খুলে বের হতে হতে সামনের চালটা খসে নিচে পড়ে যায়। সুমতি, জ্ঞানেন্দ্রবাবু জ্বলন্ত চাল চাপা পড়েন। জ্ঞানেন্দ্রবাবু তার হাত ধরে বের করে আনছিলেন; মাঝখানে সুমতি কাচে পা কেটে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। জ্ঞানেন্দ্রনাথও ছিটকে সামনে পড়ে বুকে পিঠে জ্বলন্ত খড় চাপা পড়েন। সুমতির সর্বাঙ্গ পুড়ে ঝলসে গিয়েছিল। ওঃ, সে কী মর্মান্তিক দৃশ্য! জ্ঞানেন্দ্রনাথ তখন হাসপাতালের ভিতরে বেডের উপর অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে। সুমতির দেহটা কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। তুলে দেখিয়েছিল ডাক্তার।
ওঃ! ওঃ! ওঃ! সুরমা দেবীও চোখ বুজে শিউরে উঠলেন।
গ.
কী মিষ্টি চেহারা কী বীভৎস হয়ে গিয়েছিল! উঃ! সুমতিকে মনে পড়ছে। শ্যাম বৰ্ণ, একপিঠ কালো চুল, বড় বড় দুটি চোখ, একটু মোটাসোটা নরম-নরম গড়ন; মুক্তোর পতির মত সুন্দর দাঁতগুলি, হাসলে সুমতির গালে টোল পড়ত। এবং দুজনের মধ্যে অনির্বচনীয় ভালবাসা ছিল। অফিসার মহলে এ নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। হওয়ারই কথা। ব্রাহ্ম বিলেতফেরত ব্যারিস্টার জজসাহেবের কলেজে-পড়া মেয়ের সামান্য মুনসেফের স্ত্রী গ্রাম্য জমিদার-কন্যা অর্ধশিক্ষিতা সুমতির সঙ্গে এত নিবিড় অন্তরঙ্গতা কিসের? কেউ বলেছিল—কোথায় কোন জেলা স্কুলে সুরমা ও সুমতি একসঙ্গে পড়ত। কেউ বলেছিল সুরমা ও সুমতির পিতৃপক্ষ কোনকালে দার্জিলিং গিয়ে পাশাপাশি ছিলেন, তখন থেকে সখী দুজনে। হঠাৎ এখানে সবজজের বাড়িতে দুজনে দুজনকে চিনে ফেলে, পুরনো সখিত্ব নতুন করে গড়ে তুলছে। কিন্তু সবকিছুর মধ্যেই একটানা-একটা অসঙ্গতি বেরিয়েছেই বেরিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সত্য কথাটা প্রকাশ পেল।
সুমতি ছিল তার নিজের পিসতুতো বোন; জজসাহেব অরবিন্দ চ্যাটার্জি সুমতির মামা। সুমতির মায়ের সহোদর ভাই। কলেজে পড়বার সময় ব্রাহ্ম হয়ে সুরমার মাকে বিবাহ করেছিলেন। বাপ ত্যাজ্যপুত্র করেন। ছেলের নাম মুখে আনতে বাড়িতে বারণ ছিল। কোনো সম্পর্কও ছিল না দুই পক্ষের মধ্যে। অরবিন্দবাবু বিলেত গেলেন, ব্যারিস্টার হয়ে এসে বিচার বিভাগে চাকরি নিয়ে সম্পূর্ণরূপে আলাদা মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে খবর না রাখাই স্বাভাবিক। পিতৃপক্ষও রাখতেন না। রাখেন নি। বরং এই ছেলের নাম তারা সযত্নে মুছে দিয়েছিলেন সেকালের সামাজিক কলঙ্ক ও লজ্জার বিচিত্র কারণে। এ-পরিচয় প্রকাশ হলে সেকালে সামাজিক আদান-প্ৰদান কঠিন হয়ে পড়ত। সুমতি তার মায়ের কাছে মামার নাম শুনেছিল। শুনেছিল, তিনি ব্রাহ্ম হয়ে বাড়ি থেকে চলে গেছেন, এই পর্যন্ত। তার মা বিয়ের সময় বার বার করে বলে দিয়েছিলেন, মামার কথা যেন গল্প করিস নে। কী জানি কে কীভাবে নেবে। সুরমা অবশ্য গল্প শুনেছিল, তার বাবার কাছে। ইদানীং জজসাহেব অরবিন্দ চ্যাটার্জি একটু ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে রাত্রিকালে ব্র্যান্ডি পান করে মায়ের জন্য কাঁদতেন। বলতেন, মাই মাদার ওয়াজ এ গডেস! আর কী সুন্দর তিনি ছিলেন। সাক্ষাৎ মাতৃদেবতা! যেন সাক্ষাৎ আমার বাংলাদেশ! শ্যামবর্ণ, একপিঠ ঘন কালো চুল, বড় বড় চোখ, মুখে মিষ্টি হাসি, নরম-নরম গড়ন—আহা-হা!
সুমতির চেহারা ছিল ঠিক তার মত, নিজের মায়ের মত। সেই দেখেই প্রকাশ পেল সেই পরিচয়। চিনলেন চ্যাটার্জি সাহেব নিজেই। বর্ধমানে সুমতিরা মাসদুয়েক এসেছে তখন। সবজজের বাড়িতে ছোট ছেলের বিবাহে সামাজিক অনুষ্ঠান-বউভাতের প্রীতিভোজন। সুরমা, সুরমার মা এবং বাবা বাইরের আসরে বসে ছিলেন, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, পুলিশ সাহেব, ডাক্তার সাহেবরাও সস্ত্রীক বসে ছিলেন, পাশে একটু তফাত রেখে বসেছিলেন ডেপুটি, সবডেপুটি, মুনসেফের দল। তাদের গৃহিণীদের আসর হয়েছিল ভিতরে; এই আসরের মাঝখানের পথ দিয়েই তারা ভিতরে যাচ্ছিলেন। সুমতিও চলে গিয়েছিল। সুরমার বাবা কথা বলছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। তিনি অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন, দৃষ্টিতে ফুটে উঠল অপরিসীম বিস্ময়। পরক্ষণেই অবশ্য তিনি আত্মসংবরণ করে আবার কথা বলতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু সেই ক্ষণিকের বিস্ময়-বিমূঢ়তা লক্ষ্য করেছিলেন অনেকেই। সুরমার মারও চোখ এড়ায় নি। কিছুক্ষণ পর যে কথা তিনি বলছিলেন সেই কথাটা শেষ হতেই আবার যেন গভীর অন্যমনস্কতায় ড়ুবে গেলেন। সুরমার মা আর আত্মসংবরণ করতে পারেন নি, মৃদুস্বরে প্রশ্ন করেছিলেন-কী ব্যাপার বল তো?
—অ্যাঁ—? চমকে উঠেছিলেন সুরমার বাবা।
স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হঠাৎ কী হল তোমার? তখন এমনভাবে চমকে উঠলে? আবারও যেন কেমন তন্ময় হয়ে ভাবছ!
–কতকাল পর হঠাৎ যেন মাকে দেখলাম। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চ্যাটার্জি সাহেব কথাটা বলেছিলেন।–অবিকল আমার মা। অবিকল! তফাত, এ মেয়েটি একটু মডার্ন।
—কে? কী বলছ তুমি?
–লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরে একটি মেয়ে তখন বাড়ির ভিতর গেল, দেখেছ? শ্যামবর্ণ, বড় বড় চোখ, কপালে সিঁদুরের টিপটা একটু বড়, গোঁড়া হিন্দুর ঘরে যেমন পরে। অবিকল আমার মা! ছেলেবেলায় যেমন দেখতাম।
এর উত্তরে সুরমার মা কী বলবেন, চুপ করেই ছিলেন। চ্যাটার্জি সাহেবও কয়েক মিনিটের জন্য চুপ করে গিয়েছিলেন। তারপর হঠাৎ একটু সামনে ঝুঁকে মৃদুস্বরে বলেছিলেন—একটু খোঁজ নিতে পার? কে, কে এ মেয়েটি? সহজেই বের করতে পারবে, লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরে এসেছে, ভারি নরম চেহারা, কচি পাতার মত শ্যামবর্ণ, বড় বড় চোখ, কপালে সিঁদুরের টিপটা বড়। সহজেই চেনা যাবে। দেখ না? দেখবে?
অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেন নি সুরমার মা। এবং সহজেই সুমতিকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। ফিরে এসে বলেছিলেন—এখানে নতুন মুনসেফ এসেছেন, মিস্টার ঘোষাল, তাঁর স্ত্রী।
—থার্ড মুনসেফের স্ত্রী? একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, অবিকল আমার মা। মেয়েটির সিঁথির ঠিক মুখে, এই আমার এই কপালে যেমন একটা চুলের ঘূর্ণি আছে, তেমনি একটা ঘূর্ণি আছে। আমার মায়ের ছিল।
সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে চ্যাটার্জি সাহেব মদ্যপান করে মায়ের জন্য হাউহাউ করে কেঁদেছিলেন। নিশ্চয় আমার মা! এ জন্মে
সুরমার মা বলেছিলেন পুনর্জন্মঃ বোলা না, লোকে শুনলে হাসবে।
হঠাৎ চ্যাটার্জি সাহেব বলেছিলেন তা না হলে এমন মিল কী করে হল? ইয়েস। হতে পারে। সুরো, মামি, তুমি একবার কাল যাবে এই মেয়ের কাছে? তুমি স্বচ্ছন্দে যেতে পার। জেনে। এসো, ওর বাপের নাম কী, ঠাকুরদাদার নাম কী, কোথায় বাড়ি?
সুরমার মার খুব মত ছিল না, কিন্তু প্রৌঢ় বাপের এই ছেলেমানুষের মত মা-মা করা দেখে সুরমা বেদনা অনুভব করেছিল, না-গিয়ে পারে নি।
সুমতি অবাক এবং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল প্রথমটা। খোদ জজসাহেবের মেয়ে এসেছেন, কলেজ-পড়া আধুনিকা মেয়ে! যে-মেয়ে সমাজে সভায় তাদের থেকে অনেক তফাতে এবং উঁচুতে বসে, সে নিজে এসেছে তাদের বাড়ি।
সুরমা গোপন করে নি। সে হেসে বলেছিল—আপনি নাকি অবিকল আমার ঠাকুরমার মত দেখতে। এমনকি আপনার সিঁথির সামনের চুলের এই ঘূর্ণিটা পর্যন্ত। আমার বাবার মধ্যে আবার একটি ইন্টারন্যাল চাইল্ড, মানে চিরন্তন খোকা আছে। মায়ের নাম করে প্রায় কদেন। কাল সে কী হাউহাউ করে কান্না। তাই এসেছি, আপনার সঙ্গে ঠাকুমা পাতাতে।
সুমতি স্থির দৃষ্টিতে সুরমার দিকে তাকিয়ে ছিল কিছুক্ষণ।
সুরমা হেসে বলেছিল—অবাক হচ্ছেন? অবাক হবার কথাই বটে। কিন্তু আপনার বাপের বাড়ি কোথায়, বলুন তো? আপনি কি অবিকল আপনার ঠাকুরমার মত দেখতে?
সুমতি বলেছিল–না। তবে আমার দিদিমার সঙ্গে আমার চেহারার খুব মিল। মা বলেন–অবিকল।
এর উত্তরে আসল সম্পর্ক আবিষ্কৃত হতে বিলম্ব হয় নি। সুমতি ছিল অবিকল তার দিদিমার মত দেখতে। দিদিমা তার জন্মের পরও কয়েক বছর বেঁচে ছিলেন, নইলে এই ঘটনার পর অন্তত লোকে বলত, তিনিই ফিরে এসে সুমতি হয়ে জন্মেছেন, এবং ধর্মান্তরগ্রহণ-করা অরবিন্দ চ্যাটার্জি জজসাহেবের সঙ্গে এই দেখা হওয়াটি একটি বিচিত্র ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত হত; লোকে বলত জজসাহেব-ছেলের সমাদর পাবার জন্যই ফিরে এসেছেন তিনি। এসব কথা সুমতি বলে নি, বলেছিল সুরমা। সুমতি খুব হেসেছিল, খুব হাসতে পারত সে। ঠিক এই সময়েই বাসার বাইরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। দরজায় জজসাহেবের আরদালি এবং গাড়ি দেখে কী করা উচিত ভেবে না পেয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন নিজ বাসভূমে পরবাসীর মত। সারাটা দিন মুনসেফ কোর্টে রেন্ট-সুট আর মনি-সুটের জট ছাড়িয়ে, কলম পিষে, শ্ৰান্ত দেহ ও ক্লান্ত মস্তিষ্ক নিয়ে মাইল তিনেক বাইসিক্ল ঠেঙিয়ে বাড়ি ফিরে দেখেছিলেন গৃহদ্বার একরকম রুদ্ধ, খোলা থাকলেও প্রবেশাধিকার নেই। বাইরের ঘরে সুমতির সঙ্গে কথা বলতে বলতে সুরমাই জ্ঞানেন্দ্রনাথের এই ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা দেখতে পেয়েছিল এবং প্রচুর কৌতুকে বয়স-ও স্বভাব-ধর্মে কৌতুকময়ী হয়ে উঠেছিল।
ঘ.
বয়!
সুরমা চমকে উঠলেন। স্বামী বাঙলোর মধ্যে ফিরে যাওয়ার পর থেকেই সুরমা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই ছিলেন। স্বামীর ভয়ার্ত অবস্থা এবং পিঠের বুকের ক্ষতচিহ্ন দেখে অতীত কথাগুলি মনে পড়ে গিয়েছিল। সুমতির ওই মর্মান্তিক মৃত্যুস্মৃতির বেদনার মধ্যে তাঁর নিজের তরুণ জীবনের পূর্বরাগের রঙিন দিনগুলির প্রতিচ্ছবি ফুটে রয়েছে। একরাশি কালে কয়লার উপর কয়েকটি মরা প্রজাপতির মত।
স্বামীর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন তিনি। পাজামা, পাঞ্জাবি পরে রবারের স্লিপার পায়ে কখন যে উনি এসেছেন তা তিনি জানতে পারেন নি। বাঙলোর দিকে পিছন ফিরে রক্তসন্ধ্যার দিকেই তিনি তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চেয়ার টেনে বসে পড়লেন, তাঁর চোখ-মুখ এখনও যেন কেমন থমথম করছে। তাকে দেখে সুরমা শঙ্কিত হলেন, মনে হল ক্লান্ত বড় তিনি। সুরমা এগিয়ে এসে মিঃ ঘোষালের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে তার কাঁধের উপর নিজের হাত দুখানি গাঢ় স্নেহের সঙ্গে রেখে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ডাক্তারকে একবার খবর দেব?
—ডাক্তার? একটু চকিত হয়ে উঠলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ–কেন?
—তুমি অত্যন্ত আপসেট হয়ে গেছ। নিজে বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছ না। এখনও পর্যন্ত
পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে স্ত্রীর হাতখানি ধরে জ্ঞানেন্দ্রবাবু বললেন– না। ঠিক আছি আমি।
–না। তুমি তোমার আজকের অবস্থা ঠিক বুঝতে পারছ না। আগুন নিয়ে তোমার ভয় আছে। একটুতেই চমকে ওঠ, কিন্তু এমন তো হয় না। তোমার বিশ্রাম নেওয়া উচিত। আর এভাবে পরিশ্রম–
বাধা দিয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ হেসে বললেন–নাঃ, আমি ঠিক আছি। আজকের ঘটনাটা একটু অস্বাভাবিক।
—আগুনটা কি খুব বেশি জ্বলে উঠেছিল?
—উঃ, সে তুমি কল্পনা করতে পারবে না। বাথরুমের জানালার কাচের মধ্যে দিয়ে রিফ্লেকশ্যনে ঘরটা একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছিল! অবশ্য আমিও একটু-একটু, কী বলব, dreamy, স্বধাতুর ছিলাম। ঠিক শক্তমাটির উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম না। চমকে একটু বেশি উঠেছি।
–মানে?
–বলছি। সামনে এস, পিছনে থাকলে কি কথা বলা হয়?
সুরমা সামনের চেয়ারে এসে বসলেন। এঁদের দুজনের পিছনে বাবুর্চি চায়ের ট্রে এবং খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছিল, সাহেব এবং মেমসাহেবের এই হাত-ধরাধরি অবস্থার মধ্যে সামনে আসতে পারছিল না, সে এইবার সুযোগ পেয়ে এগিয়ে এসে টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জামগুলি নামিয়ে দিল।
সুরমা বললেন–যাও তুমি, আমি ঠিক করে নিচ্ছি সব।
জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন–ইয়ে দুফে তুমহারা কসুর মাফ কিয়া গয়া, লেকিন দুসরা দফে নেহি হোগা। হুঁশিয়ার হোনা চাহিয়ে। তুমহারা সুগামে আগ লাগা যাতা তো কেয়া হোতা? আঁঃ?
সেলাম করে বাবুর্চি চলে গেল।
জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন–আজকের ঘটনাগুলো আগাগোড়াই আমাকে একটুকী বলব–একটু ভাবপ্রবণ করে তুলেছিল। এখানে এসেই তোমাকে দেখলাম, রক্তসন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছ। সেই পুরনো কবি-কবি ভাব! দীর্ঘদিন পর বললে কবিতা শোনাব। পুরনো শুকনো মাটিতে নতুন বর্ষার জল পড়লে সেও খানিকটা সরস হয়ে ওঠে। আমার মনটাও ঠিক তা-ই হয়ে উঠেছিল। মনে পড়ে গেল একসঙ্গে অনেক কথা। রক্তসন্ধ্যার দিন বর্ধমান জজকুঠিতে তোমাকে দেখার কথা। ঘরে ঢুকেই ওদিকের দরজার মাথায় তোমার সেই ছবিটা দ্যাট রিমাইন্ডেড মিসেই প্রথম দিনের পরিচয় হওয়ার কথা মনে পড়িয়ে দিলে। স্বাভাবিকভাবে মনে পড়ল সুমতিকে। সেই হতভাগিনীর কথা ভাবতে ভাবতেই বাথরুমে ঢুকেছিলাম। গেঞ্জি খুলতে গিয়ে রোজই পিঠের পোড়া চামড়ায় হাত পড়ে। আজও পড়েছিল। কিন্তু আজ মনে পড়ছিল সেই আগুনের কথা। ঠিক মনের এই ভাববিহ্বল অবস্থার মধ্যে হঠাৎ বাইরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আমার মনে হল আমাকে ঘিরে আগুনটা জ্বলে উঠল।
চায়ের কাপ এবং খাবারের প্লেট এগিয়ে দিলেন সুরমা। মৃদুস্বরে বললেন–তবু বলব আজ ব্যাপারটা যেন কেমন। আগুনকে ভয় তোমার স্বাভাবিক। কিন্তু
আগুনকে ভয় তাঁর স্বাভাবিক, অতর্কিত আগুন দেখলে চকিত হয়ে ওঠেন, খড়ের ঘরে শুতে পারেন না, রাত্রে বালিশের তলায় দেশলাই পর্যন্ত রাখেন না। সিগারেট পর্যন্ত খান না তিনি। বাড়ির মধ্যে পেট্রোল-কেরোসিনের টিন রাখেন না। কখনও খোলা জায়গায় ফায়ারওয়ার্ক দেখতে যান না। কিন্তু আজ যেন ভয়ে কেমন হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।
চায়ের কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে হেসে জ্ঞানেন্দ্রবাবু বোধ করি সমস্ত ঘটনাকে হালকা করে দেবার অভিপ্ৰায়েই হেসে সুরমার দিকে তৰ্জনী বাড়িয়ে দেখিয়ে বললেন–সব কিছু না। তুমি! সমস্তটার জন্য রেসপন্সিবল তুমি।
—আমি?
–হ্যাঁ, তুমি। কবি হলে বলতাম, এলোচুলে বহে এনেছ কি মোহে সেদিনের পরিমল! বললাম তো—আজকের তোমাকে দেখে প্রথম দিনের দেখা তোমাকে মনে পড়ে গেল। এবং সব গোলমাল করে দিলে! জজসাহেবের কলেজে-পড়া তরুণী মেয়েটি সেদিন যেমন মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল, আজও মাথাটা সেইরকম ঘুরে গেল!
হেসে ফেললেন সুরমা দেবী।
জ্ঞানেন্দ্রবাবু বললেন–ওঃ সেদিন যা সম্বোধনটা করেছিলে! ভ্যাবাকান্ত।
এবার সশব্দে হেসে উঠলেন সুরমা। বললেন–বলবে না? নিজের বাড়ির দোরে এসে বাড়িতে জজসাহেবের কলেজে-পড়া মেয়ে এসেছে শুনে একজন মডার্ন তরুণ যুবক পেটজ্বালা-করা ক্ষিদে নিয়ে মুখ চুন করে ফিরে যাচ্ছেন। কী বলতে হয় এতে তুমি বল না? গাইয়া। কোথাকার!
সেদিন বাড়ির দোর থেকে মুখ চুন করে সত্যিই ফিরে যাচ্ছিলেন থার্ড মুনসেফ জ্ঞানেন্দ্রনাথ। কী করবেন? জজসাহেবের কলেজে-পড়া মেয়ে, কোথায় কী খুঁত ধরে মেজাজ খারাপ করবে, কে জানে। তার চেয়ে ফিরে যাওয়াই ভাল। ঠিক এই সময়েই সামনের ঘরের পরদা সরিয়ে সুরমাই আবির্ভূত হয়েছিল; জ্ঞানেন্দ্রনাথের বিব্রত অবস্থা দেখে অন্তরে অন্তরে কৌতুক তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সেদিন তখন সে জজসাহেবের মেয়ে এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুনসেফ নয়; আত্মীয়তার মাধুর্য, পদমর্যাদার পার্থক্যের রূঢ় ভুলিয়ে দিয়েছে, বরং খানিকটা মোহের সৃষ্টি করেছিল এমন বিচিত্র ক্ষেত্রে। তাই সুমতির আগে সে-ই পরদা সরিয়ে মৃদু হেসে। বলেছিল—আসুন মিস্টার ঘোষাল; বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন যে! আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি। আলাপ করতে এসেছি।
সুমতি সুরমার পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হেসে বলেছিল—এস। সুরমা আমার মামাতো বোন। ওর বাবা আমার সেই মামা, যিনি বাড়ি থেকে চলে গিয়ে–
বাকিটা উহ্যই রেখেছিল সুমতি।
—কী আশ্চর্য!
একমাত্র ওই কথাটিই সেদিন খুঁজে পেয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ।
সুরমা বলেছিল-টুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশ্যন।
জ্ঞানেন্দ্রনাথ কিন্তু তখনও বসেন নি। বসতে সাহসই বোধ করি হয় নি অথবা অবস্থাটা ঠিক স্বাভাবিক বলে বিশ্বাস হচ্ছিল না। সুরমাই বলেছিল কিন্তু আপনি বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন যে? আমি তো আপনাদের আত্মীয়া। আপনজন!
বেশ ভঙ্গি করে একটু ঘাড় দুলিয়ে চোখ দুটি বড় করে বক্ৰ হেসে সুমতি বলেছিল—অতিমিষ্টি আপনজন, শালী।
সুরমাতে গ্রাম্যতার ছোঁয়াচ লেগে গিয়েছিল মুহূর্তে। সভ্যতাকে বজায় রেখে জ্ঞানেন্দ্রনাথের মত সুপুরুষ অপ্রতিভ বিব্রত তরুণটিকে বিদ্রুপ না করে তৃপ্তি হচ্ছিল না। এই গ্রাম্য ছোঁয়াচের সুযোগ নিয়ে উচ্ছল হয়ে সে বলে উঠেছিলহলে কী হবে, ভগ্নীপতিটি আমার একেবারে ভ্যাবাকান্ত।
সুমতি হেসে উঠেছিল।
পরক্ষণেই নিজেকে সংশোধন করবার অভিপ্ৰায়েই সুরমা বলেছিল মাফ করবেন। রাগ করবেন না যেন।
সুমতি আবারও তেমনি ধারায় ঘাড় দুলিয়ে বলেছিলশালীতে ওর চেয়েও খারাপ ঠাট্টা করে। এ আবার লেখাপড়া-জানা আধুনিকা শালী; এ ঠাট্টা ভেঁাতা নয়, চোখা।
এতক্ষণে জ্ঞানেন্দ্রনাথ একটা ভাল কথা খুঁজে পেয়েছিলেন, বলেছিলেন শ্যালিকার ঠাট্টা খারাপ হলেও খারাপ লাগে না, চোখা হলেও গায়ে বেঁধে না। মহাভারতে অর্জুনের প্রণাম-বাণ। চুম্বন-বাণের কথা পড়েছ তো? বাণ–একেবারে শানানো ঝকঝকে লোহার ফলা-বসানো তীর-সে-তীর এসে পায়ে লুটিয়ে পড়ত, কিংবা কপালে এসে মিষ্টি ছোঁয়া দিয়ে পড়ে যেত। শ্যালিকার ঠাট্টা তাই। ওদের কথাগুলো অন্যের কাছে শানানো বিষানো মনে হলেও ভগ্নীপতিদের কানের কাছে পুষ্পবাণ হয়ে ওঠে। তার উপর ওঁর মত শ্যালিকা।
সুমতি চা করতে করতে মুহূর্তে মাথা তুলে তাদের দিকে তাকিয়েছিল। কুঞ্চিত দুটি জ্বর নিচে সে-দৃষ্টি ছিল তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। বলেছিল—কী কথার শ্রী তোমার! ও তোমাকে পুষ্পবাণ মারতে যাবে কেন? পুষ্পবাণ কাকে বলে? কী মনে করবে সুরমা?
জ্ঞানেন্দ্রনাথ সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিলেন, ঘরের পরিমণ্ডল অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল।
ঙ.
কথাটা দুজনেরই মনে পড়ে গেল। অতীত কথার সরস স্মৃতি স্মরণ করে যে-আনন্দমুখর সন্ধ্যার আকাশে তারা ফোটার মত ফুটে ফুটে উঠছিল, তার উপর একখানা মেঘ নেমে এল। দুজনেই প্রায় একসঙ্গে চুপ করে গেলেন। একটু পর সুরমা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন আর একটু চা নেবে না?
–না।
স্থিরদৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চেয়ে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। না বলেই তিনি উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে। পিছনের দিকে হাত দুটি মুড়ে পায়চারি করতে লাগলেন। হাতার ওপাশে একটা রাখাল একটা গরুকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওঃ! সুমতি তাকে ওর চেয়েও নিষ্ঠুর তাড়নায় তাড়িত করেছে। ওঃ! গরু-মহিষের দালালরা ডগায় উঁচ বা আলপিন-গোঁজা লাঠির খোঁচায় যেমন করে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় তেমনিভাবে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। সে কী নিষ্ঠুর যন্ত্রণা! যে-যন্ত্রণায় জীবনের সমস্ত বিশ্বাস তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন ঈশ্বরে বিশ্বাস, ধর্মে বিশ্বাস, সব বিশ্বাস। ঈশ্বরের নামে শপথ করেছেন তিনি সুমতির কাছে, ধর্মের নামে শপথ করেছেন। সুমতি মানে নি। দিনের মাথায় দু-তিন বার বলত বল, ভগবানের দিব্যি করে বল! বল, ধর্মের মুখ চেয়ে বল!
তিনি বলেছেন। তার শপথ নিয়ে বললে বলেছে—আমি মরলে তোমার কী আসে যায়? সে তো ভালই হবে!
ওই প্রথম দিন থেকেই সন্দেহ করেছিল সুমতি। সে বার বার বলেছে—ওইওই এক কথাতেই আমি বুঝেছিলাম। সে-ই প্রথম দিন। তার চোখ দুটো জ্বলন্ত। প্রথম দিন রহস্যের আবরণ দিয়ে যে কথাগুলি বলেছিল তার প্রতিটির মধ্যে এ সন্দেহের আভাস ছিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুরমা দুজনের একজনও সেটা ধরতে পারেন নি সেদিন।
অরবিন্দ চ্যাটার্জির মত উদার লোককেও সে কটু কথা বলত। নিজের মায়ের সঙ্গে নিবিড় সাদৃশ্যের জন্য চ্যাটার্জি সাহেবের স্নেহের আর পরিসীমা ছিল না। সুমতিকে দিয়েথুয়ে তার আর আশ মিটত না। সুমতির স্বামী বলে জ্ঞানেন্দ্রনাথের ওপরেও ছিল তার গভীর স্নেহ। সে-স্নেহ তাঁর গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছিল জ্ঞানেন্দ্রনাথের বুদ্ধিদীপ্ত অন্তরের স্পর্শে, জ্ঞানেন্দ্রনাথের উদার মন এবং প্রসন্ন মুখশ্রীর আকর্ষণে। তিনি ওঁকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। সুমতি তার কাছে ঘেঁষতে চাইত না; অরবিন্দুবাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথকে কাছে টেনে ওঁরই হাত দিয়ে সুমতিকে স্নেহের অজস্র সম্ভার পাঠাতে চাইতেন। ওঁর জীবনের উন্নতির পথ তিনিই করে দিয়েছিলেন। রায় লেখার পদ্ধতি, বিচারের সিদ্ধান্তে উপনীত হবার কৌশল—তিনিই ওঁকে শিখিয়েছিলেন। এসব কিছুই কিন্তু সহ্য হত না সুমতির। তাঁর পাঠানো কোনো জিনিস জ্ঞানেন্দ্রনাথ নিয়ে এলে তা ফেরত অবশ্য পাঠাত না সুমতি, কিন্তু তা নিজে হাতে গ্রহণ করত না। বলত—এইখানে রেখে দাও। কী বলব দেওয়াকে। আর কী বলব দিদিমার চেহারার সঙ্গে আমার আদকে। কী বলব জজসাহেবের বুড়ো বয়সে উথলে-ওঠা ভক্তিকে। গরু মেরে জুতো দান! সেই দান আমার নিতে হচ্ছে।
রায় লেখা বা বিচার-পদ্ধতি শেখানো নিয়ে বলত—মুখে ছাই বিচার-শেখানোর মুখে। যে একটা মেয়ের জন্যে ধর্ম ছাড়তে পারে, সে তো অধার্মিক। যে অধার্মিক, সে বিচার করবে কী? ধর্ম নইলে বিচার হয়? আর সেই লোকের কাছে বিচার শেখা!
থাক। সুমতির কথা থাক! সুমতির ছবি দেওয়ালে টাঙানো থেকেও পরদাঢকা থাকে। অরবিন্দবাবু বলতেন, সুমতির কথা নিয়ে বলতেন—কী করবে? সহ্য কর। ভালবাস ওকে। Love is God, God is Love.
চ্যাটার্জিসাহেব বলতেন ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি নে। ব্ৰহ্ম-ব্ৰহ্ম ওসবও না। আমি একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম, সে ব্রাহ্ম-ঘরের মেয়ে, সেইজন্য আমি ব্রাহ্ম হয়েছি। তবে ঈশ্বরত্বের কল্পনাতে আমি বিশ্বাস করি, সেখানে পৌঁছুতে চেষ্টা করি। জ্ঞানেন্দ্র, সব মানুষ করে, সব মানুষ। ওই ঈশ্বরত্ব। একটি পবিত্র একটি মহিমময় মানুষের মানসিক সত্তায় তার প্রকাশ!
সুমতির ক্ষুদ্রতা, তার ভালবাসার জন্য ধর্মান্তর গ্রহণের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থেকে মানুষটি কখন চলে আসতেন সর্বজনীন জীবনদর্শনের মহিমময় প্রাঙ্গণে, মুখের সকল বিষণ্ণতা মুছে যেত, এই রক্তসন্ধ্যার আভার মত একটি প্রদীপ্ত প্রসন্ন প্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত মুখখানি। দূর-দিগন্তে দৃষ্টি রেখে মানসলোক থেকে তিনি কথা বলতেন—এখন আমার উপলব্ধি হচ্ছে ঈশ্বরত্বই নিজেকে প্রকাশ করছে মানব-চৈতন্যের মধ্য দিয়ে। God নন, Godliness, yes Godliness, yes; বলতে বলতে মুখখানি স্মিত হাস্যরেখায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।
তখন ভারতবর্ষে গান্ধীযুগ আরম্ভ হয়েছে। ১৯৩০ সনের অব্যবহিত পূর্বে। বলেছিলেন গান্ধীর মধ্যে তার আভাস পাচ্ছি। বুদ্ধের মধ্যে তা প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যে তার ছটা আছে। ওখানে বুদ্ধি দিয়ে পৌঁছুতে পারি; প্রাণ দিয়ে, নিজের শ্রদ্ধা দিয়ে পারি নে। পারি নে। মদ না খেয়ে যে আমি থাকতে পারি নে। আরও অনেক কিছু দুর্বলতা আমার আছে। কিন্তু অন্যের প্রতি অন্যায় আমি করি নে। করব না। ওইটেই প্রথম শিক্ষা। বিচার বিভাগে আমি ওটা প্র্যাকটিসের সৌভাগ্য পেয়েছি। বাঙলায় ওটাকে কী বলব? অনুশীলন? হ্যাঁ তাই। রায় লিখবার সময় আমি সেইরকম রায় লিখতে চেষ্টা করি, লিখি, যাকে বলা যায় ধর্মের বিচার। ডিভাইন জাস্টিস।
ডিভাইন জাস্টিস কথাটা তারই কথা।
–হুজুর!
–চকিত হয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ফিরে তাকালেন। বেয়ারা ডাকছে।
–এদিকে কাল রাত্রে একটা সাপ বেরিয়েছে হুজুর। একটু থেমে আবার বললে, তাকে বোধ করি মনে করিয়ে দিলে—অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।
মুখ তুলে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ।
সন্ধে হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, আবার আকাশে মেঘ দেখা দিয়ে ছ। দূরে দিথলয়ে গ্রামের বনরেখার চিহ্নমাত্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে অন্ধকারে, প্রান্তর ব্যাপ্ত করে ক্রমশ গাঢ় হয়ে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। বাঙলোর দিকে চাইলেন, আলো জ্বলেছে সেখানে। সুরমাও বাগানে নেই, সে কখন উঠে বাঙলোর ভিতরে চলে গিয়েছে। নিঃশব্দেই চলে গিয়েছে।
সুরমা ঘরের জানালার সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন অতীত-কথা। সুমতির কথা। আশ্চর্য সুমতি। যত মধু তত কটু। যত কোমল তত উগ্ৰ তীব্ৰ। যত অমৃত তত বিষ। অমৃত তার ভাগ্যে জোটে নি, সে পেয়েছিল বিষ। সে বিষ আগুন হয়ে জ্বলেছিল। সুমতির পুড়ে মরার কথা মনে পড়লেই সুরমার মনে হয়, হতভাগিনীর নিজের হাতে জ্বালানো সন্দেহের আগুনে সে নিজেই পুড়ে মরেছে। ওটা যেন তার জীবনের বিচিত্র অমোঘ পরিণাম। প্রথম দিন থেকেই সুমতি তাকে সন্দেহ করেছিল। কৌতুক অনুভব করেছিল সুরমা। ভেবেছিল জ্ঞানেন্দ্রনাথকে সে ভালবেসেছে বা ভালবাসবেই। ভালবাসা হয়ত অন্ধ। ভালবাসায়, কাকে ভালবাসছি, কেন ভালবাসছি, এ প্রশ্নই জাগে না। তবু ইউরোপে-শিক্ষিত জজসাহেব বাপের মেয়ে সে; আবাল্য সেই শিক্ষায় শিক্ষিত, বি-এ পড়ছে তখন, তার এটুকু বোধ ছিল যে, বিবাহিত, গোঁড়া হিন্দুঘরের ছেলে, পদবিতে মুনসেফের প্রেমে পড়ার চেয়ে হাস্যকর নির্বুদ্ধিতা অন্তত তার পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। মনে মনে আজও রাগ হয়, সুমতির মত হিন্দুঘরের অর্ধশিক্ষিত মেয়েরা ভাবে যে, তাদের অর্থাৎ বিলেত-ফেরত সমাজের মেয়েদের সতীত্বের বালাই নেই, তারা স্বাধীনভাবে প্রেমের খেলা খেলে বেড়ায় প্রজাপতির মত। জ্ঞানেন্দ্রনাথ শুধু সুমতির বর বলেই সে তার সঙ্গে হাস্যকৌতুকের সঙ্গে কথা বলেছিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুপুরুষ, বিদ্বান, কিন্তু তার দিকে সপ্ৰেম দৃষ্টিপাতের কথা তার মনের মধ্যে স্বপ্নেও জাগে নি। সুমতির বর, লোকটি ভাল, বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিল। সুমতি হতভাগিনীই অপবাদ দিয়ে তার জেদ জাগিয়ে দিলে; সেই জেদের বশে সমে দৃষ্টির অভিনয় করতে গিয়ে জড়িয়ে পড়ল সে। সুমতি সুরমাকে যেন ঠেলে নিয়ে গিয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথের গায়ের উপর ফেলে দিলে।
সুমতির সন্দেহ এবং ঈর্ষা দেখে সে জ্ঞানেন্দ্রনাথকে নিয়ে খেলা খেলতে গিয়েছিল; সুমতিকে দেখিয়ে সে জ্ঞানবাবুর সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশার অভিনয় করতে গিয়েছিল। সুমতি আরও জ্বলেছিল। বেচারা থার্ড মুনসেফ একদিকে হয়েছিল বিহ্বল অন্যদিকে হয়েছিল নিদারুণভাবে বিব্রত। সুরমার কৌতুকোচ্ছলতার আর অবধি ছিল না; তারুণ্যের উল্লাস প্রশ্রয় পেয়ে বন্য হয়ে উঠেছিল। প্রশ্রয়টা এই আত্মীয়তার। ছুটির পর কলকাতায় ফিরে গিয়ে সে কবিতার চিঠি লিখেছিল জ্ঞানবাবুকে। ইচ্ছে করেই লিখেছিল। সুমতিকে জ্বালাবার জন্য। তার বাবাই শুধু সুমতিকে ভালবাসতেন না, সেও তাকে ভালবেসেছিল। অনুগ্রহের সঙ্গে স্নেহ মিশিয়ে। যে বস্তু, সে-বস্তুর দাতা হওয়ার মত তৃপ্তি আর কিছুতে নেই। পরম স্নেহের ছোট শিশুকে। রাগিয়ে যেমন ভাল লাগে তেমনি ভাল লাগত সুমতিকে জ্বালাতন করতে। বছর দেড়েকের বড়ই ছিল সুমতি, কিন্তু মনের গঠনে বুদ্ধিতে আচরণে সুরমাই ছিল বড়। তার সঙ্গে এই ভ্যাবাকান্ত হিন্দু জামাইবাবুটিকে বিদ্রুপ করে সে এক অনাদিত কৌতুকের আনন্দ অনুভব করত। প্রথম কবিতা তার আজও মনে আছে। সুমতির পত্রেই লিখেছিল—জামাইবাবুকে বলিস–
সুমতি তোমার পত্নী, দুৰ্ম্মতি শ্যালিকা
টোবাকো পাইপ আমি, সুমতি কলিকা
পবিত্র হ্রকোর, তাহে নাই নিকোটিন।
সুমতি গরদ ধুতি, আমি টাই-পিন।
পিনের স্বধর্ম ঘেঁচা, নিকোটিনে কাশি;
ধন্যবাদ, সহিয়াছ মুখে মেখে হাসি।
উত্তরে সুমতির পত্রের নিচে দু ছত্ৰ কবিতাই এসেছিল।
ধন্যবাদে কাজ নাই অন্যবাদে সাধ
অর্থাৎ মার্জনা দেবী, হলে অপরাধ।
সুরমা কবিতা দু লাইন পড়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করেছিল, ঠোঁটে বিচিত্ৰ হাসি ফুটে উঠেছিল তার। মনে মনে বলেছিল! গবুচন্দ্ৰটি তো বেশ! ধার আছে! মিছরির তাল নয়, মিছরির ছুরি!
এর পরই হঠাৎ অঘটন ঘটে গিয়েছিল। পর পর দুটি। একখানা বিখ্যাত ইংরেজি কাগজে একটা প্রবন্ধ বের হয়েছিল—একটি অহিংস সিংহ ও তার শাবকগণ। গান্ধীজীকে আক্রমণ করে প্রবন্ধ। লেখক বলেছিলেন, একটি সিংহ হয়ত অভ্যাসে ও সাধনায় অহিংস হতে পারে, কিন্তু তাই। বলে কি ধরে নেওয়া যায় যে, তার শাবকেরাও তাদের স্বভাবধর্ম হিংসা না নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে, বা রক্তের প্রতি তাদের অরুচি জন্মাবে? প্রবন্ধের ভাষা যেমন জোরালো, যুক্তি তেমনি ক্ষুরধার। বুদ্ধের কাল থেকে এ-পর্যন্ত ইতিহাসের নজির তুলে এই কথাই বলেছেন লেখক, অহিংসার সাধনা অন্যান্য ধর্মের সাধনার মত ব্যক্তিগত জীবনেই সফল হতে পারে। রাষ্ট্রে এই বাদকে প্রয়োগ করার মত অযৌক্তিক আর কিছু হয় না। এমনকি, সম্প্রদায়গতভাবেও এ-বাদ সফল হয় নি, হতে পারে না। প্রবন্ধটি কয়েকদিনের জন্য চারিদিকে, বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজে, বেশ একটা শোরগোল তুলেছিল। সুরমা পড়েছিল সে প্ৰবন্ধ। লেকের বক্তব্য তার খারাপ লাগে নি। সেকালে সরকারি চাকুরে বিশেষ করে বড় চাকুরে যারা এবং অচাকুরে, অতিমাত্রায় ইউরোপীয় সভ্যতা-ঘেঁষা সমাজে একদল লোক মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, গান্ধীজীর এই অহিংসা নিতান্তই অবাস্তব এবং সেই হেতু ব্যর্থ হতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, অত্যাধুনিক ইউরোপীয় মতবাদ ও সভ্যতাবিরোধী এই গান্ধীবাদী আন্দোলনকে অনেকখানি। তাঁদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বলে মনে করতেন। সমাজে আসরে মজলিসে এ-সম্পর্কে অনেক আলোচনা হত। তাদের সকলেরই ধারণা ছিল যে, অহিংসার এই মতবাদ—এটা নিতান্তই বাইরের খোলসমাত্র। সিংহচর্মাবৃত গর্দভ নয়, গর্দভচর্মাবৃত সিংহ। সুরমার বাবা অরবিন্দুবাবু ভিন্ন মতের মানুষ ছিলেন। গান্ধীজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অসাধারণ। কিন্তু তবুও জজসাহেব হিসেবে তিনি এবং তার সঙ্গে স্ত্ৰীকন্যা বাধ্য হয়েই বিরোধী শিবিরের মানুষ বলে লোকের দ্বারাও গণ্য হতেন এবং নিজেরাও নিজেদের অজ্ঞাতসারেই বোধ করি তাই বলে গণ্য করতেন। সেই কারণেই প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু ভাল লেগেছিল। লেখার ঢঙটিও অতি ধারালো, বাঁকানো। দিনকয়েক পরে তার বাবা তাকে লিখলেন—এ প্রবন্ধ জ্ঞানেন্দ্র লিখেছে। আমাকে অবশ্য দেখিয়েছিল। ভাল লিখেছে, পড়ে দেখিস।
সুরমার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। এ লেখা সুমতির মুখচোরা কার্তিকের কলম থেকে বেরিয়েছে। ঠিক যেন ভাল লাগে নি! মনে হয়েছিল সে যেন ঠকে গেছে, জ্ঞানেন্দ্রনাথই তাকে। ভালমানুষ সেজে ঠকিয়েছে।
এর কিছুদিন পরেই আর এক বিস্ময়। হঠাৎ সেদিন কলেজ-হস্টেলে নতুন একখানা টেনিস র্যাকেট হাতে দেখা করতে এলেন সুমতির পতি! টেনিস র্যাকেট! হাসি পেয়েছিল সুরমার। উচ্চপদের দণ্ড। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, অনেক বিনিদ্র রাত্রি অধ্যয়ন করে পরীক্ষায় ভাল ফল করে একটি বড় চাকরি পেয়েছে, তারই দায়ে অফিসিয়ালদের ক্লাবে চাঁদা তো গুনতেই হচ্ছে, এর ওপর এতগুলি টাকা খরচ করে টেনিস র্যাকেট! বেচারাকে একদা হয়ত পা পিছলে পড়ে ঠ্যাঙখানি ভাঙতে হবে। হেসে সে বলেছিল—খেলতে জানেন, না হাতেখড়ি নেবেন?
জ্ঞানেন্দ্রবাবু বলেছিলেন শেখাবেন?
—শেখালেই কি সব জিনিস সব মানুষের হয়? নিজের ভরসা আছে?
–তা আছে। ছেলেবেলায় ভাল গুলি-ডাণ্ডা খেলতাম।
খিলখিল করে হেসে উঠেছিল সুরমা। তারপর বলেছিল—পারি নে তা নয়। কিন্তু গুরুদক্ষিণা কী দেবেন?
—বলুন কী দিতে হবে? বুঝে দেখি।
–আপনার ওই কার্তিকী ঢঙের গোঁফজোড়াটি কামিয়ে ফেলতে হবে।
হেসে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেছিলেন বিপদে ফেললেন। কারণ এই গোঁফজোড়াটি সুমতির বড় প্রিয়। ওর একটা পোষা বেড়াল ছিল, সেটা মরে গিয়েছে। তার দুঃখ সুমতি এই গোঁফজোড়াটি দেখেই ভুলেছে।
সুরমা বক্ৰহেসে বলেছিল—তা হলে ও দুটি কামাতেই হবে। আমি বরং সুমতিকে একটা ভাল কাবলী বেড়াল উপহার দেব।
এরপরই হঠাৎ কথার মোড়টা ঘুরে গিয়েছিল। পাশেই টেবিলের উপর পুরনো খবরের কাগজের মধ্যে লালনীল পেন্সিলে দাগমারা সেই কাগজখানা ছিল, সেটাই নজরে পড়েছিল জ্ঞানেন্দ্রনাথের। তিনি কৌতুকে কাগজখানা টেনে নিয়েছিলেন এবং পাশে লেখা নানান ধরনের মন্তব্যের উপর চোখ বুলিয়ে হেসে বলেছিলেনওরে বাপ রে। লোকটা নিশ্চয় বাসায় মরেছে।
উঃ, কী সব কঠিন মন্তব্য!
সুরমা মুহূর্তে আক্রমণ করেছিল জ্ঞানেন্দ্রনাথকে। কেন, তা বলতে পারে না। কারণ মন্তব্যগুলির একটিও তার লেখা ছিল না, এবং জজসাহেবের মেয়ে এই মতবাদের ঠিক বিরুদ্ধ মতবাদও পোষণ করত না। তাই আজও সে ভেবে পায় না কেন সে সেদিন এমন তীব্রতাবে আক্রমণ করেছিল তাকে। বলেছিল—বাসায় তিনি মরেন নি, আমার সামনে তিনি বসে আছেন। সে আমি জানি। ছদ্মনামের আড়ালে বসে আছেন। এই বলেই শুরু করেছিল আক্রমণ। তারপর সে অবিশ্ৰান্ত শবর্ষণ। জ্ঞানেন্দ্ৰনাথ শুধু মুচকি হেসেছিলেন। শরগুলি যেন কোনো অদৃশ্য বর্মে আহত হয়ে ধার হারিয়ে নিরীহ শরের কাঠির মতই ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিল। সুরমা ক্লান্ত হলে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেছিলেন–মিষ্টিমুখের গাল খেয়ে ভারি ভাল লাগল।
সুরমা দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল, বলেছিল—ডাকব অন্য মিষ্টিমুখীদের? বলব ডেকে যে, এই দেখ সেই কুখ্যাত প্রবন্ধের লেখক কে? দেখবেন?
জ্ঞানেন্দ্রনাথের চোখ দুটোও দপ্ কর জ্বলে উঠেছিল। সুরমার চোখ এড়ায় নি। সে বিস্মিত হয়েছিল। গোবরগণেশ হলেও তার হাতে কলম দেখলে বিস্ময় জাগে না, শখের বাবু কার্তিকের হাতে খেলার তীর-ধনুকও বেখাপ্পা লাগে না, কিন্তু ললাটবহ্নি চোখের কোণে আগুন হয়ে জ্বলল কী করে? কিন্তু পরমুহূর্তেই জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেই নিরীহ গোপাল-জ্ঞানেন্দ্রনাথ হয়ে গিয়েছিলেন।
পরমুহূর্তেই হেসে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেছিলেনদেখতে রাজি আছি। কিন্তু আজ নয়, কাল। সুমতিকে তা হলে টেলিগ্রাম করে আনাই। আমার পক্ষে উকিল হয়ে সে-ই লড়বে। কারণ মেয়েদের গালিগালাজের জবাব এবং অযৌক্তিক যুক্তির উত্তরে এই ধরনের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে তো সম্ভবপর নয়।
কতকগুলি মেয়ে এসে পড়ায় আলোচনাটা বন্ধ হয়েছিল।
তারপরই দ্বিতীয় ঘটনা। টেনিস র্যাকেট নিয়েই ঘটল ঘটনাটা।
খ.
পুজো ছিল সেবার কার্তিক মাসে। পুজোর ছুটিতে বাবা সেবার দিন-পনের দার্জিলিঙে কাটিয়েই কর্মস্থলে ফিরে এলেন। সাঁওতাল পরগনার কাছাকাছি কর্মস্থলের সেই শহরটি শরৎকাল থেকে কয়েকমাস মনোরম হয়ে ওঠে। ফিরেই সুরমা শুনেছিল, সুমতিরা পুজোর ছুটিতে সেবার দেশে যায় নি, এখানেই আছে, সুমতিরই অসুখ করেছিল। সুমতি তখন পথ্য পেয়েছে, কিন্তু দুর্বল। চ্যাটার্জিসাহেব পুজোর তত্ত্ব, কাপড়চোপড়, মিষ্টি নিয়ে নিজে গিয়েছিলেন ওদের বাড়ি, সঙ্গে সুরমাও গিয়েছিল। আসবার সময় সুরমা জ্ঞানেন্দ্রনাথকে বলে এসেছিল,বিকেলে যাবেন। আজ টেনিসে হাতেখড়ি দিয়ে দেব।
চ্যাটার্জিসাহেব নিজে ভাল খেলতেন। এককালে স্ত্রীকেও শিখিয়েছিলেন। সুরমা ছেলেবেলা থেকে খেলে খেলায় নাম করেছিল। সেদিন চ্যাটার্জিসাহেব খেলতে আসেন নি। সুরমা জ্ঞানেন্দ্রনাথকে নিয়ে একা একা খেলতে নেমে নিজে প্রথম সার্ভ করে, করে বলটার ফেরত-মার দেখে চমকে উঠেছিল। সে-বল সে আর ফিরিয়ে মারতে পারে নি। জ্ঞানেন্দ্রর মার যে পাকা খেলোয়াড়ের মার। সুরমা হেরে গিয়েছিল।
খেলার শেষে সে বলেছিল—আপনি অত্যন্ত শ্ৰুড লোক। তার চেয়ে বেশি কপট লোক আপনি। ডেঞ্জারাস ম্যান!
–কেন? কী করলাম?
–থাকেন যেন কত নিরীহ লোক, ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না, অথচ–।
জ্ঞানেন্দ্রনাথ হেসে বলেছিলেন—তা হলে গোঁফজোড়াটা থাকল আমার?
ওই খেলার ফাঁকেই কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল। জ্ঞানেন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হল সে। সুমতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল তার ওপর। গ্রাহ্য করে নি সুরমা। বরং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল ওর ওপর। চরম হয়ে গেল ওখানকার টেনিস কম্পিটিশনের সময়। বড়দিনের সময় সুরমা গিয়ে কম্পিটিশনে যোগ দিলে, পার্টনার নিলে জ্ঞানেন্দ্রকে। ফাইন্যালের দিন খেলা জিতে দুজনে ফটো তুলতে গিয়েছিল। ফটো তুলবার আগে জ্ঞানেন্দ্র বলেছিলেন, তোমার সঙ্গে ফটো তুলব, গোঁফটা কামাব না।
ওই খেলার অবসরেই আপনি ঘুচে পরস্পরের কাছে তারা তখন তুমি হয়ে গেছে।
সুরমা হেসে উঠেছিল। এবং সে-দিন জ্ঞানেন্দ্র যখন তাদের কুঠি থেকে বিদায় নেন তখন। নিজের একগোছা চুল কেটে একটি খামে পুরে তাঁর হাতে দিয়ে বলেছিল—আমি দিলাম, আমার দক্ষিণা! কিন্তু আর না। আর আমিও তোমার সঙ্গে দেখা করব না, তুমিও কোরো না। সুমতি সহ্য করতে পারছে না। আজ আমাকে সে স্পষ্ট বলেছে, তুই আমার সর্বনাশ করলি।
অনেককাল পর আজ সুরমা উঠে এসে দাঁড়ালেন টেনিস ফাইন্যালের পর তোলানো সেই ফটোখানার সামনে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। ফোকাসের সময় তারা ক্যামেরার দিকেই তাকিয়ে ছিল, কিন্তু ঠিক ছবি নেবার সময়টিতেই নিজেদের অজ্ঞাতসারে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেছিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথের কপিখানা নেই, সেখানা সুমতি—। এই ঘটনার স্মৃতি মাথার মধ্যে আগুন জ্বেলে দেয়।
ঈর্ষাতুরা সুমতি! আশ্চর্য কঠিন ক্রূর ঈর্ষা। পরলোক, প্রেতবাদ, এ-সবে সুরমা বিশ্বাস করে। না, কিন্তু এ-বিশ্বাস তার হয়েছে, মানুষের প্রকৃতির বিষই হোক আর অমৃতই হোক, যেটাই তার স্বভাব-ধৰ্ম—সেটা তার দেহের মৃত্যুতেও মরে না, যায় না; সেটা থাকে, ক্রিয়া করে যায়। সুমতির ঈর্ষা আজও ক্রিয়া করে চলেছে; জীবনের আনন্দের মুহূর্তে অকস্মাৎ ব্যাধির আক্রমণের মত আক্রমণ করে, মধ্যে মধ্যে সেই আক্রমণের থেকে নিষ্কৃতি বোধ করি এজন্মে আর হল না। কিন্তু আজ যেন এ-আক্ৰমণ অতি তীব্র, হঠাৎ ওই আগুনটা জ্বলে ওঠার মতই জ্বলে উঠেছে। খড়ের আগুনটা নিভেছে, এটা নিভল না।
গ.
তাঁর কাঁধের উপর একখানা ভারী হাত এসে স্থাপিত হল। গাঢ় স্নেহের আভাস তার মধ্যে, কিন্তু হাতখানা অত্যন্ত ঠাণ্ডা। স্বামী রবারের চটি পরে শতরঞ্জির উপর দিয়ে এসেছেন; চিন্তামগ্নতার মধ্যে মৃদু শব্দ যেটুকু উঠেছে তা সুরমার কানে যায় নি।
-অকারণ নিজেকে পীড়িত কোরো না। ধীর মৃদু স্বরে বললেন– জ্ঞানেন্দ্রনাথপরের দুঃখের জন্যে যে কাঁদতে পারে, সে মহৎ; কিন্তু অকারণ অপরাধের দায়ে নিজেকে দায়ী করে পীড়ন করার নাম দুর্বলতা। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। এস।
ঘুরে তাকালেন সুরমা, স্বামীর মুখের দিকে তাকাবামাত্র চোখ দুটি ফেটে মুহূর্তে জলে ভরে টলমল করে উঠল।
জ্ঞানেন্দ্রবাবু তাকে মৃদু আকর্ষণে কাছে টেনে এনে কাঁধের উপর হাতখানি রেখে অনুচ্চ গাঢ় গম্ভীর স্বরে বললেন– আমি বলছি, তোমার কোনো অপরাধ নেই, আমারও নেই। না। অপরাধ সমস্ত তার! হা তার! উই ডিড নাথিং ইমমরাল, নাথিং ইললিগ্যাল। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বের অধিকার আমার ছিল। সেই অধিকারের সীমানা কোনোদিন অন্যায়ভাবে অতিক্রম আমরা করি নি। বিবাহের দায়ে অপর কোনো নারীর সঙ্গে পুরুষের বা কোনো পুরুষের সঙ্গে বিবাহিতা নারীর বন্ধুত্বের বা প্রীতিভাজনতার অধিকার খর্ব হয় না। আমারও হয় নি, তোমারও হয় নি।
সুরমার চোখ থেকে জলের ফোঁটা কটি ঝরে পড়ল; পড়ল জ্ঞানেন্দ্রনাথের বাঁ হাতের উপর। বাঁ হাত দিয়ে তিনি সুরমার একখানি হাত ধরেছিলেন সেই মুহূর্তটিতে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন–তুমি কাঁদছ? না, কেঁদো না। আমাকে তুমি বিশ্বাস কর। আমি অনেক ভেবেছি। সমস্ত ন্যায় এবং নীতিশাস্ত্রকে আমি চিরে চিরে দেখে বিচার করেছি। আমি বলছি অন্যায় নয়। অন্যায় হয় নি। শুধু বন্ধুত্ব কেন সুরমা, প্রেম, সেও বিবাহের কাটা খালের মধ্যে বয় না। বিবাহ হলেই প্রেম হয়। না সুরমা। বিবাহের দায়িত্ব শুধু কর্তব্যের, শপথ পালনের। সুমতিকে বিবাহ করেও তোমাকে আমি যে-নিয়মে ভালবেসেছিলাম সে-নিয়ম অমোঘ, সে-নিয়ম প্রকৃতির অতি বিচিত্ৰ নিয়ম, তার উপর কোনো ন্যায় বা নীতিশাস্ত্রের অধিকার নেই। যে-অধিকার আছে সে-অধিকার আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলাম। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে এসেছিল ভালবাসা, তাকে আমি সংযমের বাধে বেধেছিলাম। প্রকাশ করি নি। তোমার কাছে না, সুমতির কাছে না, কারও কাছে না। আর তোমার কথা? তোমার বিচার আরও অনেক সোজা। তুমি ছিলে কুমারী। অন্যের কাছে। তোমার দেহমনের বিন্দুমাত্র বাধা ছিল না। শুধু সুমতির স্বামী বলে আমাকে তোমার ছিনিয়ে নেবারই অধিকার ছিল না, কিন্তু ভালবাসার অবাধ অধিকার লক্ষ বার ছিল তোমার। সুরমা, আজও স্থির বিশ্বাসে ভগবান মানি নে, নইলে বলতাম ভগবানেরও ছিল না। কোনো অপরাধ নেই আমাদের। বিচারালয়েই বল বা যে কোনো দেশের মানুষের বিচারালয়েই বল, সেখানে সিদ্ধান্ত নির্দোষ। জড়িমাশূন্য পরিষ্কার কণ্ঠের দৃঢ় উচ্চারিত সিদ্ধান্ত! দুর্বলতাই একমাত্র অপরাধ, যার জন্য প্রাণ অভিশাপ দেয় আত্মাকে।
স্থিরদৃষ্টিতে অভিভূতের মত সুরমা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলি শুনছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের দৃষ্টি স্থির। তিনি তাকিয়ে ছিলেন একটু মুখ তুলে ঘরখানার কোণের ছাদের। অংশের দিকে, ওইখানে ওই আবছায়ার মধ্যে দেওয়ালের গায়ে কোন মহাশাস্ত্রের একটি পাতা ফুটে উঠেছে, এবং তিনি তাই পড়ে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে, দৃঢ়কণ্ঠে।
–চল, বাইর চল, বেড়াতে যাব।
সুরমা এটা জানতেন। এইবার তিনি বাইরে যেতে বলবেন। যাবেন। অনেকটা দূরে ঘুরে আসবেন। আগে সারা রাত ঘুরেছেন, ক্লাবে গিয়েছেন, মদ্যপান করেছেন। রাত্রে আলো জ্বলে টেনিস খেলেছেন দুজনে। এখন এমনভাবে সুমতিকে মনে পড়ে কম। এবার বোধহয় দু বছর পরে এমনভাবে মনে পড়ল। সোজা পথে তো সুমতিকে তারা আসতে দেন না। কথার পথ ধরে সুমতি তাদের সামনে এসে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেই কথার পথের মোড় ঘুরিয়ে দেন তারা। অন্য কথায় গিয়ে পড়েন। আর সুমতি দীর্ঘদিন পরে ঘুরপথ ধরে সামনে এসেছে। বাথরুমের জানালা দিয়ে ওই আগুনের ছটার সঙ্গে মিশে অশরীরিণী সে ঈর্ষাতুরা এসে দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়েছে।
ঘ.
গাড়ি চলল। শ্ৰাবণ-রাত্রিতে আবার মেঘ ঘন হয়ে উঠেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নতুন অ্যাসফন্টের সমতল সরল পথ। শহর পার হয়ে, নদীটার উপর নতুন ব্যারেজের সঙ্গে তৈরি ব্রিজ পার হয়ে শাল-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে গেছে নতুন-তৈরি পথ। দুপাশে শালবনে বর্ষার বাতাসে মাতামাতি চলেছে। নতুন পাতায় পাতায় বৃষ্টিধারার আঘাতে ঝরঝর একটানা শব্দ চলেছে। মধ্যেমাঝে এক-এক জায়গায় পথের পাশে পাশে কেয়ার ঝাড়। সেখানে কেয়া ফুল ফুটেছে, গন্ধ আসছে। ভিজে অ্যাসফন্টের রাস্তার বুকে হেডলাইটের তীব্র আলোর প্রতিচ্ছটা পড়েছে; পথের বাঁকে হেডলাইটের আলো জঙ্গলের শালগাছের গায়ে গিয়ে পড়েছে; অদ্ভূত লাগছে।
গাড়ি চলেছে। এক সময় যেন প্রকৃতির রূপ বদলাল অন্ধকার যেন গাঢ়তর হয়ে উঠল। চারিপাশে আকাশ থেকে ঘন কালো মেঘপুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে মাটিতে নেমেছে মনে হচ্ছে। মেঘ নয়, ওগুলি পাহাড়, আরণ্যভূম এবং পার্বত্যভূম এক হয়ে গেল এখান থেকে। অ্যাসফন্টের রাস্তা এইবার সর্পিল গতি নিচ্ছে, সত্যই সাপের মত এঁকেবেঁকে চলেছে। দূরে কোথাও প্রবল একটাগ ঝরঝর শব্দ উঠেছে, একটানা শব্দ; দিমণ্ডল-ব্যাপ্ত করা প্রচণ্ড উল্লাসের একটা বাজনা যেন। কোথাও বেজে চলেছে; বাজনা নয়,পাহাড় থেকে ঝরনা ঝরেছে। গাড়ির মধ্যে স্বামী-স্ত্রী দুজনে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, ঘোষাল সাহেব তার হাতের মধ্যে সুরমার একখানি হাত নিয়ে বসে আছেন। মধ্যে মধ্যে দু-চারটি কথা। কাটাকাটা, পারম্পর্যহীন।
—এটা সেই বনটা নয়? যেখানে গলগলে ফুলের গাছ দেখেছিলাম?
–এই তো বাঁ পাশে; পেরিয়ে এলাম।
তারপর আবার দুজনে স্তব্ধ। গলগলে ফুলের সোনার মত রঙ। ফুল তুলে সুরমাকে দিয়েছিলেন; সুরমা একটি ফুল খোপায় পরেছিল। ঘোষাল সাহেবের হাতের মুঠো ক্রমশ দৃঢ় হয়ে উঠেছিল; অন্তরে আবেগ গাঢ় হয়ে উঠেছে। সুরমা একটি অস্ফুট কাতর শব্দ করে উঠলেন। উঃ!
–কী হল? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন স্বামী।
মৃদুস্বরে সুরমা শুধু বললেন–আংটি।
–লেগেছে? বলেই হেসে ঘোষাল সাহেব হাত ছেড়ে দিলেন। আঙুলের আংটির জন্যে হাতের চাপ বড় লাগে।
–না। অন্ধকারের মধ্যেই অল্প একটু মুখ ফিরিয়ে স্বামীর দিকে চেয়ে স্বামীর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন। না, ছেড়ে দিতে তিনি চান না।
আবার স্তব্ধ দুজনে। মনের যে গুমট অন্ধকার কেটে যাচ্ছে তাই যেন বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে। মুহূৰ্তে মুহূর্তে; তারা প্রশান্ত ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে তার চেয়ে চেয়ে দেখছেন। অকস্মাৎ দূরের একটানা বাজনার মত ঝরনার সেই ঝরঝর শব্দটা প্রবল উল্লাসে বেজে উঠল। যেন একটা পাঁচিল সরে গেল, একটা বদ্ধ সিংহদ্বার খুলে গেল। একটা চড়াই অতিক্রম করে ঢালের মুখে বাঁক ফিরতেই শব্দটা শতধারায় বেজে উঠেছে। চমকে উঠলেন সুরমা।
–কিসের শব্দ?
—ঝরনার। বর্ষার জলের ঢল্ নেমেছে। নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ। স্বরাতুর হাসি ফুটে উঠল ঘোষাল সাহেবের মুখে। সুরমা উৎসুক হয়ে জানালার কাছে মুখ রাখলেন, যদি দেখা যায়!
ঘোষাল সাহেব চোখ বুজে মৃদুস্বরে আবৃত্তি করলেন,
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব
হেসে খলখল, গেয়ে কলকল, তালে তালে দিব তালি।
কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধ থেকে আবার বললেন–এত কথা আছে এত গান আছে এত প্রাণ আছে মোর। তারপর বললেন– প্রাণ গান গাইছে। লাইফ ফোর্স। যেখানে জীবন যত দুর্বার, সেখানে তার গান তত উচ্চ। কিন্তু সব প্রাণেরই কামনা বিশ্বগ্ৰাসী, তাই তার দাবি—নাল্পে সুখমস্তি—ভূমৈব সুখম্। বিপুল বিশাল প্রাণেরও যত দাবি এক কণা প্রাণেরও তাই দাবি। বড় অনবুঝ। বড় অনবুঝ।
একটু চুপ করে থেকে বললেন––কিন্তু যার যতখানি শক্তি তার একটি কণা বেশি পাবার অধিকার তার নাই। নেচারস্ জাজমেন্ট! কোথাও নদী পাহাড় কেটে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আপন পথ করে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোথাও স্তব্ধ হয়ে খানিকটা জলার সৃষ্টি করে পাহাড়ের পায়ের তলায় পড়ে আছে, শুকিয়ে যাচ্ছে। বড়জোর মানস সরোবর। কিন্তু মাথা কোটার বিরাম নাই।
অকস্মাৎ সুরমা দেবী সচেতন হয়ে উঠলেন, বললেন–কটা বাজল?
শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন তিনি। দর্শনতত্ত্বের মধ্যে ঘোষাল সাহেব ঢুকলে আর ওঁর নাগাল পাবেন না তিনি। মনে হবে, এই ঝরনাটার ঠিক উলটো গতিতে তিনি পাহাড়ের উচ্চ থেকে উচ্চতর শিখরে উঠে চলেছেন, আর তিনি সমতলে অসহায়ের মত ওঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। ক্রমশ যেন চেনা মানুষটা অচেনা হয়ে যাচ্ছে। প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। একথা বললে আগে বিচিত্র ভঙ্গি করে তার দিকে তাকিয়ে বলতেন—তা হলে ইন্সিওরেন্স পলিসি, গভর্নমেন্ট পেপার আর শেয়ার স্ক্রিপ্টগুলো নিয়ে এস। তাই নিয়ে কথা বলি। অথবা আলমারি খুলে হুইস্কির বোতল বের করে দাও। গিভ মি ড্রিঙ্ক। হেঁটে নামতে দেরি লাগবে অনেক। তার চেয়ে স্থলিত চরণে গড়গড় করে গড়িয়ে এসে পড়ব তোমার কাছে। তোমার অঙ্গে ঠেকা খেয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকব। বলে হা-হা করে হাসতেন। যে-হাসি সুরমা সহ্য করতে পারতেন না।
আগে ঘোষাল সাহেব সত্য সত্যই এ-কথার পর মদ খেতেন, পরিমাণ পরিমাপ কিছু মানতেন না। এখন মদ আর খান না। সুদীর্ঘকালের অভ্যাস একদিনে মহাত্মার মৃত্যুদিনের সন্ধ্যায় ছেড়ে দিয়েছেন। মদ ধরেছেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুরমাদের সংস্পর্শে এসে। শুরু তার টেনিস খেলার পর ক্লাবে। সেটা বেড়েছিল সুমতির সঙ্গে অশান্তির মধ্যে। সুমতির মৃত্যুর পর সুরমাকে। বিয়ে করেও মধ্যে মধ্যে এমনই কোনো অস্বস্তিকর অবস্থা ঘনিয়ে উঠলেই সেদিন মদ বেশি খেতেন। গান্ধীজীর মৃত্যুর পর গোটা রাত্রিদিনটা তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন একখানা ঘরের মধ্যে। উপবাস করে ছিলেন। জীবনে গান্ধীজী সম্পর্কে তিনি যত কিছু মন্তব্য করেছিলেন ডায়রি উলটে উলটে সমস্ত দেখে তার পাশে লাল কালির দাগ দিয়ে লিখেছিলেন—ভুল, ভুল। সুরমা তার সামনে কতবার গিয়েও কথা বলতে না পেরে ফিরে এসেছিলেন। তারপর, তখন বোধহয় রাত্রি নটা, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বেয়ারাকে ডেকে বলেছিলেন—সেলারে যতগুলি বোতল আছে নিয়ে এস।
বোতলগুলি খুলে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন মাটিতে। তারপর বলেছিলেন—আমার খাবারের মধ্যে মাছ মাংস আজ থেকে যেন না থাকে সুরমা।
সুরমা বিস্মিত হন নি। এই বিচিত্র মানুষটির কোনো ব্যবহারে বিস্ময় তাঁর আর তখন হত না।
সেই অবধি মানুষটাই যেন পালটে গেলেন। এ আর-এক মানুষ। মানুষ অবশ্যই পালটায়, প্রতিটি দিন, প্রতিটি ক্ষণে পালটায়, প্রকৃতির নিয়ম, পরিবর্তন অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু এ-পরিবর্তন যেন দিক পরিবর্তন। একবার নয়, দুবার। প্রথম পরিবর্তন সুমতির মৃত্যুর পর। শান্ত মৃদু মিষ্টভাষী কৌতুকপরায়ণ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুমতির মৃত্যুর পর হয়ে উঠেছিলেন অগ্নিশিখার মত দীপ্ত এবং প্রখর, কথায়-বার্তায় শাণিত এবং বক্র; দুনিয়ার সমস্ত কিছুকে হা-হা করে হেসে উড়িয়ে দিতেন।
একবার, তখন জ্ঞানেন্দ্রনাথ বর্ধমানে ডিস্ট্রিক্ট জজ, তাদের বাড়িতে সমবেত হয়েছিলেন। রাজকর্মচারীদের নবগ্রহমণ্ডলী, তার চেয়েও বেশি কারণ, এঁরা ছিলেন সপরিবারে উপস্থিত। তর্ক জমে উঠেছিল ঈশ্বর নিয়ে। তর্কের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথ কথা বলেন নি বেশি কিন্তু যে কম কথা কটি বলেছিলেন তা যত মারাত্মক এবং তত ধারালো ও বক্র ব্যঙ্গাত্মক। লঙ্কা ফোড়নের মত অ্যাঁঝালো এবং সশব্দ। হঠাৎ এরই মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বার বছরের ছেলেটি বলে উঠেছিল—গড ইজ নাথিং বাট বারেশন।
কথাটা ছেলেমানুষি। শুনে সবাই হেসেছিল; কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথের সে কী অট্টহাসি! তিন দিন ধরে হেসেছিলেন।
ধীরে ধীরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হাসির উচ্ছলতা তাঁর কমে এসেছিল, কিন্তু প্রকৃতিতে তিনি পাল্টান নি। প্রথম যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন যুদ্ধের সময়। তারপর গান্ধীজীর মৃত্যুর দিনে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। এখন দৰ্শনতত্ত্বের গহনে প্রবেশপথে তাকে পিছন ডাকলে তিনি আগের মত অট্টহাস্য করেন না মদ খান না, চোখ বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকেন এবং তারই মধ্যেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়েন। এমন ক্ষেত্রে তাঁকে সহজ জীবনের সমতলে নামাতে একটি কৌশল আবিষ্কার করেছেন সুরমা। তাকে কোনো গুরুদায়িত্ব বা কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাতেই কাজ হয়।
ঙ.
আজ ওই নদীর জলের এবং ওই পাহাড়ের বাঁধের দৃঢ়তার কথা ধরে জীবনতত্ত্বের জটিল গহনে তিনি ক্ৰমে ক্ৰমে সুরমার নাগালের বাইরে চলে যাবার উপক্রম করতেই শঙ্কিত হয়ে সুরমা নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকালেন। বোধ করি বিদ্যুতের চমক দেখে আপনাআপনি চোখ বুজে ফেলার মত সে তাকানো, বললেন–কটা বাজছে? আমার ঘড়িটায় কিছু ঠাওর করতে পারছি না। চোখের পাওয়ার খুব বেড়ে গেছে। দেখ তো?
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চোখ বন্ধ করে গাড়ির ঠেসান দেওয়ার গদিতে মাথাটি হেলিয়ে দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন–গাড়ির ড্যাসবোর্ডের ঘড়িটা দেখ।
ড্যাসবোর্ডের ঘড়িটা বেশ বড় একটা টাইম-পিস। তার উপর রেডিয়ম দেওয়া আছে। জ্বলজ্বল করছে। সুরমা চমকে উঠে বললেন–ও মা। এ যে বারটা!
–বারটা? ক্লান্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। কিন্তু তার বেশি চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেন না। চোখ বুজে ভাবছিলেন, চোখ খুললেন না।
–গাড়ি ঘোরাও। বললেন– সুরমা।
–ঘোরাব?
–ঘোরাবে না? ফিরে তো আবার সেই নথি নিয়ে বসবে। ওদিকে সেসস্ চলছে, সেই দশটার সময়–
তবুও তেমনিভাবে বসে রইলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ।
গোটা কেটা মাথার মধ্যে উঘাটিতযবনিকা রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটের মত ভেসে উঠল।
জটিল বিচাৰ্য ঘটনা। নৌকো উটে গিয়েছিল। নৌকো ড়ুবেছিল ছোট ভাইয়ের দোষে। তারা জলমগ্ন হয়েছিল। ছোট ভাই আঁকড়ে ধরেছিল বড় ভাইকে। বড় ভাই ছাড়াতে চেষ্টা করেও পারে নি। শেষে ছোট ভাইয়ের গলায় তার হাত পড়েছিল। এবং সে-স্বীকার সে করেছে। কিন্তু–
আসামিকে মনে পড়ল তার!
আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি।
সুরমাও স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ স্তব্ধ হয়েই আছেন, কিন্তু তখন ড়ুবে গেছেন মামলার ভাবনার মধ্যে। সে সুরমা বুঝতে পারছেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। এ তবু সহ্য হয়। সহ্য না করে উপায় নাই! এ কর্তব্য। কিন্তু এ কী হল তার জীবনে? তিনি পেলেন না। তার সঙ্গে চলতে পারলেন না? না! হারিয়ে গেলেন? টপটপ করে চোখ থেকে তাঁর জল পড়তে লাগল। কিন্তু সে-কথা জ্ঞানেন্দ্রনাথ জানতে পারলেন না; অন্ধকার গাড়ির মধ্যে তিনি চোখ বন্ধ করেই বসে আছেন। মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছে আদালত, জুরী, পাবলিক প্রসিকিউটার, আসামি।
পরের দিন। ডকের মধ্যে আসামি দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক সেই এক ভঙ্গিতে। বয়স অনুমান করা যায়: না, তবে পরিণত যৌবনের সবল স্বাস্থ্যের চিহ্ন সর্বদেহে। শুধু আহারের পুষ্টিতে নধর কোমল দেহ নয়, উপযুক্ত আহার এবং পরিশ্রমে প্রতিটি পেশির সুদৃঢ় ছন্দে ছন্দে গড়ে উঠেছে দেহখানি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে মনে হয়, জন্মকাল থেকেই দেহের উপাদানের সচ্ছলতা এবং দৃঢসংকল্পে পরিশ্রমের অভ্যাস নিয়ে জন্মেছে। মাথায় একটু খাটো। তাম্রাভ রঙ। মুখখানা দেখে মুখের ঠিক আসল গড়ন বোঝা যায় না, দীর্ঘদিন বিচারাধীন থাকার জন্য মাথার চুল বড় হয়েছে, মুখে দাড়িগোঁফ জন্মেছে। অবশ্য আগের কালের মত রুক্ষতা নেই চুলে, আজকাল তেল পায় জেলখানার অধিবাসীরা। তবুও দাড়ি-গোঁফ-চুল বিশৃঙ্খল; হতভাগ্যের বিভ্রান্ত মনের আভাস যেন ফুটে রয়েছে ওর মধ্যে; অঙ্গারগর্ভ মাটির উপরের রুক্ষতার মত। নাকটা স্কুল; চোখ দুটি বড়, দৃষ্টি যেন উগ্ৰ। উদ্ধত কি নিষ্ঠুর ঠিক বুঝতে পারছেন না জ্ঞানেন্দ্রনাথ। পরনে সাদা মোটা কাপড়ের বহির্বাস, গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক।
খ.
—ইয়োর অনার, এই আসামি নগেনের বাল্যজীবনের প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির কথা আমি বর্ণনা করেছি। উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা সত্যের উপর তা সুপ্রতিষ্ঠিত। তারপর এই নগেন গৃহত্যাগ করে চলে যায়। অনুতাপবশেই হোক আর ক্ষোভে অভিমানেই হোক নিরুদ্দেশ হয়ে চলে যায়। এবং দীর্ঘকাল পর সন্ন্যাসী বৈরাগীবেশে ফিরে আসে।
পাবলিক প্রসিকিউটার অবিনাশবাবু তার গতকালকার বক্তব্যের মূল সূত্রটি ধরে অগ্রসর হলেন। হাতের চশমাটি চোখে লাগিয়ে কাগজপত্র দেখে একখানি কাগজ বেছে নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন
ইয়োর অনার, আমার বক্তব্যে অগ্রসর হবার পূর্বে আপনাকে আর একবার পোস্ট মর্টেম রিপোর্টের দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করব।
অবিনাশবাবু জুরীদের দিকে তাকিয়ে বললেন– রিপোর্টে আছে জলমগ্ন হয়ে মৃত্যু হলে মানুষের পাকস্থলীতে যে-পরিমাণ জল পাওয়া যায়, এই মৃতের পাকস্থলীতে জল পাওয়া গেলেও তার পরিমাণ তার চেয়ে আশ্চর্য রকমের কম। অর্থাৎ জলমগ্ন হওয়ার কারণে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু এক্ষেত্রে হয় নি। অথচ মৃত্যু ঘটেছে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে। এবং শবদেহেও সেই লক্ষণগুলি সুপরিস্ফুট। তা হলে হতভাগ্য মরল কী করে? তার প্রমাণ রয়েছে মৃতের কণ্ঠনালীতে সুস্পষ্ট পাঁচটি নখতের চিহ্নের মধ্যে লুকানো। বাঁদিকে একটি, ডানদিকে চারটি। মানুষের হাতের লক্ষণ। আসামি নগেন থানায় এবং নিম্ন আদালতে স্বীকার করেছে, খগেন জলমগ্ন অবস্থায় তাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছিল যে সেও ড়ুবে যাচ্ছিল, তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছিল। সে তার থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল। সেই অবস্থায় কোনোক্রমে তার ডান হাতটা সে ছাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয় এবং সেই হাত পড়ে খগেনের কণ্ঠনালীতে। সে কণ্ঠনালী টিপে ধরে। খগেন ছেড়ে দেয় বা সর্বদেহের সঙ্গে তার হাত শিথিল হয়ে এলিয়ে যায়। তখন সে ভেসে ওঠে। সে একথা অস্বীকার করে না। এখন দুটি সিদ্ধান্ত হতে পারে। এক, কণ্ঠনালী টিপে ধরার ফলে খগেনের মৃত্যু হওয়ায় সে ছেড়ে দেয় বা এলিয়ে পড়ে, বা মৃত্যুর কিছু পূর্বে মৃতকল্প অচেতন অবস্থায় সে এলিয়ে পড়ে। সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, মৃত্যু এই কারণে আসামির দ্বারাই ঘটেছে।
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েও দুটি বিষয়ের বিচার আছে। জটিল, অত্যন্ত জটিল। দুটি বিষয়ের একটি হল, আসামি আত্মরক্ষার জন্য অর্থাৎ মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে মানবিক সকল চৈতন্য এবং চেতনা হারিয়ে, এমন ক্ষেত্রে অবশিষ্ট জান্তব চেতনার পক্ষে অতি স্বাভাবিক প্রেরণায় মৃত খগেনের গলা টিপে ধরেছিল, অথবা তার পূর্বেই তার মানসিক কূটবুদ্ধি, লোভ-হিংসাসঞ্জাত ক্রতা ও জীবনের অভ্যস্ত পাপপরায়ণতা এই সুযোগে চকিতে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। যেমন জাগ্রত হয়ে ওঠে নির্জনে অসহায় অবস্থায় নারী দেখলে ব্যভিচারীর পাশব প্রবৃত্তি, আবার। জাগ্রত হয় লুটেরার লুণ্ঠন প্রবৃত্তি, তেমনিভাবে কাল ও পাত্রের সমাবেশে সৃষ্ট সুবর্ণ সুযোগের মত পরিবেশের সুযোগ দেখে জেগে উঠেছিল। ইয়োর অনার, সৎ এবং অসতের দ্বন্দ্বের মধ্যে এই সংসারে কতক্ষত্রে যে বিশ্বাসপরায়ণ অসহায় বন্ধুকে বন্ধু হত্যা করে তার সংখ্যা অনেক! গোপন প্রবৃত্তি সুযোগ দেখে অকস্মাৎ জেগে ওঠে দানবের মত। চিরন্তন পশু জাগে; অসহায় মানুষ দেখে বাঘ যেমন গোপন স্থান থেকে লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক তেমনিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
গোপন মনের পাশব প্রবৃত্তির অস্তিত্বই মানুষের সভ্যতার শৃঙ্খলার ভয়ঙ্করতম শত্ৰু। নানা ছদ্মবেশ পরে নানা ছলনায় মানুষের সর্বনাশ করে সে। আমি সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছি। বলেই বিশ্বাস করি যে, সেই প্রবৃত্তিই সজাগ ছিল আসামির মনের মধ্যে। এখন বিচার্য বিষয় সেইটুকু; ওই জলমগ্ন অবস্থায় আসামির মনের স্বরূপ নির্ণয়! এ নির্ণয় অত্যন্ত কঠিন; অতি জটিল; এর কোনো সাক্ষী নাই। আসামি বলে, সে জানে না। এবং এও বলে যে, সে যদি হত্যা করে থাকে তবে সে মৃত্যু-শাস্তিই চায়। আসামি বৈষ্ণব, এই বিচারাধীন অবস্থাতেও সে তিলকফোঁটা কাটে দেখতে পাচ্ছি। সে এক সময় গৃহত্যাগ করেছিল বৈরাগ্যবশে, জীবহত্যা করে কুলধৰ্ম লঙ্নের জন্য অনুতাপবশে। বার বৎসর পর ফিরে এসে এই সভাইকে বুকে তুলে। নিয়েছিল সুগভীর স্নেহের বশে। সেই ভাইকে সে-ই কুড়ি বৎসরের যুবাতে পরিণত করে তুলেছিল। এই দিক দিয়ে দেখলে অবশ্যই মনে হবে এবং এই সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হব যে, আসামি যখন ভাইয়ের গলা টিপে ধরেছিল, তখন তার মধ্যে জীবনের মৌলিক আত্মরক্ষার জান্তব চেতনা ছাড়া মানবিক জ্ঞান বা চৈতন্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে যে অপরাধ। সে করেছে, সে-অপরাধ অনেক লঘু, এমনকি তাকে নিরপরাধও বলা যায়।
বিচারক জ্ঞানেন্দ্রনাথ আবার তাকালেন আসামির দিকে। মাটির পুতুলের মত সে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তার নিজের মতই ভাবলেশহীন মুখ। তিনি জানেন, এসময় তার মুখের একটি। রেখাও পরিবর্তন হয় না; নিরাসক্তের মত শুনে যান। একটু তফাত রয়েছে। আসামির দৃষ্টিতে বিস্ময়ের আভাস রয়েছে। বিশ্লেষণের ধারা তাকে বিস্মিত করে তুলেছে। বিহ্বলতার মধ্যেও ওই। বিস্ময় তাকে সচেতন করে রেখেছে।
অবিনাশবাবু বলছিলেন কিন্তু যদি এই ব্যক্তি আকস্মিক সুযোগ, লোভ এবং হিংসার বশবর্তী হয়ে নিজের হাতে মানুষ-করা ভাইকে হত্যা করে থাকে তবে সে নৃশংসতম ব্যক্তি এবং চতুরতম নৃশংস ব্যক্তি। এবং সে তাই বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপাতদৃষ্টিতে একথা অসম্ভব বলে মনে হবে। মনে হবে, এবং হওয়াই উচিত, যে লোক ছাগল মারার অনুতাপে লজ্জায়। সন্ন্যাসী হয়েছিল, যে ভাইকে বুকে করে মানুষ করেছে, যার কপালে তিলক-ফোঁটা, গলায় কণ্ঠী, যে ব্যক্তি ও-অঞ্চলে খ্যাতনামা বৈষ্ণব, সে কি এ-কাজ করতে পারে? কিন্তু পারে। আমি বলি পারে। এক্ষেত্রে আমার দুই কথা। প্রথম কথা, মানুষের শৈশব-বাল্যের অভ্যাস, তার জন্মগত প্ৰকৃতি অবচেতনের মধ্যে স্থায়ী অধিকারে অবস্থান করে। সে মরে না, চাপা থাকে। এবং মানব-জীবন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে অহরহ পরিবর্তনশীল। নিত্য অহরহ পরিবর্তনের মধ্যেই তার জীবনের প্রকাশ এবং সেই প্রকাশের মধ্যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনও অনেকবার হতে পারে। যে-পথে সে চলে হঠাৎ তার বিপরীত ধরে চলতে শুরু করে। ইয়োর অনার, গৃহধৰ্ম মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। হঠাৎ দেখা যায় মানুষ সন্ন্যাসী হয়ে গেল, আবার দেখা যায়। সেই সন্ন্যাসীই গৈরিক ছেড়ে গৃহধর্ম করছে, মামলা মোকদ্দমা বিষয় নিয়ে বিবাদ সাধারণ সংসারীর চেয়ে শতগুণ আসক্তি এবং কুটিলতার সঙ্গে করছে। যেমানুষ পত্নীবিয়োগে বিরহের মহাকাব্য লেখে, সেই মানুষ কয়েক বৎসর পর বিবাহ করে নূতন প্রেমের কবিতা লেখে।
গ.
জ্ঞানেন্দ্রবাবু বললেন–সংক্ষেপ করুন অবিনাশবাবু। বি ব্রিফ প্লিজ!
—ইয়েস ইয়োর অনার, আমার আর সামান্য বক্তব্যই আছে। সেটুকু হল এই। এই আসামি নগেনের আবার একটি পরিবর্তন হয়েছিল। আমরা তার পরিচয় বা প্রমাণ পাই। সে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে পৃথক হবার ব্যবস্থা করছিল এই ঘটনার সময়। কিন্তু এটা বাহ্য। অভ্যন্তরে ছিল দি ইটারন্যাল ট্রায়ঙ্গল্–
—হোয়াট? ভ্রূ কুঞ্চিত করে সজাগ হয়ে ফিরে তাকালেন বিচারক।
–সেই সনাতন ত্রয়ীর বিরোধ, ইয়োর অনার—
–দুটি নারী একটি পুরুষ–?
–এক্ষেত্রে দুটি পুরুষ একটি নারী, ইয়োর অনার—
–ইয়েস।
অবিনাশবাবু বললেন– নারীটি একটি লীলাময়ী।
–লীলাময়ী? ইউ মিন এ মডার্ন গার্ল?
—না, ইয়োর অনার, মেয়েটি লাস্যময়ী। তারও চেয়ে বেশি, স্বৈরিণী। এ হার্লট। ওই গ্রামেরই একটি দরিদ্র শ্রমজীবীর কন্যা। নগেন এবং খগেনের বাপের আমল থেকে ওই মেয়েটির বাপমায়ের সঙ্গে নানা কর্মসূত্রে হৃদ্যতা ছিল। চাষের সময় মেয়েটির মা-বাপ ওদের চাষে খাটত। শেষের দিকে কয়েক বৎসর যখন নগেন-খগেনের বাপ শেষশয্যায় দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিল, তখন স্থায়ীভাবে কৃষাণের কাজও করেছিল। ওদের বাড়িতে মেয়েটির মায়ের নিত্য যাওয়া-আসা ছিল; বাড়ি ঝট দেওয়ার কাজ করত, ওদের বাড়ির ধান সেদ্ধ ও ধান ভানার কাজ করত নিয়মিতভাবে, মাইনে-করা ঝিয়ের কাজ করত। তখন থেকেই ওই মেয়েটিও, চাপা, মায়ের সঙ্গে নিত্য দুবেলাই এদের বাড়ি আসত। এবং বয়সে সে ছিল খগেনেরই সমবয়সী, দুএক বছরের বড়; খগেনের সঙ্গে সে খেলা করত, পরে চাঁপার বিবাহ হয়, সে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। তখন সে বালিকা। আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সাত-আট বছর বয়সে বিবাহের কথা সর্বজনবিদিত। তারপর এই ঘটনার দু বছর আগে বিধবা হয়ে সে যখন ফিরে আসে। তখন সে যুবতী এবং স্বভাবে পূর্ণমাত্রায় স্বৈরিণী। সে তার স্বামীর বাড়িতেই এই স্বৈরিণী—স্বভাব অর্জন করেছিল, এবং যতদূর মনে হয়, জন্মগতভাবেই সে ওই প্রকৃতির ছিল। কারণ। ওই শ্বশুরবাড়িতে থাকতেই এই স্বভাবহেতু বহু অপবাদ তার হয়েছিল। দুটি-একটি ঘটনা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। এই চাপা ফিরে এসে স্বাভাবিকভাবেই এবং অতি সহজেই ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী এই প্রিয়দর্শন তরুণ খগেন ছেলেটিকে আকর্ষণ করেছিল। তারপর। আকৃষ্ট হল বড় ভাই। এই চাঁপা মেয়েটিই মামলায় প্রধান সাক্ষী। আসামি নগেন প্রথমটা এই তরুণ-তরুণীর মধ্যে সংস্কারকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়। ভাইকে সে চাপার মোহ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্যই চেষ্টা করেছিল। মেয়েটিকেও অনুরোধ করেছিল প্রতিনিবৃত্ত হতে।
হেসে অবিনাশবাবু বললেন– সাধুজনোচিত অনেক অনেক ধর্মোপদেশ সে দিত তখন। তার পর–।
আবার হাসলেন অবিনাশবাবু। বললেন–সাধুর খোেলস তার জীবন থেকে খসে পড়ে গেল। সে তার দিকে আকৃষ্ট হল এবং উন্মত্ত হয়ে উঠল। চাপার কাছে সে বিবাহ-প্রস্তাব পর্যন্ত করেছিল। সাময়িকভাবে চাপাও তার দিকে আকৃষ্ট হয়। ছোট ভাই মৃত খগেন তখন বড় ভাইকে। বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে। কারণ সন্ন্যাসী হয়ে বড় ভাই যখন গৃহত্যাগ করেছিল, এবং বাপের মৃত্যুশয্যায় স্বমুখে বলেছিল যে, গৃহধর্ম সে করবে না, ছোট ভাইকে মানুষ করে দিয়েই সে আবার চলে যাবে, তখন পৈতৃক বিষয়-আশয়ের ওপর তার কোনো অধিকার নাই। সমস্তর। মালিক সে একা। কিন্তু আসামি নগেন তখন সে-কথা অস্বীকার করলে। বললে, সে মুখের কথার মূল্য কী? প্রকাতেই সে বলেছিল তার সে-মন আর নাই। বলেছিল, তোর জন্যেই আমাকে থাকতে হয়েছে সংসারে; সেই সংসার আজ আমাকে আঁকড়ে ধরেছে। তার জন্যেই আমাকে চাপার সংসবে আসতে হয়েছে। তুই-ই আমাকে চাপার মোহে ঠেলে ফেলে দিয়েছি। আজ আমি চাপাকে বক্টোম করে নিয়ে মালাচন্দন করে আখড়া করব। সম্পত্তির ভাগ আজ আমাকে পেতে হবে, আমি নেব।
বিরোধের একটি জটের সঙ্গে আর-একটি জট যুক্ত হয়ে রূঢ়তর এবং কঠিনতর হয়ে উঠল। তার পরিণতিতে এই ঘটনা। বিষয় নিয়ে বিরোধের শেষ পর্যন্ত গ্রামের পঞ্চজনের মীমাংসায় স্থির হয় যে, নগেন বাপের কাছে যা-ই মুখে বলে থাক, তার যখন কোনো লিখিত পঠিত কিছু নাই এবং বাপ যখন নিজে একথা বলে নি বা উইল করে যায় নি যে, তার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী একমাত্র খগেন হবে, তখন নগেন অবশ্যই সম্পত্তির অংশ পাবে। প্রায় সকল জমিই ভাগ হয়ে বাকি ছিল শুধু একখানি জমি। পঞ্চজনে বলেছিল দুজনে মাপ করে জমিটার মাঝখানে আল দিয়ে নিতে। সেই জমিখানি মাপ করে ভাগ করবার জন্যই দুই ভাই। ঘটনার দিন নদীর অপর পারে গিয়েছিল। এখানে একটা কথা বলার প্রয়োজন আছে। একটি বন্ধুর সঙ্গে মিলে ভাগে খগেনের একটি পান-বিড়ির দোকান ছিল। সে সেই দোকানেই থাকত। সেদিন কথা ছিল নগেন এসে খগেনকে ডাকবে এবং দুই ভাই ওপারে যাবে। কিন্তু নগেন আসে না, দেরি হয়। তখন খগেনই এসে নগেনকে ডাকে। নগেনের মনের মধ্যে তখন এই প্রবৃত্তি ঊকি মেরেছে বলেই আমার বিশ্বাস। একটা দ্বন্দ্ব তখন শুরু হয়েছে। এই সুযোগে যদি কাটা সরাতে পারি তবে মন্দ কী? আবার ভয়-মায়া-মমতা, তারাও স্বাভাবিকভাবে বাধা দিয়ে চলেছিল প্রাণপণ শক্তিতে। স্নেহ, দয়া প্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তিগুলি তখন শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। ওই নদীতে ভাইকে একলা পাওয়ার সুযোগ এলেই অন্তরের গুহায় প্রতীক্ষমাণ হিংসা যে হুঙ্কার। দিয়ে লাফ দিয়ে পড়বে সে তা বুঝতে পারছিল। সেই কারণেই নগেন বাড়ি থেকে বের হয় নি। তারই ডাকবার কথা ছিল খগেনকে। এর প্রমাণ পাই আমরা খগেনের দোকানের অংশীদার বন্ধুর কাছ থেকে। খগেনের সেই অংশীদার বন্ধু বলে, চাপা এবং নগেনের ব্যবহারে খগেন তখন। ক্ষোভে অভিমানে প্রায় পাগল। অভিমানে রাগে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, এ-গ্রামেই সে আর থাকবে। না। বিষয় ভাগ করে নিয়ে, সব বেচে দিয়ে, সে যত শিগগির হয় চলে যাবে অন্যত্র। দোকানের অংশ খগেন সেইদিন সকালে বন্ধুকে বিক্রি করেছিল এবং বলেছিল নদীর ওপারের এই জমিটা ভাগ হলেই সে এ-গ্রাম ছেড়ে প্রথম যাবে নদীর ওপারের গ্রামে। সেখান থেকে জমিজমা নগেনের কোনো শত্রুকে বিক্রি করে চলে যাবে দেশ ছেড়ে। সেই কারণেই সে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল নগেনের। কিন্তু নগেন এল না দেখে বিরক্ত হয়ে বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে নগেনকে ডেকে আনে। নদীর ঘাটের পথেই এই দোকানখানি। খগেনের এই বন্ধু বলে–ওপারে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে দোকান পর্যন্ত এসেও নগেন বলেছিল, খগেন, আজ থাক। আমার শরীরটা আজ ভাল নাই। এবং এও বলেছিল, বিকেলটা আজ ভাল নয়, বৃহস্পতির বারবেলা; তার উপর কেমন গুমট রয়েছে। চৈত্রের শেষ। বাতাসটাতাস উঠলে তোকে নিয়ে মুশকিল হবে।
খগেন ভাল সাঁতার জানত না। জলকে সে ভয় করত। কিন্তু সেদিন সে বলেছিল, না। আর তোমার সঙ্গে সম্পর্ক আমি রাখব না। ওই জমিটায় আল দিতে পারলেই সাতখানা দড়ির শেষখানা কেটে যাবে। আজ শেষ করতেই হবে।
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নগেন বলেছিল, তবে চল।
এর মধ্যে ইঙ্গিতটি যেন স্পষ্ট। তার বর্বর-প্রকৃতির কাছে সে তখন অসহায়। দীর্ঘনিশ্বাসটি তারই চিহ্ন! এবং পরবর্তী ঘটনা, যা এর পূর্বে আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, তাই ঘটেছে। জলমগ্ন অবস্থার সুযোগে বর্বর প্রবৃত্তির তাড়নায় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সমাধা করেছে সে।
অবিনাশবাবু থামলেন। ওদিকে বাইরে পেটা ঘড়িতে একটা বাজল। কোর্টের ঘড়িটা ও থেকে দু মিনিট স্লো।
জ্ঞানেন্দ্রবাবু উঠে পড়লেন।
খাস কামরায় এসে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু।
শরীর আজ অত্যন্ত অবসন্ন। কালকের রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির ফলে সারা দেহখানা ভারী হয়ে রয়েছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। নিজের কপালে হাত বুলিয়ে চোখ বুজে শুয়ে রইলেন। তিনি।
আরদালি টেবিল পেতে দিয়ে গেল। মৃদু শব্দে চোখ বুজেই অনুমান করলেন তিনি। চোখ বুজেই বললেন–শুধু টোস্ট আর কফি। আর কিছু না।
সকালবেলা উঠে থেকেই এটা অনুভব করেছেন। সুরমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি; তিনিও লক্ষ্য করেছেন। বলেছিলেন, শরীরটা যে তোমার খারাপ হল!
তিনি স্বীকার করেন নি। বলেছিলেন–না। শরীর ঠিক আছে। তবে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি কোথা যাবে? তার একটা ছাপ তো পড়বেই। সে তো তোমার মুখের ওপরেও পড়েছে। হেসেছিলেন তিনি।
—তা ছাড়া কালকের বিকেলের ওই আগুনটা–!
–ওঃ! এ স্নান করলেই ঠিক হয়ে যাবে।
বলেই তিনি ফাইল টেনে নিয়েছিলেন। এবং যা প্রত্যাশা করেছিলেন তাই ঘটেছিল; সুরমা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চলে গিয়েছিলেন। ফাইল খুলে বসার অর্থই হল তাই।
—প্লিজ সুরমা, এখন আমাকে কাজ করতে দাও।
সুমতি যেত না। কিন্তু সুরমা যান। এ-কর্তব্যের গুরুত্ব সুরমার চেয়ে কে বেশি বুঝবে? সুরমা বিচারকের কন্যা; বিচারকের স্ত্রী। এবং নিজেও শিক্ষিতা মেয়ে। সুমতিকে শেষ অবধি। বলতে হত—আমাকে কাজ করতে দাও! শেষ পর্যন্ত আমার চাকরি যাবে এমন করলে। সুমতি রাগ করে চলে যেত।
সুমতির প্রকৃতির কথা ভাববার জন্যেই তিনি ফাইল টেনে নিয়েছিলেন। নইলে ফাইল দেখবার জরুরি তাগিদ কিছু ছিল না। আসলে গত রাত্রির সেই চিন্তার স্রেত তার মস্তিষ্কের মধ্যে অবরুদ্ধ জলস্রোতের মত আবর্তিত হচ্ছিল। সত্যের পর সত্যের নব নব প্রকাশ নূতন জলস্রোতের মত এসে গতিবেগ সঞ্চারিত করছিল; কিন্তু সময়ের অভাবে সম্মুখপথে অগ্রসর হতে পারে নি। ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে তিনি শুয়ে পড়েছিলেন। ঘুমও হয় নি। স্বপ্নবিহ্বল একটা তার মধ্যে শুধু পড়ে ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য, স্বপ্নের মধ্যে সুমতি একবারও এসে সামনে দাঁড়ায় নি। সকালবেলায় কিন্তু ঘুম ভাঙতেই সর্বাগ্রে মনে ভেসে উঠেছে সুমতির মুখ। আশ্চর্য! অবচেতনে নয়, সচেতন মনের দুয়ার খুলে চৈতন্যের মধ্যে এসে দাঁড়াচ্ছে সে। সুমতিকে অবলম্বন করেই গতকালে অসমাপ্ত চিন্তাটা মনে জাগল। মনে পড়ে গিয়েছিল, লাইফ ফোর্সের, প্রাণশক্তির জীবন–সঙ্গীত শুনেছিলেন কাল ওই ঝরনার কলরোলের মধ্যে। সে ঝরঝর শব্দ এখনও তাঁর কানে বাজছে। সে এক বিন্দুই হোক আর বিপুল বিশালই হোক, আকাঙ্ক্ষা তার বিশ্বাসী। কিন্তু শক্তির পরিমাণ যেখানে যতটুকু, পাওনার পরিমাণ তার ততটুকুতেই নির্দিষ্ট, তার একটি কণা বেশি নয়। ব্ৰহ্মা-কমণ্ডলুর স্বল্প পরিমাণ, হয়ত একসের বা পাঁচপো জল, গোমুখী থেকে সমগ্র আর্যাবর্ত ভাসিয়ে বঙ্গোপসাগরে এসে মিশেছে তার বিষ্ণুচরণ থেকে উদ্ভব-মহিমার গুণেতে ও ভাগ্যে, সুমতির মুখে এই কথা শুনে তিনি হাসতেন। বলতেন, তা হয় না সুমতি, এক কমণ্ডলু জল ঢেলে দেখ না কতটা গড়ায়! সুমতি রাগ করত, তাঁকে বলত অধার্মিক, অবিশ্বাসী।
কথাটা প্রথম হয়েছিল দার্জিলিঙে বসে।
জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুমতিকে হিমালয়ের মাথার তুষার-প্রাচীর দেখিয়েও কথাটা বোঝাতে পারেন নি। অবুঝ শক্তির দাবি ঠিক সুমতির মতই বিশ্বগ্ৰাসী। সে-দাবি পূর্ণ হয় না। বেদনার মধ্যেই তার বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী, প্রকৃতির অমোঘ নির্দেশ জল আগুন বাতাস–এরা লড়াই করে নিজেকে শেষ করে স্থির হয়; কিন্তু জীবন চিৎকার করে কেঁদে মরে, জানোয়ার চিৎকার করে জানিয়ে যায়; মানুষ ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদে, অভিশাপ দেয়। অবশ্য প্রকৃতির মৌলিক ধর্মকে পিছনে ফেলে মানুষ একটা নিজের ধর্ম আবিষ্কার করেছে। বিচিত্র তার ধর্ম, বিস্ময়কর। মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও তৃষ্ণার্ত মানুষ নিজের মুখের সামনে তুলে ধরা জলের পাত্র অন্য তৃষ্ণার্তের মুখে তুলে দিয়ে। বলে, দাই নিড ইজ গ্রেটার দ্যান মাইন। লক্ষ লক্ষ এমনি ঘটনা ঘটেছে। নিত্য ঘটছে, অহরহ। ঘটছে। কিন্তু এমহাসত্যকে কে অস্বীকার করবে যে, যে-মরণোনুখ তৃষ্ণার্ত নিজের মুখের জল অন্যকে দিয়েছিল, তার তৃষ্ণার যন্ত্রণার আর অবধি ছিল না। ওখানে প্রকৃতির ধর্ম অমোঘ। লঙ্ন। করা যায় না। মানুষের জীবনেও ওই তো দ্বন্দ্ব, ওই তো সংগ্রাম; ওইখানেই তো তার নিষ্ঠুর যন্ত্রণা। প্রকৃতি-ধর্মের দেওয়া শাস্তি! হঠাৎ জ্ঞানেন্দ্রবাবু চোখ খুলে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সামনের দিকে চাইলেন। তাকিয়েই রইলেন।
না। শুধু তো এইটুকুই নয়। আরও তো আছে। ওই তৃষ্ণার্ত মৃত্যুযন্ত্রণার সঙ্গে আরও তো কিছু আছে। যে মরণোনুখ তৃষ্ণার্ত তার মুখের জল অন্যকে দিয়ে মরে তার মুখের ক্ষীণ একটি প্রসন্ন হাস্যরেখা তিনি যেন ওই বিস্ফারিত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছেন।
গত রাত্রে সদ্য-দেখা নদীর ব্যারাজটার কথা মনে পড়ে গেল। ব্যারাজটার ও-পাশে বিরাট রিজারভয়েরে জল জমে থইথই করছে। দেখে মনে হয় স্থির। কিন্তু কী প্রচণ্ড নিম্নাভিমুখী গতির বেগেই না সে ওই গাঁথুনিটাকে ঠেলছে ব্যারাজটার জমাট অণু-অণুতে তার চাপ গিয়ে পৌঁছেছে। সর্বাঙ্গে চাড় ধরেছে।
জীবন বাঙয়। তবু জীবনকে এচাড় এ-চাপ নিঃশব্দে সহ্য করতে হয়। চৌচির হয়ে ফাটতে চায়। তবু সে সহ্য করে।
খ.
আরদালি ট্রে এনে নামিয়ে দিলে।
জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন–কফি বানাও। ছুরি-কাটা সরিয়ে রেখে হাত দিয়েই টোস্ট তুলে নিলেন। আজ সকাল থেকেই প্রায় অনাহারে আছেন। ক্ষিদে ছিল না। রাত্রে ফিরে এসে খেতে সাড়ে বারটা বেজে গিয়েছিল। তারপরও ঘণ্টাখানেক জেগে বসেই ছিলেন। এই চিন্তার মধ্যেই মগ্ন ছিলেন। চিন্তা একবার জাগলে তার থেকে মুক্তি নেই। এ দেশের শাস্ত্ৰকারেরা বলেছেন, চিন্তা অনির্বাণ চিতার মত। সে দহন করে। উপমাটি চমৎকার। তবু তার খুব ভাল লাগে না। চিতা তিনি বলেন না। প্রাণই বহ্নি, বস্তুজগতের ঘটনাগুলি তার সমিধ, চিন্তা তার শিখা। চিন্তাই তো চৈতন্যকে প্রকাশ করে, চৈতন্য ওই শিখার দীপ্তিজ্যোতি। আপনাকে স্বপ্রকাশ করে, আপন প্রভায় বিশ্বরহস্যকে প্রকাশিত করে। যারা গুহায় বসে তপস্যা করেন, তাদের আহার সম্পর্কে উদাসীনতার মর্মটা উপলব্ধি করেন তিনি। রাত্রি জাগরণের ফলে শরীর কি খুব অসুস্থ হয়েছিল তার? না, তা হয় নি। অবশ্য খানিকটা অনুভব করেছিলেন, সমস্ত রাত্রি পাতলা ঘুমের মধ্যেও এই চিন্তা তার মনের মধ্যে ঘুরছে বিচিত্র দুর্বোধ্য স্বপ্নের আকারে। সকালবেলাতেই সে-চিন্তা ধূমায়িত অবস্থা থেকে আবার জ্বলে উঠেছে। তারই মধ্যে এত মগ্ন ছিলেন যে, খেতে ইচ্ছে হয় নি। টোস্ট খেতে ভাল লাগছে। টোস্ট তাঁর প্রিয় খাদ্য। আজ বলে নয়, সেই কলেজজীবন থেকে। প্রথম মুনসেফি জীবনে সকাল-বিকেল বাড়িতে টোস্টের ব্যবস্থা অনেক কষ্ট করেও করতে পারেন নি তিনি। সুমতি কিছুতেই পছন্দ করতে পারত না। সে চাইত লুচি-তরকারি; তরকারির মধ্যে আলুর দম। তাই তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সুরমা সুমতির এই রুচিবাতিকের নাম দিয়েছিল টোস্টোফোবিয়া। এই উপলক্ষ করেও সে সুমতিকে অনেক ক্ষেপিয়েছে। তাদের দুজনকে চায়ের নেমন্তন্ন করে তাকে দিত টোস্ট, ডিম, কেক, চা; সুমতিকে দিত নিমকি, কচুরি, মিষ্টি। সুমতি মনে মনে ক্রুদ্ধ হত কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারত না। অনেক সংস্কার ছিল সুমতির। জাতিধর্মে তার ছিল প্রচণ্ড বিশ্বাস। এবং সেই সূত্রেই তার ধারণা ছিল যে, খাদ্যে যার বিধর্মীয় রুচি, মনেপ্রাণেও সে বিধর্মের অনুরাগী। কতদিন সে বলেছে খেয়েই মানুষ বাঁচে, জন্মেই সবচেয়ে আগে খেতে চায়। সেই খাদ্য যদি এ-দেশের পছন্দ না হয়ে অন্য দেশের পছন্দ হয় তবে সে এ–দেশ ছেড়ে সে-দেশে যাবেই যাবে। এ ধর্মের খাদ্য পছন্দ না হয়ে অন্য ধর্মের। খাদ্য যার পছন্দ সে ধর্ম ছাড়বেই। আমি জানি নিজেদের কিছু তোমার পছন্দ নয়। ধর্ম না, খাদ্য না, আমি না। তাই আমি তোমার চোখের বিষ।
সুরমা এতটা অপমান করতে পারে নি। তিনিও তাকে বলেন নি। সুমতিকে নিয়ে এই জ্বালাতনের খেলা খেলবার জন্য মাঝে মাঝে স্যান্ডউইচ, কাটলেট, কেক, পুডিং তৈরি করে আরদালিকে দিয়ে পাঠিয়ে দিত। লিখত, নিজে হাতে করেছি, জামাইবাবু ভালবাসেন তাই পাঠালাম। স্যান্ডউইচে চিকেন আছে, কাটলেটের সরু হাড়ের টুকরো ভুল হবে না, কেক পুডিঙে মুরগির ডিম আছে। তোর আবার ছোঁয়ার্টুমির বাতিক আছে, ঘরে এক গোয়ালা ঠাকুরের ছবি আছে, তাই জানালাম।
আরদালি চলে গেলে সুমতির ক্ৰোধ ফেটে পড়ত।
ফেলে দিত। শুচিতার দোহাই দিয়ে স্নান করত।
সুরমা সব খবর সগ্ৰহ করত। এবং দেখা হলেই খিলখিল করে হাসত, বলত, কেমন? তিনি বাধ্য হয়ে হাসতেন। হাসতে হত। নইলে জীবন তার অসহ্য হয়ে উঠেছিল।
গ.
বেচারি সুরমা। এইসব নিয়ে তাঁর মনে একটা গোপন গ্লানি পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। মধ্যে মধ্যে অশরীরিণী সুমতি যখন তাঁদের দুজনের মধ্যে এসে দাঁড়ায় তখন ওঁর বিবৰ্ণ মুখ দেখে তিনি তা বুঝতে পারেন। সুমতির মৃত্যুর জন্য দায়ী কেউ নয়, সুরমার সঙ্গে স্পষ্ট কথা তার হয় না, কিন্তু ইঙ্গিতে হয়; বরাবর তিনি বলেছেন-কালও বলেছেন নিজেকে মিথ্যে পীড়ন কোরো না। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে দেখেছি। তবু তার মনের গ্লানি মুছে যায় না, জ্ঞানেন্দ্রনাথ জানেন অন্তরে অন্তরে সুরমা নিজেকেই প্রশ্ন করে, কেন সে এগুলি করেছিল? কে তাকে কষ্ট দিয়ে খেলতে গিয়েছিল? হয়ত সুমতি এবং তার মধ্যে সে এসে এ কৌতুক খেলা না খেলতে গেলে সুমতির এই শোচনীয় পরিণাম হত না। আংশিকভাবে কথাটা সত্য। না। দায়িত্ব প্রথম সুমতির নিজের। সে নিজেই আগুন জ্বালিয়েছিল, সুরমা তাতে ফুঁ দিয়েছিল, ইন্ধন যুগিয়েছিল। ঈর্ষার আগুন। সেই আগুনই বাইরে জ্বলে উঠল। সত্যই, তার মনের আগুন ওই টেনিস ফাইন্যালের দিন তোলা ফটোগ্রাফখানায় ধরে বাইরে বাস্তবে জ্বলে উঠেছিল। টেনিস ফাইন্যাল জেতার পর তোলানো দুজনের ছবিখানা। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে অজ্ঞাতে হেসে ফেলেছিলেন। সুরমার কপিখানা সুরমার ঘরে টাঙানো আছে। ওই টেনিস ফাইনালের কদিন পর। দোকানি ফটোগ্রাফখানা যথারীতি মাউন্ট করে প্যাকেট বেঁধে তিনখানা তাঁর বাড়িতে আর তিনখানা জজসাহেবের কুঠিতে সুরমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তিনি নিজে তখন কোর্টে। তিনি এবং সুরমা দুজনের কেউই জানতেন না যে, ছবিতে তাঁরা পরস্পরের দিকে হাসিমুখে চেয়ে ফেলেছেন। চোখের দৃষ্টিতে গাঢ় অনুরাগের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে। জানলে নিশ্চয় সাবধান হতেন। ফটোগ্রাফারকে বাড়িতে ফটো পাঠাতে বারণ করতেন; হয়ত ও ছবি বাড়িতে ঢোকাতেন। না কোনোদিন। জীবনের ভালবাসার দুর্দম বেগকে তিনি ওই নদীটার ব্যারাজের মত শক্ত বাধে বেঁধেছিলেন। যেদিকে তার প্রকৃতির নির্দেশে গতিপথ, সুরমার দুই বাহুর দুই তটের মধ্যবর্তিনী পথ, প্রশস্ত এবং নিম্ন সমতলভূমির প্রসন্নতায় যে-পথ প্রসন্ন, সে-পথে ছুটতে তাকে দেন নি। জীবনের সর্বাঙ্গে চাড় ধরেছিল, চৌচির হয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তবু সে-বন্ধনকে এতটুকু শিথিল তিনি করেন নি। নাথিং ইমমরাল নাথিং ইললিগাল! নীতির বিচারে, দেশাচার আইন সব কিছুর বিচারে তিনি নিরপরাধ নির্দোষ ছিলেন। কিন্তু সে কথা সুমতি বিশ্বাস করে নি। করতে সে চায় নি। তিনি বাড়ি ফিরতেই সুমতি ছবি কখানা তার প্রায় মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে অগ্নারের পূর্বমুহূর্তের আগ্নেয়গিরির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।
ছবি কখানা সামনে ছড়িয়ে পড়ে ছিল। একখানা টেবিলের উপর, একখানা মেঝের উপর তার পায়ের কাছে, আর একখানাও মেঝের উপরই পড়ে ছিল—তবে যেন মুখ থুবড়ে, উল্টে।
ছবি কখানা দেখে তিনি চমকে উঠেছিলেন।
সুমতি নিষ্ঠুর কণ্ঠে বলে উঠেছিল, লজ্জা লাগছে তোমার? লজ্জা তোমার আছে? নির্লজ্জ, চরিত্রহীন–
মুহূর্তে আত্মসংবরণ করে তিনি ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, সুমতি! তার মধ্যে তাকে সাবধান করে দেওয়ার ব্যঞ্জনা ছিল।
সুমতি তা গ্রাহ্য করে নি। সে সমান চিৎকারে বলে উঠেছিল, ছবিখানার দিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখ, দেখ কোন পরিচয় তার মধ্যে লেখা আছে।
জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বন্ধুত্বের। আর ম্যাচ জেতার আনন্দের।
–কিসের?
–বন্ধুত্বের।
–বন্ধুত্বের? মেয়ের ছেলের বন্ধুত্ব? তার কী নাম?
–বন্ধুত্ব।
–না। ভালবাসা।
–বন্ধুত্বও ভালবাসা। সে বুঝবার সামর্থ্য তোমার নাই। তুমি সন্দেহে অন্ধ হয়ে গেছ। ইতরতার শেষ ধাপে তুমি নেমে গেছ।
—তুমি শেষ ধাপের পর যে পাপের পাক, সেই পাঁকে গলা পর্যন্ত ড়ুবে গেছ। তুমি চরিত্রহীন, তুমি ইতরের চেয়েও ইতর, অনন্ত নরকে তোমার স্থান হবে না।
বলেই সে ঘর থেকে চলে গিয়েছিল। কর্মক্লান্ত ক্ষুধার্ত তখন তিনি; কিন্তু বিশ্রাম আহার মুহূর্তে বিষ হয়ে উঠল—তিনিও বেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। ভয়ও পেয়েছিলেন; সুমতিকে নয়, নিজের ক্রোধকে। উদ্যত ক্ৰোধ এবং ক্ষোভকে সংবরণ করবার সুযোগ পেয়ে তিনি যেন বেঁচে গিয়েছিলেন। উন্মত্তের মত মৃত্যু কামনা করেছিলেন নিজের। বৈধব্য-শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন সুমতিকে। বাইসিক্লে চেপে তিনি শহরের এক দূর-প্রান্তে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে পাথর-হয়ে-যাওয়া মানুষের মত বসে ছিলেন। প্রথম সে শুধু উন্মত্ত চিন্তা না, চিন্তা নয় কামনা, মৃত্যুকামনা, সংসারত্যাগের কামনা, সুমতির হাত থেকে অব্যাহতির কামনা। তারপর ধীরে ধীরে সে-চিন্তা স্থির হয়ে এসেছিল—দাউদাউ-করে-জ্বালা গ্রহের জ্যোতিৰ্মান হয়ে ওঠার মত। সেই জ্যোতিতে আলোকিত করে অন্তর তন্নত করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁজে দেখেছিলেন। বিশ্লেষণ করেছিলেন, বিচার করে দেখেছিলেন। পান নি কিছু। নাথিং ইম্মর্যাল, নাথিং ইললিগাল। কোনো দুর্নীতি না, কোনো পাপ না। বন্ধুত্ব। গাঢ়তম বন্ধুত্ব। সুরমা তাঁর অন্তরঙ্গতম বন্ধু, সেকথা তিনি স্বীকার করেন। আরও ভাল করে দেখেছিলেন। না, তার থেকেও কিছু বেশি। সুরমাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও আছে। আছে। পরমুহূর্তে আরও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছিলেন। না! পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নয়। পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নাই,না পাওয়ার জন্য অন্তরে ফন্ধুর মত বেদনার একটি ধারা বয়ে যাচ্ছে শুধু। এবং সে-ধারা বন্যার প্রবাহে দুই কূল ভেঙেচুরে দেবার জন্য উদ্যত নয়; নিঃশব্দে জীবনের গভীরে অশ্রুর উৎস হয়ে শুধু আবর্তিতই হচ্ছে। আজীবন হবে।
চিন্তার দীপ্তিকে প্রসারিত করছিলেন ন্যায় এবং নীতির বিধান-লেখা অক্ষয় শিলালিপির উপর। অবিচলিত ধৈর্যের সঙ্গে জীবনের শ্ৰেষ্ঠ বুদ্ধি প্ৰয়োগ করে প্রায় ধ্যানযোগের মধ্যে সেলিপির পাঠোদ্ধার করেছিলেন। কোনো সমাজ, কোনো রাষ্ট্র, কোনো ধর্মের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নি; কোনো ব্যাকরণের কোনো বিশেষ পদার্থ গ্রহণ করেন নি; এবং পাঠ শেষ করে নিঃসংশয় হয়ে তবে তিনি সেদিন সেখান থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেছে। দেশলাই জ্বেলে ঘড়ি দেখে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। এতটা রাত্রি! জানুয়ারির প্রথম সময়টা, রাত্রি পৌঁনে দশটা! আপিস থেকে বেরিয়েছিলেন পাঁচটায়। বাড়ি থেকে বোধহয় ছটায় বেরিয়ে এসেছেন। পৌঁনে দশটা। প্রায় চার ঘণ্টা শুধু ভেবেছেন। সিগারেট পর্যন্ত খান নি। তখন তিনি প্রচুর সিগারেট খেতেন। সুমতির তাতেও আপত্তি ছিল।
ঘ.
শান্ত চিত্তে তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন; ক্রোধ অসহিষ্ণুতা সমস্ত কিছুকেই কঠিন সংযমে সংযত করেছিলেন। সুমতি উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে ছিল। বাইসিক্ল তুলে রাখবার জন্য আরদালিকে ডেকে পান নি। চাকরটাও ছিল না। ঠাকুর! ঠাকুরেরও সাড়া পান নি। ভেবেছিলেন, সকলেই বোধহয় তাঁর সন্ধানে বেরিয়েছে। মনটা চি চি করে উঠেছিল। কাল লোকে বলবে কী। সন্ধান যেখানে করতে যাবে সেখানে সকলেই চকিত হয়ে উঠবে। তবুও কোনো কথা বলেন নি। নিঃশব্দে পোশাক ছেড়ে, মুখহাত ধুয়ে, ফিরে এসে শোবার ঘরে একখানা চেয়ারে বসেছিলেন। প্রয়োজন হলে ওই চেয়ারেই সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে দেবেন। সুমতি ঠিক একভাবেই শুয়ে ছিল, অনড় হয়ে। শেষ পর্যন্ত তিনি বলেছিলেন, আমাকে খুঁজতে তো এদের সকলকে পাঠাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না।
এবার সুমতি উত্তর দিয়েছিলেন, খুঁজতে কেউ যায় নি। কারণ তুমি কোথায় গেছ, সে-কথা অনুমান করতে কারুর তো কষ্ট হয় না। ওদের আজ আমি ছুটি দিয়েছি! বাজারে যাত্রা হচ্ছে, ওরা যাত্রা শুনতে গেছে। তারপরই উঠে সে বসেছিল। বলেছিল—আমি ইচ্ছে করেই ছুটি দিয়েছি, তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।
চোখ দুটো সুমতির লাল হয়ে উঠেছে। দীর্ঘক্ষণ অবিশ্রান্ত কেঁদেছিল। মমতায় তাঁর অন্তরটা টনটন করে উঠেছিল। তিনি অকৃত্রিম গাঢ় স্নেহের আবেগেই বলেছিলেন, তুমি অত্যন্ত ছেলেমানুষ সুমতি। একটা কথা তুমি কেন বুঝছ না–
–আমি সব বুঝি। তোমার মত পণ্ডিত আমি নই। সেই অধার্মিক বাপমায়ের আদুরে মেয়ের মত লেখাপড়ার ঢঙও আমি জানি না, কিন্তু সব আমি বুঝি।
ধীর কণ্ঠেই জ্ঞানেন্দ্রবাবু বলেছিলেন, না। বোঝ না।
–বুঝি না? তুমি সুরমাকে ভালবাস না?
–বাসি। বন্ধু বন্ধুকে যেমন ভালবাসে তেমনি ভালবাসি।
–বন্ধু, বন্ধু, বন্ধু! মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে! বল, ঈশ্বরের শপথ করে বল, ওর সঙ্গ তোমার যত ভাল লাগে, আমার সঙ্গ তোমার তেমনি ভাল লাগে?
–এর উত্তরে একটা কথাই বলি, একটু ধীরভাবে বুঝে দেখ–তোমার আমার সঙ্গ জীবনে জীবনে, অঙ্গে অঙ্গে, শত বন্ধনে জড়িয়ে আছে। তোমার বা আমার একজনের মৃত্যুতেও সে-বন্ধনের গ্রন্থি খুলবে না। আমি কাছে থাকি দূরে থাকি একান্তভাবে তোমার–
সুমতি চিৎকার করে উঠেছিলনা, মিথ্যা কথা।
—না মিথ্যা নয়। মনকে প্ৰসন্ন কর সুমতি, ওই প্রসন্নতাই জীবনের শ্রেষ্ঠ মিষ্টতা। ওর অভাবে অন্ন যে অন্ন তাও তিক্ত হয়ে যায়। তুমি যদি সত্যই আমাকে ভালবাস তবে কেন তোমার এমন হবে? তোমার সঙ্গেই তো আমার এক ঘরে বাস, এক আশা, এক সঞ্চয়! সুরমা তো অতিথি। সে আসে, দু দণ্ড থাকে, চলে যায়। তার সঙ্গে মেলামেশা তো অবসরসাপেক্ষ। খেলার মাঠে, আলোচনার আসরে তার সঙ্গে আমার সঙ্গ।
মিনতি করে বলেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ, কিন্তু সুমতি তীব্র কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, তাই তো বলছি। আমার সঙ্গে, আমার বন্ধনে তুমি কাটার শয্যায় শুয়ে থাক, সাপের পাকে জড়িয়ে থাক অহরহ! অল্পক্ষণের জন্য ওর সঙ্গেই তোমার যত আনন্দ, যত অমৃতস্পৰ্শ।
একটি ক্ষীণ করুণ হাস্যরেখা প্রৌঢ় জ্ঞানেন্দ্রনাথের মুখে ফুটে উঠল। আনন্দ এবং অমৃতস্পর্শ শব্দ দুটি তার নিজের, সুমতি দুটি গ্রাম্য অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছিল। তিনি তখন ক্ষুধার্ত, প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের ক্রিয়া তাঁর চৈতন্যকে জেলখানার বেত্ৰদণ্ডপাওয়া আসামির মত নিষ্করুণ আঘাত হেনে চলেছে। বেত্ৰাঘাত-জর্জর কয়েদিরা কয়েক ঘা বেত খাওয়ার পরই ভেঙে পড়ে। তার চৈতন্যও তাই পড়েছিল; প্রাণপণে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করেও তিনি পারেন। নি। অথবা কাচের ফানুস ফাটিয়ে দপ-করে-জ্বলে-ওঠা লন্ঠনের শিখার মত অগ্নিকাণ্ডে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন নিজেকে। আর সংযমের কাচের আবরণে অন্তরকে ঢেকে নিজেকে আর স্নিগ্ধ এবং নিরাপদ করে প্রকাশ করতে পারেন নি। ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ অন্তর আগুনের লকলকে বিশ্বগ্ৰাসী শিখার মত আত্মপ্রকাশ করেছিল। তিনি বলেছিলেন,তুমি যে কথা দুটো বললে, ও উচ্চারণ করতে আমার জিভে বাধে। ওর বদলে আমি বলছি আনন্দ আর অমৃতস্পৰ্শ। হ্যাঁ, সুরমার সংস্পর্শে তা আমি পাই। সত্যকে অস্বীকার আমি করব না। কিন্তু কেন পাই, তুমি বলতে পার? আর তুমি কেন তা দিতে পার না?
—তুমি ভ্ৰষ্টচরিত্র বলে পারি না। আর ভ্ৰষ্টচরিত্র বলেই তুমি ওর কাছে আনন্দ পাও! মাতালরা যেমন মদকে সুধা বলে।
–আমি যদি মাতালই হই সুমতি, মদকেই যদি আমার সুধা বলে মনে হয়, তবে আমাকে ঘৃণা কর, আমাকে মুক্তি দাও।
নিষ্ঠুর শ্লেষের সঙ্গে সুমতি মুহূর্তে জবাব দিয়েছিল সাপের ছোবলের মত—ভারি মজা হয়। তা হলে, না?
বিচলিত হয়েছিলেন তিনি সে-দংশনের জ্বালায়, কিন্তু বিষে তিনি ঢলে পড়েন নি। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে আবার তিনি ধীরকণ্ঠে বলেছিলেন—শোন সুমতি। আমার ধৈর্যের বধ তুমি ভেঙে দিচ্ছ। তার উপর আমি ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত। তোমাকে আমার শেষ কথা বলে দি। তোমার সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে গেছে সামাজিক বিধানে। সে-বিধান অনুসারে তুমি আমি এ-বন্ধন ছিন্ন করতে পারি না। তুমি স্ত্রী, আমি স্বামী। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তোমার ভরণপোষণ করব, তোমাকে রক্ষা করব, আমার উপাৰ্জন আমার সম্পদ তোমাকে দোব। আমার গৃহে তুমি হবে গৃহিণী। আমার দেহ তোমার। সংসারে যা বস্তু, যা বাস্তব, যা হাতে তুলে দেওয়া যায়, তা আমি তোমাকেই দিতে প্রতিশ্রুত, আমি তোমাকে তা দিয়েছি, তা আমি চিরকালই দোব। একবিন্দু। প্রতারণা করি নি। কোনো অনাচার করি নি।
—কর নি?
–না।
–ভালবাস না তুমি সুরমাকে? এতবড় মিথ্যা তুমি শপথ করে বলতে পার?
–তোমার অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে কাউকে ভালবাসা অনাচার নয়।
–নয়?
নানা-না। তার আগে তোমাকে জিজ্ঞাসা করব, তুমি বলতে পার, ভালবাসার আকার কেমন? তাকে হাতে ছোঁয়া যায়? তাকে কি হাতে তুলে দেওয়া যায়? দিতে পার? তোমার অকপট ভালবাসা আমার হাতে তুলে দিতে পার?
এবার বিস্মিত হয়েছিল সুমতি। একমুহূর্তে উত্তর দিতে পারে নি। মুহূর্ত কয়েক স্তব্ধ থেকে বলেছিল—হেঁয়ালি করে আসল কথাটাকে চাপা দিতে চাও। কিন্তু তা দিতে দেব না।
—হেঁয়ালি নয়। হেঁয়ালি আমি করছি না। সুমতি, ভালবাসা দেওয়ার নয়, নেওয়ার বস্তু। কেউ কাউকে ভালবেসে পাগল হওয়ার কথা শোনা যায়, দেখা যায়, সেখানে আসল মহিমা যে ভালবাসে তার নয়; যাকে ভালবাসে মহিমা তার। মানুষ আগে ভালবাসে মহিমাকে তারপর সেই মানুষকে। কোথাও মহিমা রূপের, কোথাও কোনো গুণের। সুরমার মহিমা আছে, সে হয়ত তুমি দেখতে পাও না, আমি পাই, তাই আমি তাকে প্রকৃতির নিয়মে ভালবেসেছি।
—লজ্জা করছে না তোমার? মুখে বাঁধছে না? চিৎকার করে উঠেছিল সুমতি।
–না। সবল দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন তিনি, কাঁপে নি সে কণ্ঠস্বর। চোখ তার সুমতির চোখ থেকে একেবারে সরে যায় নি। মাটির দিকে নিবদ্ধ হয় নি। সুমতিই যেন বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত পরে সে বিভ্রান্তি কাটাতে পেরেছিল। বিভ্রান্তি কাটিয়ে হঠাৎ সে চিৎকার করে বলে উঠেছিল—মুখ তোমার খসে যাবে। ও-কথা বোলো না।
—লক্ষবার বলব সুমতি। চিৎকার করে সর্বসমক্ষে বলব। মুখ আমার খসে যাবে না! আমি নির্দোষ, আমি নিস্পাপ।
—নিষ্পাপ? নিষ্ঠুরভাবে হেসে উঠেছিল সুমতি। তারপর বলেছিল-ধৰ্ম দেবে তার সাক্ষি!
–ধর্ম? হেসে উঠেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ ধর্মকে তুমি জান না, ধর্মের দোহাই তুমি দিয়ে না। তোমার অবিশ্বাসের ধর্ম শুধু তোমার। আমার ধৰ্ম মানুষের ধর্ম, জীবনের ধর্ম। সে তুমি বুঝবে না। না বোঝ, শুধু এইটুকু জেনে রাখতোমাকে বিবাহের সময় যে যে শপথ করে আমি গ্রহণ করেছি তার সবগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে আমি পালন করেছি। করছি। যতদিন বাঁচব করবই।
–কর্তব্য। কিন্তু মন?
—সে তো বলেছি, সে কাউকে দিলাম বলে নিজে দেওয়া যায় না। যার নেবার শক্তি আছে, সে নেয়। ওখানে মানুষের বিধান খাটে না। ও প্রকৃতির বিধান। যতটুকু তোমার ও-বস্তু নেবার শক্তি, তার এককণা বেশি পাবে না। তবে হ্যাঁ, এটুকু মানুষ পারে, মনের ঘরের হাহাকারকে লোহার দরজা এটে বন্ধ রাখতে পারে। তা রেখেও সে হাসতে পারে, কর্তব্য করতে পারে, বাঁচতে পারে। তাই করব আমি। আমাকে তুমি খোঁচা মেরে মেরে ক্ষতবিক্ষত কোরো না।
সুমতি এ কথার আর উত্তর খুঁজে পায় নি। অকস্মাৎ পাগলের মত উঠে টেবিলের উপর রাখা ফাইলগুলি ঠেলে সরিয়ে, কতক নিচে ফেলে তছনছ করে দিয়েছিল। তিনি তার হাত চেপে ধরে বলেছিলেন–কী হচ্ছে?
—কোথায় ফটো?
–ফটো কী হবে?
—পোড়াব আমি।
–না।
–না নয়। নিশ্চয় পোড়া আমি।
–না।
–দেবে না?
–না। ও ফটো আমি ঘরে রাখব না, কিন্তু পোড়াতে আমি দেব না।
সুমতি মাথা কুটতে শুরু করেছিল—দেবে না? দেবে না?
জ্ঞানেন্দ্রবাবু ড্রয়ার থেকে ফটো ক-খানা বের করে ফেলে দিয়েছিলেন। শুধু ফটো কখানাই নয়, চুলের-গুচ্ছ-পোরা খামটাও। রাগে আত্মহারা সুমতি সেটা খুলে দেখে নি। গোছাসমেত নিয়ে গিয়ে উনোনে পুরে দিয়েছিল।
তাঁরও আর সহ্যের শক্তি ছিল না। আহারে প্রবৃত্তি ছিল না। শুধু চেয়েছিলেন সবকিছু ভুলে। যেতে। তিনি আলমারি খুলে বের করেছিলেন ব্রান্ডির বোতল। তখন তিনি খেতে ধরেছেন। নিয়মিত, খানিকটা পরিশ্রম লাঘবের জন্য। সেদিন অনিয়মিত পান করে বিছানায় গড়িয়ে পড়েছিলেন।
সুমতির অন্তরের আগুন তখন বাইরে জ্বলেছে। সে তখন উন্মত্ত। শুধু ওই ক-খানা ফটো উনোনে খুঁজেই সে ক্ষান্ত হয় নি, আরও কয়েকখানা বাঁধানো ছবি ছিল সুরমার, তার একখানা সুরমার কাছে সুমতি নিজেই চেয়ে নিয়েছিল আর কখানা সুরমা আত্মীয়তা করে দিয়েছিল, সে ক-খানাকেও পেড়ে আছড়ে কাচ ভেঙে ছবিগুলোকে আগুনে খুঁজে দিয়েছিল আর তার সঙ্গে খুঁজে দিয়েছিল সুরমার চিঠিগুলো। ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বলে তবে এসে সে শুয়েছিল। ঘণ্টা দুয়েক পর ওই আগুনই লেগেছিল চালে। সুমতির অন্তরের আগুন। প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। বনস্পতি শাখায় শাখায় পত্রে পল্লবে ফুলে ফলে যে তেজশক্তি করে সৃষ্টিসমারোহ, সেই তেজই পরস্পরের সংঘর্ষের পথ দিয়ে আগুন হয়ে বের হয়ে প্রথম লাগে শুকনো পাতায়, তারপর জ্বালায় বনস্পতিকে; তার সঙ্গে সারা বনকে ধ্বংস করে। অঙ্গার আর ভস্মে হয় তার শেষ পরিণতি।
জ্ঞানেন্দ্রবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। পুড়ে ছাই হয়েও সুমতি নিষ্কৃতি দেয় নি।
বাইরে ঢং ঢং শব্দে দুটোর ঘণ্টা বাজল। কফির কাপটা তাঁর হাতেই ছিল। নামিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন। নামিয়ে রাখলেন এতক্ষণে।
আরদালি এসে এজলাসে যাবার দরজার পরদা তুলে ধরে দাঁড়াল। জুরী উকিল আগেই এসে বসেছেন আপন আপন আসনে। আদালতের বাইরে তখন সাক্ষীর ডাক শুরু হয়েছে।
জ্ঞানেন্দ্রনাথ এসে নিজের আসন গ্রহণ করলেন। হাতে পেনসিলটি তুলে নিলেন। দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলেন খোলা দরজা দিয়ে সামনের কম্পাউণ্ডের মধ্যে। মন ড়ুবে গেল গভীর থেকে গভীরে। সেখানে সুমতি নেই, সুরমা নেই, বিশ্বসংসারই বোধ করি নেই—আছে শুধু একটা প্রশ্ন, ওই আসামি যে প্রশ্ন করেছে। সাধারণ দায়রা বিচারে এ-প্রশ্ন এমনভাবে এসে দাঁড়ায়। না। সেখানে প্রশ্ন থাকে আসামি সম্পর্কে। আসামির দিকে তাকালেন তিনি। চমকে উঠলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ। আসামির পিছনে কী ওটা? কে?—না! কেউ নয়, ওটা ছায়া, স্কাইলাইটের ভিতর দিয়ে ঈষৎ তির্যকভাবে আকাশের আলো এসে পড়েছে আসামির উপর। একটা ছায়া পড়েছে ওর পিছনের দিকে। ঠিক যেন কে দাঁড়িয়ে আছে।
প্রথম সাক্ষী এসে দাঁড়াল কাঠগড়ার মধ্যে। তদন্তকারী পুলিশ কর্মচারী। হলপ নিয়ে সে বলে গেল—খগেনের মৃত্যু সংবাদ প্রথম পাওয়ার কথা, থানার পাতায় লিপিবদ্ধ করার কথা। আসামি নগেনই সংবাদ এনেছিল। জ্ঞানেন্দ্রবাবু আবার তাকালেন আসামির দিকে। আসামির। পিছনের ছায়াটা দীর্ঘতর হয়ে পূর্বদিকের দেওয়ালের গায়ে গিয়ে পড়েছে। বর্ষা-দিনের অপরাহ্নের আলো এবার পশ্চিম দিকের জানালাটা দিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়েছে। দারোগার সাক্ষি শেষ হল।
ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে চারটে বাজল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন– কাল জেরা হবে। উঠলেন তিনি। আঃ! তবু যেন আচ্ছন্নতা কাটছে না!
জ্ঞানেন্দ্রনাথ ফিরে এলেন সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্নের মত অবস্থায়। দুদিন পর। মামলার শেষ দিন। সব শেষ করে বাড়ি ফিরলেন। পৃথিবীর সবকিছু তার দৃষ্টি মন-চৈতন্যের গোচর থেকে সরে গেছে। কোনো কিছু নেই। চোখের সম্মুখে ভাসছে আসামির মূর্তি। কানের মধ্যে বাজছে দুই পক্ষের উকিলের যুক্তি। মনের মধ্যে রয়েছে সমস্ত ঘটনাগুলির বিবরণ থেকে রচনা-করা পট। আর চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে আসামির কথাগুলি।
থানা থেকে শুরু করে দায়রা আদালতে এই বিচার পর্যন্ত সর্বত্র সে একই কথা বলে। আসছে। হুজুর, আমি জানি না আমি দোষী কি নির্দোষ। ভগবান জানেন, আর হুজুর বিচার করে বলবেন। এবং এই কথাগুলি যেন শুধু কথা নয়। তার যেন বেশি কিছু। জবাবের মধ্যে অতি কঠিন প্রশ্ন উপস্থিত করেছে সে। কণ্ঠস্বরের সকরুণ অসহায় অভিব্যক্তি, চোখের দৃষ্টির সেই অসহায় বিহ্বলতা, তার হাত জোড় করে নিবেদনের সেই অকপট ভঙ্গি, সব মিলিয়ে সে একটা আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছে তার চৈতন্যের উপর। অপরাধ করি নি জবাব দিয়েই শেষ করে নি, প্রশ্ন করেছে—বিচারক তুমি বল সে-কথা! ঈশ্বরকে যেমনভাবে যুগে যুগে মানুষ প্রশ্ন করেছে। ঠিক তেমনিভাবে।
এ-প্রশ্ন তার সমস্ত চৈতন্যকে যেন সচকিত করে দিচ্ছে; ঘুমন্ত অবস্থায় চোখের উপর তীব্র আলোর ছটা এবং উত্তাপের স্পর্শে জেগে উঠে মানুষ যেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে, তেমনি বিহ্বল হয়ে পড়েছেন তিনি। ওই লোকটির সেই চরম সঙ্কটমুহূর্তের অবস্থার কথা কল্পনা করতে হবে। স্থলচারী মুক্তবায়ুস্তরবাসী জীব নিচ্ছিদ্র শ্বাসরোধী জলের মধ্যে ড়ুবে গিয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে কোন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল, কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, অনুমান করতে হবে। মৃত্যুর সম্মুখে সীমাহীন ঘন কালো একটা আবেষ্টনী মুহূর্তে মুহূর্তে তাকে ঘিরে ধরছিল। নিদারুণ ভয়, নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণার মধ্যে আজকের মানুষকে, হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের সভ্য মানুষকে প্রাগৈতিহাসিক আরণ্যযুগের আদিমতম মানুষের জান্তব চেতনার যুগে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে দয়া নাই, মায়া নাই, স্নেহ নাই, মমতা নাই, কৰ্তব্য নাই, আছে শুধু আদিমতম প্রেরণা নিয়ে প্রাণ, জীবন।
কল্পনা করতে তিনি পেরেছিলেন। কল্পনা নয়, ঠিক এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্মৃতি তার মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল। তিনি অনুভব করতে পারছিলেন।
খ.
অকস্মাৎ মর্মান্তিক শ্বাসরোধী সে এক নিষ্ঠুর যন্ত্রণা। কে যেন হৃৎপিণ্ডটা কঠিন কঠোর হাতের মুঠোয় চেপে ধরেছিল। তার সঙ্গে মস্তিষ্কে একটা জ্বালা। কাশতে কাশতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।ক যন্ত্রণায় আতঙ্ক-বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলেও কিছু বুঝতে পারেন নি। এক ঘন সাদা পুঞ্জ পুঞ্জ কিছু তাকে যেন ছেয়ে ফেলেছে। আর একটা গন্ধ। আর চোখে পড়েছিল ওই পুঞ্জ পুঞ্জ আবরণকে প্রদীপ্ত-করা একটা ছটা।
ধোঁয়া! মুহূর্তে উপলব্ধি হয়েছিল আগুন। ঘরে আগুন লেগেছে।
মাথার উপর গোটা ঘরের চালটা আগুন ধরে জ্বলছে। জানুয়ারিশেষের শীতে ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। ধোঁয়ায় ঘরখানা বিষবাষ্পচ্ছন্ন আদিম পৃথিবীর মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। ঘরের আলো নিভে গেছে। আগুনের ছটায় রাঙা ধোঁয়া শুধু। তার সঙ্গে সে কী উত্তাপ! তাঁর নিজের মাথার মধ্যে তখন মদের নেশার ঘোর এক যন্ত্ৰণা। মৃত্যু যেন অগ্নিমুখী হয়ে গিলতে আসছে তাকে এবং সুমতিকে। সুমতি শুয়ে ছিল মেঝের উপর। সে তখন জেগেছে, কিন্তু ভয়ার্তবিহ্বল চোখের কোটর থেকে চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। বিহ্বলের মত শুধু একটা চিৎকার।
তিনি তার মধ্যেও নিজেকে সংযত করে সাহস এনে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ধোঁয়ার মধ্যে সব ঢেকে আসছিল, চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, তারই মধ্যে তিনি গিয়ে সুমতির হাত ধরে বলেছিলেন—এস, শিগগির এস।
সুমতি আঁকড়ে ধরেছিল তাঁর হাত।
কোথায় দরজা? কোন দিকে?
সুমতি সেদিন দরজায় খিল, উপরে নিচে দুটো ছিটকিনি লাগিয়ে তবে শুয়েছিল। এগুলি খুলতে খুলতে তার শব্দে নিশ্চয় ওর ঘুম ভাঙবে। তিনি জানেন, ওর ভয় ছিল, যদি রাত্রে সন্তৰ্পণে দরজা খুলে বেরিয়ে যান।
তবুও ধৈর্য হারান নি। প্রাণপণে নিজের শিক্ষা ও সংযমে স্থির রেখেছিলেন নিজেকে। একে একে ছিটকিনি খিল খুলে বেরিয়ে এসেছিলেন বারান্দায়। সেখানে নিশ্বাস সহজ হয়েছিল, কিন্তু গোটা বারান্দার চালটা তখন পুড়ে খসে পড়ছে। একটা দিক পড়েছে, মাঝখানটা পড়ছে। মাথার উপরে নেমে আসছে জ্বলন্ত আগুনের একটা স্তর। ঠিক এই মুহূর্তেই হঠাৎ সুমতি চিৎকার করে উঠল, এবং ভারী একটা বোঝার মত মুখ থুবড়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। তার আকর্ষণে সঙ্গে সঙ্গে তিনিও পড়লেন। তাঁদের উপরে খসে পড়ল চালকাঠামোর সঙ্গে বাঁধা একটি স্তরবন্দি রাশি রাশি জ্বলন্ত খড়। সে কী যন্ত্রণা! বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড বিলুপ্ত হয়ে গেল এক মহা অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে। তবু তিনি ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাধা পড়ল। হাতটা কোথা আটকেছে! ওঃ, সুমতি ধরে আছে! মুহূর্তে তিনি হাত ছাড়িয়ে উঠে কোনো রকমে দাওয়ার উপর থেকে নিচে লাফিয়ে নেমে এসে খোলা উঠানে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি অবস্থাটা বুঝতে পারছেন। এ-অবস্থা কল্পনা ঠিক করা যায় না। তিনি পেরেছেন, ভুক্তভোগী বলেই তিনি বুঝতে পেরেছেন।
ঈশ্বর জানেন। আর হুজুর বিচার করে বলবেন। আসামির কথা কটি তার চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে এখনও ধ্বনিত হচ্ছে।
ডিফেন্সের উকিলও আত্মরক্ষার অধিকারের মৌলিক প্রশ্নটিকেই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। জীবনের জন্মগত প্রথম অধিকার, নিজের বাবার অধিকার তার সর্বাগ্রে। এই স্বত্বের অধিকারী হয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। দণ্ডবিধির সেকশন এইট্টি-ওয়ানের নজির তুলেছেন। একটি ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি। হতভাগ্য আসামি। সেকশন এইট্টি-ওয়ান ওকে জলমগ্ন অবস্থাতেও গলা টিপে ধরবার অধিকার দেয় নি। আসামির উকিল অবশ্য সুকৌশলে ও প্রয়োজনীয় অংশটুকু তুলে ধরেছেন জুরীদিগের সামনে।
A and B, swimming in the sea after a shipwreck, get hold of a plank not large enough to support both, A pushes B, who is drowned. This, in the opinion of Sir James Stephen, is not a crime…
কিন্তু এর পরও একটু যে আছে। স্যার জেমস স্টিফেন আরও বলেছেন,
……. as thereby A does B no direct bodily harm but leaves him to his chance of another plank.
এ-সেকশন যে তার মনের মধ্যে উজ্জ্বল অক্ষরে খোদাই করা আছে।
এই বিধানটি নিয়ে যে তিনি বার বার যাচাই করে নিয়ে নিজেকে মুক্তি দিয়েছেন।
সুমতির হাতখানাই শুধু তিনি ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন, কোনো আঘাত তিনি করেন নি। আঘাত করে তার হাত ছাড়ালে অপরাধ হত তার। অবশ্য সুমতির দেহে একটা ক্ষতচিহ্ন ছিল; সেটা কারুর দেওয়া নয়, সেটা সুমতিকে তার নিয়তির পরিহাস, সেটা তার স্বকর্মের ফল, সুমতির পায়ের তলায় একটা দীর্ঘ কাচের ফলা আমূল ঢুকে বিঁধে ছিল। বাঁধানো যে ফটো কখানা আছড়ে সে নিজেই ভেঙেছিল সেই ফটো-ভাঙা কাচের একটা লম্বা সরু টুকরো। সেইটে বিঁধে যাওয়াতেই অমনভাবে সে হঠাৎ সেই চরম সংকটের মুহূর্তটিতেই থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল।
বিধিলিপি! বিধিলিপির মতই বিচিত্ররূপ এক অনিবার্য পরিণাম সুমতি নিজের হাতে তৈরি করেছিল। নিষ্কৃতির একটি পথও খোলা রাখে নি। নিজের হাতে নীরন্ধ্র করে রুদ্ধ করে দিয়েছিল। জীবন-প্রকৃতি আর জয়প্রকৃতি একসঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্ষুব্ধ হলে আর রক্ষা থাকে না। সেদিন তাদের জীবনে এমনি একটা পরিণাম অনিবার্যই ছিল। সুমতির হাতের জ্বালানো আগুন ওইভাবে ঘরে না লাগলে অন্যভাবে এমনি পরিণাম আসত। তিনি নিজে আত্মহত্যা করতেন। সুমতির ঘুম গাঢ় হলেই তিনি আত্মঘাতী হবেন স্থির করেই শুয়েছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত মদের ঘোরে তার চৈতন্যের সঙ্গে সংকল্পও অসাড় হয়ে পড়েছিল। তিনি আত্মহত্যা করলে সুমতিও আত্মঘাতিনী হত তাতে তাঁর সন্দেহ নেই। কায়ার সঙ্গে ছায়ার মত সে তার জীবনকে আঁকড়ে ধরে ছিল।
গ.
কুঠির কম্পাউন্ডে গাড়ি থামাতেই তার মন বাস্তবে ফিরে এল। জজ সাহেবের কুঠি। বর্ষার ম্লান অপরাহ্র। আকাশে মেঘের আস্তরণ দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। বাড়িটা নিস্তব্ধ। কই সুরমা কই? বাইরে কোথাও নেই সে!
নেই ভালই হয়েছে।
কিন্তু বাইরের এই প্রকৃতির রূপ তার ওপর যেন একটা ছায়া ফেলেছে। স্লান বিষণ্ণ স্তব্ধ হয়ে রয়েছে সুরমা সেই বাবুর্চিখানায় আগুন-লাগার দিন থেকে।
গাড়ি থেকে নেমে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুহূর্তের জন্য দাঁড়ালেন।
একটা ছায়া। তাঁর নিজেরই ছায়া। পাশের সবুজ লনের উপর নিজেকে প্রসারিত করে দিয়েছে। আসামি নগেনের চেয়ে অনেক দীর্ঘ তার ছায়া। নগেনের চেয়ে অনেকটা লম্বা তিনি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হলেন বাঙলোর দিকে। সরাসরি আপিস-ঘরের দিকে।
বেয়ারা এসে দাঁড়ালজুতো খুলবে
–না। হাত ইশারা করে বললেন–যাও। যাও।
ঘরে ঢুকে গেলেন তিনি। আপিস-ঘর পার হয়ে এসে ঢুকলেন মাঝখানকার বড় ঘরখানায়। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন। ঘরখানা প্রায় প্রদোষান্ধকারের মত ছায়াচ্ছন্ন; তয় ছায়াটা পর্যন্ত মিলিয়ে গেছে। তিনি এগিয়ে গিয়ে সামনের দেয়ালে টাঙানো পরদাঢাকা ছবিটার উপর থেকে পরদাটা টেনে খুলে দিলেন।
সুমতির অয়েলপেন্টিং আবছায়ার মধ্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, শুধু সাদা বড় চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে।
ছবিখানার দিকে নিম্পলক চোখে চেয়ে স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলেন তিনি।
সে কি অভিযোগ করছে?
তিনি কি দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন?
—তুমি এ-ঘরে? বাইরে থেকে বলতে বলতেই ঘরে ঢুকে সুরমা স্বামীকে সুমতির ছবির দিকে চেয়ে থাকতে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।
–ওদিকের জানালাটা খুলে দাও তো!
–খুলে দেব?
–হ্যাঁ।
সে কথা লঙ্ন করতে পারলেন না সুরমা। জানালাটা খুলে দিতেই আলোর ঝলক গিয়ে পড়ল ছবিখানার উপর।
সুরমা শিউরে উঠলেন। পরমুহূর্তেই অগ্রসর হলেন–ছবির উপর পরদাখানা টেনে দেবেন। তিনি।
–না, ঢেকো না।
–কেন? হঠাৎ তোমার হল কী?
সুরমার মুখের দিকে তাকিয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন–সেইদিন থেকে ওকে মধ্যে মধ্যে মনে পড়ছে। মাঝে মাঝে এসে যেন সামনে দাঁড়াচ্ছে। আজ বহুবার দাঁড়িয়েছে। তাই ওর সামনে এসে আমিই দাঁড়িয়েছি। থাক—এটা খোলা থাক।
—বেশ থাক। কিন্তু পোশাক ছাড়বে চল। চা খাবে।
–চা এখানে পাঠিয়ে দাও। পোশাক এখন ছাড়ব না।
এ-কণ্ঠস্বর অলঙনীয়। নিজের ঘুমকে মনে মনে অভিসম্পাত দিলেন সুরমা। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। নইলে হয়ত গাড়ির মুখ থেকে জ্ঞানেন্দ্রনাথকে ফেরাতে পারতেন। এ ঘরে ঢুকতে দিতেন না।
কয়েক দিন থেকেই স্বামীর জন্য তার আর দুশ্চিন্তার শেষ নাই।
দিন দিন তিনি যেন দূর থেকে দূরান্তরে চলে যাচ্ছেন;—এক নির্জন গহনের মৌন একাকিত্বে মগ্ন হয়ে যাচ্ছেন। বর্ষার এই দিগন্তজোড়া বর্ষপণানুখ মেঘমণ্ডলের মতই গম্ভীর ম্লান এবং ভারী হয়ে উঠছেন। জীবনের জ্যোতি যেন কোনো বিরাট গম্ভীর প্রশ্নের অনিবার্য আবির্ভাবে ঢাকা পড়ে গেছে। অবশ্য জ্ঞানেন্দ্রনাথের জীবনে এ নূতন নয়। ঋতুপর্যায়ের মত এ তাঁর জীবনে এসেছে বার বার। বার বার কত পরিবর্তন হল মানুষটির জীবনে। উঃ!
কিন্তু এমন আচ্ছন্নতা, এমন মৌন মগ্নতা কখনও দেখেন নি। সবচেয়ে তাঁর ভয় হচ্ছে। সুমতির ছবিকে! সে কোন প্রশ্ন নিয়ে এল? কী প্রশ্ন? সে প্রশ্ন যাই হোক তার সঙ্গে তিনি যে জড়িয়ে আছেন তাতে তো সন্দেহ নেই। তার অন্তর যে তার আভাস পাচ্ছে। আকুল হয়ে উঠেছে। তার মা তাঁকে বারণ করেছিলেন। কানে বাজছে। মনে পড়েছে। নিজেও তিনি দূরে চলে যেতে চেয়েছিলেন। টেনিস ফাইন্যালে জেতার পর তোলানো ফটোগ্রাফ কখানা পেয়েই সংকল্প করেছিলেন সুমতি জ্ঞানেন্দ্রনাথ থেকে দূরে সরে যাবেন। অনেক দূরে। পরদিন সকালেই কলকাতা চলে যাবেন, সেখান থেকে বাবাকে লিখবেন অন্যত্র ট্রান্সফারের জন্য; অথবা জ্ঞানেন্দ্রনাথকে ট্রান্সফার করাতে। বাবাকে জানাতে তার সংকোচ ছিল না। কিন্তু বিচিত্র ঘটনাচক্র।
পরদিন ভোরবেলাতেই শুনেছিলেন মুনসেফবাবুর বাসা পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। মুনসেফবাবুর স্ত্রী পুড়ে মারা গেছেন। মুনসেফবাবু হাসপাতালে, অজ্ঞান, বুকটা পিঠটা অনেকটা পুড়ে গেছে, বাঁচবেন কি না সন্দেহ!
সব বাঁধ তাঁর ভেঙে গিয়েছিল।
যে-প্রেমকে কখনও জীবনে প্রকাশ করবেন না সংকল্প করেছিলেন সে-প্রেম সেই সংকটময় মুহূর্তে তারস্বরে কেঁদে উঠে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তিনি জ্ঞানেন্দ্রনাথের শিয়রে গিয়ে। বসেছিলেন। উঠবেন না, তিনি উঠবেন না। মাকে বলেছিলেন—আমাকে উঠতে বোলোনা, আমি যাব না, যেতে পারব না।
কাতর দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়েছিলেন বাবার দিকে।
বাবা বলেছিলেন–বেশ, থাক তুমি।
মা বলেছিলেন—এ দুই কী করছিস ভেবে দেখ। যে-লোক স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে এমনভাবে নিজের প্রাণ বিপন্ন করে তার মনে অন্যের ঠাঁই কোথায়?
লোকে যে দেখেছিল, চকিতের মত দেখেছিল সুমতির হাত ধরে জ্ঞানেন্দ্রনাথকে বেরিয়ে আসতে। চাল চাপা পড়ার মুহূর্তে সুমতির নাম ধরে তার আর্তচিৎকার শুনেছিল—সুমতি! বলে, সে নাকি এক প্রাণফাটানো আর্তনাদ!
জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভাল হয়ে উঠবার পর একদা এক নিভৃত অবসরে সুরমা বলেছিলেন—তোমার জীবন আমি সর্বস্বান্ত করে দিয়েছি। আমার জন্যই তোমার এ সৰ্বনাশ হয়ে গেল। আমাকে তুমি নাও! সুমতির অভাব
জ্ঞানেন্দ্রনাথ আশ্চর্য। সুরমার কথায় বাধা দিয়ে বলেছিলেন—অভাববোধের সব জায়গাটাই যে অগ্নিজিহ্বা লেহন করে তার রূপ রস স্বাদ গন্ধ সব নিঃশেষে নিয়ে গেছে সুরমা।
আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন নিজের পুড়ে-যাওয়া বুক এবং পিঠটাকে।
—আমার চা-টা—শুধু চা, এখানে পাঠিয়ে দাও!
–প্লিজ!
জ্ঞানেন্দ্রনাথের মৃদু গম্ভীর কণ্ঠস্বর; চমকে উঠলেন সুরমা। ফিরে এলেন নিষ্ঠুরতম বাস্তব অবস্থায়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন সুমতির অয়েল-পেন্টিঙের সামনে।
—না। আর্ত মিনতিতে সুরমা তার হাত ধরতে গেলেন।
–প্লিজ!
সুরমার উদ্যত হাতখানি আপনি দুর্বল হয়ে নেমে এল। আদেশ নয়, আকুতিভরা কণ্ঠস্বর। বিদ্রোহ করার পথ নেই। লঙ্ঘন করাও যায় না।
নিঃশব্দেই বেরিয়ে গেলেন সুরমা।
স্থির দৃষ্টিতে ছবিখানির দিকে তাকিয়ে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। ক্ষীণতম ভাষার স্পন্দন তাতে থাকলে তাকে শুনবার চেষ্টা করছিলেন, ইঙ্গিত থাকলে বুঝতে চেষ্টা করছিলেন। সুমতির মিষ্ট কোমল প্রতিমূর্তির মধ্যে কোথাও ফুটে রয়েছে অসন্তোষ অভিযোগের ছায়া?
—তুমি আজ কোর্টের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে?
জ্ঞানেন্দ্রনাথ ফিরে তাকালেন।
চা নিয়ে সুরমা এসে দাঁড়িয়েছেন। নিজেই নিয়ে এসেছেন বেয়ারাকে আনেন নি সঙ্গে।
—অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে? মাথা ঘুরে গিয়েছিল?
–কে বললে?
–আরদালি বললে। পাবলিক প্রসিকিউটারের সওয়ালের সময় তোমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল; তুমি উঠে খাস কামরায় গিয়ে মাথা ধুয়েছ–?
–হ্যাঁ। একটু হাসলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। বিচিত্র সে হাসি। বিষণ্ণতার মধ্যে যে এমন প্রসন্নতা থাকতে পারে, এ সুরমা কখনও দেখেন নি।
অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি।
পাবলিক প্রসিকিউটার আসামির উকিলের সওয়ালের পর তার জবাব দিচ্ছিলেন। তিনি গভীর আত্মমগ্নতার মধ্যে ড়ুবে ছিলেন। নিস্পন্দ পাথরের মূর্তির মত বসে ছিলেন তিনি, চোখের তারা দুটি পর্যন্ত স্থির; কাচের চোখের মত মনে হচ্ছিল। ইলেকট্রিক ফ্যানের বাতাসে শুধু তাঁর গাউনের প্রান্তগুলি কাঁপছিল, দুলছিল। তিনি মনে মনে অনুভব করছিলেন ওই শ্বাসরোধী অবস্থার স্বরূপ। আঙ্কিক নিয়মে অন্ধ বস্তুশক্তির নিপীড়ন। অঙ্কের নিয়মে একদিকে তার শক্তি ঘনীভূত হয়, অন্যদিকে জীবনের সগ্রাম-শক্তি সহ্যশক্তি ক্ষীণ ক্ষীণতর হয়ে আসে। তার শেষ মুহূর্তের অব্যবহিত পূর্বে সে চরম মুহূর্ত—শেষ চেষ্টা তখন তার, পুঞ্জ পুঞ্জ শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া, নির্মল প্ৰাণদায়িনী বায়ুর অভাবে হৃৎপিণ্ড ফেটে যায়। সকল স্মৃতি, ধারণা, বিচারবুদ্ধি অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে আসে। অকস্মাৎ বাতাস বন্ধ হয়ে যেমন আলোর শিখা বেড়ে উঠে লণ্ঠনের ফানুসে কালির প্রলেপ লেপে দেয়, তার জ্যোতির চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে নিজেও নিভে যায়—ঠিক তেমনি। ঠিক সেই মুহূর্তে খসে পড়ে জ্বলন্ত খড়ের রাশি, একসঙ্গে শত বন্ধনে বাঁধা একটা নিরেট অগ্নিপ্রাচীরের মত। আসামি ঠিক বলেছে, সেসময়ের মনের কথা স্মরণ করা যায় না। প্রকৃতির নিয়ম। হতভাগ্য আসামি জলের মধ্যে ড়ুবে যাচ্ছিল, নিষ্ঠুর বন্ধনে বেঁধেছিল তার ভাই। ঘন জলের মধ্যে গভীরে নেমে যাচ্ছিল, শ্বাসবায়ু রুদ্ধ হয়ে ফেটে যাচ্ছিল বুক, সে সেই যন্ত্রণার মধ্যে চলছিল পিছনের দিকে আদিমতম জীবন-চেতনার দিকে।
অকস্মাৎ তাঁর কানে এল অবিনাশবাবুর কথা।
খ.
পাবলিক প্রসিকিউটার বলছিলেন সেকশন এইট্টি-ওয়ানের অনুল্লিখিত অংশটির কথা। আমি খগেনের গলা টিপে ধরে তাকে আঘাত করেছে, শ্বাস রোধ করে মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েছে, খগেনকে মেরে নিজেই বেঁচেছে, খগেনকে বাঁচবার অবকাশ দেয় নি।
ইয়োর অনার, তা ছাড়া আরও একটি কথা আছে। আমার পণ্ডিত বন্ধু সেকশন এইট্টিওয়ানের একটি নজিরের অর্ধাংশের উল্লেখ করেছেন মাত্র। সে অর্ধাংশের কথা আমি বলেছি। এই সেকশন এইটি-ওয়ানেই আর-একটি নজিরের উল্লেখ আমি করব। ভগ্নপোত তিন জন নাবিক, অকূল সমুদ্রে ভেলায় ভাসছিল। দুই জন প্রৌঢ়, এক জন কিশোর। অকূল দিগন্তহীন সমুদ্র, তার উপর ক্ষুধা। ক্ষুধা সেই নিষ্করুণ নিষ্ঠুরতম রূপ নিয়ে দেখা দিল, যে-রূপকে আমরা সেই আদিম উন্মাদিনী শক্তি মনে করি। যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা যার কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবন মাথা নত করে। সেই অবস্থায় তারা লটারি করে এই কিশোরটিকে হত্যা করে তার মাংস খেয়ে বাঁচে। তারা উদ্ধার পায়। পরে বিচার হয়। সে-বিচারে আসামিদের উকিল জীবনের এই আদিম আইনের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, বিচারককে মনে রাখতে হবে, তারা তখন মানুষের সভ্যতার আইনের চেয়েও প্রবলতর আইনের দ্বারা পরিচালিত!
কিন্তু সেখানে বিচারক বলছেন, আত্মরক্ষা যেমন সহজ প্রবৃত্তি, সাধারণ ধর্ম—তেমনি আত্মত্যাগ, পরার্থে আত্মবিসর্জন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, মহত্তর ধৰ্ম। ইয়োর অনার, যে-প্রকৃতি বস্তুজগতে অন্ধ নিয়মে পরিচালিত, জন্তু-জীবনে বর্বর, হিংস্ৰ, কুটিল, আত্মপরতন্ত্রতায় যার। প্রকাশ, মানুষের জীবনে তারই প্রকাশ দয়াধর্মে, প্রেমধর্মে, আত্মবলিদানের মহৎ এবং বিচিত্র। প্রেরণায়। জন্তুর মা সন্তানকে ভক্ষণ করে। মানুষের মা আক্রমণোদ্যত সাপের মুখ থেকে সন্তানকে বাঁচাতে সে-দংশন নিজে বুক পেতে নেয়। কোথায় থাকে তার আত্মরক্ষার ওই জান্তব দীনতা হীনতা? মা যদি সন্তানকে হত্যা করে নিজের প্রাণের জন্য, পিতা যদি পুত্রকে হত্যা করে নিজের প্রাণের জন্য, বড় ভাই যদি অসহায় দুর্বল ছোট ভাইকে হত্যা করে নিজের প্রাণরক্ষা করে মহত্তর মানবধর্ম বিসর্জন দেয়, সবল যদি দুর্বলকে রক্ষা না করে, তবে এই মানুষের সমাজে আর পশুর সমাজে প্রভেদ কোথায়? মানুষের সমাজ আদি যুগ থেকে এই ঘটনার দিন পর্যন্ত অনেক অনেক কাল ধরে অনেক অনেক দীর্ঘ পথ চলে এসেছে অন্ধতমসাচ্ছন্নতা থেকে আলোকিত জীবনের পথে; এই ধর্ম এই প্রবৃত্তি আজ আর সাধনাসাপেক্ষ নয়, এই ধর্ম এই প্রবৃত্তি আজ রক্তের ধারার সঙ্গে মিশে রয়েছে; তার প্রকৃতির স্বভাবধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। আমাদের পুরাণে আছে, মহর্ষি মাণ্ডব্য বাল্যকালে একটি ফড়িংকে তৃণাঞ্জুর ফুটিয়ে খেলা করেছিলেন। পরিণত বয়সে তাকে বিনা অপরাধে রাজকর্মচারীদের ভ্ৰমে শূলে বিদ্ধ হতে হয়েছিল। তিনি ধর্মকে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কোন অপরাধে এই দণ্ড তাকে নিতে হল। তখন ধর্ম এই বাল্যবয়সের ঘটনার কথাটি উল্লেখ করে বলেছিলেন, আঘাতের প্রতিঘাতের ধারাতেই চলে ধর্মের বিচার, ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার মত অমোঘ অনিবার্য। এ থেকে কারও পরিত্রাণ নাই। ইয়োর অনার, এই মানুষের ধর্ম সম্পর্কে কল্পনা এদেশে–
ঠিক এই মুহূর্তে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।
সমস্ত কোর্টরুমটা যেন পাক খেতে শুরু করেছিল। তার মধ্যে মনে পড়েছিল—দীর্ঘদিন আগেকার কথা। তিনি হাসপাতালে পড়ে আছেন, বুকে পিঠে ব্যান্ডেজ বাঁধ; নিদারুণ যন্ত্ৰণা দেহে মনে! সুরমার বাবা তাকে বলেছিলেন-কী করতে তুমি? কী করতে পারতে? হয়ত সুমতির সঙ্গে একসঙ্গে পুড়ে মরতে পারতে? কী হত তাতে?
আজ আসামিকে লক্ষ্য করে অবিনাশবাবু যখন এই কথাগুলি বলে গেলেন, তখন তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত শরীরে শিরায় শিরায় স্নায়ুতে স্নায়ুতে তীক্ষ্ণ সূচীমুখ হিমানী-স্পর্শের প্রতিক্রিয়ায় যেন একটা অদ্ভুত কম্পন বয়ে গেল সর্বাঙ্গে। আজ আকাশে মেঘ নাই; রোদ উঠেছে; স্কাইলাইটের ভিতর দিয়ে সেই আলোর প্রতিফলনে আসামির পায়ের কাছে একটা ঘন। কালো ছায়া পুঞ্জীভূত হয়ে যেন বসে রয়েছে। তিনি টেবিলের উপর মাথা রেখে যেন নুয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সে এক মিনিটের জন্য, বোধ করি তারও চেয়ে কম সময়ের জন্য। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মাথা তুলে বলেছিলেন মিঃ মিট্রা, একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি। ফাইভ মিনি প্লিজ।
তিনি খাস কামরায় চলে গিয়ে বাথরুমে কলের নিচে মাথা পেতে দিয়ে কল খুলে দিয়েছিলেন। চার মিনিট পরেই আবার এসে আসন গ্রহণ করে বলেছিলেন, ইয়েস, গো অন প্লিজ!
ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের কল্পনার কাহিনীগুলি যতই অবাস্তব হোক তার অন্তর্নিহিত উপলব্ধি, তার ভিত্তিগত সত্য অভ্রান্ত, অমোঘ। রাষ্ট্র সমাজ সেই নিয়ম ও নীতিকেই জয়যুক্ত করে। বর্তমান ক্ষেত্রে—
অবিনাশবাবু আশ্চর্য ধীমত্তার সঙ্গে তাঁর সওয়াল করেছেন। সমস্ত আদালত অভিভূত হয়ে ছিল। সওয়াল শেষের পরও মিনিটখানেক কোর্টরুমে সূচীপতন-শব্দ শোনা যাবার মত স্তব্ধতা থমথম করছিল।
আসামি চোখ বুজে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।
সেই স্তব্ধতার মধ্যেও সকলের মনে ধ্বনিত হচ্ছিল,বর্তমান ক্ষেত্রে আমি যদি একটি নারীর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে স্নেহ-মমতা, তার সুদীর্ঘ দিনের সন্ন্যাসধর্ম বিসর্জন দিতে উদ্যত না হত, তবে আমি নিশ্চয় বলতে পারি যে, আত্মরক্ষার আকুলতায় ওই ছোট ভাইয়ের গলা টিপে ধরেও সে ছেড়ে দিত, তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করত। সেক্ষেত্রে যদি এমন কাণ্ডও ঘটত তবে আমি বলতাম যে—জলের মধ্যে সে যখন ছোট ভাইয়ের গলা টিপে ধরেছিল, তখন শুধুমাত্র জান্তব আত্মরক্ষার প্রেরণাতেই সে এ-কাজ করেছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে আসামি এবং হত ব্যক্তি ভাই হয়েও প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী, যে-দ্বন্দ্বের তীব্রতায় বিষয়ভাগে উদ্যত হয়েছিল। এক্ষেত্রে আক্রোশ। অহরহই বর্তমান ছিল তার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর এবং যথাসময়ে সুযোগের মধ্যে সে-আক্রোশ যথারীতি কাজ করে গেছে। বাল্যজীবনে চতুষ্পদ হত্যা করার চাতুর্য তার সবলতর হাতে মুহূর্তে কার্য সমাধা করেছে–ইয়োর অনার–
অবিনাশবাবুর কথাগুলি এখনও ধ্বনিত হচ্ছে-আইনই শেষ কথা নয়। পৃথিবীতে প্রকৃতির। নিয়ম যেমন অমোঘ, মানুষের চৈতন্যের মহৎ প্রেরণাও তেমনই অমোঘ। তার চেয়েও সে বলবতী, তেজশক্তিতে প্রদীপ্ত, জান্তব প্রকৃতির তমসাকে নাশ করতেই তার সৃষ্টি! ভাই ভাইকে, বড়ভাই ছোটভাইকে রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা করে নি, নিজের প্রাণরক্ষার জন্য তাকে হত্যা করেছে। এ-হত্যা কলঙ্কজনক; নিষ্ঠুরতম পাপ মানুষের সমাজে।
গ.
জুরীরা একবাক্যে আসামিকে দোষী ঘোষণা করেছেন।
আসামিও বোধহয় অবিনাশবাবুর বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিল, নতুবা বিচিত্র তার মন। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ কাঠগড়ার রেলিঙের উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল।
তার দিকে তাকাবার তখন তার অবকাশ ছিল না। তিনি তখন সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রায় ঘোষণা করেছিলেন–জুরীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং আসামির অপরাধ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে–
আবার তিনি মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়েছিলেন। হঠাৎ চোখ পড়েছিল সামনের দেওয়ালে–আসামির সেই ছায়াটা আধখানা মেঝে আধখানা দেওয়ালে এঁকেবেঁকে মসীময় একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মত দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মুহূর্তেই আত্মসংবরণ করেছেন তিনি।
রায় দিয়েছেন, যাবজ্জীবন নির্বাসন। ট্রান্সপোর্টেশন ফর লাইফ। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ধারা অনুযায়ী এই অস্বাভাবিক আসামির প্রাণান্তকর অবস্থার মধ্যে সংঘটনের উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতির করুণা পাবার বিবেচনার জন্য সুপারিশ করেছেন।
কোর্ট থেকে এসে সরাসরি ঘরে ঢুকে আপিসে বসে ছিলেন। দেওয়ালে-পড়া সেই প্রশ্নচিহ্নটা কাল ছিল আবছা, আজ স্পষ্ট ঘন কালো কালিতে লেখা প্রশ্নের মত দাঁড়িয়েছে।
সুমতির কাছে তার অপরাধ আছে? আছে? আছে? না থাকলে ছবিখানা ঢাকা থাকে কেন? কেন? কেন?
আজ দীর্ঘকাল পর অকস্মাৎ তিনি পলাতক আত্মগোপনকারী দুর্বিষহ অবস্থা অনুভব করেছেন।
তাই বাড়ি ফিরে সরাসরি এসে সুমতির ছবির কাছে গিয়ে পরদাটা সরিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। বল তোমার অভিযোগ! কোথায় তোমার ভয়? বল! বল! বল!
চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ, তারই মধ্যে মিলিয়ে গেল তাঁর মুখের সেই বিচিত্ৰ, একাধারে বিষণ্ণ এবং প্রসন্ন হাসিটুকু। সুরমা তাঁর বুকের উপর হাতখানি রেখে গাঢ়স্বরে বললেন– ডাক্তারকে ডাকি?
–না।
–মাথা ঘুরে গিয়েছিল স্বীকার করছ, তবু ডাক্তার ডাকবার কথায় না বলছ?
–বলছি। শরীর আমার খারাপ হয় নি। তুমি জান, আমি মিথ্যা কথা বলি না। ওই সুমতি; সুমতি হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল আমার। মাথাটা ঘুরে গেল।
চায়ের কাপটা টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘরের মধ্যে মাথা হেঁট করে ঘুরতে লাগলেন। সুরমা মাটির পুতুলের মতই টেবিলের কোণটির উপর হাতের ভর রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন।
হঠাৎ একসময় জ্ঞানেন্দ্রনাথের বোধ করি খেয়াল হল——ঘরে সুরমা এখনও রয়েছে। বললেন–এখনও দাঁড়িয়ে আছ? না। থেকো না দাঁড়িয়ে যাও; বাইরে যাও; খোলা হাওয়ায়; আমাকে আজকের মত ছুটি দাও। আজকের মত।
সুরমা সাধারণ মেয়ে হলে কান্না চাপতে চাপতে ছুটে বেরিয়ে যেতেন। কিন্তু সুরমা অরবিন্দ চ্যাটার্জির মেয়ে, জ্ঞানেন্দ্রনাথের স্ত্রী। নীরবে ধীর পদক্ষেপেই তিনি বেরিয়ে গেলেন। লনে এসে কম্পাউন্ডের ছোট পঁচিলের উপর ভর দিয়ে পশ্চিম দিকে অস্তমান সূর্যের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন; দুটি নিঃশব্দ অশ্রুধারা গড়িয়ে যেতে শুরু হল সূর্যকে সাক্ষী রেখে। তারও জীবনের আলো কি ওই সূর্যাস্তের সঙ্গেই অস্ত যাবে? চিরদিনের মত অস্ত যাবে?
–বয়! জ্ঞানেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।
ঘ.
জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘুরছিলেন অবিশ্রান্তভাবে। মনের মধ্যে বিচিত্রভাবে কয়েকটা কথা ঘুরছে।
মাণ্ডব্য ধর্মের বিধানের পরিবর্তন করে এসেছিলেন।
পশু পশুকে হত্যা করে খায়। শুধু হিংসার জন্যও অকারণে হত্যা করে। সে তার স্ব-ধৰ্ম। তামসী তার ধর্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মানুষ যে ধর্মকে আবিষ্কার করেছে—সে সেখানে ভবিষ্যতের গর্ভে—সেখানে সে জন্মায় নি, সেখানে কোনো দেবতার শাস্তিবিধানের অধিকার নাই। এমনকি, অনুতাপের সূচীমুখেও এতটুকু অনুশোচনা জাগবার অবকাশ নাই সেখানে। মানুষের জীবনেই এই তমসার মধ্যে প্রথম চৈতন্যের আলো জ্বলেছে। শৈশব বাল্য অতিক্রম করে সেই চৈতন্যে উপনীত হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে সকল নিয়মের অতীত। মাণ্ডব্য বলেছিলেন—যম, সেই অমোঘ সত্য অনুযায়ী আমি তোমার বিধান সংশোধন করছি। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত মানুষ অপরাধ ও শাস্তির অতীত।
সে-বিধান ধর্ম নাকি মেনে নিয়েছিলেন।
আধুনিক যুগে সে বিধান আবার সংশোধন করেছে মানুষ।
রাষ্ট্ৰীয় দণ্ডবিধির নির্দেশ, সাত বৎসর পর্যন্ত মানুষের অপরাধবোধ জাগ্রত হয় না; সুতরাং ততদিন সে দণ্ডবিধির বাইরে। রাষ্ট্রবিধাতাদের বিবেচনায় পাঁচ বৎসর বেড়ে সাত বৎসর হয়েছে। মানুষ মহামসার শক্তির প্রচণ্ডতা নির্ণয় করে শিউরে উঠে তাকে সসম্ভ্ৰমে স্বীকার করেছে। তাতে ভুল করে নি মানুষ। কায়ার সঙ্গে ছায়ার মত তার অস্তিত্ব। তাকে কি লঙ্ঘন করা। করা যায়? কিন্তু এখনও কি?
এখনও মানুষের চৈতন্য কি সাত বছর বয়সের গণ্ডি অতিক্রম করে নি?
এখনও কি আদিম প্রকৃতির অন্ধ নিয়মের প্রভাবের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণের দুর্বলতা কাটাবার মত বল সঞ্চয় করে নি? প্রাগৈতিহাসিক মস্তিষ্কের গঠনের সঙ্গে আজকের মানুষের কত প্রভেদ!
গুলিবিদ্ধ হয়ে মরণোন্মুখ মানুষ আজ অক্রোধের মধ্যে রাম নাম উচ্চারণ করতে পেরেছে। যুদ্ধে আহত মরণোন্মুখ মানুষ নিজের মুখের জল অপরের মুখে তুলে দিয়েছে তোমার প্রয়োজন বেশি। Thy necessity is greater than mine.
নিষ্ঠুরতম অত্যাচারেও মানুষ অন্যায়ের কাছে নত হয় নি; ন্যায়ের জন্য হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেছে। দুর্বল বিপন্নকে রক্ষা করতে সবল ঝাঁপ দিয়েছে বিপদের মুখে, নিজে মৃত্যুবরণ করে দুর্বলকে রক্ষা করেছে। বিবেচনা করতে সময়ের প্রয়োজন হয় নি। চৈতন্যের নির্দেশ প্রস্তুত ছিল। চৈতন্য জীবপ্রকৃতির অন্ধ নিয়মকে অবশ্যই অতিক্রম করেছে।
তিনি নিজেও তো করেছেন। ক্ষেত্রটা একটু স্বতন্ত্র।
তিনি সুরমাকে ভালবেসেছিলেন, কিন্তু সুমতির প্রতি কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি। সুমতি বেঁচে থাকতে বারেকের জন্য সুরমাকে মুখে বলেন নি, তোমাকে আমি ভালবাসি। মনে না-পাওয়ার বেদনা ছিল, সে বেদনাও তিনি বুকের মধ্যে নিরুদ্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু পাওয়ার আকাঙ্খাকে গোপনতম অন্তরেও আত্মপ্রকাশ করতে দেন নি। কোনোদিন বারেকের জন্য থামেন নি। জীবনে তমসার সীমারেখা অনেক পিছনে ফেলে এসেছেন।
চোখ দুটির দৃষ্টি তাঁর অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।
আবার এসে দাঁড়ালেন সুমতির ছবির সামনে। ভাল আলো এসে পড়ছে না, দেখা যাচ্ছে। না ভাল, তিনি ডাকলেন–বয়।
–নামা ছবিখানাকে। রাখ ওই চেয়ারের উপর।
সুমতির ছবির চোখেও যেন অভিযোগ ফুটে রয়েছে, যার জন্য ছবিখানাকে ঢেকে রাখার আদেশ দিয়েছেন। আজ ছবিখানাকে অত্যন্ত কাছে এনে, সত্যকারের সুমতির মত সামনে এনে, তার সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করবেন।
পরিপূর্ণ আলোর সামনে রেখে ছবির চোখে চোখ রেখেই স্থিরভাবে দাঁড়ালেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ।
ক্লান্ত চিন্তাপ্রখর মস্তিষ্কের মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে যেন। অন্যদিকে হৃদয়ের মধ্যে একটা কম্পন অনুভব করছেন। প্রাণপণে নিজেকে সংযত স্থির করে রাখতে চাইলেন তিনি। সমুদ্রে ঝড়ে বিপন্ন জাহাজের হালের নাবিকের মত। সব বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আছেন শুধু তিনি আর সুমতির ছবি। ছবি নয়—ওই ছবিখানা আজ আর ছবি নয় তার কাছে, সে যেন জীবনময়ী হয়ে উঠেছে। স্থির নীল আকাশ অকস্মাৎ যেমন মেঘপুঞ্জের আবর্তনে, বায়ুবেগে প্রশান্ত বিদ্যুতে, গৰ্জনে বাজয় মুখর হয়ে ওঠে তেমনিভাবে মুখর হয়ে উঠেছে। এসবই তাঁর চিত্রলোকের প্রতিফলন তিনি জানেন। আকাশ মেঘ নয়, আকাশে মেঘ এসে জমে, তেমনিভাবে ছবিখানায় নিষ্ঠুর অভিযোগের প্রখর মুখরতা এসে জমা হয়েছে।
বার বার ছবিখানার সামনে এসে দাঁড়ালেন, আবার ঘরখানার মধ্যে ঘুরলেন। দেওয়ালের ক্লকটায় পেণ্ডুলামের অবিরাম টক-টক টক-টক শব্দ ছাড়া আর শব্দ নাই। সময় চলেছে রাত্রি অগ্রসর হয়ে চলেছে তারই মধ্যে।
উত্তর তাকে দিতে হবে এই অভিযোগের। এই নিষ্ঠুর অভিযোগ-মুখরতাকে স্তব্ধ করতে হবে তার উত্তরে। তাঁর নিজেরই অন্তরলোকে যেন লক্ষ লক্ষ লোক উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছে তার উত্তর শুনবার জন্য। তাদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি নিজে।
–বল, বল, সুমতি, বল তোমার অভিযোগ!
ছবির সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন। বল!
ওঃ, কী গভীর বেদনা সুমতির মুখে চোখে!—এত দুঃখ পেয়েছ? কিন্তু কী করব? দুঃখ তো আমি দিই নি সুমতি; নিজের দুঃখকে তুমি নিজে তৈরি করেছ। গুটিপোকার মত নিজে দুঃখের জাল বুনে নিজেকে তারই মধ্যে আবদ্ধ করলে!
কী বলছ? আমি তোমায় ভালবাসলে তোমার অমন হত না? আমার মন, আমার হৃদয়, আমার ভালবাসা পেলে তুমি প্রজাপতির মত অপরূপা হয়ে সর্ব বন্ধন কেটে বের হতে? মন হৃদয় ভালবাসা না দেওয়ার অপরাধে আমি অপরাধী?
–না। স্বীকার করি না! মন হৃদয় ভালবাসা দিতে আমি চেয়েছিলাম তুমি নিতে পার নি, তোমার হাতে ধরে নি। এ সংসারে যার যতটুকু শক্তি তার এক তিল বেশি কেউ পায় না।
সে তার প্রাপ্য নয়। ঈশ্বরের দোহাই দিলেও হয় না। ধর্ম মন্ত্র শপথ কোনো কিছুর বলেই তা হয় না। হাতে তুলে দিলে হাত দিয়ে গলে পড়ে যায়, অ্যাঁচলে বেঁধে দিলে নিজেই সে অ্যাঁচলের গিঁট খুলে হারায়, আঁচল ছিঁড়ে ফেলে। হ্যাঁ, পারে, একটা জিনিস প্রাপ্য না হলেও মানুষে দিতে পারে, দান-দয়া। তাও দিয়েছিলাম। তাও তুমি নাও নি!
ছবির সামনে দাঁড়িয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ সত্যই কথা বলেছিলেন। চোখের দৃষ্টি তার স্বাভাবিক, উজ্জ্বল। ছবি যেন তার সামনে কথা বলছে। অশরীরী আবির্ভাব তিনি যেন প্রত্যক্ষ করছেন। শব্দহীন কথা যেন শুনতে পাচ্ছেন। তিনি যেন বিশ্বজগতের সকল মানুষের জনতার মধ্যে সুমতির সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন।
—কি বললে? সুরমাকে তো ভালবাসতে পেরেছিলাম?
—না পেরে তো আমার উপায় ছিল না সুমতি। তার নেবার শক্তি ছিল, সে নিতে পেরেছিল, নিয়েছিল। তাই বা কেন? তুমি নিজে না নিয়ে ছুঁড়ে তার হাতে ফেলে দিয়েছিলে, তুলে দিয়েছিলে। তুমিই অকারণ সন্দেহে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতিকে অভিশাপ দিতে গিয়ে বিচিত্র নিয়মে আশীর্বাদে সার্থক প্ৰেমে পরিণত করেছিলে। প্রীতিকে তুমি বিষ দিয়ে মারতে গেলে, প্রীতি সে বিষ খেয়ে নীলকণ্ঠের মত অমর প্রেম হয়ে উঠল।
—কী বলছ? বিবাহের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমি?
–দিয়েছিলাম। সে-প্রতিশ্রুতি আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি! সুরমাকে ভালবেসেও তুমি জীবিত থাকতে কোনোদিন তা বাক্যে প্রকাশ করি নি, অন্তরে প্রশ্রয় দিই নি, মনে কল্পনা করি নি। তুমি আমার ধৈর্যকে আঘাত করে ভাঙতে চেয়েছ। আমি বুক দিয়ে সয়েছি, ভাঙতে দিই নি। শেষে তুমি আগুন ধরিয়ে দিলে। সে-আগুন ঘরে লাগল। সেই আগুনে তুমি নিজে পুড়ে ছাই হয়ে গেলে! আমি পড়লাম। কোনো রকমে বেঁচেছি, কিন্তু আমি নির্দোষ।
–কী?
অকস্মাৎ চোখ দুটি তার বিস্ফারিত হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বিস্ফারিত চোখের নিম্পলক দৃষ্টিতে ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন–
–কী?
–কী বলছ?
—সেই চরম মুহূর্তটিতে আমি তোমার হাত থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম? আমি যে তোমাকে বিপদে-আপদে আঘাতে-অকল্যাণে রক্ষা করতে ঈশ্বর সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সে প্রতিজ্ঞা–।
–হ্যাঁ। হ্যাঁ। ছিলাম। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারি নি। স্বীকার করছি। স্বীকার করছি। কিন্তু কী করব? নিজের জীবন তো আমি বিপন্ন করেছিলাম, তবু পারি নি। কী করব? তোমার নিজের হাতে ভাঙা কাচের টুকরো–।
–কী? কী? সেটা বের করে তোমাকে বুকে তুলে নিয়ে বের হবার শেষ চেষ্টা করি নি? না, না করি নি! তোমার জীবন বাঁচাতে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে পারতাম,দেওয়া উচিত ছিল, তা আমি পারি নি। আমি দিই নি। আমি স্বীকার করছি।
–কী? পৃথিবীতে মানুষের চৈতন্য অনেকদিন সাত বছর পার হয়েছে? হ্যাঁ হয়েছে। হয়েছে। নিশ্চয় হয়েছে! অপরাধ আমি স্বীকার করছি।
অবসন্নভাবে তিনি যেন ভেঙে পড়লেন, দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তি আর ছিল না। একখানা চেয়ারে বসে মাথাটি নুইয়ে টেবিলের উপর রাখলেন। অদৃশ্য পৃথিবীর জনতার সামনে তিনি যেন নতজানু হয়ে বসতে চাইলেন। আবার মাথা তুললেন; সুমতি যেন এখনও কী বলছে।
–কী? কী বলছ?
–আরও সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে বলছ?
—বলছ, নিয়তি আগুনের বেড়াকে ছিদ্ৰহীন করে তোমাকে ঘিরে ধরেছিল, শুধু একটি ছিদ্রপথ ছিল আমার হাতখানির আশ্রয়? আকুল আগ্রহে, পরম বিশ্বাসে সেই পথে হাত বাড়িয়ে ধরেছিলে, আমি হাত ছাড়িয়ে সেই পথটুকুও বন্ধ করে দিয়েছি।
—দিয়েছি! দিয়েছি! দিয়েছি। আমি অপরাধী। হ্যাঁ, আমি অপরাধী।
চেতনা যেন তার বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে নিজেকে সচেতন রাখতে চেষ্টা করলেন। নিজের চৈতন্যকে তিনি অভিভূত হতে দেবেন না। সকল আবেগ সকল গ্লানির পীড়নকে সহ্য করে তিনি স্থির থাকবেন।
কতক্ষণ সময় পার হয়ে গেছে, তার হিসাব তাঁর ছিল না। ঘড়িটা টক-টক শব্দে চলেছেইচলেছেই; সেদিকেও তিনি তাকালেন না। শুধু এইটুকু মনে আছে—সুরমা এসে ফিরে গেছে; বয়ও কয়েকবার দরজার ওপাশ থেকে বোধ করি শব্দ করে তার মনোেযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছে। কিন্তু তিনি মাথা তোলেন নি। শুধু নিজেকে স্থির চৈতন্যে অধিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। তপস্যা করেছেন।
মাথা তুললেন তিনি। মুখে চোখে প্রশান্ত স্থিরতা, বিচারবুদ্ধি অবিচলিত, মস্তিষ্ক স্থির, চৈতন্য তাঁর অবিচল স্থৈর্যে অকম্পিত শিখার মত দীর্ঘ ঊর্ধ্বমুখী হয়ে জ্বলছে। আদিঅন্তহীন মনের আকাশ শরতের পূর্ণচন্দ্রের দীপ্তির মত দীপ্তিতে প্রসন্ন উজ্জ্বল। চারিপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য আলোকবিন্দুর মত যেন কাদের মুখ ভেসে উঠেছে। কাদের?
যাদের বিচার করেছেন—তারা?
বিচার দেখতে এসেছে তারা ডিভাইন জাস্টিস! ডিভাইন জাজমেন্ট।
কোনো সমাজের কোনো রাষ্ট্রের দণ্ডবিধি অনুসারে নয়, এ-দণ্ডবিধি সকল দেশের সকল সমাজের অতীত দণ্ডবিধি। সূক্ষ্মতম, পবিত্রতম, ডিভাইন!
আত্মসমর্পণ করবেন তিনি। কাল তিনি সব প্রকাশ করে আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। অবশ্য তার কোনো মূল্যই নেই; কারণ তিনি জানেন কোনো দেশের প্রচলিত দণ্ডবিধিতেই এ-অপরাধ অপরাধ বলে গণ্য নয়, কোনো মানুষ-বিচারক এর বিচারও জানে না। তিনি নিজেও বিচারক, তিনি জানেন নাকী এর বিচার-বিধি, কী এর শাস্তি!
বিচার করতে পারেন ঈশ্বর। ঈশ্বর ছাড়া এর বিচারক নাই। ঈশ্বরকে আজ স্বীকার করেছেন তিনি। তবুও প্রকাশ্যে আত্মসমর্পণ করবেন। তার আগে–।
সুরমা!
কই সুরমা? হয়ত পাথর হয়ে গেছে সুরমা। দীর্ঘনিশ্বাস একটি আপনি বেরিয়ে এল বুক চিরে। ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে এলেন তিনি। সুরমার সন্ধানেই চ ছিলেন। কিন্তু বারান্দায় এসে থমকে দাঁড়ালেন। মনে হল বিচারসভা যেন বসে গেছে।
মধ্যরাত্রির পৃথিবী ধ্যানমগ্নার মত স্থির স্তব্ধ। আকাশে চাঁদ মধ্যগগনে, মহাবিরাটের ললাট-জ্যোতির মত দীপ্যমান। কাটা কাটা মেঘের মধ্যে বর্ষণধৌত গাঢ়নীল আকাশখণ্ড নিরপেক্ষ মহাবিচারকের ললাটের মত প্রসন্ন। বিচারক যেন আসন গ্রহণ করে অপেক্ষা করছেন।
ধীরে ধীরে অভিভূতের মত নেমে প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে দাঁড়ালেন তিনি। সূক্ষ্মতম বিচারে নিজের অপরাধ-স্বীকৃতির মধ্য থেকে এক বৈরাগ্যময় আত্মসমর্পণের প্রসন্নতা তার অন্তরের মধ্যে মেঘমুক্ত আকাশের মত প্রকাশিত হচ্ছে। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত অমলিন জ্যোত্সার জ্যোতিৰ্মানতা ও মহামৌনতার মধ্যে তিনি যেন এক চিত্ত-অভিভূতকরা মহাসত্তাকে অনুভব করলেন। অভিভূত হয়ে গেলেন তিনি। অথচ কয়েকটা দিন বর্ষণে বাতাসে কী দুর্যোগই না চলেছে।
সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকে চলেছে এই তপস্যা। মহা-উত্তাপে ফুটন্ত, দাবদাহে দগ্ধ, প্ৰলয়ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত, মহাবর্ষণে প্লাবিত বিধ্বস্ত পৃথিবী এই তপস্যার আশীর্বাদে আজ শস্য-শ্যামলতায় প্রসন্না, প্রাণস্পন্দিতা, চৈতন্যময়ী। সেই তপস্যারত মহাসত্তা এই মুহূর্তে যেন প্রত্যক্ষ হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথের অভিভূত সত্তার সম্মুখে। ধ্যাননিমীলিত নেত্র উন্মীলিত করে যেন তার বক্তব্যের প্রতীক্ষা করছেন।
জ্ঞানেন্দ্রনাথ আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।
–বিচার কর আমার, শাস্তি দাও। তমসার সকল গ্লানির ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ কর আমাকে। মুক্তি দাও আমাকে!
পিছনে ভিজে ঘাসের উপর পায়ের শব্দ উঠছে। ক্লান্তিতে মন্থর। অন্তরের বেদনার বিষণ্ণতায় মৃদু। সুরমা আসছে। অশ্রুমুখী সুরমা।
তবুও তিনি মুখ ফেরালেন না।
আদিঅন্তহীন ব্যাপ্তির মধ্যে তপস্যারত জ্যোতিৰ্মান এই বিরাট সত্তার পাদমূলে প্রণতি রেখে তাঁর অন্তরাত্মা তখন স্থির শান্ত স্তব্ধ হয়ে আসছে। সুমতির ভ্ৰকুটি বিগলিত হয়ে মিশে যাচ্ছে। প্রসন্ন মহাসত্তার মধ্যে।
আজ যদি কোনোক্রমে সুরমা মরণ-আক্রমণে আক্রান্ত হয়—সুরমা কেন—যে-কেউ হয়, তবে নিজের জীবন দিয়ে তিনি তাকে রক্ষা করতে কাঁপিয়ে পড়বেন। মৃত্যুর মধ্যে অমৃত অসীম শূন্য আকাশের পূর্ণচন্দ্রের মত প্রত্যক্ষ। তাঁর অন্তরলোকে চৈতন্য শতদলের মত শেষ পাপড়িগুলি মেলেছে।
সুরমা এসে দাঁড়ালেন তার পাশে; শান্ত ক্লান্ত মুখখানির চারিপাশে চুলগুলি এলিয়ে পড়েছে, দুচোখের কোণ থেকে নেমে এসেছে দুটি বিশীর্ণ জলধারা, নিরাভরণা-বেদনার্তা-পরনে একখানি সাদা শাড়ি; তপস্বিনীর মত।