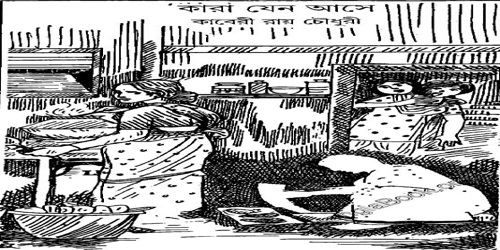শীতের বিকেল বড্ড তাড়াতাড়ি শেষ হয়। আর চায়ের তেষ্টাও পায় বেশী। ১৮৯৪ শকাব্দ শেষ হয়ে আসছে, আর মাত্র কয়েক দিন, তার পরেই ১৮৯৫ শকাব্দ শুরু হবে। কিন্তু আজকাল ভারতে সরকারি শকাব্দ কেউই আর মনে রাখেনা। সাল জিজ্ঞেস করলে ১০০ জনে ১০০ জন ভারতীয়ই বলবে এটা ১৯৭২ সাল, মানে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ। আহমেদাবাদের উপকণ্ঠের এই নতুন মহল্লায় সব বাড়ির বাসিন্দারাই বাড়ির সঙ্গে একটু করে বাগান রেখেছেন। শেষ বিকেলের ঝিরি ঝিরি ঠান্ডা হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে। গায়ে কাজকরা কাশ্মিরি শালটা ভাল করে জড়িয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসলেন অধ্যাপক। সামনে চশমা চোখে নবীন ছাত্রটিকে তাঁর বেশ পছন্দ। তার প্রশ্নের শেষ নেই। খুঁটিয়ে জানতে চায় সব কিছু।
– কিন্তু চার ছেলের মধ্যে শাহজাহান কাকে বেশী পছন্দ করতেন?
– এইটে বলা ভারি মুশকিল বাবা। বড় ছেলে দারা শিকোহ ছিলেন সেরার সেরা পন্ডিত। সুজা ও মুরাদ অদূরদর্শী, তার ওপর নেশাখোর, যুদ্ধবাজ, আরো যত্তসব ইয়ে…
– কিন্তু ঔরঙ্গজেব? তাঁর তো এসব বদ অভ্যেস ছিলোনা, তা সত্ত্বেও কি করে….
– দেখো বাছা, কুর্সী তো ওই একটিই, যতই যোগ্য লোক থাকুক না কেন। নেহাত তখন পিতৃতন্ত্র জাঁকিয়ে বসে আছে, না হলে জাহানারাও কিন্তু কম যোগ্য নন অন্য শাহজাদাদের চেয়ে। তবে জাহানারা নিজে কখনো সিংহাসনের কথা হয়ত ভাবেননি। দারাকেই দেখতে চেয়েছেন। দারাকে নিজের স্বার্থেও প্রয়োজন ছিলো জাহানারার।
মুচকি হাসল ছাত্রটি। অধ্যাপকের বসার ঘরের দরজার ওপাশে একটা ছায়া সরে গেল। যে কারনে এসে প্রতিটি ছুটির দিন বিকেল বেলা একজন পদার্থবিদ্যার ছাত্র, ইতিহাসের অধ্যাপকের কথা শুনতে বাধ্য হয় ঘন্টার পর ঘন্টা, সেই কারনটি পর্দার আড়ালে ঘুরঘুর করছে। হয়ত চায়ের কাপ হাতে এখুনি এসে উদয় হবে।
– বুঝলে হে, দারার চিন্তা ভাবনা, নিজের সময়ের চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে ছিল। অনেক মুক্ত মনের মানুষ ছিলেন দারা।
– শুনেছিলাম, কিন্তু খুব বেশী কিছু জানিনা
– সমস্ত রকম মানুষের সঙ্গে মিশতেন। সে হিন্দু, মুসলিম, জাট, রাজপুত, পাঞ্জাবী, তুর্কি, মোপলা,হাবসি, খ্রিষ্টান যে ই হোক না কেন। ওনার খুব কাছের মানুষদের অনেকেই হিন্দু, যেমন অমর সিং।
– অমর সিং রাঠোড়? দারার সঙ্গে অমর সিং এর সখ্যতা নিয়ে আমি খুব একটা কিছু জানিনা। অমর সিং তো জাঁদরেল ফৌজি। আর দারা শিকোহ পড়াশোনা নিয়েই থাকতেন, এইটুকুই জানি। বন্ধুত্বটা হলো কি করে?
– ভালোই বন্ধুত্ব ছিলো। তা না হলে ঔরঙ্গজেব হয়ত সত্যিই লড়াইতে নামতেন বড় ভাইয়ের সঙ্গে। সুজা আর মুরাদ তো তখন হয় মৃত বা গুরুত্বহীন।
– লড়াই তো প্রায় লেগেই গিয়েছিল বলছেন।
– তা লেগে গিয়েছিলো বটে। আগ্রা থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে। দারা আর ঔরঙ্গজেব মুখোমুখি। কিন্তু লড়াইটা হলোনা। দু ভাই মিটমাট করে ঘরে ফিরলেন। রাজপুত অমর সিং আর জাহানারা মধ্যস্থতা করলেন। বৃদ্ধ সাহজাহান স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছেড়ে সরে গেলেন। আর সেইটাই আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সন্ধিক্ষন হয়ে দাঁড়ালো।
– কেন? সন্ধিক্ষন কেন? মুঘল বাদশাহী তার পরের দুশ বছর টিঁকে গেল বলে?
– সে জন্যে নয়, কিন্তু সেই প্রথম মুঘল বাদশাহী বহুত্বকে সরকারি স্বীকৃতি দিলো। যদিও ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে বসলেন, কিন্তু বস্তুতপক্ষে শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে রইলেন এক জন নয়, দুজন। দারা রইলেন আইন-কানুন-বিচার, শিক্ষা, অর্থ ব্যবস্থা নিয়ে, আর ভাই ঔরঙ্গজেব রইলেন প্রশাসনিক আর সামরিক বিভাগ নিয়ে।
– দুজনের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত কতটা প্রকট ছিলো? তখনকার দিনে তো লাঠালাঠি হবার কথা প্রতি পদক্ষেপে।
– সেই জাহানারা আর অমর সিং। জাহানারার প্রবল প্রভাব ছিল ঔরঙ্গজেবের ওপর। তার ওপর জাহানারার পাশে রয়েছেন অমর সিং রাঠোড়ের মত প্রবল প্রতাপ ও ক্ষমতাশালী সেনানায়ক, যাঁর পেছনে গোটা রাজপুতানা। এমনকি সওয়াই মান সিং পর্যন্ত অমর সিং এর পেছনে। কাজেই ঔরঙ্গজেব বেশী ঘাঁটান নি। তবে প্রথম দিকে ধর্মীয় গোঁড়ামি নিয়ে থাকলেও, পরবর্তীকালে ঔরঙ্গজেব কিন্তু রাজনৈতিক প্রয়োজনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। না হলে, শিবাজী ভোঁসলে ঔরঙ্গজেবের সবচেয়ে কাছের মানুষ হতেন না।
– শিবাজির সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের বন্ধুত্বটা আমার অদ্ভুত লাগে। দুজনে দুই মেরুর মানুষ।
– সেটা বাহ্যিক। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে দুজনেই এক। একই রকম স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস রাখতেন। দুজনেরই লাভ হয়েছিল এতে। রাজপুত, ডোগরা, জাট গোষ্ঠি ছিল দারার পেছনে। এ ছাড়া শিখ আর পাঠানদের সমর্থন তো ছিলোই। ঔরঙ্গজেবের দরকার ছিল বিশ্বস্ত শক্তিশালি বিচক্ষন বন্ধু। শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠারা ঔরঙ্গজেব কে সেই ক্ষমতা দিল। আবার ঔরঙ্গজেবের কাছের লোক হয়েও মারাঠা বৈরিতার কারনে আদীলশাহী ও হায়দরাবাদের নিজাম ঔরঙ্গজেবের থেকে দুরত্ব বজায় রাখলেন। আর মহিশুর তো বিদ্রোহ ঘোষনা করে বসল।
টুংটাং আওয়াজ হচ্ছে। একটা রূপোর রেকাবিতে চায়ের পেয়ালা বসানো। চায়ের অভ্যেস এদেশের নিজের নয়। মধ্য এশীয়া হয়ে, তুর্কোমান, কাবুলি ও পাঠানের হাত ধরে চা এদেশে ঢুকেছে। কিন্তু ঢুকেই জাঁকিয়ে বসেছে গত শ খানেক বছরে। চা ছাড়া ভারতের কোন শহরকেই ভাবা যায় না, তা সে কাবুল হোক বা কলকাতা। চা পরিবেশনের সময় হালকা চোখাচুখি হল। একটু হাসি দেখা গেল কি? ফিরোজা রঙের ওড়নার ফাঁক দিয়ে বড্ড ভালো লাগে গম রঙা মুখখানা। ছাত্রটি দেখছে হাঁ করে। এই টুকু দেখা পেতে হা-পিত্যেস করে বসে থাকা।
– শিবাজী আর মারাঠারা মুঘলদের আর একটা খুব শক্তিশালী জিনিস দিয়েছিলেন। সেটা হলো কানহোজি আঙরের নেতৃত্বে মারাঠা নৌবহর।
– তার আগে মুঘলদের নৌবহর ছিলোনা?
– ধুস। মুঘলরা নৌবহরের গুরুত্ব বুঝতোনা। এই প্রথম তারা সেটা বুঝলো, যখন আরব সাগরে আন্দালুসি আর পর্তুগিজ নৌবহরের সঙ্গে তাদের লড়াই বাঁধলো।
– কিন্তু তার আগে মুঘলরা বাংলায় নৌসেনা তৈরি করেনি?
– করেনি বলেই তো ব্রহ্মপুত্রের ওপর সরাইঘাটে লচিত বরগোঞায়ের হাজার খানেক অহোম সেপাই মুঘল পল্টনকে ধরে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিলো। কিন্তু পশ্চিম উপকুলে এই নৌবহর ছিলো বলেই মালাবার-কোঙ্কন-কচ্ছ-সিন্ধ আন্দালুসি-পর্তুগালি হার্মাদের থেকে রক্ষা করে গেছে।
– ভাবছি যদি ইয়োরোপীয়রা আমাদের উপকূলে পা রাখতো, তাহলে কি হতো!
– টমাস রো বা তাভেরনিয়ের মত বা মার্কো পোলো কি ইবনে বতুতার মত এলে তো সমস্যা নয়, সমস্যা ওই ভাস্কো-দা-গামার মত এলে। যদি কচ্ছ কি সিন্ধু উপকূলে এরা নেমে পড়ত, তাহলে হয়ত এই আহমদাবাদের নাম বদলে অন্য কিছু হয়ে যেত।
চায়ের সঙ্গে একটা পাথরের থালায় করে কিছু আখরোট, বাদাম, কাঠবাদাম, কাজু, তরমুজের বীজ, কিসমিস এই সব মিলিয়ে মিশিয়ে রাখা। অধ্যাপকের আদিভূমি পেশাওয়ারের মানুষের এ ধরনের মুখচটকা খাওয়া খুব পছন্দের। গুজরাতের মানুষ, বিশেষ করে তরুন ছাত্রটির আপন মেহসানাতে লোকজন ভাজাভুজি বেশি খায়, সঙ্গে চড়া স্বাদের চাটনি বা আচার। কিন্তু তরুন ছাত্রটির, মৃদু স্বাদের এই থালাটি বড় প্রিয়।
– ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, বাহাদুর শাহ বসলেন মুঘল তখতে। কিন্তু ওদিকে প্রায় ১৫ বছর আগে দারার মৃত্যুর পর দারার জায়গায় বসেছেন সুলেমান শিকোহ। একে তিনি বাহাদুর শাহর চেয়ে বয়সে বড়, তার ওপরে শাসনকার্যে অভিজ্ঞতাও বেশী। বাহাদুর শাহ একটু লক্কা পায়রা গোছের ছিলেন। ওদিকে ঔরঙ্গজেবের প্রধান সমর্থক শিবাজীর পরিবারে তখন খুব গন্ডগোল। শিবাজীর নাতি শাহুজী তাঁর কাকিমা তারাবাঈয়ের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়েছেন মারাঠা শক্তির অধীশ্বর হবার জন্যে।
– দাঁড়ান দাঁড়ান। গুলিয়ে যাচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি বললে বুঝে উঠতে পারিনা। মানে, ঔরঙ্গজেবের পর দিল্লির তখতে তখন সেই দুই শাসক, একজন সুলেমান শিকোহ, আর একজন বাহাদুর শাহ? সুলেমান শিকোহ আইন-কানুন,শিক্ষা, অর্থ ইত্যাদির দায়িত্বে আর বাহাদুর শাহ প্রশাসনিক আর সামরিক প্রধান, তাই তো?
– একদম ঠিক। সুলেমানের পেছনে, পিসিমা জাহানারা এবং তাঁর পরিচিত মহলের সমর্থন ছিলোই। উপরন্তু জাট, শিখ এবং পাঠান কৌমি নেতারাও সুলেমানের পেছনে। অম্বরের রাজপুত রাজা যসবন্ত সিং সুলেমানের পার্শ্বচর। ওদিকে বাহাদুর শাহর বড় ভরসা মারাঠারা তখন বিভক্ত। কাজেই বাদশা নিজেই নিজের ক্ষমতা দেখাতে গিয়ে কতগুলো চরম হঠকারি কাজ করে বসলেন।
– বাহাদুর শাহ কতগুলো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন এইটুকু মনে করতে পারছি। কিন্তু কি কি লড়াই, কাদের সঙ্গে লড়াই, সেই সব একদম মনে নেই।
– স্বাভাবিক। এসব মনে থাকা কঠিন। কেননা, এই যুদ্ধবিগ্রহগুলো, সমকালিন বা পরবর্তী ইতিহাসে একটুও ছাপ ফেলেনি। এমন কি বাহাদুর শাহর মৃত্যুর পর বছরখানেকের জন্যে গদিতে বসেন জাহান্দার শাহ। তিনিও ছাপ রেখে যাবার মত কিছুই করে উঠতে পারেন নি।
– মুঘল সামরিক ক্ষমতা কি এই ভাবেই ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়ায়?
– একদম তাই। এবং আঞ্চলিক সামরিক নেতারা নিজেদের ক্ষমতা বাড়ানোর খেলায় মেতে ওঠেন। যেমন ধরো পেশোয়া, নিজাম, মহিশুর।
– কিন্তু মুঘল অর্থনৈতিক আর আইনি ব্যবস্থা সুলেমানের হাতে পড়ে বোধহয় অনেকটা উন্নত হয়েছিল, মানে ইতিহাস বইতে সেরকমই পড়েছিলাম মনে পড়ছে।
– এইটা হয়েছিল বলেই জান্দাহার শাহর পরের বাদশা ফররুখশিয়ার একটা কেলেংকারি করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত পারেন নি। ইয়োরোপের পশ্চিমে ইংলিস্তানের কিছু বানিয়া বাদশার কাছে একটা অনুমতি চান ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে। ইংলিস্তানের লোক ভারতকে ইন্ডিয়া বলে। বাদশা দরাজ দিল হয়ে সেটা দিয়েই দিতেন, নেহাত বৃদ্ধ সুলেমান শিকোহ জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে সে ফরমান বাতিল করেন, কারন বাদশার এখতিয়ার ছিলোনা অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিক ব্যাপারে হুকুম চালানো।
– ইংরেজদের মতলব কি ভালো ছিলোনা?
– মোটেই সুবিধের ছিলোনা। দিনেমার, ওলন্দাজরা সুবা বাংলায় অনেকদিন ধরেই বানিজ্যকুঠি তৈরি করে কারবার চালাচ্ছিলো। ফরাসিরাও শুরু করেছিলো দক্ষিন আর পূর্ব ভারতে তাদের ব্যবসা। কিন্তু ইংরেজদের মতলব ভাল ছিলোনা।
– ফরাসিদের সঙ্গে ইংরেজদের সে আমলে খুব আখচাআখচি ছিলো শুনেছি।
– সে তো ছিলোই। সেই জন্যেই ইংরেজরা প্রথমে মুর্শীদকুলি খানকে হাত করবার চেষ্টা করেছিল, যাতে বাংলায় তারা জমিয়ে বসতে পারে, আর ফরাসিদের খেদিয়ে দেওয়া হয়।
– তার পর?
– মুর্শীদকুলি খান সম্পর্কে কতটুকু পড়েছ ইতিহাসে?
– সেরকম কিছুই না, বলা ভাল প্রায় কিছুই পড়িনি, বা পড়লেও মনে নেই।
– মুর্শীদকুলির জন্ম কিন্তু দক্ষিন ভারতে, কন্নড় হিন্দু ব্রাহ্মন পরিবারে। অত্যন্ত গরীব বলে বছর দশেক বয়সে ওনাকে হাজি সফি বলে এক ইরানি আশ্রয় দেন ও বড় করেন। হাজি সফির সঙ্গে মুর্শীদকুলি ইরানে যান, সেখানে বছর পাঁচেক থাকেন, আর হাজি সফির মৃত্যুর পর আবার ভারতে ফিরে আসেন, এবং বিদর্ভে মুঘল প্রশাসনিক বিভাগে যোগ দেন। ইরানে থাকার দরুন, ইয়োরোপীয়দের সাম্রাজ্যবিস্তারের গপ্পসপ্প তাঁর ভালোই জানা হয়ে যায়। বিদর্ভেই মুর্শীদকুলি ঔরঙ্গজেবের নজরে পড়েন, এবং ঔরঙ্গজেব তাঁকে বাংলায় পাঠান। এই মুর্শীদকুলি হয়ে উঠলেন সুবে বাংলার সর্বেসর্বা।
– এত বৈচিত্রময় জীবন বলেই বোধহয় ওনার ইংরেজদের চিনতে ভুল হয়নি।
পেশাওয়ারি অধ্যাপকের চা খাওয়ার ধরনটি খাঁটি মধ্যএশিয় বা রুশি। প্রথম পেয়ালা চায়ের সঙ্গে অধ্যাপকের ছোটো কন্যা একখানা সামোভার রেখে গেছেন। তাতে গরম জল ফুটছে। আর একটি খোপে কড়া লিকার। অধ্যাপক অল্প একটু লিকার ঢাললেন নিজের পেয়ালায়, তার পরে গরম জল মিশিয়ে চুমুক দিলেন। চৌকো চৌকো চিনির টুকরো যদিও রয়েছে, কিন্তু উনি চিনি নিলেন না। এদিকে ছাত্রটির গুজরাতি জিভে চায়ের স্বাদ মানে বেশ কিছুটা দুধ, প্রচুর চিনি, এবং প্রায়শঃই তাতে আদা, এলাচ, এসবের উপস্থিতি।
– তোমার বাড়ি তো মেহসানা জেলায়, তাই না?
– আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার বাবার ওখানে একটা দোকান আছে, মুদির দোকান বলতে পারেন
– তোমাদের জেলায় তো মোষের দুধ বিখ্যাত, তোমার নিশ্চই দুধ দিয়ে চা খাওয়া অভ্যেস
– খান সাহেব, আপনি কি ভাবে বুঝে ফেলেন বলুন তো?
চা আর এক কাপ খেতে যে খুব ইচ্ছে করছিলো এমন নয়, কিন্তু দুধের উপস্থিতি মানেই আকাশী ওড়নার দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা, তাই সুযোগটুকু নেওয়াই সঙ্গত। অধ্যাপক পাস্তো ভাষায় একটু গলা তুলে দুধের হুকুম করলেন।
– সুলেমান শিকোহ মারা যাবার আগে একটা চমৎকার কাজ করে গিয়েছিলেন, মুঘল আইনি ও অর্থনৈতিক-বানিজ্যিক বিভাগকে বিকেন্দ্রিভূত করে।
– তার মানে?
– মানে, আগে যেমন সব কিছু সুলেমান শিকোহ বা দারা নিয়ন্ত্রন করতেন দিল্লি থেকে, এবার সেটা না হয়ে ক্ষমতা গেল মজলিস-এ-ইত্তেহাদুল-কানুনির হাতে। আর ঠিক এই জায়গা থেকেই, রাজা-বাদশা ছাড়াও, সাধারন নাগরিকের একটা জায়গা হলো মুঘল শাসন ব্যবস্থায়। প্রথম দিকে গন্যমান্য বাদশাহি লোকজন থাকলেও, আস্তে আস্তে প্রকৃত গুনি এবং পন্ডিত মানুষজন আসতে শুরু করলেন মজলিসে। আর সেই হিসেবে, বিভিন্ন জাতের ও ধর্মের মানুষের প্রতিনিধিত্ব পেলো সরকারি স্বীকৃতি
– তার মানে, দারা এবং সুলেমানই এ দেশের জনপ্রতিনিধিভিত্তিক শাসনের প্রতিষ্টাতা?
– তা নয়, এর বহু বহু আগেই ব্রিজি, লিচ্ছবী বা যৌধেয় গনরাজ্য ছিলো ভারতে। কিন্তু সে ব্যবস্থা স্থায়ী হতে পারেনি। মুঘল ব্যবস্থা টিঁকে যাবার অন্যতম কারন, অত্যন্ত ক্ষমতাশালী মুঘল সামরিক শক্তি। যে বাইরের শত্রুর আক্রমনের পথ বন্ধ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে নিরাপত্তা দিয়ে বিকশিত হতে দিয়েছিল।
– তার মানে আপনি বলছেন সামরিক শক্তি ছাড়া প্রশাসনিক স্থায়িত্ব দেওয়া সম্ভব নয়?
– নিরাপত্তার দিক থেকে দেখলে কিছুটা তো বটেই। আমি একটা সুন্দর করে কিছু সাজাতে শুরু করলাম, কিন্তু প্রথম রাতেই চোরে সব চুরি করে নিয়ে গেল, তাহলে কি আমি কিছু তৈরি করতে পারব?
– তা বটে।
– কিন্তু মুঘল সামরিক শক্তির বহর বেশী থাকলেও তারা স্থবীর হয়ে পড়ছিলো, নাহলে তুর্কোমান …………।
– স্থবির মানে?
– মানে অনেক দিন বসে থাকতে থাকতে সেনাবাহিনির যুদ্ধক্ষমতা কমে গিয়েছিলো, তার ওপরে সময়মত আধুনিক প্রযুক্তিও তারা গ্রহন করেনি। তাই রুশিরা যখন মধ্য এশিয়া আক্রমন করলো, আর বুখারা, সমরকন্দ মুঘল বাদশার সাহায্য চাইলো, আমাদের ফৌজ কাবুল থেকে পাঠাতেই বহু দেরি হয়ে গেল। না হলে হয়ত আমার বাবা পাসপোর্ট ছাড়াই আশকাবাদ কি সমরকন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে যেতে পারতেন।
পর্দার ওপাশে আবার টুংটাং আওয়াজ। দুধের ছোট্ট কেতলি সমেত আকাশী ওড়নার আগমন। কয়েক মুহুর্তের চোখাচুখি। খান সাহেব চারমিনার সিগারেটে টান দিলেন জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। সন্ধ্যে নামছে, একে একে আলো গুলো জ্বলে উঠছে রাস্তায়। হালকা কুয়াশায় আলোগুলো কেমন ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। কাছাকাছি কেউ রেডিওতে খেলার ধারা বিবরনী শুনছে, আজ বোধহয় বড় ফুটবল ম্যাচ আছে দিল্লিতে। ফুটবল নিয়ে এ দেশের লোক পাগল। অবশ্য গোটা বিশ্বের লোকই তাই। ফুটবলে ভারতের সুনাম ছড়িয়েছে বিশ্বে। তবে বিশ্বকাপের আসরে ভারত কোয়ার্টার ফাইনালের গন্ডি পেরোয়নি কখনো। ছাত্রটির দিকে তাকালেন খান সাহেব। সে আনমনে একবার কুর্তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে আবার বের করে নিল। খান সাহেব কে সিগারেট ধরাতে দেখে, তার ও ইচ্ছে হয়েছে বোধহয়, কিন্তু গুরুজনের সামনে ধুমপান করার প্রচলন ভারতীয় সমাজে নেই। এই ছোকরার মতিগতি তিনি ভালোই বোঝেন, সে কেন আসে এ বাড়িতে, ইতিহাসের মত একটা নিরস বিষয় নিয়ে কেন সে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করে, তবুও একটা প্রশ্রয় সূচক নিরবতা পালন করে চলেন তিনি। মা মরা ছোটো মেয়ে, সে বাবার বড় আদরের। তার ভাললাগাকে তিনি বাধা দিতে পারেন না।
– সোভিয়েত অধিকারে থাকা তুর্কোমেনিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ভারত নৈতিক সমর্থন জানিয়ে আসছে, এটা ভাল না খারাপ?
– ভাল-খারাপ এসবের বিচার করবার আমরা কে? আমরা বড়জোর পক্ষে আর বিপক্ষের যুক্তি টুকু সাজাতে পারি। কিন্তু ভেবে দেখো বিচারের জায়গায় এলেই তুমি বা আমি, কোনো না কোনো ভাবে প্রভাবিত হয়ে , কোনো এক দৃষ্টিকোন থেকে দেখতে শুরু করব।
– তার মানে আমরা কি ভাল খারাপ বিচারই করবনা?
– তা ঠিক নয়, তবে কিনা, মন খোলা রাখা উচিত। যা ঠিক, যা ঠিক মনে হচ্ছে, তা ছাড়াও অন্য সম্ভাবনা থাকতেই পারে। এইটুকু মনে রাখতে পারলেই অনেক। এতে বহুত্ববাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা পোক্ত হয়।
– মুঘল বাদশা আস্তে আস্তে শুধু মাত্র নামেই রয়ে গিয়েছিলেন, ইতিহাসে পড়েছি। ফররুখশিয়ারের সময় থেকেই মুঘল বাদশার প্রতিপত্তি কমতে থাকে, ও আইন সভার প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। এমন কি বাদশা মুহম্মদ শাহের সময় এমন অবস্থা পৌঁছয়, যে বেশীরভাগ সেনানায়করা মজলিস, বা আইন সভার কথায় চলতেন। কেননা মুহম্মদ শাহ ভালবাসতেন কাব্য-শিল্প-সাহিত্য, নিজেও ভাল লিখতেন।
– মুহম্মদ শাহের নামটা একটু….
– চেনা চেনা লাগছে? এই ইনিই তো সেই বিখ্যাত কথাটা বলেছিলেন ফার্সিতে – “দিল্লি দূর অস্ত্”
– সে তো নাদির শাহের ভারত আক্রমনের সময়।
– একদম ঠিক। নাদির শাহ একটু করে এগিয়ে আসেন, প্রথমে কান্দাহার তার পর গজনী হয়ে নাদির কাবুল আক্রমন করলেন। এদিকে যতবার খবর আসে দিল্লিতে, মুহম্মদ শাহ আর কিছুতেই গা তোলেন না, খালি বলেন “দিল্লি দূর অস্ত্”, মানে দিল্লি এখনো অনেক দূর। শেষে জালালাবাদে নাদির শাহর পৌঁছনোর খবর পাওয়া গেল যখন, দিল্লির বড় বড় বাদশাহী পদাধিকারীরা প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেলেন। জালালাবাদের পরেই খাইবার, যা পেরোলে পেশাওয়ার, আর তার পরে খোলা মাঠের মত পড়ে রয়েছে পাঞ্জাব। তখন তাঁরা দল বেঁধে গেলেন আইন সভার কাছে, মজলিশে।
– মজলিশে কেন? মজলিশ তো কেবল আইন কানুন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর ব্যাবসা বানিজ্য দেখতো।
– তা হলেও, বাদশা কে বাদ দিলে, গোটা মুঘল রাস্ট্রব্যবস্থার মধ্যে এই মজলিশই হলো সার্বভৌম। কাজেই, বাদশা ছাড়া আর কেউ যদি থাকে, তো সে এই মজলিশ।
– আচ্ছা, তাহলে কি এই ঘটনার পর থেকেই মজলিশের প্রভাব বাড়তে থাকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে?
– ঠিক ধরেছ। মজলিশের মাথা তখন মারাঠি চিতপাবন ব্রাহ্মন বল্লাল ভট্ট। অত্যন্ত বিচক্ষন আর ক্ষুরধার বুদ্ধির লোক। তবে নিজের নামে ওনাকে লোকে বেশী চেনেনা, যতটা চেনে বালাজি বাজিরাও, বা পেশোয়া বালাজি বাজিরাও নামে। ইনি ছিলেন শিবাজির নাতি শাহুজির মারাঠা মন্ত্রি বা পেশোয়া। তখন মুঘল শক্তির প্রধানতম উৎস মারাঠা লস্কর ও মারাঠা সেনাপতিরা। দিল্লিতে তাঁদের প্রবল প্রতাপ। তাই বাজিরাওয়ের বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব দেখে শাহুজী এনাকে দিল্লি মজলিশে নিয়ে আসেন মারাঠা প্রভাব বাড়াতে, আর নিজের গুনেই মজলিশের প্রধান হয়ে বসেন পেশোয়া বাজিরাও।
– বাজিরাও শুনেছি মারাঠা বাহিনি নিয়ে………
– বাজিরাও গুনী আর ব্রাহ্মন পন্ডিত হলে কি হবে? অন্যদিকে তিনি দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও সেনানায়কও ছিলেন। আর তাঁর মারাঠা সেনাবাহিনিও সেরকমই ছিল। মারাঠা লস্করের প্রধান গুন হলো, খুব তাড়াতাড়ি তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছতে পারত, কারন তারা মূলতঃ ঘোড়সওয়ার সেনা।
– মারাঠা ফৌজ তখন দিল্লিতেই ছিলো?
– না না, তারা তখন পুনেতে। সেখানেই তাদের ঘাঁটি। কিন্তু খবর পাওয়া মাত্র মারাঠা পল্টন রওনা দেয়। এদিকে পেশাওয়ারে হানা দেয় নাদির শাহর বাহিনি। স্থানীয় মুঘল লস্কর আর উপজাতীয় পাঠানরা প্রচন্ড প্রতিরোধ দেয়, কিন্তু নাদিরকে আটকানো যায়নি। নাদির সিন্ধু অতিক্রম করে লাহোরের দিকে আসতে থাকেন।
– আর মারাঠারা?
– মারাঠারা তখন দিল্লি পৌঁছচ্ছে। বাজিরাও একদিনও বিশ্রাম না দিয়ে সেনা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। নাদিরের সঙ্গে মুঘল-মারাঠা সেনার লড়াই হয় কার্নাল বলে একটা ছোট শহরের কাছে। সংখ্যায় অনেক কম হওয়া সত্বেও মারাঠা ফৌজের উন্নত কলাকৌশল আর বুদ্ধির কাছে নাদিরের ইরানি ফৌজ হার মানে। নাদিরকে বন্দী করে দিল্লির দরবারে হাজির করা হয়।
– কিন্তু বাদশা তো নাদিরকে ছেড়ে দেন।
– ছেড়ে দেন বটে, তবে বাজিরাওয়ের পরামর্শে কাবুল–কান্দাহার-গজনী-হেরাতের ওপর থেকে চিরকালের মত ইরানি দাবী তুলে নিতে তাঁকে বাধ্য করা হয়। তার ওপর প্রচুর ধনরত্নও নাকি আদায় করা হয়েছিলো। এমন কি ইরানের রাজপরিবারের সিংহাসন পর্যন্ত দিল্লিতে রেখে দেওয়া হয়। নাদির যেখানে যেতেন, আপন সিংহাসন সঙ্গে করেই নিয়ে যেতেন। সবই বাজিরাওয়ের পরামর্শে।
– মানে মজলিশ এবং বাজিরাওয়ের প্রভাব আকাশ ছোঁয়া হয়ে উঠলো।
– হ্যাঁ আর সেই সঙ্গে বাদশার প্রভাব কমতে থাকলো। কেননা এর পরের দুজন মুঘল বাদশা, আহমদ শাহ আর দ্বিতীয় আলমগীর এই মহম্মদ শাহের মতোই অকর্মন্য। আহমদ শাহ যদিও মাত্র দেড় মাস বাদশা ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় আলমগীর রাজত্ব করেন প্রায় ৯ বছর। কিন্তু সিংহাসনে বসার সময়েই তিনি ৫৫ বছরের প্রৌঢ়, তার ওপর না করেছেন একটাও যুদ্ধ, না করেছেন কোনো প্রশাসনিক কাজ। কাজেই, তাঁর কোনো অভিজ্ঞতাই ছিলোনা। এই ৯ বছর মুঘল ইতিহাসে নিস্ফলা। পরের বাদশা তৃতীয় শাহজাহান, তিনিও রাজত্ব করেন মোটে ১ বছর। সেই এক বছরে বলার মত তেমন কিছুই ঘটেনি।
বাড়ির ভেতর থেকে রেডিওর গান ভেসে আসছে। বিবিধ ভারতী প্রচার তরঙ্গে ছায়াছবির গান। খান সাহেবের গান-বাজনা নিয়ে তেমন জ্ঞান-গম্মি বা আকর্ষন কোনোটাই নেই। তবে তাঁর ছোটো মেয়ের কাছে সঙ্গীত হল প্রায় জীবনের মত। সে মহম্মদ রফির গানের খুব ভক্ত, আর সিনেমায় তার প্রিয় অভিনেতা রাজেশ খান্না, এইটুকু খান সাহেব জানেন। ভারতীয় উর্দু ছবির বেশীরভাগ নায়কই লাহোর আর তার চারপাশ থেকে এসেছেন। সেদিন যেন কোন একটা কাগজে পড়ছিলেন এই নিয়ে একটা লেখা। লাহোর বলতেই মনে পড়ে যায় অনেক কিছু। সেই আনারকলি বাজার, শাল্মি মহল্লা…
– লাহোর গেছ কখনো?
– লাহোর? আজ্ঞে না খান সাহেব। যাওয়া হয়নি। শুনেছি খুব জাঁকজমকের শহর।
– জানো তো, কথায় আছে, “যে লাহোর দেখেনি, সে কিছুই দেখেনি”। দেশ কে দেখতে হবে, বুঝলে ছোকরা। জানতে হবে। মানুষজন, তাদের সংস্কৃতি, অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গি, সব কিছু জানতে হবে। ভারতীয় সমাজকে চিনতে হবে।
– আজ্ঞে আমার ও ইচ্ছে, ঘুরে ঘুরে দেখি গোটা দেশ। কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
– ইচ্ছে থাকলে উপায় ও হয়। তোমার মতই আর এক জন, তোমারই নামের, আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর আগে গোটা দেশ ঘুরেছিলো পায়ে হেঁটে। ভেবে দেখো। কি ছিলো তার সঙ্গে? সন্ন্যাসি মানুষ। তুমিও গেরূয়া ধারন করে বেরিয়ে পড়তে পারো।
– খান সাহেব, আমি যতদুর জানি, আপনি নিজে ইশ্বর বিশ্বাসী নন। এমন কি ……
– এমনকি??
– মানে, আমি না, লোকে বলে……
– কি বলে?
– মানে, বলে যে, আপনি নাকি রাজনৈতিক ভাবে বামপন্থী।
– যারা বলে, তারা ঠিকই বলে। আরে আমি তো প্রত্যক্ষ্য বাম রাজনীতি করেছি একটা সময়।
– এটা আমার জানা ছিলোনা
– ও, তাই বুঝি তুমি সোভিয়েতের দখল থেকে তুর্কোমানদের স্বাধীনতার দাবী নিয়ে আমার মত জানতে চাইছিলে?
– ছাড়ুন না
– বেশ, ওসব ছাড়লুম। তবে কিনা, তুমি এখন ঝাড়া হাত পা ছোকরা, তাই বলি, বেরিয়ে পড়ো, দেশ দেখো। অনেক অনেক কিছু শিখবে।
– লাহোর যাবোই
– লাহোর নিয়ে খুব আদিখ্যেতা ছিলো বাদশা শাহ আলমের। ওনার নামেই লাহোরের কেন্দ্রস্থলে মূল মহল্লার নাম শাহ-আলমী, সেটাই এখন মুখে মুখে হয়ে গেছে শাল্মি। শাহ আলম শেষ মুঘল বাদশা, যিনি সেনাবাহিনীর কর্তৃক্ত ফিরে পেতে চেষ্টা করেছিলেন। সে সময় সুবে বাংলায় মুর্শীদকুলির নাতি সিরাজউদ্দৌলা কে সরিয়ে তাঁরই সেনানায়ক মিরজাফর বাংলার ক্ষমতা হাতে নিতে চাইছে। সিরাজ পালিয়ে মুঙ্গেরে মুঘল কেল্লায় আশ্রয় নেন। মিরজাফর মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়তে, আর কিছু না পেয়ে ইংরেজদের ডেকে আনেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইংরেজ সৈন্যবল ছিলো খুব অল্প। মুঙ্গের থেকে মুঘল ফৌজ মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। মিরজাফর দক্ষিনে পালাতে থাকেন ইংরেজের ঘাঁটি সুতানুটির দিকে। পলাশী বলে একটা জায়গায় মুঘল ফৌজ আর মিরজাফরের বাহিনির ঘোরতর লড়াই হয়। সিরাজও যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, এবং একটা গোলার ঘায়ে তিনি মারাও যান। কিন্তু মিরজাফরের সেনাদের একটা অংশ মুঘল বাহিনির বিপক্ষে অস্ত্র ধরতে না চেয়ে লড়াই করলনা, ফলে মিরজাফর পরাজিত হলেন। ইংরেজ অধিনায়ক ক্লাইভকে বন্দি করা হয়। বাংলার রাজধানী মুর্শীদাবাদ মুঘল অধিকারে আসে, এবং আরো দক্ষিনে গিয়ে গঙ্গার ধারে ব্রিটিশ ঘাঁটি দখল করে মুঘল ফৌজ।
– কলকাতার উত্থান কি তার পর থেকেই?
– কালীঘাটের কালীক্ষেত্র থেকে নাকি লোকের মুখেমুখে সুতানুটি-গোবিন্দপুরের নাম দাঁড়ালো কলকাতা। নামের উৎস নিয়ে অবিশ্যি অনেক মত আছে। পর পর তিন জন বাঙালী বাবুকে জিজ্ঞেস করে দেখো, তিন জন তিন রকম কথা বলবেন। মুঘল সেনার একটা বড় ঘাঁটি রাখা হয় কলকাতায়। নতুন দুর্গ তৈরি হয় শাহ আলমের নামে, আলম কেল্লা। এর ফলে দক্ষিনে সমুদ্র থেকে ইংরেজ ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় শক্তি আর কখনো পূর্ব ভারতে মাথা গলাতে পারেনি। আর শাহ আলম কলকাতাকে সাজিয়ে তোলেন। অজস্র্ প্রাসাদ, বাড়ি, কেল্লা, মিনার তৈরি করা হয়। কলকাতার বিখ্যাত শহিদ মিনার, সিরাজের স্মৃতিস্তম্ভ। কিন্তু তার পর তো তাই নিয়ে অনেক জল ঘোলা হল।
– কলকাতাকে তো প্রাসাদের শহর বলে। সে শহরেও একবার যাবার ইচ্ছে আছে।
– হ্যাঁ। তবে সব প্রাসাদ তো আর শাহ আলম করে যেতে পারেন নি, ওনার পর অন্য মুঘল বাদশারাও সাজিয়েছেন ওই নতুন মুঘল শহরকে। দিল্লি, আগ্রা, লাহোর, কাবুল তখন অনেক পুরোনো শহর। নোংরা, ঘিঞ্জি। তাই নতুন শহর হিসেবে সেজে উঠলো কলকাতা, আর আওয়াধের রাজধানী লখনৌ। কিন্তু যতই পয়সা খরচ করুন বাংলায়, শাহ আলমের মনে যদি একটি শহর থেকে থাকে, সেটা কলকাতা নয়, দিল্লিও নয়। তা হলো লাহোর।
– আচ্ছা, এই শাহ আলমের সময়েই কান্দাহারে বিদ্রোহ শুরু হয় না?
– কান্দাহারের হর্তাকর্তা ছিলো দুররানি বংশ। কান্দাহার এমন একটা জায়গা, যেটা ভারতের একদম পশ্চিম সীমানা, এবং তাদের সঙ্গে পাশের ইরানি ভূমির প্রচুর মিল।
– দুররানিরাও কি ইরানি?
– না না, এরা ইরানিদের মত শিয়া নয়, সুন্নি। আর তা ছাড়া পাখতুনি সংস্কৃতির প্রচুর প্রভাব রয়েছে এদের ভেতর। কিন্তু নাদির যখন হেরাত কান্দাহারের পথে ভারতে আক্রমন করলেন, তখন এই কান্দাহারের দুররানিরা নাদিরের সঙ্গে যোগ দিলেন। সেটা না করলে অবশ্য ইরানি ফৌজের সঙ্গে লড়তে হতো।
– তার পর?
– যুদ্ধে হেরে ইরানি ফৌজ পালিয়ে গেল। আর কিছু ইরানি যোদ্ধা কান্দাহারেই থেকে গেল। এদের নিয়েই মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নামেন আহমদ শাহ আবদালী।
– আহমদ শা আবদালী কি ইরানি?
– না না, ইনি হলেন হোতাকি বংশের লোক, এনারা কান্দাহারের স্থানীয় মুঘল শাসক হিসেবে কাজ করতেন। আচমকা বিদ্রোহ করার ফলে, এনার আশেপাসে অনেক লোকজন জড়ো হয়ে গেল। নাদিরের দলছুট ইরানি সেনারা, স্থানীয় উচ্চাকাঙ্খী লোকজন এসব খুব তাড়াতাড়ি আদবদালীর পাশে এসে দাঁড়ালো।
– এদের উদ্দেশ্য কি ছিলো?
– উদ্দেশ্য বলতে, স্থানীয় ভাবে নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়ে মুঘল শাসন থেকে বেরিয়ে যাওয়া। সেই উদ্দেশ্যেই আবদালী গজনী দখল করে কাবুল পৌঁছন, আর কাবুলের মুঘল শাসন উৎখাত করেন। শোনা যায় বেশ কয়েক দিন ধরে কাবুলে লুঠতরাজ চলে।
– আজকাল ভাবাই যায়না, এখনকার কাবুলের মত এরকম একটা শান্ত সুন্দর সাজানো শহর, এত বার তচনছ হয়েছে।
– কাবুল একটা অসাধারন সুন্দর শহর। আর আমাদের সৌভাগ্য এখানেই, এত বার ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়েও কাবুল কিন্তু সেই সৌন্দর্্য্য ধরে রাখতে পেরেছে। আজকে ভারতের মানুষ ছুটি কাটাবার নাম করলেই দুটি শহরের কথা প্রথমেই মাথায় আসে, এক কাবুল, দুই শ্রীনগর। আর ওই শান্ত সমাহীত পাহাড় ঘেরা রূপের জন্যেই দেখো, আজকের ভারতের কয়েকটা সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ওই কাবুলে। পড়াশোনার জন্যে বড় সুন্দর পরিবেশ।
– আবদালী কি খাইবারের রাস্তায় ভারত আক্রমন করেন?
– অবশ্যই। তবে একবার নয়, সাত বার।
– সাত বার? এটা আমি প্রথম শুনলাম কিন্তু।
– ১৭৪৮ থেকে শুরু করে মোট সাতবার আক্রমন চালায় আবদালী। তবে সব চেয়ে বড় আক্রমন ছিল ১৭৬১ সালে। সেবার আবদালী প্রায় দিল্লি পৌঁছে গিয়েছিল।
– ১৭৬১? সে বছরেই কি পানিপতের তৃতীয় যুদ্ধ হয়েছিল না?
– সেই বছরেই, এই আবদালীর সঙ্গে মুঘল ফৌজের ধুন্ধুমার লড়াই বেঁধেছিলো পানিপতে।
– কিন্তু আবদালী এতটা ভেতরে চলে এলেন আর কেউ রুখলো না?
– স্থানীয় পাঞ্জাবী আর পাখতুন সর্দাররা কিছুটা প্রতিরোধ দেবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু আবদালীর এক লাখ সিপাহীর দুর্ধর্ষ ফৌজের কাছে সেটা কিচুই নয়। সে সময়ে মুঘলদের সেরার সেরা শক্তি হলো পেশোয়ার মারাঠা ফৌজ। তাদের কৌশল, শৃংখলা, তালিম, সবই বাকিদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। কিন্তু মুশকিল একটাই। মারাঠা ফৌজের ঘাঁটি ছিলো পুনে। সেখান থেকে দিল্লি পৌঁছতে কিছুটা সময় লেগে যেত। আর সেই সময়ের মধ্যেই আবদালী পৌঁছে গেল দিল্লি থেকে মাত্র ৯০ কিলোমিটার দূরে পানিপতে।
– মারাঠা ফৌজ?তারা তখন কোথায়?
– আবদালীর পাঞ্জাব আক্রমনের খবর পেয়েই মারাঠা ফৌজ রওনা দেয় পুনে থেকে। পানিপত পৌঁছে আবদালী দেখল মারাঠা ঘোড়সওয়ারদের ক্ষুরের ধুলো উড়ছে দিগন্তে। শোনা যায় মারাঠা ফৌজের এগিয়ে আসা দেখে নাকি আবদালীর কোনো কোনো সেনাপতি ফিরে যেতে চেয়েছিল। বিশেষ করে যারা আগের বার নাদিরের সঙ্গে এসে মারাঠা সেনার বিক্রম দেখে গেছে।
– আবদালী নিশ্চই ফিরে যেতে চান নি।
– সে তো চাইবেই না। তার ভরসা ছিলো নিজের কলাকৌশলের ওপর। তার ওপরে মারাঠা ফৌজের সংখ্যা মেরে কেটে ৫৫ হাজার হয় কি না হয়, আবদালীর ফৌজের অর্ধেক। আর এবারে পেশোয়া বাজিরাও আসেননি, মারাঠা ফৌজের নেতা হয়ে এসেছেন বাজিরাওয়ের ভাইপো সদাশিবরাও ভাউ, যে কিনা নেহাতই এক তিরিশ বছরের ছোকরা। কাজেই আবদালী কোমর কষে লড়াইয়ের মহড়া নিলো।
– শুনেছি প্রচন্ড লড়াই হয়েছিলো, এবং বিস্তারে ও আকারে তৃতীয় পানিপত নাকি প্রথম ও দ্বিতীয় পানিপতের যুদ্ধকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।
– প্রচন্ড যুদ্ধ হয়েছিলো। শৃংখলাবদ্ধ আর নিয়মিত তালিম পাওয়া মারাঠা ফৌজ, আবদালীর ফৌজকে গতি ও রনকৌশলে হতবাক করে দেয়। কিন্তু আবদালীর সেনাবাহিনি অনেক বড়। কাজেই শুরুর দিকের লোকক্ষয় কাটিয়ে উঠে আবদালীর ফৌজ পালটা আক্রমনে যাবার চেষ্টা করল আর মারাঠা সেনাপতি বিশ্বাসরাও ঘেরাও হয়ে পড়লেন শত্রুর হাতে। সামান্য কয়েকজন মারাঠা দেহরক্ষী ছাড়া বিশ্বাসরাওয়ের সঙ্গে আর কেউ ছিলোনা। নিশ্চিত মৃত্যূ, কিন্তু ঠিক সেই সময়, উত্তর দিক থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে শিখ সর্দার জেসসা সিং আলুওয়ালিয়ার নেতৃত্বে প্রায় হাজার ছয়েক শিখ সৈন্য আবদালীর বাহিনিকে আক্রমন করল। এই আক্রমনে আবদালীর ফৌজ হতচকিত ও আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়ে।
– শিখ সেনাদের খবর দিলো কে? তারা এসেছিলোই বা কেন?
– মুঘল রাজনীতি। বুঝলে? উত্তরে শিখ গোষ্ঠি বা মিস্ল্ গুলো তখন সবে তৈরি হচ্ছে। তারা দেখেছিলো পশ্চিম পাঞ্জাবে তাদের বেরাদর পাঞ্জাবীরা কি ভাবে কচুকাটা হয়েছে। তা ছাড়া দিল্লিতে মুঘল শাসক না থাকলে, চরম অরাজকতায় তাদের শিখ মিস্ল্ গুলো, বা খালসা, কোনোটাই বাঁচবেনা। তাই কাছেই পাতিয়ালার জেস্সা সিং এর কাছে মুঘল এলচি (দুত) যখন খবর নিয়ে গেল, যে মারাঠা ফৌজ আবদালীর মোকাবিলা করতে এগিয়েছে, তখন শিখ বাহিনিও রওনা দিলো মারাঠাদের সাহায্যে।
সন্ধ্যের ঘন অন্ধকার নেমেছে। একটু আগে স্থানীয় মসজিদ থেকে উদাত্ত আজান শোনা গেছে। এবারে রাস্তার মোড়ের স্বামীনারায়ন মন্দিরের আরতির ঘন্টার মিঠে মিঠে আওয়াজ ভেসে আসছে। একটু পরেই মহল্লায় প্রসাদ বিতরন শুরু হবে। খান সাহেবের বাবা, খান আবদুল গফফর খান, যাঁকে লোকে আদর করে বলত বাচ্চা খান, ধর্মের বিধিনিষেধ, বেড়াজাল কখনো মানেননি। একেবারে মনের অন্তস্থল থেকে তিনি নাস্তিক, এবং আজীবন বামপন্থী রাজনীতি করে এসেছেন। খাইবার-পাখতুনি এলাকায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিখ্যাত লালকোর্তা সংগঠন তাঁর হাতেই তৈরি। পরবর্তিকালে অবশ্য কয়েক বছর দশকে মুম্বাই, সুরাত, কলকাতা আর কানপুর শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার জন্যে তাঁকে পেশোয়ারের বাইরে কাটাতে হয়। আর এই পন্ডিত মানুষটি তিরিশের দশকের গোড়ায় চলে যান লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততত্ত্ব পড়াতে। বাচ্চা খানের ছেলে মেয়েরাও তাই একদম ছোটো থেকে মুক্ত হাওয়ায় মানুষ হয়ে উঠেছে। ধর্মীয় গোঁড়ামি তাদের মধ্যে কোনোকালেই ছিলোনা। খান সাহেব জানেন তাঁর মেয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কলেজে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেছে। আর সেই সুত্রেই এই ছোকরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। বাবার পথ ধরে খান আবদুল ওয়ালি খান অধ্যাপনার পেশা নিয়েছেন। ইতিহাস তাঁর বিষয়। বর্তমানে প্রত্যক্ষ রাজনীতি না করলেও, বামপন্থার প্রতি তাঁর সমর্থন সকলেই জানে।
– বিশ্বাসরাও ভাউ যুদ্ধে মারা যান। শিখ সর্দার জেসসা সিং আলুওয়ালিয়া যখন বিশ্বাসরাওয়ের দেহ খুঁজে বের করেন, তখন তাঁর মৃতদেহের চারপাশে অন্ততঃ ১৫ জন শত্রু সৈনিকের মৃতদেহ পড়েছিল। বুঝতেই পারছ, বালাজি বাজিরাওয়ের ব্যাটা, ২০ বছর বয়সি বিশ্বাসরাও কেমন লড়ুয়ে ছিলেন।
– আবদালীও তো শুনেছি মারা গিয়েছিলেন।
– না, আবদালীর মারা যাবার খবর রটেছিল, কিন্তু আবদালী মারা যায়নি। সে উত্তর পশ্চিমে পালায় কিছু সহচর নিয়ে। প্রথমে পেশাওয়ার, পরে বদখশান হয়ে আরো উত্তরে জুঙ্গারদের এলাকায় চলে যায়। সে এলাকা এখন সোভিয়েত তাজিকিস্তানের ভেতর। পরে আর তার কোনো খবর পাওয়া যায়নি।
– পানিপতের তৃতীয় যুদ্ধের পর, ভারতের মাটিতে তেমন বড় যুদ্ধ বোধ হয় হয়নি।
– না, এত বড় আকারের দুই বাহিনির যুদ্ধ আর হয়নি। ছোটোখাটো লড়াই হয়েছে। কিন্তু ১৭৬১ সালের পর দেশের ভেতরে আর তেমন বড় লড়াই হয়নি। তবে ভারতীয় সেনা, সীমান্তে আর দেশের বাইরে লড়েছে। নাদির শাহের পরেই আহমদ শাহ আবদালীর ভারত আক্রমন, মুঘল শাসনের মধ্যে আরো অনেক পরিবর্তন আনতে বাধ্য করে।
– কিন্তু মুঘল রাজত্ব তো আরো প্রায় ১০০ বছর টিকে গেল।
– তা গেল। কিন্তু এবার পরিস্কার বোঝা যাচ্ছিলো, দিল্লিতে বসে কামরূপ থেকে কাবুল রক্ষা করা সহজ কাজ নয়। আর এত বড় মারাঠা ফৌজকে নিয়ে এসে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে বসিয়ে রাখা, বা দিল্লিতে বসিয়ে রাখাও খুব কঠিন। খরচ যোগাবে কে? তা ছাড়া মারাঠাদের বাড়বাড়ন্ত দেখে দিল্লির পাঠান, তুর্কি, রোহিলা, রাজপূত, জাট আমির-ওমরাহ বেশ ভয়ই পাচ্ছিলেন। যদি কখনো মারাঠারা মুঘল শাসনকে উৎখাত করতে চায়, তাহলে তাদের বাধা দেবার মত কোন শক্তি সেই সময় ভারতে ছিলোনা।
– বাদসা শাহ আলম তো সে সময় বেশ বয়স্ক হয়ে পড়েছেন। তাঁর প্রভাব কতটা ছিলো?
– শাহ আলমের রাজত্বকাল, মুঘল বাদশাহদের মধ্যে দৈর্ঘ্য হিসেবে তৃতীয়। ঔরঙ্গজেব আর আকবরের পরেই। শাহ আলম দিল্লির বাদশাহ ছিলেন ৪৬ বছরের কিছু বেশী। কিন্তু শেষ দিকে এসে, মজলিসের কর্তৃক্তেই চলতে থাকে মুঘল শাসনব্যবস্থা।আর মজলিসে মাথায় বসে আছেন মারাঠা পেশোয়া। পানিপতের কিছুদিন পরেই মজলিসে আর এক মারাঠা নেতার উত্থান হয়। তিনি হলেন মহাদজি সিন্দে।
– গোয়ালিয়রের সিন্দে?
– হ্যাঁ, গোয়ালিয়রের সিন্দে বংশের রাজা এই মহাদজি। মজলিসে মারাঠাদের প্রভাব দিন দিন বাড়তে থাকায়, আর উত্তর পশ্চিম ভারতে, মুঘল পক্ষের কোনো বড় শক্তি না থাকায়, ভারতবর্ষ খুব অরক্ষিত হয়ে পড়ছিল। বার বার আক্রমন আসছে উত্তর পশ্চিম থেকে। এই সময় বাদশা শাহ আলম, একদম বৃদ্ধ বয়সে শিখ শক্তিকে এক করবার চেষ্টা করলেন।
– শিখরা কেন? পাখতুনরা নয় কেন? তারা তো আরো উত্তর পশ্চিমে ছিলো। আর তাদের লড়াইয়ের খ্যাতিও খুব।
– আমাকে দেখে পাখতুনদের বিচার করোনা ছোকরা। তাও আবার ২০০ বছর আগেকার। সে সময় পাখতুনরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠিতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি মারদাঙ্গা লেগেই আছে। শিক্ষা ও শৃংখলা, দুইই তাদের মধ্যে খুব কম।
– তাহলে?
– তাহলে আর কি? পাখতুন এলাকার পরে, পড়ে রইল পাঞ্জাব। সেখানে জনসংখ্যার প্রায় ৭০% মুসলমান, ১৭% শিখ আর ১৩% হিন্দু। কিন্তু যদি সামাজিক কাঠামোর কথা ধরি, তাহলে ব্যবসা-বানিজ্য মূলতঃ ছিলো হিন্দুদের হাতে, আর মুসলিমদের মধ্যে সেই অর্থে সঙ্ঘবদ্ধতা ছিলোনা, যেটা ছিলো শিখদের মধ্যে। সেই সঙ্ঘবদ্ধতাকে আরো প্রাতিষ্টানিক রূপ দেন শিখ গুরু গোবিন্দ সিং, খালসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। খালসা ছিলো শিখ সামাজিক জীবনধারা যা কিনা শিখ সমাজকে প্রচন্ডভাবে সামরিক নিয়মে বেঁধে ফেলে।
– বুঝলাম। এই সামরিক শিক্ষা আর সঙ্ঘবদ্ধতাকে মুঘল বাদসা কাজে লাগাতে চাইলেন।
– হ্যাঁ, আর শিখ সমাজও মুঘল পৃষ্টপোষকতা পেয়ে সামাজিক ভাবে ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় অনেকটা গুরুত্ব পেল প্রথম বারের মত। তবে প্রথম দিকটা মুঘলদের সমস্ত গোষ্ঠি শিখদের এই স্বীকৃতি ভাল চোখে দেখেনি। এমন কি স্থানীয় কিছু মনসবদার ও সেনানায়ক শিখদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। কেননা আগে ঔরঙ্গজেবের সময় শিখদের সঙ্গে মুঘলদের প্রচন্ড শত্রুতা ছিলো।
– সে শত্রুতা কি এবার মুঘল শাসনে নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্যে?
– হ্যাঁ। মুঘল বাদসার অভিসন্ধি ছিলো, ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে শক্তিশালী যোদ্ধা গোষ্টির বসতি স্থাপন করা। যাতে আক্রমন হলে খুব তাড়াতাড়ি সৈন্য সমাবেশ করা যায়। ঠিক যে ভাবে রাশিয়ার কসাক জনগোষ্ঠিকে সীমান্ত বরাবর বসতি স্থাপন করানো হতো। কসাকরাও শিখদের মতই যোদ্ধা গোষ্ঠি।
– কিন্তু শিখ জনগোষ্টি ও তাদের নেতারা বোধহয় শুধু এই ব্যবস্থায় খুশি থাকেনি
– হ্যাঁ তাদের উচ্চাকাঙ্খা ছিলো অনেক বেশী। তারা শিখ রাজত্বের স্বপ্ন দেখেছিলো, আর সে স্বপ্ন তাদের দেখিয়েছিলেন মহারাজা রনজিত সিং। ১৮০১ সালে রনজিত সিং শিখদের নেতা নির্বাচিত হন, আর নিজের ঘাঁটি স্থাপন করেন লাহোরে। আর এখান থেকেই রনজিত সিং নিজের প্রভাব উত্তরপশ্চিম ও উত্তরপূর্বে বাড়াবার পরিকল্পনা করতে থাকেন।
– রনজিত সিং তার মানে খুব দক্ষ যোদ্ধাও ছিলেন।
– রনজিত সিং নিজে যেমন খুবই দক্ষ সেনানায়ক ছিলেন, তেমনি তাঁর চারিদিকে আরো কয়েকজন দুর্দান্ত শিখ সেনানায়ককেও তিনি পেয়েছিলেন। এই সেনানায়কদের সবাই যে শিখ ছিলেন তা নয়, কেউ শিখ, কেউ হিন্দু আবার কেউ মুসলমান। এমনকি ইয়োরোপীয়ও ছিলেন।
– মানে শিখশক্তির ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিলোনা।
– না , তা ছিলোনা। দেখো, একদিকে যেমন মিশির দিওয়ানচাঁদ, দিওয়ান মোখামচাঁদের মত হিন্দুরা ছিলেন, অন্য দিকে হরি সিং নালওয়া, শ্যাম সিং আট্টারিওয়ালা, বীর সিং ঢিল্লোঁ, গুলাব সিং এর মত শিখ, হাকিম আজিজুদ্দিন বা জাঁ জ্যাকুই আলার্দের মত মুসলমান বা ইয়োরোপীয় খৃষ্টানও ছিলেন। এমন কি আমার শহর পেশাওয়ারের শাসনকর্তা হিসেবে রনজিত সিং নিয়োগ করেন এক ইতালিয়কে। তাঁর নাম পাওলো আভিতাবিল, আমাদের পেশাওয়ারের লোকজনের মুখে মুখে তাঁর নাম দাঁড়িয়েছিলো আবু তাবেলা।
– শিখদের সময়ে ভারত আক্রমন করেনি কেউ বাইরে থেকে?
– করেছিলো তো। আবার কান্দাহারের উপজাতীয় লোকজন জুটিয়ে এনে আকবর খান আর আফজল খান এই দুই সর্দার হামলা চালান পেশাওয়ারের ওপর ১৮৩৭ সালে। তখন হরি সিং নালওয়া পেশাওয়ারের রয়েছেন, সঙ্গে সামান্য কিছু শিখ সিপাহি, সংখ্যায় তারা ৮০০ মত। আর উলটো দিকে খাইবার পেরিয়ে আক্রমনে এলো প্রায় ২৯ হাজার ফৌজের এক বিশাল বাহিনি।
– শিখ সেপাইদের তো ধুলো হয়ে যাবার কথা
– সে তো বটেই। পেশাওয়ারের সাধারন মানুষ তখন ভয়ে কাঁপছে। কেননা শিখ সেনারা হেরে গেলেই শহরে অবাধ লুঠতরাজ হবে। কিন্তু ওই। সেই হরি সিং নালওয়া। নিজের সেনাদের নিয়ে তিনি পেশাওয়ার ছেড়ে আরো কিছুটা পশ্চিমে গেলেন জমরুদ দুর্গে। এই জমরুদ দুর্গ হলো খাইবার গিরিপথে ঢুকবার মুখ। এইখানে তুমুল লড়াই হলো। আকবর খান, আফজল খানের ফৌজ কিছুতেই ৮০০ শিখকে পেরিয়ে পেশাওয়ার যেতে পারলোনা। লড়াইতে প্রায় সমস্ত শিখ সৈনিক মারা পড়ে, হরি সিং নালওয়াও মারা যান। কিন্তু মারা যেতে যেতেও শত্রুকে আটকে রেখে যান, এবং সেই অবসরে লাহোর থেকে ৩০ হাজার শিখ সৈন্যের বাহিনি এসে পৌঁছে যায়। ফলে আকবর খান, আফজল খানের সেনারা পালায়।
– সাংঘাতিক লোক তো, ৮০০ সৈন্য নিয়ে ২৯ হাজারের সঙ্গে লড়া যায়?
– আরে হরি সিং নালওয়ার নামে, এখনো খাইবারের ওপাশে বাচ্চাদের ভয় দেখিয়ে ইউসুফজাই মায়েরা ঘুম পাড়ায় “চুপ্ শা, হরি সিং রাঘলে” (চুপ কর, হরি সিং আসছে)। কাজেই বুঝে দেখ, কেমন বিক্রম ছিলো। পেশাওয়ারের মানুষ আজও হরি সিং এর নাম করে তাদের রক্ষা করার জন্যে।
– আর কেউ এরকম?
– জোরাওয়ার সিং। গিলগিট বালটিস্তান পেরিয়ে, লাদাখ দখল করেন। তার পর এগিয়ে গিয়ে তিব্বতে ঢুকে পড়েন, ও মানস সরোবর পর্যন্ত নিজের দখলে আনেন। কিন্তু শেষে মহাচীনের চিং সেনারা ও তিব্বতীরা জোরদার প্রতিরোধ করে, এবং আচমকা হামলায় জোরাওয়ার সিং মারা যান। তখন তাঁর সেনারা পেছিয়ে আসে, এবং লাদাখ দখল করতে এগিয়ে আসে চীনা সৈন্য, কিন্তু শিখ সেনা ঘুরে দাঁড়িয়ে পালটা মার দেয় আর চীনে সেনাপতিকে মেরে ফেলে। ১৮৪২ সালে দুপক্ষের মধ্যে চুশুলের সন্ধি হয়।
– এই সব ধুন্ধুমারের মধ্যে দিল্লির কি অবস্থা?
– দিল্লিতে তখন বাদশা শাহ আলমের পর তখতে বসেছেন আকবর শাহ। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা বলতে তেমন কিছুই নেই। সমস্তটাই প্রায় মজলিসের হাতে চলে গেছে। কিন্তু কিছু আমির-ওমরাহ বিশেষ করে আওয়ধ, বুন্দেলখন্ড, রোহিলখন্ড, পাটনা, কলকাতা, ঢাকা এই সব এলাকার কিছু ক্ষমতাশালী লোকজন, মারাঠা আর শিখদের প্রভাব একেবারেই ভাল চোখে দেখছিলেন না। এনাদের প্রভাব তখন একেবারেই পড়তির দিকে। ১৮৩০ সালে কলকাতার রামমোহন রায় মুঘল বাদশার এলচি হয়ে ইংল্যান্ডে রাজদরবারে যান। ইংল্যান্ড তখন উঠতি শক্তি, চারিদিকে তাদের দাপট। সেই রাজ পরিবারের সঙ্গে মুঘল বাদশার সম্পর্ক স্থাপিত হলে বাদশার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়বে, এবং আখেরে এই সব আমীর-ওমরাহরা অনেকটা সুবিধে পেতে পারেন।
– রামমোহন রায় তো হিন্দুদের মধ্যে একটা শুদ্ধিকরন আনতে চেয়েছিলেন। বাংলায় সতীদাহ প্রথাও উনি বন্ধ করান বাদশার হুকুমনামা দিয়ে।
– হ্যাঁ, যুগের পক্ষে রামমোহন রায় যথেষ্ট প্রগতিশীল। কিন্তু তিনি যাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে ইংল্যান্ড গেলেন, সেই শাসকের দিন তখন ফুরিয়ে এসেছে। উনি ইংল্যান্ডেই মারা যান। এদিকে বাংলায় তাঁর শুরু করা শুদ্ধিকরন রূপ নেয় সামাজিক আন্দোলনের। পরবর্তীকালের ভারতের ইতিহাসে, বাংলা এবং বাংলার মানুষ যে ভাবে উঠে এলেন এবং প্রভাব বিস্তার করলেন, তার শুরুটা রামমোহনের হাত দিয়ে হয়েছিল এটা বলা যায়।
সন্ধ্যে পেরিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে অন্ধকার ঘন হতে শুরু করেছে। বাড়ির ভেতরে দেওয়াল ঘড়িতে গুরুগম্ভীর আওয়াজে ৭ টা বাজল। আজ কথাবার্তা জমে উঠেছে। অধ্যাপক সামোভার থেকে আর এক পেয়ালা চা ঢাললেন। পর্দার ওপারে টুং টুং করে চুড়ির আওয়াজ, হাতে একটা রেকাবি নিয়ে আবার নীল রঙের ওড়নার দেখা পাওয়া গেল। এবার রেকাবিতে অবশ্য বিশুদ্ধ গুজরাতি বস্তু। নির্ঘাত মহল্লার চৌমাথায় জিগনেশভাইয়ের দোকান থেকে আনা পুর ভরা বেসনে ডুবিয়ে ভাজা বড় বড় লঙ্কা আর সবুজ চাটনি। এ বস্তু খান সাহেবের বড়ই প্রিয়। তিনি এই আহমেদাবাদে এসে যে কটি খাবারের প্রেমে পড়েছেন, তার মধ্যে এই পুর ভরা লঙ্কাভাজা একটা।
– শিখ আর মারাঠাদের প্রভাব খর্ব করতে বাদশাহের চারপাশের কিছু লোকজন অনেক দিন ধরেই চাইছিলেন। এদিকে, বাংলায় শিক্ষাদিক্ষা ও সামাজিক আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠায় দেশের সাধারন মানুষ এই প্রথমবারের মত নিজের অধিকার বুঝে নিতে সচেতন হলো। হয়ত কিছুটা নিজের অজান্তেই। শাসক ও শাসিতের মধ্যে, অভিজাত সমাজ আর খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে প্রথম বারের মত একটা সংঘর্ষের বাতাবরন তৈরি হলো।
– ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ?
– হ্যাঁ। তখন দিল্লির মসনদে বাহাদুর শাহ জাফর। কিন্তু তাঁর বয়স আশী পেরিয়েছে। আর কবি সাহিত্যিক হিসেবে দারুন খ্যাতি থাকলেও, শাসক হিসেবে বাহাদুর শাহর কখনই বিশেষ নাম ডাক ছিলো না। এদিকে দেশে তখন কিছু কিছু জায়গায় সাধারন শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে, মজলিসের দৌলতে প্রাদেশিক আইন ব্যবস্থা বেশ শক্তপোক্ত হয়েছে। কলকাতার মত কিছু শহর থেকে সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। ফলে এতকালের জাঁকিয়ে বসা অভিজাত শ্রেনীর সামন্ততান্ত্রিক শাসনের প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠতে লাগল। আর বাড়তে বাড়তে শেষে সেনাবাহিনিতেও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ল।
– সেনাবাহিনিতে কেন অসন্তোষ ছড়ালো এটা আমার মাথায় ঠিক ঢোকেনি।
– দেখো, সাধারন মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হচ্ছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে তারা জানতে পারছিলো অন্য দেশের সমাজব্যবস্থার কথা। বিশেষ করে আমেরিকার গনতন্ত্রের কথা, ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্র সত্বেও সেখানকার সংসদ পরিচালিত শাসনব্যবস্থার কথা। যার ফলে মানুষ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিল। সেনার সাধারন সিপাহীরা সাধারন ঘর থেকেই যেত। যার ফলে তাদের মধ্যে সেনার উঁচু পদের লোকজনের অভিজাত ব্যবস্থা ও তার গর্ব-অহংকার নিয়ে অসন্তোষ গড়ে উঠতে লাগল। আর কলকাতার উপকন্ঠে এক সেনা ছাউনিতে একটা ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেনা বাহিনিতে বিদ্রোহ দেখা দিল।
– পেছনে নিশ্চই কিছু প্রভাবশালী লোকের মদত ছিলো।
– হ্যাঁ ওই যে বললাম, মূলতঃ গাঙ্গেয় উপত্যকা ও আশপাশ অঞ্চলের ক্ষমতাশালী রাজা আর নবাব দের সমর্থন ছিলো সিপাহীদের প্রতি। এনারা চাইছিলেন বাহাদুর শাহ জাফরের নেতৃত্বে নিজেদের শাসন ব্যবস্থা আবার কায়েম করতে, এবং মজলিশকে খতম করতে। কেননা মজলিশ পরিচালিত আইনি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বহুযুগ ধরে কায়েম হয়ে থাকা এই স্থানীয় রাজা-নবাবদের সামাজিক কাঠামোকে ভেঙে দিয়েছিলো।
– কিন্তু ভারতের দক্ষিন বা পশ্চিম দিকের লোকেরা কেন এই বিদ্রোহে অংশ নিলোনা?
– দক্ষিন ভারতের সামাজিক কাঠামো গাঙ্গেয় উপত্যকার মত নয়। সেখানে সামাজিক অসাম্য কিছুটা কম। সামন্ততন্ত্র এইভাবে জাঁকিয়ে বসেনি। আর তা ছাড়া বার বার বাইরের শত্রুর আক্রমনে ধ্বংস হতে হয়নি বলে, সেখানে সমাজ অনেকটা মুক্ত আর বিকশিত হতে পেরেছে নিজের মত করে। এবার আসি পশ্চিম ভারতের কথায়। পাঞ্জাব, রাজপুতানা, সিন্ধ, বালুচিস্তান, পাখতুন এলাকা, কাবুল, গজনী কান্দাহার। শিখ মহারাজা রনজিত সিং ১৮৩৯ সালে মারা যাবার পর রাজা হন তাঁর একমাত্র পুত্র দলিপ সিং। কিন্তু দলিপ সিং এর বয়স তখন মাত্র ১ বছর। এই অবস্থায় দলিপ সিং এবং তাঁর মা রানী জিন্দন কাউর অবধারিত ভাবে দরবারী রাজনীতির শিকার হলেন। কিছু বছর শিখ প্রভাবিত অঞ্চলে, মানে পাঞ্জাব, কাশ্মীর, পাখতুনি এলাকা ইত্যাদি জায়গায় প্রচন্ড অরাজকতা চলল। নিজেদের মধ্যে লড়াই। যার ফলে দলিপ সিং এর ১৫ বছর বয়সে মজলিস আদেশ দেয় তাঁকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে।
– নির্বাসন?
– হ্যাঁ, দলিপ সিং কে নির্বাসন দেওয়া হয় রানী জিন্দন কাউরের সঙ্গে। যদিও দলিপ সিংকে আশ্রয় দেয় সাগরপারের ইংরেজ, তারা সব সময়েই ভারতে নিজেদের পা রাখার জায়গা খুঁজতো। আর রানী জিন্দন কাউরকে আশ্রয় দেন নেপালের মহারাজা। ওদিকে কাশ্মির নিজে আলাদা হয়ে রইল মুঘল অধীনে। রাজপুতানাও বিদ্রোহে গেলোনা, কেননা শিক্ষার বিস্তার ও সামাজিক ভাবে রাজপুতানা তখনো খুব পেছিয়ে পরা এলাকা। সেখানে স্থানীয় রাজা মহারাজাদের কথাই আইন।আর কাবুল কান্দাহার গজনী তখন বহুবছরের রনক্লান্ত এলাকা। নতুন অশান্তি কেউই চাইছিলোনা। সিন্ধ-ভরুচ-কচ্ছ তখন নতুন করে সেজে উঠছে। সুরাত, আর করাচিতে বানিজ্য ফুলে ফেঁপে উঠছে। মুঘল নৌসেনা হরমুজ প্রনালী থেকে সোকোত্রা ও আদন বন্দর পর্যন্ত টহল দিয়ে বেড়ায়। ভারতীয় বানিজ্যতরনী নিশ্চিন্তে বানিজ্য করে আসতে পারত। কাজেই গাঙ্গেয় উপত্যকা ছাড়া বাকি অঞ্চলে সিপাহীদের এই বিদ্রোহ খুব একটা সাড়া পেলোনা। কিন্তু যেখানে পেলো, সেখানে আগুন জ্বলে গেল।
– শুনেছি কিছু এলাকায় মজলিশ পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা মুছে গিয়েছিল কিছু মাসের জন্য।
– কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, পাটনা, গয়া, মুঙ্গের, এলাহাবাদ, কানপুর, ঝাঁসি, মেরঠ কয়েক দিনের মধ্যেই বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায়। সেখানে মজলিশের প্রতিনিধি সমস্ত আধিকারিকদের নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়, অথবা বন্দী করা হয়। বিদ্রোহীরা বাহাদুর শাহ জাফরের নাম লেখা ঝান্ডা উড়িয়ে দেয় সর্বত্র। সেনা ছাউনিতে, হাবিলদার, সুবাদার, রিসালাদার, সর্দার বা আর উঁচু পদের আধিকারিকদের হত্যা করা হয়।
– এতে করে তো সিপাহীরা নেতৃত্বহীন হয়ে পড়বে।
– সেটাই তো হলো। এবং সেই জায়গায় নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলো পুরোনো নবাব-রাজারা, এবং এই জায়গাতেই আবার গন্ডগোল বাঁধলো। দিল্লি তখন বিদ্রোহী সিপাহীদের অধিকারে, এবং এখানে বসেই এই সব স্থানীয় রাজা ও নবাবরা এক এক জায়গায় বিদ্রোহী সিপাহীদের নেতৃত্ব গ্রহন করলেন। কিন্তু সিপাহীরা এটা ভালভাবে নিলোনা। তারা অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলো, আবার এই সব রাজাদের গোলামী তারা মানলোনা, এবং আস্তে আস্তে তারা দলছুট হতে শুরু করল।
– মজলিশের লোকজন তখন কোথায়?
– মজলিশের সকলে প্রথমে দিল্লি ছেড়ে আম্বালা চলে যান। সেখানে শিখ সেনার একটা বড় ছাউনি ছিলো, এবং শিখ সেনারা মজলিশের অনুগত ছিলো। সেখান থেকে অমৃতসর আর তার পর মজলিশ চলে যায় লাহোর হয়ে রাওয়ালপিন্ডি, আর শেষে কাশ্মিরের মহারাজার আশ্রয়ে শ্রীনগর। সেখানে পৌঁছনো সহজ ছিলোনা সিপাহীদের পক্ষে।
– কিন্তু দক্ষিনে যেতে পারতেন মজলিশের লোকজন।
– হয়ত কাছেই পাঞ্জাবে নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যাবে, তাই দক্ষিনে যান নি। এদিকে সেনাবাহিনির কিছু অংশ, যারা বিদ্রোহে ভাগ নেয়নি, যেমন ডোগরা, রাজপুত, শিখ, পাঠান এবং পাঞ্জাবী মুসলমান সেনা, তাদের নিয়ে মজলিশের নেতারা পাল্টা আক্রমনের পরিকল্পনা করলেন। এবং দিল্লি দখল করা হলো ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৫৭। বাহাদুর শাহ বন্দি হলেন।
– বন্দি করে তো তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।
– সে সময়, বিদ্রোহের ঠিক আগে মজলিশে মনোনিত হয়েছিলেন কলকাতার দ্বারকানাথের ছেলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতবর্ষের অন্যতম প্রথম শিল্পপতি হিসেবে দ্বারকানাথ অনেক আগেই মজলিশে মনোনিত হয়েছিলেন। বাংলার প্রাদেশিক মজলিস তিনিই পরিচালনা করতেন। রামমোহন যদিও সুবা বাংলার মজলিশে মনোনিত হননি, কিন্তু তা হলেও বাংলার মজলিশে তাঁর ধর্ম আন্দোলনের যথেষ্ট প্রভাব ছিলো। যখন বিদ্রোহ শুরু হয়, দেবেন্দ্রনাথ তখন সিমলা সফর করছেন। সিমলাকে তার কিছুদিন আগেই দিল্লির কাছে পাহাড়ি ছোট্ট শহর হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছিল। জাহাঙ্গিরের আমলে গ্রীষ্মকালে বাদশা যেতেন কাশ্মীর। সে দিল্লি থেকে বড় দুরের দেশ। সিমলা বরং অনেক কাছের।
– তার মানে দেবেন্দ্রনাথ বিদ্রোহের সময় কলকাতা ছিলেন না। থাকলে হয়ত বিদ্রোহী সিপাহীদের হাতে তাঁর বিপদ হতে পারত।
– ঠিক সেরকম নয়। দেবেন্দ্রনাথ খুব অল্পসংখ্যক কয়েকজন মজলিশের সদস্যের মধ্যে একজন, যাঁকে সিপাহীরা শ্রদ্ধা করত। আর সেই জন্যেই লড়াইয়ের পর, তিনি দু পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করান। বাহাদুর শাহ কে কলকাতায় গঙ্গার ধারে আলম কেল্লায় এনে রাখা হয় কিছুদিন। তার পরে বাদশার জন্যে বিশাল জাফরমহল তৈরি হয়। আজকাল যাকে কলকাতার লোক বাংলায় রাজভবন বলেন। মুঘল বাদশাহির বাকি ইতিহাস ঐ কলকাতায়। শহরের পূবদিকে নতুন মহল্লা বসানো হয় রাজাবাজার নামে। সেখানে বাদসার পার্শচর সব আমীর ওমরাহদের থাকার জায়গা দেওয়া হয়।
– ১৮৫৭ সালেই তো মুঘল শাসনের শেষ বলে ধরা হয়।
– হ্যাঁ। শেষ। এর পরে ভারতের শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে বসেন গোটা দেশের নেতারা। নেতৃত্ব দেন সৈয়দ আহমেদ খান। মুঘল বাদশা যদিও থেকে গেলেন, কিন্তু তাঁর হাত থেকে সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা মজলিশ নিজের হাতে নিলো। এবং জনাব সৈয়দ আহমেদ খান একটা ১৫ সদস্যের দল তৈরি করলেন শাসন ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য। এবং এই ১৫ জন সদস্যই ৫৪ দফা শাসন সংস্কার নিয়ে আসেন। এর ফলে দেশে প্রাদেশিক আইন সভা প্রবর্তন হলো। তবে কিছু এলাকা রাজা বা নবাবদের শাসনাধীনে থেকে গেল, তার মধ্যে কাশ্মীর, হায়দরাবাদ, পাতিয়ালা, ভাওয়ালপুর, কালাত, গোয়ালিয়র, জামনগর ইত্যাদি ছিল। এরা সরাসরি কেন্দ্রীয় মজলিশের অধীনে রইল। বাকি অঞ্চলগুলো সুবা বা প্রদেশে ভাগ হয়ে প্রাদেশিক আইন সভার অধীনে এলো। সেনাবাহিনিও দিল্লির মজলিশের অধীনস্থ রইল।
– তার মানে বাদশার বাদশাহি গেল, কিন্তু স্থানীয় রাজা-নবাবরা এবারেও টিঁকে গেল।
– একদম ঠিক ধরেছ। তবু বলা যায়, কিছুটা হলেও ভারতের সমাজে কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলো। ইতিমধ্যে বাইরের ইয়ো্রোপীয় শক্তি ঘন ঘন এশিয়ায় হানা দিচ্ছে। চীনে তো জোরদার লড়াই করে তারা নিজেদের অধীকার জমিয়ে রেখেছে। ভারতের বুকেও তারা গেড়ে বসবার ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে গেছে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে যতই লড়ুক ভারতীয়রা, বাইরের শত্রুর আক্রমন এলেই তারা সব ভুলে বার বার এককাট্টা হয়েছে। আর মুঘল নৌবহর,যা ১৮৫৭র পরে ভারতীয় নৌবহর, এদেশের ধারে কাছে ইয়োরোপীয় শক্তিকে ঘেঁসতে দেয়নি। আর উনবিংশ শতকের শুরু থেকে ভারতীয় পুঁজিপতিদের বিকাশ শুরু হয়। নিজেদের মুনাফার জন্যে হলেও, এরা বৈজ্ঞানিক গবেষনা ও কারিগরিতে বিনিয়োগ করে এসেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে, আর বিদেশী অত্যাধুনিক কারিগরি ও প্রযুক্তি আমদানি করে গেছে। তাই ভারতীয় সেনা কখনো প্রযুক্তিগত দিক থেকে পেছিয়ে থাকেনি।
ভেতর থেকে পাশতো ভাষায় কিছু বলা হলো। খান সাহেব মৃদু হাসলেন। তার পর মাথা নাড়লেন। খান সাহেবের ছোটো কন্যাটি অনুরোধ করছে, খান সাহেবের ছাত্র যেন রাত্রে খেয়ে যায়। তার জন্যে নিরামিষ রান্না করা হয়েছে। খান সাহেব তাকালেন ছাত্রের উৎসুক মুখের দিকে। উজ্জ্বল দু খানি চোখ। চোখে মোটা কালো চশমা, মুখে হালকা দাড়ি গোঁফ। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। একটা ছেয়ে রঙের কুর্তা, সাদা পাজামা, কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ। দিল্লির ছাত্র মহলে এই ধরনের হুলিয়াকে বলে ঝুলাওয়ালা। ওখানে ছাত্র সমাজ রাজনৈতিক শিবির হিসেবে এক এক ধরনের নাম ধারন করেছে। টোপিওয়ালা, ঝুলাওয়ালা, চাড্ডিওয়ালা আর দাড়িওয়ালা। ঝুলাওয়ালা হলো মার্কামারা বামপন্থী ছাত্রদের পরিচয়। জওয়াহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় এই বাম ছাত্রদের অবাধ বিচরনক্ষেত্র।
– আচ্ছা খান সাহেব, কার্ল মার্ক্স ১৮৫৭র বিদ্রোহ নিয়ে নিয়মিত একটা কলম লিখতেন না ইংল্যান্ডের কোনো একটা কাগজে?
– অবশ্যই। বিদ্রোহের মাত্র কয়েক বছর আগে মুম্বাই থেকে পুনে আর কলকাতা থেকে রানীগঞ্জ রেল লাইন পাতা হয়। প্রধানতঃ কলকাতা ও মুম্বাইয়ের শিল্পপতিদের পুঁজিতে আর মালপত্র পরিবহনের জন্যেই এটা করা হয়। কিন্তু পরে দেখা যায় সেনা পরিবহন এবং সাধারন মানুষের যাতায়াতের জন্যেও রেল গাড়ি খুব ভাল উপায়। কার্ল মার্ক্স লেখেন – এই যে “পুঁজিপতিরা নিজেদের মুনাফার জন্যে আজকে ভারতে রেল লাইন পাতছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করছে, ছাপা খানা আর সংবাদ পত্রের প্রচার করছে এতে করে ভারতের বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা জনগোষ্ঠী গুলো খুব তাড়াতাড়ি সংঘবদ্ধ হবে, এবং নিজেদের বঞ্চনা ও সামাজিক অধিকার বুঝতে পারবে”। দেখ, ঠিক সেটাই হলো।
– এই লেখাগুলো কোথাও পাওয়া যাবে?
– বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে তো নিশ্চিতভাবেই পাওয়া যাবে। তবে কিনা, তুমি আর যে সব সংগঠনের সঙ্গে কাজ করো, তাদের কাছেও পেতে পারো। তাদের প্রকাশনা খুব ভাল।
– না, মানে আজ্ঞে, আমি তো আর……
– ঠিক আছে, যেতে দাও সে কথা। এই যে মজলিশ থেকে প্রাদেশিক আর কেন্দ্রীয় আইনসভা তৈরি হলো, দেখা গেল নেতৃত্বে জনাব সৈয়দ আহমেদ খানের মত প্রগতিশীল মানুষ থাকলেও সেই অমুক রাজা, তমুক রানা, তুসুক খান বাহাদুর বা নবাব সাহেব এনারাই প্রায় সব পদ দখল করে বসে আছেন। খুব বেশী হলে দ্বারকানাথের মত হাতে গোনা বড় জমিদার এবং উদ্যোগপতি। কিন্তু সাধারন মানুষের প্রতিনিধিত্ব একেবারেই নেই। এই সময়টা বলতে পারো ভারত একটা বড় জমিদারি হিসেবে চলত। যদিও শিক্ষার বিস্তার হচ্ছিলো, শিল্পের বিস্তার ঘটছিলো। কিন্তু গ্রামে, প্রান্তিক চাষি ও ক্ষেতমজুরদের দুরবস্থার শেষ ছিলো না। ওদিকে শহরে শ্রমজিবী সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটছিলো। বড় শিল্পকেন্দ্র শহরগুলোর চারপাশে ঘন জনবসতির মজদুর মহল্লা গড়ে উঠলো। আর গড়ে উঠলো এক কেরানি সম্প্রপদায়।
– এই সময় থেকেই তো রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে বোধহয়।
– হ্যাঁ, উনবিংশ শতকের শেষ থেকেই রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু প্রথমদিকটা সেই সংগঠনগুলোর গতিপ্রকৃতি বোঝা যায়নি। মূলতঃ কলকাতা, চেন্নাই, মুম্বাই, করাচি, লাহোরের কিছু আইনজিবী আর সরকারী কর্মচারি ও আমলা এই সংগঠন গুলো গড়ে তুলতে থাকেন বিচ্ছিন্ন ভাবে। ১৮৮৫ সালে মুম্বাই শহরে এনাদের একটা সম্মেলন হয়। এই সব আইনিজিবী আর আমলারা শহুরে নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়, আর দেশের বাইরের কিছুটা খবরাখবর এনারা রাখতেন। সে সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ বেঁধেছে। গোটা দুনিয়ায় সেই নিয়ে হইচই। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও সেই প্রভাব থেকে বাদ যায়নি। আমেরিকানদের অনুসরন করে এনারা নিজেদের সংগঠনের নাম দেন কংগ্রেস।
– সেই কি আজকের জাতীয় কংগ্রেস?
– হ্যাঁ, সেই সংগঠনই আজকের জাতীয় কংগ্রেস। এনাদের দাবী ছিলো, আইন সভাগুলোয়, ওই রাজা নবাব আর জমিদার ছাড়াও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকতে হবে। প্রথমটা সেরকম ভাবে বোঝা যায়নি, কিন্তু দেখা গেল, এই কংগ্রেস যদিও সাধারন মানুষের প্রতিনিধিত্বের কথা বলে, তবুও তারা শহুরে শিক্ষিত কেরানী ও উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের থেকে আসা লোকজন। আর অন্য দিকে, যেটা কেউ লক্ষ্য করলোনা, সেটা হলো, কংগ্রেসের উত্থানের পেছনে হাত ছিল নব্য পুঁজিপতি সম্প্রদায়ের। এই পুঁজিপতি শিল্পপতিরা তাদের শিল্প সাম্রাজ্য তৈরি করছিলো বটে, কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাদের কোনো কথা বলার জায়গা ছিলোনা। সরকার প্রবর্তিত নীতিতে তাদের কোনো মতামত নেওয়া হতো না। এদিকে সে সময় ভারতের বেসরকারি অর্থনৈতিক লেনদেন ব্যবস্থা যাকে ইংরিজিতে বলে ব্যাংক, সে গুলো এই পুঁজিপতিদের হাতে।
– তাই তারা রাজনৈতিক সংগঠনের পেছনে সমর্থন ও সাহায্য জোটাতে লাগল, যাতে করে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগ তারা পায়, আর সরকার তাদের স্বার্থে নীতি নির্ধারন করতে পারে।
– একদম ঠিক বলেছ। আর সেটার হয়ত কিছুটা দরকারও ছিল। কারন মুঘল বাদশার হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাবার পরে, ভারতের শাসনব্যবস্থা অনেকটাই স্থবীর হয়ে পড়েছিল। যদিও ৫৪ দফা সংস্কার করা হলো, কিন্তু দেখা গেল, আদতে ক্ষমতা সেই অভিজাতদের কুক্ষিগতই হয়ে আছে। বরং সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আনা হয় সেনাবাহিনিতে। আগেকার মনসবদারী প্রথা তুলে দেওয়া হয়। এবং সেনাবাহিনিকে পশ্চিমি কায়দায় ঢেলে সাজানো হয় রেজিমেন্টের ভিত্তিতে। সেনায় এমন অনেক জাতীর রেজিমেন্ট তৈরি হয়, যাদের এর আগে মুঘল ফৌজে কখনো নেওয়া হয়নি। যেমন উত্তর-পূর্বের উপজাতিরা, বাঙালিরা, দক্ষিনি তামিল-তেলেগু-কন্নড়-মোপলারা। এ ছাড়া পেশাদার সেনা আধিকারিক তৈরি করা হয়, ইংরেজিতে যাকে বলে অফিসার কোর। প্রথম দিকে এদের অবশ্য বিদেশি সেনাদের থেকে কিছু শিক্ষক এনে তালিম দিতে হয়। সব চেয়ে বেশি বিদেশি শিক্ষক আসেন ইংল্যান্ড ও জার্মানী থেকে।
– আর নৌ সেনা?
– সেখানেও একই ভাবে ইংরেজ, ফরাসী ও আমেরিকানদের এনে তালিম দেওয়া হয়, আর নৌবহর কে বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করে দেওয়া হয়, যাতে পরিচালনের সুবিধে হয়।
– উনবিংশ শতকের শেষের দিকে, মজলিসের প্রধান তখনও জনাব সৈয়ব আহমেদ খান, কিন্তু সেই সময় সৈয়দ আহমেদ খানের অন্যতম বিশ্বস্ত সহযোগী, দাদাভাই নওরোজি কেন্দ্রীয় আইন সভা থেকে পদত্যাগ করেন বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্যের জন্য। দাদাভাই নওরোজি চাইতেন দেশীয় পুঁজিপতিদের আইনসভায় নিয়ে এসে তাদের সঙ্গে সরকারকে কাজ করাতে। অন্যদিনে জনাব সৈয়দ আহমেদ খান পুঁজিপতিদের সন্দেহের চোখে দেখতেন। এইখানে দুটো ঘটনা ঘটল। একদিকে দাদাভাই নওরোজি কেন্দ্রীয় আইনসভা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে বিভিন্ন শহরে গড়ে ওঠা সংগঠন গুলোকে নিয়ে কংগ্রেস নামের মঞ্চ গড়লেন। আর অন্য দিকে, কিছু পুঁজিপতি প্রকাশ্যে তাদের সংবাদপত্রে প্রচার শুরু করল, জনাব সৈয়দ আহমেদ খান, হিন্দুদের পছন্দ করেন না, তাই শিল্পপতিদের তিনি আইনসভায় ঢুকতে দিচ্ছেন না। ঘটনাচক্রে, সে সময় ভারতের ব্যবসাবানিজ্য ও পুঁজির সবটাই প্রায় ছিলো হিন্দু শেঠদের হাতে।
– মানে সাম্প্রদায়ীক প্রচার মাথাচাড়া দিতে শুরু করল।
– হ্যাঁ আর এই সুত্রেই পরবর্তিকালে হিন্দু জাতীয়তাবাদ আর তার পালটা মুসলিম জাতীয়তাবাদ জেগে উঠবার জায়গা তৈরি হলো।
– কিন্তু এই হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়ীকতা কোনো দিন ভারতের মাটিতে কল্কে পেলোনা।
– পাবে কি করে? গত ৭০০ বছর এরা পাশাপাশি রয়েছে। ঝগড়া মারামারি কাটাকাটি হয়নি তা নয়। অনেক হয়েছে। গোটা উত্তর ভারতে এমন কোনো হিন্দু মন্দির পাবেনা যেটা ২০০-৩০০ বছরের পুরোনো। সব ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু এর পরে এরা বুঝেছে, মারামারি করে যেটা হয়, সেটা হলো দুপক্ষেরই ক্ষতি। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন জনাব সৈয়দ আহমেদ নিজেই। তিনি ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজান। আর এই শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। কাজেই সাম্প্রদায়ীক প্রচার এ দেশে জায়গা পেলোনা। পুঁজিপতির চক্রান্ত কাজ করলনা।
– কিন্তু কংগ্রেসের আন্দোলন?
– কংগ্রেসকে প্রথমে অভিজাত মহলে কেউ পাত্তা দিতে চায়নি। কলকাতা, মুম্বাই, করাচি, চেন্নাইএর মত কিছু বানিজ্যিক নতুন গড়ে ওঠা শহরে তাদের রমরমা ছিলো। কিন্তু পুরোনো শহর বলতে এক লাহোর আর পেশাওয়ার ছাড়া কোথাও তাদের তেমন মজবুত সমর্থন ছিলোনা। তাদের নেতারা অবশ্য যথেষ্ট নাম করেছেন বিংশ শতকের গোড়ায়। এবং এনাদের মধ্যে দু এক জন কেন্দ্রীয় আইনসভার শীর্ষেও উঠেছিলেন। যেমন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। মাত্র বিয়াল্লিস বছর বয়সেই দেশের শীর্ষে পৌঁছনো বড় কম কথা নয়। এই বিচক্ষন মানুষটি কেন্দ্রীয় আইনসভার শীর্ষে পৌঁছেও কিন্তু কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। তবে কিনা সে আমলেও রাজানুগ্রহ ছাড়া আইনসভায় মনোনিত হওয়া কিন্তু সম্ভব ছিলোনা। গোখলের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে কাবুলের আমীর হবিবুউউলাহ খান বাহাদুর তাঁকে আইন সভায় নিয়ে আসেন।
– হঠাৎ আমীর হবিবুল্লাহ গোখলেকে কেন নিয়ে এলেন?
– দিল্লির বাবুয়ানি আর বাদশাহী আদবকায়দার জগতে কাবুল কান্দাহার কে কিছুটা নিচু নজরে দেখা হতো। সেখানে ছড়ি ঘোরাতেন রাজপুত, মারাঠা রাজারা আর আওয়াধি নবাবরা। আমীর হবিবউল্লাহ আইন সভায় এমন একজন বিচক্ষন কাউকে আনতে চেয়েছিলেন, যিনি কিনা আমিরকে তাঁর প্রাপ্য সমীহ আদায় করে দেবেন। গোখলের লেখা পড়ে আমীর মুগ্ধ হন, এবং যেচে গোখলের সঙ্গে আলাপ করেন।
– গোখলে তো মাত্র কয়েক বছর শীর্ষে ছিলেন।
– হ্যাঁ গোখলের অকালমৃত্যূতে ভারতের প্রচন্ড ক্ষতি হয়। যদিও লোকমান্য টিলক এবং পরে চিত্তরঞ্জন দাসকে হবিবউল্লাহ নিয়ে আসেন আইনসভায়্ কারন তখন ইয়োরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। কিন্তু সেই অর্থে সর্বজনগ্রাহ্য নেতৃত্ব দেওয়ার মত কেউ ছিলোনা। আইনসভার প্রধান হিসেবে মনোনিত হন সুলতান মহম্মদ শাহ, যাঁকে সবাই আগা খান হিসেবে জানে। এনার সবচেয়ে বড় যোগ্যতা ছিলো, সেই আমলে ইনি পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। আগা খান ছিলেন ইসমাইলি সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। কাজেই বুঝতে পারছ, ভারতের শাসন ব্যবস্থার হাল কি হয়েছিল। তা ছাড়া সে সময় বিশ্ব রাজনীতিতে ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাব ক্রমশঃ বাড়ছে। ভারতের শাসকরা ধিরে ধিরে এই বিদেশী শক্তিগুলোর তাঁবেদারীও শুরু করেন। আমাদের বিদেশনিতি অনেকাংশেই স্থির করে দেওয়া হতো লন্ডন বা ওয়াশিংটন থেকে।
– তবুও, প্রথম মহাযুদ্ধে ভারত তো নিরপেক্ষই থাকতে ছিলো?
– হ্যাঁ। প্রথম মহাযুদ্ধে ভারত প্রথমে কোনো পক্ষে সরাসরি যোগ দিয়ে লড়াই করেনি বটে, কিন্তু খাদ্য, ওষুধ আরো বহু ধরনের রসদ সরবরাহ করেছিলো মিত্রপক্ষের দেশগুলোকে। ভারতীয় ফৌজি চিকিৎসকরা অনেকগুলো হাসপাতাল তৈরি করে ফ্রান্সে। কিন্তু যখন ওসমানি তুর্কি বাহিনি মেসোপটেমিয়া (ইরাক) আক্রমন করে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে থাকলো পূব দিকে, তখন মিত্রপক্ষের থেকে অনুরোধ এলো ভারতের কাছে, যে ভারত যেন মেসোপটেমিয়ায় ওসমানি তুর্কিদের প্রতিরোধ করে।
– ভারতীয় সেনার অবস্থা তখন কেমন?
– সেনার তালিম ভালোই ছিলো, কিন্তু দীর্ঘকাল ভারতীয় ফৌজ তেমন বড় লড়াই লড়েনি। ফলে অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। আর আমাদের প্রতিরক্ষা সচিবের তাড়াহুড়ো করে সেনা পাঠাতে যাওয়ার ফলে ইরাকে ফৌজের রসদের বড় কোনো ঘাঁটি তৈরি করা সম্ভব হয়নি। করাচি বন্দর থেকে তড়িঘড়ি পুনে রিসালাদার রেজিমেন্টকে জাহাজে চাপিয়ে বসরা পৌঁছে দেওয়া হলো। তারা যখন কুট-এল-আমারা পৌঁছয়, তখন সেখানে ওসমানি ফৌজের মোকাবিলা করে। প্রথম দিকে খুব সফল লড়াইয়ের পর ওসমানি বাহিনি পিছু হটে যায়্ আর কুট-এল-আমারা ভারতীয় ফৌজের দখলে আসে।
– কিন্তু ওসমানি ফৌজ তো বোধহয় এক জার্মান সেনানায়কের নেতৃত্বে আবার ফিরে আসে।
– হ্যাঁ, এই জার্মান জেনারেলের নাম কাউন্ট ভন ডার গোল্টজ্।
– ইতিহাসে পড়েছি, বেশ লম্বা সময়ের জন্যে তুর্কি ফৌজ অবরোধ করে কুট-এল-আমারা।
– হ্যাঁ, ১৯১৫ সালের ডিসেম্বর থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে প্রায় তিরিশ হাজার ভারতীয় সৈন্য। আর এখানেই ভারতীয় পরিকল্পনার গলদ প্রকট হয়ে পড়ে। সেনার দীর্ঘকাল বসে থাকার জন্যে যে পরিমান রসদ ও গোলাবারুদ জমা করার দরকার ছিলো, তার প্রায় কিছুই করা হয়নি। আর কুট এক আমারা এমন এক জায়গায়, যেখানে ভারত থেকে রসদ পৌঁছনো সম্ভব নয়। ফলে ভারতীয় বাহিনি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। খাবার নেই, গোলাবারুদ নেই। এরকম অবস্থাতেও প্রায় পাঁচ মাস লড়াই চালিয়ে যায় ভারতীয় ফৌজিরা। কিন্তু শেষরক্ষা হয়না। ১৩ হাজার ভারতীয় সৈনিক মারা যায়, বেশীরভাগই অনাহারে।
– সেনাবাহিনিতে প্রতিক্রিয়া হয়নি?
– হলেও সে সম্পর্কে তেমন কিছু খবর বাইরে আসেনি। কিন্তু দেশের বড় শহরগুলোতে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।
– আচ্ছা, যুদ্ধের ঠিক আগে গান্ধীজি ভারতে ফিরে আসেন না?
– হ্যাঁ, তার আগে উনি ব্রিটিশ শাসিত দক্ষিন আফ্রিকায় ছিলেন অনেক বছর। কিন্তু যুদ্ধের ঠিক আগে দেশে ফেরেন, এবং যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ পক্ষকে সাহায্য করার জন্য ভারতের অনেক জায়গায় প্রচার করেন। তাতে অবশ্য দোষের কিছুই ছিলোনা, কেননা ভারত সরকার মিত্রপক্ষকে সাহায্য করছিলো। কিন্তু তার আগেই দক্ষিন আফ্রিকায় বর্নবৈষম্যের বিরুদ্ধে গান্ধীজির প্রতিবাদ ও আন্দোলনের গল্প এদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই তিনি যখন এসে মুম্বাইতে নামলেন ১৯১৪ সালে, তখন তাঁকে বিশাল অভ্যর্থনা দেওয়া হয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে।
– গান্ধীজি কংগ্রেসে যোগ দিলেন?
– সে সময় সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সংগঠন বলতে কংগ্রেস। হিন্দু মহাসভা বা মুসলিম লীগ কে কেউ পাত্তাই দেয়নি। কাজেই কিছু করতে হলে, কংগ্রেসই সবচেয়ে বড় মঞ্চ। দেশে ফিরে গান্ধীজি লক্ষ্য করলেন, এখানেও সামাজিক বৈষম্য মাত্রাছাড়া। শুধু যে অভিজাত শাসক শ্রেনীর সঙ্গে বাকিদের বৈষম্য তাই নয়, সামাজিক ভাবে জাত পাত গোষ্ঠী এসব মিলিয়ে সমাজ শতধা বিভক্ত। আর কংগ্রেসের মধ্যে কিছু প্রগতিশীল লোকজন থাকলেও, সাধারন মানুষের হাতে দেশের ক্ষমতার আন্দোলন গতি পাচ্ছিলোনা কারন তাতে শহুরে শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত মানুষ ছাড়া আর কেউ সামিল হয়নি।
– সেই জন্যেই কি গান্ধীজি দেশ ভ্রমনে বেরোলেন?
– হ্যাঁ, উনি ঘুরে ঘুরে দেশ চিনলেন, গ্রাম চিনলেন, মানুষজন চিনলেন। এবং স্থানীয় সামাজিক অন্যায় গুলোর বিরুদ্ধে সমাজের একদম নিচের তলার মানুষদের নিয়ে আন্দোলনে নামলেন। চম্পারনে ভূমিহার জমিদারদের বিরুদ্ধে গরীব কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন, গান্ধীজির পায়ের তলায় শক্ত সমর্থনের ভিত গড়ে দেয়। চম্পারন, খেড়া, এই সব আন্দোলনের ফলে খেটে খাওয়া মানুষ গান্ধীজিকে নিজেদের নেতা বলে চিনলো। আর এই সমর্থনের ভিত তৈরি হতেই গান্ধীজি সেটাকে কংগ্রেসের পতাকার তলায় নিয়ে এলেন।
– দেশের লোকে তো ইতিমধ্যে অপদার্থ শাসনব্যবস্থার ওপরে ভরসা হারিয়ে ফেলেছিলো। কারন শুনেছি শুধু অপদার্থতা নয়, দুর্নিতিও মাত্রা ছাড়িয়েছিলো। আর বিদেশী শক্তির তাঁবেদারী।
– চরম দুর্নিতি। আর অভিজাত শাসক গোষ্ঠী, নবাব রাজারা নিজেদের পকেট ভরে চলেছিলো। তাদের সম্পত্তি আয় ব্যায়ের কোনো হিসেব ছিলোনা। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেল মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিলো যুদ্ধের চাপে। দেশে লক্ষ লক্ষ বেকার। কাজ নেই। কৃষি উৎপাদন তলানিতে। প্রচন্ড বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছিলো । ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে এরকমই এক প্রতিবাদ সভায় স্থানীয় কোতোয়ালির দারোগার আদেশে গুলি চলল। হাজারের ওপর মানুষ মারা গেল। এবার দেশে আগুন জ্বলে গেল। নোবেল বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরকারি সিতারা-এ-হিন্দ খেতাব ফিরিয়ে দিলেন। কংগ্রেস নেতারা গোটা দেশে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। সরকারের সঙ্গে অসহযোগীতা। পুরোভাগে রইলেন গান্ধীজি।
– কিন্তু এ আন্দোলনের মূল ছিলো আন্দোলন হবে অহিংস, তাই না?
– হ্যাঁ, গান্ধীজির আন্দোলন বা রাজনীতির মুল কথাটাই অহিংসা। আমার বাবাও এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এবং অহিংসার ভিত্তিতেই। গোটা দেশে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। সরকার কে অকেজো করে দেওয়া হয়। ভারত এই ধরনের গন আন্দোলন দেখেনি এর আগে। এই প্রথম বার সাধারন মানুষ লাখে লাখে সামিল হলো। দাবী ছিলো কেন্দ্রীয় আইনসভায় সাধারন মানুষের প্রতিনিধিদের নিতে হবে।
– কিন্তু আন্দোলন তো থামিয়ে দেওয়া হয় চৌরিচৌরায় কোতোয়ালি আক্রান্ত হবার পর।
– আর এই থামিয়ে দেওয়াতে গোটা দেশে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। কিছু এলাকায় হিংসাত্মক প্রতিঘাত করার জন্যে সংগঠন গড়ে ওঠে। বিশেষ করে বাংলায়।
– ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদের হিন্দুস্তান সমাজবাদী প্রজাতান্ত্রিক সঙ্ঘের এই সময়েই কি উত্থান হয়?
– হ্যাঁ এই সময়েই। গান্ধীজির আন্দোলন থামিয়ে দেওয়াতে গোটা দেশের জনমানসে যে প্রচন্ড হতাশা তৈরি হয়েছিলো তার ফল হিসেবে বাংলায় অনুশীলন সমিতি, উত্তর ভারত আর পাঞ্জাবে চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগত সিং এর সংগঠন এবং আরো পশ্চিম দিকে খাইবারের আসেপাশে পেশাওয়ারে আমার বাবা, খান আবদুল গফফর খানের লাল কোর্তা সংগঠন। লাল কোর্তা প্রথমে অহিংস অবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনে নেমেছিলো। কিন্তু আন্দোলন থামিয়ে দেওয়ার পর তারা থেমে যেতে রাজি হয়নি। অন্য দিকে ১৯১৭ সালের পর রুশি ইনিকিলাবি ধারনা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছিলো। আমার বাবাও তাতে প্রভাবিত হয়েছিলেন প্রচন্ড ভাবে। যার ফলে, ভারতবর্ষে কংগ্রেস ছাড়াও আরো কিছু গনসংগঠন তৈরি হয়ে গেল, যারা কোনো ভাবেই আপসকামী নয়, এবং সাধারন মানুষের নির্বাচিত সরকারের হাতে পুরো ক্ষমতার দাবীতে অটল। এই সব সংগঠনই কিন্তু বাম চিন্তাধারায় দীক্ষিত হয়েছিলো, এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্রগঠনের ডাক দিলো। প্রচন্ড সরকারি দমন পীড়ন চলেছিলো। ভগৎ সিং সহ অনেকের মৃত্যুদন্ড হয়। আজাদ মারা যান সরকারি ফৌজের সঙ্গে সংঘর্ষে।
– ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও কি এই সময়েই তৈরি হয়?
– হ্যাঁ এই আগুন জ্বলা সময়ের মধ্যেই ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। বামপন্থী সংগঠনগুলোকে এক করার কাজ শুরু হয়। যদিও শুরুর দিকে কমিউনিষ্ট নেতারা সকলেই প্রবাসে ছিলেন, কেননা তাঁদের নামে দেশে হুলিয়া ছিলো। দেশে পা দিলেই গ্রেফতার হতেন। আস্তে আস্তে বাংলা, উত্তর ভারত এবং খাইবার অঞ্চলের সমাজতান্ত্রিক সংগঠনগুলো এক হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলো।মতপার্থক্য ছিলো বিস্তর। কিন্তু তবুও পার্টির মধ্যে শৃংখলা এনে ফেলা গিয়েছিলো।
– কংগ্রেসের মধ্যেও অনেকে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ পোষন করতেন শুনেছি। জওহরলাল নেহেরু, সুভাষবাবু রা।
– ওপরে ওপরে সবাই মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলত। কেননা, দেশের লোকে সেটাই চাইছিলো। কিন্তু কংগ্রেস সেই শুরুর দিন থেকেই ভারতীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থে কাজ করে এসেছে। গান্ধীজি নিজের কৃতিত্বে দেশের সাধারন মানুষকে কংগ্রেসের আন্দোলনের মঞ্চে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেসের আন্দোলন সেই মুহুর্তে ছিলো দিশাহীন। কংগ্রেসের ভেতরে, যাঁরা তুলনামুলক ভাবে কম বয়সি এবং রক্ত গরম, যেমন নেহেরু, সুভাষবাবু, জিন্নাহ, এনারা অনেকটাই সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিলেন। সেই জন্যেই পরে তিরিশের দশকে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল তৈরি হয়। কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্য সে দলকে সামাজিক-ফ্যাসিবাদী তকমা দেয়। তাদের মতে সমাজতান্ত্রিক গনতন্ত্র (সোশ্যাল ডেমোক্রাসি), একটা সোনার পাথরবাটি।
– কেন? তা কেন? তাতেও তো সমাজতন্ত্রের পথে এগোনো সম্ভব।
– শোনো হে ছোকরা, একটু পড়াশোনা করো। যে পথে চলবার কথা ভেবেছ, যে আদর্শকে মাথায় নিয়েছ, তা তোমার কাছে অনেক পরিশ্রম, অনেক ভাবনা চিন্তা দাবী করে। বলি, একদিকে আমি সমাজতন্ত্র ফলাবো, অন্য দিকে আমি বৃহৎ পুঁজিপতিদের নিয়ে বিকাশ চাইবো, এ কখনো হয়? কংগ্রেসের সমাজবাদী পরিকল্পনা এই রকমের। তার সঙ্গে আছে উৎকট জাতীয়তাবাদী মশলা।
– কিন্তু কংগ্রেস তো তার আগেই জনগনের হাতে পূর্ন ক্ষমতার দাবী জানিয়েছিলো
– ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস সেই দাবী জানাতে বাধ্য হয়। কেননা দেশের সাধারন মানুষ ক্রমশঃ আরো বেশি করে বিপ্লবী চিন্তাধারার দিকে চলে যাচ্ছিলো, এবং কংগ্রেস জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। জওহরলাল নেহেরু লাহোর কংগ্রেসে সভাপতি হিসেবে দাবী জানান, যে জনগনের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধীদের হাতে হাতে পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। নবাব-রাজা রাজড়ার কেন্দ্রীয় আইনসভার শাসন আর মেনে নেওয়া হবেনা। তখনকার রাষ্ট্রপ্রধান আগা খান অবশ্য এই হুমকিকে মোটেই পাত্তা দেন নি। কারন তিনি জানতেন, কংগ্রেস কখনো চরম বিপ্লবাত্মক পথে যাবেনা। বরং তাঁর ভয় ছিলো কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলন।
– কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলন বোধহয় গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি।
– না, তা পারেনি। উত্তর পশ্চিমে পেশোয়ারে লালকোর্তাদের আন্দোলন, পূবে বাংলায় তেভাগা আন্দোলন, মুম্বাই সুরাত অঞ্চলে কাপড়ের কলের শ্রমিক আন্দোলন আর তেলেঙ্গানায় কৃষক আন্দোলন, এই চার রকমের আন্দোলন গড়ে তোলা গিয়েছিলো তিরিশের দশকে। প্রতিটিই খুব জোরদার। কিন্তু তবুও, দেশ জুড়ে সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি, কেননা পার্টিকে কাজ করতে হচ্ছিলো গা ঢাকা দিয়ে। ইংল্যান্ড ও মার্কিন বিদেশ দফতর, এ দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে শেষ করতে সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।
– কমিউনিস্ট পার্টি বিদেশ থেকে সাহায্য পায়নি?
– বিদেশ বলতে তো তখন কেবল সোভিয়েত দেশ। সে নিজের গৃহযুদ্ধেই পর্যুদস্ত। আর ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাবে ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত দেশের সম্পর্ক একেবারেই ভাল নয়। কবি রবীন্দ্রনাথ গেলেন মস্কো, পরে সেই নিয়ে ছোট্ট বই লিখলেন রাশিয়ার চিঠি। বলা ভাল কিছু চিঠির সংকলন। সে বইকে ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হলো। বুঝে দেখো। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ তখন ভারতের সাংস্কৃতিক বিভাগ দেখাশোনা করেন। তাঁর বেশীরভাগ সময় কাটে বিদেশে। কাজেই, ভাল করে না দেখেশুনেই বই নিষিদ্ধ হলো।
– বুঝেছি। কিন্তু দেশে এতখানি জনসমর্থন সত্ত্বেও কংগ্রেস কেন আরো জোরদার আন্দোলনে গেলোনা? সরকারের তো ক্ষমতা কমে এসেছিলো সে সময় বলেই শুনেছি।
– ভয় হে ছোকরা, স্রেফ ভয়। যদি কংগ্রেস বিপ্লবাত্মক আন্দোলনে যায়, তাহলে কমিউনিস্ট পার্টি অনেক বেশী সুবিধে পেয়ে যাবে, কেননা তারা এই ধরনের আন্দোলনই চায়। কিন্তু কংগ্রেস চিরকাল আবেদন নিবেদনের নীতিতে চলেছে। গান্ধীজিও অসহযোগ আন্দলনের পর আর এই ধরনের বড় আন্দোলনে যেতে চান নি।
– উপরন্তু আগা খান বোধহয় মুসলিম লীগ কে দিয়ে সাধারন মানুষের মধ্যে একটা বিভাজন করতে চেষ্টা করেছিলেন।
– কিন্তু সফল হন নি। কেননা মৌলানা আজাদ, জিন্নাহ, আলামা ইকবালের মত নেতারা এগিয়ে এসে সেই আগুনে জল ঢেলে দিলেন। এই সময়েই লেখা হয় ইকবালের সেই বিখ্যাত গান “সারে যাঁহা সে আচ্ছা, হিন্দোস্তাঁ হামারা”, যা আজকে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। প্রচন্ড চাপের মধ্যে পড়ে আগা খান প্রাদেশিক নির্বাচন ও মন্ত্রিসভা গঠন করতে বাধ্য হলেন তিরিশের দশকের শেষে। কারন সেটা না হলে গোটা দেশে অচল অবস্থা তৈরি হচ্ছিল।
– ওনেক গুলো প্রদেশে কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা তৈরি হলো। কোথাও কোথাও অন্য স্থানীয় দলও মন্ত্রিসভা গঠন করল, যেমন বাংলায় ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি, পাঞ্জাবে কির্তী কিষান পার্টি। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকার দরুন নির্বাচনে অংশ নিতে পারেনি। এবারে কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ও সংসদ থেকে মনোনিত জনপ্রতিনিধিরা এলেন সরকারে অংশ নিতে। কিছুটা পরিমানে সাফল্য এলো বটে, কিন্তু তবুও আগা খানই রাষ্ট্রের প্রধান থেকে গেলেন। সেই সঙ্গে বাকি নবাব রানা, রাজা-রাজড়া, আমীররাও রয়ে গেলেন।
– নেহেরুকে বোধহয় স্বরাষ্ট্র দফতর দেওয়া হয়, জিন্নাহ পররাষ্ট্র আর সুভাষবাবু প্রতিরক্ষা পান। মৌলানা আজাদ শিক্ষা দফতর। এই কজন সচিবের নাম আমার মনে পড়ছে।
– বল্লভভাই প্যাটেল কে দেশীয় রাজ্য বিষয়ক সচিব মনোনিত করা হয়। আর চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী হলেন আইন বিষয়ক সচিব। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখ, কংগ্রেস সমাজবাদী দলের নেতারা সংখ্যাগুরু হলেও, অ-কংগ্রেসি কেউ কিন্তু স্থান পেলোনা। ইতি মধ্যে ইয়োরোপে শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। জার্মানি আক্রমন করেছে পোল্যান্ডের পশ্চিম সীমান্ত।
– এই যুদ্ধে তো ভারত প্রথম থেকেই মিত্র পক্ষকে সমর্থন করে।
– কারন আমাদের সেই সময়ের সরকার ইঙ্গ-মার্কিন তাঁবেদার। আর দক্ষিন এশিয়ায় এত বড় শক্তির সাহায্য পাওয়া মিত্র পক্ষের খুব দরকার ছিলো। এই অঞ্চলে ভারতকে এড়িয়ে কিছু করা সম্ভব নয়। আমাদের বন্দর গুলোতে ব্রিটিশ ও আমেরিকান যুদ্ধজাহাজকে নোঙ্গর ফেলতে ও রসদ জোগাড় করতে দেওয়া হয়। লোহিত সাগরের পথে প্রায় দু লক্ষ ভারতীয় সেনাকে উত্তর আফ্রিকায় পাঠানো হয় জেনারেল আরউইন রোমেলের বিখ্যাত জার্মান বাহিনির মোকাবিলা করতে। ভারতীয় বিমান বাহিনির সুব্রত মুখার্জী, অর্জন সিং এই সব বাছা বাছা পাইলটরা ইংল্যান্ডে গিয়ে জার্মান লুফত্ওয়াফের সঙ্গে লড়াই করেন ব্রিটিশ বায়ুসেনার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। এ ছাড়া বালুচিস্তানের সীমান্ত পার হয়ে ভারতীয় সেনা ইরানের তেলের ঘাঁটি আর বন্দর গুলোকে সুরক্ষা দিতে এগিয়ে যায়। এখানেই সোভিয়েত লাল ফৌজ ও ভারতীয় সেনার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন হয়। কারন ততদিনে জার্মানী, সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমন করেছে। আর ইরানের মধ্যে দিয়ে সোভিয়েত কে সাহায্য পাঠাতে সে দেশের বন্দর গুলো ব্যবহার করছে ইঙ্গ-মার্কিন জাহাজ।
– রোমেলের হাতে মার খেয়ে ইংরেজ সৈন্যরা তো পালিয়ে মিশরে ঢুকে পড়েছিল। শুনেছি তার পর ভারতীয় সৈন্য জার্মান আক্রমন রুখে দেয়।
– আমাদের চতুর্থ পদাতিক ডিভিশন প্রথম জার্মান ফৌজকে রুখে দেয়। তব্রুক আর এল-আলামাইন এ সাঙ্ঘাতিক লড়াই চলে। ভারি অস্ত্রশস্ত্র, যেমন ট্যাংক আর বিমান বহরের সমর্থন ছাড়াই যে ভাবে ভারতীয়রা রোমেল কে রুখেছিলো, তাতে গোটা দুনিয়া অবাক হয়ে যায়। সুবাদার রিচপাল রাম শুধুই যে মরনোত্তর পরমবীর চক্র লাভ করেন তাই নয়, ইংরেজরা রিচপাল রামকে তাদের সর্বোচ্চ মেডেল – ভিক্টোরিয়া ক্রস দেয়।
– ওদিকে পূর্ব এশিয়াতেও তো চরম লড়াই চলছিলো। জাপানীরা এগিয়ে আসছিলো।
– জাপান পার্ল হারবার আক্রমন করে মার্কিন প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরকে একেবারে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে অনেক জাহাজ ধ্বংস করলেও মার্কিন বিমানবাহী জাহাজের একটাও সে সময় পার্ল হারবারে ছিলোনা। ফলে সে গুলো বেঁচে যায়। এদিকে মাত্র কয়েকমাসের মধ্যে জাভা, সুমাত্রা, বালি, বোর্নিও, মালয়, চাম-পা, শ্যামের পতন হয়। ইংল্যান্ডের বড় নৌঘাঁটি সিঙ্গাপুরে দারুন লড়াই লাগে।
– সেখানে তো কিছু ভারতীয় সৈন্যকেও পাঠানো হয়েছিলো।
– ইংরেজরা সিঙ্গাপুরের যাবতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করেছিলো সমুদ্রের দিকে, দক্ষিন দিকে। কিন্তু অত্যন্ত চালাক জাপানীরা সমুদ্রের দিক থেকে আসেনি। তারা এসেছিলো উত্তর দিক থেকে জোহর প্রনালী পেরিয়ে মালয়ের ভেতর দিয়ে। সিঙ্গাপুরের পতন ঘটে এবং প্রায় তিরিশ হাজার ভারতীয় সৈনিক যুদ্ধবন্দী হয়।
– এই সৈনিকদের নিয়েই তো জাপানীরা একটা ভারতীয় বাহিনি তৈরি করতে চেয়েছিলো। মোহন সিং এর নেতৃত্বে।
– কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। কারন সুভাষ বাবু তখন প্রতিরক্ষা সচিব হিসেবে অত্যন্ত সক্রিয়, এবং তিনি রেডিওতে ডাক দিয়েছেন প্রতিটি বন্দী ভারতীয় সৈনিককে যে তারা যেন কিছুতেই মাতৃভূমির বিপক্ষে অস্ত্র না ধরে। সুভাষবাবুর জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। জাপানীরা যখন বার্মা আক্রমন করল, সুভাষবাবু সিদ্ধান্ত নিলেন, ভারতের পূর্ব সীমান্ত রক্ষার জন্যে এগিয়ে গিয়ে বার্মার ভেতরে প্রতিরক্ষা বলয় গড়তে হবে। বার্মা সে সময় ব্রিটিশ অধীকারে। তাদের সন্মতি আদায় করে আনেন বিদেশসচিব
জওয়াহরলাল নেহেরু।
– সুভাষবাবু তো রেঙ্গুনে গিয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসেন এবং রেডিওতে প্রচার চালাতে থাকেন। সেই সঙ্গে গোটা দেশের মানুষ কে ভারত রক্ষার আহ্বান জানাতে থাকেন। শুনেছি নাকি বাড়ির মহিলারা পর্যন্ত এসে তাঁদের সব গয়নাগাটি প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করে যেতেন সুভাষবাবুর কথা শুনে।
– জেনারেল আয়ুব খানের সুযোগ্য নেতৃত্বে বার্মায় ভারতীয় ফৌজ জাপানী বাহিনিকে আটকাতে পারল। মার্কিন ও ব্রিটিশরা ভারতীয় বিমানবাহিনিকে প্রচুর বিমান সরবরাহ করে, কারন ভারতে সে সময় বিমান তৈরি হতো না। ঢাকা, চট্টগ্রাম আর কলকাতার আকাশে জাপানী ও ভারতীয় বিমান বাহিনির মরনপন লড়াই চলে। কিন্তু কোথাও এতটুকু পিছু হটেনি ফৌজ। বন্দী ভারতীয় সিপাহীদের জাপানীরা নিয়ে গিয়েছিলো চীনে। তখন চীনের সমগ্র পশ্চিম অঞ্চল জাপানের দখলে। সেখানেও মারাত্মক লড়াই চলছে। জাপানী বাহিনিকে রুখছে চীনা ৯ নম্বর পদাতিক বাহিনি, জেনারেল ঝু-দে তাদের সেনানায়ক। আর এখানে ঝু-দের সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় ডাক্তার দ্বারকানাথ কোটনিস। তাঁকে কয়েক বছর আগে জওহরলাল নেহেরু পাঠিয়েছিলেন চিনের মুক্তি যুদ্ধে ভারতীয় ডাক্তার হিসেবে।
– এই কোটনিসই বোধহয় রেডক্রসের প্রতিনিধি সেজে জাপানীদের দিকে গিয়ে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আর তাদের রাজি করান জাপানীদের কথা মত অস্ত্র হাতে তুলে নিতে।
– হ্যাঁ, আর তার পরে সেই অস্ত্রই তারা জাপানীদের দিকে ঘুরিয়ে ধরে, এবং চার দিনের লড়াইয়ের পর, জাপানী লাইন ভেঙ্গে তারা চীনা অধিকারে থাকা অঞ্চলে পৌঁছতে পারে। জেনারেল ঝু-দে ছিলেন মাও-সে-তুং এর ডান হাত। তাঁর ৯ নম্বর পদাতিক বাহিনিই পরবর্তীকালে চীনা গনমুক্তি ফৌজ। এখানে এই ভারতীয় সেনারা কয়েকমাস থাকার পর, কুনমিং-ইউনান হয়ে বার্মা রোড দিয়ে অশেষ কষ্ট স্বীকার করে পায়ে হেঁটে এসে পৌঁছয় কোহিমা। কিন্তু যেহেতু তারা জাপানীদের দেওয়া অস্ত্র ধরতে রাজি হয়েছিলো, তাই তাদের বন্দী করা হলো, এবং তাদের নেতাদের, শাহনওয়াজ খান, গুরবকস সিং ঢিল্লোঁ আর প্রেমকুমার সেহগল কে দিল্লির লাল কেল্লায় নিয়ে যাওয়া হয়।
– কিন্তু কেউ এটা দেখলোনা যে তারা তাদের মাতৃভূমির প্রতি আনুগত্যে অটুট থেকেছে?
– আসল কারন অন্য। চীনা কমিউনিস্ট ফৌজের সংস্পর্ষে এসে, এই সেনারা হয়ত নিজেরাও কমিউনিস্ট হয়ে গেছে। সেই সন্দেহ। শুধু যে আগা খান এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা এই সন্দেহ পোষন করতেন, তাই নয়, অনেক কংগ্রেস নেতাও এরকম ভাবতেন। তবে সুভাষবাবু প্রবল ভাবে পাশে দাঁড়ান বন্দি সিপাহীদের। এবং তাঁদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন যুদ্ধের পর। আর নিজের সেনাদের সঙ্গে এই ব্যবহার ও প্রকাশ্যে তাদের বিরুদ্ধে বিবৃতি, ভারত সরকারের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনিতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।
– যুদ্ধের ঠিক পরেই সেনা বিদ্রোহ?
– হ্যাঁ, ১৯৪৬ সালের বিরাট সেনা বিদ্রোহ। ভারত সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। এবং জরুরী অধিবেশন বসে। অবশেষে ঠিক এক বছর পর, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে পুরোনো আইন সভা বিদায় নিলেন ১৫ই আগস্ট।
– তার পর থেকে মোটামুটি জানি। প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন সুভাষবাবু, তিনি তখন ফৌজের আদরের নেতাজী। আর প্রধানমন্ত্রি হলেন জিন্নাহ। জওহরলাল পররাষ্ট্রমন্ত্রক পেলেন, আর বল্লভভাই প্রতিরক্ষা। মুঘল বাদশাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হলেও এতদিন বাদসার বংশধররা খেতাব ব্যবহার করতে পারতেন। এবার সেই খেতাব ব্যবহার করার অধিকার ও আর রইলনা তাঁদের। বাকি সমস্ত স্বশাসিত রাজ্য গুলোকেও বল্লভভাই পাতিল ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে নিয়ে আসেন। আম্বেদকার সাহেব নতুন সংবিধান রচনা করলেন তিন বছর ধরে। ১৯৫০ এ আমরা প্রজাতন্ত্র হলাম। ১৯৪৮এ জিন্নাহ মারা যাবার পর পন্ডিত নেহেরু প্রধানমন্ত্রি।
– কিন্তু তার পরেও কি কাঙ্খিত মুক্তি এসেছে? শোষন মুক্ত করা গেছে সমাজ কে? খেটে খাওয়া মানুষ তার অধিকার পায়? মুনাফাখোরি আর মধ্যসত্বভোগী সম্প্রদায় লুপ্ত হয়েছে?
– না একেবারেই না। বরং পুঁজিপতিদের উত্থান দেখছি চারিদিকে আরো বেশী করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে যা চালানো হচ্ছে, তা আসলে পুঁজির সর্বগ্রাসী বিস্তার আর বাজারি অর্থনীতির রমরমা। সরকারে, সংসদে পুঁজিপতিদের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব। ভারত আজ পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ন অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি। কিন্তু তার সামাজিক অসাম্য আর শোষন, মুনাফাখোরী তাকে ভেতর থেকে দিনে দিনে দুর্বল করে দিচ্ছে।
– দেখো, আমাদের নেতাদের মধ্যে অনেকেরই সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কারোর দ্বিমত থাকতে পারেনা। সুভাষবাবু, লালবাহাদুর এনাদের বিরুদ্ধে তুমি কাউকে একটি কথাও বলতে শুনবেনা। কিন্তু গলদটা অন্য জায়গায়। নোনা ধরা দেওয়ালের ওপরে দামি রঙ আর পলেস্তারা চাপিয়ে লাভ নেই। দুদিনেই ভেতরের দৈন্য ফুটে বেরোবে। দরকার ভেতর থেকে বদল। একদম কাঠামোর মূল ধরে বদল শুরু করতে হবে।
ভেতর থেকে এবার ডাক এলো। খান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন কেদারা থেকে। খিদেও পেয়েছে বটে। খান সাহেবের বাড়িতে খাওয়ার কায়দা এখনো খাস পেশাওয়ারি। তবে আজ ছাত্রের জন্য বেশীরভাগ পদই নিরামিষ। কাবুলি চানা রয়েছে, পনীরের একটা লালচে ঘন বস্তু দেখা যাচ্ছে। বড় বড় নান রুটি, পোলাও, ডাল আর বেশ কিছু ফলমূল রয়েছে। একটা লম্বা দস্তরখানের ওপর এক একটা বড় থালায় এক এক রকম বস্তু সাজানো। এটা ওটা থেকে হাত দিয়ে তুলে তুলে খাবার নিয়ম। গুজরাতি নিয়মে অবশ্য থালায় সবাইকে ছোটো ছোটো বাটিতে আলাদা আলাদা করে দেওয়া হয়। কিন্তু এই পাঠানি কায়দা বড় ভাল লাগল ছাত্রটির।
– লজ্জা করোনা বুঝলে? পাঠানের খাওয়া জানো তো? মনে হবে যেন শেষ খাওয়া খাচ্ছে।
– আজ্ঞে আমি বড় বেশী খেতে পারিনা।
– তুমি মিষ্টি পছন্দ করো না? গুজরাতে তো সবাই মিষ্টি খুব ভালোবাসে।
– আজ্ঞে তা আমিও বাসি বটে
– তাহলে এই বস্তুটা একটা খেয়ে দেখো দেখি
– বাঃ দিব্যি দেখতে তো। আচ্ছা, এটা কি রসগোল্লা? এ তো বাংলার জিনিস।
– তাই বটে। এখানে পাওয়া যায়না। আমাদের প্রফেসর মিত্র, মানে অর্থনীতির মিত্র, কলকাতা থেকে ফিরলো কাল, আমার জন্যে এক হাঁড়ি এনেছে। আমার বাবা খুব ভালবাসতেন জানো।
– তাই বুঝি? তিনি এ জিনিস খেলেন কোথায়?
– ও বাবা, কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলনে তো কাবুল থেকে কলকাতা চষে বেড়াতেন। আর আজও যেমন, তখনও কমিউনিস্ট পার্টিতে বাঙালিদের সংখ্যা অনেক ছিলো। কাজেই তাদের প্রভাব তো পড়বেই।
– আচ্ছা খান সাহেব, এই যে ভারতের কয়েকটা এলাকায়, যেমন কাবুলে রাজ্যসরকার কমিউনিস্টদের, বারবাক কা্রমাল মুখ্যমন্ত্রি সেখানে। এমন কি পাখতুনি এলাকায় কমিউনিস্ট প্রভাব খুব বেশী, পেশোয়ার নগরপালিকাও কমিউনিস্ট পার্টির, লাহোরেও তাই। কেরালায়, তেলেঙ্গানায় কমিউনিস্ট জোটের সরকার। বাংলাতেও তাদের শক্তি অনেক। কিন্তু বাকি জায়গায় পার্টি এখনো দাঁড়াতে পারছেনা কেন?
– ধরো আজ বাদে কাল গোটা দেশের সব কটা লোকসভার আসনে কমিউনিস্ট পার্টি জয়ী হলো। তার পর?
– না, মানে তার পর জনমুখি নীতি গুলো কার্যকর করা হবে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরন, শিক্ষার আরো বিস্তার……… সমাজতন্ত্রের পথে আরো কিছুটা এগিয়ে যাওয়া।
– আর?
– আর , মানে সামাজিক বৈষম্য দূর হবে। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে। শোষন নীপিড়ন বন্ধ হবে।
– তাহলে তোমার আর জয়প্রকাশ নারায়ন, জুলফিকর আলি ভুট্টোর সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যে তফাত কি? তারাও তো ওই কথাই বলে। শোনো ছোকরা। নেতাদের ভাষায় কথা বলোনা। বরং প্রথমে ভাবতে চেষ্টা করো, তোমার কল্পনায় ভবিষ্যৎ ভারত রাষ্ট্রের রূপটি কেমন। তার সমাজের রূপ কেমন? শ্রমজীবি মানুষের স্থান সেখানে কোথায়? মধ্যসত্বভোগীরা কি করবে? শ্রেনীহীন সমাজ গড়তে গেলে অনেক কিছু ভাঙতে হবে, তবে জায়গা হবে নতুন সমাজ জন্মানোর। মুক্তি তবেই আসবে। পতাকা লাল হলেই সব হয়ে যায় না বাবা। তোমার দৃষ্টি সবার আগে স্বচ্ছ হওয়া দরকার। কল্পনা করা দরকার, আর সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার আমরা ঠিক কি চাই। বা আমি কি চাই। তার পরে সেই চাওয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি করো। যত বেশী বিতর্ক, তত শুদ্ধ হতে থাকবে তোমার লক্ষ।
– তার মানে আপনি বলছেন পার্টির শৃংখলা সব নয়?
– পার্টির শৃংখলার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। নিজেকে সৈনিক হিসেবে ভাবতে চেষ্টা করো। সৈনিক হতে গেলে আগে তোমাকে তালিম নিয়ে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। পড়াশোনা, বিতর্ক এসবই তোমার তালিমের অঙ্গ। তার পরে তুমি যখন কর্মী হিসেবে এগিয়ে যাবে, তখন তোমার লক্ষ্য স্থির, তুমি নিশ্চিত। নিজেকে গড়তে গেলে আগে দেশকে, নিজের মানুষ কে চিনতে হবে যে?
– আর পার্টির আন্দোলন, ভোট, নেতাদের দেখানো পথ?
– দেখো বাবা, একটা কথা বলি। এই যে দেখো আমার জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, দেওয়ালে পোস্টার মেরে গেছে তোমার পার্টি – ব্যাংক কর্মচারীদের বেতন কমিশনের জন্যে ভারত জোড়া ব্যাংক ধর্মঘট। আমি বলছিনা এই আন্দোলন অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু ভেবে দেখো, এই আহমেদাবাদ থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে কচ্ছ উপসাগরের ধারে শ্রমিকরা সারা দিন নুন কেটে বস্তায় ভর্তি করে টন পিছু ১০ পয়সা পায়। সে নিয়ে তোমরা কিছু বলছোনা কেন? এ দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতা কি জানো? নেতাদের অধিকাংশই উঠে এসেছেন পাতি-বুর্জোয়া ঘর থেকে। শহুরে মধ্যবিত্ত। কজন জন মজুর আজ পর্যন্ত নেতা হয়েছেন বলো দেখি?
– কিন্তু খান সাহেব, আমি কাউকে ছোটো না করেই বলছি, নেতৃত্বে যাবার জন্যে একটা ন্যুনতম শিক্ষা তো লাগে।
– আরে আমারও তো সেইটাই কথা। যার হাতে গাঁইতি চালাতে গিয়ে কড়া পড়েনি, সে কি করে লাল ঝান্ডা ধরবে? শিক্ষাটাই তো নেই। কলম পিষে কি কমিউনিস্ট পার্টি হয়?
– আর আমাদের বুদ্ধিজিবীরা? গননাট্য সঙ্ঘ বা গনতান্ত্রিক লেখক শিল্পি সঙ্ঘ?
– সে গুলো শাখা সংগঠন। তোমাকে সাহায্য করবে, কিন্তু বুদ্ধিজিবী দিয়ে বাম রাজনীতি চালাতে যাওয়ার ফলাফল ভয়ংকর হতে পারে। তোমাকে একটা বই দিচ্ছি দাঁড়াও। এটা পড়ে দেখো। আন্তোনিও গ্রামসি বলে এক ইতালিয়ানের তত্ত্ব।
– দেখি বইটা। এনার নাম তো আগে শুনিনি।
– শুনবে শুনবে। এবং চারিদিকে তাকিয়ে দেখবে, এই ভদ্রলোকের তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে কি সুন্দর ভাবে বুর্জোয়া আর ফাসিস্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমাদের মগজ ধোলাই করে চলেছে।
– বেশ মোটা বই। পড়তে সময় লাগবে। কিছুদিন রাখি তাহলে?
– একেবারেই রেখে দাও। এটা তোমাকে দিলাম। নাম লিখে দিই দাও। তোমরা গুজরাতিরা তো আবার নামের মাঝখানে বাবার নামও লেখো, তাই না?
– হ্যাঁ খান সাহেব। আমার বাবার নাম দামোদরদাস। আপনি আমার পুরো নামটাই লিখে দিন , নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি।
———————
টিকা-টিপ্পনি
এই লেখা যতজন দেখবেন, তার ১০% হয়ত পড়বার জন্য উৎসাহ দেখাবেন। আর যতজন পড়তে শুরু করবেন, তাঁদের মধ্যেও বড় জোড় ১০% শেষ পর্যন্ত পড়বেন। কাজেই আপনি যদি এই টিকাটিপ্পনি পর্যন্ত পৌঁছে থাকেন, তাহলে আপনি আমার সেই কুল্লে ১% পাঠকের মধ্যে একজন, যিনি এই নিরস এবং সৃষ্টিছাড়া লেখাটা পুরো পড়ে ফেলেছেন। আপনার এই পরিশ্রমকে কুর্নিশ করে, কয়েকটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে। তাই দয়া করে নিচের লাইন কখানি একটু ধৈর্য্য ধরে পড়ুন।
১। Alternate History বা অন্য ইতিহাস আসলে নিছক কল্পনা। যা হয়নি, তা নিয়ে লেখা, এমন বলবনা। বরং বলতে পারি, যা ঘটেছে, তার ফলাফল যদি একটু অন্যরকম হত, তবে কেমন হত? অন্য ইতিহাস নিয়ে বিদেশে আজকাল চর্চা হতে দেখি অনেক। আমাদের এখানে ইতিহাস চর্চাই এত কম, যে অন্য ইতিহাসের বিলাসিতা করা সাজেনা। তবে, অন্য ইতিহাস শুধুই কল্পনা নয়। যা ঘটেছে, স্থান কাল পাত্র ধরে নিয়ে, তাকে একটু অন্য ভাবে দেখা। এ লেখা লিখতে প্রথম ইচ্ছে জাগে কিছুদিন আগে, আগ্রা দুর্গে মুঘল বাদশার সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে।
২। লেখায় কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা অবশ্যই বদলানো হয়েছে। যেমন ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে দারার লড়াই ও দারার বন্দি অবস্থায় মৃত্যু। পলাসী, কার্নাল ও পানিপতের লড়ায়ের ফলাফল। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখুন, এই তিনটে ছাড়া আর তেমন কোনো বড় পরিবর্তন আমি করিনি। শিখ শক্তির উত্থান, হরি সিং নালওয়ার মাত্র ৮০০ সৈনিক নিয়ে ২৯০০০ আফগানের মোকাবিলা করা, সিপাহী বিদ্রোহ, বাহাদুর শাহ জাফর, স্যার সৈয়দ আহমেদ খান, জাতীয় কংগ্রেস, অসহযোগ আন্দোলন, অগ্নিযুগ, দুই মহাযুদ্ধ। কুট এল আমারা, উত্তর আফ্রিকা ও বার্মা তে ভারতীয় ফৌজের লড়াই। এবং আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন। সব কিছুই এই স্বল্প পরিসরে এনে ফেলেছি। আরো অনেক অনেক কিছু বাদ পড়ে গেল, তার জন্যে আমি মার্জনা চাইছি। রাসবিহারী বসুর মত মানুষকে এ লেখায় ঢোকাতে পারিনি। লালা লাজপত রাই অনুপস্থিত। এসব আমার অক্ষমতা। ওপরে দেওয়া প্রতিটি ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহিত, এবং তাদের নিচে যা লেখা হয়েছে, সে তথ্য এতটুকু বিকৃত করিনি। কুট এল আমারায় অনাহারক্লীষ্ট ভারতীয় যুদ্ধবন্দির ছবিটিও জ্বলজ্বলে সত্যি ঘটনা।
৩। প্রথমেই বলেছি, এ লেখা উদ্ভুট্টে। কিন্তু ভেবে দেখুন, যা হতে পারেনি, তা যদি হতো, কেমন হতো? তেমনি, আজ যা ভাবছি, যা করতে যাচ্ছি, সেটা না ভেবে যদি অন্য ভাভে ভাবার চেষ্টা করি, অন্য কিছু করার চেষ্টা করি, তাহলে হয়ত আমাদের ভবিষ্যতের ইতিহাসটাই অন্য ইতিহাস হয়ে যেতে পারে।
৪। লেখার একদম শেষে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রির নাম এনেছি। এবং সে নামের সঙ্গে অন্য এক রাজনৈতিক আদর্শবাদ জড়িত। এর উদ্দ্যেশ্য ভারতের বহুত্ববাদী কাঠামোকে তুলে ধরা। এর সঙ্গে বাস্তবের কোনো মতেই কোনো মিল নেই, সে কথা বলাই বাহুল্য। ভারতবর্ষের বহুমত এবং বহুত্ববাদী কাঠামোর মধ্যেই দেশের ঐক্য লুকিয়ে আছে। এবং সে ঐক্য চিরন্তন। জয় হিন্দ।