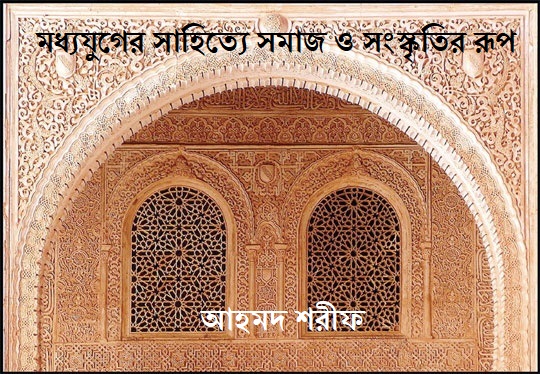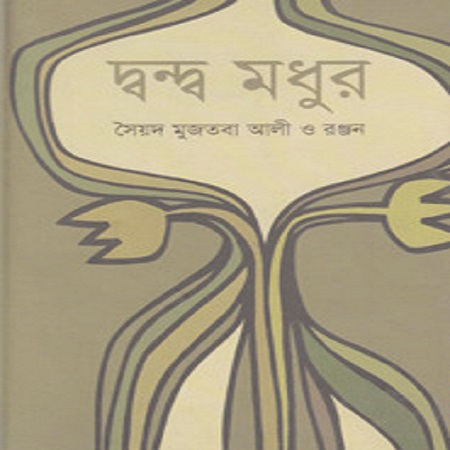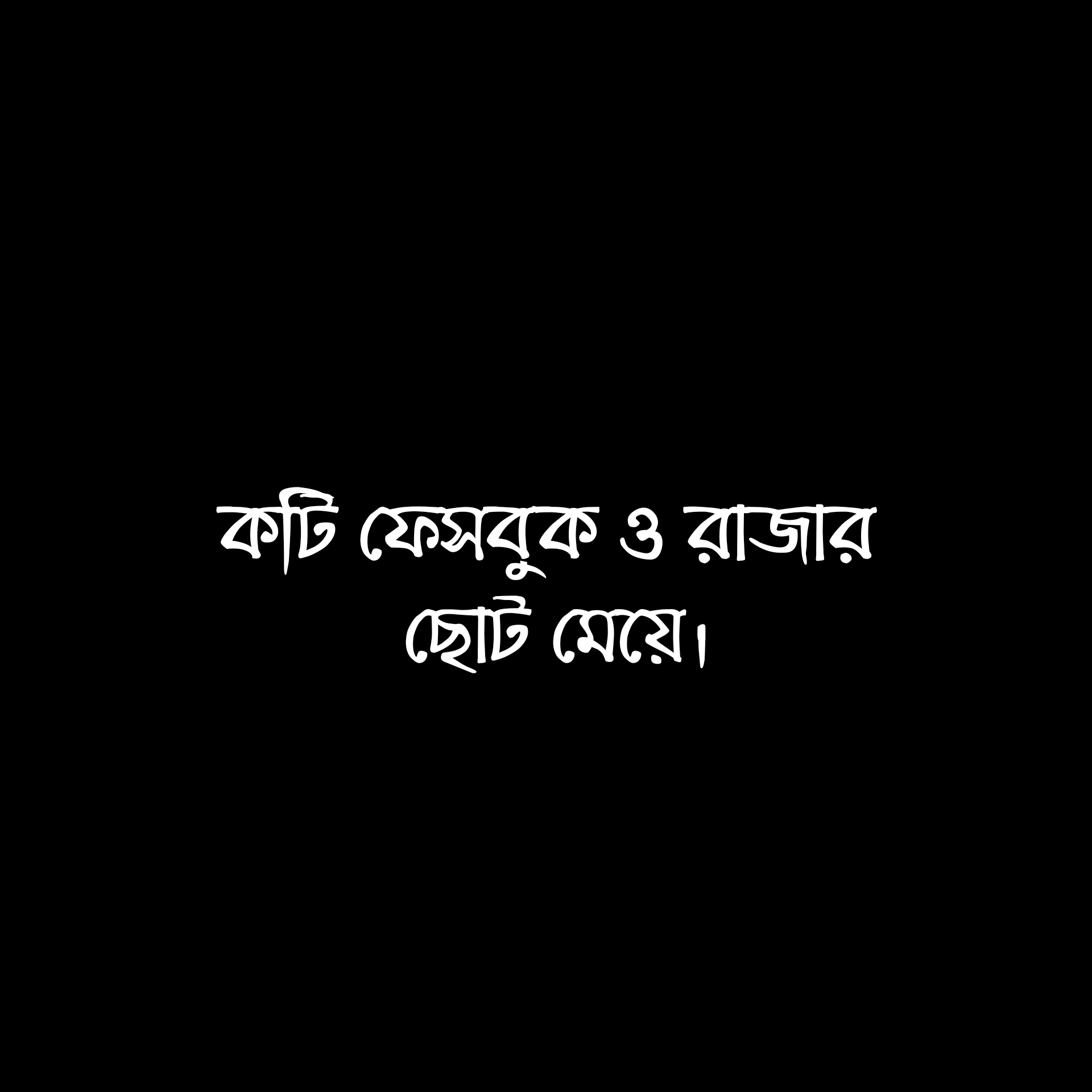ভূমিকা –মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ:
বাঙলাদেশে সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগৎ-এর প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে সম্ভবত ড. আহমদ শরীফ-ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সকলের কাছে প্রিয় হওয়ার দূর্বলতাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছিলেন। পণ্ডিত ও বয়স্ক বিদ্রোহী ড. আহমদ শরীফ চট্টগ্রামের পটিয়ার সুচক্রদণ্ডী গ্রামে ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ সনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ সনে ঢাকায় প্ৰয়াত হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৪ সনে বাঙলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ও ১৯৬৭ সনে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। কলেজে অধ্যাপনার (১৯৪৫-৪৯) মধ্য দিয়ে পেশাগত জীবন শুরু। পরে এক বছরের কিছু বেশি সময় তৎকালীন রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রে অনুষ্ঠান সহকারী হিসেবে থাকার পর ১৯৫০-এর শেষের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে যোগ দিয়ে একটানা ৩৪ বছর অধ্যাপনা করে ১৯৮৩ সনে অধ্যাপক হিসেবে অবসরগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ অধ্যাপনা জীবনে তিনি বাঙলা বিভাগের চেয়ারম্যানসহ সিন্ডিকেট সদস্য, সিনেট সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি, শিক্ষকদের ক্লাবের সভাপতি ও কলা অনুষদের চারবার নির্বাচিত ডিন ছিলেন। সেই সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অন্যতম রূপকার ছিলেন। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রথম “কাজী নজরুল ইসলাম অধ্যাপক” পদে ১৯৮৪-১৯৮৬ পর্যন্ত নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।
দেশ-কাল সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রথাগত সংস্কার পরিবর্তনের লক্ষ্যে সবসময় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তিসহ সমাজতন্ত্রের প্রতি ছিল তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ। ভাববাদ, মানবতাবাদ ও মার্কসবাদের যৌগিক সমম্বয় প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর চিন্তা চেতনা, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণে, বক্তব্যে ও লেখনীতে। তাঁর রচিত একশতের অধিক গ্রন্থের প্রবন্ধে তিনি অত্যন্ত জোরালো যুক্তি দিয়ে পরিত্যাগ করেছিলেন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা, বিশ্বাস ও সংস্কার এবং আন্তরিকভাবে আশা পোষণ করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য। পঞ্চাশ দশক থেকে নব্বই দশকের শেষ অবধি সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাসসহ প্ৰায় সব বিষয়ে তিনি অজস্র লিখেছেন। দ্রোহী সমাজ পরিবর্তনকামীদের কাছে তার পুস্তকরাশির জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয়, তাঁর রচিত পুস্তকরাশির মধ্যে বিচিত চিন্তা, স্বদেশ অম্বেষা, বাঙলার সুফি-সাহিত্য, বাঙালির চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা, বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি, এ শতকে আমাদের জীবনধারার রূপরেখা নির্বাচিত প্ৰবন্ধ. প্ৰত্যয় ও প্রত্যাশা এবং বিশেষ করে। দুখণ্ডে রচিত ‘বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য” তাঁর অসামান্য কীর্তি। তবে একথা নির্দিধায় বলা যায় যে, পিতৃব্য, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ-এর অনুপ্রেরণায় মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে পাহাড়সম গবেষণা কর্ম তাঁকে কিংবদন্তী পণ্ডিতে পরিণত করেছে। উভয় বঙ্গে এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং অদ্যাবদি স্থানটি শূন্য রয়ে গেছে। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করে তিনি মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাস রচনা করেছিলেন। বিশ্লেষাণাত্মক তথ্য-তত্ত্ব ও যুক্তি সমৃদ্ধ দীর্ঘ ভূমিকার মাধ্যমে তিনি মধ্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস বাঙলা ভাষা-ভাষী মানুষকে দিয়ে গেছেন, যা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অমর গাথা হয়ে থাকবে। তিনি জীবৎকালে বেশ কিছু পুরস্কার লাভ করেছিলেন, তার মধ্যে রাষ্ট্ৰীয় পুরস্কার একুশে পদকসহ পশ্চিম বঙ্গের রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে “সম্মান সূচক ডিলিট” ডিগ্রি পেয়েছিলেন।
মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার প্রাগ্রসর ড. আহমদ শরীফ পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ (১৯৫২), লেখক সংগ্রাম শিবির (১৯৭১), বাঙলাদেশ লেখক শিবির (১৯৭২), স্বদেশ চিন্তা সংঘ (১৯৮৩), সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদবিরোধী নাগরিক কমিটি (১৯৮১), মুক্তিযুদ্ধচেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি (১৯৯২), সমাজতান্ত্ৰিক বুদ্ধিজীবী সংঘ (১৯৯৯) সহ অন্যান্য প্রগতিশীল সংগঠনের সাথে জড়িত থাকাসহ উভয়বঙ্গে বহুবার সংবর্ধিত হয়েছিলেন।
তাঁর বিশাল পুস্তকরাশির মধ্যে যেমন মানুষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক মুক্তির কথা রয়েছে তেমনি তৎকালীন পাকিস্তানের বেড়াজাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের তাত্ত্বিক নেতা সিরাজুল আলম খান-এর নেতৃত্বে ১৯৬২ সনে গঠিত “নিউক্লিয়াস”-এর সাথেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯৬৫ সনে রচিত “ইতিহাসের ধারায় বাঙালী” প্রবন্ধে পূর্ব পাকিস্তানকে “বাঙলাদেশ” এবং “আমার সোনার বাঙলা, আমি তোমায় ভালবাসি” গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে প্রস্তাব করেছিলেন। এছাড়া বাঙলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ব সময় থেকে তাঁর মৃত্যু অবধি তিনি দেশের সব ক্ৰান্তিলগ্নে কখনো এককভাবে, কখনো সম্মিলিতভাবে তা প্রশমনের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন।
উপমহাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে অসামান্য পণ্ডিত, বিদ্রোহী, অসাম্প্রদায়িক, যুক্তিবাদী, দার্শনিক, বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব, প্রগতিশীল, মানবতাবাদী, মুক্তবুদ্ধির ও নির্মোহ চিন্তার ধারক ড. আহমদ শরীফকে ধর্মান্ধিরা শাস্ত্র ও প্রথা বিরোধিতার কারণে “মুরতাদ” আখ্যায়িত করেছিলেন। কথা ও কর্মে অবিচল, আটল, দৃঢ় মলোভাবের নাস্তিক সবরকমের প্রথাসংস্কার শৃঙ্খল ছিন্ন করে ১৯৯৫ সনে লিপিবদ্ধ করা “অসিয়তনামা”-র মাধ্যমে মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান করে গেছেন। অসিয়তনামায় উল্লেখ ছিল “চক্ষু শ্রেষ্ঠ প্রত্যঙ্গ, আর রক্ত হচ্ছে প্ৰাণ প্রতীক। কাজেই গোটা অঙ্গ কবরের কীটের খাদ্য হওয়ার চেয়ে মানুষের কাজে লাগাই তো বাঞ্চনীয়।”
পরিশেষে বলতে হয় যে, বর্তমান গ্রন্থটি ১৯৭৭ সনে প্রকাশিত হওয়ার পর প্রথম সংস্করণ বহু বছর পূর্বেই নিঃশেষ হয়ে যায়। আগ্রহী পাঠকদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ও সর্বপরি বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশ করা হল। পূর্বের ন্যায় বর্তমান সংস্করণটিও নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যের উৎসুক পাঠকদের মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশা করছি।
বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশ করার ব্যাপারে। জনাব মাহমুদ করিম-এর উৎসাহ, এডভোকেট যাহেদ করিম স্বপন-এর উৎসাহ ও সহযোগিতা এবং সময় প্ৰকাশন-এর জনাব ফরিদ আহমেদএর একান্ত আগ্রহের জন্য গ্রন্থটি পাঠকদের কাছে পৌছাতে পেরেছে। তাদের সবাইর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।
সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশ-বিবর্তন ধারা
এই সৌরজগৎ ও পৃথিবী কত লক্ষ কোটি বছরের পুরোনো তার সঠিক অনুমান সহজ নয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন। প্ৰায় আট কোটি বছর আগে থেকেই অঙ্গ এবং মস্তিষ্ক একধারায় বিবর্তন শুরু করে। আর অন্তত পাঁচ-ছয় লাখ বছর আগে থেকেই আজকের মানুষের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের সূচনা হয়। সেসব জটিল তত্ত্ব সাধারণের পক্ষে জানা-বোঝা সহজ নয়, তাই শুনেও বিশ্বাস-বিস্ময়ের দ্বন্দ্ব ঘোচে না। তবে কিছুটা প্রমাণে এবং অনেকটা অনুমানে আজকের বিদ্বানেরা স্বীকার করেন যে মোটামুটি গত দশ হাজার বছরের বুনো, বর্বর ও ভদ্র মানুষের বিচ্ছিন্ন, কঙ্কালসার ও আনুমানিক একটা আবছা! ইতিহাস খাড়া করা সম্ভব। যদিও আজকের মানুষের পূর্ণাঙ্গ পূর্বপুরুষের উদ্ভব ঘটেছে অন্তত পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ হাজার বছর আগে।
তা ছাড়া বিজ্ঞানীরা গত দশ লক্ষ বছরের প্রাকৃতিক বিবর্তনের তত্ত্বও জ্ঞানগত করেছেন বলে দাবি করেন। বরফ বা তুষার-যুগ হিমবাহ-যুগ ঐ দশ লাখ বছরে অন্তত চারবার এসেছে। ফলে জীব-উদ্ভিদজীবনেও ঘটেছে শ্রেণীগত জন্ম-মৃত্যু-উন্মেষ-বিনাশ। গত দশ হাজার বছরের মানুষের জীবন-জীবিকারীতির ধারণাও আমাদের স্পষ্ট কিংবা নিশ্চিত নয়। তবে গত ছয়-সাত হাজার বছরের ভাঙা-ছেড়া, টুটা-ফাটা জীবন-জীবিকাচিত্র নানা সূত্রে কিছু কিছু মিলেছে, এখনো মিলছে। তাতে বাস্তবের কাছাকাছি একটা সমাজচিত্র তথা রৈখিক নকশা তৈরি করা চলে। মানুষের জীবন, মনন ও জীবিকার আঞ্চলিক বিবর্তনধারা মোটামুটিভাবে জানিবার-বুঝবার জন্যেই এর গুরুত্ব অশেষ।
জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে মানুষের বিকাশ-বিস্তারধারায় তার ভাব-চিন্তা-কর্মের কতখানি তার প্রাণিসুলভ সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তির প্রসূন, আর কতখানি তার মননলব্ধ তথা অর্জিত ও সৃষ্ট, তা পরখ করে দেখার জন্যেও স্থানিক ও কালিক ব্যবধানে গৌত্রিক স্বাতন্ত্র্য ও বিকাশধারা অনুধাবন করা আবশ্যিক।
মানুষের পুরাতত্ত্বজানতে হলে প্রকৃতিবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীর উদঘাটিত ও অনুমিত তত্ত্বেও আস্থা রেখে, ঐগুলো স্বীকার করে ও ভিত্তি করেই সন্ধানে, বিশ্লেষণে ও সমন্বয়ে এগুতে ও সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হয়।
নৃবিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষের জীবনের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও মনন-উৎকর্ষজীবিকাপদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। জীবিকা-পদ্ধতি আবার প্রাকৃতিক প্রতিবেশের প্রসূন। আমরা জানি, দুনিয়ার সর্বত্র সে-প্রতিবেশ অভিন্ন নয়। উত্তর মেরুর বরফ-ঢাকা এলাকায় এস্কিমোরা যেমন আজও তুষার-যুগ অতিক্রম করতে পারে নি, তেমনি সৃষ্টিশীল কিংবা গ্ৰহণকামীও নয় বলে সভ্যদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আদিম বুনোমানুষও দুর্লভ নয়। আফ্রিকা এবং এশিয়া-য়ূরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা ছোট-বড় দ্বীপে বাস করেছে, তারাও উদ্ভাবন-আবিষ্কার-প্ৰয়াসের অভাবে কিংবা খাদ্যাভাব ও জনবৃদ্ধিপ্রসূত প্রয়োজন প্রেরণার অনুপস্থিতির ফলে আদিমানবের তথা পুরোপোলীয় যুগের জীবন-জীবিকা স্তরেই রয়ে গেছে। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ও গোত্রের মানুষ প্রাকৃতিক প্রতিবেশ-নিয়ন্ত্রিত জীবিকাপদ্ধতি-প্রসূত প্রয়োজনানুরূপ সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণবিধি এবং ঐহিক-পারিত্রিক চিন্তা-চেতনার জন্ম দিয়েছে। জীবিকা অর্জন সর্বদা ও সর্বত্র কখনো সহজ, সরল ও সুসাধ্য ছিল না। কেননা অজ্ঞআনাড়ি-অসহায় মানুষ তখন ছিল একান্তই প্রকৃতির আনুকূল্য-নির্ভর। ঝড়-বৃষ্টি-বন্যাশৈত্য-খরা-কম্পন ছাড়াও ছিল অপ্রতিরোধ্য শ্বাপদ-সরীসৃপ আর নিদানবিহীন লঘুগুরু নানা রোগ। গা-পা যেমন ছিল নিরাবরণ, মন-মেজাজও তেমনি ছিল আত্মপ্রত্যয়বিহীন। এমন মানুষ ভয়-বিস্ময়-কল্পনাপ্রবণ হয়, আর বিশ্বাস-ভরসা রাখে ও বরাভয় খোজে অদৃশ্য অরিমিত্র দেবশক্তিতে। তার চাওয়া-পাওয়ার অসঙ্গতির ও ব্যৰ্থতার এবং অপ্রত্যাশিত প্ৰাপ্তির কিংবা বিকলতার অভিজ্ঞতা থেকেই এই অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্বের ও প্রভাবের ধারণা অর্জন করে সে। তখন থেকেই তার জীবনজীবিকা ইহ-পরলোকে প্রসারিত। স্বায়ত্ত নয় বলেই জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার ও স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্যের কামনা তাকে দৈবাশ্রিত হতে বাধ্য করেছে।
প্ৰাণী হিসেবে মানুষেরও কিছু সহজাত বুদ্ধি, নিরাপত্তা-প্ৰয়াস, জীবিকা-চেতনা ও জ্ঞাতিত্ববোধ ছিল অর্থাৎ প্রাণিসুলভ একটা জীবনোপায়বোধ ছিলই। কিন্তু তার আঙ্গিক সৌকর্যপ্রসূত অনন্যতা এবং অনন্য মননশক্তি তাকে একান্তই বৃত্তি-প্রবৃত্তি-নির্ভর প্রাণী রাখে নি। তার অনন্যতার কারণ ছয়টি–প্রত্যঙ্গের বিশিষ্টতা, মস্তিষ্কের বিশেষ বিকাশশক্তি, বিশেষ যৌথজীবন-প্রবণতা, বাকশক্তি, হাতিয়ার ব্যবহারের সামৰ্থ্য ও মননশক্তি। আসলে সবটাই তার আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের উপজাত। ফলে শীঘ্রই সে নিশ্চয়ই অস্পষ্টঅবচেতন মনে আত্মশক্তির অনুভবে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে প্রকৃতিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তার সমস্ত বিকাশ-বিস্তারের মূলে রয়েছে ঐ আত্মপ্রত্যয়প্রসূত দ্রোহ। তাই মানুষমােত্রই প্রকৃতিদ্রোহী। আঙ্গিক সুষ্ঠুতা ও সৌকর্য তাকে দিয়েছে হাতিয়ার ব্যবহারের প্রবর্তনা। কাজেই হাতিয়ারবিরহী মানুষ কল্পনাতীত। হাতিয়ারবিহীন মনুষ্য-জীবিকা তাই আমাদের ধারণায় অসম্ভব। অতএব মানুষ বলতে সহাতিয়ার মানুষই বোঝায়। ফলে মানুষের ইতিহাস হচ্ছে প্রকৃতি-জিগীষু, যুধ্যমান, জয়শীল, হাতিয়ারস্রষ্টা এবং জীবিকার উৎকর্ষ ও প্রসারকামী মানুষের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বাধা-বন্ধ ও পতন-অভু্যদয়ে বন্ধুর পথ অতিক্রমণের বহু বিচিত্র দীর্ঘ ইতিকথা। কাজেই শ্রম, হাতিয়ার ও মনন প্রয়োগে প্রকৃতিকে বশ ও দাস করে জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধন এবং আনুষঙ্গিকভাবে ভাব-চিন্তা-কর্ম-সংস্কৃতি ও সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগমন তথা জীবনপ্রবাহে সার্বিক পরিশ্রুতি আনয়নপ্রয়াসই মনুষ্যজীবনচর্যার ইতিবৃত্ত। আগেই বলেছি, নানা কারণে এ কারো পক্ষে হয়েছে সম্ভব, কারো কাছে রয়েছে আজও আয়ত্তাতীত। বিকাশের এক স্তরে মনুষ্য ইতিহাস ও সমস্যা সংহত হয়ে মুখ্যত জীবিকা-সম্পদ-প্রতীক বিনিময়মুদ্রার অধিকারে তারতমাপ্রসূত শ্রেণীসংগ্রামের রূপ নেয়। এবং সে-মুহূর্ত থেকেই জীবিকা অর্জন ও জীবনধারণ পদ্ধতি জটা-জটিল হয়ে ওঠে। অধিকাংশ মানুষের পক্ষে তখন জীবন-জীবিকা দুঃসহ, দুর্বহ, যন্ত্রণাময় হয়ে পড়ে। একালে দুনিয়াব্যাপী সেই যন্ত্রণামুক্তির উপায় উদ্ভাবনে, প্ৰয়াসে, সংগ্রামে, দ্বন্দ্বে-সংঘর্ষে-সংঘাতে মানুষ কখনো মত্ত, কখনো আসক্ত, কখনো-বা পর্যুদস্ত। জয়-পরাজয়ের আবর্তে কখনো আর্ত, কখনো আশ্বস্ত। প্রবহমান জীবনে যন্ত্রণা ও আনন্দ, সমস্যা ও সমাধান, বর্জন ও অর্জন, দ্বন্দ্ব ও মিলন, বিনাশ ও উন্মেষ চিরকাল এমনি দ্বান্দ্বিক সহাবস্থান করবে। চলমান জীবনস্রোতে নতুন দিনে নতুন মানুষের নতুন পথের নতুন বাঁকে নতুন সমস্যা ও সম্পদ, যন্ত্রণা ও আনন্দ থাকবেই। কেননা চলমানতার এসব নিত্য ও চিরন্তন সঙ্গী।
মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্মে-আচরণে যা-কিছু অভিব্যক্তি পায়, তার কিছুটা প্ৰাণিসুলভ সহজাত, আর কিছুটা মননলব্ধ তথা অর্জিত। এ দুটোর সংমিশ্রণে অবয়ব পায় মানুষের চরিত্র, অভিব্যক্ত হয় জীবনাচরণ। অনুশীলন-পরিশীলনের স্তরভেদে কোনো বিশেষ স্থানে ও কালে ব্যষ্টি ও সমষ্টির আচার-আচরণে কখনো প্রাণিসুলভ স্কুল-অসংযত স্বভাব প্রবলভাবে প্রকাশ পায়, কখনো-বা অর্জিত আচরণ প্রাধান্য পায়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই কখনো অবিমিশ্র বা অনপেক্ষ কোনো আচরণ সম্ভব নয়। তাই আজকের সভ্যতম সংস্কৃতিবান মানুষেও আদিম মানুষের আচার-আচরণের ছিটেফোঁটা মেলে—কখনো আদিরূপে, কখনো-বা রূপান্তরে।
বিভিন্ন স্থানে বিচিত্র ব্যবহারিক-বৈষয়িক প্রয়োজনে ও মানসিক কারণে নানা স্থানের নানা গোত্রীয় মানুষের সম্পর্কজাত নানা পারস্পরিক প্রভাবে মানুষের শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কার, সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনা বহুমুখী, বিচিত্রধর্ম ও দুর্লক্ষ্য জটিল হয়ে উঠেছে। কারা কাদের প্রভাবে কী পেয়েছে কিংবা কী হয়েছে, তা আজ নিঃসংশয়ে বলা-বোঝা অসম্ভব। তবু আমাদের জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে হয় এবং সন্ধানে, নিদর্শনে, বিশ্লেষণে, প্রমাণে ও অনুমানে যা মেলে, তা দিয়েই মনোময় উত্তর তৈরি করে আমাদের কৌতুহল মিটাই এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোনো কোনো মানবিক সমস্যার মূলানুসন্ধানে, কারণ-করণ নিরূপণে ও সমাধানচিন্তায় সে জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত কাজে লাগাই।
জগৎ ও জীবনের উদ্ভব সম্বন্ধে প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা যেমন নানা তথ্য উদঘাটন ও তত্ত্ব উদ্ভাবন করে বিভিন্ন পদার্থের ও জীব-উদ্ভিদের উদ্ভব ও বিকাশের নানা স্তরবিন্যাস করেছেন, তেমনি নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীরাও মানুষের ক্রমবিকাশ ও বিস্তারের নানা স্তর আবিষ্কার ও অনুমান করেছেন। সাধারণভাবে বন্য, বর্বর ও ভব্যকালে ও শ্রেণীতে মানুষকে বিভক্ত করে মনুষ্যজীবনপ্রবাহের ক্রমোন্নতি নিরূপণের চেষ্টা হলেও দীর্ঘকাল পরিসরের পরিপ্রেক্ষিতে কালিক স্তর ও হাতিয়ারের উপকরণ ও উপযোগ অনুসারে যুগবিভাগ করার স্বীকৃত রীতি-নীতিও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন হাতিয়ারের উপকরণ অনুসারে হাতিয়ারবিহীন ফল-মূল-পাতাজীবী আদিম মানুষের যুগ, খাদ্য সংগ্রহে কাঠঢ়িল-পাথরখণ্ড ব্যবহারকারী পুরোপোলীয় যুগ বা পুরোনো পাথর-যুগ, অস্ত্ররূপে ঘষামাজা পাথর প্রয়োগকারী নব্যপোলীয় বা নবপাথর যুগ, তামা আবিষ্কারের ও ব্যবহারের তাম্রযুগ, পিত্তল আবিষ্কারের ও ব্যবহারের পিত্তল বা ব্রোঞ্জ-যুগ, লৌহ আবিষ্কারের ও প্রয়োগের লৌহ-যুগ। এর মধ্যেও নানা বস্তুর আবিস্ক্রিয়া কৌশলের উদ্ভাবন এবং বস্তুর ও কৌশলের উপযোগ সৃষ্টিভেদে ও ক্রমবিকাশে নানা উপস্তুর তৈরি হয়েছে। হাতিয়ার তথা যন্ত্র মানুষের আঙ্গিক শক্তির বহুল বিস্তৃতিতে ও সুনিপুণ, সুষ্ঠ, সুপ্রয়োগে অপরিমেয় সহায়তা দিয়েছে। আধুনিক বৈদ্যুতিক-আণবিক যন্ত্র সেই যন্ত্র বা হাতিয়ার আবিষ্কার-উদ্ভাবনের প্রবণতা ও প্ৰয়াসেরই ক্রমপরিণত রূপ।
এই যন্ত্র-চর্চা কেবল অগ্নি-অন্ন, আসবাব-তৈজস, অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, বস্ত্ৰ-বৰ্ম, কাস্তে-কোদাল, জাল-জাহাজ নির্মাণে অবসিত হয় নি, চন্দ্ৰ-সূৰ্য-গ্ৰহ-নক্ষত্র ও জল-বায়ুর গতিবিধি ও মেজাজ-মর্জি জানা-বোঝার প্রবর্তনাও দিয়েছে। এভাবে মানুষ আকাশ ও মাটির এবং এদের মধ্যেকার সমস্ত গুপ্ত ও ব্যক্ত পদার্থকেই কেজো সম্পদে পরিণত করার সাধনায় হয়েছে নিরত।
মানুষের ক্রমবিকাশ ত্বরান্বিত করেছে। যেসব আবিক্রিয়া ও উদ্ভাবন সেসবের মধ্যে মুখ্য হচ্ছে ভাষা, আগুন, টাকা, লিপি, লোহা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও সম্পদ-প্রতীক বিনিময়-মুদ্রা। মানুষের জীবনপদ্ধতি আর প্রাকৃত রইল না, হল কৃত্রিম ও স্বসৃষ্ট।
কালপ্রবাহে ময়াটি-ক্ল্যান, ফ্রাটি-ট্রাইব, সম্প্রদায়-সমাজ, দেশ-রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে জীবন-জীবিকার প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে। সহজে কিংবা সরলভাবে নির্বিঘ্নে কিছুই হয় নি। কোনো কোনো বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে আজও মানুষ ক্ল্যান স্তরেই রয়ে গেছে।
মননের ক্ষেত্রেও অনেক মানুষ আজও সর্বপ্রাণবাদের, জাদু-বিশ্বাসের, টোটেমটেবু তত্ত্বের, প্ৰেত-সংস্কারের ও প্যাগান-বোধের নিগড়ে নিবদ্ধ। এভাবে পাথর-মাটিদূর্ব, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, কূর্ম-কুমির-মকর-হাঙর-মৎস্য ফুল-ফল-তরুলতা থেকে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র এবং অদৃশ্য অনেক কল্পিত শক্তি মানুষের ভয়-ভরসার কারণরূপে পূজ্য ও আরাধ্য হয়েছে। পরে প্রমূর্ত প্রতিমা হয়ে কেবল মনে হয়, ঘরে-সংসারেও ঠাই পেয়েছে। এ বিচিত্র বিবর্তন-বিকাশ হতে সময় লেগেছে হাজার হাজার বছর। মননশক্তির বিকাশে, যুক্তি-বুদ্ধির ও রুচির উন্মেষে টোটেম পেয়েছে স্রষ্টার ও দেবতার মর্যাদা, সংস্কার উন্নীত হয়েছে শাস্ত্রে, বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ধ্রুব সত্যে। টোটেম-টেবু তত্ত্বের উদ্ভব হয়তো খাদ্য ও নিরাপত্তার অনুকূল ও প্রতিকূল চেতনাপ্রসূত।
প্রচলিত ধর্মের মধ্যে বৈদিক বা ব্ৰাহ্মণ্যধর্ম নানা কারণে বিশিষ্ট। দুনিয়াল আর আর ধর্ম হচ্ছে ব্যক্তি-প্রবর্তিত ধৰ্ম, আর ব্ৰাহ্মণ্যধর্ম হচ্ছে বিবর্তিত ধর্ম। সুদীর্ঘকালের পরিসরে লোকহিতকামী বহু জ্ঞানী মনীষীর কালিক অনুভব,-প্রয়োজন-চেতনা, শ্রেয়োবোধ ও মননপ্রসূত তথ্য, তত্ত্ব, নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্য-নির্দিষ্ট আচার-আচরণ বুদ্ধি থেকে ক্ৰমবিকাশের ধারায় এর স্বাভাবিক।-উদ্ভব ও প্রসার। তাই এতে মনুষ্য-চেতনার ও আচারের আদিম রূপ যেমন মেলে, মনুষ্য-মননের সূক্ষ্মতম বিকাশ ও উচ্চতম বোধও তেমনি এতে দুর্লভ নয়। টোটেম যুগের কূর্ম-বরাহ-অশ্ব-অশ্বতর, যক্ষ, কুকুর, রক্ষঃ, পেচক, গরুড়, হনুমান, সাপ, মকর, গজ, গরু, মহিষ, বিন্দ্ৰ, অশ্বথ, তুলসী, শিলা প্রভৃতি দেবকল্প কিংবা দৈত্যকল্প জীব-উদ্ভিদ ও পদার্থ যেমন বধ্য কিংবা পূজ্য রয়েছে, রয়েছে। টোটেম কিংবা টেবু হয়ে, তেমনি ঔপনিষদিক তত্ত্বচিন্তা এবং নিরীশ্বর দার্শনিক চেতনাও সমভাবে আদর-কদর পেয়েছে। হিন্দুশাস্ত্ৰে, সংহিতায়-পুরাণে যেসব ইতিবৃত্ত বিধৃত রয়েছে, সেগুলো দিয়েই ভারতীয় মানুষের বুনো-বর্বর-ভাব্যস্তরে ক্রমোন্নয়নধারার ইতিকথা রচনা করা সম্ভব।
খাদ্য-সংগ্রাহক যাযাবর মানুষ, খাদ্যশিকারি যাযাবর মানুষ, পশুপালক যাযাবর মানুষ, কৃষিজীবী অর্ধ-যাযাবর মানুষ, কৃষি-শিল্পজীবী স্থায়ী বস্তির মানুষ, পণ্যবিনিময় স্তরের মানুষ, মুদ্রাবিনিময় স্তরের নাগরিক মানুষও-যে সর্বত্র সমান কুশলী, মননশীল কিংবা উন্নত সামাজিক ও সংস্কৃতিবান মানুষ ছিল, তা নয়–যেমন আজকের পৃথিবীর বুনো কিংবা শহুরে মানুষ আজও সমস্তরের নয়। প্রাকৃতিক প্রতিবেশে দেশ কাল ও মানুষভেদে তারতম্য থেকেই যায়। তবু মানুষের জীবনপ্রয়াস-যে অন্য প্রাণীর মতোই খাদ্যভিত্তিক তা মিথ্যা হয়ে যায় না। খাদ্যের আহরণে, সংরক্ষণে ও সুলভতায় নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাদান প্ৰয়াসেই মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম নিয়োজিত। এই প্ৰয়াসের মুখ্য ও গৌণ কারণ এবং ফলস্বরূপ এসেছে মানুষের আর আর আনুষঙ্গিক আবিক্রিয়া ও উদ্ভাবন যা ব্যবহারিক, বৈষয়িক কিংবা মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করে। অতএব খাদ্য উৎপাদনলক্ষ্যে শ্রম ও হাতিয়ার প্রয়োগই মানুষের সার্বিক উন্নতি ও বিকাশের মূল। খাদ্যসংগ্ৰাহক ও শিকারি মানুষ খাদ্য সংরক্ষণ করতে জানত না বলে উদার ছিল, উদরপূর্তির পর উদৃত্ত খাদ্য অপরকে দিতে দ্বিধা করত না। কিন্তু পশুপালক ও কৃষিজীবী মানুষ সঙ্গত কারণেই সম্পদ-সচেতন ও স্বার্থপর হয়ে ওঠে। তখন থেকেই বৈষম্যবীজ ও শ্রেণীচেতনার অনিৰ্দেশ্য ও নিরুদ্দিষ্ট উন্মেষ।
যেমন মানুষের আঙ্গিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় ও শ্রেণীনিরূপণ করেন, সমাজবিজ্ঞানীরা তেমনি মুখ্যত জীবনচর্যার মাপে মানুষের বিকাশধারা বুঝতে চান। নৃবিজ্ঞানীরা গুরুত্ব দেন চোখ-চুল-নাকে, মাথা-চোয়াল-কপালের গড়নে, আর আদিম জীবনাচরণ ও মননধারার নমুনায়। সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, আদর্শ-উদ্দেশ্য, উৎপাদন-বন্টন, মন-মনন, প্ৰথা-পদ্ধতিপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতির গঠন-বৈচিত্র্যের ও বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণপ্রবণ। তবু নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রায় অভিন্ন। কেননা একটা ছেড়ে অন্যটা আচল। বলতে গেলে, এগুলো মানব-পরিচিতির একাধারে তিনটে দিক ও স্তরমাত্র এবং সব কয়টির উদেশ্য হচ্ছে সামষ্টিক জীবনধারায় অভিব্যক্ত জীবনচর্যায় স্বরূপ নিরূপণ।
ব্যক্তি হিসেবেও মানুষের জৈবিক, নৈতিক, বৃত্তিক, বৌদ্ধিক, শান্ত্রিক ও শ্রেণিক বা সামাজিক আচরণ তার বলনে-চাহনে-চলনে কিংবা ক্রীড়ায়-কর্মে-ভঙ্গিতে, হাসি-ঠাট্টায়ক্ৰোধে-ক্ষোভে, দয়ায়-দাক্ষিণ্যে-সেবায়-সমবেদনায়, ঈর্ষায়-অসূয়ায়, লিন্সায়-নিষ্ঠুরতায় নিত্য প্ৰকাশমান। ব্যষ্টি নিয়ে সমষ্টি, সেই সামষ্টিক আচরণে একটা সমাজসত্তার বা জাতিসত্তার সামানীকৃত আচরণ বা অভিব্যক্তি নিরূপণই নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকের সন্ধিৎসার মূল লক্ষ্য।
মানুষের মনন ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় জন্মসূত্রে লব্ধ পারিবারিক-সামাজিক-শান্ত্রিকসাংস্কৃতিক বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, নীতি-আদৰ্শ, প্ৰথা-পদ্ধতি-প্রতিষ্ঠান, উৎসবপার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির প্রভাবে। এদিক দিয়ে কোনো মানুষই স্বাধীন ও স্বসৃষ্ট নয়, হাজার অদৃশ্য ‘বাগে’ ও বাঁধনে তার ভাব-চিন্তা-কর্ম ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত। অতএব সামাজিক আচরণমাত্রই কৃত্রিম তথা অর্জিত, অনুশীলিত ও পরিস্রুত।
এই বহু ও বিচিত্র বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, আচার-আচরণ, উৎসব-পার্বণ, প্ৰথা-পদ্ধতি, দারু-টোনা-ঝাড়-ফুক-তাবিজ-মাদুলি-বাণ-উচাটন প্রভৃতির সম্ভাব্য উৎস নির্দেশ, তার আদি ও রূপান্তর নিরূপণ, টোটেম-টেবু-জাদুর জড় আবিষ্কার প্রভৃতি আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য বা প্ৰায় অসাধ্য বটে, তবে আমাদের তথ্য পরিবেশনা বিদ্বনবিজ্ঞানীদের তত্ত্ব নিরূপণের ও মূলানুসন্ধানের সহায়ক হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। তাই আমাদের এ প্ৰয়াস এবং প্ৰয়াসের সার্থকতাও এখানেই।
আমরা প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের শ্রেণী ভাগ করেছি। সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক এই উপকরণগুলো প্ৰায় পাঁচশ বছরের পরিসরে রচিত গ্রন্থাবলি থেকে সংগৃহীত ও সংকলিত। সে-যুগে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলের যন্ত্রগুলো আবিষ্কারপূর্ব যুগে সমাজের বিবর্তনের গতি ছিল স্থবিরপ্রায় মন্থর। আবর্তনই ছিল স্বাভাবিক। পাঁচশ বছরেও পরিবর্তন ছিল দুর্লক্ষ্য। বরং সে-যুগে মনন-বিবর্তন যত সহজ ছিল, তত স্বাভাবিক ছিল না ব্যবহারিক–বৈষয়িক-জীবনধারার পরিবর্তন। তাই জন্মমৃত্যু শাসিত জীবনস্রোত তথা লোকপ্রবাহ ছিল, কিন্তু তেমন ক্রমবিবর্তন ছিল নাজীবনযাত্রার ধারায় কেবল আবর্তিত প্রবাহই ছিল স্বাভাবিক। জন্মসূত্রে পাওয়া সং ও ধর্মশাস্ত্ৰই-যে মানুষের মনন ও আচরণ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে, তা কেউ অস্বীকার করে না। সেজন্যেই আমরা কেবল মুসলিম-রচিত বাংলাসাহিত্য থেকেই উপাদান সংগ্ৰহ করেছি। যাতে দেশজ মুসলমানের শাস্ত্ৰ, সমাজ ও সংস্কৃতিগত আচার-আচরণের একটা সার্বিক ও সামগ্রিক রূপ মেলে এই প্ৰত্যাশায়।
সঞ্চয়বুদ্ধিই যৌথজীবনের প্রবর্তনা দেয়। তাই মানুষ ছাড়াও উই-পিঁপড়ে-মৌমাছির মধ্যেও এ যৌথজীবন-পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করি। এমনকি সন্তান জন্মানোর ও লালনের জন্যে নীড় নির্মাণ করতে হয় বলে কাক-কবুতর-বক-বাবুই প্রভৃতি অনেক পাখির মধ্যেও সাময়িক দাম্পত্য বা যৌথজীবনাসক্তি দেখতে পাই। কোনো কোনো পশু-পাখির মধ্যেও সর্বগণমান্য দলপতি বা গোষ্ঠীপতি, তথা পরিচালক বা নেতা, অগ্রগামী খাদ্যসন্ধানী দল এবং রক্ষক প্রহরী ও রক্ষাবৃহের ব্যবস্থা দেখা যায়। সংগৃহীত খাদ্যবস্তু বাইরে সঞ্চয় করে রাখার সামৰ্থ্য নেই বলে ছানার জন্যে সংগৃহীত খাদ্য এরা উদরেই রাখে কিছুক্ষণ। গরিলা-শিম্পাঞ্জি-গিবনদের মধ্যেও রয়েছে দাম্পত্য। তা ছাড়া তোতা-কাক-শকুনহাঁস-শিয়াল-বানর-ভেড়া-শূকর-হাতি-বেবুন-গিবন-গরিলা-শিম্পাঞ্জি-ওরাঙউটাং প্রভৃতি বহু বহু প্ৰাণীও জ্ঞাতিত্ববোধে, যৌথজীবনে এবং একপ্রকারের সামাজিক দায়িত্ব পালনে অভ্যস্ত। কাজেই প্ৰাণী হিসেবে হয়তো আদি মানুষও যুথবদ্ধ হয়েই থাকত। তবে তার আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ও মননশক্তি তার যৌথজীবনে উৎকর্ষ ও বিকাশ দান করেছে দ্রুত। যুথবদ্ধ থাকতে হলে নেতা ও নীতি ভাগে স্বীকৃতি দরকার, তার সঙ্গে আবশ্যিক সমস্বার্থে বা স্ব স্ব স্বার্থে সহিষ্ণুতা, সহাবস্থান ও সহযোগিতার স্থায়ী অঙ্গীকার। যৌথজীবন এ না। হলে চলতেই পারে না। এ বোধ থেকেই পালনীয় ও বর্জনীয় নিয়মনীতিস্বরূপ আইন এবং প্রয়োগকারী সংস্থা সরকারের ক্রমোদ্ভব। তাই আমরা আদিমানুষে পাই দৃঢ় ক্ল্যানচেতনা, তা থেকে ক্ৰমান্বয়ে ফ্রাটি, ময়াটি ও ট্রাইব। এই ট্রাইব বা গোত্রীয় জীবন বন্য, বর্বর ও ভব্য জীবনে দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল। তারপর সর্বপ্ৰাণ-টোটেম-টেবু-জাদু-প্যাগান তত্ত্ব-চেতনার ক্রমোন্নতিতে যখন বিবর্তিত বা প্রবর্তিত শাস্ত্রীয় ধর্মে উত্তরণ ঘটল, তখন সহ ও সম-মতবাদীর দল বা সম্প্রদায় গড়ে উঠল। এভাবেই পরে কালপ্রবাহে অগ্রসর মানুষের পরিচয় দেশ-গোত্র-জািত-বর্ণ-ধর্ম-বৃত্তি-শ্রেণী-সম্পদভিত্তিক হয়ে দাঁড়াল। অনগ্রসর বুনো ও বিচ্ছিন্ন মানুষ আজও ক্ল্যান-ফ্রাটি ময়াটি-ট্রাইব স্তরে আটকে রয়েছে। কিন্তু আজকের অগ্রসর মানুষেও কিন্তু সেই কওম-চেতনা মুছে যায় নি, আদিরূপে কিংবা বিবর্তিত রূপে তা ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিক কিংবা সামাজিক আচরণে কখনো কখনো প্ৰকটি হয়েই প্ৰকাশ পায়।
জীবনচর্যার উৎস প্রতিবেশ-প্রভাবিত জীবিকা হলেও হাতিয়ার ও নৈপুণ্যের বিবর্তনধারায় তা জটিল পথে মুখ্য-গৌণ, প্ৰত্যক্ষ-পরোক্ষ হয়ে পড়ায় কারণ-ক্রিয়ায় বোধসূত্র লোকস্মৃতিতে গেছে হারিয়ে। তাই অনেক আচার-সংস্কারই হয়ে পড়েছে আপাত নিরুদ্দিষ্ট ও তাৎপৰ্যহীন। ফলে সম্পর্ক-স্বরূপ নিৰ্ণয় হয়েছে দুঃসাধ্য। যেমন নাচ-গান–চিত্ৰ—এগুলো ছিল আদিতে শিকার-সাফল্যের, অনুকূল রোদ-বৃষ্টি আবহসৃষ্টির ও বিপদমুক্তির প্রাকৃত বা দৈবিক আবহসৃষ্টির বাঞ্ছাপ্রসূত উদ্ভাবন। এখন নাচ-গান-চিত্র আমাদের মানসিক-নান্দনিক বিলাসক্রিয়া মাত্র।
যখন মানুষ খাদ্যরূপে ফল-মূল সংগ্রাহক মাত্র ছিল, যখন খাদ্য সংগ্ৰহকালে সঙ্গীসহচর থাকলেও ঐ কার্যে সহযোগী-সহকারীর প্রয়োজনই ছিল না, তখনো কিন্তু জৈবিক কারণে নারী-পুরুষের মিলন কাম্য ছিল। তখনো হয়তো ব্যক্তিক বিবাদের কারণ ঘটত নারীসম্ভোগ নিয়ে—জীবজগতে আমরা যেমনটি দেখতে পাই। তা ছাড়া মনুষ্যস্মৃতিতে কামই বিপদ-বিবাদের উৎস। আদম-ইভের স্বৰ্গচ্যুতি ঘটে কাম-চেতনা জাগার ফলেই। প্রথম পার্থিব বিবাদ ও নরহত্যার মূলে ছিল নারীর লাবণ্য। কাবিলের হাবিল-হত্যা দিয়েই শুরু ভ্রাতৃ-হননের তথা নরনিধনের। গ্রিক-হিন্দু পুরাণেও রয়েছে দেব-দানবের নারীকেন্দ্রীয় বিবাদ-বিগ্রহের কাহিনী। হোমার-বাল্মীকি-ব্যাসের কাব্যে নয় কেবল, দুনিয়ার রূপকথা, উপকথা ও ইতিকথার মূলেও রয়েছে পুরুষ-ভোগ্য নারী।
কাজেই ‘জমি’র আগে ‘জরু’ই ছিল দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উৎস। তারপর পশুপালক ও কৃষিজীবী মানুষের জীবনে বিবাদ-বিগ্রহের কারণ দাঁড়াল দুটো–জারু ও জমি। আরো অনেক পরে যুক্ত হল। আরেকটি কারণ–তা হচ্ছে ‘জওহর’।
সংস্কারমুক্ত স্বৈরিণী নারীর যে-কোনো পুরুষকে দেহ দানে হয়তো আপত্তি ছিল না, কিন্তু সন্তানধারণ ও লালনের জন্যে সে নিশ্চয়ই সহকারীর প্রয়োজন অনুভব করত। সেই আদি জৈব-জীবনে কে করবে। কার সহায়তা! তাই বোধহয় সামাজিকভাবে নারী এক বিশেষ পুরুষের প্রতিই গ্ৰীতি রাখত সাহায্য-সহযোগিতা লাভের প্রত্যাশায়। আজকের মতো এত সচেতন কিংবা সূক্ষ্ম না হোক, নারী কিংবা পুরুষ একেবারে দুর্লভ-দুর্লক্ষ্য না হলে সেদিনও হয়তো অবচেতন রুচিরও একটা প্রেরণা ছিল। যদি এ অনুমান সত্য হয়, তা হলে মানতেই হবে যে পুরুষ ও নারীমাত্ৰই অবিচারে একে অপরের কাম্যজন ছিল না। সেদিনও হয়তো পুরুষে পুরুষে বিরোধ-বিবাদের কারণ ঘটত যৌবনবতী স্বাস্থ্যসুন্দর নারীর রূপ-যৌবন উপভোগের দাবি নিয়েই। নারীও হয়তো বুকে পড়ত সবল-সুরূপপৌরষদৃপ্ত পুরুষের প্রতি। তাই আপ্তবাক্যে ‘জরু ও জমি বীরভোগ্যা’।
অতএব নারী-সমস্যাই মনুষ্যজীবনের আদি ও গুরু সমস্যা–এ অনুমান অসঙ্গত নয়। তাই নিয়ন্ত্রিত কামচৰ্চার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান খুঁজেছে আদিসমাজ। আদম-ইভের প্রতিবারের সন্তান হত বিপরীত লিঙ্গের যমজ। তাদের মধ্যে বিয়ে হতে পারত না। আদিম বুনো বর্বর সমাজে যখন ব্যক্তি-বিয়ে চালু হয় নি, তখন যে নির্বিচার সঙ্গমের রেওয়াজ চালু ছিল, তাতে দেখা যায় স্ব-ক্ল্যান সঙ্গম ছিল টেবু বা নিষিদ্ধ। দুই ভিন্ন ক্ল্যানের নারী-পুরুষে হত কামচৰ্চা–এরই নাম যৌথ বিয়ে। দ্ৰৌপদীকে পাঁচ ভাই বিয়ে করলেন বটে, কিন্তু বিরোধ-বিবাদ এড়ানোর জন্যেই ভাইদের মধ্যে পালাভোগ ছিল। আজও হিন্দুদের মধ্যে জ্ঞাতি বিয়ে নিষিদ্ধ। বৌদ্ধ জাতক মতে রাম-সীতা ছিলেন ভাই-বোন। চার ভাইয়ের এক সুন্দরী বোন থাকলে ভ্ৰাতৃবিরোধ ও ভ্রাতৃহন্তা এড়ানো অসম্ভব দেখেই কেবল ভাই-বোনে নয়, বিশেষ বিশেষ নিকটাত্মীয় বিয়ে আদিসমাজেই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তবু আগে যাদের মধ্যে সঙ্গম-সম্পর্ক হতে পারত, পরবর্তীকালে তা অনভিপ্রেত হলেও, আজও ঠাট্টা-মস্কারার মধ্যে সেসম্পর্ক-স্মৃতির রেশ মেলে। উনিশ শতকেও আরাকানে বর্ময় রাজা ‘মা’ ছাড়া সব পিতৃপত্নীর সম্ভোগ-অধিকার পেত উত্তরাধিকার সূত্রেই। কোনো কোনো বুনোমানুষ সসম্পত্তি বিধবা মামিকে পত্নীরূপে পায়। কোথাও কোথাও মামা-ভাগ্নী বিয়ে করতে পারে। অনেক সমাজেই নিজের পিতা-মাতার সন্তান ছাড়া, ভাই-বোন সম্পর্কিত নিকটাত্মীয়দের বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। ইসলামে চৌদ্দ রকম সম্পর্কের আত্মীয়-কুটুম্বে বিয়ে নিষিদ্ধ। যখন মাতৃকেন্দ্রী ক্ল্যান ছিল তখনো হয়তো রানী মৌমাছির মতোই সঙ্গমের কিছু প্ৰাকৃত বা উদ্ভাবিত বিধি-বিধানের বেড়ার বাধা ছিল। নানা কারণে মনে হয়, আদিমানুষের মধ্যেও কামচৰ্চা ছিল কোনোরকমের বিধি-নিয়ন্ত্রিত–তা গোত্রপতির নির্দেশেই হোক কিংবা জাদু-সংস্কারবশেই হোক। মানতেই হবে যে-সমাজে যেদিন ব্যক্তিক বিয়ে চালু হল, সেদিন থেকেই সে-সমাজে আধুনিক সংজ্ঞার পরিবার-পরিজনও গড়ে ওঠে। সভ্যতা-সংস্কৃতির পত্তন সে-মুহূর্ত থেকেই। যথার্থ আত্মীয়, আত্মীয়তা ও আত্মীয়-সমাজ গড়ে ওঠে ব্যক্তিক-বিয়ে ভিত্তি করেই। জারু নিয়ে নিত্য বিবাদের আশঙ্কা এভাবেই ঘুচিল। কিন্তু জমি নিয়ে বিবাদ বৃদ্ধির কারণও বাড়ল।
ব্যক্তিক বিয়ে থেকেই সামাজিক স্বীকৃতির উদ্দেশ্যেই হয়তো বিয়ের উৎসব ও ভোজ চালু হয়। আর নারী যখন প্রবল পুরুষের ভোগ্যা, তখন রূপ-গুণ-যৌবনবতী নারীও বেচা-কেনার পণ্য হল। পণ আভরণ ও নামান্তরে বিক্রি কিংবা ভাড়ামূল্যই। এই দাম্পত্যলব্ধ সন্তানই নন্দন-নন্দিনী। কাজেই তেমন সন্তানের জন্মে আনন্দ-উৎসবের এবং কল্যাণে নানা আচার-সংস্কারের উদ্ভব। অতএব স্থায়ী দাম্পত্য মানবিক বৃত্তিবিকাশের ও মানব-সমাজ-সংহতির একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ও স্তর। দাম্পত্য-ভিত্তিক পরিবার-পরিজন-আত্মীয়-কুটুম্ব্বের পারস্পরিক প্রীতিপ্রসূত বিশ্বাস-ভরসা ও নির্ভরতা এবং পারস্পরিক দায়িত্ব-চেতনা ও কর্তব্য বুদ্ধি মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-রেওয়াজ, প্ৰথা-প্রতিষ্ঠান ও আচার-আচরণকে মিলনমুখী ও কল্যাণধৰ্মী করতে সহায়তা করেছে। সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশে এসবের প্রভাব গভীর ও ব্যাপক হয়েছিল। অবাধ কামচৰ্চা শুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করেছিল বলেই হয়তো অবৈধ কামচৰ্চা আজও গুরুতর পাপ, লজ্জা, নিন্দা ও শাস্তির বিষয়। বন্ধু-সখী মহলে এমনকি দাম্পত্যজীবনেও রতিক্রিয়ার আলোচনা অশ্লীল, অনভিপ্রেত ও লজ্জাকর।
ঘুমে-অচেতন মানুষ স্বপ্ন দেখে। তা থেকেই সে সহজাত বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছে, দেহ ও চৈতন্য পৃথক সত্তা। তা ছাড়া স্বপ্নে মৃতমানুষকেও সে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পায়, সে-কায়াধারী মৃত্যমানুষ অশনে-বসনে-আসনে-কথায়-কাজে অবিকল জীবিত মানুষের মতো। এর থেকেই মানুষের ধারণা ও নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছে যে আত্মা নামে জীবচৈতন্য অবিনশ্বর-অমর। কাজেই আনুষঙ্গিকভাবে পরলোক-প্রেতলোক-আত্মালোক, দেবলোক, স্বৰ্গ-নরকলোকে কল্পনা করা ও সেগুলোর অস্তিত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা অবশ্যম্ভাবী ও আবশ্যিক হয়ে পড়ে। বিদেহী আত্মার অমরত্বে আস্থা রাখলে সে-সম্পর্কিত চিন্তাচেতনা এড়ানো যায় না। পারলৌকিক দায়িত্ব-কর্তব্যও বর্তায় এবং তাতে দেহ-মনের কাজ বাড়ে। নিজের জন্যে তো বটেই, মৃত আত্মীয়-স্বজনের জন্যেও কিছু করতে হয়। জীবিতমাত্রেই খাদ্য চায়, কাজেই জীবিত আত্মারও খাদ্য দরকার। এর জন্যে খাদ্য পানীয় প্রভৃতি জীবিতের যাবতীয় আবশ্যিক বস্তুর ব্যবস্থা করতে হয়। আবার আত্মা যেহেতু অমর এবং কায়াহীন আত্মার স্থিতি এখনো ধারণাতীত, সেহেতু মমি করেও দেহ রাখার ব্যবস্থা। মৃতের সৎকার, প্রার্থনা, শ্ৰাদ্ধ, ভোজ, মমি, পিণ্ডি, জানাজা, জেয়ারত, পিতৃপুরুষ পূজা, প্ৰেত পূজা, শোকপ্রকাশ প্রভৃতি আচার-প্ৰথা-পদ্ধতি তাই স্বরূপে কিংবা রূপান্তরে আদিম এবং সর্বজনীন। শিব কেউ কবর দেয়, কেউ পোড়ায়, কেউ শকুনকে বিলায়, কেউ ভাসায়। প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগে বিলুপ্ত (১৬০,০০০ বছর আগে উদ্ভূত এবং ৪০,০০০ বছর আগে বিলুপ্ত) Neanderthalers জাতীয় আদিমানুষেরা পশ্চিম এশিয়ায় ও উত্তর য়ূরোপে বাস করত। তাদের মধ্যে প্ৰাণিপূজা, জাদু ও মৃতের শাস্ত্রীয় সৎকারের রীতি চালু ছিল। শিকার-সহায় ‘ভালুক’ টোটেমরূপে অবলম্বন ছিল—পরে নব্যপোলীয় যুগের য়ূরোপে দেখি ষাঁড়, ইরাক-ইরান-মহেনজোদারোতেও পাই ষাঁড়। উত্তর ও পশ্চিম য়ূরোপে ও সাইবেরিয়ায় টোটেমরূপে পিতৃপুরুষ প্রতীক। ‘ভালুক’ পূজার রেওয়াজ ছিল। স্মৃতিরক্ষার জন্যে চিতায়-কবরে সৌধ রচনাদি নানা ব্যবস্থা আজও অবিরল।
আবার প্রত্যক্ষ বাস্তব ঐহিক জীবন থেকে কাল্পনিক পারিত্রিক জীবন কখনো অধিক কাম্য হতে পারে না। তাই মৃত্যু ও মৃত দুই-ই বিনাশপ্রতীক ও ভীতিপ্রদ। ন্যায়-অন্যায়, সুকৰ্ম-দুষ্কর্ম, শাপ-বর ও পাপ-পুণ্য চেতনা ক্ৰমে সেই ভয় বৃদ্ধি করেছে। আগে থেকেই তো জগৎ ও জীবন-নিয়ন্ত্রী একটা বা একাধিক সার্বভৌম অদৃশ্য-অলৌকিক শক্তির ধারণা ছিলই, শাস্ত্রীয় যুগে তা তত্ত্ব-দর্শনের বিষয় হয়ে সুসামঞ্জস, সুসংহত, সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অমিত শক্তির আধার এবং দান-দয়া ও দণ্ড-মুণ্ডের মালিকরুপে চিরন্তন স্থিতি পেল। কাজেই মানুষের জন্ম-জীবন-জীবিকা, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ প্রভৃতির মালিক, নিয়ন্তা ও বিচারকরূপী স্রষ্টা বিধাতাও উপাস্য হলেন। তাকে বা তাদের এড়ানো সরানো চলে না বলেই তাঁর বা তাদের শাসন-লালন মানতেই হয়। তাই সুখে-দুঃখে, রোগেশোকে, লাভে-ক্ষতিতে আনুগত্য অবিচল রাখতে হয়-বিদ্রোহ কেবল বিপদ-যন্ত্রণাই বৃদ্ধি করবে–এ বিশ্বাস মানুষের জীবনে এত গভীর যে তার প্রভাবে কোনো আস্তিক মানুষই আত্মিক শক্তিতে আস্থা রেখে কোনো কাজি সাফল্য সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয়ী হতে পারে না। তাই আস্তিক মানুষ মাত্রেই দেবনির্ভর। ধর্মের মূল্যের, গুরুত্বের ও ধর্মে আনুগত্যের কারণ এ-ই। গোত্রীয় মানুষকে মতবাদভিত্তিক ঐক্য ও সংহতি দান করে ধর্মমত সেইদিন দুশমন ও দূরের মানুষ নিয়ে বৃহত্তর সমাজ ও সম্প্রদায় গঠনের কারণ হয়েছিল এবং মনুষ্য-সভ্যতার ক্রমোন্নতি ত্বরান্বিত করেছিল। গোত্রীয় জীবনধারার অবসানের পরেও পশুপালন এবং কৃষিকাৰ্য দুটোই সমাজ-বিকাশের বিশেষ স্তরে যৌথ প্ৰয়াস ও কর্মসাপেক্ষ ছিল। জীবিকা উৎপাদন ও বণ্টন যখন জনবৃদ্ধির সঙ্গে আনুপাতিক সমতা রক্ষায় ব্যর্থ হয় তখনই শক্তিবৈষম্য ও জীবিকা সম্পদে হ্রাস-বৃদ্ধি প্রকট হয়ে ওঠে। কায়িক শক্তিতে-বুদ্ধিতে-কৌশলে ও সম্পদে যে দুর্বল, সে-ই প্রবল দুর্জনের দীেরাত্ম্যের শিকার হল। জীবিকার জন্যেই বাহুবল, ধনবল, বুদ্ধিবল যার বা যাদের ছিল, তারাই অনন্যেপায় দুর্বলকে বশ বা দাস করতে পারল। দাসদের খাটিয়ে মালিকের পক্ষে তার পশুর বৃহৎ পাল পোষণ ও চাষের জমির সীমা বৃদ্ধি করা সম্ভব হল। এমনি করে ধনী আরো ধনী ও গরিবরা দাসে পরিণত হচ্ছিল; পরিণামে তা-ই সামন্তসমাজের উদ্ভব ঘটোল। গোত্রীয় জীবনের অবসান-মুহূর্তে যদি বিনিময় প্রতীক মুদ্রা চালু থাকত, তা হলে হয়তো দাসপ্রথা এমন সর্বব্যাপী ও দীর্ঘস্থায়ী হত না। কারণ সে-ক্ষেত্রে এখনকার মতো মুদ্ৰামূল্যেই মজুর মিলত।
ক্রমবিকাশের ধারায় যেখানে যেখানে জীবিকার সৃষ্টি ও অর্জনপদ্ধতি বৈচিত্ৰ্য লাভ করেছিল এবং জীবনধারণে আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় কিংবা স্বাচ্ছন্দ্যসামগ্ৰী বা বিলাসব্যাসন বস্তু নব নব আবিষ্কারে ও উদ্ভাবনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল; তখন সেই বহু ও বিচিত্র দ্রব্য ও পণ্য নির্মাণে, উৎপাদনে কিংবা অন্যপ্রকার উপযোগ সৃষ্টির কাজে বর্ধিত হারে শ্রমশক্তি বিনিয়োগ আবশ্যিক হয়ে ওঠে। অর্থাৎকৃষি-শিল্প-বাণিজ্য এবং ধোয়া-মােছা-কাটা ছাড়াও ঘর-ঘাট, বাট-মাঠ-মন্দির নির্মাণ, পূজা-শিন্নি, পঠন-পাঠন, রোগ-নিদান-চিকিৎসা-শুশ্রুষা প্রভৃতি হাজারো রকম প্রাত্যহিক কর্তব্য ও কাজ দেখা দিচ্ছিল। তখন দায়িত্ব ও কর্মভাগ আবশ্যিক হল। ক্ৰমে উচ্চ-তুচ্ছ, লঘু-গুরু, শক্ত-সহজ, কুশল-অকুশল, প্রয়োজনবিলাস ও ক্ষয়-অর্জন ভেদে শ্রমিকেরও ধন-মান-যশও গুরুত্বভেদ হল, এবং পরিণামে পৃথিবীব্যাপী সর্বত্র ধর্মভেদে জািত-জন্ম-মান-বৰ্ণভেদ দেখা দিল। তাই দুনিয়া ব্যাপী সর্বত্র মানুষের সমাজে নানাপ্রকারের বৈষম্য-বিভেদ-বিরোধ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত-পীড়নপোষণ-শাসন-শোষণ আজ অবধি রয়েছে, কেবল তা কোথাও গণমানবের অজ্ঞতাঅসহায়তার দরুন গুরু, কোথাও-বা নানা কারণে লঘু। সেটার আধুনিক নাম শ্রেণীদ্বন্দ্ব। সুবিধাভোগী ধনী-মানীরা স্ব-স্বার্থেই স্রষ্টা, শাস্ত্র ও সমাজের দোহাই দিয়ে সেই বৈষম্যকেই চিরন্তন করে রাখতে চেয়েছে, এখনো চায়। ফলে যারা পীড়ক-শোষক তারাও যেমন এর মধ্যে অন্যায়-অবিচার দেখে না, যারা পীড়িত-শোষিত তারাও ঐ বঞ্চনা দুর্ভোগকে অদৃষ্ট বলেই মানে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এদের জীবন-মনন চিত্র স্বল্প কথায় সঠিক অভিব্যক্ত :
স্ফীতকায় অপমান
অক্ষামের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া, বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার।…
ওই যে দাড়ায়ে নত শিরে
মূক সবে, স্নান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী, স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চ’লে মন্দ গতি যতক্ষণ থাকে প্ৰাণ তার–
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি
নাহি ভৎসে অদৃষ্টরে; নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনো মতে কষ্ট-ক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।
সাহিত্যও শিল্প–জীবন-শিল্প। জগৎ-পরিবেশে জীবিকা-সম্পূক্ত এবং মনন ও অনুভবপুষ্ট জীবনের উদ্ভাস, প্রতিচ্ছবি কিংবা অনুকৃতিই সাহিত্য। অতএব সাহিত্য হচ্ছে জগৎ ও জীবিকা-সম্পৃক্ত জীবনানুকৃতি। জীবনে যা ঘটে, যা চাওয়ার ও পাওয়ার, যা সম্ভব ও সম্ভাব্য, যা প্ৰাপ্য ও প্রত্যাশার, যা অনভিপ্রেত ও পরিহারযোগ্য, তার সবটাই পাই সাহিত্যে। তাই সুখ-দুঃখ-আনন্দ-যন্ত্রণা, সম্পদ-সমস্যা, স্নেহ-প্ৰীতি-প্ৰেম, ঈর্ষাঅসূয়া-রিরংসা, লোভ-ক্ষোভ-তেজ-তিতিক্ষা, সাফল্য-ব্যর্থতা, রাগ-বিরাগ প্রভৃতি ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া প্রভাবিত জীবনের চিত্রাঙ্কনই সাহিত্যকর্ম। জীবিকা-সম্পৃক্ত জীবনাচরণই তথা ভাব-চিন্তা-কর্মে ও আচরণে জীবনের সার্বক্ষণিক অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। অন্য কথায়, মনুষ্যজীবনের অর্জিত স্বভাবের সার্বিক অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। তবু সূক্ষ্ম, পরিস্রুত ও সুন্দর-শোভন অভিব্যক্তিকেই আমরা বিশেষভাবে সংস্কৃতি বলি। কাজেই সংস্কৃতি ভাবচিন্তা-কর্মে ও আচরণে প্রকটিত জীবনেরই লাবণ্য। এই তাৎপর্যে সাহিত্যও সংস্কৃতিরই প্রসূন। সাহিত্যেও সংস্কৃতিরই প্রকাশ। প্ৰাণধর্মের তাগিদেই জীবন সর্বক্ষণ প্রকাশ ও বিকাশপ্ৰবণ-নানা ভাবি-চিন্তা-কর্মে-আচরণে জীবনের বাস্তব ও মানস অভিব্যক্তি ঘটছে। অর্থাৎ তার সৃষ্ট ভাব-জগৎ, তার আচারিক ব্যবহারিক জীবনাচরণপদ্ধতি এবং তার নির্মিত ও ব্যবহৃত বস্তু-জগৎ তার সংস্কৃতির নিদর্শন। অতএব জীবনধারণের ও উপভোগের প্রয়াসপ্রসূত মানবক্রিয়ামাত্রই সংস্কৃতি। তাই সামাজিক জীবনের আচার-ব্যবহার, রীতিরেওয়াজ, প্ৰথা-প্রতিষ্ঠান, নীতি-আদৰ্শ, উৎসব-পার্বণ থেকে ব্যবহারিক জীবনের ঘরঘাট-হাট-বাট, তৈজস-আসবাব, অশন-বসন-আসন কিংবা মানবজীবনের দারু-চারুকারুশিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত, স্থাপত্য-ভাস্কৰ্য, ইতিহাস-দৰ্শন-গণিত-বিজ্ঞান সবটাই কোনো বিশেষ দেশ-কালের ও গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সামাজিক, সার্বিক ও সামগ্রিক সংস্কৃতি এবং যুগপৎ সাংস্কৃতিক নিদৰ্শন-যাকে বলা চলে বিশিষ্ট দ্বৈতাদ্বৈত। সবটাই চলমান জীবনে তার অনুভব, মনন ও ব্যবহারিক প্রয়োজনবোধের প্রসূন।
যাহোক, আমাদের সংস্কৃতির কোথাও মর্মে, কোথাও-বা অবয়বে আদিম সংস্কৃতি, লোক-সংস্কৃতি ও অনুকৃত সংস্কৃতির ছাপ দুৰ্লক্ষ্য নয়। ভাব-চিন্তাকৃতির যে-অংশ হিতকর ও গৌরবের তা-ই যেমন ঐতিহ্য বলে খ্যাত, তেমনি জীবনচর্যার যে-অংশ সুন্দরশোভন ও কল্যাণকর তা-ই সংস্কৃতি, বাদবাকি কৃতি বা আচারমাত্র। এ তীেলে যাঁরা মাপেন তাদের কাছে জীবনচর্যার কিংবা জীবনযাত্রার সবটাই সংস্কৃতি নয়। তাঁদের সংজ্ঞায় নগরবিহীন সভ্যতাও নেই। আমাদের ধারণায় সংস্কৃতির উৎকর্ষে সভ্যতার উদ্ভব। সংস্কৃতির বস্তুগত ও মানসসম্মুত অবদানপুষ্ট জীবনপদ্ধতির সার্বিক ও সামগ্রিক উত্তরাধিকারই সভ্যতা।
২
মধ্যযুগের মুসলিমরচিত বাঙলাসাহিত্যে বিধৃত সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন আমরা এ-গ্রন্থে সংগ্রহ ও সংকলন করেছি। বিষয়ানুসারে গুচ্ছবদ্ধ করলে স্থান, কাল ও কবি গুরুত্ব হারাত, তাই সে চেষ্টা করি নি।
কোনো দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দান অতি বড় জ্ঞানী-মনীষী গবেষকের পক্ষেও হয়তো সম্ভব নয়। দেশে-কালে, বিশ্বাসে-সংস্কারে, আচারে-আচরণে সামাজিক মানুষ বিচিত্ৰভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কারণ সমাজ-সদস্য হলেও মানুষের ব্যক্তিক ভাব-চিন্তা-রুচি-আচরণের ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য কিছুটা থাকেই এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষকে অনুকরণ করার প্রবণতা অন্য মানুষের সাধারণ স্বভাব। এতে অতি মন্থর গতিতে এবং অলক্ষ্যে সামাজিক আচার-আচরণ, প্ৰথা-পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান বদলায়।
বহুমুখী মানস-শিকড় দিয়ে মানুষ আহরণ করে জীবনরস। তার মন-মননের পরতে পরতে রয়েছে হাজারো বছরের সঞ্চিত নানা সম্পদ। কখন কোন বিশ্বাস, সংস্কার, আদর্শ বা অভিপ্ৰায়ের প্রেরণায় মানুষের কোন ভাব, চিন্তা অভিব্যক্তি পাচ্ছে, তা সহসা বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য। তা ছাড়া সমকালের সব পরিবেশ, ঘটনা ও আচার সব মানুষের মনে ছায়াপাত করে না। মানস-গড়ন, রুচি, প্রবণতা, প্রয়োজন-বুদ্ধি প্রভৃতি থেকেই জাগে কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা-তাই কেউ ক্রীড়া-জগতে, কেউ বাণিজ্য-জগতে, কেউ রাজনীতির ক্ষেত্রে মানস-বিচরণ করে; কেউ কৃষি-উৎপাদনে, কেউ শিল্প-উৎপাদনে হ্রাস-বৃদ্ধি-বৈচিত্ৰ্য নিয়ে মাথা ঘামায়। কেউ সাহিত্যে, কেউ সঙ্গীতে, কেউ চিত্রকলায়, কেউ নৃত্যকলায়, কেউ সংস্কৃতিতে, কেউ নৃতত্ত্বে, কেউ সমাজতত্ত্বে, কেউ ধনবিদ্যায়, কেউ-বা বিজ্ঞানে, কেউ-বা দর্শনে, কেউ ইতিহাসে, কেউ গণিতে, কেউ জ্যোতির্বিদ্যায়, কেউ জীব-উদ্ভিদবিজ্ঞানে আগ্রহী। এজন্যেই কোনো ভ্রমণবৃত্তান্তে, কোনো জীবনীগ্রন্থে, কোনো ইতিহাসগ্রন্থে কোনো দেশের বিশেষ স্থানের ও কালের জীবনযাত্রার, কর্ম ও নর্ম প্রবাহের, ধন-ধর্ম-আচার-আচরণ-সংস্কৃতির একটা সার্বিক বর্ণনা মেলে না। কেউ ধর্মের কথা, কেউ বাজারাদরের কথা, কেউ খাদ্যবস্তু ও রান্নার কথা, কেউ খেলাধুলার কথা, কেউ তরুলতা-ফুল-ফল-মূলের কথা, কেউ পশু-পাখির বর্ণনা, কেউ উৎসব-পার্বণের কথা, কেউ শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্যের বর্ণনা রেখে গেছেন বা রাখেন বটে, কিন্তু দেশকালগত সামষ্টিক তথা সামাজিক জীবনধারার পূর্ণাঙ্গ চিত্র দান কোনো একক জ্ঞানী-মনীষীপর্যটক, ঔপন্যাসিক, কাব্যকর বা ইতিবৃত্তকারের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। আলবেরুনী-আবুল ফজলরা তাই চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়েছেন।
জীবনের সর্বতোমুখী চেতনা কোনো একক মানুষের চিন্তা, কর্ম কিংবা আচরণে ধরা দেয় না। এ-যুগেও পরিবেশ কিংবা জীবনসচেতন কোনো মহৎকথাশিল্পী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববিদ কিংবা রাজনীতিকের রচনায় সমকালীন জীবনের ও ঘটনার সব খবর মেলে না। মনের প্রবণতা অনুসারে তুচ্ছ ঘটনাও কারো কাছে গুরুত্ব পায়, আবার গুরুতর বিষয়ও পায় অবহেলা। তা ছাড়া দৃষ্টি আর বোধেও থাকে ভঙ্গি ও মাত্রাভেদ। জগৎ ও জীবনকে সর্বজনীন দৃষ্টি ও বোধ দিয়ে কেউ প্রত্যক্ষ করতেও পারে না। বিদ্যা-বুদ্ধি, বোধি-প্ৰজ্ঞ, বিশ্বাস-সংস্কার, আদর্শ-নীতিজ্ঞান প্রভৃতি নানাকিছুর প্রভাবে মানুষের দৃষ্টি ও বোধ নিয়ন্ত্রিত। কেউ অনপেক্ষ বা নিরপেক্ষ নয়, সবারই রয়েছে রঙিন চশমা, আপেক্ষিক বোধ ও বিচারপদ্ধতি।
আমাদের আলোচিত পাঁচালি কাব্যগুলো মুখ্যত রাজপুত্র-রাজকন্যার কাহিনী। সেসূত্রে উজির-কোটাল-সওদাগরের কথাও কিছু রয়েছে। ক্বচিৎ মালিনী-পরিচারিকার কথাও মেলে। আর অশুভ প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে উপস্থিত রয়েছে দেও-দৈত্য-রাক্ষস, ক্বচিৎ সাপ-বাঘ-পাখি। কারণ, এ হচ্ছে সামন্তযুগের সাহিত্য। তখনো ব্যক্তিমানুষ সম্পর্কে কৌতুহল জাগে নি! মনোসমীক্ষণরীতি তখনো অজ্ঞাত। স্কুল চেতনায় আকাশচারিতাতেই চরম দার্শনিকতা ও কল্পনা-বিলাসিতা সীমিত। দেবলোক ছেড়ে সবেমাত্ৰ মর্ত্যে নেমেছে মানবকল্পনা ও কৌতুহল। বাহ্য জীকই কৌতুহল জাগার আর কৌতুহল নিবৃত্তির অবলম্বন। গোত্রীয় ঐক্য, আঞ্চলিক সংগতি, ধমীয় একাত্মতা এবং রাষ্ট্ৰীয় চৌহদির ভিত্তিতে সমাজ রচিত এবং জীবন নিয়ন্ত্রিত। প্ৰবল দুরাত্মাই শাসন-শোষণ ও পোষণ-পেষণের মালিক। তখন রাজা-শাসক-সামন্তরূপ মালিক-প্রভুর ঐশ্বৰ্য, সুখ, বিলাস, মান-যশ, প্রভাব, প্ৰতাপ, প্রতিপত্তিই শাসিত জনগণের সুখ-যশ-মান ও ঐশ্বর্যের প্রতীক ও প্রতিভূ। তাই রাজা ও রাজপুত্ৰই সাহিত্যে নায়ক। সে-সমাজে ছিল ছিটেফোঁটা কৃপাভোগী মন্ত্রিপুত্র ও সওদাগর, দুরাত্মা-দুৰ্বত্ত কোটাল আর দর্প ও দাপটপ্রবণ বিলাসী সামন্তমানস। এবং যশ-মানপ্রতাপলিন্দু ভোগ-প্রিয় ছিল সে-জীবন। তাই বাহুবল, মনোবল ও বিলাসবাঞ্ছাই সেজীবনের আদর্শ, সংগ্রামশীলতা ও বিপদের মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠাই সোঁ-জীবনের ব্ৰত এবং ভোগই লক্ষ্য। এককথায় সংঘাতময় বিচিত্র দ্বান্দ্ৰিক জীবনের উল্লাসই সাধারণত সামন্তযুগের সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত।
সে-কালে সাধারণের কাছে ভবনের বাইরের ভুবন ছিল অজ্ঞাত। স্বল্প চাহিদার অজ্ঞ মানুষের গ্রামীণজীবন ছিল স্বনির্ভরতার প্রতীক। কুয়োর মাছের মতোই সংকীর্ণ পরিসরে তাদের কায়িক জীবন হত আবর্তিত। নানা সূত্রে শোনা যেত মহাসমুদ্রের কল্লোল ও তার তটস্থ দিগন্তপারের পৃথিবীর কথাও। কল্পভ্রমণে মিটিয়ে নিত বিশাল পৃথিবী পরিভ্রমণের সােধ। তাই অলৌকিক অস্বাভাবিক-ভৌতিক-দৈবিক চেতনাই ছিল তাদের সম্বল। ঝঞা-সংকুল সমুদ্রই ছিল দূরযাত্রার একমাত্র পথ। ডাক কিংবা তারবেতারের ব্যবস্থাও ছিল না। তাই স্বপ্ন, ছবি ও পক্ষীর দৌত্যে জগত পৃথিবীর নাম-না–জানা প্রান্তের রাজকন্যার প্রতি প্ৰেম। তাই জাদুতে ও দৈবশক্তিতে আস্থা রাখতেই হয়েছে। দৈত্য-রাক্ষস যেমন হয়েছে অরি, তেমনি কখনো কখনো পশু-পাখি হয়েছে নায়কের সহায়। প্রকৃতির সঙ্গে মননের ও হৃদয়ের যোগ হয়েছে ঘনিষ্ঠ।
সে-যুগে কিছুই সহজে পরিবর্তিত হত না। যান্ত্রিক যানবাহনের অভাবে তখনো পৃথিবীর আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ঘোচে নি। বিভিন্ন অঞ্চলের ও দেশের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধ তখন সহজে গড়ে উঠত না। তাই নতুন ভাব-চিন্তা-কর্ম কিংবা বস্তুর আবিষ্কার ও উপযোগ উদ্ভাবন ছিল মন্থর। জ্ঞান-বিদ্যা-মননেরও এমন বিচিত্র ও বহুধা বিকাশ-বিস্তার হত না। তাই পাঁচশ বছরেও সমাজে আচারে চিন্তায় কিং ব্যবহারসামগ্রীর লক্ষণীয় পরিবর্তন সম্ভব ছিল না। শাস্ত্ৰ-শাসিত জীবনে-সমাজে স্বাধীন চিন্তার অবাধ সুযোগ ছিল না, সমাজানুগত্যও ছিল ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক। ফলে শাস্ত্রীয় ও সামাজিক শাসনের কঠোরতা সমাজ-চিন্তা ও আচারকে রেখেছিল স্থিতিশীল তথা গতিহীন ও অপরিবর্তিত। এজন্যে কালিক ব্যবধানে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে পার্থক্য দেখা যেত সামান্য।
যাতায়াতের সহজ ব্যবস্থা ছিল না বলে একই দেশে অভিন্ন শাস্ত্রীয় সমাজের মধ্যেও অঞ্চল-ভেদে সামাজিক-সাংস্কারিক-আচারিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকত। যন্ত্রযানের বদৌলতে এ-যুগে পৃথিবী অখণ্ড, সংহত ও ক্ষুদ্র হয়ে গেছে। পৃথিবীব্যাপী মানুষ পারস্পরিক অনুকৃতির মাধ্যমে অথবা উন্নতদের অনুকৃতির ফলে, ঘরোয়া জীবনযাত্রায় তৈজসে-আসবাবে, আহার্যে-আচারে, অস্ত্রে-বস্ত্রে, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ও সামাজিক আদব-কায়দায় প্রায় অভিন্ন হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া ভাব-চিন্তা-আদর্শে, বিদ্যা-বিজ্ঞানে, কৃৎকৌশলে ও যন্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে পৃথিবীর মানুষ আজ স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে।
সে-যুগেও অবশ্য স্বল্পমাত্রার বাণিজ্যিক, পরাক্রান্ত জাতির সাম্রাজ্যিক এবং শাস্ত্রীয় সম্পর্ক বিভিন্ন দূরাঞ্চলের মানুষের সঙ্গে গড়ে উঠত। সে-সূত্রে বিদেশী বিজাতি বিভাষী বিধমীর সাংস্কৃতিক, ভাষিক, প্রশাসনিক ও আচারিক প্রভাব স্বীকার করতেই হত। কিন্তু যন্ত্রবিজ্ঞানের বিকাশ ছিল না বলে সে-প্রভাব এ-কালের পর-প্রভাবের মতো তেমন ত্বরায় প্রকট হয়ে উঠত না-সর্বজনীন বা সর্বব্যাপীও হত না।
৩
এ কারণেই দেশজ মুসলমানের মধ্যে বৌদ্ধ-হিন্দু পিতৃপুরুষের আচার-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, তত্ত্ব-চেতনা ও মনন-ধারা থেকে গিয়েছিল। নিরক্ষর অজ্ঞ মানুষ সুফি-দরবেশের ব্যক্তিত্ব ও কেরামত প্রভাবে ইসলামে দীক্ষিত হল বটে কিন্তু প্রতিবেশ ছিল প্রতিকূল। শাস্ত্রটি ছিল দূর দেশের এবং অবোধ্য ভাষায়। তার আচারিক কিংবা তাত্ত্বিক আবহছিল না। এদেশে। তাই ব্যবহারিক ও মানস-চৰ্যায় বৌদ্ধ-হিন্দুর আচার-সংস্কারই রইল প্ৰবল। দেশী মুসলমানের এই ধর্মাচরণকে বুঝবার সুবিধের জন্যে বিদ্বানেরা চিহ্নিত করেছেন ‘লৌকিক ইসলাম’ নামে। উল্লেখ্য যে বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলিম বাঙালি নির্বিশেষের মর্মমূলে রয়েছে সেই ঐতিহ্যিক কায়াসাধন তত্ত্ব। যোগ্যতান্ত্রিক বামাচারী কিংবা বামাবর্জিত সাধনা বাঙালির মজ্জাগত ধর্মসাধনা | রজঃ-বীৰ্য সংযত, ধারণ ও উর্ধায়ন করেই চলে সাধনা। কৃষ্ণের কালীয় নাগ দমনও ঐ কাল কামবিষ দমনেরই রূপক। চন্দ্রাণীর সর্পদংশনও ঐ কামবিষের প্রতীক।
এ-সূত্রে এ-ও উল্লেখ্য যে সংখ্যালঘু মানুষ শাসক, সামন্ত কিংবা প্ৰভু হলেও সামাজিক-বৈষয়িক জীবনে সংখ্যাগুরুর প্রভাব এড়াতে পারে না। সংখ্যালঘু যে আচারেসংস্কারে, রুচি-সংস্কৃতিতে কিংবা ভাষায় স্বাতন্ত্র্য ও স্ববৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে পারে না, তার দৃষ্টান্ত রয়েছে ভারতের শাসক তুর্কি-মুঘলের (প্রথম যুগের ইংরেজদেরও) জীবনে। সংখ্যাগুরুদের প্রভাবে তারা তাদের ভাষা-খাদ্য, আচার-সংস্কার ও জীবন-ধারণপদ্ধতির প্রায় সবই হারিয়েছিল। অবশ্য প্রভুকে অনুকরণ করার শাসিতসুলভ হীনমন্যতা-প্রসূত আগ্রহের ফলে শাসকদেরও খাদ্যের, পোশাকের ও দরবারি ভাষার এবং বস্তুসংলগ্ন ও মানস-সভূত সংস্কৃতিও কিছুটা রয়ে গেল।
দৈশিক প্রতিবেশে দেশজ মুসলমান মাতৃভাষায় দৈশিক রীতি-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের অনুসরণে সাহিত্য-চৰ্চা করেছেন; এজন্যে তাদের রচনায় দেশী আবহই বিশেষ করে বর্তমান। আগেই বলেছি, যে-ধর্মশাস্ত্রের তারা অনুসারী, তাতে পুরো আনুগত্য রক্ষা করার মতো সে-শাস্ত্ৰ জানা-বোঝা বা শোনার সুযোগ-সুবিধে তাদের ছিল না। তাই স্বশস্ত্রীয় অপূর্ণ জ্ঞানের শূন্যতা পূরণ করেছে তারা দেশী বৌদ্ধ-হিন্দু সাংখ্য-যোগ-তন্ত্র, দেহতত্ত্ব, রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণকাহিনী ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা দিয়ে। ফলে মুসলিম শাস্ত্ৰকথায়ও দেশী পুরাণ ও সংস্কারের প্রভাব পড়েছে। আর মুসলিম অধ্যাত্মতত্ত্বে ও মারফত-মরমিয়া সাধনায় যোগতন্ত্র ও বাউল প্রভাব প্রকট। তা ছাড়া বৌদ্ধ গুরুবাদ তথা পিরবাদ, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ বা সৰ্বেশ্বরবাদও নিদ্বিধায় গৃহীত হয়েছে। তাই বৌদ্ধ-হিন্দু বিষয়ভিত্তিক (নাথ-সাহিত্য, গোরক্ষাবিজয়, হরগৌরীসম্বাদ, রাধাকৃষ্ণ, যোগতত্ত্ব) সাহিত্য-রচনায় কিংবা অধ্যাত্মতত্ত্ববৰ্ণনায় মুসলিম তাত্ত্বিক-দার্শনিকঅধ্যাত্মবাদীর উৎসাহ লক্ষণীয়।
মুসলিম-রচিত বাঙলাসাহিত্যের প্রায় সবটাই হিন্দি-আওধি-ফারসি-আরবি গ্রন্থের কায়িক, ছায়িক বা ভাবিক অনুবাদ। অনুবাদকরা সর্বত্র ইচ্ছেমতো গ্ৰহণ, বর্জন ও সংযোজনের স্বাধীনতা রক্ষা করেছেন। প্ৰণয়োপাখ্যানগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে অমুসলিম কাহিনী হলেও মুসলিম-কবির নীতিবোধের বা সামাজিক রীতির পরিপন্থি ছিল না। দেবপূজাদির কথা ছাড়া অন্য ব্যাপারে রীতি-নীতি ও সংস্কারে হিন্দু-মুসলমানে পার্থক্য ছিল না হয়তো। বিদেশী-বিভাষা থেকে অনুবাদ হলেও নৈতিক সামাজিক আচার-আচরণেদৈশিক আবহ ও সংস্কার রক্ষিত হয়েছে। আবার হিন্দু নায়ক-নায়িকার কাহিনী বর্ণনায় কবি অজ্ঞাতে মুসলিম রীতি-নীতির প্রয়োগ করেছেন, কিংবা সুদূর অতীতের প্রথা প্রয়োগ করেছেন–যেমন লোরকরাজ কর্তৃক বামন-বউ চন্দ্ৰাণীহরণ ও স্ত্রীরূপে গ্রহণ।
এখনকার দিনে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ-সুরুচি, দেশপ্ৰেম,মানবগ্ৰীতি, মানবতা, সুনাগরিকতা প্রভৃতির দোহাই দিয়ে মানুষের বিবেকবুদ্ধি, নীতিবোধ ও সদাচারবোধ জাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়, নিয়ন্ত্রিত হয়ে নৈতিক চরিত্র।
সে-যুগে মানুষের জীবন ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। তাই মানুষের নৈতিক চেতনার মুখ্য উৎসও ছিল ধর্মবিধি ও শাস্ত্রানুশাসন। ফলে নৈতিক জীবনবোধ জাগানোর লক্ষ্যে রচিত হত সাহিত্য। নীতিকথা-নিরপেক্ষ কাব্য-উপাখ্যান কিংবা শাস্ত্ৰ-নিরপেক্ষ সাহিত্যিক রচনা ছিল বিরল প্ৰয়াসে সীমিত। অবশ্য ডাক-খনার আপ্তবাক্য, চাণক্য-শ্লোক ও প্রবচনাদির মতো বিচ্ছিন্ন তত্ত্বকথা বা জ্ঞানগর্ভ বাণী ছিল গুরুত্বে ও প্রভাবে ধর্মশাস্ত্রেরই প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু এগুলোও ছিল ধর্মশাস্ত্রের মতো অদৃশ্য অপার্থিব বিশ্বাস-সংস্কারের প্রলেপে আবৃত।
পূৰ্বপুরুষের বৌদ্ধ-ঐতিহ্যের ধারক বাঙালি মুসলিমরা আল্লাহর পরিভাষা হিসেবে ধর্ম (সগীর ও দৌলত উজীরের কাব্যে), নাথ, নিরঞ্জন এবং হিন্দু-ঐতিহ্যের প্রভাবে করতার (কর্তার) ব্যবহার করেছেন। আরবের আল্লাহ ইরানে হয়েছেন “খুদা’ এবং ইসলামের মৌলিক তত্ত্বপ্রতীক শব্দগুলোও ইরানি রূপান্তর পেয়েছে। ফলে সালাৎ, সিয়াম, মলক, জন্নাৎ জাহান্নাম, নবি-রসুল যথাক্রমে নামাজ, রোজা, ফেরেস্তা, বেহেস্ত, দোজখ, পয়গম্বর হয়েছে। ফারসি দরবরি-ভাষা ছিল বলেই তার প্রভাবে ক্রমে ফারসি প্ৰতিশব্দগুলো জনপ্রিয় হয় মুসলিম-সমাজে। দেশজ মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলায়ও সংস্কারে-বিশ্বাসে, ঐতিহ্যে ও পুরাণে গড়ে উঠেছে দেশী শব্দের বাকপ্রতিমা। তাই মুসলিম-রচিত সাহিত্যের ভাষায়ভঙ্গিতে, উপমাদি-অলঙ্কারে, বাকপ্রতিমা নির্মাণে মুখ্যত দেশী উপাদান-উপকরণ, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভৃতিই বক্তব্য প্রকাশের বাহন হয়েছে।
৪
প্ৰেম সম্পর্কে ইসলামে তেমন কোনো স্পষ্ট শাস্ত্রীয় নির্দেশ নেই। মুসলিম-কবি প্রণয়কাহিনী রচনা করতে গিয়ে রূপজ প্রেম তথা দৰ্শন-শ্রবণজাত পূর্বরাগ-অনুরাগ দিয়ে বর্ণনা শুরু করেছেন; মিলনের পথে দুস্তর বাধাই স্মরণ-চিন্তন মাধ্যমে প্ৰেমাকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য, বিরহবোধ গভীর ও মিলনপ্ৰয়াস তীব্র করে তুলেছে। অবশেষে নায়কনায়িকার যখন গোপন মিলন হচ্ছে তখন সঙ্গম বা রমণ ছাড়া চুম্বন আলিঙ্গনাদি বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে (আবদুল নবির আমীর হামজা’ কাব্য)। কাজেই পরপুরুষ কর্তৃক দেহ-স্পর্শ মাত্ৰই নারীর সতীত্ব নষ্ট হওয়ার মতো রামায়ণী সংকীর্ণতাকে এঁরা প্রশ্ৰয় দেননি। কেবলমৈথুনেই, অর্থাৎরতিরমণেই সতীত্ব নষ্ট হয়–এ-ই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। অ-মুসলিম নায়ক-নায়িকার ক্ষেত্রে সত্য-সাক্ষী করে মালাবদল করলেই গান্ধৰ্ব বিয়ে হয়ে যায়। অবশ্য সতীত্ব দেহে কিংবা মনে তা আজও তত্ত্বের ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে নিণীত হয় নি। নারীর সতীত্ব-যে পুরুষভোগ্য বস্তুর ধারণা থেকে অর্থাৎ ব্যক্তি-পুরুষের একাধিপত্যের বা একক-পুরুষ নিষ্ঠারই সামাজিক স্বীকৃতিমাত্র-তার বেশি কিছু নয়, বড়জোর সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আরোপ করার জন্য পিতৃত্ব নির্দিষ্ট রাখার প্রয়োজনপ্রসূত, সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষার গরজে এ-সত্য কখনো স্বীকৃতি পায় না। যদিও প্লেটো থেকে কার্ল মার্কস অবধি অনেকেই বিয়ের তথা সতীত্বের গুরুত্ব স্বীকার করেন নি। পুরাণে মহাভারতেও সতীত্বের এমন বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। কোনো কোনো বুনো সমাজে অন্তত পার্বণিক উৎসবে মা-মেয়ে প্রভৃতি কিছু রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয় ব্যতীত যে-কোনো নারীর সঙ্গে সঙ্গম করা শান্ত্র ও সমাজসম্মত রীতি। একে “গণ-সঙ্গম’ পাৰ্বণও বলা চলে। পুরাণে মহাভারতে ছান্দােগ্য উপনিষদে উদ্যালক, বিরোচন প্রভৃতির উক্তিতে ও কাহিনীতে বোঝা যায় পর্যন্ত্রী সম্ভোগ একসময় সামাজিক সদাচার বহির্ভূত ছিল না।
৫
দুনিয়ার সব আদিম মনুষ্যসমাজে জীবন-জীবিকার ও নিরাপত্তার অবলম্বন ছিল জাদুবিশ্বাস। জাদু ঐন্দ্রজালিক শক্তির জনক। মন্ত্রেই তার আবাহন। আনুষঙ্গিক কিছু মুদ্রাভিঙ্গি ও উপচারও থাকে। এই আদিম বিশ্বাস-সংস্কার আজও উন্নত সভ্যতা ও উচু সংস্কৃতির স্রষ্টা ও ধারক-বাহকদের মধ্যেও অবিরল রয়ে গেছে। ভূত-প্ৰেত-দেও-দানু-জিন-পরি প্রভৃতি মন্দশক্তির প্রতীক আজও শঙ্কা-ত্রাসের কারণ হয়ে সাধারণ মানুষের মনোলোকে বেঁচেবর্তে রয়েছে।
বৌদ্ধ প্ৰাবল্যের যুগে অলৌকিক শক্তিধর সিদ্ধপুরুষ ও নারী ডাক-ডাকিনী, যোগীযোগিনীর প্রভাবে এ বিশ্বাস, সংস্কার ও আচার গভীর ও ব্যাপক হয়। বৈদিক মন্ত্র কিংবা যজ্ঞও ঐ জাদুনির্ভর-ঐন্দ্রজালিক শক্তির উদ্বোধনুই লক্ষ্য। এসব জাদুমন্ত্র-প্রসূত তুকতাক, দারু-টোনা, মন্ত্ৰ-উচাটন, বাণ-ফোঁড়, ঝাড়-ফুক প্রভৃতি মঙ্গোল-গোত্রীয়দের প্রভাবে বহু ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। ডাকিনী-যোগিনীর সঙ্গে কামরূপ-কামাখ্যার সম্পর্ক ও ঐতিহ্য এভাবেই গড়ে উঠেছে এবং লোকস্মৃতিতে তা আজও অম্লান। তন্ত্র ও তান্ত্রিক আচারও তিব্বতি-চীনা মঙ্গোলীয়দের দান। তুক-তাক-মন্ত্রের জগৎ একটি দুৰ্ভেদ্য রহস্যলোক। মানুষকে মারা-বাঁচানো ছাড়াও মানুষের জন্ম-মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ থেকে মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-ব্যাধি, রূপান্তর-দেহান্তর, স্বৰ্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে দৃশ্যে বা অদৃশ্যে বিচরণ অবধি সার্বিক জীবন-নিয়ন্ত্রণের শক্তি রাখে ঐ যোগসিদ্ধি বা কায়াসিদ্ধি। গোরক্ষাবিজয়ে ময়নামতীর গানে গোপীচাঁদের গানে এই চৌরাশি আঙ্গুল পরিমিত দেহ-সাধনায় সিদ্ধ ‘চৌরাশিসিদ্ধারা’য় তথা কায়াসাধক বৌদ্ধ নাথসহজিয়াদের কেরামতির কথাই বিবৃত হয়েছে।
আধুনিক প্রতীচ্য চিকিৎসাশাস্ত্র ও ঔষধ এদেশে চালু হবার আগে সেই আদিম বা বুনো মানুষের মতো এদেশী মানুষও রোগমাত্রকেই দৈব-নিগ্রহের কিংবা অরিঅপদেবতার কুনজর বলেই বিশ্বাস করত। বিশেষ করে যেসব রোগের নিদান ছিল না, সেগুলো সম্পর্কেবদ্ধমূল ছিল এ ধারণা। দেশী কলেরা-বসন্ত-প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর তো বটেই, আয়ুৰ্বেদে তথা দেশী চিকিৎসাশাস্ত্রে কিংবা ইউনানি তিব্বিয়ায় সব রোগের চিকিৎসা-নিদান ছিল না, আজকালের মতো আশু উপশমদানের ব্যবস্থাও ছিল স্বপ্ন। দ্রব্যগুণ-নির্ভর টোটকা চিকিৎসাই ছিল বাস্তব ব্যবস্থা। কাজেই কলেরা-বসন্ত-শিশুরোগ প্রভৃতির জন্যে ওলা-শীতলা-ষষ্ঠী প্রভৃতি অপদেবতা তো ছিলই, অন্য অনেক দুরন্ত দুশ্চিকিৎস্য অনির্ণিত অনির্দেশ্য রোগমুক্তির জন্যে ঐসব মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, পানিপড়া, তাবিজ-কবজ, পূজা-শিন্নি, মানত-ধর্না, বলি-সদকা, কাঙাল-মিসকিন-ভোজন প্রভৃতিই ছিল ভরসা।
তাই তুক-তাক, দারু-টোনা, তন্ত্র-মন্ত্র, উচাটন-বশীকরণ, ঝাড়-ফুঁক। তাবিজ-কবজে মানুষের আস্থা ছিল প্রবল, ভরসা ছিল অপরিমেয়। সত্যকলিবিবাদ সম্বাদে কিংবা ময়নামতীর গানে দেখি মন্ত্রবলে মানুষ ইচ্ছেমতো কীট, মাছি, পশু, পাখি, সাপ, ব্যাঙ সবকিছুতে রূপান্তরিত হতে পারত, অপর মানুষের রূপ গ্ৰহণ করে আত্মগোপন কিংবা ছিলনা করতেও ছিল না কোনো বাধা। এমনকি মন্ত্রবলে দর্পণে নারী সৃষ্টি করা, মৃতে ও জড়বস্তুতে প্ৰাণ-সঞ্চার করা, অন্য মানুষের উপর অদৃশ্যে ভর করা প্রভৃতি সহজ ছিল। ‘পরঘাট সঞ্চারিতে আহ্মি মন্ত্র জানি’ (সত্যকলিবিবাদ)। তবে এসব ছিল যোগ্যতান্ত্রিক কায়সাধন সাপেক্ষ-ভুতসিদ্ধি, খেচর সিদ্ধি, কায়াসিদ্ধি প্রভৃতি ছিল কঠোর সাধনালভ্য।
মন্ত্রবলে স্বৰ্গ-মর্ত-পাতালের সর্বত্র থাকত অবাধগতি। যুদ্ধে অস্ত্ৰ জোড়ার সময়েও মন্ত্রপূত অন্ত্রের লক্ষ্য হতো অমোঘ। ‘নানামন্ত্রে আমন্ত্রিয়া এড়ে অস্ত্ৰবাণ’ (সত্যকলি)। রামায়ণ-মহাভারতেও আমরা অগ্নি-বায়ু-সৰ্প-চন্দ্র প্রভৃতি বহু বিচিত্ৰ বাণের ব্যবহার দেখি। ভূত-প্ৰেত-জিন-পরি-দেও-দানুর প্রভাবেও লোকের বিশ্বাস ছিল অবিচল। ভূতপ্ৰেত-দেও-দানব-জিন-পরি ছাড়াবার তাড়াবার ব্যবস্থাও ছিল বিচিত্র ও বিবিধ, তাতে অমানবিক নির্যাতনমূলক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হত। তাবিজ-কবজ, মন্ত্র-স্বস্ত্যয়ন, দোয়াকোরআনখানি, পূজা-শিন্নিদান-সদকা, বলি-কুরবানি অনুষ্ঠানেও ধূপ-ধূনো-লোবান, সোনা-রুপা-লোহা প্রভৃতির ধোয়াজলে ও লোহা ধারণে ছিল অপদেবতার হামলাভীত মানুষের নির্ভর ও ভরসা। এমনি হাজারো ঘরোয়া, নৈতিক ও সামাজিক কুসংস্কার নিয়ন্ত্রণ করত মানুষের ভাব-কর্ম-আচরণ। এগুলো-যে নিরাপত্তাকামী আদি মানবগোষ্ঠীর ভয়-বিস্ময়-কল্পনাপ্রসূত জাদু-বিশ্বাস ও আচারের ক্রমোৎকর্ষপ্রাপ্ত সংস্কার ও রূপ তা বলার অপেক্ষা রাখে নিনা। এমনি রূপান্তরে আদিম বিশ্বাস-সংস্কার ও আচার দুনিয়ার সভ্যতম সমাজেও জগদ্দল হয়ে আজও টিকে আছে।
নানা শুভ ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মে ছাড়াও গৃহ-নির্মাণে ও গৃহ-প্রবেশে, স্নানে, বিশেষ করে পার্বণিক স্নানে, নববস্ত্ৰ পরিধানে কিংবা পরিহারকালে মাস-দিন-ক্ষণ-গ্ৰহ-নক্ষত্ররাশিনির্ভর শুভাশুভ জানতে ও মানতে হত; এখনো হয়। অনেক রোগই ভূত-প্ৰেতদেও-দানু-জিন-পরির কুদৃষ্টির ফল, তাই রোগ এড়ানোর জন্যেও কথায়, কাজে, চলায়-ফেরায় কালাকাল মানতে হয়। মুহম্মদ খানের ‘সত্যকলিবিবাদ সম্বাদে’, আলাউলের ‘তোহাফা’য়, মুজাম্মিলের ‘নীতিশাস্ত্রবার্তা’য় এবং আরো অনেক গ্রন্থে প্রাসঙ্গিকভাবে গ্রহ-নক্ষত্ৰ-রাশির প্রভাব কিংবা অপদেবতার অপদূষ্টি কুনজরের লক্ষণ, নিদান এবং তা এড়ানোর উপায় প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।
যেমন শ্রাবণ-ভদ্ৰে নতুন ঘর করলে সে-ঘর সর্বদা রোগ-শোক-আপদে আকীর্ণ থাকে। স্পষ্টত বর্ষাকালে নির্মিত ঘর স্যাতসেঁতে হবে এবং তজজাত রোগও অবশ্যম্ভাবী, তেমনি আশ্বিনেও ঝঞা-বন্যার আশঙ্কার সঙ্গে গৃহ-উপকরণও দুর্লভ-দুর্মুল্য হবে।
সোম, বুধ ও বৃহস্পতিবারে স্নান করলে ধন বাড়ে। শুক্রবারে স্নানও উত্তম। মঙ্গলবারে স্নান করলে আয়ুকমে এবং দুশ্চিন্তা বাড়ে। গাছতলায় দিগম্বর মানে নেংটাি হলে রোববারে রোগে ধরে এবং মানুষের কুদৃষ্টি পড়লে কিংবা ভূতে ভর করলে হাঁস বা ছাগল দান করে আরোগ্য লাভ করা যায়। বুধবারে যে-রোগের শুরু তা থেকে আরোগ্যের উপায় হচ্ছে কালো মুরগি দান। ভূতদৃষ্টিজাত রোগের নিরাময়ের জন্যে ছাগ-বৃষ দান করতে হয়। অশ্বের কপালের লোম পুড়ে ধ্রুয়া দিলে ও ময়ূরের পুচ্ছ নিয়ে তালপাতা বা ছাতার মতো ধরলে দেও-এ ভর-করা মানুষ নিষ্কৃতি পায়। হিঙ্গুল, কম্ভরী, শস্যধূম, জতুর গুড়ো, কালো-মটি, গাভীর হাড়, মাছের পিত্ত, হরিদ্রা, চিলের মাংস, প্যাচার নখ, কালো বিড়াল ও কালো মুরগির বিষ্ঠা, গন্ধক প্রভৃতিও বিভিন্ন চিকিৎসার উপকরণ। শুক্রবারে নববস্ত্ৰ পরিধান এবং রোববারেই নববস্ত্ৰ ছেড়া বিধেয়।
বিবাহ ও অন্য পুণ্যকর্ম শুক্রবারে, শনিবারে মৃগয়া, রোববারে গৃহ-নির্মাণ, বাণিজ্যোদেশে শনিবারে বিদেশ যাত্ৰাই শুভ আর যুদ্ধ মঙ্গলবারে শুরু করাই ভালো।
৬
আগেই বলেছি, সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রই তৈরি করেছে বাঙালির অধ্যাত্ম-সাধনার ভিত্তি। এ-ক্ষেত্রে বৌদ্ধ, হিন্দু কিংবা মুসলিমে ভেদ মতগত নয়, আচার-পদ্ধতিগত। সবাই দেহসাধনায় আস্থা রাখে। দেহতত্ত্ব সবারই অবশ্য জ্ঞেয়। নির্বাণকামী বিকৃত বৌদ্ধদের দেহবাদ, ঈশ্বরবাদী হিন্দু-মুসলিমে দেহাত্মবাদে রূপান্তর পেয়েছে। বৈরাগ্য-সন্ন্যাসের ঐতিহ্য আরো পুরানো, নাস্তিক আজীবিক, জৈন শ্রাবক, বৌদ্ধ ভিক্ষু, বজ্রযানী-সহজযানী-তান্ত্রিক-কাপালিক-বীরাচারী-বীভৎসাচারী-চীনাচারী নানা তান্ত্রিক ব্ৰহ্মচারী, যোগী-সন্ন্যাসী বৈষ্ণবসহজিয়া-বাউল-বৈরাগী আকীর্ণ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙলায় যোগীর আদর-কদর ছিল অসামান্য। বৈরাগ্যে, সেবায়, সততায়, সুচিকিৎসায়–অলৌকিক শক্তিধর সাধনসিদ্ধ নিগৃহ যোগী ছিল লোকচক্ষে আদর্শ মানুষ। বাঙলাসাহিত্যের গোড়া থেকে রবীন্দ্রনাথের রূপকসাঙ্কেতিক নাটক অবধি আমরা এজন্যেই বিশ্বাস, ভরসা ও নির্ভর করবার মতো আদর্শ-চরিত্র মানুষ হিসেবে পাই কেবল যোগী-সন্ন্যাসীকেই। ঘর-সংসার করেও বৈষয়িক মানুষ-যে আদর্শনিষ্ঠ, সেবাপরায়ণ, সত্যসন্ধ ও ত্যাগপ্রবণ হতে পারে, তা যেন আমাদের দেশের মানুষের কাছে সুপ্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি অজ্ঞাত। তাই আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যে (বঙ্কিম-সাহিত্য অবধি) পরহিতব্ৰতী উপচিকীযুঁ, ঈৰ্ষা-অসূয়ামুক্ত, সেবা-সততা-ত্যাগতিতিক্ষীসুন্দর মানুষমাত্ৰই যোগী-সন্ন্যাসী-ব্ৰহ্মচারী। তাই সাধু আমাদের চেতনায় বেনে নয়, সন্ন্যাসী। সংসারী বিষয়ী মানুষের সততায় ও মনুষ্যত্বে এদেশের মানুষ চিরকাল এমন আস্থাহীন যে এদেশে রাজনীতির নেতা হতেও বৈরাগ্যের ভান ও ভেক দরকার।
গায়ে ছাই, কানে কড়ি, গলে মালা, হাতে নড়ি ও খাপর, কাঁধে কাঁথা ও কুলিএমন যোগীর সাক্ষাৎ মধ্যযুগের মুসলিম-রচিত সাহিত্যের সর্বত্র মেলে। বাঙালি তথা ভারতীয় মুসলিমের মারফত-সাধনায়ও যোগ ও যোগ-পন্থাই হয়েছে অবলম্বন। শাহ শরফুদ্দীন বুআলি কলন্দর, গউস গোয়ালিয়র থেকে সৈয়দ সুলতান, ফয়জুল্লাহ, হাজী মুহম্মদ, শেখ চান্দ, আবদুল হাকিম, আলি রাজা প্রমুখ সবাই যোগভিত্তিক সুফি সাধনাতেই আস্থা রেখেছেন। এ সাধনাতত্ত্বের প্রাপ্ত উৎস হচ্ছে ভোজবৰ্মণ রচিত ‘অমৃত-কুণ্ড’। ‘বাঙলার সুফী সাহিত্য’ গ্রন্থে এসব বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। ইসলামের ‘নবীবংশ’-প্রণেতা পির মীর সৈয়দ সুলতান বলেছেন, ‘হযরত মুহম্মদ ও উমর যোগপন্থ শিখাইলা, শিখাইলা জ্ঞান।’ কিংবা ‘ফিরিস্তা সকলে তন্ত্রমন্ত্র শিখাইলা।’ এই-ই হচ্ছে নবি ও খলিফা প্রচারিত ইসলাম! মারফত ও মরমিয়া সাধনার ক্ষেত্রে সুফিবাদের আবরণে মুসলমানরা সাংখ্যাতন্ত্র ও যোগতত্ত্ব বরণ করলেও কিন্তু তারা সচেতনভাবে পৌত্তলিকতাবিরোধী ও বিদ্বেষী। যদিও হজব্ৰত উদযাপনকালে কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ (তায়াব) করা, পাথর চুম্বন করা, অদৃশ্য শয়তানের প্রতি পাথর ছোড়া, হযরত হাজরার স্মৃতির সম্মানে ছুটোছুটির অভিনয় করা প্রভৃতি মুসলিমদের অবশ্য কর্তব্য এবং গুরুজনে কদমবুসি, পির-পূজা, দরগাহ জেয়ারত ও কবর সালাম করা, খিজির কিংবা সত্যপীরে শিন্নিদান, ওলা-শীতলা-ষষ্ঠী-বনবিধি ও হিংস্র জন্তু-আধুষিত জলে-ডাঙায় হাঙর-কুমির-সাপ-বাঘ-হাতি প্রভৃতিকে অরি-দেবতা জ্ঞানে মান-মানতে বশ করা প্রভৃতি তাদের অনেকেরই জীবনাচরণের অঙ্গ, তবু এসব তাদের চোখে পৌত্তলিকতা নয়। এসব সংস্কার-বিশ্বাস-আচরণ মিলে বাঙালি মুসলমানের আচরণীয় মুসলমান ধর্ম বা লৌকিক ইসলামের উদ্ভব।
৭
বিবাহে পাণ-প্রথা চালু ছিল; হিন্দুসমাজে বরপণ এবং মুসলমানসমাজে ছিল কন্যাপণ। বাল্যবিবাহ জনপ্রিয় ছিল। ধনীরা সাধারণত বহুপত্নীক এবং গরিবেরা একপত্নীক থাকত। নজর, শিকলি, যৌতুকদানও সামাজিক রেওয়াজের আবশ্যিক অঙ্গ ছিল। পণ ও নির্ধারিত অলঙ্কার প্রভৃতির দেনাপাওনার ব্যাপারে অভাবে কিংবা স্বভাবদোষে পারস্পরিক প্রতারণার ঘটনা বিরল নয়, সুলভাই ছিল। তাই বিয়ের আসরে ঝগড়া-বিবাদ-মারামারি, বিয়েভাঙা প্রভৃতি প্রায়ই ঘটত। বিয়ের প্রস্তাব-পয়গাম পাঠানো থেকে বিয়ের পরের কয়দিনও উভয়পক্ষের মধ্যে ভোজ-উৎসব চলত নানা অজুহাতে–যেমন ঘর-বাড়ি দেখা, বরকনে দেখা, পাকাকথা, দিন-তারিখ ঠিক করা, বিয়ের ভোজ, কনে-ভোজ, বর-ভোজ প্রভৃতি। বিবাহোৎসবে বা খৎনা, কান-ফোড়ন, আকিকা, অন্নপ্রাশন, নাম-রাখা, গায়ে হলুদ ও হাতে-মেহদি প্রভৃতিতে বাদ্য-বাজি, নাচ-গান, আবির-ফাগ, সোহাগ, কেশরঅগুরু-চুয়া, আন্তর, রঙ মাখা-ছোড়া, কাদা-ছোড়া, মেয়েলি নাচগান, পুতুল নাচ, জাদুকরের খেলা প্রভৃতির ব্যবস্থা আর্থিক সাচ্ছল্যানুসারে থাকতই।
ঘরজামাই বরের বা শ্বশুরঘরে বউয়ের তেমন কোনো মর্যাদা ছিল না। বিশেষ করে মেয়েদের বাপের বাড়ি ছিল, শ্বশুরবাড়ি ছিল, কিন্তু নিজের বাড়ি বা সংসার থাকত না। বধূর উপর পীড়ন-আশঙ্কায় বিবাহিতা মেয়ের মা-বাপ-ভাই-বোন সবসময় বর-পরিবারের সঙ্গে তোয়াজের ভাষায় ব্যবহার করত অর্থাৎ বরপক্ষের মন যুগিয়ে চলতে হত তাদের। কন্যার পিতা হিসেবে এ-ক্ষেত্রে রাজা ও ভিখারির মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। ‘পিতৃগৃহে কন্যা জন্ম অন্যের কারণে।’—এটি শিশু বালিকারাও জানত-বুঝত, পুতুল-খেলায় তা ছিল সুপ্রকট। পুরুষ-প্রধান সমাজে নারী ছিল নরপোষ্য, তাই অসহায় ও স্বাধীনসত্তাবিহীন। কন্যারূপে পিতার, জায়ারূপে স্বামীর, মাতারূপে সন্তানের আশ্রয়ে ও অভিভাবকত্বে জীবন কাটে তার। এ-কারণেই হয়তো অপরিচিত মনিববাড়ির বালক-ভূত্যের মতো পরকে আপন করার, অনান্তীয় নিয়ে ঘর করার, এবং নতুন জায়গায় ঘর বাঁধার মতো মনের জোর, স্বভাবের ঐশ্বর্য ও মানসপ্রস্তুতি থাকে তার বালিকা-বয়স থেকেই। স্বয়ম্বরের কাল তখন অপগত বটে, কিন্তু জামাতা (গদা-মালিকা দ্রষ্টব্য) নির্বাচন কালে তার শাস্ত্ৰজ্ঞান, বুদ্ধি, যোগ্যতা, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য-চেতনা প্রভৃতির পরীক্ষা হত। অশিক্ষিতের মধ্যে হত হেঁয়ালিধাঁধা দিয়ে। বর-ঠকানো নানা হেঁয়ালি তখন খুব চালু ছিল। বিয়ের সময় দিন-ক্ষণ-তিথি-লগ্ন মানা হত। বিবাহানুষ্ঠানের জন্যে সুসজ্জিত মঞ্চ তৈরি হত, কলাগাছ পোতা হত, আমের ডাল জলপূৰ্ণামঙ্গলঘট তথা কলসির মুখে বসানো হত। উপরে থাকত চাঁদোয়াএই আচ্ছাদনের অপর নাম আলাম বা ছত্র। মেঝে আলপনা আঁকা হত। ঐ মঞ্চের নাম ছিল মারোয়া। এর মধ্যেই বর-কনের চরিচোখের মিলন হত। দুইপক্ষের সখিবন্ধু-আত্মীয়রা তখন হর্ষধ্বনি ও শুভ কামনার সঙ্গে ঠাট্টা-মশকরা ও নানা রঙ্গরস করত। এর নাম জুলুয়া বা জোলুয়া (জলুস?)—‘জলুয়া দিলেন্ত দীয়া (দীপ), করি হুড়াহুড়ি’। বর-কনের মধ্যে তখন পাশাদি ক্রীড়া চলত। বর-কনে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষরুপে ফুলের স্তবক দিয়ে ছোড়া-লোফা খেলাও খেলত। পদাবলীর সেই ফুলের গেরুয়া (স্তবক) সঘনে লোফএ’ ক্রীড়াও এ-রকমেরই। এ খেলার নাম ছিল গেরুয়া খেলা। এ যেন বিবাহোত্তর Courtship। শরম-সঙ্কোচ ভাঙার জন্যেই হয়তো এ ব্যবস্থা। [কবি আইনুদ্দীনের গেরুয়া খেলা দ্রষ্টব্য]। বর-কনের অন্য বাড়িতে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা থাকত। এর নাম ‘গস্ত্ ফিরানো।’ নিরক্ষর গরিব মুসলিম ধুতি পরেই বর সাজত। অন্যদের তখনো বর-পোশাক ছিল ইজার-পাগড়ি, তাঞ্জাম-চৌদোল ও শিবিকা বা পালকিই ছিল বর-কনের বাহন।
সাধারণের বিয়েতে মেয়েমহলে বাঁদীশ্রেণীর ভাড়া-করা নারী কিংবা গৃহস্থঘরের বৌ-ঝিরা নাচ-গান করত। ধনীগৃহে উৎসবকালে নাচিয়ে-গাইয়ে-বাজিয়ে বেশ্য আনা হত। বেশ্যারা সমাজে খুব ঘৃণ্য ছিল না। বাইজি’ সম্বোধন ও পরিচিতির মধ্যেই রয়েছে সামাজিক স্বীকৃতির আভাস। তা ছাড়া ধনীলোকের নজরীরূপে দাসীসম্ভোগ ও উপপত্নী রাখা নিন্দার কিংবা অগৌরবের ছিল না।
বিবাহাদি অনুষ্ঠানে নানা রীতি-রেওয়াজ ও আচার-সংস্কার রয়েছে। কালো অস্ট্রিকরা হলুদ মেখে স্নান করে গাত্রবর্ণের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে। আলপনা-আঁকা কুলা বা ডালায় ধান, দূর্বা, দীপ, হলুদ ও জলপূৰ্ণ ঘটের মুখে আম্রপত্র রাখে, ঘরের দ্বারে কলাগাছ পুঁতে, বিয়ের পূর্বদিনে বর-কনের বাড়িতে দই-মাছ পাঠায়, বর-যাত্রার সময় বরের কোলে একটা শিশু বসায়। এসব হচ্ছে আদিম জাদু-সংস্কার। ধান খাদ্যসম্পদ ও সন্তানবৃদ্ধির প্রতীক, দূর্ব জীবনীশক্তির, কলাগাছ ও আম্রপত্র দীর্ঘ আয়ু ও প্রাণশক্তির, হলুদ সৌন্দর্যের, মাছ প্রজননশক্তির, বরের কোলে শিশু সৃষ্টিশীলতার, ও দীপ আশার প্রতীক। পৃথিবীর আদিম ও বুনোসমাজে এগুলো নানাভাবে ও বিভিন্ন আকারে রয়েছে। জরু-যে জমির মতোই বীরভোগ্য, অর্থাৎ বাহুবল ও পৌরুষ দিয়ে আয়ত্ত করতে হয় এবং আদিযুগে-যে নারীকে হরণ করেই বরণ করার প্রথা চালু ছিল, তার রেশ রয়ে গেছে। দরজায় বর আটকানো প্রথায়। পূর্বে কনেপক্ষ সত্যি বাধা দিত; এখন ছদ্ম বাধা সৃষ্টি করে আর্থিক ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দেয়; এখন তা ঠাট্টা-সম্পর্কিতজনদের আমোদ-ফুর্তির উপলক্ষমাত্র। পাঁচ পুকুরের পানি মিশিয়ে পাঁচ হাতে স্নান করানো, পাঁচ হাতে মেহদি লাগানো, শুভকর্ম বন্ধ্যা ও বিধবা-ভীতি প্রভৃতি আমাদের বিস্মৃত আদিম পূর্বপুরুষ থেকে পাওয়া ঐতিহ্য, আচার ও উত্তরাধিকার। সংস্কার-যে মৰ্মমূলে কীভাবে চেপে বসে, তার প্রমাণ বেহুলা-লখিন্দরের বাসররাতের দুর্ভাগ্যভীত বাঙালি হিন্দুরা বিয়ের প্রথম রাত ‘কালরাত্ৰি’ হিসেবেই মানে।
৮
সাড়ে চার কিংবা পাঁচ বছর বয়সে মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার জন্যে। “হাতেখড়ি’ অনুষ্ঠান হত। এতে উৎসবের আয়োজন হত। ভোজপায়েস-শিন্নি-গুড়-বাতাসা-মিষ্টি এবং পান ও তেল (তেলোয়াই) যোগে উপস্থিত জনেরা অভার্থিত ও আপ্যায়িত হত। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, কাব্য, নাটক, সঙ্গীত, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও শান্ত্রিশিক্ষার সঙ্গে রতিশাস্ত্ৰও কখনো কখনো কোথাও শিক্ষা দেয়া হত। বাৎসায়নের ‘কামসূত্র’ কিংবা ‘নায়িকা লক্ষণ’ প্রভৃতি সে-যুগে তেমন লজ্জাজনক গুহ্যবিদ্যা ছিল না। তাই কাব্যে-উপাখ্যানে রতি-রমণের ও নারীরূপের বিস্তৃত বর্ণনা থাকত। সামন্ত-ঘরে চিত্রাঙ্কন ও সূচী শিল্পেরও চর্চা ছিল। তবে সাধারণের শিক্ষা সূচিতে শাস্ত্ৰ, ব্যাকরণ, সাধারণ গণিত (জল, জমি ও বস্তুর মাপ ও হিসাব সংক্রান্ত আর্যাদিই ছিল প্রধান), কাব্য, অলঙ্কার ও পত্র-দলিল-দস্তাবেজ রচনা প্রভৃতিই থাকত। সামাজিক উৎসবে-পার্বণে, নাচ-গান-বাদ্য-প্ৰমোদের জন্যে ছিল নীচজাতীয় গাইয়ে-বাজিয়েনাচিয়ে-নাটুকে বৃত্তিজীবী। উচ্চবিত্তের অভিজাত সামন্ত ও রাজ-পরিবারের লোকেরা কলা-চৰ্চা করত নিজেদের বা অন্তরঙ্গাজনের চিত্তবিনোদনের জন্যে। নারীশিক্ষাও একেবারে বিরল ছিল না।
শিক্ষা বলতে সে-যুগে ধর্মশিক্ষাই মুখ্য লক্ষ্য ছিল বলে ব্ৰাহ্মণ-অত্ৰাহ্মণ ও হিন্দুমুসলমানের বিদ্যালয় পৃথক ছিল। সাধারণত পণ্ডিতের ঘরে টোল ও আলিমের ঘরে বা মসজিদে মক্তব্য থাকত। পাড়ার ছেলেমেয়েরা তাদের কাছে পড়ত। কিছু দক্ষিণা বা নজরানা দিত, তা-ও সবসময় কড়িতে নয়-ফসল তোলার মৌসুমে ধানাদি শস্য কিংবা ফলমূল তরকারির আকারে ও বার্ষিক বরাদে। সাধারণ শিক্ষার জন্যে কোথাও কোথাও পাঠশালা ছিল। উচ্চশিক্ষার জন্যে ক্বচিৎ কোথাও সরকারি বা সামন্ত-সাহায্যে পরিচালিত টোল-মাদরাসা থাকত। সে-যুগে সব শ্রেণীর লোকের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল না। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সে অধিকারও ছিল না। নিম্নবর্ণেরও নিম্নবিত্তের দীক্ষিত মুসলিম সমাজেও ঐতিহ্যাভাবে বিদ্যার্জনে আগ্রহ ছিল না। কাজেই ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ই বেশি ছিল এবং পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল নগণ্য। গুরু-ওস্তাদের শাস্ত্রীয় সংস্কারপ্রসূত মর্যাদা ও সম্মান ছিল। শাপে সর্বনাশ হওয়ার আশঙ্কা ছিল বলে পড়ুয়ারা তো বটেই অন্যেরাও গুরু-ওস্তাদকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করত, তা ছাড়া বিদ্বান ও জ্ঞানী বলেও তাঁরা সম্মানিত ছিলেন। হিন্দুপণ্ডিত পৌরোহিত্য, পাতিদান, কোষ্ঠী তৈরি, ভাগ্যগণনা ও শ্ৰাদ্ধাদি শাস্ত্রীয় সামাজিক ও পার্বণিক অনুষ্ঠানে স্ব স্ব কর্তব্য পালন করে অর্থে পার্জন করতেন।
মৌলবি-মুনশি-ওস্তাদ-মোল্লা-খোন্দকারেরাও গায়ের শাস্ত্রীয় উৎসবে-পার্বণে, বিবাহে-মৃতসৎকারে শাস্ত্রীয় দায়িত্ব পালন করতেন। মুরগি জবেহ, ফাতেহা পাঠ, জানাজায় ইমামতি, মসজিদে মুয়াজ্জিন ও ইমামের কাজ প্রভৃতি ছিল তাঁদেরই। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাথীরা শিক্ষকের নিঠুর শারীরিক পীড়নের শিকার ছিল :
শিখিতে না পারে তবু শিখাইতে না ছাড়ে
মারিয়া বেতের বাড়িএ ঠেঙ্গা করে।
কতু কভু বান্ধ্যা রাখে বুকে বসে রয়
উচিত করএ শাস্তি যেদিন যে হয়।
(দয়াময়ের সারদামঙ্গল)
এখানেই শেষ নয়, নাডুগোপাল করা (হাত-পা জড়ো করে রাখা), ধান বা কাঁটা দিয়ে কপাল চিরে রক্ত ঝরানো, সূর্যের দিকে মুখ করে বসানো, বিছুটি পিঁপড়ে প্রভৃতি গায়ে লাগিয়ে দেয়া ছিল স্বাভাবিক শাস্তির অঙ্গ। কলম ছিল কঞ্চি কিংবা হাঁসের, শকুনের বা ময়ূরের পালকের। বালকেরা কলাপাতায়; অন্যেরা লিখত তুলেটি কাগজে, তালপাতায়। কালি তৈরি হত বিভিন্ন পদ্ধতিতে। ছাত্ৰশিক্ষকেরা বসতেন চাটাই, মাদুর, পাটি, কুশাসন ও ফরাশ প্রভৃতির উপর। ছাপাখানা ছিল না বলে সব গ্রন্থ ছিল হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি। পেশাদার লিপিকার থাকত।
৯
গান-বাজনা সমাজে লোকপ্ৰিয় ছিল। শরিয়তপস্থিরাও যেন তখন তেমন রক্ষণশীল ছিল না। তাই সর্বপ্রকার উৎসবে-পার্বণে নাচ-গানের আসর বসত দেখা যায়। চট্টগ্রামের হিন্দু ও মুসলিম রচিত রাগ-তালের বহু গ্ৰন্থ ষোলো শতক থেকেই মিলছে। বিশেষত সঙ্গীত (হালকা-দারা-সামা) কলন্দরিরা, চিশতিয়া ও কান্দিরিয়া সুফিদের সাধন-ভজনের অঙ্গ। প্ৰায় সব মুসলিম-কবিই গান রচনা করেছেন, কেউ-কেউ রাগ-তালের গ্রন্থও ৷ কবি আলাউল তো প্রথম জীবনে সঙ্গীতশিক্ষকই ছিলেন। গাইয়ে-বাজিয়ে তো ছিলেনই, তিনি সঙ্গীত রচনা ছাড়া ‘রাগতালনামা’ও রচনা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, সবার সব সঙ্গীতই রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়-রূপকে রচিত। ব্যতিক্রম ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়।
১০
ঘরে-সংসারে একরকমের নেশা চালু ছিল। উননের কাছে জলভরা ঘড়ায় প্রতিদিন এক মুষ্টি ভাত রেখে কয়েক দিন পর ভাতপচা পানি ছেকে নিয়ে পান করত তারা, এর নাম আমানি বা ঘড়া কাজি। এতে সামান্য নেশা ধরত। ভেতো মদের আরাকানি নাম ‘সিফত’। তা ছাড়া ধেনো, তালো, খেজুরে মদ, গাজা, চরস, চণ্ডও বহুলপ্রচলিত ছিল। মুখশুদ্ধির জন্যে পান-সুপারি তো ছিলই। কিন্তু পরে যখন প্রায় নির্দোষ ব্যসন ‘তামাকু” চালু হল, তখন তামাক সেবনের নিন্দায় উচ্চকণ্ঠ হয়েছে সমাজহিতৈষীরা। ‘তামাকু’ সেবন গোড়াতে ছিল শাহ-সামন্ত অভিজাতদের দর্প ও দাপট প্রকাশের প্রতীক। তাই মনিব ও মান্যজনের সম্মুখে তামাকু সেবন ছিল বেয়াদবি, ঔদ্ধত্য, অসৌজন্য ও অসংস্কৃতির লক্ষণ ও প্রকাশ। পরে এ অভ্যাস যখন গণমানবে সংক্রমিত হল, তখনো তামাকু সেবন রইল। অবজ্ঞেয় ও নিন্দনীয়। এর কারণ বোধহয় তামাকু সেবনলিন্সু ব্যক্তিরা অধৈর্য হয়ে হাঁকা কেড়ে নিয়ে ধূমপান করতে চায়। তাই আমরা আঠারো শতকের কবি শেখ সাদী ও আফজল আলিকে তামাকুসেবীর নিন্দায় মুখর দেখি। রামপ্রসাদ, শান্তিদাস ও সিতকর্মকার যথাক্রমে ‘তামাকুমাহাত্ম্য’, ‘তামাকুপুরাণ’, ও ‘ইকাপুরাণ’ রচনা করে তামাকখোরকে বিদ্রুপ করেছেন এবং দ্বিজ রামানন্দ সঙ্গীতে গাজা-তামাকুর মহিমা প্রচারে হয়েছেন মুখর। ফকির-দরবেশরাও তামাকখোর হয়ে উঠেছিলেন। ‘চৌদিশত দরবেশ চলে আলবোলা হাতে’ (দ্বিজ ষষ্ঠীবর)।
১১
সে-যুগে নারীর অলঙ্কারবাহুল্য ছিল। মেয়েরা মাথায় সিঁথিপাট, টিকলি, কণ্ঠে হাঁসুলি, মালা, টাকার ছড়া; এক, তিন ও সাত লহরি হার, তাবিজ; হাতে কঙ্কণ, বালা, তাড়, চুড়ি, খাড়ু, পৈচি, অঙ্গদ, অনন্ত; আঙুলে অঙ্গুরীয়; নাকে কোর, চাঁদ বোলাক, বালি, ডালবোলাক, লোলক, নাকমাছি, নাকছবি, বেশর; কানে কানফুল, বোলতা, কুমড়োফুল, ঝুমকা কুণ্ডল, নোলক, ঝিঙ্গাফুল, কুণ্ডল, কানবালা, বালি; পায়ে পাজব, পাসুলি, নূপুর, ঘুঙুর, মকর, খাডু, মলতোড়র, বাকপাত, বঙ্করাজ, মল, উনচটি, উঝটি; কোমরে চন্দ্রহার, ঝুমঝুমি, নীবিবন্ধ, কিঙ্কিণী; হাতের পাতায় আঙুল-সংলগ্ন রতনচুড়; গ্ৰীবায় গ্ৰীবাপত্ৰ; বাহুতে তাড়, কেয়ূর, জসিম, বাজুবন্ধ, বাজু প্রভৃতি বহু ও বিচিত্র গড়নের অলঙ্কার ছিল। আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থানভেদে এগুলো তালপাতা, ঝিনুক, শিঙ থেকে তামাপিতল-সিসা-রুপা-সোনা-মুক্তা, হীরা-মণি-কাচপাথর প্রভৃতি যে-কোনো উপাদানে তৈরি হত। শেখশুভোদয়ায় তালপত্রে নির্মিত কর্ণােভরণের কথা আছে। কাচুলি নানা বৈচিত্র্যে আকর্ষণীয় ও জরি-রত্নখচিত ছিল। অবশ্য কাচুলি অভিজাত ও ধনীঘরের নারীই কেবল ব্যবহার করত। নানা ছাদের বেণী ও কবরী হত। কানাড়ি (কর্নটদেশীয়) ছাদে বাধা কবরীর কদর ছিল বেশি। কবরীতে বেণীতে নানা রঙের ফিতা ছাড়াও ফুল জড়ানো ছিল সৰ্বজনীন রীতি। বেণীর প্রান্তে ফুল বাধা থেকেই হয়তো গ্রন্থের সর্গ বা গ্ৰন্থ সমাপ্তিজ্ঞাপক ‘পুষ্পিকা’ নামের উৎপত্তি।
পূরুষেরও বাহুতে কবচ ও বাজু, বাহুতে, গলায় ও কটিতে তাবিজ; কানে কুণ্ডল, হাতে বলয় ও গলায় একছড়ি হার বা কালো সূতার তাগা’ থাকত। ধাৰ্মিক মুসলমানেরা খিলালের প্রয়োজনে লোহার বা পিতলের খিলাল-শলাকা গলায় বুলিয়ে রাখত।
নারীর প্রলেপ প্রসাধনদ্রব্যের মধ্যে ছিল সিন্দূর, চন্দন, মেহদি, কুমকুম, কম্ভরী, কাফুর, কেশর, অগুরু, কাজল, অঞ্জন, সূৰ্মা, তেল, আতর ও ঠোঁটে তাম্বলরাগ। পুরুষেরাও এসব প্রসাধনদ্রব্য উৎসব-পার্বণকালে অঙ্গে ধারণ করত। চুল-দাড়ি রাঙানো মুসলিম ধাৰ্মিকসমাজে বহুলপ্রচলিত ছিল।
শাহ সামন্ত-অভিজাত এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ঘরে নারী পর্দা ছিল, তবে শাসনপ্রশাসনে জড়িত বা নিয়োজিত নারীর পর্দা-নীতি শিথিল ছিল। নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের ঘরে পর্দা কখনো প্রথারূপে চালু ছিল না। পর্দা প্রথা ছিল না। বাউল-বৌদ্ধ-বৈষ্ণবদেরও। দরিদ্রঘরের নারীদের ঘরে-বাইরে, ক্ষেতে-খামারে, হাটে যেতে হত। ভিখারিনি তো ছিলই। আর দাসী-বান্দী-ক্রীতদাসীর পর্দা রাখার তো নিয়মই ছিল না। তা ছাড়া তান্ত্রিক-কাপালিক-সহজিয়া-বাউল প্রভৃতি কায়াসাধকরা বামাচারী। মণ্ডল, ভৈরবীচক্র, নৈশমিলনচক্র, গৌপীচক্র রসের ভিয়ান, রজঃ শুক্ৰ পান প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ও যৌথ রতি-রমণ হচ্ছে সাধনার অঙ্গ। কাজেই এদের মধ্যেও পর্দাপ্রথা ছিল না।
১২
গরিবেরা কাজের সময়ে কৌপীন, গামছা ও অন্য সময়ে খাটো শাদা ধুতি বা তহবন। পরত। মাথায় টুপি (কাপড়ের, তালপাতার বা বেতের) ও পাগড়ি পরত। জুতা পরা হয়তো বিয়ের মতো পার্বণিকই ছিল। হিন্দুরাও কৌপীন, গামছা, খাটো ধুতি ও গায়ে উত্তরীয় পারত, কেউ-কেউ মাথায় পাগড়িও বাধত। পাগড়ি বাঁধার পদ্ধতিতে হিন্দুমুসলমানে ভেদ ছিল। চট্টগ্রাম ছাড়া অন্যত্র নারীমাত্রই শাড়ি পরত। চট্টগ্রামে আরাকানি শাসন প্রভাবে ঘামচা” ও “উড়নী” দুই খণ্ড কাপড় পরীত মেয়েরা। রাজপুরুষ ও সামন্তঅভিজাত উচ্চবিত্তের শিক্ষিতারা পরীত ইজার, কামিজ, কাবাই, চাপাকান, আসকান, আলখাল্লা, চৌকা, সিনাবন্দ (waist coat) কোমরবন্দ ও পাগড়ি, শামলা কিংবা টুপি। গলাবন্দ, দোয়াল, অঙ্গুরীয়ও তারা পরত। শাসকশ্রেণীর অনুসরণে হিন্দু রাজপুরুষ, ধনী এবং অভিজাতরাও পরত। এসব পোশাক (কাল ধল রাঙা টুপি সবার মাথে/পাসরি পটকা দিয়া বান্ধে কোমরবন্ধ। –রূপরাম চক্রবর্তী, ধর্মমঙ্গল)।
আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থানকিংবা সরকারি চাকরিভেদে এসব পোশাক সুতোর, রেশমের, জরির কিংবা সোনা-রুপা-মুক্তা-মণিখচিতও হত। ধনীঘরের বউ-ঝিরা কীচুলি (Biodice) এবং অন্তর্বাস বা ছায়া (petti coat) পরত। গরিব ও মধ্যবিত্তের পোশাক ছিল মোটা তীতে নির্মিত। ঘরে ঘরে চরকায় সূতা তৈরি হত। তাঁতি শুধু বানিয়ে দিত।
চটক, মটক, গরাদ, ধুতি ছাড়াও শাড়ির মতো মোটা-পেড়ে নানা ধুতি ছিল। মেয়েদের ছিল ময়ুর পেখম, আগুন পাট, কালপাট, আসমান তারা, হীরামন, নীলাম্বরী, যাত্রাসিদ্ধি, খুঁঞা, নেত, মঞ্জাফুল, অগ্নিফুল, মেঘডুমুর, মেঘলাল, গঙ্গাজলি প্রভৃতি নানা নামের শাড়ি। মসলিন, পাটাম্বর তথা রেশমের (সিস্কের) কারুখচিত বহুমূল্য শাড়ি ছাড়াও উচ্চমূল্যের বেলন পাটের (সিস্কের) নোতের শাড়িও আনুষ্ঠানিক ও পার্বািণক প্রয়োজন মিটাত।
১৩
বৃত্তিভেদে নিম্নবিত্তের নিরক্ষর দেশজ মুসলিমসমাজ
কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম প্রদত্ত বিবরণ :
রোজা নামাজ না করিয়া কেহ হৈল গোলা
তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা।
বলদে বাহিয়া নাম বলয়ে মুকেরি
পিঠা বেচিয়া নাম ধরাইল পিঠারী।
মৎস্য বেচিয়া নাম ধরাইল কাবারী
নিরন্তর মিথ্যা করে নাহি রাখে দাড়ি।
সানা বান্ধিয়া নাম ধরে সানাকার
জীবন উপায় তার পাইয়া তাতিঘর।
পট পড়িয়া কেহ ফিরএ নগরে
তীর্যকর হয়্যা কেহ নির্মএ শরে।
কাগজ কুটিয়া নাম ধরাইল কাগতি
কলন্দর (ফকির) হয়্যা কেহ ফিরে দিবারাতি।
বসন রাঙাইয়া কেহ ধরে রঙ্গরেজ
লোহিত বসন শিরে ধরে মহাতেজ।
সুন্নত করিয়া নাম বোলাইল হাজাম…
গোমাংস বেচিয়া নাম বোলায় কসাই…
কাটিয়া কাপড় জোড়ে দরজির ঘটা…
সাধারণভাবে সৈয়দ, শেখ, তুর্কি, মুঘল, পাঠান প্রভৃতি বিদেশাগত মুসলমানরা অভিজাতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিক্ষিতদের মধ্যে কাজি, মোল্লা, শাস্ত্ৰবিৎ আলিম, সুফিসাধক, ফকির প্রভৃতি সমাজে মর্যাদাবান ও সম্মানিত ছিলেন। শিয়া-সুন্নি এই দুই মুখ্যভাগেও নানা উপসম্প্রদায় এখনকার মতোই ছিল। শিয়ারা আঠারো শতকে মুশির্দাবাদ-ঢাকা প্রভৃতি শাসনকেন্দ্রে প্রবল হয়। সুন্নিদের মধ্যে হানাফি, সাফি, আহমদি ও হাম্বলি-মাযহাব বা সম্প্রদায় ছিল। হানাফিরা ছিল সংখ্যাগুরু, অন্যদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তেমনি সুফিদেরও ছিল বিভিন্ন গুরুপন্থি খান্দান–চিশতিয়া, সুহরাওয়াদীয়া, নক্সবন্দিয়া, কাদেরিয়া, মাদারিয়া প্রভৃতি। গুরুবাদে বা পিরবাদে শরিয়ৎপস্থিদের অবিচল আস্থা ছিল।
বৃত্তি ও বর্ণভেদে হিন্দুসমাজ
রায়গুণাকর ভারতচন্দ্ৰ বৰ্ণিত বিবরণ :
ব্ৰাহ্মণ মণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন
ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন।
ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খ ঘণ্টারব
শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব।
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধি ভেদ
চিকিৎসা করএ পড়ে কাব্য আয়ুৰ্বেদ।
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারী
বেনে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারী-শাঁখারী।
গোয়ালা তামুলী তিলি তাঁতি মালাকার
নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার।
আগরী প্রভৃতি আর নাগরী যতেক
যুগী-চাষী, ধোপা-চাষী কৈবর্ত অনেক।
সেকরা ছুতার সূরী ধোপা জেলে গুড়ী
চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচি শুঁড়ী।
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালী তেয়র
কেলি কলু ব্যাধ বেদে মালী বাজিকর।
বাইজী পটুয়া কান কসবী যতেক
ভাবক ভক্তিরা ভাঁড় নর্তক অনেক।
এমনি ছত্ৰিশ জাতের এ বৃত্তি-বেসাতের লোক নিয়ে ছিল হিন্দুসমাজ।
প্রাচীনকালে হিন্দুদের মধ্যে সেলাই-করা কাপড়-জামা পরার রেওয়াজ ছিল না বলেই ‘কাটিয়া কাপড় জোড়ে’ রূপে দরজির পরিচয় দেয়া হয়েছে। এমনি লবণনির্মাতা মুলুঙ্গী, পান উৎপাদক বারুই, পালকিবাহক কাহার, সূত্রধর, কুমার, ঘরামি, কলু, বাজিকর, গায়েন, নট, বেদে উত্যাদি।
মন্থর হলেও মুসলিমসমাজ বিদ্যা ও ধন-মান যোগে বিবর্তন বা পরিবর্তনশীল ছিল। এ-সূত্রে স্মর্তব্য-‘গত বছর জোলা ছিলাম, এবার শেখ হয়েছি, ফসল ভালো হলে আগামী বছর সৈয়দ হব।’
অথবা :
আগে ছিল উল্লা-তুল্লা পরে হৈল মামুদ
পিছনের নাম আগে নিয়া এখন হৈল মোহাম্মদ
অতএব সমাজে বৈষম্য ছিল ধনী-নির্ধনে, আশরাফে-আতরাফে। এবং সম্পদ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পদ, বৃত্তি ও বংশভেদে কেউ ঘৃণ্য ও অবজ্ঞেয়, কেউ-বা শ্ৰদ্ধেয়-সম্মানিত ছিল। তবু মুসলিম-সমাজে হিন্দুর মতো জন্মসূত্রে জাতে-বর্ণে ঘৃণ্য-সম্মানিত হত না। মুখ্যত ধনই ছিল মানের মাপকাঠি। কাঞ্চনে অর্জিত কৌলীন্য কেউ ঠেকাতে বা অস্বীকার করতে পারত না।
ক. ধন হোন্তে অকুলীন হযন্ত কুলীন
বিনি ধনে হয় যথ কুলীন মলিন।
ধন হেন্তে যথ কাৰ্য পারে করিবারে।
[সৈয়দ সুলতান : নবী বংশ]
খ. অকুলীন কুলীন হৈব কুলীন হৈব হীন
অকুলীন ঘোড়ায় চড়িব কুলীনে ধরিব জীন।
[চট্টগ্রামের প্রাচীন ছড়া]
গ. নির্ধনী হইলে লোক জ্ঞাতি না আদরে
ফলহীন বৃক্ষে যেন পক্ষী নাহি পড়ে।
ধন্যবন্ত মূর্খক পূজএ সর্বলোক
ধন হোন্তে মান্যজন যদ্যপি বর্বর।
[সত্যকলিবিবাদ সম্বাদ]
একালের মতো কৃতী ও কীর্তিমান পুরুষ ছিল সেই—
‘যে দোলা ঘোড়া চলে,
আর
দশ বিশ জন যার আগেপাছে নড়ে।’
মুসলিম-সমাজেও কোনো কোনো বৃত্তি-বেসাত ঘৃণ্য ছিল। সামাজিক-বৈবাহিক সম্পৰ্কও অবাধ ছিল না কখনো :
ক. নারী বলে আহ্মি হই ধীবরের জাতি
আহ্মাতু অধিক হীন নাহি কোন জাতি।
খ. জাতিকুল না জানিয়া বিহা দিলে তোরে
শুনি জ্ঞাতিগণ সবে গঞ্জিবেক মোরে।
[নবী বংশ]
সে-যুগেও আভিজাত্যের উৎস ছিল তিনটে-ধন, বিদ্যা ও পদ। সমকালে তো বটেই ধন-বিদ্যা-পদধারীর বিচ্যুত বংশধরগণ অতীত-স্মৃতির পুঁজি নিয়েও কয়েক পুরুষ ধরে এমনকি চিরকাল সেই আভিজাত্য-গৌরব-গৰ্ব সামাজিক-বৈবাহিক জীবনে সুফলপ্ৰসূ রাখত। এরাই এবং মোল্লা-পুরুত-কায়স্থ-গোমস্তা-মুৎসুদি ও ছোট বেনেরাই ছিল মধ্যযুগের সেই শাহ-সামন্তশাসিত সমাজে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। সামন্ত প্রশাসকদের পরেই নিরক্ষার সমাজে ছিল এদের দাপট। এরাই ছিল গ্ৰাম্যসমাজে প্রধান। তবে রাজতন্ত্রের যুগে রাজনীতি দরবার-বহির্ভূত ছিল না বলেই এদের কোনো রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল না। কিন্তু সমাজ-সংস্কৃতির এরাই ছিল ধারক ও বাহক। সে-যুগে সমাজ-সংস্কৃতি ছিল স্থাণু ও স্থায়ী আচার ও অনুষ্ঠানে নিয়ন্ত্রিত। কেননা, নতুন ভাব-চিন্তা-চেতনা কিংবা আচার অশিক্ষা-আচ্ছন্ন দুৰ্গম গ্রামীণসমাজে সহজে পৌঁছত না।
দারিদ্র্য, অনাহার, দুৰ্ভিক্ষ ও দুর্জনের দৌরাত্ম্য কোনো যুগেই নতুন কিংবা অনুপস্থিত ছিল না। সাধারণ মানুষের ভাত-কাপড়ের কোনো বিলাস কিংবা প্ৰাচুৰ্য ছিল না কোনো কালেই। ‘দুধভাত’ই তার পার্বণিক পরমান্ন।
তরুণাং সৰ্যাপী শাকং নিবেদনং পিচ্ছিলানি চ দধীনি
অল্প ব্যয়েন সুন্দরি গ্রাম্য জনো মিষ্ট মুশ্নাতি।
(বৃত্তরত্নাকর : কেদার ভট্ট)
–কচি সরিষার শাক দিয়ে নয়া চালের ভাত আর পাতলা দই–সুন্দরি, অল্প ব্যয়ে এমনি ভালো খাদ্য গ্রাম্য লোকে খায়।
নির্জিত লোক বেঁচে থাকাতেই তুষ্ট থাকত। ‘শেখ শুভোদয়া’য় বিজয় সেনের জবানিতে পাই “আমার স্ত্রীপুত্ৰ আছে, ঘরে ভাঙা খোরা আছে, কলসীতে খুদ আছে। তা-হলে আমি হতভাগা কিসে।।” (সুকুমার সেন : প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, পৃ. ১৭) আবার তখনো এমন দরিদ্র ছিল যার জীর্ণতম কুটির মেরামতের মতো আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না, আজও যেমন রয়েছে অসংখ্য নীড়হারা নিগৃহ পরিবার। মুকুন্দরাম বর্ণিত ফুল্পরারও এমনি দুর্দশা স্মর্তব্য :
চলৎ কাষ্ঠং গলৎ কুড্যুমুত্তানতৃণ সঞ্চয়ম
গঞ্জ পদাথি মণ্ডুকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম।
-কাঠ খসে পড়ছে, দেয়াল গলে পড়ছে, চালের তৃণ জড়ো হয়ে গেছে। আমার জীর্ণ ঘর কেঁচো-সন্ধানী বেড়ে আকীর্ণ।
বস্ত্রেরও অভাব ছিল। শীতের রাতে বস্ত্ৰহীনার করুণ দুর্দশার চিত্রও রয়েছে :
ধূমৈরশ্রম নিপাতয় দহ শিখয়া দহন মলিনয়াঙ্গারৈঃ
জাগরায়িষ্যতি দুর্গত গৃহিনী তাং তদপি শিশিরনিশি।
[৩০৪নং আৰ্যসপ্তশতী : কবি গোবর্ধন আচাৰ্য]
–ধোঁয়ায় চোখে পানি ঝরে, দহনে দেহ উক্তপ্ত (দগ্ধ) হয়, অঙ্গারে দেহবর্ণ মলিন হয়, তবু দুৰ্গতি গৃহিণী সারা শীতরাত্র (হে অগ্নি) তোমাকে জ্বালিয়ে রাখে।
গায়ে তখনো শাসন-শোষণ-পীড়ন-পেষণ ছিল। প্রবলের প্রতাপ, দুর্জনের দৌরাত্ম্য, দুর্বলকে সেকালেও পিষ্ট ও ক্লিষ্ট করত:
প্রতি দিবস ক্ষীণ দশস্তবৈষ বসনাঞ্চলোহত্যিকর কৃষ্টঃ
নিজনায়কমতি কৃপণং কথয়তি কুগ্ৰাম ইব বিরলঃ
[৩৭১ সং আৰ্যসপ্তশতী]
–বারবার হস্ত-ধৃত হয়ে দিনে দিনে ক্ষীণ দশা প্ৰাপ্ত তোমার সুতোবিরল বস্ত্রাঞ্চল,–অতি করভারে পীড়িত জনবিরল কুগ্রামের মতো (এই সত্যই) নির্দেশ করে যে তোমার নিজপতি অতিকৃপণ।
বোঝা যাচ্ছে শোষণের করভারে পীড়িত গ্রামবাসী গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যেত। ভিক্ষাবৃত্তিও ছিল (৪৯২), অরাজকতা ছিল (২৭), অত্যাচার-অবিচার-নিষ্ঠুরতাও ছিল (৩১৫ আর্যসপ্তশতী)।
কবি-পণ্ডিতদের কাম্য জীবন :
১. গোষ্ঠীবন্ধঃ সরস কবিভিৰ্বাচি বৈদৰ্ভরীতির্বাসো
গঙ্গা পরিসর ভুবি স্নিগ্ধাভোগ্য বিভূতি।
সৎসুমেহঃ সদসি কবিতাচার্যকং ভুভুজাং মে
ভক্তির্লক্ষ্মী পতিচারণয়োরস্তু জন্মান্তরেহপি।
(ধোয়ী)
বঙ্গানুবাদ :
সহৃদয় কবিদের সঙ্গে সৌহার্দ্য, বৈদর্ভী রীতিতে কাব্য রচনা, গঙ্গাতীরভূমিতে বাস, ধনৈশ্বৰ্য আত্মীয়-স্বজনের ভোগে লাগা, সজনের সহিত মৈত্রী, রাজসভায় আচাৰ্য কবির সম্মান এবং লক্ষ্মীপতির চরণ কমলে ভক্তি যেন আমার জন্মান্তরেও হয়।
(সুকুমার সেন প্ৰ. বা. বা, পৃ. ২৭)
২. আদর্শমানুষের সংজ্ঞা এরূপ :
মাতোবাসীৎ পরস্ত্রীভবতি পরাধনে ন স্পৃহা যস্য পুংসো
মিথ্যাবাদী ন ষঃ স্যান্ন পিবতি মদিরাং প্রাণিনো যো ন হন্যাৎ।
মর্যাদাভঙ্গভীরুঃ সকরুণ হৃদয়স্ত্যক্ত সর্বাভিমানো
ধর্মাত্মা তে স এষ প্রভবতি ভগবন পাদ পূজাং বিধূধাতুম
(রামচন্দ্ৰ কবিভারতী : ভক্তিশতক)
-সুকুমার সেন: প্ৰা. বা. বা. পৃ. ৪১
-পরস্ত্রী যার কাছে মাতৃসম, যে পুরুষ পরিধানে নিস্পৃহ, যে মিথ্যাবাদী, মদ্যপায়ী, প্ৰাণহন্তা নয়; যে মানীর মান ভঙ্গে ভীত, যে করুণাহিদয়, যে নিরাভিমান–সে মহাত্মাই ভগবানের পূজার অধিকার পায়।
১৪
আদব-লোহাজ-তবিয়তেই সংস্কৃতির মুখ্য প্রকাশ। কবি আলাউলের তোহফায় মুসলিম আচরণ” বিধির উল্লেখ আছে। অন্যত্র তেমন কিছু মেলে না। পিতামাতা, পির ও গুরুজনদের কদমবুসি করা, মান্য ও গুরুজনদের চোখে চোখ রেখে কথা না বলা, গুরুজনদের সুমুখ থেকে উঠে আসতে পিছু হঠে আসা, লাঠি হাতে বা জুতো পায়ে গুরুজনদের সামনে না যাওয়া, তাদের সামনে তামাক না খাওয়া, উচ্চাসনে বা সুমুখ সারিতে না বসা, বাম হাত দেয়া-নেয়া না করা, গুরুজন কিংবা মান্যজনকে কিছু দিতে বা তার থেকে কিছু নিতে হলে জোড়হাতে নতশিরে দেয়া-নেয়া করা, তাদের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বা রূঢ় কষ্ঠে কথা না বলা, পথে তাদের আগে না চলা, মজলিশে বা ঘরে মান্যজনের নেতৃত্বে একসঙ্গে খাওয়া শুরু ও শেষ করা, মান্যজনের দেহের স্পর্শ বঁচিয়ে চলা, বৈঠকে বা সারিতে বা মজলিশে দুজনের মধ্যদিয়ে চলতে হলে দুই বাহু প্রসারিত করে দেহ বাকিয়ে (রুকুহুর মতো) চলা, বয়োজ্যেষ্ঠদের নাম ধরে না ডাকা, বয়স্ক কনিষ্ঠদেরও সন্তানের নাম করে ‘অমুকের বাপ বা মা’ বলে ডাকা, বাসনে অল্প অল্প করে খাদ্যবস্তু নিয়ে ছোট ছোট গ্রাসে খাওয়া এবং ঠোঁট বন্ধ করে চিবানো, পা দেখিয়ে বা ছড়িয়ে না বসা, মান্য ও বয়োজ্যেষ্ঠকে সালাম দিয়ে সম্ভাষণ করা প্রভৃতি ছিল সার্বক্ষণিক সাধারণ আদব-কায়দার অঙ্গ। গায়ে অধিকাংশ লোক ছিল দরিদ্র ও অশিক্ষিত, তাই এসব অমান্য করবার মতো উদ্ধত দ্রোহী ছিল বিরল।
১৫
নবজাতককে, খৎনায় কিংবা কানফোড়নে ছেলেমেয়েকে, বিবাহে নব দম্পতিকে ও নতুন কুটুম্বকে নজর, শিকলি ও উপহার দেওয়াও ছিল রেওয়াজ। নাপিত-ধোপামোল্লা-মুয়াজ্জিন-ওস্তাদ-ভৃত্যু-গােলাম-বাদী প্রভৃত্ত্বিও এসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে বকশিশ পেত। সমাজে নাপিতের ভূমিকা ছিল বহু ও বিচিত্র। এরা প্রতিঘরের পরিজনই যেন ছিল। উৎসবে-অনুষ্ঠানে তারা ছিল অপরিহার্য। ধনী ও অভিজাতদের দু-দশ ঘর গোলাম-বাঁদী থাকত।
সাধারণের ঘরবাড়ি হত মাটির ও বাঁশের। গরিবের দোচালা, সাধারণের চৌচালা এবং উচ্চমাধ্যবিত্তের আটচালা ঘরও থাকত। গরিবের ঘর-কুটির, মধ্যবিত্তের বাড়ি-ভবন, ধনীর অট্টালিকা, রাজার প্রাসাদ-মহল। বাড়ি হত সাধারণত চক-মিলানো। চট্টগ্রামের মুসলমানেরা ঘরের প্রবেশকক্ষকে ‘হাতিনা’, মধ্যকক্ষকে ‘পিঁড়া’ ও পেছনের শেষ কক্ষকে ‘আওলা’ বলে। পিঁড়া’র উল্লেখ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতেও মেলে।
গাঁয়ের মানুষের একবা একাধিক (ঈর্ষা-অসূয়াজাত দলাদলির কারণে অথবা আশরাফ-আতরাফ ভেদে) ‘মাহালত’ বা সমাজ থাকত। একজন প্ৰধান সমাজপতি, সর্দার বা মাতব্বরের নেতৃত্বে প্রতি গোষ্ঠী-নেতার সহযোগে সামাজিক, পাবণিক, আনুষ্ঠানিক কাজ এবং মৃতের সৎকারাদি, জেয়াফত-বিবাহাদি ও দ্বন্দ্ব-বিবাদাদির সালিশ-ইনসাফা-মীমাংসা হত।
১৬
অদৃষ্টবাদী কুসংস্কারপ্রবণ সমাজে নজুম-গণক দৈবজ্ঞ-দরবেশের কদর ছিল। দান-সদকায় ‘বলা’-বালাই এড়ানোর সহজ পন্থা ছিল সবারই প্রিয়। ফাতেহাখানি-কুলখানি-জেয়াফতমেজবানি যোগে ভোজ দিলে মৃতব্যক্তির পাপমোচন হয়-এ আদিম মানবিক ধারণা শাস্ত্রীয় প্রশ্রয়ে আজও প্রবল এবং মৃতের আত্মার সদগতির জন্যে বুনো-বর্বর-ভাব্য নির্বিশেষে মানুষ চিরকালই দান-পান-ভোজন অনুষ্ঠান আবশ্যিক বলে জানে ও মানে।
নিরক্ষর দরিদ্ররা তো বটেই, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেও ফুল ও বাগানের আদর-কদর ছিল বলে মনে হয় না। কেননা আজকের দিনেও গাঁয়ে ফুল বা ফুলের বাগান দুৰ্লক্ষ্য। তবু সাহিত্যে ফুলের নাম করতে হয় বলেই প্রথা সিদ্ধ উপায়ে কবিগণ কিছু ফুলের নাম করতেন; মাধবী, মালতী, চম্পা, নাগেশ্বর, জাতী, যুখী, লবঙ্গ, কেতকী, বক, ভূমিকেশর, টগর, ভূরাজ, গোলাপ ইত্যাদি।
আমাদের দেশে দরিদ্র গৃহস্থঘরে তৈজস–হাঁড়া-সরা-পাতিল-বাসন-কর্দা-কর্তি (পানপত্র) সবটাই ছিল কুমারের তৈরি মাটির। নারকেলের মালা ও ঝিনুক ব্যবহৃত হত চামচরূপে। কিন্তু সাহিত্যগ্রন্থে এসব মেলে না। কারণ সাহিত্যে সবকিছু কৃত্রিম এবং আদর্শায়িত রূপে চিত্রিত হওয়াই ছিল নিয়ম। তা ছাড়া সে-যুগে সাহিত্যের বিষয় ছিল দেবতা ও রাজা-বাদশার কাহিনী। কাজেই গরিবঘরের তৈজস-আসবাবের কথা সেখানে মেলে না। হর-পাৰ্বতী, ফুল্লরা, হরিহোড়ের মতো কোনো কোনো দরিদ্রের কিছু খবর মেলে বটে, কিন্তু তা পূর্ণচিত্র দেয় না। Manrique ও অন্যান্য পর্যটকের বিবরণ থেকে দরিদ্রের ভাঙা ঘরে সম্পদের মধ্যে ছেঁড়া কাঁথা-মাদুর-চাটাই ও মাটির হাঁড়া-সরা-ঘড়ার এবং জীর্ণ-ছিন্ন বস্ত্রের কথামাত্র ক্বচিৎ মেলে।
বিভিন্ন ব্যঞ্জন রান্না ছাড়াও বাঙালির পিঠা সাধারণত গুড়, চালের গুড়ো, তেল, ঘি, দুধ যোগেই তৈরি হত। তাল, কলা, নারিকেল, খেজুর-রস প্রভৃতিও কোনো কোনোটাতে মিশ্রিত হত। এ ছাড়া চালভাজা, খই, দই, চিড়া, মুড়ি-মোয়া-বাতাসা, মিছরি প্রভৃতি সুপ্রাচীন। দুধের রূপান্তরে দই, মাখন, ঘোল, ঘি, সন্দেশ, পায়েস, রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্ন তৈরিতে এদের কৃতিত্ত্ব গৌরবের।
বাদ্যযন্ত্রের নামেও দেখি প্রাচীনতা ও গতানুগতিকতা। ঢাক-ঢোল, ধামা, পিনাক, সারিন্দা, পাখোয়াজ, দোহরিমোহরি, চঙ্গ বাঁশি, ভরী, মৃদঙ্গ, ঝাঁঝরা, করতাল, কর্নাল, ভেউর, রবার, বেণু, সিঙ্গা, কাড়া, কবিলাস, ডম্বর, মন্দিরা, তাম্বুরা, জঙ্গলী, শঙ্খ, দুমদূমি, নাকাড়া, দমা, মঞ্জীর, সানাই, বীণা, দোনা, তবল, ভূষঙ্গ, কাস, ভাঙ্গরি ইত্যাদি।
তেমনি যুদ্ধাস্ত্রগুলোও সেই রামায়ণ-মহাভারত যুগের। নতুন অস্ত্রের তথা কবির সমকালীন অন্ত্রের নাম মেলে না। শল্য, শূল, গদা, মুষল, মুদগর, ন্যারোচ, নালিকা, অসি, খঞ্জর, বিভিন্ন ধনুৰ্বাণ–অগ্নি, সিংহ, সৰ্প, চন্দ্র, অর্ধচন্দ্র, গজ, বরুণ, মেঘবাণ ইত্যাদি। এগুলো মন্ত্রপূত হলে অমোঘ হয়। যুদ্ধবাহন–অশ্ব, গজ, রথ । যুদ্ধে বাদ্যও প্রয়োজন।
১৭
অস্ট্রিক-মঙ্গোলীয় বাঙালির কোম-সমাজের রীতি-নীতির কিছু কিছু রূপান্তরে আজও বিদ্যমান। সাংখ্য-যোগ-তন্ত্র-দেহতত্ত্বাদি তাদের মানস বিকাশের সাক্ষ্য। জড়বাদসুলভ বিশ্বাস-সংস্কার ও প্রাকৃত শক্তির পূজাও তাদের মধ্যে চালু ছিল। নারী-বৃক্ষ-পশু ও পাখি দেবতা, দেহচর্যা, জন্মান্তরে আস্থা, ঘট ও পাথর প্রতীকে দেবপূজা তাদের মধ্যে চালু ছিল। বৰ্ণাশ্রম ছিল না, বৃত্তিভাগ ছিল। নিরক্ষর সমাজে বৃত্তিগত সংস্কৃতি ছিল, সমাজে নৈতিক-চেতনা তেমন দৃঢ়ভিত্তিক ছিল না। নিষাদ-কিরাত সমাজে কৈবর্ত-শুঁড়ি-চণ্ডালহাড়ি-ডোম-তাঁতি-কামার-কুমার-নাপিত-চাষি-ওঝা-চিকিৎসক প্রভৃতি বৃত্তিই ছিল প্রধান।
মৌৰ্য আমলে জৈন-বৌদ্ধ মতের সঙ্গে উত্তর-ভারতীয় শাস্ত্ৰ-সমাজ-শাসন-ভাষা-সভ্যতাসংস্কৃতি গ্ৰহণ করতে থাকে। এদেশীয়রা। সে-সময়েও জৈন-বৌদ্ধ সমাজে বর্ণবিন্যাস ছিল না। ব্ৰাহ্মণ্য গুপ্ত ও শশাঙ্কের আমলে বর্ণবিন্যাস শুরু হয় এবং সেন আমলে বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে তা পূর্ণতা পায়। বৃহদ্ধর্ম পুরাণোক্ত অস্পৃশ্যতদুষ্ট ছত্ৰিশ জাতি এভাবেই বিন্যস্ত হয়। উত্তর-ভারত থেকে সাগ্রিক যজ্ঞিক ব্ৰাহ্মণ আনয়ন গুপ্ত আমলেই শুরু হয়, তবু সেনেরা নতুন একদল ব্ৰাহ্মণ আনয়ন করে এখানে গীতা-স্মৃতির প্রভাব প্ৰবল করার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন ধরনের পূজাপাৰ্বণ ও শাস্ত্ৰসম্পৃক্ত আনন্দ-উৎসব চালু হয়। জাতকর্ম, ষষ্ঠী, অনুপ্রাশন, চুড়াকরণ, শালাকর্ম, অশৌচ, শ্ৰাদ্ধ তিথি নক্ষত্রে উপবাসাদি ব্ৰত পালন; ধর্ম-সম্পৃক্ত শাবরোৎসব, কামমহোৎসব, হোলি, নৃত্য-গীত-কথকতার অনুষ্ঠান; বিবাহাদি সামাজিক উৎসব প্রভৃতি ছিল। জুয়া, মদ, বেশ্যা–এ তিনে লোকের আসক্তি ছিল, এবং পার্বণিক উৎসবে সামাজিকভাবেই উপভোগ করা হত এসব।
হিউ এনৎ সাঙের সময়ে সমতটের লোক ছিল শ্রমসহিষ্ণু, তাম্রলিপ্তিবাসীরা ছিল দৃঢ় ও সাহসী, চঞ্চল ও ব্যস্তবাগীশ এবং কর্ণসুবর্ণবাসীরা ছিল সৎ ও অমায়িক। ক্ষেমেন্দ্র তাঁর দশোপদেশ” কাব্যে বাঙালি ছাত্রদের ক্ষীণকায়, উগ্র ও মারামারিপ্রবণ বলে উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞানেশ্বর ও পরবর্তীকালের অনেক পর্যটক বাঙালিকে কুদুলে বলে জানতেন। বাৎস্যায়ন ও বৃহস্পতির মতে রাজপুরীতে ও উচ্চবিত্তের অভিজাতদের ঘরে নারীরা ব্যভিচার ও দুনীতিপরায়ণা ছিল। নারীর শাড়ি ও পুরুষের খাটো ধুতি পরার রেওয়াজ ছিল। সাধারণ লাকে কায়িক শ্রমকালে পরত। গামছা-কর্পট। নারী বা পুরুষের উর্ধ্বােঙ্গ কৃচিৎ ওড়নাচাদরাবৃত থাকত। চৌলি-কঁচুলির আটপৌরে ব্যবহার নিম্নবর্ণ ও নিম্নবিত্তের মেয়েদের মধ্যে ছিল না। অলঙ্কারে নারী-পুরুষে প্ৰভেদ ছিল সামান্য। বিত্তভেদে অলঙ্কার হত তালপাতার, শঙ্খের, পিতলের, কাচের, রুপার, সোনার ও মণিমুক্তার। অঙ্গুরী, কুণ্ডল, হার, কেয়ূর, বলয়, মেখলা, মল প্রভৃতি বহুলব্যবহৃত অলঙ্কার। বাঙালি নারী-পুরুষের কোনো শিরোভূষণ ছিল না। ব্ৰাহ্মণেরা ও ভিক্ষুরা কাঠের খড়ম পারত, পদস্থ সৈনিকরা চামড়ার জুতা ব্যবহার করত, ছাতা ছিল পাতার ও কাপড়ের, বিজনী ছিল তালপাতার, বীশের ও বেতের। সিন্দূর, কুমকুম, চন্দন, আলতা প্রভৃতি ছিল প্রসাধনদ্রব্য। বীণা, বাঁশি (বিভিন্ন ধরনের), মৃদঙ্গ, ঢাকা, ঢোল, করতাল, ডম্বুরু, কাণ্ড (কাড়া), কাহল প্রভৃতি ছিল মুখ্য বাদ্যযন্ত্র। মন্দিরে দেবদাসীরা ও বেশ্যারা এবং হাড়ি-ডোমেরা গাইয়ে-বাজিয়েনাচিয়ে ছিল। ভেলা-নীেকা-গরু-টানা শকট ছিল যানবাহন। এ ছাড়া বড়লোকের বাহন ছিল ঘোড়া, গাধা ও হাতি। ধান, ইক্ষু, কলাই, নারিকেল, সুপারি, আম, কঁঠাল, কলা, লেবু, পান প্রভৃতিই প্রধান ফল ও ফসল ছিল। এদেশেও ক্ষৌম (শণের সূতার তৈরি), দুকুল ও সূতী কাপড় তৈরি হত। রঙ ও নকশার ব্যবহারও ছিল। সাধারণের গাৰ্হস্থ্যজীবনে প্রয়োজনীয় দারু-কারু ও চারুশিল্প এবং মূর্তিশিল্পের শিল্পী ছিল অবশ্যই দেশী লোক। খাজা, মোয়া (মোদক), নাডু, খাড়, পিঠা, ফেনি (বাতাস), কদমা, দুধশাকব (পায়েস), ক্ষীরসা, দই, শিখারিনী (ঘি দই গুড় আদা দিয়ে তৈরি—সুকুমার সেন) প্রভৃতি ছিল মিষ্টান্ন। জাড়ি, ভান্তী, হাঁড়ি, তেলাবনী (তেলোন) প্রভৃতি ছিল মৃৎপাত্র। অবশ্য শাস্ত্ৰ, শিক্ষা, বিত্ত ও বৃত্তিভেদে খাদ্য, আসবাব-তৈজস-পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরদের প্রভৃতি সব ব্যাপারেই পার্থক্য ও বৈচিত্র্য ছিল। আমরা কেবল সাধারণ-রূপের কথাই বললাম।
এ সূত্রে একটা কথা উল্লেখ্য যে, আর্যরা ‘ঋক’বেদের কতকাংশ সঙ্গে করে বিজেতা হিসেবে ইরান থেকে ভারতে প্ৰবেশ করে। ইরানে জাতিদ্বন্দ্বে এরা ছিল দেশত্যাগী। আর্যরা ছিল প্রাকৃতিশক্তির হোতা ও পশুপালক এবং সে-কারণে অর্ধ-যাযাবর। ইষ্টফল বাঞ্ছা করে তারা ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য প্রভৃতি প্রাকৃতশক্তির উদ্দেশে যাতবেদের (অগ্নির) মাধ্যমে যজ্ঞ হোম করত। এ স্তরে পশুপালনই ছিল তাদের মুখ্য জীবিকা। তখনো তাদের মধ্যে দেবপূজা চালু ছিল না। গোধনই তাদের প্রধান ধন। ক্রমে সংখ্যাগুরু দেশী লোকের প্রভাবে তাদের মধ্যে দেশী জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ, ধ্যান, মন্দির-উপাসনা, মূর্তিপূজা, বৃক্ষ-পশু-পাখি ও নারীদেবতা পূজা চালু হল, সে-সঙ্গে এল নানা ব্ৰত-পূজাপার্বণ এবং লৌকিক ও স্থানিক বিশ্বাস সংস্কার। এভাবেই বৈদিক জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনা ক্ৰমে দৈশিক দেহতত্ত্বে ও পরলোকতত্ত্বে প্রভাবিত হয় এবং দৈশিক সাধনাতত্ত্বও গ্রহণ করে তারা। ফলে দেশী সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র ব্ৰাহ্মণ্য মতের, শাস্ত্রের ও সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে, এমনকি ব্ৰাহ্মণ্য তথা আর্যতত্ত্বচিন্তার চরমবিকাশপ্রতীক উপনিষদও পুর্ব-ভারতের অনার্য-মননে ঋদ্ধ বলে কারো কারো ধারণা। আর্যবর্তী ব্ৰহ্মাবর্ত তথা উত্তরাপথ-বহির্ভূত বাংলায় আর্যধর্ম-সংস্কৃতি প্রবেশ করে অনেক পরে এবং তা জৈন-বৌদ্ধ প্ৰাবল্যের ফলে গণ-মানবে কখনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তাই বাঙলাদেশে ব্ৰাহ্মণ্যধর্ম সেন আমলেও পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এ কারণে বাঙলায় আমরা গীতা-স্মৃতি-সংহিতার পাশে দেশজ লৌকিক দেবতার প্রাধান্যও দেখতে পাই। দুই বিরুদ্ধ মত ও সংস্কৃতির পুরাণ মাধ্যমে আপসের ফলে গড়ে উঠেছে বাংলার ব্ৰাহ্মণ্যবাদী পঞ্চোপাসক হিন্দুসমাজ। এতে আর্যভাগ নগণ্য, অনার্য লক্ষণ প্রধান ও প্রবল। মুসলিম-সমাজেও ছিল স্থানিক ও লৌকিক বিশ্বাস-আচারের প্রবল প্রভাব। উনিশ শতকের ওহাবি-ফরায়েজি আন্দোলনের ফলে লৌকিক ইসলাম আজ বাহ্যত প্ৰায় অবলুপ্ত।
১৮
মধ্যযুগের সাহিত্যে যথার্থ কিংবা পূর্ণাঙ্গ সমকালীন সমাজচিত্র মেলে না। মুখ্যত বৰ্ণিত বিষয় ও বক্তব্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক না হলে কিছু বর্ণনা করা সম্ভব হয় না। তা ছাড়া সেযুগের সাহিত্যের বিষয় ছিল প্রাচীনকালের তথা অতীতের দেব-দৈত্য-নর কিংবা রাজাবাদশাহ-সামন্ত-সর্দার। আজকালকার গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধের মতো সমকালের ও স্বস্থানের জগৎ-জীবন-জীবিকা, সমাজ-সংস্কৃতি, সমস্যা-সম্পদ কিংবা আনন্দ-যন্ত্রণা সে-যুগের লিখিয়েদের রচনার বিষয় ছিল না; তাই সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র সেখানে দুর্লভ। ক্বচিৎকবির অনবধানতায়-অজ্ঞতায়-কল্পনার দৈন্যে সমকালীন প্রতিবেশ ক্ষণিকের জন্যে উকি মেরেছে মাত্র। তাই আমাদের লোকায়ত জীবনে, লোকাচারে, লোক-সংস্কারে, বিশ্বাসে, প্ৰথা-পদ্ধতি-অনুষ্ঠানে যে আদিম লোক-বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-রীতি-রেওয়াজ অবিকৃত কিংবা রূপান্তরে আজও রয়ে গেছে, সে-তথ্য আমরা লিখিত সাহিত্যে পাইনে, পাই লোক-সাহিত্যে, লোক-আচারে ও গ্রামীণ উৎসবে-পার্বণ-অনুষ্ঠানে নানা আচার ও রীতিপদ্ধতির মধ্যে। আল্পনায়, লোকনৃত্যে, পার্বণিক লোক-সঙ্গীতে-যেমন গাজনে, গম্ভীরায় লোকবাদ্যে; যেমন-একতারায়-দোতরায়-শিঙ্গায়-বাঁশিতে, ভেঁপুতে, মন্দিরায়খঞ্জনীতে ও ঢাকে-ঢোলে, আঁতুড়ঘরের আচারে, ষষ্ঠীপূজায়, সাধভক্ষণে, গায়েহলুদে, পানিভারণে কিংবা কলাগাছ-ঘট-আত্মসার, ধানে-দূর্বায়-হলুদে-দীপে-ধূপে-ধূনায়-তোলোয়াইতে (অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবার মাথা তেলসিক্ত করা-অভ্যর্থনা আপ্যায়ন ও বরণ করার জন্যে), মারোয়া সাজানোর আচারে, দুধ-মাছ-তত্ত্বে, তুক-তাক-জাদু-উচাটনে, বসুমতীপূজায়, কুমারীর বীজ বপনে, পানি মাঙনে ও নানা কৃষি ও বুননসংক্রান্ত ব্ৰতে, শক্তিপ্রতীক কাল্পনিক পিরপূজায়, বুনো হিংস্র জীবপূজায়, মহামারীর দেবতাপূজায় এবং প্রতিবেশানুকূল খেলাধূলায় আদি অস্ট্রিক-মঙ্গোলের অবিকশিত বুনোসমাজের ধ্যান-ধারণা ও আচার-সংস্কারের রেশ রয়ে গেছে-সেগুলোর কিছু কিছু আজও আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আরণ্য-মানবে ভিন্নাকারে দেখা যায় এবং অন্য দেশের বিভিন্ন আদিম বুনোমানুষের সংস্কারে সেগুলোর জড় মেলে। বিভিন্ন মাটিফে’ বিন্যাস বিশ্লেষণ হলে আচারে ও তাৎপর্যে সাদৃশ্য যাচাই করা সহজ হবে।