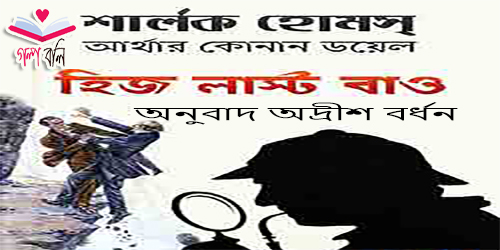চাষি ও চাষের জমি নিয়ে বাংলাদেশে বর্তমান আন্দোলনের উৎপত্তি হয়েছে মন্টেগু চেমস্ফোর্ড রিফর্মে, অর্থাৎ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইনে। গত এক নম্বর মহাযুদ্ধের অবসানের পূর্বেই বেশ বোঝা গেল, মর্লি-মিন্টো নামাঙ্কিত যে শাসনপদ্ধতি ভারতবর্ষে চলছিল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষেরা তার বদল ঘটাবেন। ফলে কোনও কোনও বিষয়ে আইন করার সামান্য কিছু ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতে আসবে। কিন্তু এই সামান্য উদ্দেশ্যের উপায়স্বরূপে আইনসভাগুলির সভ্যসংখ্যা বাড়বে একটু অসামান্য রকমে। এবং অনুপাকৃত তার চেয়েও অনেক বেশি বাড়ানো হবে ভোটদাতাদের সংখ্যা, যাদের ভোট কুড়িয়ে শাসনপরিষদে আসন পাওয়া যাবে। এদেশের বেশির ভাগ লোক চাষি। যে গুণে ভোটের অধিকার আসবে তাতে ভোটদাতাদের তালিকায় চাষির সংখ্যা হবে বেশ মোটা রকমের। তাঁরা যদি দল বাঁধতে পারে তবে তাদের ভোট উপেক্ষা করা বেশির ভাগ সভ্যপদপ্রার্থীর পক্ষেই সম্ভব হবে না। দেশময় সাড়া পড়ে গেল। বিশেষ করে বাংলাদেশের কথাই বলছি। জমিদারেরা বহু সভা করে প্রমাণ করলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সওয়াশো বছরের পুরাতন স্বীকৃতিতে তাঁরা যে শুধু চাষের জমির মালিক তা নন, তারাই হচ্ছেন চাষিদের স্বভাবসংগত নেতা, natural leaders of the people। কারণ, ও-কথাটা আইনে না। হোক তখনকার দলিল-দস্তাবেজে কোনও কোনও ইংরেজ রাজপুরুষ ব্যবহার করেছিলেন। জমিদারের স্বার্থ ও চাষির স্বাৰ্থ এক; অর্থাৎ জমিদারের স্বার্থই চাষির স্বাৰ্থ, চাষির হিতই জমিদারের হিত। যদস্তু হৃদয়ং মম তদন্তু হৃদয়ং তব। চাষিদের প্রকৃত স্বাৰ্থসিদ্ধি হবে তাঁরা যদি ভোট দিয়ে জমিদারদের বেশি সংখ্যায় আইনসভায় পাঠায়। ঘরভেদী দুষ্ট লোকের কথায় চাষিরা যেন কান না দেয়। দুষ্ট লোকের অভাব ছিল না। দেশময় রায়তদের সভায় তাঁরা প্রমাণ করতে লাগল যে, বাংলার চাষির যত দুঃখ তার মূলে বাংলার জমিদার। জমির সঙ্গে এরা কোনও সম্পর্ক রাখে না, সম্পর্ক শুধু জমির খাজনার সঙ্গে, অথচ এরাই জমির মালিক। সেই মালিকত্বের জোরে রায়তের খাজনা এরা ক্ৰমাগত বাড়িয়ে চলেছে, জমি যেন ইন্ডিয়া রবার। রায়ত ইচ্ছামতো তার জমি বিক্রি করতে পারে না, জমিদারকে দিতে হবে উচু নজর; নইলে জমি থেকে উচ্ছেদ। নিজের জমির গাছ রায়ত নিজে কেটে নিতে পারবে না, ঝড়ে-পড়া গাছও নিতে পারবে না; কারণ তারও মালিক জমিদার। নিজের জমিতে রায়ত ইচ্ছামতো পাকাবাড়ি করতে পারবে না, পুকুর কাটতে পারবে না, এ রকম আইনি অত্যাচার তো আছেই, তার উপর বে-আইনি অত্যাচারের শেষ নেই–জমিদারবাবুদের ও তাদের আমলাবাবুদের। এ সব বন্ধ করো। জমির খাজনার উচিত হার ঠিক করে খাজনা চিরকালের জন্য বেঁধে দাও, তার যেন আর বৃদ্ধি না হয়। জমিদারদের রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে। রায়তের খাজনারও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হোক। জমির মালিকি স্বত্ব দেওয়া হোক রায়তকে, যাতে সে যদৃচ্ছা জমির ভোগ-ব্যবহার দান-বিক্রি করতে পারে। জমিদার থাকবে শুধু নির্দিষ্ট খাজনার মালিক, অর্থাৎ খাজনা আদায় করে রাজস্ব দেবার তহশীলদারির মুনাফার মালিক। তার অতিরিক্ত তাদের আর কিছু প্ৰাপ্য নয়। চাষের জমি তার সে-জমি যে চাষ করে শস্য ফলায়। ‘স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগম’। বনের পশু বাণ দিয়ে যে মারে সে পশু তার, শস্যের খেত শস্যের জন্য যে তৈরি করে সে-খেতের জমিও তার। এইসব পরিবর্তন ঘটিয়ে বাংলার চাষিকে যদি চাষের জমির মালিক করা যায়, আর তার খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তবে তার কোনও দুঃখই থাকবে না। তার গোয়ালভরা গোরু আর গোলােভরা ধানে সোনার বাংলা প্রকৃতই সোনার বাংলা হয়ে উঠবে। এর উপায় হচ্ছে যে-সব রােয়ত-হিতৈষীরা সভা করে রায়তদের তাদের হিত বোঝাচ্ছেন ভোট দিয়ে বেশি সংখ্যায় তাদের আইনসভায় পাঠানো। যাতে রায়তদের সুবিধামতো আইন পরিবর্তন তাঁরা ঘটাতে পারে। যাদের আইনসভার সভ্য হবার, বা আত্মীয়বন্ধুদের সেখানে পাঠাবার কোনও অভিপ্ৰায় ছিল না, তাদেরও অনেকে এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই ভরসায় যে, রায়তেরা দল বাঁধলে নতুন আইনসভায় আইন মারফত রায়তের কিছু উপকার হতে পারে। আর, বাংলার রায়তের উপকার গোটা বাংলাদেশের উপকার। এই সাময়িক আন্দোলন বাংলা ভাষায় একটি স্থায়ী সাহিত্যিক ছাপ রেখে গেছে–শ্ৰীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর ‘রায়তের কথা’ ও রবীন্দ্রনাথের লেখা তার ভূমিকা। এ আন্দোলন যে বাঙালির মনের অন্তস্তলে নাড়া দিয়েছিল এ তারই প্ৰমাণ।
মহাত্মার নন-কো-অপারেশন আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। ১৯১৯ সালের আইনে প্রতিষ্ঠিত আইনসভাগুলির সঙ্গে অসহযোগ উপলক্ষ করে। সুতরাং, কংগ্রেস প্রারম্ভে এ সভাগুলি বর্জন করল। তার ফলে অন্তত বাংলাদেশে যে স্বাদগন্ধহীন আইনসভার সৃষ্টি হল ভালমন্দ কোনও কাজ তার সাধ্য ও বুদ্ধির অতীত। চাষি ও চাষের জমি নিয়ে বিশেষ কোনও আলোচনা সে সভায় উঠল না। এবং, অসহযোগ আন্দোলনের বিজ্ঞাপিত ফল–‘ছ’মাসে স্বরাজ–যখন হাতে হাতে ফলিল না, যেমন প্ৰায় আন্দোলনের-ই ফলে না, তখন দেশব্যাপী দেখা দিল নিরাশা ও অবসাদের ভাব। তার প্রতিক্রিয়ায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিত মতিলাল কংগ্রেসের মধ্যে স্বরাজ্যদল গড়ে তুললেন, তার মূল কর্মপদ্ধতি হল ১৯১৯ সালের আইনের আইনসভাগুলিকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দখল করে তাদের আচল করা, অর্থাৎ ওই আইনের শাসনপ্ৰথাকে ব্যৰ্থ করা। অসহযোগ বাইরে থেকে ভিতরে নেওয়া, বর্জনের নীতিকে বিনাশের রীতিতে রূপান্তরিত করা। এই প্ৰস্তাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কংগ্রেসে দু-দল দেখা দিল। প্র-গতি ও অ-গতি, প্রে-চেঞ্জার ও নো-চেঞ্জার, দলের অনেক ঝগড়াঝাঁটি ও গালমন্দের পর কংগ্রেসের অনুমতি পেয়ে পরবতী নির্বাচনে স্বরাজ্যদল আইনসভাগুলিতে ঢুকলেন, বাংলাদেশে মোটের উপর মোটা সংখ্যায়। প্রথমে কিছুকাল গেল ও সভাকে আঁচল করার চেষ্টায়। কতক সাফল্য ও মোটের উপর অসফলতার মধ্য দিয়ে শেষটা স্বরাজ্যদল হল আইনপরিষদে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধ দলের প্রধান দল–যে পরিণতি পূর্ব থেকে অনুমান করা কঠিন ছিল না। এমনধারা অবস্থায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর, ংলা পরিষদে বাংলার প্রজা ও জমিদার অর্থাৎ চাষি ও খাজনাগ্রাহীদের স্বত্বাব্স্বত্বের ১৮৮৫ সালের মূল আইনের কতকগুলি ব্যবস্থার পরিবর্তন করে ১৯২৮ সালে স্বরাজ্যদলের সহযোগিতা ও সহায়তায় এক আইন পাশ হল। নূতন আইনে চাষের জমির গাছে চাষি সম্পূর্ণ স্বত্ব পেল; সে জমির গাছ সে ইচ্ছামতো কেটে নিতে কি ঝড়ে বা অন্য রকমে পড়ে গেলে আত্মসাৎ করতে পারবে–জমিদারকে নজর না দিয়ে। চাষের জমিতে সে পাকা বাড়ি করতে পারবে নিজের ও পরিবারের লোকদের বসবাসের জন্য। পুকুর কাটতে পারবে নিজেদের পানীয় জলের জন্য। ইতিপূর্বে আইন ছিল চাষের বিঘ্ন ঘটালে চাষি প্রয়োজনমতো জমির গাছ কাটতে পারবে কিন্তু সে গাছ নিজে নিতে পারবে না, সে গাছ নেবে জমির জমিদার। পূর্বের আইনে চাষের জমিতে চাষি বাসের জন্য বাড়ি তৈরি করতে পারত, কিন্তু সে বাড়ি হওয়া চাই চাষির প্রয়োজনের উপযোগী, এবং সম্পূর্ণ পাকা বাড়ি চাষির প্রয়োজনের অতিরিক্ত। সে আইনে চাষের জমিতে চাষি পুকুর কাটতে পারত চাষের কাজে প্রয়োজন হলে এবং চাষে নিযুক্ত মানুষ ও পশুর প্রয়োজনে, নিজের ও পরিবারের লোকদের পান-মানের প্রয়োজনে নয়। কেউ যদি মনে করেন যে, চাষিকে যাদৃচ্ছিা গাছ কাটতে দিলে জঙ্গল লোপাট হওয়ার ফলে চাষের অবনতি ঘটে, কি ক্ৰমাগত পুকুর কাটার ফলে চাষের জমির লাঘব হয়, এবং সাধ্যের অতিরিক্ত খরচে বাড়ি করে চাষি ঋণগ্রস্ত হতে পারেএসব অমঙ্গল থেকে দেশ ও চাষিকে রক্ষা করাই ছিল ও-রকম আইনের উদ্দেশ্য, তবে তিনি মস্ত ভুল করবেন। দেশের হিত কি চাষির অনিষ্টের সঙ্গে ও-সব বিধিনিষেধের কোনও সম্পর্ক নেই। কারণ, জমিদারকে নজরের টাকা গুণে দিতে পারলেই ও-সব কোনও কাজেই চাষির আর বাধা থাকত না। এ সকল বিধিব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ছিল বিশুদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের উপর; ওগুলি laws of pure reason। জমিদার জমির মালিক। মালিকি স্বত্বের অর্থই হচ্ছে বস্তুকে যতরকমে সম্ভব ব্যবহার ও তা থেকে যত কিছু লাভের অধিকার। এ অধিকারের যতটুকু মালিক অন্যকে দেবে কেবল ততটুকু মাত্র তার অধিকার হবে, বাকি অধিকার মালিকের থেকে যাবে। জমিদার তার মালিকি স্বত্বের জমি চাষিকে দিয়েছে চাষের জন্য, খাজনার বিনিময়ে। সুতরাং চাষের জন্য যে ব্যবহার প্রয়োজন এবং চাষ করে যা লাভ সম্ভব, তাতেই মাত্ৰ চাষির অধিকার। এর বেশি অধিকার কি লাভ যদি সে চায়–যেমন গাছ কেটে নেবার, কি পাকা বাড়ি করবার, কি ইচ্ছামতো পুকুর কাটবার, তবে সে অধিকার জমির মালিকের কাছ থেকে খাজনার অতিরিক্ত আরও দাম দিয়ে কিনে নিতে হবে। এই দামের ভদ্রতা-সংগত নাম নজর বা সেলামি। ন্যায়ের নির্ভুল যুক্তি, এতে দেশের হিতাহিতের কোনও প্রশ্ন নেই। ১৯২৮ সালের নূতন আইনে জমিদারের খাজনা বাড়ীৰার ক্ষমতার কোনও লাঘব হল না, পূর্বের ক্ষমতাই বহাল থাকল। আন্দোলনটা খুব বেশি হয়েছিল চাষের জমি চাষির ইচ্ছামতো দান-বিক্রির দাবি নিয়ে। সুতরাং নুতন আইনে চাষিকে সে ক্ষমতা দেওয়া হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা হল যে, সে-জন্য জমিদারকে জমির দামের শতকরা কুড়ি টাকা নজর দিতে হবে। পূর্বের আমলে যখন জমিদারের বিনা সম্মতিতে জমি বিক্রি করলে জমিদারের ইচ্ছা হলে ক্রেতাকে প্ৰজা স্বীকার না করে তাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারতেন তখনও শতকরা নিরানব্বইটি জায়গায় মোটের উপর ওই পরিমাণ নজর নিয়েই জমিদার ক্রেতাকে প্ৰজা স্বীকার করে নিতেন, যদি না কোনও কারণে জমিদার কি আমলাবাবুদের ক্রেতাকে কিঞ্চিৎ ‘শিক্ষা’ দেবার মতলব থাকত। কারণ, জমিদার জমি চায় না, চায় টাকা–আর চাষি চায় জমি। কিন্তু তখন এ টাকাটা আদায় হত কিছু দেরিতে, অল্পবিস্তর দর-কষাকষির পর। নুতন আইনে এই নজরের টাকা হাতে হাতে আদায়ে গভর্নমেন্ট হলেন জমিদারের তহশীলদার। নজরের টাকা রেজেষ্টি আপিসে জমা না দিলে বিক্রির দলিল রেজেষ্টি হবে না, এবং বিনা রেজেক্টিতে বিক্রি অসিদ্ধ। টাকাটা জমিদারের কাছে পৌঁছে দেবার ভার গভর্নমেন্ট নিজে নিলেন, অবশ্য চাষির কাছ থেকে খরচাটা নিয়ে। মোটের উপর নূতন আইনে জমিদারের আর্থিক ক্ষতি না হয়ে বরং লাভই হল। কিন্তু তবুও এটা তার মালিকি স্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ, খেয়ালমাফিক ক্রেতাকে বহাল কি উচ্ছেদের অধিকারের সংকোচ। এর ক্ষতিপূরণ দরকার। সুতরাং বিধান হল জমিদার ইচ্ছা করলে নজরের টাকাটা না নিয়ে ক্রেতাকে জমির দাম ও তার উপর শতকরা দশ টাকা বেশি দিয়ে আদালতযোগে জমি খাস করে নিতে পারবেন। অর্থাৎ, কিছু টাকা খরচের বদলে প্রয়োজনমতো ক্রেতাকে ‘শিক্ষা’ দেবার পূর্ব ক্ষমতা জমিদারের বহাল থাকল, এবং অবস্থাবিশেষে খাস করার ভয় দেখিয়ে, মোচড় দিয়ে কিছু বেশি নজর আদায়ের পথটাও খোলা রইল। কারণ, পূর্বেই বলেছি, জমির প্রয়োজন জমিদারের কিছুমাত্র নেই, প্রয়োজন টাকার; আর চাষি জমি বেচে কিনে লাভ করতে চায় না, তার নিতান্ত প্রয়োজন জমির। ইংরেজি প্ৰবচনের কথায়, বাংলার চাষি চেয়েছিল রুটি, পেল পাথরের ঢেলা।
মহাত্মার প্রথম অসহযোগ-আন্দোলনে বাংলার চাষি, যাদের অধিকাংশ মুসলমান, কংগ্রেসের ডাকে প্রবল সাড়া দিয়েছিল, কংগ্রেসকে মনে করেছিল নিজের জিনিস। তেমন ঘটনা পূর্বে কখনও ঘটেনি। এই অভূতপূর্ব অবস্থার সুযোগে বাংলার কংগ্রেসের নেতারা বাংলার রাষ্ট্ৰীয় বুদ্ধি ও আন্দোলনকে ধর্মভেদের নাগপাশ থেকে মুক্তি দেবার কোনও চেষ্টাই করেননি। নিজেদের শ্রেণিগত স্বার্থের চিন্তা তাদের বুদ্ধিকে অন্ধ ও কর্মকে পঙ্গু করেছিল। বাংলার চাষির অনায়াসলভ্য নেতৃত্ব বাংলার কংগ্রেসের পক্ষে অসাধ্য হয়েছিল। ১৯২৮ সালের আইন-সংশোধন ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ হল বাংলার আইনসভার কংগ্রেসী সভ্যদের কাছে চাষির স্বার্থের চেয়ে জমিদারের স্বাৰ্থ বড়। এই প্ৰস্তাবিত আইনের আলোচনায় স্বরাজ্যদলের এক বৈঠকে একজন বিখ্যাত নেতা বলেছিলেন যে, গাছ কেটে নেবার যে টোনা স্বত্ব চাষিকে দেওয়া হল it will strike their imagination, অর্থাৎ তাতেই বাংলার চাষিরা বাংলার কংগ্রেসের চাষি-হিতৈষণার মুগ্ধ থাকবে। বাংলার চাষি চাষা বটে, কিন্তু অতটা বোকা নয়। এর পর বাঙালি চাষির আনুগত্য বাংলার কংগ্রেস আর ফিরে পায়নি। কিন্তু জমিদারের স্বার্থরক্ষার এই চেষ্টা শেষ পর্যন্ত বিফল হল। ১৯২৮ সালের বিধান বেশিদিন টিকে থাকল না। অর্থাৎ বাংলার কংগ্রেসের পিয়াজ ও পয়জার দু-ই হল।
বিলাতের পার্লামেন্ট ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন প্রণয়ন ও পাশ করলেন। এই আইনের কমু্যুনাল প্রতিনিধি ও কমু্যুনাল নির্বাচনের ব্যবস্থায় বাংলার আইনপরিষদে মুসলমান সভ্যেরা হলেন সবচেয়ে দলে ভারী। আর, এ সভ্যদের বেশির ভাগ নির্বাচিত হলেন মুসলমান চাষির ভোটের জোরে। সুতরাং, এবারকার আইনসভায় চাষির দাবি অগ্রাহ্য করে চলা আর সম্ভব হল না। ১৯৩৮ সালে ১৮৮৫ সালের টেনেসি আইন আবার সংশোধন হল। ১৯২৮ সালের আইনে চাষিরা গাছ কেটে নেবার, জমিতে ইচ্ছামতো পুকুর কাটবার ও পাকা বাড়ি তোলার যে সব স্বত্ব পেয়েছিল তা বহাল রইল। কিন্তু এবারের আইনে জমি বেচা-কেনার অধিকার হল নির্বাধি ও নিরুপদ্রব্য; ১৯২৮ সালের আইনে দেওয়া জমিদারের নজর পাওয়ার স্বত্ব ও ক্রেতার কাছ থেকে কিনে নেবার স্বত্ব দু-ই বাতিল হল। জমিদার যেমন তার জমিদারি বিক্রি করতে পারে, গভর্নমেন্টের কোনও দাবিদাওয়ার ভয় না রেখে, চাষিও তার জমি বিক্রির স্বত্ব পেল জমিদারের কোনও দাবি মেটাবার দায়ে না থেকে। চাষের জমির খাজনা বাড়াবার পূর্বের বিধি আইনের পৃষ্ঠায় বহাল থাকল বটে, কিন্তু বিধান হল ১৯৩৭ সাল থেকে দশ বছরের জন্য ও-সব বিধির প্রয়োগ বন্ধ থাকবে, অর্থাৎ ওই সময়ের মধ্যে জমির খাজনা আর বাড়ানো চলবে না। এই সাময়িক বাধা যে জমিদারের খাজনা বাড়াবার স্বত্বের লোপ বা বিশেষ সংকোচের সূচনা, তাতে কারও সন্দেহ নেই। এবং এই লোপ বা সংকোচের আইন বিধিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ওই দশ বছরের মেয়াদ যে মাঝে মাঝে আইন করে বাড়ানো হবে, তাও নিঃসন্দেহ।
১৮৮৫ সালের টেনেন্সি আইন পাশের প্রাককালে কবি হেমচন্দ্ৰ লিখেছিলেন–
টেনেন্সি বিল নামে আইন হচ্ছে তৈয়ার করা,
গয়া গঙ্গা গদাধর ভূস্বামী প্রজারা।
অর্থাৎ, ও আইনে চাষের জমিতে জমিদারদের মালিকি স্বত্বের গয়াশ্রাদ্ধ হয়ে গেল। সে আইনে তেমন কিছুই হয়নি, মাসিক শ্ৰাদ্ধও নয়। কিন্তু ১৯৩৮ সালের আইনে গায়াশ্রাদ্ধ হয়ে জমিদারের মালিকি স্বত্বের প্ৰেতাত্মা দূর না হোক, সে স্বত্বের যে সপিণ্ডীকরণ হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুকে ইচ্ছামতো অগুন্তি রকমে ব্যবহারে লাগাবার অধিকার যদি হয় মালিকি স্বত্ব তবে বাংলাদেশের চাষের জমিতে মালিকি স্বত্ব মোটামুটি এসেছে চাষির হাতে, নির্দিষ্ট খাজনা পাবার অধিকার ছাড়া আর বেশি কিছু অধিকার জমিদারের অবশিষ্ট নেই। ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনের সমসাময়িক রােয়ত-আন্দোলনে চাষিদের পক্ষে যে সব দাবি উপস্থিত করা হয়েছিল, ১৯৩৮ সালে তার প্রায় সমস্তই পূরণ হয়েছে। কিন্তু বাংলার চাষির গোয়াল যদি গোরুতে ভরতি হয়ে থাকে, আর তার গোলা যদি ধানে বোঝাই হয়ে গিয়ে থাকে–তার একমাত্র কারণ, সে গোয়াল ও গোলা নিতান্তই ছোট; পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। চাষের জমির মালিকি স্বত্ব পেয়ে বাংলার চাষির আর্থিক দুৰ্দশা কিছুই ঘোচেনি। সোনার বাংলা কবিতা ও গানের ‘সোনার বাংলা’ রয়ে গেছে।
আকাঙ্ক্ষার পূরণে আশাভঙ্গের এই রহস্যের মূল খুঁজলেই চাষের জমির স্বত্ব নিয়ে চাষি ও জমিদারের ঝগড়ার প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যাবে; এবং বোঝা যাবে, এই বিবাদের মীমাংসায়, সে মীমাংসা সম্পূর্ণ চাষির অনুকূলে হলেও, কোন চাষির ও দেশের বেশি কিছু উপকার সম্ভব নয়। চাষের জমির মালিকি স্বত্বের ভাগ-বাটোয়ারার যে-সব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি সেগুলি অতীত কালের বাতিল প্রশ্ন। যথাকলে তার সদুত্তরের ফল কি হাত সে ঐতিহাসিক আলোচনা আজ নিম্ফল। চাষের জমি নিয়ে বর্তমানের প্রশ্ন অন্য প্রশ্ন। প্ৰাচীন প্রশ্নের মীমাংসা তার কোনও উত্তর নয়।
আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের আরম্ভ, বাংলাদেশে যখন ইংরেজের শাসন ও আইন কায়েম হচ্ছে, সে হল ইংল্যান্ডে ধনতান্ত্রিক যুগপরিবর্তনের কাল। পূর্বকালের ধনতন্ত্র আবর্তিত হত। জমির উৎপন্ন ফসলকে কেন্দ্র করে। এই ফসলের যত বড় অংশের উপর যার যতখানি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মালিকত্ব সে ছিল তত বড় ধনী। সুতরাং, প্রাচীন ঐতিহাসিক কারণে যে অভিজাত ‘সম্প্রদায় ছিল জমির মালিক, সেই সম্প্রদায় ছিল দেশের ধনী সম্প্রদায়। এবং এই সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধিই ছিল রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য, কারণ তারাই ছিল রাষ্ট্রের কর্ণধার। দেশে যে প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হত তা হত শিল্পীর নিজের বাড়িতে, শিষ্যসকরোদদের সহায়তায়। আর, তার ক্ৰয়-বিক্রয় সচরাচর আবদ্ধ থাকত আশপাশের ছোট গণ্ডির মধ্যে। যে-সব বিশেষ শিল্পদ্রব্য তৈরি হত অল্প জায়গায়, কিন্তু যার চাহিদা থাকত দেশময় বা দেশের বাইরেও, ব্যবসায়ী মহাজনেরা শিল্পীদের বাড়ি বাড়ি তা সংগ্ৰহ করে সে চাহিদা মেটোত, এবং সে-ব্যবসায়ের মুনাফায় তারাই ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের পর দেশের ধনী লোক। এই সময় ইংল্যান্ডের করিতকর্মী লোক আবিষ্কার করল যে, শিল্পীদের বাড়ি বাড়ি শিল্পদ্রব্য সংগ্ৰহ না করে যদি অনেক শিল্পীকে এক জায়গায় এনে তাদের মজুরি দিয়ে জিনিস তৈরি করিয়ে নেওয়া যায়, তবে অল্প খরচে ও অল্প সময়ে জিনিস তৈয়ারি হয়। অনেক বেশি, এবং তা বেচে লাভ হয় আরও বেশি। ইংল্যান্ডের বহু জায়গায় ওয়ার্কশপ গড়ে উঠল, সেখানে পূর্বের দেশময়-ছড়ানো স্বাধীন শিল্পীরা এক জায়গায় জমায়েত হয়ে অন্যের কাছ থেকে মজুরি নিয়ে ফরমায়েশমতো জিনিস তৈরি করে দিতে লাগল। যাঁরা ছিল শিল্পী, craftsman, তাঁরা হল মজুরির চাকরি, workman; যাঁরা ছিল দ্রব্যসংগ্রহ ও কেনাবেচার মহাজন, merchant, তাঁরা হল শিল্পীর শ্রমের মজুরিদাতা মালিক, industrialist এর নাম industrial revolution। হাতের কাজ কলে করা, কল চালাতে স্টিম ইঞ্জিন লাগানো, এগুলি industrial revolution-এর গোড়ার কথা নয়। ওগুলি নুতন শিল্পোৎপাদন-ব্যবস্থাকে সহস্ৰগুণ ফলপ্ৰসূ করেছে, এবং সে ব্যবস্থায় মালিকদের মুনাফা বাড়িয়েছে তার চেয়ে বেশিগুণ; এবং এই নূতন শিল্পব্যবস্থার ফলেই কল ও ইঞ্জিন কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু industrial revolution-এর গোড়ার কথা হচ্ছে, শিল্পীদের মজুর করে একসঙ্গে খাটিয়ে তাদের কাজের নিট লাভ অল্প লোকে বেঁটে নেওয়া। কলা ও ইঞ্জিন কাজে লাগানোর পূর্বেই industrial revolution আরম্ভ হয়েছিল। কল ও ইঞ্জিনের আবিষ্কার অনেকটাই ওই revolution-এর ফল, তার কারণ নয়।
এই নুতন শিল্পব্যবস্থায় ইংল্যান্ডের শিল্পনেতাদের হাতে যে অর্থ জমা হতে লাগল তাতে তারাই হয়ে উঠল। সে দেশের প্রধান ধনী সম্প্রদায়। তাদের ধনের পরিমাণ জমিসর্বস্ব প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায়ের ধনকে ছাড়িয়ে যেতে লাগল। তার ফলে রাষ্ট্রে ও সমাজে এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাকে ছাড়িয়ে না গেলেও, ইংল্যান্ডে। আজও তা যায়নি, তাদের স্বার্থসিদ্ধির অনুকুল ব্যবস্থা প্রণয়ন রাষ্ট্রের একটা প্রধান কাজ হল এবং তার অনুকুল মনোভাবের সৃষ্টি ও প্রচার ইংরেজ ধনবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা উৎসাহের সঙ্গে করতে লাগলেন। কার্ল মার্কসের কথায়, সমাজের তৎকালীন এই সবচেয়ে প্ৰগতিশীল ধনোৎপাদক বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের প্রয়োজনকে আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির চিরন্তন মূলসূত্র বলে পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করাতে ও বিশ্বাস করতে লাগলেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল নূতন প্রথায় শিল্পসৃষ্টির জন্য যা কিছু উপকরণ তার উপর শিল্পনেতাদের অবাধ অধিকার। এ উৰ্দ্ধকরণ দু-রকমের; মানুষের শ্রম ও সে-শ্রম প্রয়োগের জন্য জমি ও জিনিস। মানুষের শ্রমকে ইচ্ছামতো আয়ত্তে আনার যে-কৌশল আবিষ্কার হল তার নাম freedom of contract, চুক্তিতে আবদ্ধ হবার অবাধ স্বাধীনতা। এবং, সে স্বাধীনতার প্রয়োগে একবার চুক্তিতে বদ্ধ হলে সে চুক্তি যাতে ভঙ্গ না হয় সে জন্য রাষ্ট্রীয় শাসন। এর নাম sanctity of contract, চুক্তির পবিত্রতা, অর্থাৎ চুক্তিভঙ্গ পাপের আইনের দণ্ডে প্ৰায়শ্চিত্ত। শিল্পনেতারা সংখ্যায় অল্প এবং পকেট ভরতি থাকায় পেটে ক্ষুধার জ্বালা নেই। তাদের পক্ষে দল বেঁধে শ্রমিকদের দাবি পেটভ্যতার সীমানায় ঠেকিয়ে রাখা খুব কঠিন নয়। শ্রমিকেরা সংখ্যায় বহু, এবং পূর্ব আমলের কুটিরশিল্প নূতন আমলের ফ্যাক্টরিশিল্পে ধ্বংস হওয়ায় বেকার, পেটে ক্ষুধার জ্বালা। সুতরাং, স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগে শিল্পনেতাদের শর্তেই রাজি হওয়া ছাড়া তাদের অন্য গতি ছিল না। গত শতাব্দীর শেষ দিকে যখন শ্রমিকেরা দল বাঁধতে শিখে নিজেদের শ্রম বিক্রির শর্তের দাবি উপস্থিত করতে আরম্ভ করল তখন সে স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগকে দলবদ্ধ গুন্ডামি নাম দিয়ে ইংল্যান্ডের আইন-আদালত ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়নি। দলবদ্ধ শ্রমিকদের চাপে এ স্বাধীনতাকে অনেকটা স্বীকার করতে হয়েছে। এবং চুক্তির স্বাধীনতা ও পবিত্রতা, freedom ও sanctity, বহু রকমে খৰ্ব করে অনেক আইন-কানুন গড়তে হয়েছে যার সবটাই শ্রমিকদের হিতে নয়। দু’পক্ষের স্বাধীন চুক্তির লড়াই এখন চলছে। যে পক্ষই জয়ী হোক চুক্তির স্বাধীনতার জয় হবে না। কিন্তু এ অনেক পরের কথা। আঠারো শতকের শেষে ও উনিশ শতকের আরম্ভে ইংল্যান্ডে অবাধ চুক্তিবাদের ছিল জয়জয়কার, কারণ তার সুফলভাগী ছিল নূতন ধনশ্ৰষ্টা সম্প্রদায়, এবং সে ধনের পরিমাণ পূর্ব পূর্ব কালের তুলনায় এত বেশি যে, তার চমক কাটিয়ে তার সৃষ্টিকৌশলের গলদের দিকে দৃষ্টি পড়ার তখনও সময় নয়।
শিল্পীসৃষ্টির অন্য উপকরণ, জমি ও জিনিসে অবাধ অধিকারের যে-তত্ত্ব আবিষ্কার হল তার মূলকথা হচ্ছে কোনও বস্তু থেকে সবচেয়ে বেশি কাজ আদায়ের উপায়–কোনও লোককে সে-বস্তু যাদৃচ্ছিা ব্যবহারের ক্ষমতা দেওয়া। এই ক্ষমতা পেলেই সে লোক ওই বস্তু থেকে যাতে সবচেয়ে লাভ হয় সে-চেষ্টায় প্রাণপাত করবে, না পেলে করবে না। এ-তত্ত্বের নাম magic of property, মালিকত্বের মহামায়া–যার প্রভাবে মালিক পাথরে ফুল ফোটায়, মরুভূমিতে ফসল ফলায়। সুতরাং দেশের জমি ও জিনিস দেশের সবচেয়ে বেশি হিতে লাগাতে হলে তার কৌশল হচ্ছে ওদের মালিকি স্বত্ব দেশের কতক লোকের মধ্যে বেঁটে দেওয়া, এবং মালিকদের ইচ্ছামতো ব্যবহারের পথে যথাসম্ভব কম বাধা দেওয়া। তা হলেই প্ৰতি মালিক তার মালিকি স্বত্বের জমি ও জিনিসকে নিজের সবচেয়ে হিতকর কাজে লাগাতে চেষ্টা ও পরিশ্রমের ত্রুটি করবে না। এবং তাদের হিতের যোগফল সমাজের হিত, কারণ সমাজ ব্যক্তিরই সমষ্টি।
কি অবাধ চুক্তিবাদ, কি মালিকত্বের মায়াবাদ কোনওটির প্রয়োগই কেবল শিল্পনেতাদের প্রয়োজনে বদ্ধ থাকল না। ওদের মেনে নেওয়া হয়েছিল উন্নতিশীল সমাজের আর্থিক উর্ধগতির দুটি অপরিহার্য মূলসূত্র বলে। সুতরাং যেখানেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেখানেই ওদের প্রয়োগ হতে লাগল। অভিজাত সম্প্রদায় ছিলেন দেশের জমির মালিক। তাদের অধীনে চাষিরা চাষ করত, অপর লোক অন্য রকমে জমিকে কাজে লাগাত। এই চাষিদের ও অন্য লোকদের জমিতে অনেক রকম স্বত্ব স্বীকৃত হয়ে আসছিল যাদের উৎপত্তি মালিকের সঙ্গে চুক্তিতে নয়, পূর্ব প্রচলিত প্রথায়। মালিক ইচ্ছা করলেই সে সব স্বত্ব রদ কি বদল করতে পারতেন না। জমির মালিকের জমিকে যাদৃচ্ছিা ব্যবহারের ক্ষমতার মধ্যে এ সব স্বত্ব খাপ খায় না। এবং চুক্তিবাদের মূলতত্ত্বের সঙ্গেও এদের বিরোধ; সে-তত্ত্ব হচ্ছে উন্নতিশীল সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের আর্থিক সম্বন্ধের বুনিয়াদ হয় চুক্তি, আর স্থিতিশীল সমাজেই তা হয় চুক্তিনিরপেক্ষ প্রথা। সুতরাং অন্য সব লোকের স্বত্বের খাতিরে জমির ব্যবহারে মালিকের যে-সব বাধা ছিল উর্ধর্বগতি সমাজের অনুপযোগী প্রাচীন ফিউডাল ব্যবস্থা বলে তাদের দূর করা হল। নিজের যাতে সবচেয়ে লাভ হয় জমিকে তেমন ব্যবহারে লাগাতে মালিকের কোনও বাধা থাকল না। ইংল্যান্ডে চাষের জমির মালিক অনেকে দেখলেন যে, জমি থেকে চাষিদের বিদায় করে যদি সেখানে ভেড়া পোষা যায়। তবে পশম বেচে লাভ হয় অনেক বেশি। সুতরাং চাষের খেত ভেড়া চরানোর মাঠ হল। উৎখাত চাষিরা পেটের দায়ে শিল্পনেতাদের দরজায় ভিড় করে জমা হতে লাগল মজুরি বেচার জন্য। এবং, শ্রমিকের সংখ্যাবাহুল্যে শিল্পনেতারা খুব কম দামেই শ্রম কিনতে লাগলেন। এই স্বল্প মূল্যের শ্রমে তৈরি শিল্পদ্রব্য, মায় পশমের কাপড়, প্রতিদ্বন্দ্বহীন পৃথিবীর বাজারে বিক্রি হয়ে মুনাফা আসতে লাগল বেশ মোটা রকম। ওই মুনাফার এক অংশের বদলে বিদেশ থেকে ইংল্যান্ডে শস্য আমদানি হতে লাগল, তার পরিমাণ ভেড়া-চরানো চাষের খেতের শস্যের চেয়ে অনেক বেশি, তা দামেও দেশে-উৎপন্ন শস্যের চেয়ে অনেক সস্তা। উন্নতির চাকা যে জোরে ঘুরছে, তাতে কারও সন্দেহ থাকল না। আজ যখন ইংল্যান্ডের শিল্পদ্রব্যকে পৃথিবীর বাজারে নানা দেশের শিল্পদ্রব্যের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করতে হয়, যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষ দেশে খাদ্য আমদানির পথে মারাত্মক বাধা জন্মায়, তখন বাধ্য হযে চাষি-বনাম–ভেড়া নীতির অনেক পরিবর্তন করতে হচ্ছে। দেশের চাষকে সুবিধা ও উৎসাহ দেবার জন্য চাষের জমিতে চাষির এমন অনেক স্বত্ব স্বীকার করতে হচ্ছে যা মালিকের স্বাধীন ইচ্ছা-পরিচালনার বাধা। কিন্তু এ সব আজকের দিনের কথা। শিল্পবিপ্লবের আদিকালে ও-নীতির বিরুদ্ধে যাঁরা কিছু কথা বলেছিল তাঁরা ধনবিজ্ঞানী পণ্ডিত নয়, কবি কি ভাবুক গোছের মানুষ, অর্থাৎ ‘হৃদয়তাপের ভাপে ভরা ফানুস’। স্বভাবতই তাদের কথায় কেউ কান দেয়নি।
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে নবলব্ধ বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের সুরাহার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে সব কর্মচারী চাষের জমির বিলি-বন্দোবস্ত নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন, স্বদেশীয় মালিকি স্বত্বের এই অবাধ পরিচালনার আদর্শে এবং তার অবশ্যম্ভাবী সুফল সম্বন্ধে একান্ত বিশ্বাসে তাদের মন ও বুদ্ধি ছিল ভরপুর। সুতরাং এদেশের চাষের জমিতে নানা লোকের নানা রকম স্বত্বের দাবিতে, এবং তার মধ্যে জমির মালিকের নিঃসন্দেহ সন্ধান না। পাওয়াতে, তারঁা একটু দিশাহারা হলেন। এমন কাকেও দেখা গেল না যে, জমির যথেচ্ছ ব্যবহারে তার-অধিকার আছে এবং অন্য লোকের জমিতে যা কিছু স্বত্ব তা তার সঙ্গেই চুক্তির ফল। এ ব্যাপার তাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়কার তর্ক বিতর্কের একজন প্রধান নায়ক সার জন শোর লিখলেন
The most cursory observation shows the situation of things in this country to he singularly confused. The relation of a zamindar to government, and of a ryot to a zamindar, is neither that of a proprietor nor of a vassal; but a compound of both. The former performs acts of authority, unconnected with proprietary–the latter has rights without real property. Much time will, fear, elapse before we can establish a system, perfectly consistent in all its parts, and before we can reduce the compound relation of a Zamindar to goverinent, and of a ryot to a zamindar to the simple principles of land lord and tenant.
শ্ৰীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কথায়, ‘শোর সাহেবের কথাই প্রমাণ যে, এদেশে জমিদারের সঙ্গে রায়তের সম্বন্ধ তার কাছে বড়ই গোলমেলে ঠেকেছিল। কাজেই যা গোল তাকে তিনি চৌকোশ করবার প্রস্তাব করেছিলেন।’ অৰ্থাৎ মালিক যখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তখন গোলমাল দূর করার একমাত্র উপায় মালিক সৃষ্টি করা। তবেই যা এলোমেলো তা হবে সুসংগত, যা জটিল তা হবে সরল। ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় জমিদারদের বাংলার চাষের জমির মালিক করা হল। জমিদারেরা যখন হলেন চাষের জমির মালিক তখন তাঁরা যে সে-জমি থেকে যত বেশি সম্ভব লাভের চেষ্টায় মনোযোগী হবেন, অর্থাৎ জমিতে যত বেশি। ফসল ফলে সেই কাজে বুদ্ধি ও শক্তি নিয়োগ করবেন, তাতে আর সন্দেহ থাকল না। কারণ মালিকি স্বত্বের ভেলকি যাবে কোথায়। Magic of property-তে এই আস্থাইলট কর্নওয়ালিস প্রকাশ করেছেন চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্তের সনন্দ ১৭৯৩ সালের ১ নং কানুনে–
The Governor-General in Council trusts that the proprietors of land, sensible of the benefits conferred upon them by the public assessment being fixed for ever, will exert themselves in the cultivation of their lands, upon the certainty that they will enjoy exclusively the fruits of their own good management and industry.
যে জমিদারদের জমির মালিক করা হল তাদের কর্মে উৎসাহ ও শক্তি কতটা, লাটসাহেবের তা অজানা ছিল না। যে সার জন শোর তাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ওকালতি করেছিলেন। ১৭৮৯ সালে তিনি লিখেছিলেন–
It is allowed that the Zamindars are, generally speaking, grossly ignorant of their true interests, and of all that relates to their estates.
পুনশ্চ–
If a review of the Zamindars of Bengal were made, it would be found that very few are duly qualified for the management of their hereditary lands, and that in general they are ill-educated for this task, ignorant of the common forms of business, and of the modes of transacting it; inattentive of the conduct of it, even when their own interests are immediately at stake, and indisposed to undertake it.
জমিদারদের এ বর্ণনায় যদি কেউ বিস্ময় ও সন্দেহ প্ৰকাশ করে তাদের লক্ষ্য করে শোর সাহেব লিখলেন
They are the result of my own experience, combined with that of others; and I fear no refutation of them, where they are examined with candour, and can be ascertained by local reference and information.
এই প্রকৃতির লোক জমির মালিকি স্বত্ব পেয়েই জড়তা ত্যাগ করে, অজ্ঞতা ও নিৰ্বদ্ধি কাটিয়ে চাষের উন্নতিতে উৎসাহের সঙ্গে লেগে যাবে, এ বিশ্বাস ম্যাজিকে বিশ্বাস ছাড়া অন্য কিছু নয়। ১৭৯৩ সালের পর দেড়শো বছর কেটেছে। এর মধ্যে জমিদারি হাতবদল হয়েছে অনেক। কিন্তু লক্ষ বিঘা জমির জমিদার থেকে একশো বিঘা জমির জমিদার পর্যন্ত কেউই চাষের কাজে নজর দিয়ে চাষ হবার মতো ছোটলোকী বুদ্ধির কখনও পরিচয় দেননি। পেটের দায়ে ও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় চাষি যে-ফসল ফলিয়েছে তার যতটা সম্ভব বড় অংশ খাজনায় ও খরচ-মাথট-ভিক্ষা ইত্যাদি ফিকিরে আদায় করতে পারে এমন নায়েব-গোমস্তা বহালে তাঁরা তৎপরতা মন্দ দেখাননি; কিন্তু এ ফসল যাতে বাড়ে সে-চেষ্টায় কখনও অর্থ কি সামৰ্থ্য খরচ করেননি। ইংল্যান্ডের কর্মক্ষম ও উৎসাহী শিল্পনেতারা লাভের লোভে ধনসৃষ্টির কাজে অনেক জিনিসে অবাধ মালিকি স্বত্ব দাবি করেছিল, এবং তা পেয়ে ধনের পরিমাণ ও লাভের পরিমাণ অনেক বাড়িয়েছিল। সুতরাং যে-কিছুতে যে-কোনওজনকে মালিকি স্বত্ব দিলে ধন সৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে যাবে, এটা ন্যায়ের এমন সাধারণ ফাকি যে ন্যায়শাস্ত্রের প্রাথমিক পাঠ যার পড়া আছে সেই বুঝতে পারে। কিন্তু, ওই ফাকিকেই যুক্তি মনে করে সমাজ ও রাষ্ট্রের অনেক কাজ চলছে। সে যাই হোক, পশ্চিমের ম্যাজিক পূৰ্বদেশে কেরামতি দেখাতে পারলে না। মাটির দোষ।
ইংরেজ-শাসনের আরম্ভে চাষের জমির মালিকি স্বত্ব জমিদারদের না দিয়ে চাষিদের দিলে (তার পূর্বে চাষিরাই জমির মালিক ছিল কি না সে-তর্ক ছেড়ে দিচ্ছি) চাষিরা যে পরবর্তী কালের অনেক অন্যায় ও জুলুম থেকে রক্ষা পেত। তাতে সন্দেহ নেই। ফলে, চাষির আত্মসম্মান অনেকটা অক্ষুন্ন থাকত, এবং সম্ভব, বাংলার চাষি-সম্প্রদায় এখনকার চেয়ে স্বাধীন ও দৃঢ়চিত্ত হত। কিন্তু আজ তাঁরা যে ফসল ফলাচ্ছে মালিকি স্বত্বের জাদুতে তার চেয়ে প্রকারে ও পরিমাণে ভাল ও বেশি ফসল ফলাত কিনা তাতে সন্দেহ আছে। প্ৰাণের তাগিদে চাষি নালায়েক জমিতে চাষ বিস্তৃত করেছে জমিদারকে নজর ও খাজনা দিয়ে। লাভের আশায় নূতন ফসল চাষ করেছে, কি অল্প জমিতে যে-ফসলের চাষ হত তার আবাদ অনেকগুণ বাড়িয়েছে–যেমন পাট ও গোল-আলু। এতে জমিদারের কোনও সাহায্য পায়নি, যদি সরকারের সাহায্য পেয়ে থাকে তা নগণ্য। চাষির অতি সামান্য যা উদ্ধৃত্ত, এ দেশের কৃষিব তাই মূলধন। পুরুষপরম্পরাগত বহু প্ৰাচীন যে জ্ঞান ও কৌশল চাষি বাপপিতামহের কাছে শেখে এ দেশে তাই কৃষিবিদ্যা। চাষের যে যন্ত্রপাতি বাংলাব চাষি আজ ব্যবহার করে বহু শতাব্দী ধরে তার কোনও পরিবর্তন হয়নি। দেড়শো বছর পূর্বে বাংলাদেশের চাষে যে মূলধন, বিদ্যাবুদ্ধি ও কৌশলের প্রয়োগ হত দেড়শো বছর পরেও তাই হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য কোনও বদল হয়নি। জমিদারেরা চাষের জমির মালিকি স্বত্ব পেয়ে এর কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র উন্নতির চেষ্টা করেননি। তাদের সামাজিক পদমর্যাদা যাই হোক, দেশের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মোটা মুনাফায় রাজস্বের ইজারাদার ছাড়া তাঁরা আর কিছু নন। এবং এক প্রাচীন দলিল ছাড়া তাদের টিকিয়ে রাখার অন্য কোনও কৈফিয়তও নেই। কিন্তু মালিকি স্বত্ব জমিদারের হাত থেকে চাষির হাতে তুলে দিলেই চাষের উন্নতি হয়ে দেশ কৃষিসম্পদে ভরে যাবে, এমন বিশ্বাস কর্নওয়ালিসি ম্যাজিক-বিশ্বাসেরই চাষি-সংস্করণ। মালিকি জাদু জমিদারের কাছে ফলেনি ইচ্ছার অভাবে, চাষির কাছে ফলবে না ক্ষমতার অভাবে।
বাংলায় ও ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসনের আমলেই অন্য অনেক সভ্যদেশে কৃষির জন্মান্তর ঘটেছে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও সমাধান পশ্চিম ইউরোপের মনে ও জীবনে যুগান্তর এনেছে মানুষের জীবনযাত্রায় তার ব্যাপক প্রয়োগ আরম্ভ হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই। কৃষিকার্যে তার প্রয়োগ আরম্ভ হয়েছে তারও অনেক পরে, মোটামুটি গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে। চিরস্থায়ী বন্দােবস্তের সময় যে বিদ্যায় ও কৌশলে এদেশের চাষের জমি চাষ হত, অন্য সভ্যদেশের কৃষিবিদ্যা ও কৌশল তা থেকে বেশি। তফাত ছিল না। আজ আমরা বক্তৃতায় প্রবন্ধে প্রদর্শনীতে ছক কেটে তুলনায় দেখাই, নানা দেশের বিঘা প্রতি ফসল কত বেশি, আমাদের দেশে কত কম। সকলেই জানি, তার কারণ সে-সব দেশে কৃষির সহায় নূতন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কৌশল, আর সে জ্ঞান ও কৌশলের প্রয়োগ আমাদের দেশের কৃষিতে নেই। বাংলার ও ভারতবর্ষের চাষের জমির আজ প্রথম প্রয়োজন ও প্রধান সমস্যা–এই নুতন জ্ঞান ও কৌশল কৃষির কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করা। দেশে খাদ্যশস্যের যে-ফলন হয় গুণে ও পরিমাণে দেশের সমস্ত লোককে সুস্থ ও কর্মঠ শরীরে বঁচিয়ে রাখার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়; লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে এই অপ্রাচুর্যের পরিমাণ বেড়ে চলেছে। এই লোকের অধিকাংশ হচ্ছে চাষি ও তাদের পরিবার। অন্য কৃষিপণ্য যা উৎপন্ন হয়। চাষির ও দেশের দারিদ্র্য তাতে ঘোচে না। এ অবস্থার একমাত্র প্রতিকার চাষের কাজে নূতন জ্ঞানবিজ্ঞান-কৌশলের প্রয়োগ, নানা সভ্যদেশ আজ যা করছে। জমির মালিক জমিদারেরা এ-কাজে কোনও সাহায্য করবেন, এমন কল্পনা কেউ করে না। চাষিরা নিজে থেকে এতে উদ্যোগী হবে, সে ভরসাও কারও নেই–জমির ভোগদখলে যত সুবিধাই তাদের হোক আর জমির খাজনার হার যত কমানোই হোক। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এদেশে বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রবর্তনে কি কি প্রয়োজন তার তালিকা মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করে থাকেন। জমিতে জৈব ও রাসায়নিক সার দেওয়া, উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার, জলসেচ ও জলনিকাশের ব্যবস্থা, ভূমি-উদ্ভিদ-আবহ-বিদ্যার নানা তথ্যের ব্যাবহারিক প্রয়োগ। সংবাদপত্র থেকে চোখ তুলে যখন তাকাই দেশের চাষির দিকে–তার দাবিদ্র্য, তার অস্বাস্থ্য, তার অশিক্ষা, এবং ফলে তার মনের নিদারুণ দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা দেখে তখন ওইসব ফর্দ ও ফিরিস্তি নির্মম পরিহাস বলে মনে হয়। এ চেষ্টা সার্থক হতে পারে। যদি সমস্ত দেশের শুভবুদ্ধি ও কর্মের উৎসাহ উদ্ধৃদ্ধ হয়, এবং দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাষ্ট্রশক্তির মধ্য দিয়ে সে-বুদ্ধি ও উৎসাহ যদি আত্মপ্রকাশের পথ পায়। চাষের জমিতে মালিকি স্বত্বের লোভ দেখিয়ে এ ভার শ্রেণি-বিশেষকে দেওয়া চলে না, দিয়ে ফললাভের আশা করাও চরম মুঢ়তা।
আমাদের দেশে যে সরকারি কৃষিশালা কি পরীক্ষাগার নেই, তা নয়; দু-চারটে আছে। এ দেশে বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রবর্তনে চাষিকে সাহায্য করা তাদের কাজ নয়। নূতন জ্ঞানের আবিষ্কারে ও অথবা তা কাজে লাগাবার উপায়-উদ্ভাবনেও এদের সার্থকতা নয়। এদেশে ইংরেজ-শাসন যে পূর্বকালের রাজশাসনের মতো শান্তি ও শৃঙ্খলা-রক্ষার উদ্দেশ্যে সৈন্য ও পুলিশ-শাসন মাত্র নয়, একালের আদর্শ অনুযায়ী দেশবাসীর সর্ব-হিতে-রত মঙ্গলময ব্যবস্থা–তারই চিহ্নস্বরূপ এদের দাড় করিয়ে রাখা হয়। এগুলি প্ৰতীকমাত্র, বস্তু নয়। ছোট-বড় লাটের বক্তৃতার এরা উপাদান জোগায়। এবং প্রসঙ্গত, গুটিকয়েক ইংরেজের বড় মাহিয়ানায়, ও কয়েকজন ইংরেজিশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ভারতবাসীর ছোট মাহিয়ানায় চাকুরি সৃষ্টি করে। অথচ, কৃষিতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কৌশলের প্রয়োগে ফসলের প্রকার ও পরিমাণ বহুগুণে বাড়ানো খুব বেশিদিনের কাজ নয়। চোখের সামনে সোভিয়েট রুশিয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রাক-সোভিয়েট রুশিয়ায় কৃষির অবস্থা প্রায় আমাদের দেশের মতোই ছিল। মাত্র পাঁচিশ বছরের চেষ্টার ফল আজ সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ব্যাবহারিক প্রয়োগ সভ্যতার বহিরঙ্গ। তার প্রসার মানুষের বুদ্ধির স্তরে। সে-স্তর ছাড়িয়ে অন্তর্মুখীন হওয়ার তার প্রয়োজন নেই। সেইজন্য তাকে আয়ত্ত করতেও জাতির সময় লাগে না।
কিন্তু চাষের জমিতে এই বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রবর্তন দেশের সমগ্ৰ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্রভাবে ঘটানো সম্ভব নয়। এই আংশিক পরিবর্তন নির্ভর করে সমগ্রের গতি ও পরিণতির উপর। যেদিন আমাদের দেশের ধনতান্ত্রিক জীবনকে নতুন পৃথিবীর উপযোগী করে ভেঙে গড়ার কাজ আরম্ভ হবে, কৃষির উন্নতির প্রকৃত চেষ্টাও সেই দিন আরম্ভ হবে, তার পূর্বে নয়। সোভিয়েট রুশিয়ার দৃষ্টান্তই প্রত্যক্ষ প্ৰমাণ। সেই ভাঙা-গড়ার মধ্যে চাষের জমির দখল-ভোগের ব্যবস্থা কেমন রূপ নেবে বা নেওয়া উচিত হবে, তার আগাম নকশা বা blue print তৈরি করতে বসা আজ পণ্ডশ্রম। যতদিন আমাদের দেশের হিতচিন্তার গুরুভার বিদেশিকেই কষ্ট করে বহন করতে হবে, ততদিন কমিশন বসবে, সমুদ্রপার থেকে মোট ভাতায় অজ্ঞাতনামা বিশেষজ্ঞেরা আসবেন, রিপোর্ট তৈরি হবে, চাকুরির সৃষ্টি হবে, আর দেশের অবস্থা ও দুরবস্থা যেমন আছে তেমনি থাকবে। তাই স্বাভাবিক। বিদেশির শ্রম লাঘব করে দেশেব ধনসৃষ্টি ও বণ্টনের ভার যেদিন দেশের লোককেই নিতে হবে তখন শুভবুদ্ধির যদি নিতান্ত অভাব না হয়, তবে চাষের জমির মালিকি স্বত্ব–ব্যবহার, অব্যবহার ও অপব্যবহারের অধিকার–কেউ পাবে না। সে নুতন ব্যবস্থার প্রধান প্র৩িবন্ধক হবে বর্তমান চাষি সম্প্রদায়; কারণ, চাষের জমির মালিকি স্বত্বের বড় অংশ তাঁরা পেয়েছে, তার চেয়ে বড় আর কিছু তাঁরা পায়নি এবং কল্পনা করতেও শেখেনি। সোভিয়েট রুশিয়ার ইতিহাস তারও দৃষ্টান্ত।